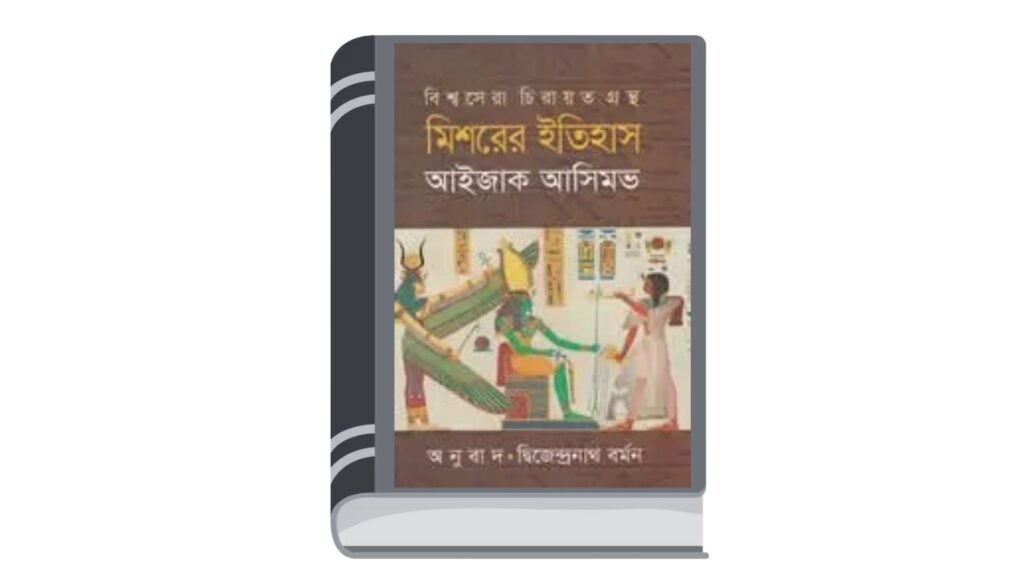০২. প্রাচীন মিশর
২. প্রাচীন মিশর
ইতিহাস
সাধারণভাবে, মানব ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তিনটি উৎস থেকে উৎসারিত। প্রথমত কিছু উপকরণ যেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসের উৎসরূপে পেছনে ফেলে রাখা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আদি মানবের দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও মৃৎপাত্র, যে সবের অবশেষ লক্ষ লক্ষ বছর অতীতের উপর অস্পষ্ট আলোকপাত করে।
অবশ্য এসব অবশেষ অখণ্ড কাহিনীর ধারক হয়ে ওঠেনা। বরং এগুলি হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের আলোয় বই পড়ার চেষ্টার মতো। অবশ্য সম্পূর্ণ নেতিবাচকতার চাইতে বরং এটাও অনেক ভালো।
দ্বিতীয়ত পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলে আসা কাহিনী। তবে বার বার বলতে বলতে এর অধিকাংশই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে পুরাণ আর কল্পকথা যাকে কখনোই আক্ষরিক সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না, যদিও এর অনেকগুলির মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ সত্য লুকিয়ে আছে।
এভাবেই গ্রিক পুরাণে কথিত ট্রয়ের যুদ্ধ পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলে এসেছে। গ্রিকরা এগুলিকে গ্রহণযোগ্য ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছে। আসল সত্য লুকিয়ে আছে এদুয়ের মাঝখানে। গত শতাব্দীর পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে তথ্য মিলেছে যে হেমারে বর্ণিত অনেক কাহিনীই প্রকৃত ঘটনার কাছকাছি (হোমারে বর্ণিত দেবতাদের কাহিনী নিছক রূপকথা)।
সবশেষে রয়েছে লিখিত রেকর্ড, পৌরাণিক কাহিনীও যার অন্তর্গত। যখন এসব লিখিত বিষয় লেখকের সমসাময়িক ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেটা ঐতিহাসিক যে কোনো বিবরণের চাইতে অনেক বেশি সন্তোষজনক। এটাকে অবশ্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ লেখকেরা মিথ্যাও বলতে পারে বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে অথবা ভুলভ্রান্তিও থাকতে পারে। তাছাড়া তারা সঠিক লিখলেও পরবর্তিকালে কপি করার সময় অসাবধানতাবশত বিকৃত হয়ে থাকতে পারে। এক ঐতিহাসিকের সাথে আর এক ঐতিহাসিকের তুলনা করলে, বা সকল ঐতিহাসিক বিবরণের সাথে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের তুলনা করলেই ভুল বা বিকৃতিটা ধরা পড়বে।
তবু লিখিত বিবরণের চাইতে বিস্তারিত অন্য কোনো উৎস থেকে পাওয়া যায় না। মোটের উপর আমরা যখন মানুষের ইতিহাসের কথা বলি, তখন মূলত কোনো না কোনো লিখিত বিবরণের কথাই বোঝাতে চাই। লিখনপদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে কোনো বিশেষ অঞ্চলে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা ইতিহাসপূর্ব হলেও সভ্যতাপূর্ব নয়।
এভাবেই ৫০০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টপূর্ব মিশরীয় সভ্যতার বিবরণ আমাদের জ্ঞানের সীমায় এসেছে, তবে সভ্যতার এই পর্বটাকে অবশ্যই প্রাগৈতিহাসিক বলা যায়, কারণ তখনও লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি। একটি জাতির প্রাচীন ইতিহাস অবশ্যই অস্পষ্ট, ঝাপসা, আর ইতিহাসবিদরা দুঃখের সাথে এটা মেনে নিয়েছে। লিখন আবিষ্কারের পরও যখন সেটার পাঠোদ্ধার করা যায় না, তখন ঐতিহাসিকদের কাছে এটা কতটা হতাশাব্যঞ্জক তা সহজেই অনুমেয়। সামনে রয়েছে ইতিহাস তবে সেটা তালাবদ্ধ।
৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটাই ছিল মিশরের ইতিহাস, আর সত্যি বলতে কি অন্যান্য সভ্যতার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যেসব প্রাচীন ভাষা পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিল সেগুলি হলো ল্যাটিন, গ্রিক আর হিম। তাই গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রাচীন ইতিহাস লেখা হয়েছিল তা এসব ভাষাতেই, যে ইতিহাস পূর্ণ বা আংশিকভাবে আধুনিককাল পর্যন্ত চলে এসেছে। সে কারণেই, রোমান, গ্রিক এবং ইহুদি ইতিহাস আমরা ভালোভাবে জানতে পারি। এর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রাগৈতিহাসিক পুরাণকথা আমাদের কাছে চলে এসেছে।
মিশর অথবা ইউফ্রেতিস তাইগ্রিস এলাকার অধিবাসীদের প্রাচীন ইতিহাস তিনটি পরিচিত ভাষার কল্পকথার মাধ্যম ব্যতিত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অজানাই রয়ে যায়। তাদের সময়ে গ্রিকরা আমাদের সময়ের মতোই মিশরীয় ব্যাপারে তফাতই রয়ে যায়। তারাও হায়ারোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি, আর তাই কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিশরীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞই রয়ে যায়। তাদের সময়ে মিশরীয় সভ্যতা জীবন্তই ছিল আর বিকাশ লাভ করছিল। সেখানে ছিল মিশরীয় পুরোহিতরা, যারা বোধগম্যভাবে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন ছিল।
কৌতূহলী গ্রিক, যারা ৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর দল বেঁধে মিশরে ঢুকে পড়েছিল আর প্রাচীন মিশরের প্রকাণ্ড সব স্মৃতিচিহ্ন দেখে যাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত, আর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তারা খোঁজ খবর নিত, তবে মিশরীয় পুরোহিতরা ছিল সন্দেহপ্রবণ আর বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। সেজন্য তারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকত।
গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশর ভ্রমণে এসে পুরোহিতদের নিবিড়ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। তার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছিল আর এভাবে প্রাপ্ত তথ্য তার ইতিহাসের বইতে সন্নিবেশ করেছিলেন। তবে তার অধিকাংশ তথ্যই অবিশ্বাস্য মনে হয়। ধারণা করা যায় পুরোহিতরা ইচ্ছাকৃতভাবে অনভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের লেগ পুল করেছিল যিনি পুরোহিতদের যে কোনো তথ্য চিন্তাভাবনা না করেই গোগ্রাসে গিলেছিলেন।
অবশেষে ২৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যখন গ্রিকরা মিশরে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে, তখন একজন মিশরীয় পুরোহিত রক্ষণশীলতার খোলস থেকে বেরিয়ে নূতন শাসকের সুবিধার্থে নিজ হাতে গ্রিক ভাষায় মিশরের ইতিহাস লিখেছিলেন। অবশ্য সন্দেহ নাই, এতে তিনি পৌরোহিত্যের উৎসকেই ব্যবহার করেছিলেন। তার নাম ছিল মানেথো।
৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পরে কিছুদিনের জন্য মিশর সত্যিকারের ঐতিহাসিক মিশর হয়ে উঠতে পেরেছিল, এমনকি যদিও মানেথো আবশ্যিকভাবেই ছিলেন অসম্পূর্ণ এবং তার কাহিনী তিনি সাজিয়েছিলেন পক্ষপাতদুষ্ট মিশরীয় পুরোহিতের দৃষ্টিভঙ্গিতে।
অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত মানেথোর ইতিহাস বা তার উৎস কোনোটাই টিকে থাকেনি। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ঐতিহাসিক মিশর মানুষের অজ্ঞতার তিমিরে হারিয়ে যায়, আর পরবর্তী চৌদ্দশ বছর ধরে সেভাবেই রয়ে যায়। এমনটা নয় যে অজ্ঞতাটা ছিল চূড়ান্ত। মানেথোর লেখা থেকে অনেক লেখকই টুকরো টুকরোভাবে উদ্ধৃত করেছেন, যাদের লেখা এখন পর্যন্ত টিকে আছে। বিশেষ করে মিশরীয় শাসকদের একটা দীর্ঘ তালিকা, যা মানেথোর ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় মানেথোর ছয় শতাব্দী পরে জীবিত সিজারিয়ার একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক ইউসেবিয়াসের নাম। তবে এর মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ, যাকে মেটেই যথেষ্ট বলা চলে না। রাজার তালিকা শুধু ঐতিহাসিকদের তৃষ্ণাই বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তাতে করে পারিপার্শ্বিক অন্ধকারকেই আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।
অবশ্য এখনও মিশরের অনেক জায়গাতেই হায়ারোগ্লিফিক লিপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবে সেগুলি এখন কেউই আর পড়তে পারে না। সবকিছু হতাশাজনকভাবে রহস্যময়ই রয়ে গেছে।
এরপর ১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরে যুদ্ধাভিয়ান শুরু করেন। বোশার্দ নামে এক ফরাসি জেনারেলএকটা দুর্গ মেরামত করতে গিয়ে একটা কৃষ্ণপ্রস্তর দেখতে পান। দুৰ্গটা ছিল নীলের এক পশ্চিম শাখানদের মোহনায় অবস্থিত রশিদ শহরের নিকটবর্তী। ইউরোপীয়রা জেনারেলের নামানুসারে পাথরটার নাম দিয়েছিল “রোজেট্টা” পাথর।
রোজেট্টা পাথরে গ্রিক ভাষায় কিছু উৎকীর্ণ ছিল, যেখানে তারিখ দেওয়া ছিল ১৯৭ খ্রিস্টপূর্ব। লেখাটা নিজে থেকে তেমন কৌতূহলোদ্দীপক ছিল না, তবে যে বিষয়টা রোজেটা পাথরকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল তা হলো, সেখানে পাশাপাশি দুধরনের হায়ারোগ্লিফিকও ছিল। যেমনটা মনে হয়েছিল তিনটি আলাদা লিপিতে একই কথা লিখিত ছিল, তাহলে ধরে নেয়া যায় অন্য দুটি লিপি হায়ারোগ্লিফিকেরই অনুবাদ।
রোজেট্টা পাথরের পাঠোদ্ধার করেছিলেন ইংরেজ চিকিৎসক টমাস ইয়ং এবং ফরাসি পুরাতত্ত্ববিদ জঁ ফ্রাসোয়া শাপোলিয়োঁ। শাপোলিয়োঁ বিশেষ করে আর একটা ভাষা কপ্টিক ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করেছিলেন, যা তখন পর্যন্ত মিশরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল। বর্তমানে মিশরে প্রচলিত ভাষা আরবি, তেরোশ বছর আগে আরবদের মিশর বিজয়কে ধন্যবাদ। শাপোলিয়ে এই মত পোষণ কতেন যে কপ্টিক ভাষা আমাদেরকে আরব বিজয়ের পূর্বের প্রাচীন ভাষার রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ১৮৩২ সালে মৃত্যুর পূর্বে শাপোলিয়োঁ প্রাচীন মিশরীয় ভাষার একটি অভিধান ও একটি ব্যাকরণ লিখে রেখে গিয়েছিলেন।
আপাতদৃষ্টিতে শাপোলিয়োঁকে সঠিক বলেই মনে হয়, কারণ ১৮৬০ এর দশকে তিনি হায়ারোগ্লিফিকের রহস্য উন্মোচনে সক্ষম হয়েছিলেন, আর ধীরে ধীরে সকল প্রাচীন লিপিরই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলেন।
উৎকীর্ণ লিপিগুলিকে অবশ্য ভালো ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা যায় না (কল্পনা করুন আপনি বিভিন্ন সরকারি বাসভবন আর সমাধি লিখন থেকে আমেরিকার ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করছেন)। এমনকি যেসব লিপি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলিও কোনো না কোনো শাসকের গুণগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলিকে বলা যায় সরকারি প্রপাগান্ডা আর তা অকাট্যরূপে সত্য নয়।
তথাপি এসব লিপি এবং অন্যান্য উৎস থেকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মানেথোর রাজাদের তালিকা, ঐতিহাসিকরা যতটা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, তার থেকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস যে পরিমাণে উন্মোচিত হয়, রোজেটা পাথর আবিষ্কারের পূর্বে তা কেউ কল্পনাও করতে পারত না।
.
একত্রিকরণ
মানেথো রাজাদের তালিকা শুরু করেন যিনি উভয় মিশর, আপার ও লোয়ার একত্র করে তার সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসেন। ঐতিহ্যবাহী এই রাজার নাম ছিল মেনেস, যা মিশরীয় শব্দ মেনার গ্রিক রূপান্তর। একত্রিকরণের পূর্বে স্পষ্টতই আপার ঈজিপ্টে রাজত্ব করতেন।
একসময় ধারণা করা হতো মেনেস ছিলেন একজন কল্পকথার রাজা, বাস্তবে এমন রাজার অস্তিত্বই ছিল না। যাহোক, একজন শক্তিশালী রাজার তো অবশ্যই থাকার কথা যিনি সমগ্র মিশরকে এক করবেন, আর তিনি যদি মেনেস নাও হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই অন্য কেউ।
প্রাচীন উত্তীর্ণ লিপিগুলি নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তবে প্রায়শই দেখা যায়, রাজারা সিংহাসনে আরোহণের সময় অন্য নাম গ্রহণ করতেন, তাদের প্রকৃত নামের থেকে যা সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি মৃত্যুর পরেও তাদের নাম পরিবর্তন হতো। ১৮৯৮ সালে একটা প্রাচীন সমাধি খনন করে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে দেখা গেছে একজন রাজার নাম নামার, প্রথমে যাকে দেখা গিয়েছিল রাজমুকুট মাথায় আপার ঈজিপ্টের শাসক, তারপর তাকেই দেখা গেল লোয়ার ঈজিপ্টের মুকুট মাথায়। প্রাসঙ্গিকভাবে তাকেই মিশর একত্রীকরণের নায়ক হিসাবে ধরে নেওয়া যায়, আর সম্ভবত নার্মার আর মেনেস একই ব্যক্তির দুই বিকল্প নাম।
যেভাবেই হোক, মেনেস গোটা মিশরের রাজা হন ৩১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, ঠিক যখন মিশরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটছিল। বিস্মিত না হয়ে উপায় নাই কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল। মেনেস কি একজন মস্ত যোদ্ধা ছিলেন, নাকি একজন সুচতুর কূটনীতিক? এটা কি দৈবাৎ, নাকি সুপরিকল্পিত? এর সাথে কি কোনো “গোপন অস্ত্র” জড়িত ছিল?
কারণ একটা বিষয় লক্ষণীয়, মেনেসের কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই মিশরে এশীয় অভিবাসন শুরু হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত নিরাপত্তাহীন দেশের চাইতে সবুজ শ্যামল উর্বর শান্তিপূর্ণ নীল অববাহিকাকে অধিক বাসযোগ্য মনে করেছিল (আর এটা চলেছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যখন এই উপত্যকায় হাতির দেখা মিলত, এত উর্বর, এত প্রশস্ত, এত কম জন অধ্যুষিত)।
এযুগে সূক্ষ্ম এশীয় প্রভাব লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু স্থাপত্য ও শৈল্পিক কৌশল যার আবির্ভাবকাল ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে নির্ণয় করা গেছে, তার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে তৎকালীন এশীয় কৌশল লক্ষণীয়। এশীয় অভিবাসীরা নিশ্চয়ই তাদের সাথে ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস অঞ্চলে প্রচলিত লিপিও সাথে করে নিয়ে এসেছিল।
এসময়ে এই প্রভাব লোয়ার ঈজিপ্টের চাইতে আপার ঈজিপ্টে বেশি লক্ষ করা যায়, কাজেই সভ্যতার যে অগ্রগতি তার সূচনা আপার ঈজিপ্টেই ঘটেছিল।
অপরপক্ষে এটা আপাত দৃশ্যমান যে একটা পুরাতাত্ত্বিক দুর্ঘটনার ফলেই এটা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। লোয়ার ঈজিপ্ট শতাব্দীর পর শতাব্দী নীলবাহিত পলির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কাজেই সেই অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁড়ে বের করা ছিল বেশ কঠিন। তুলনামূলকভাবে আপার ঈজিপ্ট ও লেক মিয়েরিসের মতো স্বল্প বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে এটা ছিল অনেক সহজ। এই কারণেই হয়তো লোয়ার ঈজিপ্টকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। তবু যখন দুই মিশরকে এক জাতিতে একত্র করা হয়, বিজেতার অভ্যুত্থান হয়েছিল আপার ঈজিপ্ট থেকেই।
এশীয় অভিবাসীরা শিল্পরীতি এবং লিখনশৈলী ছাড়া আরও কিছু কি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, যেমন যুদ্ধ এবং দেশ জয়ের কৌশল, আদিযুগে যেটা শান্তিপূর্ণ মিশরীয় জনগণের মধ্যে কখনোই গড়ে ওঠেনি। মেনেস নিজেও কি এশীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন, যাদের ঐতিহ্য ছিল যুদ্ধ এবং বিজয়, যাদের সৈন্যরা তাদের প্রতিবেশীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত? তিনিও কি তার পূর্বজদের মতো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন?
মেনেসের সময়ের বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বেই উত্তর-পূর্ব মিশরের সিনাই উপদ্বীপ এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাপ্ত আকরিক গলিয়ে তামা সগ্রহ করতে শিখেছিল। নিশ্চিত করে বলা যায়, সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি ধাতু মাটির অভ্যন্তরে পিণ্ডাকারে অনেক আগেই পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলি গলানোর প্রয়োজন হতো না (বাদারিয়ানের ধ্বংসাবশেষ থেকে তামার তৈরি কিছু উপচার পাওয়া গিয়েছে যার সময় নির্ণয় করা হয়েছে প্রায় ৪০০০ খ্রীস্টপূর্ব)। এমনকি লৌহ ধাতুরও সন্ধান মিলেছে যা আকাশের উল্কাপাতের মাধ্যমে সৃষ্ট। অবশ্য অবিমিশ্র ধাতু পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুর্লভ এবং এসব ধাতু খুব অল্প পরিমাণেই পাওয়া যেত, যা শুধু অলংকার রূপেই ব্যবহার করা হতো।
ধাতু গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কারের সাথে সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চয়ের উৎস থেকে তামা সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর মতো নানা উপকরণ তৈরি শুরু হয়। তামা নিজে থেকে অস্ত্রশস্ত্রে ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট শক্ত নয়, তবে টিনের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ে তা দিয়ে ব্রোঞ্জ বানালে তা যথেষ্ট শক্ত হয়। যে যুগে সৈন্যবাহিনীকে ব্রোঞ্জের উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করা হয়, তাকে অভিহিত করা হয় ব্রোঞ্জ যুগ রূপে।
মেনেসের রাজত্বকাল শেষ হওয়ার কয়েক শতাব্দী পার হওয়ার পূর্বে ব্রোঞ্জ যুগ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি, তবে তার বিশেষ বাহিনীকে সজ্জিত করার মতো কি যথেষ্ট ব্রোঞ্জ সহজলভ্য ছিল? এসব অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যেই কি তিনি মিশরের উপর শাসন চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন? হয়তো এটা কোনো দিনই নিশ্চিতরূপে জানা যাবে না।
মানেথোর বিবরণ অনুসারে মেনেসের জন্ম শহর ছিল থিনিস, যার অবস্থান ছিল আপার ঈজিপ্ট, মোটামুটিভাবে প্রথম জলপ্রপাত ও বদ্বীপের মাঝামাঝি স্থানে। মেনেস এবং তার উত্তরাধিকারীরা এখান থেকেই রাজ্য শাসন করতেন।
মেনেস হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন লোয়ার ঈজিপ্টের উপর তাকে যদি অধিকার কায়েম রাখতে হয় তাহলে তাকে যথাসম্ভব স্বদেশীরূপে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, দূরত্বও কমিয়ে ফেলতে হবে, আবার আপার ঈজিপ্টের লোকের কাছেও নিজের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এর সমাধান হলো দূই অঞ্চলের মাঝামাঝি এক জায়গায় তার রাজধানী স্থাপন করতে হবে- যেটা দুই রাজ্যের বলেই প্রতিভাত হবে- আর এটাকে অন্তত খণ্ডকালীন রাজধানী বানাতে হবে (যুক্তরাষ্ট্রেও এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করা হয়েছিল যখন এর বিভিন্ন অঞ্চল একীভূত করা হয়। সংবিধান প্রণয়নের পর দেখা গিয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলি পরস্পরের প্রতি সহনশীল নয়, তাই দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি একটি জায়গা ওয়াশিংটনে রাজধানী স্থাপন করা হয়েছিল)।
মেনেসের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বদ্বীপের অগ্রভাগ থেকে পনেরো মাইল দক্ষিণে। মিশরীয়রা হয়তো এর নাম দিয়েছিল খিকুণ্ঠা (প্টার বাড়ি), হয়তো মিশরীয়রা এখান থেকেই “এজিপ্টস” নামটা পেয়েছিল আর আমাদের কাছে যেটা হয়ে দাঁড়ায় ঈজিপ্ট। পরবর্তীকালে শহরটার মিশরীয় নাম দাঁড়িয়েছিল মেনফে গ্রিকদের কাছে যে নামটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেসি, আর ইতিহাসে এটা এই নামেই পরিচিত।
৩৫০০ বছর ধরে মিশরের ইতিহাসে মেম্ফিস ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ শহর, আর অধিকাংশ সময় ধরে এটা ছিল রাজধানী ও রাজকীয় সংস্থাপনের ধারক বাহক।
.
পারলৌকিক জীবন
মানেথো মিশরীয় শাসকদের বিভিন্ন রাজবংশে বিভক্ত করেন। প্রতিটি বংশ একটি নির্দিষ্ট পরিবারের অন্তর্গত যারা পুরুষানুক্রমে মিশরের উপর কর্তৃত্ব করেছে, শাসন করেছে। মানেথো তিন সহস্র বর্ষব্যাপী ত্রিশটি রাজবংশের তালিকা প্রদান করেছেন।
তালিকার মধ্যে সেইসব রাজন্যবর্গকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা শুধু একত্রীকরণের পরই শাসক ছিলেন, কাজেই প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন মেনেস। মেনেসের আগের শাসনকালকে বলা হয়েছে “প্রাক-বংশীয় মিশর”, যা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক মিশরের সমার্থক।
প্রথম দুই বংশ, যাদের প্রত্যেকেই ছিল থিনিসের জাতক, তাদেরকে বলা হয়েছে থিনিসীয় বংশ। তাদের শাসনকালকে বলা হয়েছে মিশরের প্রাচীন যুগ, আর স্থায়ীত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ থেকে ২৬৮০ পর্যন্ত চার শতাব্দীর অধিক সময় পর্যন্ত।
মেম্ফিসের গুরুত্ব, এমনকি প্রাচীন মিশরের পরিপ্রেক্ষিতেও নির্ণয় করা যায় সে সময়ের সমাধিগুলি দেখে। আর ইতিহাসে কবরের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় এর ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে, বিশেষ করে প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম।
প্রাচীন মিশরীয় ধর্মের উদ্ভবকে যুক্ত করা যায় প্রাগৈতিহাসিক শিকার-নির্ভর জীবনযাত্রার সাথে, যখন জীবিকানির্ভর করত শিকারপ্রাপ্তির উপর, আর কোন শিকারপ্রাপ্তিকে মনে করা হতো দৈবনির্ভর। তাই সে যুগে এক ধরনের প্রাণী-দেবতার উদ্ভব ঘটে, কারণ বিশেষ দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে সেই দেবতার নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রাণী শিকার সহজ হবে। যদি প্রাণীটি বিপজ্জনক হয় তবে আংশিকভাবে সেই প্রাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে প্রাণীটি শিকার কম ক্ষতিকর হবে। মনে হয় সেই কারণেই, এমনকি পরবর্তী কালেও দেখা গেছে মিশরীয় দেবতাদের মাথা রূপ নিয়েছে বাজ, শেয়াল, ইবিস, নয়তো জলহস্তির।
তবে যখন কৃষি জীবনধারণের প্রধান উপায়রূপে আবির্ভূত হলো তখন নতুন দেবতা এবং নতুন ধর্মীয় বিশ্বাস প্রাচীন ধারার সাথে যুক্ত হলো। প্রাকৃতিক উপাসনার পর্যায়ে উঠে এল সূর্যদেবতা। নিমেঘ মিশরীয় আকাশে সূর্য ছিল শক্তিশালী অনুষঙ্গ, আর তা ছিল আলো ও উত্তাপ বিতরণের প্রধান উৎস। তদুপরি মিশরে বন্যার আগমন ঘটত কেবল তারকাদের সাথে সূর্যের একটা নির্দিষ্ট অবস্থানের সময়েই। কাজেই সূর্যকে দেখা হতো নদীর প্রাণদায়ী শক্তি হিসাবে এবং সকল প্রাণের উৎসরূপে। হাজার হাজার বছর ধরে মিশরীয়রা সূর্যকে পূজা করেছে বিভিন্ন নামে। রে বা রা নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।
সম্ভবত জীবনচক্র; জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্মের ধারণা থেকেই সূর্যপূজার উদ্ভব। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়, আবার ভোরবেলায় উদিত হয়। মিশরীয়রা প্রভাতে সূর্যোদয়কে কল্পনা করেছিল এক শিশুর জন্ম, যে দ্রুত বেড়ে উঠে মধ্যাহ্নে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে জরাজীর্ণ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু তারপরেও পাতালপুরীর অন্ধকার গুহাপথ পেরিয়ে পরদিন প্রভাতে আবার শিশুরূপে তার পুনর্জন্ম ঘটে।
কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষির ক্ষেত্রেও অনুরূপ জীবনচক্র সহজ লক্ষণীয়। ফসল পাকে, সেটা কাটা হয়, যা মৃত্যুর সমতুল্য, তবে পরবর্তী মওশুমে বীজ থেকে আবার ফসলের জন্ম।
ঘটনাক্রমে এমনি এক জীবনচক্র মিশরীয় ধর্মেও প্রতিফলিত। এটা গড়ে উঠেছে ফসলের দেবতা ওসিরিসকে কেন্দ্র করে যাকে পুরোপুরি মানবিক চরিত্রে চিত্রিত করা হয়েছে। পুরাণকথা অনুসারে তিনিই মিশরীয়দের শিল্প ও কলা বিদ্যা শিখিয়েছেন, যার মধ্যে কৃষিও অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সভ্যতার রূপকার।
কল্পকথা প্রচলিত আছে যে অসিরিস তার ছোট ভাই সেট এর দ্বারা নিহত হয় (সেট সম্ভবত শুষ্ক মরুভূমির রূপকল্প, কারণ যদি কোনো কারণে নীলের বন্যা ব্যাহত হয়, তাহলে ফসলহানি অনিবার্য)। অসিরিসের সুন্দরী ও একান্ত অনুগত স্ত্রী আইসিসেরও সম্পূর্ণ মানবিক রূপ লক্ষণীয়, বার বার তার শরীর পুনরুদ্ধার করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করা হয়, কিন্তু সেট বার বার তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, আর পূনর্নির্মানের সময় একটা টুকরা হারিয়ে যায়। অসম্পূর্ণ অসিরিস কখনো মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, আর তাই সে পাতালপুরিতে চলে যায়, যেখানে সে অধঃপতিত মানব আত্মার উপর কর্তৃত্ব করে।
অসিরিস ও আইসিসের পুত্র হোরাস (বাজপাখির মাথাবিশিষ্ট দেবতা, যে ছিল প্রাচীন পৌরাণিক শস্য-দেবতার নূতন রূপ) সেটকে হত্যা করে তার প্রতিশোধস্পৃহা নিবৃত্ত করে)।
এই গল্পটিও সূর্যচক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অসিরিসকে অস্তায়মান সূর্যের প্রতিরূপ কল্পনা করা যেতে পারে, যে নিহত হয় রাত্রির দ্বারা। মৃতপ্রায় সূর্য পাতালপুরিতে অবতরণ করে, যেমন করে অসিরিস।
স্বাভাবিকভাবেই এমনি একটি জীবনচক্র মানুষের উপরও আরোপিত করা যায়। খুব কম লোকই মৃত্যুকে স্বাগত জানায় আর প্রায় সবাই আশা করে মৃত্যুর পরেও কোনোভাবে যেন জীবন দীর্ঘায়িত হয়, অথবা পুনর্জীবন লাভ করা যায়, যেমনটা ঘটে থাকে শস্য এবং অসিরিসের ক্ষেত্রে।
মানুষের পুনর্জন্মের নিশ্চয়তা প্রদানে দেবতারা, (বিশেষ করে অসিরিস), এসব ব্যাপারে যার ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ, তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উপাসনা করতে হবে।
মিশরীয়রা সাবধানতার সাথে প্রার্থনার আনুষ্ঠানিকতা, মন্ত্র এবং প্রার্থনা-সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করে রাখত, সেগুলি যেন সঠিকভাবে উচ্চারণ করা যায় এবং গীত হয়, যাতে মৃত্যুর পরে আত্মার অবিনাশিতা নিশ্চিত হয়। এসব মন্ত্র আনুষ্ঠানিকতা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হতে থাকে, তবে প্রকৃতপক্ষে এগুলির সময়কাল প্রাচীন যুগে প্রসারিত, এমনকি মিশরে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও পূর্বে।
এসব ফর্মুলার তালিকাভুক্ত একটা দলিল- যা একটা হায়ারোগ্লিফিক সংগ্রহ, আর যার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে বাইবেলের একটা প্রার্থনা সঙ্গীতের সাথে যেটা ১৮৪২ সালে কার্ল রিচার্ড লেপসিনস নামে এক জার্মান মিশরতত্ত্ববিদ প্রকাশ করেন। এটা তার কাছে বিক্রি করে এক লুটেরা, একটা প্রাচীন সমাধি লুট করার সময় সে এটা পেয়েছিল।
দলিলটার নামকরণ হয় “দ্য বুক অব দ্য ডেড,” যদিও এই নামটা মিশরীয়দের দেওয়া নাম নয়। বইটাতে দেওয়া আছে সেইসব মন্ত্র ও ফর্মুলা যাতে মৃতরা নিরাপদে বিচারগৃহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যেতে পারে। আর যদি পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় (পাপ পুণ্য সম্বন্ধে মিশরীয়দের ধারণা আধুনিক কালের একজন সৎ মানুষের মতোই), তাহলে সে অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করবে আর দেবতা অসিরিসের সাথে অনন্তকাল বাস করবে।
পরকালের অনন্ত সুখ উপভোগ করতে হলে সশরীর উপস্থিতি প্রয়োজন। হয়তো এই ধারণাটার উদ্ভব ঘটেছে মিশরের শুষ্ক ভূমির কারণে, যেখানে মৃতের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হতো অত্যন্ত ধীর গতিতে, যেখানে দীর্ঘদিন শরীরের স্বাভাবিকত্ব বজায় থাকত। এ থেকেই মিশরীয়রা শরীরের প্রলম্বিত ধারণা লাভ করে, যে ধারণাটা ছিল তাদের কাছে যেমন স্বাভাবিক তেমনি কাক্ষিত, আর তারা এটাকে দীর্ঘায়িত করার উপায় উদ্ভাবন করেছিল।
এভাবেই বুক অব ডেড-এ মৃতের শরীর সংরক্ষণের উপায় নিয়ে নির্দেশনা ছিল। অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (যাতে প্রথমেই পচনক্রিয়া শুরু হয়) তা অপসারণ করে আলাদা পাত্রে সংরক্ষণ করা হতো, তবে হৃৎপিণ্ড, যাকে জীবনের কেন্দ্র বলে মনে করা হয়েছিল, তা শরীরের অভ্যন্তরেই রেখে দেয়া হতো।
তারপর দেহটি কেমিক্যালে ডুবিয়ে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে তার উপর পিচের প্রলেপ মাখিয়ে দেয়া হতো যাতে আর্দ্রতা রোধ করা যায়। এভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলে “মমি”। মমি একটি ফার্সি ভাষার শব্দ, যার অর্থ পিচ (ফার্সি কেন? কারণ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে একসময় পারসিকরা মিশর শাসন করত, তাদের কিছু কিছু শব্দ গ্রিক ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে আর সেখান থেকে আমাদের কাছে।
হতে পারে মমিকরণ বিষয়টি মিশরীয়দের উৎকণ্ঠা আর কুসংস্কারের ফসল, তবে অবশ্যই এর কিছু ভালো ফল রয়েছে। এটা মিশরীয়দের রাসায়নিক সম্বন্ধে জানার প্রেরণা যোগায়। এভাবে তারা অনেক ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেছিল, এমনকি অনেকে মনে করে “খেম” (Khem) শব্দ থেকে কেমিস্ট্রি (Chemistry) শব্দের উদ্ভব। এই খেম শব্দটি প্রাচীন মিশরের নাম।
যদি কোনো কারণে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে বা অপহৃত হয়, তাহলে জীবন পুনস্থাপনের জন্য অন্য ব্যবস্থাও রাখা হতো। মৃত ব্যক্তির মূর্তি নির্মাণ করে সমাধির মধ্যে স্থাপন করা হতো, আর জীবিত অবস্থায় ব্যক্তিটি যেসব জিনিস ব্যবহার করত- যেমন যন্ত্রপাতি, অলংকার, আসবাব ও চাকর বাকরের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ, এমনকি খাদ্য পানীয়ও রেখে দেয়া হতো।
তাছাড়া মৃত ব্যক্তিটির জীবৎকালের ঘটনাবলি সমাধির দেয়ালে উৎকীর্ণ এবং চিত্র খোদাই করে রাখা হতো। এসব দেয়াললিখন ও চিত্র থেকে সেকালের মিশরীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। হাতি, জলহস্তি ও কুমীর শিকারের ছবি উৎকীর্ণ রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে সেকালের নীল উপত্যকার সমৃদ্ধ জীবনযাপনের লেখচিত্র।
ভোজনোৎসবের চিত্রও দেখা যায়, যেখান থেকে আমরা মিশরীয় খাবারের ধারণা লাভ করতে পারি। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক জীবন ও ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার ছবিও দেখা যায়। পারিবারিক জীবনে উষ্ণ প্রেমের সম্পর্কও দেখানো হয়েছে। মেয়েরা সমাজে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করত (গ্রিকদের চাইতে অনেক উঁচু); শিশুরা অনেকটা বেশি প্রশ্রয় পাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যেত। এটা বেশ অবাক করার মতো যে মিশরীয়দের ইহলৌকিক চিন্তার চাইতে পারলৌকিক ভাবনা অনেক বেশি অগ্রাধিকার লাভ করেছিল।
মৃত্যুর পরে জীবনের নিশ্চয়তাবিধান অনেক বিস্তার ও ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত এটা এই কারণে যে প্রথম দিকে শুধু রাজন্যদের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য ছিল। রাজাকে দেখা হতো দেবতাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আর সেজন্য রাজার উপর দেবত্ব আরোপ করা হতো। যদি তিনি সকল রীতিনীতি মেনে দেবতাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, তাহলে নীলের পানির স্ফীতি সঠিক মাত্রায় থাকবে, অঢেল ফসল ফলবে আর রোগবালাই দূরে থাকবে। রাজাই সবকিছু, রাজাই মিশর।
স্বাভাবিকভাবে রাজার মৃত্যু হলে সকল আনুষ্ঠানিকতা যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা আবশ্যক ছিল, কারণ এটা ছিল সমগ্র মিশরের সমাহিতকরণ, আর তার রাজত্বকালে যাদের মৃত্যু হয়েছে, রাজার সাথে সাথে তারা সবাই অনন্ত জীবন লাভ করবে।
সময় গড়িয়ে চলার সাথে সাথে মিশরের সম্পদ বৃদ্ধি হতে থাকে, বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিরা, প্রাদেশিক শাসকরা- যারা অভিজাত সম্প্রদায় একই সম্মাননা প্রত্যাশা শুরু করে। তারাও সমাধি মন্দির আর মমিকরণ কামনা করে ব্যক্তিগত চিরস্থায়ীত্ব, রাজার মাধ্যমে নয়। এটা বৃহত্তর ধর্মীয় মাত্রা সংযোজন করতে পারলেও, মিশরীয়দের জাতীয় প্রচেষ্টার অধিকাংশই একটা নিষ্ফল সমাহিতকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই ব্যয়িত হয়ে যায়। তাছাড়া অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বেড়ে যায় বিপজ্জনক মাত্রায়।
যেহেতু সম্পদশালী আর ক্ষমতাশালীরাই এভাবে সমাহিত হতো, তাই একে অন্যকে অতিক্রম করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ত। তাই মৃতের আত্মীয়স্বজন সর্বদাই চেষ্টা করত স্বজনদের জাঁকজমকপূর্ণভাবে সমাহিত করার।
সমাধিগৃহে মূল্যবান ধাতুর অলংকার ও তৈজস দেওয়ার কারণে সর্বদাই তা কবর লুটেরাদের আকর্ষণ করত। তাই কবর রক্ষা, মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ রাখা, আইনের প্রতিবন্ধকতা ও দেবতাদের রোষ থেকে বাঁচনো অত্যন্ত কঠিন ছিল, আর খুব অল্পসংখ্যক কবরই আজকের দিন পর্যন্ত টিকে রয়েছে।
আমাদের বুঝতে হবে এমন এক সময় যখন বিকল্প কাগজের মুদ্রার প্রচলন হয়নি, তখন মিশরীয়দের এভাবে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ কবরে রেখে দেয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না, যাতে করে অর্থনীতিতেও ধস নেমেছিল। কবর লুটেরাদের মতলব যাই থাকুক না কেন, তারা সোনারূপা বের করে এনে মুদ্রা সার্কুলেশন বজায় রাখতে সহায়তা করেছিল।
কবরের নজির থেকেই প্রাচীনকালে মেম্ফিসের গুরুত্ব বোঝা যায়। এক সময় যেখানে মেম্ফিস শহর ছিল, সেখানে নীল নদের প্রান্ত ঘেঁষে শুরু হয়ে মরুভূমির সীমান্ত পর্যন্ত মৌচাকের মতো অসংখ্য চুনামাটির কবর ছড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে এখানে রয়েছে সাক্কারা নামে একটা গ্রাম, আর সমাধিক্ষেত্রটাও এই নামেই পরিচিত।
প্রাচীনতম কবরগুলি বাড়ির বাইরে নির্মিত আয়তাকার বেঞ্চের মতো। আধুনিক আরবি ভাষায় এই বেঞ্চগুলিকে বলে “মাস্তাবা,” আর প্রাচীন কবরগুলিকেও এই নামেই অভিহিত করা হয়। প্রাচীন মাস্তাবাগুলি ছিল ইটের তৈরি। সমাধিকক্ষটি ছিল একটি সুরক্ষিত কফিন, কোনো কোনোটি পাথরের তৈরি, কোনো কোনোটির উপরিতলও পাথরের। এর উপরে থাকত একটা চেম্বার যেখানে মৃত ব্যক্তি জীবনচিত্র অঙ্কিত থাকত যাতে লোকে তার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে পারে। সর্বপ্রাচীন কোনো কোন সমাধিকে মনে করা হতো প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের। যদি তাই হয়, তাহলে কিছুকালব্যাপী মেম্ফিস ছিল সেই সময়ের রাজধানী।