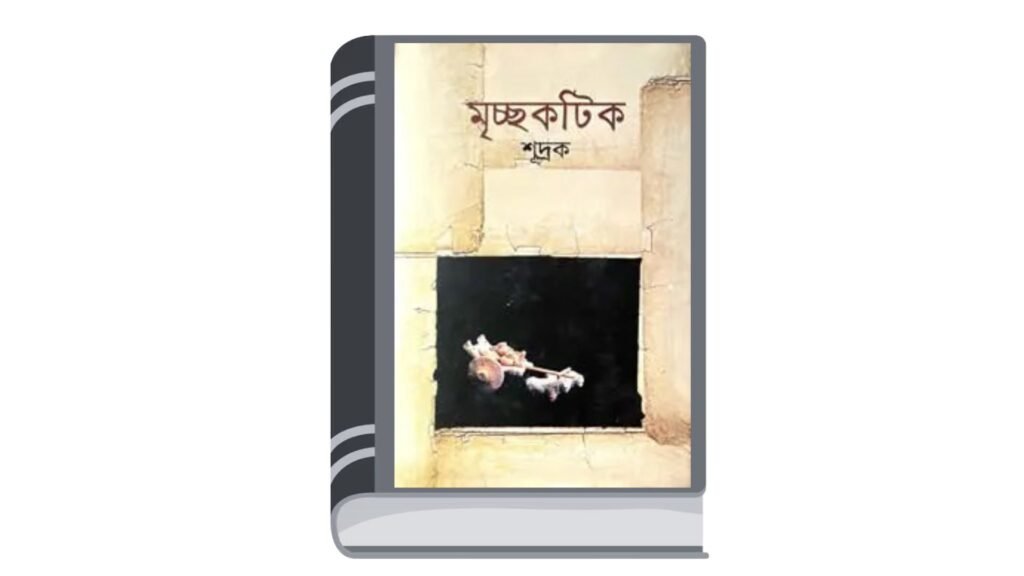মৃচ্ছকটিক – প্রথম অঙ্ক
পর্যঙ্কাসনের[১] গ্রন্থিবন্ধনে দ্বিগুণিত সর্পের কুণ্ডলীতে যাঁর জানু দুইটি বদ্ধ, শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণাদিবায়ুর নিরোধে সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় যাঁর ইন্দ্রিয়[২] নিরুদ্ধ, যিনি তত্ত্বদৃষ্টিতে (সম্যক্ জ্ঞানদৃষ্টিতে) ইন্দ্রিয়বৃত্তিরহিত হয়ে[৩] নিজের মধ্যেই নিজেকে প্রত্যক্ষ করছেন[৪] এমন শম্ভুর বাহ্যজ্ঞানশূন্যতায় স্থিরতাপন্ন ব্রহ্মলগ্ন সমাধি তোমাদের রক্ষা করুক[৫] ॥১॥
এবং
নীলকণ্ঠের[৬] কৃষ্ণমেঘবর্ণ যে কণ্ঠে গৌরীর বাহুলতা বিদ্যুৎ-লেখার মতো শোভা পায় সেই কণ্ঠ তোমাদের রক্ষা করুক[৭] ॥২॥
(নান্দীর প8)
সূত্রধার — দেখছি, অভিনয় দেখার জন্যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী উৎসুক হয়ে উঠেছেন— তাই আর অযথা কথা বাড়িয়ে তাঁদের বিব্রত করতে চাই না। উপস্থিত শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলীকে প্রণাম করে নিবেদন করছি যে আজ আমরা মৃচ্ছকটিক প্রকরণ[৮] মঞ্চস্থ করব বলে ঠিক করেছি। এই প্রকরণের রচয়িতা হলেন বিখ্যাত কবি শূদ্রক— যিনি গজপতিগতি, যাঁর নয়ন চকোরের মতো এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দর, যাঁর শরীর সুগঠিত এবং যিনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং গম্ভীরহৃদয় ॥ ৩॥ তাছাড়া-
ইনি ঋগ্বেদ, সামবেদ, অঙ্কশাস্ত্র, বৈশিকী, হস্তীবিদ্যা প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার কলা শিক্ষা করে শিবের অনুগ্রহে আঁধারমুক্ত দৃষ্টি লাভ করেছেন। ইনি একশ বছর পরমায়ু অতিবাহিত করে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করার পর অগ্নিতে প্রবেশ করেন[৯] ॥ ৪ ॥
আবার,
এই শূদ্রক ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়, ত্রুটিহীন বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, তপস্যায় ধনী এবং সর্বদা শ্রেষ্ঠ হাতির সঙ্গে[১০] বাহুযুদ্ধে প্রলুব্ধ ॥ ৫ ॥
তাঁর এই প্রকরণের মূল বিষয় :
উজ্জয়িনী পুরীতে ব্রাহ্মণদের নেতৃস্থানীয় এক দরিদ্র যুবক বাস করতেন। এঁর গুণে অনুরক্তা বসন্তশ্রীধারিণী গণিকা বসন্তসেনা ॥ ৬ ॥
রাজা শূদ্রক এঁদের দুজনকে কেন্দ্র করে উত্তম সুরতোৎসব, নীতির প্রচার, খল স্বভাবের চিত্র, দুষ্টের আচরণ, ভবিতব্যের রূপ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন ॥৭॥
(পরিক্রমণ ও অবলোকন করে)
এ কী! আমাদের এই সংগীতশালা যে শূন্য! নট-নটীরা সব গেলেন কোথায়?
— (চিন্তা করে) ও, বুঝতে পেরেছি।
পুত্রহীনের ঘর শূন্য, যার সৎ বন্ধু নেই তার ঘরও শূন্য, মূর্খের কাছে চারিদিক শূন্য আর যে দরিদ্র তার কাছে সবই শূন্যময় ॥ ৮ ॥
আমার সংগীত শেষ হয়েছে। অনেকক্ষণ সংগীতচর্চা করে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্যকিরণে যেমন পদ্মবীজ শুকিয়ে যায় তেমনি ক্ষুধার জ্বালায় আমার চোখদুটো শুকিয়ে খট্খট্ করছে। এখন তাহলে গৃহিণীকে ডেকে জেনে নিই কপালে প্রাতরাশ জুটবে কিনা। প্রয়োজনের দাবিতে আর অভিনয়ের অজুহাতে এখন তবে প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা চালানো যাক্।
ওহ্ কী কষ্ট! অনেকক্ষণ সংগীতচর্চার ফলে শুকনো পদ্মের ডাঁটার মতো আমার সমস্ত শরীরটা যেন শুকিয়ে গেছে। যাই, বাড়ি গিয়ে খোঁজ করি, গৃহিণী আগে থাকতে কিছু যোগাড়-টোগাড় করে রেখেছেন কিনা। (পরিক্রমণ করে এবং দেখে) এই তো আমাদের বাড়ি, ভেতরে যাওয়া যাক্। (প্রবেশ করে এবং দেখে)। ব্যাপার কী! বাড়িতে দেখছি অন্য ধরনের আয়োজন চলছে। পথে চাল-ধোয়া জলের দীর্ঘ স্রোত বয়ে চলেছে— যুবতীরা কপালে তিলক কাটলে দেখা যায় যে শোভা তার থেকে বেশি শোভার সৃষ্টি হচ্ছে লোহার কড়ায় ঘষাঘষিতে মাটিতে কালো দাগ পড়ে। রান্নার সুঘ্রাণ ক্ষুধার জ্বালাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে কি পূর্বপুরুষের কোনো গুপ্তধন পাওয়া গেছে? না কি আমি ক্ষুধার্ত বলেই সমগ্র জগৎ আজ অন্নময় দেখছি? কিন্তু ঘরেও প্রাতরাশ কিছুই দেখছি না। এদিকে ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ যায় যে! এখানে সব ব্যবস্থাদি নতুন রকমের দেখছি। কেউ-বা রঙ পিষছে, কেউ-বা মালা গাঁথছে। (চিন্তা করে) ব্যাপার কী! ঠিক আছে, গিন্নিকে ডেকে আসল কথাটা জেনে নেওয়া যাক। গিন্নি, গিন্নি, একবার এদিকে এসো তো।
(নটীর প্রবেশ)
নটী— আর্য, এই যে আমি এসেছি।
সূত্রধার— আর্যে, এসো, এসো।
নটী— আমায় কী করতে হবে, আদেশ করুন।
সূত্রধার— আর্যে, (‘অনেকক্ষণ ধরে সংগীতচর্চা করে’ ইত্যাদি বলার পর) ঘরে খাবার দাবার কিছু আছে কি?
নটী— আর্য, সবই আছে।
সূত্রধার— কী কী আছে?
নটী— এই যেমন গুড়ের পায়েস আছে, দধি আছে, ঘৃত আছে, তণ্ডুল আছে— আপনার খাবার মতো রসাল উপাদেয় সবকিছুই আছে, তবে এখন দেবতাদের অভিরুচি।
সূত্রধার— সে কী! যা বলছ আমাদের ঘরে তা সবই আছে? না, না, তুমি পরিহাস করছ!
নটী— (স্বগত) পরিহাসই বটে! (প্রকাশ্যে) আছে সবই— কিন্তু দোকানে।
সূত্রধার— (ক্রোধে) তবে রে অনার্যে, এইরকম তোমারও যেন আশাভঙ্গ হয়–খাবার না জোটে। ঢেলার মতো উপরে ছুড়ে দিয়ে শেষে আমাকে নিচে ফেলে দিলে?
নটী— আমায় মাপ করুন, মাপ করুন, আর্য। আমি পরিহাস করছিলাম।
সূত্রধার— তবে এসব নতুন ধরনের আয়োজন কিসের জন্যে? কেউ রঙ পিষছে, কেউ-বা ফুলের মালা গাঁথছে— এইসব পাঁচরঙা ফুলে ঘরের মেঝে সাজানো।
নটী— আজ্ঞে আমার উপোস।
সূত্রধার— উপোস? কিসের?
নটী— ‘সুন্দর পতিলাভ’-এর উপবাস।
সূত্রধার— পতিটি ইহলৌকিক না পারলৌকিক?
নটী— আজ্ঞে পারলৌকিক।
সূত্রধার— (ক্রোধে) দেখুন, দেখুন, মশাইরা। আমারই অন্নের শ্রাদ্ধ করে পারলৌকিক পতির খোঁজ করা হচ্ছে!
নটী— রাগ করো না, রাগ করো না, আর্য। পরের জন্মে তোমাকেই যাতে পতিরূপে পাই তার জন্যেই এই ব্ৰত!
সূত্রধার— তা এই উপবাসের মন্ত্রণাটি কে দিলেন?
নটী— তোমারই প্রিয় বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ।
সূত্রধার— (ক্রোধে) ওরে দাসীপুত্র চূর্ণবৃদ্ধ! রাজা কবে যে ক্রুদ্ধ হয়ে নববধূর সুগন্ধ চুলের মতো তোকে কেটে ফেলবেন আমি তা দেখার জন্যে বসে আছি।
নটী— আর্য, রাগ করো না। তোমাকেই জন্মজন্মান্তর ধরে পতিরূপে পাবার জন্যে এই উপবাস করছি। (পায়ে লুটিয়ে পড়ে)
সূত্রধার— আর্যে, ওঠ, ওঠ। এই উপবাসে কী কী করতে হবে তাই বলো।
নটী— আমাদের অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করতে হবে।
সূত্রধার— ঠিক আছে, আমাদের অবস্থার উপযুক্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করছি।
নটী— তোমার যা অভিরুচি। (প্রস্থান)
সূত্রধার— (পরিক্রমণ করে) তাই তো। এই সমৃদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীতে আমাদের অবস্থার মতো ব্রাহ্মণ খুঁজে পাই কী করে? (দেখে) এই যে, চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয়মশাই এই দিকেই আসছেন দেখছি। প্রথমে ওঁকেই জিগ্যেস করা যাক। মৈত্রেয়মশাই, সবার আগে আপনিই আজ আমাদের বাড়িতে আহার গ্রহণ করুন।
(নেপথ্যে)
ওহে অন্য কোনো ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করো। আমি এখন অন্যত্র ব্যস্ত আছি।
সূত্রধার— মহাশয়, আহার প্রস্তুত, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। তাছাড়া কিছু দক্ষিণারও ব্যবস্থা আছে।
(নেপথ্যে)
ওহে প্রথমেই তো আমি তোমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি। তবু বার-বার আমাকে জিগ্যেস করছ কেন?
সূত্রধার— ইনি আমার নিমন্ত্রণ রাখলেন না। বেশ, তবে অন্য কোনো ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা যাক। (প্রস্থান)
ইতি প্রস্তাবনা
(উত্তরীয় হাতে মৈত্রেয়ের প্রবেশ)
মৈত্রেয়— “অন্য কোনো ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা যাক”-– আমি মৈত্রেয়, আমাকে কিনা এখন নিমন্ত্রণ খাওয়ার জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে। হায়, কী শোচনীয় অবস্থা আমার। অথচ এই কিছুদিন আগে চারুদত্তের অবস্থা যখন ভালো ছিল তখন দিন-রাত মিষ্টান্ন খেয়ে উদ্গার তুলতাম। চতুঃশালার অন্তঃপুরের দ্বারে বসে সযত্নে প্রস্তুত নানান ব্যঞ্জন পাত্রে পরিবেষ্টিত হয়ে শিল্পীর মতো-আঙ্গুলের সাহায্যে সব শেষ করতাম, নগর চত্বরে বৃষভের মতো বসে বসে রোমন্থন করতাম। সেই আমি কিনা সারাদিন এখানে-ওখানে খাবার খেয়ে ভিখিরির মতো এখানে আসি গৃহপালিত পায়রার মতো রাত্রে শুধু বিশ্রাম করতে।
চারুদত্তের প্রিয় বন্ধু আমাদের চূর্ণবৃদ্ধ এই যুঁইফুলের গন্ধমাখা উত্তরীয়টি আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন চারুদত্তের দেবপূজা শেষ হলে তাঁকে দেবার জন্যে। তাহলে আগে চারুদত্তের খোঁজ করা যাক। (পরিক্রমণ করে এবং দেখে) এই তো, দেবপূজা সেরে গৃহদেবতার নৈবেদ্য হাতে চারুদত্ত এই দিকেই আসছেন দেখছি।
(চারুদত্ত ও রদনিকার প্রবেশ)
চারুদত্ত— (উপর দিকে চেয়ে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায়, একদিন আমার ঘরের দেওয়ালের ধারে হাঁস-সারসের দল পরম আগ্রহে কত খাবার খেয়ে বেড়িয়েছে, আজ কিনা সেই জায়গায় ঘাস আর আগাছায় ভরে গিয়েছে, পোকামাকড়েরা খুঁটে খাচ্ছে দু-একটা শস্যের দানা। ওহ্! ॥ ৯ ॥
(এই বলে ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করে এবং তারপর বসে)
বিদূষক— এই তো চারুদত্ত। তাহলে ওঁর কাছেই যাওয়া যাক। (কাছে গিয়ে) সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনার শ্রীবৃদ্ধি হোক।
চারুদত্ত— এই তো আমার চিরদিনের বন্ধু মৈত্রেয়। এসো, এসো, বন্ধু বসো।
বিদূষক— তা না হয় বসছি। (বসে) এই নিন বন্ধু, আপনার পরম বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ আমার হাত দিয়ে এই যুঁইফুলের গন্ধমাখা উত্তরীয়টি পাঠিয়েছেন আপনার দেবপূজা শেষ হলে আপনাকে দেবার জন্যে।
(হাতে দিলেন)
চারুদত্ত– (হাতে নিয়ে চিন্তামগ্ন )
বিদূষক— বন্ধু, কী ভাবছেন?
চারুদত্ত— ভাই, ঘন অন্ধকারে দীপশিখার মতো দুঃখ-কষ্টের পর সুখভোগ বড় মনোরম, তাই না? কিন্তু বিলাস-ব্যসন উপভোগের পর মানুষ যখন কষ্টে পড়ে তখন সেটা তার পক্ষে মৃত্যুতুল্য, সে তখন কেবল দেহের ভার বয়ে বেড়ায় ॥ ১০ ॥
বিদূষক— আচ্ছা বন্ধু, বলুন তো, মৃত্যু আর দারিদ্র্য— এ দুটোর মধ্যে আপনার পছন্দ কোনটি?
চারুদত্ত— দারিদ্র্য আর মৃত্যু— এ দুয়ের মধ্যে আমি বরং মৃত্যুকেই বরণ করব, দারিদ্র্য কখনো নয়। মৃত্যু তো ক্ষণকাল যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু দারিদ্র্যদহনের যেন শেষ নেই। ॥ ১১ ॥
বিদূষক— দুঃখ করবেন না, বন্ধু। একদিন আপনি দরিদ্রদের সম্পদ বিলিয়েছেন আজ তাই দরিদ্র অবস্থাতেও আপনি সুন্দর—সুরলোকের পীতশেষ চন্দ্রের মতো রমণীয়।
চারুদত্ত— বন্ধু, আমার দুঃখটা ঠিক অর্থের জন্যে নয়, কিন্তু— দুঃখটা কোথায় জান?
আজ আমার দুরবস্থা বলে অতিথিরা আর আসে না। মদকাল শেষ হলে হাতির গালদুটো যখন একেবারে শুকিয়ে যায় তখন কি ভ্রমরেরা উড়ে আর হাতির কাছে আসে? ॥ ১২ ॥
বিদূষক— বন্ধু, এইসব নীচ অর্থলোভী অতিথিরা সুবিধাবাদী রাখাল বালকের মতো যে মাঠে যতক্ষণ সুবিধা পায় সেই মাঠে ততক্ষণ থাকে।
চারুদত্ত—না, আজ আমার ঐশ্বর্য নেই বলে যে আমি দুঃখিত ঠিক তা নয়। ভাগ্যক্রমেই ধন আসে, ধন যায়। শুধু দুঃখটা কী জান? ধন-সম্বল চলে গেলে লোকের কাছ থেকে স্নেহভালোবাসা আর পাওয়া যায় না ॥ ১৩ ॥
তা ছাড়া—
দারিদ্র্য মানুষকে দেয় লজ্জা, লজ্জা তেজের বিনাশ ঘটায়, তেজ বিগত হলে আসে নিরাশা, নিরাশা থেকে শোক, শোক-দুঃখে মানুষ হয় বুদ্ধিভ্রষ্ট আর বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষ হয় বিধ্বস্ত। আশ্চর্য! দারিদ্র্যই সব দুর্ভাগ্যের মূল ॥ ১৪ ॥
বিদূষক— বন্ধু, তুচ্ছ অর্থের কথা ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছেন?
চারুদত্ত— দেখ, মানুষের কাছে দারিদ্র্যই দুশ্চিন্তার আবাস, দারিদ্র্য দেয় নিদারুণ অপমান, জন্ম দেয় শত্রুতার, নিয়ে আসে বন্ধু-বিচ্ছেদ, আত্মীয়-স্বজন আর সাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করে ঘৃণা। দারিদ্র্যের ফলে মানুষ নিজের স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়ে নিতে চায় বনবাস, হৃদয়স্থ দুঃখের আগুন তাকে জ্বালায় কিন্তু একেবারে দগ্ধ করে না। ১৫।
তা বয়স্য, আমি গৃহদেবতার পূজা শেষ করেছি, এখন তুমি রাজপথের চৌমাথায় গিয়ে মাতৃপূজার নৈবেদ্য দিয়ে এসো।
বিদূষক— না আমি যাব না।
চারুদত্ত— যাবে না? কেন?
বিদূষক— কারণ, এত পুজোর ঘটা করেও তো আপনি দেবীর কৃপা পাচ্ছেন না, আর পুজো করে লাভ আছে কিছু?
চারুদত্ত— বয়স্য, ও কথা বলো না। এটা গৃহস্থ মানুষের অবশ্য কর্তব্য।
শুদ্ধ দেহে, সভক্তিচিত্তে, প্রসন্ন বাক্যে ও প্রশান্ত মনে এবং নৈবেদ্যদানে পূজা করলে দেবতারা সবসময়েই তুষ্ট হন। এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে কী হবে? ॥ ১৬ ॥ কাজেই যাও, মায়ের পূজা দিয়ে এসো।
বিদূষক— না বয়স্য, আমি যাব না। অন্য কাউকে যেতে বলুন। আমার মতো হতভাগ্য ব্রাহ্মণের কপালে সবসময় বিপরীত ফলই জোটে। দর্পণের ছায়ার ক্ষেত্রে যেমন ডান-দিকটা হয় বাঁ-দিক আবার বাঁ-দিকটা ডান-দিক, ঠিক তেমনি। তা ছাড়া, এখন এই সন্ধ্যায় রাজপথে গণিকা, বিট, চেট ও রাজার প্রিয়পাত্রেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সামনে পড়লে আমার দশা হবে ঠিক কালসাপলোভী ব্যাঙের মুখে ইঁদুরের মতো। তা আপনি এখানে বসে থেকে কী করবেন?
চারুদত্ত— ঠিক আছে, তুমি তা হলে একটু অপেক্ষা করো। আমি জপটা সেরে নিই। (নেপথ্যে)
দাঁড়াও, বসন্তসেনা, দাঁড়াও।
(বিট, শকার ও চেট অনুসৃতা বসন্তসেনার প্রবেশ)
বিট— দাঁড়াও, বসন্তসেনা, দাঁড়াও।
ভয় পেয়ে কেন তুমি তোমার দেহসুষমা হারিয়ে নৃত্যমৃদুল ছন্দিত চরণে ভয়চকিত কটাক্ষ হেনে ব্যাধতাড়িতা ভীতা হরিণীর মতো ছুটে যাচ্ছ? ॥ ১৭ ॥
শকার— দাঁড়াও, বসন্তসেনা, দাঁড়াও।
কেন তুমি যাচ্ছ, দৌড়াচ্ছ, পালাচ্ছ, স্খলিত চরণে ছুটে যাচ্ছ? কথা শোনো বালিকা, একটু দাঁড়াও। কামের দহনে আমার অসহায় হৃদয় জ্বলন্ত অঙ্গারে নিক্ষিপ্ত মাংসখণ্ডের মতো দগ্ধ হচ্ছে ॥ ১৮ ॥
চেট— ওগো নারী, দাঁড়াও, দাঁড়াও।
অকারণে ভয় পেয়ে গ্রীষ্ম-ময়ূরীর মতো কলাপ মেলে আমার কাছ থেকে কেন দূরে চলে যাচ্ছ? তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতো। এই যে আমাদের প্রভু অরণ্যে ধাবমান কুক্কুটশাবকের মতো তোমার কাছে ছুটে যাচ্ছেন ॥ ১৯ ॥
বিট— দাঁড়াও, বসন্তসেনা, দাঁড়াও।
রক্তবস্ত্রপরিহিতা তুমি বালকদলীর মতো রেশমি আঁচল বাতাসে আন্দোলিত করে অস্ত্রাঘাতে বিদীর্যমান মনঃশিলা-গুহার মতো কমল-মুকুল বিকিরণ করতে করতে কেন পালাচ্ছ? ॥২০॥
শকার— একটু দাঁড়াও, বসন্তসেনা।
কামানলশিখা দ্বিগুণ করে আর আমার রাতের নিদ্রা হরণ করে ভয়ভীতা তুমি স্খলিত চরণে চলে যাও কেন? এখন রাবণের কুক্ষিগত কুন্তীর মতো[১১] তুমি আমার বশীভূতা ॥ ২১ ॥
বিট— বসন্তসেনা, আমার চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছ কেন? তুমি কি খগেন্দ্রের ভয়ে সচকিতা সর্পিণী? চলার বেগে আমি পবনকেও পরাস্ত করতে পারি, কিন্তু হে বরগাত্রী! তোমাকে নিগ্রহ করার প্রচেষ্টা আমার নেই ॥ ২২ ॥
শকার— বন্ধু, বন্ধু–
তস্কর-প্রেয়সী, মৎস্য-ভোজিনী, নৃত্য-বিলাসিনী, সর্বনাশিনী, কুলনাশিনী, অবশ্যা, কামের পেটিকা, সুবেশিনী, বেশবধূ, বেশাঙ্গনা—এই দশ নামে ডাকি তবু সে আমার দিকে ফিরেও চায় না ॥ ২৩ ॥
বিট— ভয়বিহ্বল হয়ে তুমি ছুটে চলেছ কেন? তোমার কর্ণকুণ্ডল ইতস্তত আন্দোলিত হয়ে তোমার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করছে। তুমি বুঝি কুশলী শিল্পীর নখাহত বীণা অথবা তুমি যেন মেঘগর্জনে ভীতা সারসী ॥ ২৪ ॥
শকার— বিচিত্র অলঙ্কারের ঝন্ঝন্ শব্দ তুলে রাম-ভীতা দ্রৌপদীর মতো[১২] তুমি পালাচ্ছ কেন? বিশ্বাবসুর ভগিনী সুভদ্রাকে যেমন হনুমান হরণ করেছিলেন তেমিন তোমাকে আমি সহসা হরণ করব[১৩] ॥২৫॥
চেট— এই রাজবল্লভের মনোরঞ্জন করার পর তুমি মাছ-মাংস পাবে। মাছ-মাংস পেলে কুকুর আর মৃতদেহ স্পর্শ করে না ॥ ২৬ ॥
বিট— ওগো বসন্তসেনা, কটিতটে তারকার মতো উজ্জ্বল চন্দ্রহার, তোমার মুখদেশ মনঃশিলা-চূর্ণলেপনে শোভিত। এইভাবে ভীত হয়ে নগর-দেবীর মতো কোথায় চলেছ?॥ ২৭॥
শকার— কুকুরের ভয়ে ভীতা শৃগালীর মতো তুমি আমাদের ভয়ে দ্রুত পালাচ্ছ আর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ আমার হৃদয়টিকে ॥ ২৮ ॥
বসন্তসেনা— পল্লবক, পল্লবক– পরভৃতিকা, পরভৃতিকা।
শকার— (সভয়ে) বন্ধু, বন্ধু, এখানে লোকজন আছে দেখছি!
বিট— ভয় নেই, ভয় নেই।
বসন্তসেনা— মাধবিকা, মাধবিকা
বিট— (হেসে) দূর বোকা! ও তো পরিচারিকাদের খুঁজছে।
শকার— ও কি তা হলে স্ত্রীলোকদের ডাকছে?
বিট— হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ।
শকার— একশ জন স্ত্রীলোক আসুক না কেন, আমি তাদের মেরে ঠাণ্ডা করব। তারা জানে না, আমি কত বড় বীর।
বসন্তসেনা— (কেউ আসছে না দেখে) হায়, কী বিপদ! আমি এখন কী করি! পরিচারিকারাও সব পালিয়েছে দেখছি। এখন নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে হবে।
বিট— কই, ডাকো, ডাকো।
শকার— বসন্তসেনা, ডাকো তোমার পরভৃতিকাকে ডাকো— তোমার পল্লবককে ডাকো কিংবা গোটা বসন্তঋতুটাকেই ডাকো। আমি তোমাকে অনুসরণ করছি— দেখি, কে তোমাকে রক্ষা করে।
জমদগ্নির পুত্র ভীমসেন, কিংবা কুন্তীর পুত্র রাবণ,— দেখি কে তোমাকে বাঁচাতে পারে। আমি আজ তোমার কেশগুচ্ছ ধারণ করে দুঃশাসনের ভূমিকাকে রূপ দেব[১৪] ॥ ২৯ ॥
এই দেখো, এই দেখো এদিকে!
এই আমার সুতীক্ষ্ণ অসি, তোমার মস্তকটিও আমার নাগালে, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব অথবা মেরে ফেলব। অতএব, পালানোর দরকার নেই। যে মরবেই তাকে কে বাঁচায় দেখব ॥ ৩০ ॥
বসন্তসেনা— দোহাই আপনার, আমি অবলা–
বিট— তাইতো তোমাকে ধরছি।
শকার— তাই আজ প্রাণে বাঁচলে তুমি।
বসন্তসেনা— (স্বগত) এর অভয়বাণীতেও ভয় হয়। যাক্ যা আছে কপালে, (প্রকাশ্যে) আপনারা কি আমার এই অলঙ্কারগুলো নেবেন?
বিট— সে কী কথা? ছি, ছি! বাগানের লতা থেকে তো ফুল ছিঁড়ে নেওয়া যায় না।
তোমার অলঙ্কারে আমাদের প্রয়োজন নেই।
বসন্তসেনা— তবে আমাকে ধরে বা মেরে আপনার লাভ কী?
শকার— আমি দেবকল্প পুরুষ, আমি নররূপী শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে ভজনা করতে হবে।
বসন্তসেনা— (রেগে) শান্ত হন, যথেষ্ট হয়েছে, অসভ্যের মতো কথা বলবেন না।
শকার— (হাততালি দিয়ে ও হেসে) বন্ধু, শুনছ, এ কী বলছে? আমার ওপর দরদ দেখিয়ে বলছে, ‘এসো, তুমি শ্রান্ত’– সত্যি, প্রিয়ে, তোমার দিব্যি, আমি গ্রামান্তরেও যাইনি, নগরান্তরেও যাইনি, তোমার পেছনে ছুটে ছুটেই আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।
বিট— (স্বগত) আশ্চর্য, ও যখন বলেছে ‘শান্ত’ তখন নির্বোধটা মনে করেছে ‘শ্রান্ত’। (প্রকাশ্যে) ওগো, বসন্তসেনা, তুমি যা বললে তা যে গণিকালয়ের বিরুদ্ধ কথা। তা দেখ, বসন্তসেনা, যুবকের সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই গণিকালয় চলে, তোমরা গণিকারা হলে ঠিক পথের ধারে বেড়ে ওঠা লতার মতো। তোমার দেহটিকে তো অর্থ দিয়ে কেনা যায় অর্থাৎ ওটি বাজারের পণ্য। কাজেই তোমার প্রিয়জন-অপ্রিয়জন—উভয়কেই সমানভাবে সেবা কর ॥ ৩১ ॥
তা ছাড়া, একই দিঘিতে পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, মূর্খ, নীচ সকলেই স্নান করে। যে পুষ্পিত বিনম্র লতায় ময়ূর বসে সেই লতাতেই আবার কাকও বসে। একই নৌকোয় চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ নদী পার হয়। অতএব, দিঘি, লতা অথবা নৌকোর মতো তুমি সকলেরই সেবা কর ॥ ৩২ ॥
বসন্তসেনা— কিন্তু গুণই অনুরাগের কারণ, শক্তি প্রয়োগে অনুরাগ জন্মায় না!
শকার— শুনেছ বন্ধু, এই গর্ভদাসীটি কামদেবের উদ্যানে তাকে দেখার পর সর্বস্বান্ত চারুদত্তের প্রেমে পড়েছে, তাই আমাকে আর পছন্দ হয় না। এই যে বাঁ-দিকেই চারুদত্তের বাড়ি। দেখো বন্ধু এ যেন তোমার-আমার হাতছাড়া না হয়।
বিট— (স্বগত) আহ্, যে কথাটা গোপন রাখা দরকার মূর্খ সেটা ফাঁস করে দিল। বসন্তসেনা মহৎ চারুদত্তের প্রেমে পড়েছে। একেই বলে মণিকাঞ্চন যোগ, কথাটা খুবই ঠিক। তা হলে একে পালাতেই দেওয়া যাক; নির্বোধটার হাতে একে দিয়ে কী হবে? (প্রকাশ্যে) দেখ, শকার বাঁ-দিকেই কিন্তু সেই বণিকের বাড়ি।
শকার— হ্যাঁ, বাঁ-দিকেই তার বাড়ি।
বসন্তসেনা— (স্বগত) আশ্চর্য! সত্যি তো বাঁ-দিকেই তাঁর বাড়ি। এই লোকটি আমার ক্ষতি করতে গিয়ে আমার উপকারই করল— আমার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিল।
শকার— দেখ বন্ধু, মাষকলাইয়ের রাশির মধ্যে যেমন কালির গুঁড়ো মিশে যায়, তেমনি দেখতে দেখতে বসন্তসেনাও কোথায় হারিয়ে গেল।
বিট— সত্যি তো, কী ঘন অন্ধকার!
আমার আলোকবিস্তৃত নয়ন যেন সহসা অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, অন্ধকারে চোখ খোলা রেখেও মনে হচ্ছে আমি বুঝি চোখ বুজে আছি ॥৩৩॥ আবার,
অন্ধকারে আমার সর্বাঙ্গ লিপ্ত হচ্ছে, আকাশ যেন কাজল বর্ষণ করছে, [১৫] এবং
অসৎ পুরুষের সেবার মতো আমার দৃষ্টি বিকল হয়েছে ॥ ৩৪ ॥
শকার— বন্ধু, আমি তা হলে বসন্তসেনাকে খুঁজে দেখি?
বিট— কোনো চিহ্ন-টিহ্ন দেখতে পাচ্ছ কি যা লক্ষ্য করে খুঁজতে পার?
শকার— কী ধরনের চিহ্নের কথা বলছ?
বিট— যেমন ধর, তার অলঙ্কারের শব্দ, কিংবা ঘ্রাণসুখকর মালার সৌরভ।
শকার— ঠিক, আমি তার মালার গন্ধ শুনতে পাচ্ছি,[১৬] কিন্তু অন্ধকারে আমার নাক
একেবারে ভরে গেছে, তার অলঙ্কারের শব্দ দেখতে পাচ্ছি না। [১৭]
বিট— (জনান্তিকে) ওগো বসন্তসেনা, এই অন্ধকারে তুমি অদৃশ্য মেঘের বুকে বিদ্যুৎ-এর মতো, কিন্তু হে ভীরু, তোমার মালার সুবাস আর নূপুরের নিক্কণ তোমার অবস্থিতি ঘোষণা করে ॥ ৩৫ ॥
বসন্তসেনা, শুনতে পাচ্ছ?
বসন্তসেনা— (স্বগত) শুনেছি, বুঝতেও পেরেছি। (নূপুর ও মালা খুলে ফেলে, কিছুটা পরিক্রমা করে এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করে) এই তো, দেওয়ালে হাত দিয়ে বুঝতে পারছি, এটা বাড়ির পার্শ্বদার— কিন্তু এ যে বন্ধ!
চারুদত্ত— বন্ধু, আমার জপ শেষ হয়েছে। এখন তুমি যাও মাতৃদেবতাদের পূজার উপচার দিয়ে এস।
বিদূষক— না, আমি যাব না।
চারুদত্ত— হায়! ধিক!
দারিদ্র্যের দরুন মানবের আত্মীয়-স্বজনও তার কথা শোনে না, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও দূরে সরে যায়, তার নানা সমস্যা তীব্রতর হয়, সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তার চরিত্র-চন্দ্রের দীপ্তি ম্লান হয় আর অন্যের অপকর্মের দুর্নামের বোঝা তার ওপরেই চাপে ॥ ৩৬ ॥
তা ছাড়া,
দরিদ্রের সঙ্গ কেউ কামনা করে না, তাকে সাদর সম্ভাষণও জানায় না কেউ, সে যদি ধনীর গৃহের কোনো উৎসব উপলক্ষে যায় তখন সবাই তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। সামান্য পোশাক পরিহিত বলে সে লজ্জায় ধনীদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে। তাই, আমার মনে হয় দারিদ্র্য পঞ্চমহাপাপের অতিরিক্ত ষষ্ঠ মহাপাপ ॥ ৩৭ ॥
আবার,
হে দারিদ্র্য! তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। তুমি এতদিন পরম বন্ধুর মতো আমার সঙ্গে কাটালে, কিন্তু আমার মৃত্যুর পর তুমি কোথায় যাবে আমার সেই চিন্তা। ॥ ৩৮ ॥
বিদূষক— (সলজ্জভাবে) আচ্ছা, আমাকে যদি যেতেই হয় তবে রদনিকাও আমার সঙ্গিনী হোক।
চারুদত্ত— রদনিকা, তুমি মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও।
রদনিকা— আপনি যা বলেন।
বিদূষক— এই নৈবেদ্য আর বাতিটা ধরো তো রদনিকা, আমি এই দরজাটা খুলি।
(পার্শ্বদ্বার উন্মুক্ত করল)
বসন্তসেনা— (স্বগত) কে যেন দয়া করে দরজাটা খুলে দিল। তাহলে ভেতরে যাই।
(দেখে) আহ্, কী মুশকিল, একটা প্রদীপ রয়েছে যে!
চারুদত্ত— কী হল, মৈত্ৰেয়?
(শাড়ির আঁচলে প্রদীপ নিভিয়ে ভেতরে প্রবেশ)
বিদূষক— দরজাটা খুলতেই দমকা হাওয়া এসে প্রদীপটা নিভিয়ে দিল। রদনিকা, তুমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও, আমি চতুঃশালা থেকে প্রদীপটা জ্বেলে আনি। (প্রস্থান)
শকার— বন্ধু, আমি তবে বসন্তসেনাকে খুঁজে দেখি।
বিট— খুঁজে দেখো, খুঁজে দেখো।
শকার― (খুঁজে দেখে)— ধরেছি— ধরেছি, এই তো।
বিট— আরে মূর্খ, এ তো আমি।
শকার— তবে তুমি এখান থেকে সরে গিয়ে কোণে দাঁড়াও। (আবার খুঁজে এবং দাসকে ধরে) বন্ধু, এই এবার ধরেছি।
চেট— প্ৰভু, আমি দাস।
শকার— এইদিকে যাও বন্ধু, দাস তুমি ওইদিকে যাও। ও বন্ধু, ও দাস ও দাস, ও বন্ধু— তোমরা পাশে সরে যাও। (আবার খোঁজ করতে করতে রদনিকার কেশ ধারণ করে) এইবার আমি সত্যিই ধরেছি বসন্তসেনাকে, সত্যিই ধরেছি। অন্ধকারে পালাচ্ছিল, কিন্তু মালার গন্ধ পেয়ে বুঝেছি। যেমন চাণক্য দ্রৌপদীর[১৮] কেশাকর্ষণ করেছিল, আমিও তেমনি এর কেশপাশ ধরেছি ॥ ৩৯।
বিট— যৌবনগর্বে তুমি এক সৎ বংশজাত ব্যক্তিকে ধরতে যাচ্ছিলে, এখন তোমারই পুষ্পশোভিত সুচারু কেশ মুষ্টিতে ধরা পড়েছে ॥ ৪০ ॥
শকার— বলো! তোমার কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করে তোমাকে ধরেছি। এইবার উচ্চকণ্ঠে শম্ভু, শিব, ভগবান বলে চেঁচাও অথবা আর্তনাদ করো ॥ ৪০ ॥
রদনিকা— (সভয়ে) মশাইরা এ কী করছেন?
বিট— ওহে, এ যে অন্য কারও কণ্ঠস্বর!
শকার— দই-সরের লোভে বেড়াল যেমন গলার স্বর পালটায় এ বেটিও তেমনি গলার আওয়াজ বদলেছে[১৯]।
বিট— কী বললে! গলার স্বর পালটেছে! আশ্চর্য! না, না, এতে অবাক হবার কিছু নেই। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে কণ্ঠস্বর পরিবর্তনের কায়দাটি এ ভালোভাবেই রপ্ত করেছে—সেইসঙ্গে প্রতারণার কৌশলটিও ॥ ৪২॥
(বিদূষকের প্রবেশ)
বিদূষক— আহা, চমৎকার! হাড়িকাঠে বাঁধা বলির ছাগলের প্রাণটার মতো সন্ধ্যার মৃদুমন্দ বাতাসে প্রদীপের শিখা ফুর ফুর্ করছে। (অগ্রসর হয়ে রদনিকাকে ওই অবস্থায় দেখে) রদনিকা—
শকার— বন্ধু, মানুষ, মানুষ।
বিদূষক— এ ভারী অন্যায়। আমাদের সদাশয় চারুদত্তের অবস্থা পড়ে গেছে সত্যি কথা, কিন্তু তাই বলে তার ঘরে এমন পরপুরুষ ঢুকবে?
রদনিকা— মৈত্রেয়মশাই দেখুন, এরা আমায় কীভাবে অপমান করছে।
বিদূষক— কী বললে? অপমান? তোমার, না আমাদের?
রদনিকা— হ্যাঁ, এ আপনাদেরই অপমান।
বিদূষক— বলাৎকার নাকি?
রদনিকা— তা ছাড়া আর কী?
বিদূষক— সত্যি?
রদনিকা— সত্যি।
বিদূষক— (রেগে গিয়ে লাঠি তুলে) এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। নিজের আবাসে কুকুরও রুখে দাঁড়ায়। আমি তো একজন ব্রাহ্মণ। আমাদের ভাগ্যের মতোই বাঁকা এই লাঠি দিয়ে আয়, জীর্ণ-শুষ্ক বাঁশের আগার মতো তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই।
বিট— ক্ষমা করুন, হে সৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষমা করুন।
বিদূষক— (বিটের দিকে চেয়ে) না, এ কোনো অপরাধ করেনি— (শকারের দিকে চেয়ে) ওই লোকটাই অপরাধী। ওরে ব্যাটা, রাজার শ্যালক—সংস্থানক, অমানুষ, পাষণ্ড! এ তোর উচিত নয়। চারুদত্ত আজ দরিদ্র হয়েছে কিন্তু তাঁর গুণে কি উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত নয়? তবে তুই কোন সাহসে তারই গৃহে প্রবেশ করে এইভাবে তার দাসীদের লাঞ্ছনা করিস?
দারিদ্র্যে কারও অপমান হয় না, দৈবও দরিদ্র হিসেবে ব্যক্তিকে বিচার করে না। তাছাড়া ধনী লোকও যদি চরিত্রহীন হয় তবে সে-ই প্রকৃত দরিদ্র ॥ ৪৩ ॥
বিট— (লজ্জিত হয়ে) ক্ষমা করুন, মহাব্রাহ্মণ, ক্ষমা করুন। অন্য একজনকে মনে করে ভুল করে আমরা এই অন্যায় কাজ করে ফেলেছি— দেখুন, আমরা এক কামুকী নারীর অন্বেষণ করছিলাম—
বিদূষক—কী! এই নারীটিকে খুঁজছিলে? বিট— ছি, ছি, তা কেন হবে?
এক স্বাধীন-যৌবনা নারীকে (বারবনিতাকে) খুঁজছিলাম। সে যে কোথায় পালিয়ে গেল, আর এই জন্যেই ভ্রমক্রমে আমাদের এই চরিত্রচ্যুতি। ॥ ৪৪।। দয়া করে আমার যথাসর্বস্ব গ্রহণ করুন (তরবারি ফেলে দিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে পদতলে লুটিয়ে পড়ে
বিদূষক— তুমি তো ভালো লোক—ওঠো, ওঠো। আমি না জেনে তোমায় দোষ দিয়েছি। এখন জেনে আবার অনুনয় করছি।
বিট— আমি আপনার কাছেই অপরাধী— আমাকেই আপনি ক্ষমা করুন। যদি একটা কথা দেন তো উঠি
বিদূষক— কী কথা?
বিট— ব্যাপারটা চারুদত্তকে বলবেন না, দয়া করে।
বিদূষক— আচ্ছা, বলব না।
বিট— হে ব্রাহ্মণ, তোমার অনুগ্রহ মাথায় করে রাখব। আমরা সশস্ত্র কিন্তু গুণের অস্ত্রে আমরা পরাজিত ॥ ৪৫ ॥
শকার— (ঈর্ষাযুক্ত ক্রোধে) হাত জোড় করে তুমি এই অপদার্থ লোকটার পায়ে লুটিয়ে পড়ছ। ব্যাপার কী, বলো তো।
বিট– কারণ, আমি ভীত হয়েছি।
শকার— কার কাছে ভীত?
বিট— চারুদত্তের গুণের কাছে।
শকার— যার ঘরে গিয়ে কেউ একমুঠোও খাবার পায় না তার কী গুণ আছে, শুনি? বিট ও কথা বোলো না—
আমাদের মতো মানুষের প্রার্থনা মেটাতে গিয়েই তিনি আজ নিঃস্ব। ধনের গর্বে তিনি কাউকে কোনোদিন অপমান করেননি। গ্রীষ্মকালের পরিপূর্ণ জলাশয় যেমন পিপাসার্তদের তৃষ্ণা মিটিয়ে শুষ্ক হয়ে যায় তেমনি তিনি অভাবী মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে শুষ্ক হয়ে পড়েছেন ॥ ৪৬ ॥
শকার— (অসহিষ্ণুভাবে) এই গর্ভদাসীর পুত্তুরটি কে? তিনি কি পাণ্ডুর সেই সাহসী ও বীর পুত্র শ্বেতকেতু? অথবা তিনি কি রাধার ইন্দ্রদত্ত পুত্র রাবণ? কিংবা তিনি কি রামের ঔরসজাত কুন্তীপুত্র? না কি তিনি ধর্মপুত্র জটায়ু?[২০] ॥ ৪৭॥
বিট— ওরে মূর্খ, তিনি হলেন স্বনামধন্য চারুদত্ত। তিনি দুঃখীর কাছে ফলভারে অবনত কল্পতরু, ধার্মিকের আত্মীয়া। তিনি হলেন বিদ্বানের দর্পণ, নৈতিক আচরণের কষ্টিপাথর আর চরিত্ররূপ তীরভূমির সাগর। তিনি অতিথিবৎসল, কাউকে অসম্মান করেন না তিনি। তিনি পুরুষোচিত গুণের আধার, স্বভাবে অনুকূল ও উদার। বহুগুণের অধিকারী তিনিই একমাত্র প্রশংসার পাত্র। অন্যেরা শুধু বেঁচে আছে মাত্ৰ ॥ ৪৮ ॥
অতএব, চলো, আমরা এখান থেকে সরে পড়ি।
শকার— বসন্তসেনাকে না নিয়েই চলে যাব?
বিট— তোমার বসন্তসেনা হারিয়ে গেছে।
শকার— তাই নাকি? কেমন করে?
বিট— তোমাকে দেখে তিনি অন্ধের দৃষ্টি অথবা রোগীর পুষ্টির মতো, অথবা অলস ব্যক্তির সিদ্ধি কিংবা পাপাসক্ত ও দুর্বলস্মৃতিগ্রস্ত মানুষের পরমা বিদ্যার মতো অথবা শত্রুর প্রতি অনুরক্তির মতোই অলীক বস্তু হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছেন॥ ৪৯॥
শকার— বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি যাব না।
বিট— তুমি কি এটাও জান না যে—
হস্তী ধরা পড়ে বন্ধনস্তম্ভে, অশ্ব বাঁধা পড়ে বল্গায়, আর নারীকে ধরা যায় হৃদয়ের বন্ধনে। হৃদয় যদি না থাকে তোমার তাহলে বিদায় হও।। ৫০॥
শকার— তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার, আমি যাচ্ছি না।
বিট— বেশ, তবে আমিই চলে যাচ্ছি। (প্রস্থান)
শকার— তা হলে ও চলেই গেল দেখছি। (বিদূষকের প্রতি) ওরে কাক-পদ- ঝুঁটিওয়ালা শয়তান! বোসো বোসো বলছি।
বিদূষক— আমাদেরও আগেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।
শকার— কে বসিয়ে দিল?
বিদূষক— ভাগ্য।
শকার— বুঝেছি, এখন ওঠো তো দেখি, ওঠো।
বিট— হ্যাঁ, আমরা উঠে দাঁড়াব।
শকার— কখন?
বিদূষক– যখন ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হবে।
শকার— তা হলে, কাঁদো, কাঁদো I
বিদূষক— আমাদের তো কাঁদাচ্ছেই।
শকার— কে?
বিদূষক— দারিদ্র্য।
শকার— তবে হাসো হাসো।
বিদূষক— হ্যাঁ, হাসব
শকার— কখন?
বিদূষক— যখন মহান্ চারুদত্ত আবার ঐশ্বর্য ফিরে পাবেন তখন।
শকার— ওরে দুর্বৃত্ত, ভিখারি চারুদত্তকে আমার এই নির্দেশ জানাস— স্বর্ণাভরণে অলঙ্কৃতা, নবনাট্যের প্রদর্শনে প্রধানা অভিনেত্রীরূপা গণিকা বসন্তসেনা কামদেবের উদ্যানে যে তোমার প্রেমে পড়েছে তাকে জোর করে লাভ করতে গিয়েছিলাম বলে সে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে। এখন তাকে যদি তুমি স্বেচ্ছায়, আইনের আশ্রয় না গিয়ে মুক্তি দাও এবং আমার হাতে সমর্পণ কর তবে তোমার ও আমার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। কিন্তু যদি তুমি তাকে ছেড়ে না দাও তবে আমাদের মধ্যে আমরণ শত্রুতা থেকে যাবে। তাছাড়া, আরো মনে রেখো গোবরলিপ্ত বৃত্ত, শুষ্ক সবজি, রান্না-করা মাংস এবং শীতকালের-রাতে সিদ্ধকরা ভাতের মতো এই শত্রুতা সময়ের ব্যবধানে নষ্ট হবার নয় ॥ ৫১॥
ভালো করে বলবে আর কৌশলে বলবে। এমনভাবে বলবে যাতে আমি আমার প্রাসাদের চিলেকোঠায় বসে শুনতে পারি। যদি অন্যরকম বলো তাহলে কপাটে পিষ্ট কয়েতবেলের খোলের মতো তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব।
বিদূষক— আমি ঠিক ঠিক বলব।
শকার— (জনান্তিকে) চেট, বিট কি চলে গেছে?
চেট— আজ্ঞে হ্যাঁ।
শকার— তাহলে আমরাও এবার চলি।
চেট– কর্তা, আপনার তরোয়াল।
শকার— ওটা তোমার হাতেই থাক।
চেট— না কর্তা, এাঁ,। আপনার, আপনিই নিয়ে যান।
শকার— (বিপরীত দিক ধারণ করে)
মূলোর খোসার বর্ণবিশিষ্ট কোষমুক্ত এই তরবারি কাঁধে রেখে আবার তা কোষে আবৃত করে কুক্কুর-কুক্কুরী বিতাড়িত শৃগালের মতো এখন ঘরে ফিরে যাচ্ছি ॥ ৫২ ॥
(পরিক্রম করে প্রস্থান)
বিদূষক— রদনিকা, তোমার এই লাঞ্ছনার কথা চারুদত্তকে যেন বোলো না। একেতেই তিনি দারিদ্র্যদগ্ধ, তার ওপর এ সংবাদ পেলে তিনি দ্বিগুণ দুঃখ পাবেন।
রদনিকা— মৈত্রেয়মশাই, আমি রদনিকা— আমি মুখ খুলব না।
চারুদত্ত— (বসন্তসেনাকে উদ্দেশ্য করে) রদনিকা, বায়ুসেবনাভিলাষী রোহসেন এখন এই রাত্রিবেলায় শীতে কাতর হয়ে পড়েছে। তাকে ভেতরে নিয়ে যাও আর এই চাদরটি দিয়ে ঢেকে দাও।
বসন্তসেনা— (স্বগত)
(চাদরটি নিয়ে আঘ্রাণ করে এবং সাগ্রহে স্বগতোক্তি করে) আহ্! চাদরটিতে যুঁইফুলের কী সুন্দর সুবাস! মনে হচ্ছে এঁর যৌবনটি মোটেই উদাসীন নয়।
(একপাশে দাঁড়িয়ে চাদরটিতে নিজেকে আবৃত করে)
চারুদত্ত— রদনিকা, রোহসেনকে নিয়ে ভেতরে যাও।
বসন্তসেনা— (স্বগত) আহা! তোমার গৃহে প্রবেশ করার সৌভাগ্য কি আমার আছে?
চারুদত্ত— রদনিকা! উত্তর দিচ্ছ না— হায়, যখন কোনো মানুষ ভাগ্যচক্রে সম্পদ হারানোর বেদনা লাভ করে তখন তার বন্ধুরা পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়। এমনকি, সে তার দীর্ঘদিনের অনুরক্ত জনের কাছেও বিরাগভাজন হয়ে ওঠে ॥ ৫৩ ॥
(রদনিকা ও বিদূষক অগ্রসর হয়)
বিদূষক— মশাই, এই যে রদনিকা।
চারুদত্ত— এ তবে আমাদের রদনিকা! তাহলে আমার অজ্ঞতাবশত প্ৰদত্ত বস্ত্ৰে দূষিতা এই মহিলাটি তবে কে?
বসন্তসেনা— (স্বগত) ‘দূষিতা’ নয়, বরং ভূষিতা।
চারুদত্ত— শরতের মেঘে আবৃত চন্দ্রকলার মতো ইনি কে? ॥ ৫৪ ॥
না, পরস্ত্রীদর্শন অন্যায়।
বিদূষক— মশাই, পরস্ত্রীদর্শনের আশঙ্কা এখানে নেই। ইনি হলেন বসন্তসেনা—যিনি কামদেবের উদ্যানে গিয়ে আপনার প্রেমে পড়েছেন।
চারুদত্ত— তাহলে ইনিই বসন্তসেনা। (স্বগত) এঁর দ্বারাই আমার সর্বসত্তায় প্রেমোন্মাদনা জেগে উঠে আবার তা আমার বিশাল ঐশ্বর্যনাশের ফলে ভীরুজনের অক্ষম ক্রোধের মতো মিলিয়ে গেছে। ৫৫ ॥
বিদূষক— বন্ধু, রাজার শ্যালক যা বলেন তা হল-
চারুদত্ত — কী?
বিদূষক— ‘বসন্তসেনা নামে এই স্বর্ণভূষণে আচ্ছাদিতা, নবনাট্যের প্রদর্শনে উত্থিতা প্রধানা নটীরূপা (সূত্রধারিণী) গণিকা বসন্তসেনা যে কামদেব-উদ্যানে তোমার প্রেমে পড়েছে তাকে বলপ্রয়োগে লাভ করার চেষ্টা করতে সে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে।’
বসন্তসেনা— (স্বগত) সত্যি কথা বলতে কি, এই ‘বলপ্রয়োগে লাভ করা’ কথাগুলো যেন আমাকেই ধন্য করছে।
বিদূষক– এখন যদি বিচারালয়ের আশ্রয়ে না গিয়ে নিজে থেকেই তুমি আমার কাছে এঁকে ফিরিয়ে দাও তা হলেই আমার সঙ্গে তোমার প্রীতির সম্পর্ক না হলে আমরণ শত্রুতা থাকবে।
চারুদত্ত— (ঘৃণার ভাব নিয়ে) সে একটা আস্ত নির্বোধ। (স্বগত) আহা! এই নারী দেবীর মতো উপাস্যা। যখন তাকে আমার গৃহে প্রবেশ করতে আদেশ করলাম তখন সে আমার দুরবস্থার কথা স্মরণ রেখে প্রবেশ করল না। যদিও সে নানা পুরুষের সঙ্গে সপ্রতিভভাবে নানা ভঙ্গিতে কথা বলতে অভ্যস্ত তবু সে নীরব রইল। ৫৬
(প্রকাশ্যে) আর্যা বসন্তসেনা, আমি চিনতে না পেরে তোমাকে দাসী ভেবে তোমার প্রতি যে আচরণ করেছি তার জন্যে আমি নতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থী। বসন্তসেনা—এ জায়গায় অনধিকার প্রবেশ করায় আমিই অপরাধী এবং এ জন্যে
আমি নতশিরে প্রণাম করে আপনার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি
বিদূষক—বেশ, আপনারা দুজনেই ধানক্ষেতের দুই আলের মতো সুখে মাথা নুইয়ে
পরস্পর অভিবাদনের আদান-প্রদান করুন আর আমিও গজশাবকের অবনত জানুর মতো মাথা নিচু করে আপনাদের দুজনেরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।
চারুদত্ত— যাক, আর অনুনয়-বিনয়ে কাজ নেই।
বসন্তসেনা— (স্বগত) এঁর কথাবার্তা কী পরিপাটি আর মধুর! কিন্তু ওঁর এই দুরবস্থায় এভাবে এখানে আসাটা আমার উচিত হয়নি। ঠিক আছে, তবে এইভাবে বলি। (প্রকাশ্যে) দেখুন আমার প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে দয়া করে এই অলঙ্কারগুলো আপনার কাছে গচ্ছিত রাখুন— এই অলঙ্কারের জন্যেই দুর্বৃত্তরা আমার পিছু নিয়েছিল।
চারুদত্ত— এগুলো রাখবার পক্ষে কিন্তু আমার গৃহ নিরাপদ নয়।
বসন্তসেনা— আর্য, এ কথা ঠিক নয়। কারণ, গচ্ছিত রাখা হচ্ছে ব্যক্তির কাছে, গৃহের কাছে নয়।
চারুদত্ত— মৈত্রেয়, তা হলে এ অলঙ্কার রেখে দাও।
বসন্তসেনা— অনুগৃহীতা হলাম। (অলঙ্কার প্রদান )
বিদূষক— (গ্রহণ করে) আপনি সুখী হোন।
চারুদত্ত— আরে বোকা, গচ্ছিত রাখতে বলা হচ্ছে, দাতব্য করা হচ্ছে না।
বিদূষক– (অলক্ষে) তাই নাকি, তাহলে চোরে যেন চুরি করে নেবে।-
চারুদত্ত— অল্প দিনের মধ্যেই
বিদূষক— এঁর এই গচ্ছিত জিনিস—
চারুদত্ত— আমি এঁকে ফিরিয়ে দেব।
বসন্তসেনা— আর্য, এই মহাশয় যদি আমায় বাড়ি পৌঁছে দেন—
চারুদত্ত— মৈত্রেয়, এর সঙ্গে যাও।
বিদূষক— এই রাজহংসীর সঙ্গে রাজহংসের মতো আপনি গেলেই মানাবে। আমি সামান্য ব্রাহ্মণ, আমি গেলে লোকে আমাকে মারবে, চতুষ্পথে আনা নৈবেদ্য যেমন কুকুরে খায় আমিও তেমনি কুকুরের খাবার হব।
চারুদত্ত— ঠিক আছে, আমিই এঁকে পৌঁছে দিচ্ছি। দীপ জ্বেলে রাজপথ ভালোভাবে আলোকিত করার ব্যবস্থা করো।
বিদূষক— বর্ধমানক দীপ জ্বালাও।
চেটী— (জনান্তিকে) তেল ছাড়া মশাল জ্বলবে কী করে?
বিদূষক— (জনান্তিকে) কপর্দকশূন্য প্রেমিক জুটলে গণিকারা যেমন স্নেহশূন্য হয়ে পড়ে তেমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তেলহীন দীপগুলোর।
চারুদত্ত— মৈত্রেয়, দীপ থাক তবে। চেয়ে দেখ,— কামময়ী নারীর গণ্ডদেশের মতো পাণ্ডুর রাজপথের প্রদীপ চন্দ্র ওই গ্রহ পরিবেষ্টিত হয়ে উদিত হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে এর শুভ্ররশ্মি আর্দ্র কর্দমে ক্ষীরধারার মতো পতিত হচ্ছে ॥৫৭॥ (অনুরাগ সহ) বসন্তসেনা, এই তোমার গৃহ, প্রবেশ করো।
(অনুরাগের দৃষ্টি হেনে বসন্তসেনার প্রস্থান)
চারুদত্ত— সখা, বসন্তসেনা চলে গেলেন, এখন চলো আমরাও ঘরে ফিরি। রাজপথ জনশূন্য, কেবল প্রহরীরা চলাফেরা করছে, আমাদের চোর বলে ভুল না করে কেউ। রাত্রির অনেক দোষ। (পরিক্রমা করে) এই অলঙ্কার পেটিকাটি রাত্রে তোমার কাছে রাখবে, দিনের বেলা এটা থাকবে বর্ধমানকের কাছে। ৫৮ ॥
বিদূষক— আপনি যা বলেন।
(উভয়ের প্রস্থান)
॥ মৃচ্ছকটিকের ‘অলঙ্কারন্যাস’ নামক প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ॥
—
টীকা
পর্যঙ্কাসনকে সাধারণত ‘বীরাসনের’ সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। বীরাসনের লক্ষণ—
একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরুণি সংস্থিতম্।
ইতরস্মিংস্তথা চান্যং বীরাসনমূদাহৃতম্ ॥
(রঘুবংশম্-এর ত্রয়োদশসর্গীয় ৫২নং শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত)।
কিন্তু ‘পর্যঙ্ক’কে পৃথক্ আসন বলাই ভালো। শিবমহাপুরাণে অষ্টাসনের মধ্যে ‘পর্যঙ্ক’ ও ‘বীরাসন’ পৃথক আসনরূপে উল্লিখিত—
স্বস্তিকং পদ্মং মধ্যেন্দুং বীরং যোগং প্রসাধিতম্
পর্যঙ্কং চ যথেষ্টং চ প্রোক্তমাসনমষ্টধা ॥ শিবমহাপুরাণ ৭।২।৩৭।২০
২. একাদশ ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয় :
মনঃ কর্ণো তথা নেত্রে রসনা চ তয়া সহ।
নাসিকা চেতি ষট্ তানি ধান্দ্রিয়াণি প্রচক্ষতে!
–এখানে এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ই বিবক্ষিত।
৩. মূলের ‘ব্যপগতকরণং’ পদটি ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত। করণ = ইন্দ্রিয়। এখানে একাদশ ইন্দ্রিয়ই বিবক্ষিত। সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি ও অহংকারও ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত।
৪. এককথায় দর্শন অর্থাৎ নিজের ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি :
‘দ্রষ্টুঃ স্বরূপোহবস্থানম্’ (পাতঞ্জল যোগ, সূত্র ১৩)
৫. তুলনীয় :
পর্যঙ্কবন্ধস্থির পূর্বকায়মৃায়তং সংনমিতোভয়াংসম্ উত্তালপাণিদ্বয়সংনিবেশাৎপ্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥
ইত্যাদি শ্লোক, কুমারসম্ভভম্ (৪৫-৫০)
৬. সমুদ্রমন্থনে উদ্ধৃত বিষপানে শিবের কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করেছিল, তাই তাঁর নাম নীলকণ্ঠ।
৭. ‘গৌরী’-পদটি বিদ্যুল্লতার সঙ্গে উপমাটিকে সার্থক করেছে। দ্বিতীয় শ্লোকটি সম্ভবত বস্তুনির্দেশের জন্যেই লেখা হয়েছে (‘অর্থতঃ শব্দতো বাপি মনাগ্-বাক্যার্থসূচনম্’)। শিবের কণ্ঠে গৌরীর ভুজলতা স্থাপন চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেমোপাখ্যানেরই ইঙ্গিত। তাঁদের মিলন যে বর্ষার পটভূমিতে ঘটবে ‘নীলাম্বুদ’ পটটিতে তারই আভাস। ভাসের নাটক ‘চারুদত্তে’ মঞ্চে নান্দীপাঠ নেই। সেখানে আছে নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ। নান্দী সেখানে নেপথ্যেই অনুষ্ঠিত, মঞ্চে নয়।
৮. ‘ভূমিকা’ দ্রষ্টব্য।
৯. ‘বেশ’ সম্বন্ধীয় বিদ্যা। ‘বেশ’ কথাটি নানার্থক—
১. বেশ্যাদের বাসস্থান ২. অগ্নিবেশ-রচিত কামশাস্ত্র ৩. নেপথ্য। এখানে ‘নেপথ্যকলা’ একটু ব্যাপক অর্থে সাধারণ নাট্যকলাকেই বোঝাতে পারে।
১০. ‘অগ্নিং প্রবিষ্ট’; কথাটি নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। Wilson-এর মতে এর অর্থ স্বেচ্ছায় অগ্নিতে জীবনাহুতি; ‘Zarmancohagas (Sramanachaya ) burnt himself at Athens after the custom of his country, and colunus (Kalyana) mounted the funeral pile at pasaegadae in the resence of the astonished Greeks.)
(অগ্নিং প্রবিষ্টঃ— এই অংশে Wilson-এর টীকা)
M. R. Kale (‘অগ্নিং প্রবিষ্টঃ’ পদটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেননি; The words are not to be taken in their literal sense. They simply mean, like পুরন্দরাতিথিরভবৎ বা অমরেম্ব্রগণ্যত, ‘he died’. The writer has used the expression : only to show that Sudruka was an agnihotrin till his death, as we speak of a devotee of Siva as going to the mountain Kailasa, or of Vishnu to Vaikuntha. (টীকা : অগ্নিং প্রবিষ্টঃ)
১১. ‘পরবারণ’ অর্থ শত্রুর হাতিও হতে পারে, শ্রেষ্ঠ হাতিও হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থটিই সঙ্গত।
‘শত্রুর হাতির সঙ্গে’– এই মানে সহজ হলেও সঙ্গত নয়। হাতির সঙ্গে মানুষের বাহুযুদ্ধ কল্পনায়ও আসে না।’
–ড. সুকুমার সেন, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।
১২. শকারের একটি বিশেষ বাগভঙ্গী যেখানে আছে ঘটনা, কাল বা চরিত্রের বৈবরীত্য।
১৩. ১১নং টীকা দ্রষ্টব্য।
শকার-চরিত্রটিকে হাস্যোদ্দীপক করার জন্যেই এ ব্যবস্থা।
১৪. বলা বাহুল্য শকারের এই পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখটি অভ্রান্ত।
১৫. ভাসের চারুদত্ত নাটকেও এই শ্লোকটি আছে। এটি কাব্যপ্রকাশে প্রথমে উৎপ্রেক্ষা ও পরে সংসৃষ্টির উদাহরণ হিসেবে আলোচিত। দণ্ডীর কাব্যপ্রকাশেও এটি উদ্যহৃত।
১৬-১৭. ড. সুকুমার সেনের সরস মন্তব্য : ‘এখনকার দিনের অভিনব-কবিভারতীয় অনুপযুক্ত নয়’।
(ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৩০৫)
of: Eye of man hath not heard, norear ser.
(Midsummer Night’s Dream)
১৮. ১১, ১২-১৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।
১৯. শকারের উপমাপ্রয়োগ কিন্তু মাঝে মাঝে চমকপ্রদ!
২০. শকারের সেই পরিচিত বাক্শৈলী : এখানে উল্লিখিত সব চরিত্রই শৌর্যের জন্যে খ্যাত। শকার পুরাণেতিহাস জানে না তা নয়, তবে একজনের সঙ্গে আর একজনকে গুলিয়ে ফেলে, মজাটা সেখানেই।