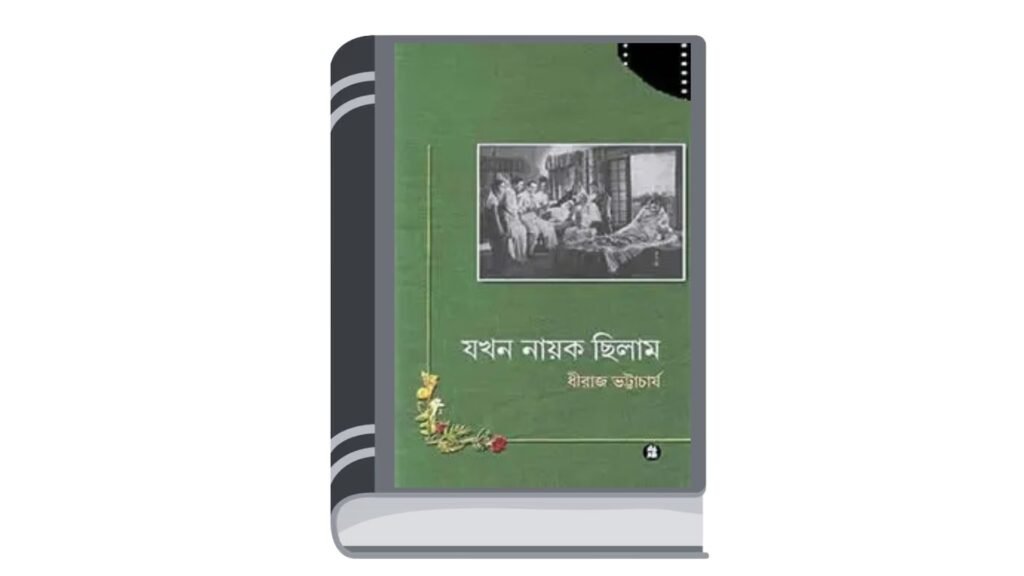৩. ম্যাডান স্টুডিও
ম্যাডান স্টুডিওর দক্ষিণ-কোণ ঘেঁষে গড়িয়াহাট রোডের উপর বহুদিনের জীর্ণ পুরোনো একখানি চালাঘর। বেশ খানিকটা দুর থেকে উগ্র গন্ধে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে ওটা তাড়ির আড্ডা। সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি আটটা-নটা পর্যন্ত হৈ-হল্লা, মারামারি আর অবিরাম গান চলে দোকানটিতে। পচা তাড়ির দুর্গন্ধে এক-এক সময় স্টুডিওতে কাজ করাও কষ্টকর হয়ে পড়ত। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যেতাম এই ভেবে যে, দোকানটি ম্যাডান স্টুডিওর সীমানার মধ্যে হলেও কেউ প্রতিবাদ করে না বা ওদের তুলে দেবার জন্যে চেষ্টাও করে না।
সেদিন মৃণালিনী ছবির শুটিং-এ মেক-আপ রুমে সবে এসে বসেছি, কানে এল তাড়ির আড্ডার বেসুরো গোলমাল। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার মনে করে মেক আপ করেই চলেছি, হঠাৎ দেখি স্টুডিওর সব কর্মী, এমনকি মেক-আপ ম্যান পর্যন্ত ছুটেছে গেটের দিকে। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি! অসমাপ্ত মেক-আপ নিয়ে মেক-আপ রুমের দরজায় দাঁড়ালাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম দোকানটা, সামনে রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক। একটু বাদেই দেখি পুবদিক থেকে চার-পাঁচটা খাকি পোশাক পরা পুলিশ ছুটে চলেছে দোকানমুখো। কৌতূহলে ছটফট করতে লাগলাম। মুখে খানিকটা রং মাখা, নইলে নিজেই চলে যেতাম। গেটের দিক থেকে পরিচালক জ্যোতিষবাবুকে এদিকে আসতে দেখা গেল। একরকম ছুটে গিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী?
জ্যোতিষবাবু বললেন, ব্যাপার আবার কী! নতুন কিছুই নয়। দুজনে তাড়ি খেতে খেতে ঝগড়া হয়। একজন আরেকজনের মাথায় তাড়ির কলসি ভেঙেছে। মাথা ফেটে চৌচির।
বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বললাম,সাহেবরা ইচ্ছে করলেই তো ঝেটিয়ে দুর করে দিতে পারেন। কী জন্যে এই সব নোংরা উৎপাত সহ্য করতে ওদের পুষে রেখেছে বলতে পারেন?
–পারি, কিন্তু বলব না। অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন জ্যোতিষবাবু।
–আপনাদের এসব হেঁয়ালির কথা বুঝি না মশাই, পুলিশও কিছু করতে পারে?
–না।
গেটের কাছে একটা শোরগোল শুনে দুজনে ফিরে চাইলাম। চার-পাঁচটা লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলেছে থানামুখো, পিছনে হুজুগপ্রিয় জনতা মজা দেখতে চলেছে সঙ্গে।
জ্যোতিষবাবু বললেন,ঐ তো নিয়ে চলেছে, কাল সকালে এসে দেখো জমজমাট আচ্ছা, যেন কিছুই হয়নি।
বললাম, দোহাই আপনার মিঃ ব্যানার্জি, দয়া করে আসল কথাটা বলবেন কি?
–আসল কথা?
চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিলেন জ্যোতিষবাবু, তারপর আমায় আরও খানিকটা দূরে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বললেন, তাড়ির দোকান নিয়ে বেশি কৌতূহল দেখিও না। শুধু এইটুকু জেনে রেখো ওদের পেছনে মুরুব্বি হলো আমাদের সাহেবরা। নিজের চোখে দেখলে ওদের ধরে নিয়ে গেল থানায়। সন্ধ্যের মধ্যেই সাহেবদের যে কেউ এসে জামিন হয়ে ওদের ছাড়িয়ে নেবে। তারপর কোর্টে কেস উঠলে যা ফাইন হবে তাও দিয়ে দেবে।
হাঁ করে শুধু চেয়েই আছি। জ্যোতিষবাবু হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না? সাহেবরা ছেলেবুড়ো সবাই তাড়ি খায়। তাড়িটা ওদের ডালভাতের মতো নিত্য-প্রয়োজনীয় পানীয়। ভোরবেলায় টাটকা তাড়ির জোগান দেয় ঐ দোকান। এবার বুঝলে আসল কথাটা? এখন যাও, আর দেরি কোরো না, বেলা সাড়ে আটটা বাজে। মেক-আপটা সেরে ফেল। আজ যেতে হবে বজবজের দিকে।
মেক-আপ শেষ করে হেমচন্দ্রোচিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে বেরোতেই নটা বেজে গেল। ছোট প্রাইভেট গাড়িটায় আমি, জ্যোতিষবাবু আর ক্যামেরাম্যান চালর্স ক্রীড, পিছনে একটা বড় ভ্যানে ক্যামেরা ও তার সাজসরঞ্জাম, গোটা দশ-বারো রিফ্লেক্টার, পাঁচ-ছটা বেতের মোড়া, একটা বড় শতরঞ্জি, ডাব সোডা লেমনেড আর সব। সহকর্মীরা।
দিন পনেরো হল মৃণালিনীর শুটিং আরম্ভ হয়েছে। রোজ শুটিং থাকে না, হপ্তায় দুতিন দিন শুটিং পড়ে। প্রথম দিন এসেই ক্যামেরায় যতীন দাসকে না দেখে তার বদলে সাত ফুট লম্বা চওড়া বিরাটকায় আইরিশম্যান চালর্স ক্রীডকে দেখে অবাক হয়ে জ্যোতিষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, যতীনকে নিলেন না কেন?
জ্যোতিষবাবু বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন, কেন নেব? গাঙ্গুলীমশাই দেবীচৌধুরাণী ছবিতে নিয়েছেন যতীনকে?
কিছু বুঝলাম না, চুপ করে রইলাম।
জ্যোতিষবাবু বললেন, ইটালীর জাহাজ কলকাতার জেটিতে ভিড়তে না ভিড়তেই কোত্থেকে খবর পেয়ে ইটালীর নামকরা ক্যামেরাম্যান টি. মারকনিকে একেবারে ছোঁ মেরে গাঙ্গুলীমশাই নিয়ে তুললেন ৫নং ধর্মতলা স্ট্রীটে। সেদিন আবার ফ্রামজী আমেরিকা চলে যাচ্ছেন। দুমিনিটের মধ্যে দেখি মারকনির কাঁধে হাত দিয়ে বিজয়গর্বে ফ্রামজীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন গাঙ্গুলীমশাই। শুনলাম মারকনি শুধু গাঙ্গুলীমশাইয়ের ছবি তুলবে। যাকে বলে এক্সকুসিভ। মাসে ছশ টাকা মাইনে। তুমিই বলো ধীরাজ, আমি তাহলে কেন পঞ্চাশ টাকার ক্যামেরাম্যান যতীন দাসকে দিয়ে মৃণালিনী তুলব? খুঁজতে লেগে গেলাম, তারপর ক্রীড সাহেবকে রাজী করিয়ে ধরে নিয়ে গেলাম রুস্তমজীর কাছে। চারশ টাকায় সব ঠিক করে পরদিন থেকে শুরু করলাম শুটিং।
কথা শেষ করে বিজয়ী সেনাপতির মতো সোজা হয়ে সিগারেট ধরালেন জ্যোতিষবাবু। বেচারী যতীনের জন্যে একটি সমবেদনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করবার রইল না।
চার্লস ক্ৰীড একজন নামকরা মেকানিক। ক্যামেরা, প্রোজেক্টিং মেসিন এইসব সারাতে ক্ৰীড সাহেবের জোড়া তখন কলকাতায় ছিল না। সদালাপী নিরহংকার মানুষ, অল্প সময়ের মধ্যেই চট করে হৃদ্যতা হয়ে যায়।
জ্যোতিষবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত জায়গা থাকতে বজবজে এমন কী লোকেশান পেলেন?
ফলাও করে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত-মুখ নেড়ে কথা বলা জ্যোতিষবাবুর একটা সহজাত অভ্যাস। বললেন, চারদিকে ধূধূ করছে তেপান্তর মাঠ। দূরে, বহু দূরে দেখা যায় একটা বড় পুকুর, কাছে গেলে দেখা যাবে শানবাঁধানো ঘাট। ঘাটের দুপাশে দুটি বিশাল বটগাছ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে পথশ্রান্ত হেমচন্দ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে।
আতঙ্কিত হয়ে বললাম, এই কাঠফাটা রোদ্দুরে ঐ ধূধুকরা তেপান্তর মাঠ ভেঙে হাঁটতে হবে আমাকে।
সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জ্যোতিষবাবু বললেন, ইয়েস।
বললাম, হেমচন্দ্র তো রাজা, লোকজন হাতি ঘোড়া এমন কি একটা ছাতা পর্যন্ত না নিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন কেন, বুঝলাম না।
–বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলে মহা উৎসাহে বলতে শুরু করলেন জ্যোতিষবাবু, কোনো গুরুতর রাজনৈতিক কারণে সকলের অগোচরে ছদ্মবেশে, মানে রাজকীয় পরিচ্ছদ একটা চাদরে ঢেকে হাতি ঘোড়া লোকজন কিছু না নিয়ে সাধারণ নাগরিকের মতো একাকী হেঁটে চলেছেন হেমচন্দ্র গুরুদেব মাধবাচার্যের সন্ধানে। সাধারণ রাজপথ। নগর-গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেলে হয়তো কেউ চিনে ফেলতে পারে তাই সাধারণের অগম্য মাঠঘাট ভেঙে চলেছেন তিনি। ঐ বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বটগাছতলায় একটু বিশ্রাম করে, শান বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে নেমে অঞ্জলি করে জলপান করে তৃষ্ণা অপনোদন করবে তুমি। তারপর
বাধা দিয়ে বললাম–অজানা পুকুরের ঐসব নোংরা জল আমি কিন্তু খেতে পারবো না বাঁড়ুয্যেমশাই।
একটু ভেবে নিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, কুছ পরোয়া নেই, খাওয়ার ভঙ্গী কোরো–তাহলেই আমি ক্যামেরায় ম্যানেজ করে নেব।
–পুকুরের জল খেয়ে তারপর কী করব?
–বাঁ পাশের রাস্তা ধরে সটান ঢুকবে গিয়ে জঙ্গলে, কিন্তু পুকুরের পাড় ঘেঁষে এমনভাবে হাঁটবে যাতে তোমার ছায়া পড়ে পুকুরের জলে।
একে কাঠফাটা রোদ্দুর তার উপর শুটিং-এর যা ফর্দ শুনলাম তাতে খুশি হবার কথা নয়। চুপ করে বসে হতভাগ্য হেমচন্দ্রের কথা ভাবছিলাম, কানে এল–পুওর ধীরাজ।
চেয়ে দেখি আমার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছেন ক্রীড সাহেব। বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, আপনি বাংলা বুঝতে পারেন?
তেমনি হাসতে হাসতেই ক্রীড সাহেব বললেন, ইয়েস, কিনটু বালো বুলটে পারে না।
হাসি গল্পে বাকি সময়টা কেটে গেল। আমরা লোকেশানে পৌঁছে গেলাম। বহুদিন আগে বোধহয় কারও বাগানবাড়ি ছিল। এখন বাড়ির চিহ্নও নেই। ধু ধু করছে মাঠ, সেই মাঠ ভেঙে সামনে পড়ে শানবাঁধানো পুকুরটা।
জ্যোতিষবাবু বললেন, কাল ছ-সাতজন লোক পাঠিয়ে পুকুরটার শ্যাওলা তুলিয়ে ঘাট পরিষ্কার করে রেখে গেছি। এ লোকেশানের একমাত্র সম্পদ হলো ঘাটের দুপাশে দুটি বটগাছ। তারই ছায়ায় শতরঞ্জি মোড়া বিছিয়ে সবাই বসলাম।
মামুলি শুটিং। শুধু হাঁটা, কোনও বৈচিত্র্য নেই। রোদ্দুরের তাপ বেড়ে উঠলে মাঝে মাঝে বটগাছতলায় এসে বসি। ডাব, সোলা, লেমনেড খাই। আবার খুঁটি। এইভাবে বেলা চারটে পর্যন্ত শুটিং চলল। সব গোছগাছ করে স্টুডিওতে গিয়ে মেক-আপ তুলে পোশাকআশাক ছেড়ে বাড়ি আসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল।
শোবার ঘরে তক্তপোশের পাশে ছোট গোল টেবিলটার উপর একখানা খামের চিঠি, অপরিচিত মেয়েলি হাতের লেখা। আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ভয়ে ভয়ে চিঠি খুললাম। খিদিরপুর থেকে রিনি লিখেছে–
শ্রীচরণকমলেষু,
ছোড়দা, আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হইতে চলিল, তুমি আমাদের বাড়ি আসো না। ব্যাপার কী? গোপাদির কলেজ বন্ধ, প্রায় রোজই আমাকে পড়াইতে আসেন। তিনিও তোমার কথা বলেন। আমরা কী এমন অপরাধ করিয়াছি যাহার জন্য তুমি কোনো খবর পর্যন্ত দাও না? লক্ষ্মী ছোড়দা, এ রবিবারে আসা চাই-ই কিন্তু। আমরা তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিব। ইতি–তোমার স্নেহের,
পার্ল হোয়াইট
ছোট্ট চিঠি। বক্তব্যও অস্পষ্ট নয়, তবুও একবার দুবার তিনবার পড়লাম চিঠিখানা। খিদিরপুর যাবার আকুল আহ্বান যে একা শুধু রিনির নয়, এটা বুঝতেও কষ্ট হয় না। সংকল্প সেদিনই রাত্রে চৌরঙ্গি রোডে দাঁড়িয়ে ঠিক করে ফেলেছিলাম। কুহকিনী আশা তবুও মনটাকে দোলা দিতে লাগল। ভাবলাম যাই না রবিবার, গোপাকে সব কথা খুলে বলে আমার তাসের অট্টালিকা চিরদিনের মতো ভূমিসাৎ করে দিয়ে আসি। পরক্ষণেই মনে হল সে দৃঢ় মনোবল আমার নেই, আর তা ছাড়া তাতে লাভই বা কী! তার চেয়ে বরং রিনিকে লিখে দিই–পার্ল হোয়াইট, তোমার চিঠি পেলাম। ইচ্ছে থাকলেও অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বিধানে যাদের হাত-পা বাঁধা, সেই সব অসহায় হতভাগ্য জীবগুলোর মধ্যে তোমার ছোড়দা অন্যতম। না, ঠিক হচ্ছে না। এই লিখি তোমার গোপাদিকে বোলো, কুঁড়েঘরে শুয়ে অট্টালিকায় বাস করার স্বপ্ন দেখা ভাল, তাতে কারও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু বিপদ হয় তখনই, যখন কুঁড়েঘরের বাসিন্দা স্বপ্নকে সত্য মনে করে অট্টালিকার পানে হাত বাড়ায়–।
হঠাৎ মনে হল খুব কবিত্ব করে চিঠি তো লিখছি কিন্তু চিঠিটা দেব কাকে? রিনিকে? রিনিকে দেওয়া মানে কাকা কাকিমার হাতে সে চিঠি পড়বেই। তখন? চিঠি দিয়ে ক্ষণিক সান্ত্বনা হয়তো পাব, কিন্তু আমাকে উপলক্ষ করে দুটো সংসার-অনভিজ্ঞা সরল মেয়ের জীবনে যে অশান্তি ও বিপ্লবের আগুন জ্বলবে তা নিভতে অনেক সময় লাগবে। মন ঠিক করে ফেললাম–রিনির চিঠির জবাবও দেবো না, খিদিরপুরেও আর যাবো না। টুকরোটুকরো করে রিনির চিঠিটা জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলাম। চেয়ে দেখি, শুটিং থেকে এসে জামাকাপড় ছাড়িনি। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম।
কতক্ষণ মনে নেই–জেগেই ছিলাম। চমক ভাঙল মায়ের কথায়। বিছানার কাছে মা দাঁড়িয়ে বলছেন, তোর আজ হল কী? শুটিং থেকে এসে মুখ হাত ধুলি না, খাবার খেলি না। এদিকে রাত নটা বাজে। এখন দয়া করে খেয়ে নিয়ে আমায় রেহাই দাও। সারাদিনের পর একটু জিরিয়ে বাঁচি।
সত্যিই লজ্জা পেলাম। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে খেতে চলে গেলাম। খেয়ে দেয়ে বাইরের অন্ধকার রকটায় চুপ করে বসে রইলাম। একটু বাদে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাবা এখনও টিউশনি থেকে ফেরেননি। মা-ও না খেয়ে বাবার জন্যে বসে আছেন। সাধারণত নটা সাড়ে নটার মধ্যে ফেরেন, আজ এত দেরি হবার কারণ কী? বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়ল, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি বাবা। বাবার সাড়া পেয়ে মা-ও সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বাবা মাকে বললেন, তোমরা খেয়ে নাও, আমি কিছু খাব না। জ্বরটা একটু বেশি বলেই মনে হচ্ছে।
গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেশ গরম। বাবার সঙ্গে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলাম। জুতো জামা খুলে দিতেই বাবা শুয়ে পড়লেন। কাছে বসে কপালটায় হাত বুলোত বুলোতে জিজ্ঞাসা করলাম, জ্বরটা কবে থেকে হচ্ছে?
ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাবটা মা-ই দিলেন, আজ চার-পাঁচ দিন রোজ বিকেলে স্কুল থেকে এসেই শুয়ে পড়েন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি গরম। বিশ্রাম নিতে বললে বলেন–ও কিছু নয়, শীতকালে বিকেলবেলায় ওরকম হয়।
বললাম, আমায় এসব জানাওনি কেন?
মা বললেন, উনি বলতে দেননি। বলেন, মিছিমিছি ওকে ব্যস্ত কোরো না।
লজ্জায় ধিক্কারে মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। স্বার্থপরের মতো নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-অভিমান নিয়েই মত্ত হয়ে ছিলাম, আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজনই মনে হয়নি।
বাবাকে বললাম, কাল থেকে আপনাকে কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে বাবা, আমি সকালেই ডাঃ এন. এন. দাসকে ডেকে আনব।
ডাঃ এন. এন. দাস বাবার বিশেষ বন্ধু এবং তখনকার দিনে ভবানীপুর অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। পূর্ণ থিয়েটারের বিপরীতে পপুলার ফার্মেসী ওঁরই প্রতিষ্ঠিত।
ম্লান হেসে বাবা বললেন, দাসকে একবার ডাকতে পারো, তবে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সামনে ছেলেদের বাৎসরিক পরীক্ষা, খুব ক্ষতি হবে। তাছাড়া সামান্য জ্বরে তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন?
বললাম, সামান্য হোক আর যাই হোক, কাল থেকে ভাল ভাবে না সেরে ওঠা পর্যন্ত আপনি স্কুল বা টিউশনিতে যেতে পারবেন না। মা-ও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন দেখে বাবা দু একবার ক্ষীণ আপত্তি তুলে চুপ করে গেলেন।
মিত্র ইনস্টিটিউশনের দীর্ঘ কুড়ি বছর চাকরির মধ্যে বাবা খুব কমই ছুটি নিয়েছিলেন। পরদিন পনেরো দিনের একটা ছুটির দরখাস্ত হেডমাস্টারমশাইকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করে এলাম। ঠিক হলো দুজন উঁচু ক্লাসের ছাত্র বাড়িতে এসে পড়ে যাবে, বাকি দুজন যারা নীচু ক্লাসে পড়ে তাদের সন্ধ্যার পর আমি গিয়ে পড়িয়ে আসব।
সব শুনে মা বললেন, সবই তো হলো, কিন্তু রাত জেগে পড়াশুনোটা বন্ধ করতে পার?
বাবার এই রাত জেগে পড়াশুনোর পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। বাবা আমার ঠাকুর্দার একমাত্র ছেলে। শৈশবে মাতৃহীন, কাজেই ছোটবেলা থেকেই ভীষণ একগুয়ে ও খেয়ালি ছিলেন। তখন স্কুলে পড়েন, এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাত্র এক বছর বাকি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রবল ভাবে শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশে। বাবাও মেতে উঠলেন। স্কুল ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর্দাকে বললেন, ম্লেচ্ছভাষা পড়ব না, দেবভাষা পড়ব। যে কথা সেই কাজ। কৃষ্ণনগরে গিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্কৃত টোলে ভর্তি হয়ে পড়লেন। কুমার ক্ষৌণিশচন্দ্র তখন খুব ছোট। পরে বাবা তার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এর পরের বিচিত্র ইতিহাস বর্তমান কাহিনীতে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকতাই বর্তমানেই ফিরে যাচ্ছি।
মিত্র ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার সতীশচন্দ্র বোস বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। দুজনের বন্ধুত্বও ছিল প্রগাঢ়। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি একদিন স্কুলের ছুটির পর বাবাকে নিভৃতে ডেকে বললেন, ভারি বিপদে পড়েছি ললিতবাবু, স্কুল ইন্সপেক্টর সার্কুলার পাঠিয়েছেন হাইস্কুলে ননম্যাট্রিক মাস্টার রাখা চলবে না। আপনাকে ছাড়তেও প্রাণ চায় না অথচ আইন মানতে গেলে রাখতেও পারছি না। কী করি বলুন তো? একটু চুপ করে থেকে বাবা বললেন, সার্কুলার ঠিক কবে থেকে কার্যকরী হবে? সতীশবাবু বললেন, বছরখানেক তো বটেই, আরও ছমাস চেষ্টা করলে বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। বাবা বললেন, ঠিক আছে আপনি ভাববেন না। এর পরই রাত জেগে পড়তে শুরু করলেন বাবা। দিনে একদম সময় পেতেন না, রাতে জেগে পড়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ১৯২২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিঙে ছেলের বয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে পরীক্ষা দিলেন। ওর মধ্যে বাবার কয়েকটি ছাত্র ছিল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বার হলে দেখা গেল, বাবা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছেন। তখনকার দিনের কয়েকটি নামকরা দৈনিকে এ সম্বন্ধে সরস মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।
ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানি হেডমাস্টার সতীশবাবুর হাতে দিয়ে বাবা বললেন, নেশা যখন একবার লাগিয়ে দিয়েছেন তখন এতেই মামলা শেষ হলো না প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে বি.এ. পর্যন্ত পাস করে তবে থামব। অদ্ভুত অধ্যবসায় ও মেধা ছিল বাবার। আমরা বয়সের কথা উল্লেখ করলে বলতেন–পড়াশুনার কি বয়স আছে রে। যে সময়ের কথা বলছি, বাবা তখন প্রাইভেটে আই.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমনিতেই বাবা খুব রোগা ছিলেন। আজ লক্ষ্য করে দেখলাম যেন আরও রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মাথার বালিশ ও তোশকের নীচে লুকিয়ে রাখা আই.এ. কোর্সের বইগুলো জড়ো করে নীচে নেমে এলাম।
রাজ্যহারা মগধ রাজকুমার হেমচন্দ্র। লোকালয় ছেড়ে মানুষের অগম্য বন জঙ্গল ভেঙে হেঁটেই চলেছেন। অবশেষে দেখা গেল দূরে গুরুদেব মাধবাচার্যের ক্ষুদ্র পর্ণকুটির। কুটিরের নিকটবর্তী হয়ে হেমচন্দ্র দেখলেন বাইরে কুটির সংলগ্ন উঠোনে মৃগচর্মাসনে বসে আচার্য চক্ষু মুদ্রিত করে জপে নিযুক্ত আছেন। যুক্তকরে হাঁটু গেড়ে বসে গরুড়পক্ষীর মতো হেমচন্দ্র গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।
জ্যোতিষবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন,কাট!
ক্রীড সাহেব ক্যামেরার হাতল ঘোরানো বন্ধ করলেন। আমি ঐ অস্বস্তিকর হাঁটু ভেঙে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁচলাম। মাধবাচার্য মৃগচর্মের নীচে লুকিয়ে রাখা একটা চৌকো টিনের কৌটো থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে পরমানন্দে টানতে লাগলেন।
শুটিং হচ্ছিল স্টুডিওর পূর্ব দিকের জঙ্গলে। বাঁশ খড় লতাপাতা দিয়ে স্টুডিওর মিস্ত্রিরা তিন-চারদিন ধরে তৈরি করেছে এই ঘরখানি। দূর থেকে দেখলে আঁকা ছবির মতো দেখায়। মাটির দেয়াল। মাটি উঁচু করে দাওয়া। সামনে খানিকটা জায়গায় ঘাসগুলো কোদাল দিয়ে চেঁছে গোবর নিকিয়ে হয়েছে উঠোন। পাশে ছোট্ট একটা মাটির বেদীর উপর তুলসী গাছ। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটিরখানি। চারপাশে ঘন গাছ-আগাছার জঙ্গল। ঘরের মধ্যে ধ্যানে বসলে আলো পাওয়া যাবে না। অগত্যা বাধ্য হয়েই গুরুদেবকে উঠোনে মৃগচর্ম বিছিয়ে বসতে হয়েছে। মাধবাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন কার্তিকচন্দ্র দে। বিরাট দেহ, প্রায় সাড়ে ছফুট লম্বা। সাদা দাড়ি গোঁফ, মাথায় বিরাট জটা। পরনে গেরুয়া কাপড় ও আলখাল্লা, তার উপর বাঘছাল আঁটা। দেখলে ভক্তি দেশ ছেড়ে পালায়, আসে ভয়।
জ্যোতিষবাবু ক্রীড সাহেবকে ক্যামেরা কাছে আনতে বললেন। এবার ক্লোজ শটে নেওয়া হবে ডায়লগগুলো। একটু পরেই ক্ৰীড সাহেব বললেন, ইয়েস, আই অ্যাম রেডি মিঃ ব্যানার্জি। আবার সেই আগের মতো হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসলাম। জ্যোতিষবাবু বললেন, স্টার্ট ক্রীড সাহেব ক্যামেরার হাতল ঘোরাতে শুরু করলেন।
গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গ হল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে আমার দিকে চাইলেন। ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললাম, গুরুদেব! আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কী আদেশ করেন? যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব বিধিলিপি। নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গৌড় জয় করিল কী প্রকারে?
মাধবাচার্য–বৎস, দুঃখিত হইও না। দৈব নির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি—
গুরুদেব আর বলতে পারলেন না। নিস্তব্ধ জঙ্গলে যেন কাটার মতো গলায় মাধবাচার্যের গম্ভীর গলাকে চাপা দিয়ে কে বলে উঠল, চুপ কর, আঃ চুপ কর।
চমকে আমি ও কার্তিকবাবু জ্যোতিষবাবুর দিকে তাকালাম। ক্যামেরার হাতল বন্ধ করে ক্রীড সাহেবও অবাক হয়ে চারদিকে চাইছেন। জ্যোতিষবাবু গর্জন করে উঠলেন, তোমরা অ্যাক্টিং থামিয়ে ক্যামেরার দিকে চাইলে কেন? বললাম, বাঃ, আমরা ভাবলাম অভিনয় ঠিক হচ্ছে না বলে আপনিই আমাদের থামতে বললেন?
–আমি তো কিছুই বলিনি! অবাক হয়ে বললেন জ্যোতিষবাবু। তবে বলল কে? সবাই পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। নিস্তব্ধ জঙ্গলে কারও মুখে কথা নেই।
জ্যোতিষবাবু বললেন, এমন শটটা মাটি হয়ে গেল। এখন আবার রিফ্রেক্টার সাজিয়ে শট নিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। কী যে করি! হঠাৎ ক্যামেরার পিছনে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন জ্যোতিষবাবু–এত ভিড় কেন? শুটিং-এর লোক ছাড়া এখানে কেউ থাকবে না। আপনারা দয়া করে বাইরে যান।
বাইরের অচেনা অনেকগুলি দর্শক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরার পিছনে। জ্যোতিষবাবুর কথায় নিতান্ত অনিচ্ছায় একে একে সরে পড়ল সবাই।
জ্যোতিষবাবু বললেন, ঠিক আছে। শটটা যেখানে বন্ধ হয়েছে সেইখানে কেটে মাধবাচার্যের বাকি দরকারি কথাগুলো টাইটেলে লিখে জুড়ে দেব। ভালই হল।
ক্যামেরা আরো কাছে আনা হল। বারো-তেরোখানা রিফ্লেক্টার আশেপাশে সাজিয়ে ক্রীড সাহেব প্রস্তুত হলেন।
জ্যোতিষবাবু বললেন, তাড়াতাড়ি এই শটগুলো সেরে নিতে হবে, নইলে এ জঙ্গলে বেশিক্ষণ রোদ্দুর পাওয়া যাবে না। তারপর সন্ধ্যের সময় আসল সিনটা নেওয়া হবে। তোমরা সংলাপগুলো ভাল করে মুখস্থ করে নাও, যেন আটকে না যায়।
কার্তিকবাবু ও আমি রীতিমতো তালিম নিতে শুরু করে দিলাম। জ্যোতিষবাবু মৃণালিনী বইটায় লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া সংলাপগুলো প্রম্পট করতে শুরু করলেন। আবার শুটিং আরম্ভ হল।
হেমচন্দ্রগুরুদেব, আপনি আশামাত্রের আশ্রয় লইতেছেন। আমিও তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমি কী করিব আজ্ঞা করুন।
মাধবাচার্য–আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ নগর মধ্যে তোমার আর অবস্থান করা অকর্তব্য। কেননা, যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সংকল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা, তুমি অদ্যই এ নগর ত্যাগ করিবে।
হেমচন্দ্র–কোথায় যাইব?
–চুলোয়!
আবার সেই কণ্ঠস্বর। আরো তীব্র, আরো ক্রুদ্ধ।শালারা জ্বালায়ে মারল, দুর হ! নইলে এক্কেরে মাইরা ফালামু।
উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে জ্যোতিষবাবুর দিকে চাইলাম। জ্যোতিষবাবুও দেখলাম বেশ হকচকিয়ে গেছেন। হাঁ করে চারদিকে চাইতে চাইতে বললেন, এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার! কে এইভাবে শুটিং ডিস্টার্ব করছে? বাইরের লোক যারা ছিল, সব সরিয়ে দিয়েছি। আমার ইউনিটের কারও সাহস হবে না। তবে? মাধবাচার্যরূপী কার্তিকবাবু হেঁড়ে গলায় বললেন, ভূত!
জঙ্গলের থমথমে নীরবতা মুহূর্তের জন্যে হালকা হাসিতে কেঁপে উঠল। জ্যোতিষবাবু বললেন, জঙ্গলটা একবার ভাল করে দেখতো মনে হয় ওর ভিতর লুকিয়ে থেকে কোনও দুষ্টু লোক এইসব করছে। দুতিন জন সেটিং-এর লোক জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে এল, কোথাও কেউ নেই। শুধু কয়েকটা শেয়াল ছুটে পালিয়ে গেল আর কতকগুলো ছোটবড় পাখি বৃক্ষান্তরে উড়ে গিয়ে বসল।
জ্যোতিষবাবু জঙ্গলের চারপাশে চার-পাঁচজনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আবার রিফ্লেক্টার ঠিক করে শুটিং আরম্ভ হল। ক্লোজ শটে মিড-শটে আমার আর কার্তিকবাবুর সিনগুলো ঘন্টাখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। আর কোনো রকম ডিস্টার্বেন্স হল না।
হেমচন্দ্রের কাছে মৃণালিনীর বিবাহ এবং পরে ব্যোমকেশের সব বৃত্তান্ত শুনে গুরুদেব খুশি হয়ে হেমচন্দ্রকে সস্ত্রীক মথুরায় গিয়ে বাস করবার নির্দেশ দিলেন। ঠিক হল মাধবাচার্য এখান থেকে সোজা কামরূপ চলে যাবেন এবং উপযুক্ত সময় এলে হেমচন্দ্রকে কামরূপাধিপতি দূত পাঠিয়ে আহ্বান করবেন। মৃগচর্ম, কমণ্ডলু প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিসগুলো নিয়ে মাধবাচার্য উঠে দাঁড়ালেন। হেমচন্দ্রও প্রণাম করে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, হঠাৎ মাধবাচার্য বললেন–দাঁড়াও!
সিনটা এইখানে কাট হল। জ্যোতিষবাবু বললেন–ব্রেক ফর লাঞ্চ। কাছে গিয়ে বললাম–সিনটা তো শেষ হল না বাঁড়ুয্যেমশাই, কাট বললেন কেন?
হেসে জবাব দিলেন জ্যোতিষবাবু, পরিচালক হও, তখন বুঝতে পারবে।
স্টুডিওর বাবুর্চি আহমেদ-এর রান্না খুব ভাল। সেদিন খেলাম মাংসের চাপাটি, মুগের ডাল, মুরগীর কারি জাতীয় একটা প্রিপারেশন। সরু সুগন্ধি চালের ভাত আর বড় একটা মর্তমান কলা। খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। বললাম, দুপুরের ভূতুড়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?
একটু ভেবে নিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, সত্যি কথা যদি শুনতে চাও, আমাদেরই মধ্যে কেউ কাছ থেকে ঐরকম আওয়াজ করেছে। ক্যামেরার আওয়াজ, তার উপর অতগুলো রিফ্লেক্টার। হঠাৎ অন্যদিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়–এ অবস্থায় ধরা না পড়ে একটু মজা করা খুব আর্ম নয়। আচ্ছা, কালকের মধ্যেই আমি রিয়েল কালপ্রিটকে বার করব।
খাওয়া-দাওয়ার পর প্রসঙ্গ বদলে গেল, বললাম, খালি তো আমাকে নিয়েই শুটিং চালাচ্ছেন। আপনার নায়িকা মৃণালিনীর তো দর্শন আজও পেলাম না।
বেশ একটুগম্ভীর হয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, পাবে,পাবে, ধৈর্য ধর। একদিন শুটিং করে চার পাঁচদিন বন্ধ দিচ্ছি কীসের জন্যে? শুধু মৃণালিনীকে তালিম দেওয়ার জন্যে। যেদিন শুটিং না থাকে, ডরিসকে হেড অফিসে এনে রীতিমতো ট্রেনিং দিচ্ছি। এরপর যখন বাজারে ছাড়ব, সবার তাক লেগে যাবে।
অবাক হয়ে বললাম, ডরিস! বাঙালি মেয়ে নয়?
মাথা নেড়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, ননা, কিন্তু এ মেয়ে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালি মেয়েকে লজ্জা দেবে–এ আমি ভবিষ্যদ্বাণী করলাম। আরও একটা বিশেষ কারণে হুট করে নামাচ্ছি না।
বললাম, কী কারণ?
আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আশেপাশে একবার দেখে নিয়ে চুপিচুপি বললেন জ্যোতিষবাবু, ভাংচি দেবে।
চুপ করে রইলাম। দ্বিগুণ উৎসাহে জ্যোতিষবাবু শুরু করলেন, মেয়েটির নাম মিস ডরিস স্মিথ। কিন্তু বাংলা ছবির নায়িকার ও নাম তো চলবে না, দাও না একটা প্রাণমাতানো বুককাঁপানো মিষ্টি বাংলা নাম।
ম্লান হেসে বললাম–মাফ করবেন স্যার, ফিরিঙ্গি মেয়েদের দেখলে আমার এমনিতেই বুক কেঁপে ওঠে। আপনিই যা হয় একটা নাম দিয়ে দিন না!
চিন্তিত মুখে আকাশের দিকে চেয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন জ্যোতিষবাবু। মনে হল নাম-সাগরে তলিয়ে গেছেন।
চুপচাপ বসে চারদিকে চাইছি, হঠাৎ দেখি, উত্তরদিকে একটা আমগাছের আড়াল থেকে বকের মতো গলাটা বাড়িয়ে হাসছে মনমোহন। আস্তে আস্তে উঠে এক-পা দু-পা করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা আঙুল মুখে দিয়ে আমাকে চুপ করতে বলে একরকম টেনেই নিল গাছটার আড়ালে। বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, কী মনমোহন, এতক্ষণ ছিলি কোথায়?
–এখানে।
–এখানে ছিলি, অথচ এতক্ষণ দেখতে পেলাম না, ব্যাপার কী?
এতক্ষণ বাদে শুরু হল মনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ হাসি। বলল, মেসোমশাই মানা করে দিয়েছে শুটিং-এ আসতে। আমি কিন্তু আগাগোড়া তোদের শুটিং দেখেছি।
অবাক হয়ে বললাম, কী করে?
হাত দিয়ে আমগাছটার উঁচু ডালটা দেখিয়ে মনমোহন বলল, ওখানে বসে। হারে, তোদের মাধবাচার্য কি পূর্ববঙ্গের ভাষায় সংলাপ বলছে?
–কেন বলতো?
–ডালে বসে পাতার আড়াল থেকে অতদুর স্পষ্ট দেখা না গেলেও মনে হল। মাধবাচার্য ভয়ানক রেগে গিয়ে তোক বাঙাল ভাষায় তড়পাচ্ছে।
রহস্যের মাঝখানে একটুখানি ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেলাম যেন।
বললাম, ছিঃ মনমোহন, কাজটা ভাল করিসনি, জ্যোতিষবাবু ভীষণ চটে গেছেন।
ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল মনমোহনের। বলল, কী বলতে চাইছিস তুই?
বললাম, আমি অবিশ্যি তোর নাম বলব না, কিন্তু উনি যদি কোনোরকমে জানতে পারেন–।
কথা কেড়ে নিয়ে মনমোহন বলল, কী জানতে পারেন, আমি গাছ থেকে লুকিয়ে শুটিং দেখেছি, এই কথা?
জবাব দেবার আগেই শুটিং-এর ডাক পড়ল। তাড়াতাড়ি জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। সূর্য গাছের আড়ালে ঢাকা। মাধবাচার্যের কুটিরের চারপাশে অন্ধকার হয়ে আসছে। মনে মনে ভাবলাম, এই আলোতে শুটিং হবে কী করে!
জ্যোতিষবাবু বললেন, একটু অন্ধকার না হলে এ সিনটা নেওয়া বৃথা হতো। সেই জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।
এরই মধ্যে দেখলাম, জ্যোতিষবাবুর সহকারী জয়নারায়ণ মাধবাচার্যের দাওয়ায় মাটির পিলসুজের উপরে রাখা একটি মাটির প্রদীপ তেল-সলতে দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। ব্যাপারটা ঠিক তখনও বুঝতে পারিনি। প্রদীপ জ্বালা হলে জ্যোতিষবাবু কার্তিকবাবু ও আমাকে ডেকে বললেন, সিনটা ভালো করে শুনে বুঝে নাও কী করতে হবে তোমাদের। আগের শটে তোমাকে দাঁড়াও বলেছেন মাধবাচার্য। এবার শট আরম্ভ হলেই তিনি দাওয়ার উপর থেকে মাটির প্রদীপটা হাতে করে নিয়ে সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে কুটিরের ঐ খড়ের চালায় আগুন লাগিয়ে দেবেন। তুমি ধীরাজ অবাক হয়ে বলবে, গুরুদেব, এ কী করছেন! তখন কার্তিকবাবু বলবেন–বস হেমচন্দ্র, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি বড়ই জটিল, পিছনে যবন সৈন্য আমাদের অনুসরণ করছে, এমতাবস্থায় কোনও চিহ্ন রেখে যাওয়া মৃতার পরিচায়ক–তাই এ স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে কুটির ভস্মীভূত করে যাচ্ছি। তারপর তোমরা যখন দেখবে যে, আগুন বেশ জ্বলে উঠেছে তখন আস্তে আস্তে ক্যামেরার ডান পাশ দিয়ে সিন থেকে আউট হয়ে যাবে। বুঝেছ?
দুজনে উৎসাহভরে মাথা নাড়লাম।
জঙ্গলের উপর একটু একটু করে পাতলা অন্ধকার নেমে আসছে। জ্যোতিষবাবুর নির্দেশমতো কুটিরে আগুন লাগিয়ে আমরা সরে এলাম। শুকনো বশ-খড়-দরমা দেখতে দেখতে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। সমস্ত জঙ্গলের উপর কে যেন ধামা ধামা আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। তন্ময় হয়ে ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ গগনভেদী চিৎকার, বাঁচাও, পুইড়্যা মল্লাম, আমারে বাঁচাও।
কণ্ঠস্বর পরিচিত। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এবার বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আওয়াজ আসছে মাধবাচার্যের জ্বলন্ত কুটিরের ভেতর থেকে। বোধহয় কয়েক সেকেন্ড। তারপরেই চার-পাঁচজন সেটিং-এর লোক ছুটে গিয়ে অনেক কষ্টে ঢুকে পড়ল ঐ জ্বলন্ত কুটিরে। এদিকে চিৎকারের কামাই নেই–বাঁচাও, আমারে বাঁচাও! আজও মনে হলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।
ক্যামেরা থামিয়ে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বললাম-তোমরা বেরিয়ে এসস, এক্ষুনি ঘর পড়ে যাবে। শুধু ফটাস ফটাস করে বাঁশের গিয়েগুলো ফাটার শব্দ। একটু পরেই একটা লোককে চ্যাংদোলা করে ধরে বেরিয়ে এল সেটিং-এর লোকগুলো। একরকম সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপ করে জ্বলন্ত কুটিরের চালখানা পড়ে গেল।
বাইরে এনে আধমরা লোকটাকে ওরা ঘাসের উপর শুইয়ে দিল। কুটিরের আগুনে মুখ দেখে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, মধুসূদন!
মধুসূদন ধাড়ার বাড়ি পূর্ববঙ্গে, বছরতিনেক আগে চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় এসে কী করে সেটিং-মাস্টার দীনশা ইরানীর নজরে পড়ে যায়। সেই থেকে সেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। আগের দিন মাইনে পেয়েছে, আজ কী কারণে যেন সেটিং ডিপার্টমেন্ট বন্ধ। সকাল থেকে স্টুডিও-সংলগ্ন বিখ্যাত তাড়ির দোকানে বসে আকণ্ঠ তাড়ি খেয়ে বেলা দশটার মধ্যেই প্রায় বেহুঁশ হয়ে নির্জনে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে মাধবাচার্যের কুটিরে ঢুকে খড় লতাপাতা জড়ো করে তার উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দুর্ঘটনা না বললেও চলে।
ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখলাম, দুতিন জায়গায় ফোস্কা পড়ে গেছে। বেশ কয়েকদিন ভুগবে, প্রাণে মরবে না।
রাগে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে জ্যোতিষবাবু বললেন, ব্যাটা পুড়ে মরলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম।
এরকম নিষ্ঠুর কথা জ্যোতিষবাবুর মুখে এর আগে কখনও শুনিনি। অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলাম। আমার দিকে চেয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, কথাটা কেন বললাম বুঝতে পারলে না? ব্যাটা মরলে খবরটা সাহেবদের কানে যেত। তাহলে যত অশান্তির মূল ঐ তাড়ির দোকানটা তুলে দেবার একটা ছুতো অন্তত খুঁজে পেতাম।
.
দেড় মাস পরের কথা। মৃণালিনী ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এর মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটেনি। আর ঘটে থাকলেও সেদিকে দৃষ্টি দেবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। তবে স্টুডিওতে একটা বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার ভাব যেন লক্ষ্য করলাম। গেট দিয়ে ঢুকেই যেখানে সামনের বড় আমগাছটা কেটে ফেলা হয়েছে, সেখানে গাড়ি গাড়ি ইট চুন সুরকি সিমেন্ট গাদা করে রাখা হয়েছে। শুনলাম, ওখানে একটা বড় ফ্লোর তৈরি হবে টকি ছবি তোলার জন্য। ফ্রামজী এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিয়ে আমেরিকার আর.সি.এ. কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে এসেছেন। মাসখানেকের মধ্যেই টকি-মেশিন ও দুতিনজন বিশেষজ্ঞ এসে যাবে, তার আগেই ফ্লোর কমপ্লিট করা চাই-ই চাই। রাত-দিন মিস্ত্রি খাটতে লাগল।
মন ভাল নেই। বাবার শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে। পনেরো দিন বিশ্রাম নিয়ে বেশ একটু সুস্থ হয়েই আবার স্কুল, টিউশনি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাতে লুকিয়ে আই.এ-র পড়া শুরু করে দেন। ফলে দিন সাতেক বাদেই আবার বুকের ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। স্কুলে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, এবার ছুটি নিলে বিনা বেতনেই নিতে হবে, কেননা পাওনা ছুটি আর নেই। দ্বিতীয় উপায়, ওঁর জায়গায় আর একটি মাস্টার সাময়িকভাবে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার মাইনে বাবার মাইনের থেকে কেটে দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে, তাই দেওয়া হবে। স্কুলে বাবা মাইনে পেতেন মাত্র সত্তর টাকা। তা থেকে টেম্পোরারি মাস্টারকে অন্তত চল্লিশ টাকা দিলে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ত্রিশ টাকা। মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম। বললাম, স্যার আমি ম্যাট্রিক পাশ, বাবা যতদিন ভাল রকম সুস্থ না হন, ততদিন যদি পড়াতে অনুমতি করেন, তাহলে সবদিক রক্ষা হয়। হেডমাস্টার সতীশচন্দ্র বোস একটু গুম হয়ে কী ভেবে নিলেন, তারপর হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, ভেরি গুড আইডিয়া।
তাই ঠিক হল। সকালে নিচু ক্লাসের ছেলে দুটোকে পড়িয়ে এসে দুপুরে স্কুল মাস্টারি করতে শুরু করে দিলাম। উঁচু ক্লাসের ছেলে দুটি বাবার অসুখের কথা শুনে বাড়িতে এসে বাবার কাছে পড়ে যেতে সানন্দে রাজি হয়ে গেল।
গোল বাধলো স্টুডিও নিয়ে। জ্যোতিষবাবুকে সব খুলে বললাম। সব শুনে বললেন, সে জন্য তুমি ভাবছ কেন? মৃণালিনীতে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। বক্তিয়ার খিলজির সসৈন্যে অশ্বপৃষ্ঠে কতগুলো পাসিং শট নিতে বাইরে যাব। তুমি সঙ্গে থাকলে ভালই হতো। কিন্তু এ অবস্থায় তোমার যাওয়া কোনমতেই চলতে পারে না। বাড়ি গিয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও, আর প্রতি মাসের তিন তারিখে হেড অফিসে এসে মাইনে নিয়ে যেও। তাছাড়া টকি আসছে, কর্তাদের এখন মাথা খারাপ। হৈচৈ করেই তো ছমাস কাটবে।
নিশ্চিন্ত মনে মিত্র স্কুলে মাস্টারি শুরু করলাম। আমাকে বেশির ভাগ নিচু ক্লাসেই পড়াতে হতো। কখনও কখনও উঁচু ক্লাসে পড়াতাম। পড়াতাম বললে ভুল হবে, গল্প বলতাম। ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলের দল হৈহৈ করে উঠত, গল্প বলুন স্যার, গল্প!
সত্যি কথা বলতে কি পড়াবার আমি জানিই বা কী? ক্লাসে ঢুকবার আগেই বুকের ভেতরটা কাঁপত। যদি ভুল হয়, অথবা কোনও কথার ভুল মানে বলে ফেলি, আর ছেলেরা ধরে ফেলে? তাই গল্প বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে মৌখিক দুএকবার আপত্তি করলেও মনে মনে খুশিই হতাম। এখানে উল্লেখযোগ্য, অধুনা ফিল্মের বিখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায় এবং কঙ্কাল, দুজনায় প্রভৃতি বহু নাম করা ছবির অন্যতম প্রযোজক গোবিন্দ রায় আমার ছাত্র। স্কুলে আমার কাছে পড়েছেন বা গল্প শুনেছেন।
একটা বিচিত্র জগৎ, বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা। বেশ লাগত। কোনো ছেলে হয়তো। শ্লেটে বদর এঁকে নিচে লিখেছে অজয় নন্দী। রাগে কাঁপতে কাঁপতে অজয় নন্দী টেসমেত আসামিকে নিয়ে একেবারে আমার কাছে হাজির। অন্য সময় হলে হেসে ফেলতাম। কিন্তু মনে পড়ে গেল, আমি এখন বিচারক মাস্টার। বেশ খানিকটা ধমকে দিলাম অপরাধীকে, খুশি হয়ে অজয় নন্দী সিটে বসল। এরকম খুঁটিনাটি ব্যাপার অসংখ্য।
হয়তো কোনো ক্লাসে অনেক কষ্টে গল্প না বলে ডিকটেশন দিতে শুরু করেছি। মাঝপথে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার!
বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলি, কী?
একটু ইতস্তত করে ছেলেটি বলে, হনুমানের বাপের নাম জাম্বুবান নয় স্যার?
আশ্চর্য হয়ে বলি, কে বলেছে তোমায়?
চুপ করে থাকে ছেলেটি। রাগ হয়, বলি, কাল তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে এসো। তিনি কী বলেন শুনে তারপর বলব। এখন ডিসটার্ব কোরো না, কাজ কর।
তবু দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটি। বলি, কী হল?
আমতা আমতা করে ছেলেটি বলে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাকে।
অসহিষ্ণু হয়ে বলি, কী বললেন তিনি?
লজ্জায় লাল হয়ে সহপাঠীদের দিকে চাইতে থাকে ছেলেটি। এবার বেশ একটু ধমকে উঠি, কী বলেছেন তোমার বাবা?
–বাবা বললেন, আমিই নাকি একটা জাম্বুবান।
হাসির রোল উঠল ক্লাসে। ম্যানেজ করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আর ডিকটেশন দিতে পারলাম না।
আর একদিন একটু উঁচু ক্লাসে বাংলা পড়াবার ভার পড়ল আমার। মনে মনে ঠিক করলাম আজ আর কিছুতেই গল্প বলব না। সব ক্লাসেই যদি না পড়িয়ে গল্প বলে কাটিয়ে দিই, হেডমাস্টারমশাই তাহলে ভাববেন কী! চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যে মুখখানা যথাসাধ্য গোমড়া করে ঢুকলাম ক্লাসে। হৈচৈ করে উঠল ছেলের দল, গল্প বলুন স্যার, রবার্ট ব্লেকের গল্প।
হাত তুলে ওদের চুপ করতে বলে গম্ভীরভাবে বললাম, রোজ রোজ পড়ার আওয়ারে গল্প বলা ঠিক নয়। হেডমাস্টারমশাই ওতে রাগ করেন–
বাধা দিয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ছেলের দল, মোটই নয়। এইতো খানিক আগে আমরা হেডস্যারের কাছে গিয়ে বললাম। তিনি তো হেসেই মত দিলেন। ক্লাসসুদ্ধ ছেলের কাছে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। পড়ানো আর হল না, হল রবার্ট ব্লেকের গল্প।
মাসের তিন তারিখে হেড অফিসে গিয়ে খাতায় সই করে মাইনে নিয়ে আসি, আর বাকি উনত্রিশ দিন স্টুডিওর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, স্কুল মাস্টারি আর টিউশনি করে কাটিয়ে দিই। একদিন নরেশদার সঙ্গে দেখা। তিনিও মাইনে নিতে এসেছেন। সব খুলে বললাম নরেশদাকে। একটু চিন্তা করে বললেন, তাইতো, খুবই ভাবনার কথা। এভাবে তো বেশিদিন চলবে না। দুদিন বাদে যখন টকি ছবির শুটিং আরম্ভ হবে, তখন ছুটি একদম পাবে না। তাছাড়া জাহাঙ্গীর সাহেব এখন হত্তাকত্তা। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ছবিটা টকিতে তুলতে।
সাগ্রহে বললাম–আপনিই পরিচালনা করবেন তো নরেশদা?
শ্লাঘার হাসি হেসে নরেশদা বললেন, দেখ, শেষ পর্যন্ত কী হয়!
এখানে জাহাঙ্গীরজী ম্যাডানের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। রুস্তমজী সাহেব স্বর্গত জে. এফ. ম্যাডানের জামাতা, তিনিই সর্বেসর্বা। ম্যাডানের বড় ছেলে বজ্জরজী মদের দোকান ও শো-হাউসগুলো দেখাশোনা করতেন। সেজ ফ্রামজীর উপর ভার ছিল ফিল্ম প্রোডাকসনের তত্ত্বাবধান করা। তৃতীয় পুত্র হলেন জাহাঙ্গীর সাহেব, ফোপরদালালের মতো সব ডিপার্টমেন্টে ঘুরে বেড়াতেন। ফ্রামজী আমেরিকা চলে গেলে ওঁর উপর স্টুডিও দেখাশোনার ভার পড়ে। মিষ্টভাষী, অমায়িক, নিরহংকার জাহাঙ্গীর সবার প্রিয় ছিলেন। আর দুটি ছেলে স্কুলে বা কলেজে পড়ত। স্টুডিওর সংস্রবে তাদের আসতে দেওয়া রুস্তমজীর নিষেধ ছিল।
মাইনে নিয়ে আসবার সময় সিঁড়িতে জাহাঙ্গীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নরেশদা আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার মাইনের কথাটাও সাহেবকে শুনিয়ে দিলেন নরেশদা। বললেন–সত্যি ওর উপর অবিচার করা হয়েছে। সব শুনে হাসিমুখে আমার কাঁধে হাত রেখে জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি, এটা মিঃ গাঙ্গুলীজ ডুইং। হাউএভার, স্টুডিওয় আমার সঙ্গে দেখা কোরো তুমি।
রাস্তায় নেমে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত এসে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। নরেশদা বললেন, তুমি বোধহয় শোননি ধীরাজ, আমরা একটা ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার পার্টি করেছি। কলকাতার কাছাকাছি সব জায়গায় শশা দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দলে আছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, রবি রায়, ভূমেন রায়। মেয়েদের মধ্যে মিস লাইট, চারুবালা, পদ্মাদেবী প্রভৃতি আরও অনেক মেয়ে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল যতদিন না নিজস্ব হাউস কলকাতায় হয়, ততদিন বাইরে বাইরে শশা করে বেড়ান। আর একটি কথা। এখন কাউকে বোলো না। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর বড়তলা থানার পশ্চিম গা ঘেঁষে যে জমিটা, ওটা লিজ নিয়ে ওখানে আমাদের হাউস তৈরি হবে, নাম হবে রঙমহল,কেমন নাম?
বললাম, চমৎকার!
–তা, তোমার বাবার যদি মত হয় তাহলে আমাদের দলে তোমাকে নিতে পারি। বাড়তি আয় হিসেবে কথাটা ভেবে দেখো।
কালীঘাটের ট্রাম এসে গেল, দুজনে উঠে পড়লাম।
সেইদিন রাত্রেই কথাটা বাবার কাছে পাড়লাম। শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইলেন বাবা। তারপর বললেন, না ধীউবাবা, থিয়েটারে তোমার চুকে কাজ নেই। সিনেমা করছ ঐ কর। তাছাড়া ঐ সব সংসর্গে রাতবিরেতে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো–না না, দরকার নেই।
বাবার একান্ত অনিচ্ছা আমি থিয়েটারে যোগদান করি। চুপ করে গেলাম। এরই মধ্যে একদিন রবিবারে রিনির দল এসে হাজির, মানে রিনির বাবা মা ভাইবোনরা, বাবার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছে। একটু নিরিবিলি হতেই রিনি বলল
তুমি আর যাও না কেন ছোড়দা?
হেসে বললাম, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা না করে, চাঁদের দুরত্ব মনে রেখে দূরে থাকাই ভাল নয় কি?
–তোমাদের ওসব হেঁয়ালির কথা বুঝি না, গোপাদি কিন্তু সত্যি তোমাকে ভালবাসে।
তাড়াতাড়ি রিনির মুখে চাপা দিয়ে বলি, ভুলেও আর কোনও দিন ঐ সর্বনেশে কথা উচ্চারণ করিস না রিনি। সত্যিই যদি ছোড়দার ভাল চাস আমার এ অনুরোধটা রাখিস বোন। তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে সেদিনকার দৈনিক কাগজটা পড়বার ভান করি, ব্যথাভরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে রিনি।
পরদিন সকাল থেকে আবার চলল সেই রুটিনবন্দী কাজ। টিউশনি, স্কুল, বাবার অসুখের রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি। দিনপনেরো এইভাবে কাটল। বাবার জ্বর ও বুকের সর্দি একটুও কমল না, বরং খারাপের দিকেই গেল। আগে জ্বর রেমিশন হয়ে আবার আসত। কদিন থেকে দেখলাম রেমিশন হয় না। নামে একশ, কোনও দিন নিরানব্বই পয়েন্ট চার, আবার তার উপরই জ্বর আসে একশো তিন-চার পর্যন্ত।
ডাক্তার নগেন দাসকে একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলাম, কী রকম বুঝছেন ডাক্তারবাবু?
-জ্বরটা রেমিটেন্ট টাইপের মনে হচ্ছে। বুকের সর্দিটা কমে গেলে জ্বরটাও বন্ধ হয়ে যাবে। দেখি, চেষ্টার তো কসুর করছি না।
বুকের একটা মালিশ দিলেন ডাক্তারবাবু আর জ্বরের এক শিশি মিকশ্চার। কী একটা পর্বোপলক্ষে স্কুল দুদিন বন্ধ, দুপুরে খেয়েদেয়ে স্টুডিওতে গেলাম। বোধহয় দিনপনেরো আসিনি। এর মধ্যেই চেহারা পালটে গেছে স্টুডিওর। ঢুকেই বাঁ হাতে প্রকাণ্ড ফ্লোর। সামনে লাল সুরকি আর খোয়া দিয়ে পেটা পথ। পূর্বদিকের জঙ্গলটাও প্রায় পরিষ্কার। সবাই ব্যস্ত কাজে। জ্যোতিষবাবু সদলে বাইরে গেছেন ছবি তুলতে, এখনও ফেরেননি। গাঙ্গুলীমশাই ও মুখুজ্যে দেবীচৌধুরাণীর এডিটিং নিয়ে ব্যস্ত। উদ্দেশ্যহীনের মতো খানিক ঘুরে বেরিয়ে বাড়ি চলে আসব কিনা ভাবছি, দেখি একখানা মোটর থেকে জাহাঙ্গীর সাহেব ও নরেশদা নামছেন। নমস্কার করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নরেশদা বললেন, কথা আছে ধীরাজ, এখুনি চলে যেও না যেন।
জাহাঙ্গীর সাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত স্টুডিওটা দেখতে লাগলেন নরেশদা। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে সাহেব গাড়ি করে চলে গেলেন।
কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন নরেশদা, তারপর, তোমার বাবার শরীর কেমন আছে?
সব বললাম। শুনে নরেশদা বললেন, আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না। জ্বরটা কেমন বাঁকা লাগছে। তুমি অন্য ডাক্তার দেখাও।
বললাম, বাবা রাজি হচ্ছেন না। ওঁর ধারণা ডাক্তার দাসই ওঁকে ভাল করে দেবেন। একথা সেকথার পর নরেশদা বললেন, একটা মন্দের ভাল খবর তোমায় দিয়ে রাখি শোনন। জাহাঙ্গীর সাহেব তোমার কুড়ি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার পরিচালিত নৌকাডুবি ছবির শুরু থেকে ঐ বাড়তি মাইনে পাবে।
জিজ্ঞাসা করলাম, কবে থেকে শুরু হবে নরেশদা?
একটু ভেবে নিয়ে নরেশদা বললেন, দেখি, তবে তাড়াহুড়ো করে এ ছবি আমি করব না। এটা খাস জাহাঙ্গীর সাহেবের ছবি। তার উপর টকি মেশিন এলে এইটাই হবে প্রথম বাংলা সবাক ছবি।
মনে মনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললাম, আমায় কী পার্ট দেবেন নরেশদা?
নরেশদা বললেন, সাহেব বলছেন নায়ক রমেশের পার্ট তোমায় দিতে। আমার ইচ্ছে নলিনাক্ষের পার্টটা তুমি কর।
চোখের সামনে নৌকাডুবি উপন্যাসের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলো ভেসে উঠল। নরেশদার হাত দুটো ধরে বললাম, না নরেশদা, নলিনাক্ষ অথরস ব্যাকিং পার্ট, খুব সুখ্যাতি পাওয়া যাবে। কিন্তু রমেশের ভূমিকা মনস্তত্ত্বে জটিল হলেও, লোভনীয়। আমি রমেশ করব।
একটু চিন্তা করে নরেশদা বললেন, তা যেন হল। কিন্তু এতো নির্বাক ছবি নয়, সবাক। রীতিমতো রিহার্সাল দরকার। তুমি তো আবার মাস্টারি শুরু করে দিয়েছ। রিহার্সাল দেবে কী করে?
মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম। একদিকে অত বড় চান্স, অন্য দিকে কর্তব্য। কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখি?
নরেশদাই সমাধান করে দিলেন। বললেন, তোমার স্কুল তো চারটেয় ছুটি হয়? মাথা নেড়ে সায় দিলাম।
-তাহলে একটা কাজ আমি করতে পারি। দুপুর দুটো থেকে মেয়েদের নিয়ে রিহার্সাল শুরু করে দেব। চারটের পর তুমি এলে পুরো রিহার্সাল চলবে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।
বাড়ি চলে এলাম। বাবার জ্বর অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। নিরানব্বইয়ে নেমে উঠেছে এক শ পয়েন্ট চার। বুকের মালিশটাতেও কিছু কাজ হয়েছে মনে হল। সর্দিটা সহজভাবেই উঠে যাচ্ছে। বালিশে ঠেসান দিয়ে সেদিনকার দৈনিক কাগজটা পড়ছিলেন বাবা। কাছে এসে নরেশদার কথাগুলো সব বললাম। শুনে একটু চিন্তা করে বললেন, ভাল কথা। তবে মুখের কথায় খুব বেশি আশান্বিত হয় না, দুঃখটা কম পাবে।
রাত্রে খেয়েদেয়ে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।
পরদিন সকালে টিউশনি থেকে ফিরতেই সাড়ে নটা হয়ে গেল। বাড়ির দরজার কাছে পিওনের সঙ্গে দেখা। আমার নামে খামে একখানা চিঠি।
অপরিচিত হাতের লেখা। বেশ একটু অবাক হয়ে গেলাম। ইতস্তত করে খুলে ফেললাম। লেখা–
ধীরাজবাবু, আগামী বুধবার অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। বিশেষ দরকার। আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তরদিকের রাস্তায় গাড়িতে আপনার জন্য সন্ধ্যে ছটা হইতে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। আমাদের গাড়ির নম্বর ৫৬৭৮০, ওল্ড মডেল মিনার্ভা।
–গোপা
সন্দেহ সংশয় ভয়, অন্যদিকে আশা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহল। এই সব কটি অনুভূতি যখন একসঙ্গে জোট বেঁধে মনটাকে তোলপাড় করে ফেলে, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যুক্তিহীন বেপরোয়া যৌবনের অদম্য কৌতূহলই অন্য সবাইকে দাবিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। আমারও ঠিক তাই হল। আগের দিন রাত্রে সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম যুক্তি তর্ক দিয়েও মনকে বোঝাতে পারলাম না যে, গোপার সঙ্গে দেখা না করাটাই হবে আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ভাবলাম, দেখাই যাক না কী বলতে চায় গোপা। আমার দিক থেকে এমন কোনও অপরাধ করিনি, যার জন্য কাপুরুষের মতো লুকিয়ে থাকতে হবে।
ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে যখন পৌঁছলাম, তখন ছটা বেজে গেছে। শীতের সন্ধ্যা। মনে হল বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। চারদিকে আলোর মালায় ঘেরা অগণিত স্বাস্থ্যান্বেষী স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুর কলকপ্টমুখর প্রস্তরসৌধ যেন কিছুক্ষণের জন্য সজীব হয়ে উঠেছে। উত্তর দিকের ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড় করানো গাড়িগুলোর নম্বর প্লেটের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে পুব থেকে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। বেশ কিছুদূর এগিয়েও গোপাদের গাড়ির নম্বর দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, তবে কি সমস্ত ব্যাপারটা ডুয়ো ধাপ্পাবাজি? আমাকে বোকা বানিয়ে নিছক খানিকটা কৌতুক করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য? কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে এভাবে কৌতুক করতে পারে এমন কোনো লোককে আমার স্মরণ-গন্ডির মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পেলাম না। আবার এগোতে লাগলাম। ফুটপাথ প্রায় শেষ। হয়ে এল, হঠাৎ দেখি দশ-বারো হাত দূরে অপেক্ষাকৃত নির্জন ও অন্ধকার জায়গায় বিরাট কালো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে একখানা গাড়ি, পিছনে টকটকে রেড লাইটের ঠিক নিচেই রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে গোপার দেওয়া নম্বর–৫৬৭৮০। বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। ভাবলাম, চলেই যাই। এ সাক্ষাতের পরিণাম কোনও দিক দিয়েই যে শুভ হবে না, তা জেনেও কেন–।
লোভী যৌবন গর্জন করে উঠল–কাপুরুষ! জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার বাসনা আছে, সাহস নেই? এ-রকম ভীরু মন নিয়ে আর কোনো দিন বাইরে বেরিও না। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থেকো!
যা হবার হবে। এক পা-দুপা করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম গাড়িটার পাশে। গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। আবছা আলোয় মনে হল কোনো মহিলা বসে আছেন। কী করব না করব ভাবছি, এমন সময় ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে এল পুরু খাকি প্যান্ট ও গলাবন্ধ কোট পরা ড্রাইভার। বুকের ডানপাশে হিজিবিজি মনোগ্রাম, দেখে অনুমানে বুঝলাম, রায়বাহাদুরের নাম। ড্রাইভার দরজা খুলে পাশে দাঁড়াল, বুঝলাম গাড়িতে উঠতে বলছে। দুরুদুরু বক্ষে উঠে বসলাম। ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে আদেশের অপেক্ষায় বসল। আমার সিটের অন্য ধার থেকে বেশ গুরুগম্ভীর গলায় আদেশ হল, চালাও।
একটু সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে গাড়ি মন্থরগতিতে চলল রেড রোড ধরে। কিছুদূর গিয়ে একটি শাখাবহুল গাছের তলায় আসতেই আবার শুনলাম, থামাও।
গাড়ি থেমে গেল। আদেশ হল, রঘুনন্দন, কাছাকাছি থেকো। ডাকলেই যেন পাই।
মাথার গোল টুপিটায় ডান হাত ছুঁইয়ে রঘুনন্দন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।
এমনিতেই রেড রোড জনবিরল। ক্কচিৎ কখনো দুএকখানা গাড়ি আসে যায়। রাস্তা নিঝুম, গাড়ির ভিতরটাও তাই। রুক্ষ গম্ভীর কণ্ঠ নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিল, বুঝতে পেরেছ বোধহয় আমি গোপা নই, গোপার মা?
অনুমানে আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। চুপ করেই রইলাম।
–চিঠিটা অবিশ্যি লিখেছিল গোপাই, আসবার কথাও ছিল তার, কিন্তু ধন্মের কল বাতাসে নড়ে, তাই হরিমতী ব্যাপারটা আগেই আমার কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।
একটু চুপ করে আবার প্রশ্ন:
–তুমি আজকাল খিদিরপুরে যাও না কেন?
–এমনি, সময় পাই না বলে।
–সময় পাও না, না মারের ভয়ে?
–মারের ভয়ে!
-–হ্যাঁ, এবার খিদিরপুরে গেলে হাত-পা নিয়ে আস্ত ফিরে আসতে পারবে না।
অবাক হয়ে তাকালাম। অন্ধকারে গোপার মায়ের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম না, শুধু ক্রুদ্ধ চোখের মতো নথের হীরে দুটো রাস্তার ম্লান আলোতেও জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল।
শান্ত কণ্ঠে বললাম, কী উদ্দেশ্যে এত বড় ছলনার আশ্রয় নিয়ে আজ আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জানি না, জানবার কৌতূহলও নেই। শুধু আমাকে মারধোর করলেই যদি আপনার আক্রোশ খানিকটা নিবৃত্ত হয়, তাহলে ড্রাইভার রঘুনন্দনকে ডাকুন। আমাকে মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাক। বাধা দেব না, আর দিয়ে কোন লাভও হবে না।
চুপ করে রইলেন গোপার মা। চলমান একটা গাড়ির হেডলাইট ভিতরের অন্ধকার কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঘুচিয়ে দিল। গোপার মাকে দেখলাম। প্রকাণ্ড গোল মুখ। মিশমিশে না হলেও বেশ কালো রং। নাকে প্রকাণ্ড গোল নথ, তাতে নানা রঙের দামী পাথর বসানো। বেশ রাশভারি চেহারা, দেখলে ভয় হয়।
গোপার মা-ই শুরু করলেন, মাকাল ফলের মতো কটা রং আর একরাশ বিশ্রী বাবরি চুল নিয়ে যদি মনে করে থাকো মেয়েরা তোমায় দেখলেই পাগল হয়ে যাবে, তাহলে মস্ত ভুল করেছ।
জবাব দেবার প্রশ্ন নয়। চুপ করেই রইলাম।
গোপার মা বলে চললেন, পইপই করে কত্তাকে বলেছিলাম মেয়েছেলেকে অত লেখাপড়া শিখিও না। ভাল ঘর দেখে একটা নৈকুষ্য কুলিনের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। শুনলেন না আমার কথা। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝুন।
কথাগুলো বলেই বোধহয় বুঝতে পারলেন যে, এই সব পারিবারিক আলোচনা একজন বাইরের লোকের সামনে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখনই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।
–রিনির বাবা তোমার আপন কাকা?
–না, বাবার মামাতো ভাই।
–হুঁ, তাই বল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। এবার যেন নিজের মনেই বলতে শুরু করলেন গোপার মা।–ঐ একফোঁটা মেয়ে দেখতে, কিন্তু এদিকে বিষ-পুঁটুলি, ঐ তো যত নষ্টের মূল।
এই সব অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ত কথাগুলোর শেষ পরিণতি কোথায় জানবার জন্য একটু অসহিষ্ণু হয়েই বললাম, কী জন্যে আমাকে ডেকেছেন দয়া করে বলবেন কি?
গর্জন করে উঠলেন গোপার মা, নিশ্চয় বলব, নইলে কি তোমার সঙ্গে হাওয়া খেতে ঘর-সংসার ফেলে লজ্জাশরম ছেড়ে এতদূর ছুটে এসেছি? গোপাকে বিয়ে করার আশা তুমি ছেড়ে দাও, অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না।
বললাম, দিলাম।
এত সহজ স্পষ্ট উত্তর আশা করেননি গোপার মা। একটু অবাক হয়ে তক্ষুনি আবার জ্বলে উঠলেন, তোমার কথায় বিশ্বাস কী? যারা বায়োস্কোপ করে বেড়ায়, তাদের কথার দাম আছে নাকি? এর আগে কখানা চিঠি দিয়েছে গোপা?
–একখানাও না।
–কী জন্যে তাহলে চিঠি লিখে এখানে দেখা করতে চেয়েছিল সে?
–জানি না।
–জানো, বলবে না। আর একটা কথা। দুপুরবেলা নিরিবিলি কাকার বাড়িতে গিয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা আর কোনো দিনও কোরো না। তোমার কাকা সব কথা শুনে ভীষণ রেগে গেছেন আর সেই খুদে মেয়েটাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন। দুদিন খাওয়া বন্ধ।
অন্ধকারে শিউরে উঠলাম। রিনি, আমার পার্ল হোয়াইট। কাকা এত বড় অমানুষ যে, ঐ ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটাকে–। চোখে জল এসে গেল। কিন্তু করবার কিছু নেই, শুধু নিজের মনে গুমরে মরা ছাড়া।
অনুমানে আমার অবস্থা কল্পনা করেই যেন খুশি হয়ে গোপার মা বললেন, চমৎকার মানুষ তোমার কাকা। তিনি তো স্পষ্টই বললেন, ওদের সাথে সম্পর্ক আছে, এটা স্বীকার করতেও লজ্জা হয়। তোমার বাবাই বা কী রকম–
বাধা দিয়ে বললাম, আমার বাবাকে এর মধ্যে টানবেন না। আপনার অনুযোগ আমার বিরুদ্ধে। আমায় যা খুশি বলুন।
অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারলাম আমার দিকে চেয়ে আছেন গোপার মা। এতক্ষণ বাদে বাইরে চাইলাম। এরই মধ্যে ঘন কুয়াশার আস্তরণ নেমে এসেছে গড়ের মাঠে। চারপাশে আলোগুলো কেমন নিস্তেজ, মিটমিট করছে জোনাকির মতো। কিছু দূরে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ অস্পষ্ট স্বপ্নপুরীর মতো দেখাচ্ছে। ঘড়ি না দেখেও বুঝলাম, রাত বেশ হয়েছে। সহজভাবেই বললাম, আপনার কথা আশা করি শেষ হয়েছে। এবার আমি যাচ্ছি। রাত হয়ে যাচ্ছে।
গাড়ির ভিতরকার হ্যাঁন্ডেলটা ঘুরিয়ে দরজা খুলতে যাব, এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গোপার মা, অনেক কটু অপ্রিয় কথা বলেছি তোমায় বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো।কছু মনে করো না, গোপা আমাদের একমাত্র মেয়ে। আমাদের মান-সম্ভ্রম সাধ-আহ্লাদ সবই নির্ভর করছে ওর উপর। তুমিই বলতো বাবা, আজ যদি তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে হয়, তাহলে সমাজে, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে?
এতক্ষণ শুধু দাম্ভিকা রায়বাহাদুর গৃহিণীর কথাই শুনছিলাম। এবার কথা কইলেন গোপার মা। অভিভূত হয়ে গেলাম।
গোপার মা বললেন, বাপের অসম্ভব আদুরে ও অভিমানী মেয়ে গোপা। আমার শুধু ভয় হয় কখন কী করে বসে। গরীব হলেও আপত্তি হত না, শুধু যদি তুমি বায়োস্কোপ না করতে আর আমাদের পাল্টা ঘর হতে।
চুপ করে রইলাম। আঁচলে চোখের জল মুছে গোপার মা বললেন, কখনও কোনো পরপুরুষের সামনে বার হইনি বা কথা কইনি। আজ শুধু মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। একটা কথা আমাকে দিয়ে যাও বাবা।
বললাম, কী!
–গোপার জীবন থেকে তুমি সরে দাঁড়াও।
একবার ভাবলাম বলি, সিনেমার লোকের কথার দাম কী! কিন্তু আর আঘাত দিতে প্রবৃত্তি হল না।
বললাম, আমার দিক থেকে আমি রাখব আপনার কথা, কেননা ভেবে দেখেছি কোনও দিক দিয়েই এ মিলন শুভ হতে পারে না। না আমার দিক থেকে, না গোপার। কিন্তু আপনার মেয়ে যদি না শোনে আপনাদের কথা?
মিনিটখানেক উদ্দেশ্যহীনভাবে বাইরে চেয়ে কী যেন ভাবলেন গোপার মা, তারপর বললেন, সে ভার আমাদের। তার জন্যে যদি–যাক অনেক রাত্রি হয়ে গেল বাবা, চল, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই। কোথায় থাক তুমি?
–ভবানীপুরে, হরিশ পার্কের কাছে নামিয়ে দিলেই হবে।
গোপার মা ডাকলেন, রঘুনন্দন।
আলাদিনের দৈত্যের মতো অন্ধকার কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়াল বিরাটকায় রঘুনন্দন।
–চল, বাবুকে নামাতে হবে হরিশ পার্কের কাছে।
মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কথাটা শোনাই ছিল, ওর সত্যিকারের অর্থটা জানা ছিল না। আজ সেটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। হিসাবের খাতায় জমার ঘরে শুন্য আগেই দিয়ে রেখেছিলাম। তারই পাশে গোপার মা আরও কয়েকটি শূন্য যোগ করে দিলেন। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, আমাকে উপলক্ষ করেই দুটো মেয়ের জীবনে নেমে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। অথচ আমার কিছু করবার নেই, শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের আসনে বসে বিয়োগান্ত দৃশ্যগুলোতে হা-হুঁতাশ করা ছাড়া।
পথ অল্প। নিঃশব্দে বসে আছি দুটি প্রাণী, একই চিন্তা নিয়ে। হরিশ পার্কের মাঝামাঝি আসতেই গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়লাম। হঠাৎ সাময়িক খেয়ালে একটা কাণ্ড করে বসলাম। গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে গোপার মাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে পশ্চিমদিকের ফুটপাথ ধরে হনহন করে চলতে শুরু করলাম। পিছন ফিরে না চেয়েও বেশ স্পষ্ট অনুভব করলাম, রঘুনন্দনকে গাড়ি চালাবার হুকুম দিতে ভুলে গিয়ে আমার গমনপথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন গোপার মা।
.
১৯৩০ সাল, ২৪ ডিসেম্বর। আমার জীবনের খরচের খাতায় আর সব কিছু মুছে নিঃশেষ হয়ে গেলেও ধ্রুবতারার মতো অম্লান হয়ে চিরদিন জেগে থাকবে ঐ একটি দিন। একটু আগে থেকেই শুরু করি। ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই নৌকাডুবির শুটিং আরম্ভ হল। সবাক নয়, নির্বাক। মাসখানেক আগে থেকেই হ্যারিসন রোডে পার্শি অ্যালফ্রেড থিয়েটারে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। রমেশ–আমি, হেমনলিনী–শান্তি গুপ্তা, কমলা–সুনীলা দেবী (গত যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবালার ছোট বোন), অক্ষয়–নরেশদা, অন্নদাবাবু কুমার কনকনারায়ণ, যোগেশ–গিরিজা গাঙ্গুলী, ডাঃ নলিনাক্ষ মিঃ রাজহন্স প্রভৃতি। সবাক নৌকাডুবির জন্য আমরা রীতিমত প্রস্তুত হঠাৎ শুনলাম সবাক হবে না। প্রধান কারণ হল, বিশ্বভারতী ফিল্ম রাইটের জন্য প্রচুর টাকা চাইছেন। দ্বিতীয় কারণ, তখনও, কী কারণে জানি না, টকি মেশিন এসে পৌঁছয়নি। জাহাঙ্গীর সাহেব রেগেমেগে নরেশদাকে বললেন, কুছ পরোয়া নেহি–নির্বাকই তোল। বলা বাহুল্য অনেক আগে থেকেই ম্যাডানের নির্বাক চিত্ৰস্বত্ব কেনা ছিল।
বড়ুয়া সাহেব তখন তাঁর নিজস্ব বড়ুয়া স্টুডিওতে নির্বাক অপরাধী ছবি তুলছেন। তিনিই প্রথম ইলেকট্রিক লাইটে ঘরের মধ্যে ছবি ভোলা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেন এই ছবিতে, ফলও খুব খারাপ হয়নি। আমরা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই। বাইরে সিন খাঁটিয়ে আয়না ও রিফ্লেকটার দিয়ে ক্যামেরাম্যান যতীন দাস নৌকাডুবি তুলতে আরম্ভ করে দিল। যদিও সবাক ছবির জন্য একটি ফ্লোর প্রস্তুত ছিল এবং ইলেকট্রিক লাইটও এসে গিয়েছিল। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবার লোক তখনও আমেরিকা থেকে না আসায় সেদিকে মাথা ঘামানো দরকার বোধ করল না কেউ।
নভেম্বরের গোড়া থেকেই নৌকাডুবির রিহার্সাল শুরু হয়। জাহাঙ্গীর সাহেবের কথামতো ঐ মাস থেকেই বাড়তি কুড়ি টাকা মাইনের খাতায় জমা হয়ে গেল। স্কুলে হেডমাস্টারমশাইকে সব বললাম। ত্রিশ টাকায় একজন টেম্পোরারি মাস্টার নিচু ক্লাসে পড়াবার জন্য ঠিক হয়ে গেল। সবই একরকম ঠিক হন্ত, হল না শুধু বাবার ভেঙে পড়া শরীরটা। দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে লাগল। ডাক্তার নগেন দাস একদিন আমায় আড়ালে ডেকে স্পষ্টই বলে দিলেন, তোমার যদি ইচ্ছে হয় অন্য ডাক্তার দেখাতে পার, আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না। গত বাইশ দিন জ্বর একেবারে রেমিশান হয় না, তার উপর বুকের সদিটা রয়েছে।
দিশেহারা হয়ে গেলাম। তখন ডাঃ পি. সাহা হোমিওপ্যাথিতে সবে নাম করতে শুরু করেছেন। তাঁর শরণাপন্ন হলাম। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, একটু দেরি হয়ে গেছে। দেখি, কতদুর কী করতে পারি।
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলতে লাগল। সারাদিন শুটিং করে এসে সন্ধ্যা থেকে বাবার কাছে বসি। কোনো কোনো দিন সারা রাত কেটে যেত। সংসারের যাবতীয় কাজ, তার উপর রাত জাগা, একা মা পেরে উঠতেন না। বাবা আপত্তি করতেন, আমরা শুনতাম না। ইতিমধ্যে আমার ছোট বোনকে অনেক কষ্টে বাবার অসুখের অজুহাতে নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে স্বামী ও শাশুড়ির অমানুষিক নির্যাতনে বেচারী মরতে বসেছিল। ঐ একটি মাত্র বোন। আমাদের অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন বছরচারেক আগে। সেই থেকে আর পাঠায়নি, অজুহাত বিয়ের সময় গলার হারে তিনভরি সোনা কম হয়েছিল। বছরদুয়েকের একটি ছেলে ও ছমাসের একটি মেয়ে নিয়ে যেদিন একবস্ত্রে প্রথম বাবার সামনে এসে দাঁড়াল বোনটা, বাবা কেঁদে ফেলেছিলেন। বাবার চোখে জল বোধহয় এই প্রথম দেখলাম। দুতিন দিন বাদে একদিন রাত্রে আমার বোনের রক্তহীন শীর্ণ হাতখানি আমার হাতের উপর রেখে বাবা বললেন, আজ থেকে একে তোমার আর একটি ছোট ভাই বলে মনে করবে, তোমার যদি একমুঠো জোটে এরও জুটবে। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও একে কোনো দিন শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে না। কথা দাও। দিয়েছিলাম, আর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছিলাম। অবশেষে একটু একটু করে ঘনিয়ে এল সেই সর্বনেশে দিন ২৪ ডিসেম্বর। সকাল থেকে বেশ ভালই ছিলেন বাবা, জ্বর ও কাশিটা বাড়ল বিকেল থেকে। সারাদিন বাড়ির বার হলাম না, সন্ধ্যার পর মা কাঁদছেন দেখে বাবা হেসে বললেন, ছিঃ লীলা(আমার মায়ের নাম লীলাবতী), তুমি কাঁদছ? কত বড় গুরুভার আমার ধীউ বাবার ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ না? কোথায় ওকে উৎসাহ দেবে তা নয়, তুমি নিজেই স্বার্থপরের মত কেঁদে ভাসাচ্ছা
পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম, বললাম, আমাকে থিয়েটারে ঢোকবার অনুমতি দিয়ে যান বাবা। নরেশদা বলেছেন আপাতত পঁচাত্তর টাকা মাইনে ওঁরা দেবেন, নইলে এত বড় সংসার, মাত্র আশি টাকায় কী করে চালাব আমি!
ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে অনুমতি দিলেন বাবা।
আজ কথা কইবার নেশায় পেয়ে বসেছে বাবাকে। ছেলেবেলায় কী রকম দুষ্ট ছিলেন, অবাধ্য হয়ে আর দুষ্টুমি করে কত দুঃখ দিয়েছেন ঠাকুদাকে, তা গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন। বেশি কথা বলা ডাক্তারের নিষেধ ছিল। আমি ও মা অনেক করে বললাম অত কথা না কইতে, কিন্তু আজ বাবা যেন মরিয়া। প্লাবনের নদী, বাঁধন দিয়ে আটকে রাখা অসম্ভব। বললেন, ধীউ বাবা, আমি ছেলেবয়স থেকে মা-হারা, তাই সংসার আমাকে বাঁধতে পারেনি। কিন্তু তোমার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন, তার উপর রেখে গেলাম তোমার মাকে।
অনেকগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন বাবা। মা বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। একটু সুস্থ হয়ে আবার শুরু করলেন বাবা, আমি জানি, মাকে দুঃখ কষ্ট কোনও দিনই তুমি দেবে না। তবুও বলে যাই-সংসারে প্রত্যক্ষ দেবতা মা বাবাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে যারা কল্পিত পাথরের মূর্তির সামনে মাথা খুঁড়ে মরে, পুণ্য তাদের কোনো দিনই হয় না, শুধু মাথাব্যথাই সার হয়।
বুকের ঘড়ঘড়ানিটা যেন বেড়েছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল বাবার। মাকে ইশারা করে একটু বেদানার রস দিতে বললাম। খেয়ে একটু সুস্থ হলেন যেন। পায়ের কাছে বসেছিলাম, ইশারা করে কাছে আসতে বললেন। বুকের কাছে ঝুঁকে বললাম, আমায় কিছু বলবেন বাবা?
উত্তর না দিয়ে হাতখানি বুকের উপর চেপে ধরে চোখ বুজে রইলেন বাবা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, বাপের কর্তব্য কিছুই করে যেতে পারলাম না। তোমাদের জন্য রেখে গেলাম শুধু একরাশ দেনা, আর–।
গলা ধরে গেল বাবার। একফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল বালিশের উপর।
বললাম, ওসব চিন্তা করে আপনি মন খারাপ করবেন না বাবা। আপনি রেখে যাচ্ছেন আশীর্বাদ, খুব কম ছেলের বাবা-মা যা রেখে যেতে পারেন। টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি চিরস্থায়ী নয়। বাবা-মা প্রচুর রেখে গেলেও বুদ্ধির দোষে দুদিনেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। আপনি শুধু আমায় আশীর্বাদ করে যান বাবা, যেন দুঃখ অশান্তি অভাব আমাকে কোনও দিন বিচলিত করতে না পারে।
স্পষ্ট মনে আছে। একটা প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠেছিল বাবার সমস্ত মুখখানায়। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। বাবা বললেন, যাও একটু বিশ্রাম কর। আজ কদিন ধরে দিনে রাতে একটুও বিশ্রাম পাওনি। মাও বললেন, আমি তো বসে আছি, তুমি যাও, একটু ঘুমিয়ে নাওগে।
উপরে বাবার ঘরের পাশেই একটা চওড়া ঘেরা বারান্দা, সেইখানেই খালি তক্তপোশের উপর একটা মাদুর ও বালিশ নিয়ে ব্যাপার মুড়ি দিয়ে শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।
কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, একসময় কী একটা চিৎকার শুনে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘরে ঢুকে দেখি, মা, ছোট বোন, ছোট ভাইটা, সব একসঙ্গে বুকফাটা কান্না শুরু করে দিয়েছে বাবাকে ঘিরে। চিত হয়ে শুয়ে হাত জপের ভঙ্গিতে বুকের উপর রেখে শান্ত সৌম্য মুখখানাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি নিয়ে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন বাবা।
পাখিরা ঘুম ভেঙে বিচিত্র কলরবে স্বাগত জানাচ্ছে নবারুণের উদ্দেশে। পুবের আকাশে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সবে একটুখানি আলোর আভাস দিয়েছে। বাবার মুখে শুনেছিলাম এই সময়টিকে ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে–ভাগ্যবান না হলে এই শুভ মুহূর্তে জন্ম-মৃত্যু হয় না।
ছোট ভাই রাজকুমার ছেলেমানুষ, বাড়িতে পুরুষ বলতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি দেখেই তিন-চারদিন আগে মামাকে খবর দিয়ে দেশ থেকে আনিয়েছিলাম। দেখলাম, ঘরের মাঝখানে বসে হাঁটুর উপর মুখ রেখে তিনিও কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন। বাবার বিছানার পাশে রাখা কাঠের একটা চৌকো বাক্স ছিল, ওতেই টাকাকড়ি দরকারি কাগজপত্তর সব থাকত। খুলে দেখি নগদ ও খুচররা মিলিয়ে টাকা-আড়াই এর বেশি বাক্সে নেই। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এ দিয়ে বাবার শেষ কাজ দূরে থাক, কাঠের খরচই কুলোবে না। চিন্তার সময় নেই–ছোট ভাইকে বাবার দেহ ছুঁয়ে বসিয়ে দিয়ে নিচে এসে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম।
পূর্ণ থিয়েটারের দক্ষিণের গা ঘেঁষে একটি চায়ের দোকান, নাম বেঙ্গল রেস্টুরেন্ট। দোকানের মালিক সুধীর তরফদার আমার সহপাঠী। সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুধীর তখন সবে দোকান খুলে ধূপ-ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে দেওয়ালের র্যাকে বসানো গণেশের মূর্তিকে প্রণাম করছে। মুখ তুলতেই চোখাচোখি। কোনও কথা না বলে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল-কত?
এখানে একটু বলে রাখি, সুধীর বাবার অসুখের বাড়াবাড়ির কথা জানত। আমিও একটু আভাস দিয়ে রেখেছিলাম যদি হঠাৎ দরকার হয় কিছু টাকা প্রস্তুত রাখতে। বললাম, গোটা কুড়ি টাকা এখন দে, পরে দরকার হলে বলব।
দ্বিরুক্তি না করে ক্যাশবাক্স খুলে দুখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিল সুধীর। সটান বাড়ি এসে মামার হাতে টাকাটা দিয়ে বললাম, কাছা ও থান কাপড়চোপড় যা দরকার কিনে আনুন। আমি সৎকারের লোক ডাকতে যাচ্ছি।
বাবার রোগজৰ্জর অস্থির দেহটিকে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে ভস্মীভূত করে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন বেলা দুটো বাজে।
ঘরের মেঝেতে একখানা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আর একখানি মুড়ি দিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে যাব, নিচ থেকে পিওন হাঁকল-রেজিস্ট্রি চিঠি বাবু! বাবার নামে চিঠি, আসছে খুলনা লোন অফিস থেকে। যথারীতি সই করে চিঠি নিয়ে পড়ে দেখি–গত কয়েক বছর ধরে বাবা কিছু কিছু ধার নিয়েছেন লোন অফিস থেকে, মাঝে মাঝে সুদের টাকা পাঠিয়েছেন, ওরাও চুপ করে আছে। গত তিন বছরের মধ্যে সুদ কিছুই দেওয়া হয়নি। ওদের সুদই পাওনা হয়েছে প্রায় পাঁচশ টাকা। চিঠি প্রাপ্তির পর থেকে সাত দিনের মধ্যে সমস্ত সুদ পরিশোধ না করে দিলে ওরা আইনের সাহায্যে দেশের সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে তা থেকে প্রাপ্য টাকা নিয়ে নেবে। ছোট বোনের বিয়ের সময় একটা মোটা টাকা ধার করতে হয়েছিল, তাছাড়া মাঝে মাঝে টিউশনি না থাকলে সংসারের খরচের জন্য কিছু কিছু ধার করতেন, জানতাম। কিন্তু এ যে একেবারে শিরে সংক্রান্তি! আমাকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে সের দরে বিক্রি করলেও কেউ পাঁচশ টাকা দেবে না। কী করি? অনেক ভেবেও কোনও কুল কিনারা পেলাম না।
রাত্রে ঘুম হল না। সারা রাত বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, এত শিগগির আমাকে এরকম কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন বাবা!
সকালে একটু বেলায় নরেশদার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এসেছেন। থিয়েটারের অনুমতি পেয়েছি শুনে খুশি হলেন, বললেন, সামনের জানুয়ারি থেকেই তোমাকে দীপালি নাট্যসংঘে ভর্তি করে নেব।
রেজিষ্ট্রি চিঠিটা দেখালাম। পড়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন নরেশদা, বললেন, তাইতো, ভাবনার কথা। একটা কাজ তুমি করতে পার, অফিসে রুস্তমজী সাহেবকে একবার বলে দেখতে পার।
ম্লান হেসে বললাম, সব শুনে সাহেব যদি চটে গিয়ে চাকরিটাই খতম করে দেন?
একটু ভেবে নরেশদা বললেন, খানিকটা রিস্ক অবিশ্যি আছে। কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায়ও তো দেখতে পাচ্ছি না।
আগের দিন একগ্লাস মিছরির জল ছাড়া কিছুই খাইনি। গঙ্গায় স্নান করে তাড়াতাড়ি হবিষ্যি রান্না করে খেয়ে খালি পায়ে অশৌচের কাপড়চোপড়ের উপর একটা ব্যাপার চাপা দিয়ে ধর্মতলার ট্রামে উঠে বসলাম।
প্রকাণ্ড দরদালানের মতো লম্বা ঘর, সামনেটা বিলিতি মদের দোকান। দক্ষিণের শেষ প্রান্তে কাঁচের পার্টিশন দেওয়া অফিস। পার্টিশনের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। অগুনতি লোক ভেতরে যাচ্ছে আসছে। মুখ খুলে কথা কইবার অবসর নেই সাহেবের। বেশ খানিকটা দমে গেলাম। বেলা প্রায় একটার সময় ভিড় একটু কমল, ভেতরে যাব কি যাব না ইতস্তত করছি, দেখি পার্টিশনের দিকে চেয়ে হাত ইশারায় কাকে ডাকছেন রুস্তমজী সাহেব। আশেপাশে চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। দুরুদুরু বক্ষে আস্তে আস্তে পার্টিশনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাহেবের এত কাছে এর আগে আসবার সৌভাগ্য হয়নি। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, দুধের মতো সাদা ঘন গোঁফ। চুল, এমনকি ভুরু দুটো পর্যন্ত সাদা। প্রকাণ্ড ভারী মুখ, তীক্ষ্ণ নাকের উপর সোনার চশমা, তারই ভেতর দুটো উজ্জ্বল অনুসন্ধানী চোখ। রাশভারি লোক–হঠাৎ কাছে গেলে ভয়ের সঙ্গে কেমন একটা শ্রদ্ধাও এসে পড়ে। আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সাহেব বললেন, ব্যাপার কী?
শুনেছিলাম রুস্তমজী সাহেব বাংলা পরিষ্কার বুঝতে পারেন, ভাল বলতে পারেন। বাবার অসুখ থেকে শুরু করে আমার মাইনের কথা, খুলনা লোন অফিসের দেনার কথা সব একনিশ্বাসে বাংলায় বলে গেলাম। সব শুনে সাহেব একটুখানি চুপ করে কী যেন ভাবলেন। কম্বলের আসনে মোড়া রেজিষ্ট্রি চিঠিখানা বার করে সাহেবের সামনে ধরলাম। হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে সাহেব ইংরেজিতে বললেন, ঘন্টাখানেক বাদে আমার সঙ্গে দেখা করবে।
পার্টিশন ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। এক ঘন্টা কোথায় কাটাই? পাশেই কোরিন্থিয়ান থিয়েটার, ঢুকে পড়ে একখানা গদিমোড়া চেয়ারে কম্বলের আসন বিছিয়ে বসে পড়লাম। একটা উর্দু নাটকের রিহার্সাল হচ্ছিল। স্টেজের উপর দেখলাম মাস্টার মোহন ও মিস শরিফাঁকে। তখনকার দিনে মাস্টার মোহন শিশিরবাবু ও দানীবাবুর মতো হিন্দি নাট্যজগতে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন–মাইনে পেতেন দেড় হাজার টাকা। নাটকটির নাম বা বিষয়বস্তু কিছুই মনে নেই, শুধু আবছা সিনটা মনে আছে। নায়ক মাস্টার মোহন ওথেলোর মতো নায়িকা শরিফার চরিত্রে সন্দিহান হয়ে যা-তা কটুক্তি করে শেষকালে যাবার সময় বলে গেলেন যে, তার মতো কুলটার আত্মহত্যা করে মরাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ। বেশ প্রাণবন্ত অভিনয় করে গেলেন মাস্টার মোহন। তার প্রস্থানের পরই গান ধরলেন নায়িকা শরিফা।অবাক হয়ে ভাবছিলাম,এটা কী করে, কোন যুক্তিবলে সমর্থন করলেন নাট্যকার ও পরিচালক!বিদুৎ ঝলকের মতো তখনই মনে পড়ে গেল, শুধু হিন্দি বা উর্দু নাটকে নয়, আমাদের বাংলাতেও তো এরকম হয়। চন্দ্রশেখর নাটকে দলনী বেগমের সিনটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। দলনীকে বিষ দিয়ে বলা হল, নবাব স্বয়ং পাঠিয়েছেন এই বিষ তার জন্যে। হাতে নিয়ে বিষ পান করবার আগে দলনী বেগম গাইলেন সেই বিখ্যাত গান–আজু কঁহা মেরি, হৃদয়কি রাজা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঁকি মেরে চাইলাম মদের দোকানের বড় দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। দুটো বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পার্টিশনের পাশে দাঁড়ালাম। দেখলাম লোকজন কেউ নেই। রুস্তমজী সাহেব মুখ নিচু করে খাতায় কী লিখছেন।
নমস্কার করে কাছে দাঁড়াতেই মুখ না তুলে সাহেব হাত ইশারায় টেবিলের উপর রাখা সাদা একটা খাম দেখিয়ে বললেন, টেক দ্যাট এন্ড গো হোম।
কাঠের পুতুলের মতো খামটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। অদম্য কৌতূহল বাড়ি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হল না।
নরেশদা বললেন, সেই কথাই আলোচনা করতে সাহেবের কাছে এসেছিলাম। আমার ভয় ছিল, হয়তো বলবেন–অন্য লোককে রমেশের পার্ট দিয়ে শুটিং চালিয়ে যাও। কিন্তু সাহেব নিজে থেকেই বললেন–তোমার হিরো খানিক আগে এসেছিল, ওর বিপদের কথা সব শুনেছি। মাস দুই শুটিং বন্ধ রাখ, আর ওকে বলে দিও মাসের তিন তারিখে শুধু মাইনে নিতে আফিসে আসতে।
দ্বিধাভরে বললাম, কিন্তু এই পাঁচশ টাকার কী ব্যবস্থা হবে?
একটু হেসে নরেশদা বললেন, এরকম গোপন দান রুস্তমজীর অনেক আছে। এ নিয়ে হৈচৈ করলে সাহেব ভীষণ চটে যান। তাইতো টাকার কথা বলতেই চটে উঠলেন। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যাও। ও টাকা কোনো দিনই তোমার মাইনে থেকে কাটা হবে না।
জাহাঙ্গীর সাহেবের বেয়ারা এসে বলল, সাহেব সেলাম দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেলেন নরেশদা।
ফুটপাথ থেকে দুতিন পা পুব দিকে এগিয়ে গেলেই মদের দোকানের সামনে পড়া যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো প্রকাণ্ড লম্বা ঘর। শেষ প্রান্তে কাঁচের পার্টিশন। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও আবছা দেখা যায়, কালো পার্শি কোট ও টুপি মাথায় রুস্তমজী সাহেবকে। একদৃষ্টে চেয়ে মনে মনে ভাবলাম, এ যুগে এরকম মনিবও আছে?
বোধহয় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, দেখলাম চেনা-অচেনা অনেকেই বেশ একটু অবাক হয়ে চাইতে চাইতে যাচ্ছেন।
আমাদের পাড়ার একটি ভদ্রলোক-মুখের চেনা পরিচয়, বিশেষ আলাপ ছিল না, তিনি যেতে যেতে থমকে আমার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মিনিটখানেক নীরবে একবার আমার দিকে একবার দোকানের প্রবেশপথের দুধারে কাঁচের শো-কেসে রাখা রঙ-বেরঙের বিলিতি মদের বোতলগুলোর দিকে চেয়ে বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, এখনও অশৌচ কাটেনি, এর মধ্যেই কথামালার শৃগালের মতো দ্রাক্ষাফলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছ, ছিঃ! উত্তরের অপেক্ষা করলেন
ভদ্রলোক, হনহন করে এগিয়ে বোধহয় এই মুখরোচক খবরটা পাড়ার চেনা অচেনা সবাইকে পরিবেশন করবার জন্যই গেলেন।
রুস্তমজীর কথাই সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ছিল, চেষ্টা করেও অন্য কিছু ভাবতে পারছিলাম না। ধর্মতলায় এসে কালীঘাটের ট্রামে উঠে বসলাম। গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে হুহু করে ছুটে চলেছে ট্রাম, মনটাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে বাড়ির দিকে।
খুলনা লোন কোম্পানির সমস্ত সুদের টাকা শোধ করে বছরের মত নিশ্চিন্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। পাঁচশ টাকার সবটা লাগেনি, পঁচিশ ত্রিশ টাকা বাঁচল। সেই টাকায় আর দীপালি নাট্যসংঘের একমাসের অগ্রিম পঁচাত্তর টাকা নিয়ে যথাসময়ে বাবার পারলৌকিক কাজ শেষ করলাম। একদিন কিছু ভাববার সময় পর্যন্ত পাইনি। এইবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সব দিক বেশ করে ভেবে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দুপুরবেলায় উপরের ঘরে শুয়ে এইসব চিন্তা করছি, ছোট ভাই এসে বলল, বাড়িওয়ালা লালবিহারীবাবু নিচের ঘরে বসে আছেন। এদিকটা একদম ভেবে দেখিনি। মাথায় নতুন করে আকাশ ভেঙে পড়ল।
বাড়িওয়ালা লালবিহারী মুখোপাধ্যায় কলকাতার কাছে বৈদ্যবাটীতে বাস করতেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। ছফুট লম্বা জোয়ান চেহারা, মুখে অল্প দাড়ি ও গোঁফ। সদালাপী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার। পেনসন নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকেন। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে সকালে আমাদের বাড়িতে এসে দুপুরে খেয়েদেয়ে বাড়িভাড়া নিয়ে বৈদ্যবাটী ফিরে যেতেন। বাবা ওঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন এবং দাদা বলে ডাকতেন। সেই সুবাদে আমরা সবাই জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। বাবার অসুখের তিন-চার মাস কি আরও বেশিদিন থেকে উনি আসেন না।
তাড়াতাড়ি উঠে নিচে নেমে গিয়ে প্রণাম করে পাশে বসলাম। মামুলি কুশল প্রশ্নাদির পর একটু ইতস্তত করে কথাটা উনিই পাড়লেন–বাবা ধীরাজ, তোমার এই দুঃসময়ে কথাটা তুলতে লজ্জা হচ্ছে আমার। কিন্তু বাবা জানতো, বাড়িতে একগাদা পোয্য। সম্বল মাত্র পেনশনের কটি টাকা আর এই বাড়িভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। তাও আজ এগারো মাস পাইনি।
বাড়িভাড়ার ব্যাপারে কোনও দিন মাথা ঘামাইনি, আর বাবাও সে সম্বন্ধে কোনওদিন কিছু বলেননি আমাকে। কিন্তু এগারো মাস বাড়িভাড়া দেওয়া হয়নি এটা কল্পনাতীত। কী উত্তর দেব, মুখ নিচু করে বসে রইলাম।
জ্যাঠামশাই বললেন, জানি বাবা, এখন তোমার পক্ষে এক মাসের ভাড়া দেওয়াও অসম্ভব। আর সেজন্যও আমি আসিনি। তুমি যদি কিছু মনে না কর–
কথাটা শেষ করলেন না জ্যাঠামশাই, কেমন একটা সঙ্কোচ এসে বাধা দিল। বললাম, আপনি বলুন জ্যাঠামশাই, আমি জানি, আপনি যা বলবেন আমার ভালর জন্যই বলবেন।
জ্যাঠামশাই বললেন, বাড়িভাড়া তোমার সুবিধা মতো যখন পার কিছু কিছু করে দিও, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় মাসে পয়তাল্লিশ টাকা বাড়িভাড়া দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব কি? সেইজন্যে আমি বলছিলাম, তুমি যদি অল্প ভাড়ার একটা বাড়ি দেখে উঠে যেতে, তাহলে আমাদের দুপক্ষেরই সুবিধা হত।
খুব যুক্তিপূর্ণ কথা। এদিক দিয়ে একেবারে ভেবে দেখিনি। বললাম, তাই হবে জ্যাঠামশাই, এ মাসের শেষ দিকে আমি বাড়ি ছেড়ে দেব, বাকি ভাড়া প্রতি মাসে কিছু কিছু করে দেব।
ঐ পাড়াতেই বলরাম বোসের ঘাটের কাছেই দুখানা টিনের ঘর পাওয়া গেল। মাটির দেওয়াল। মেঝে ও রক সিমেন্ট করা, সামনে ছোট্ট একফালি উঠোন, পুবদিকে একটা এঁদো পুকুর। বড় রাস্তা বলরাম বোস ঘাট রোড, থেকে একটা সরু গলি বেয়ে খানিকটা এসে বাড়িটা। রান্নাঘর নেই, দাওয়ার একপাশ ঘিরে রান্নাঘর করতে হবে। কেননা দিক দিয়েই পছন্দ হবার কথা নয়, শুধু ভাড়াটা ছাড়া। এগারো টাকা ভাড়া। দীপালি নাট্যসংঘ আর আমার বাড়তি মাইনেতে এর চেয়ে ভাল বাড়ি নিতে পারতাম। কিন্তু মা বললেন, না। কম ভাড়ার বাড়ি নিয়ে আগে তোমার জ্যাঠামশাইয়ের বাকি পড়া ভাড়া শোধ কর। তাই করলাম।
.
আর. সি. এ. মেসিন, সঙ্গে তিনজন বিশেষজ্ঞ অবশেষে সত্যিই এসে পড়ল। স্টুডিওতে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। শুটিং সব বন্ধ। মাসের তেসরা তারিখে শুধু খাতায় সই করে মাইনে নিতে হেড অফিসে যাই। বলা বাহুল্য, মাইনে থেকে রুস্তমজী সাহেবের দেওয়া টাকার এক পয়সাও কাটা হয়নি। কাজকর্ম নেই, সময় আর কাটতে চায় না। ছোট একটা ছিপ জোগাড় করে দুপুরবেলা এঁদো পুকুরের পাড়ে বসে পুঁটি মাছ ধরে সময় কাটিয়ে দিই।
দু তিনদিন পরের কথা। সেদিনও যথা নিয়মে পুঁটি মাছের বংশক্ষয়ে মনোনিবেশ করে ছোট্ট ফাতনাটার দিকে চেয়ে বসে আছি, মনে হল, বাইরের রাস্তা থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। নেহাত অনিচ্ছায় উঠে অন্ধকার গলির পথ পেরিয়ে বলরাম বোসের ঘাট থেকে রোডে পড়েই দেখি, আশেপাশে বাড়িগুলোর জানলা-দরজায় বেশ লোক জড়ো হয়েছে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মুখুজ্যে খালি বলে চলেছে, বলতে পারেন এখানে কোন বাড়িতে ধীরাজ উঠে এসেছে? আগের বাড়িতে যারা এসেছে তারা বলল, ঘাটের কাছাকাছি বস্তিতে উঠে গেছে।
হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে কাছে এসে বলল, এই যে নদেরাদ, এরকম আত্মগোপন করে থাকার হেতু?
হেসে বললাম, অবস্থার ফেরে পাণ্ডবদেরও আত্মগোপনের প্রয়োজন হয়েছিল, আমি তো কোন ছার।
–থাক, আর কবিত্ব করে কাজ নেই। এখন ভেতরে চল দেখি, কথা আছে। বলে একরকম আমাকে ঠেলে নিয়ে যায় আর কী। মহা লজ্জায় পড়লাম। মাত্র দুখানি পায়রার খোপের মতো ঘর, জিনিসপত্তরই সব ধরে না, সেখানে নিয়ে বসাব কোথায়!
আমায় ইতস্তত করতে দেখে মুখুজ্যে বলল, ব্যাপার কী, বাড়ি নিয়ে যেতে আপত্তি আছে নাকি?
বললাম, না না, তা নয়, মানে সবে এসেছি। জিনিসপত্তর চারদিকে ছড়ানো তার মধ্যে।
বুঝেছি। বলে চারদিকের কৌতূহলী লোকগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল মুখার্জি, যাই বল ভাই, তোমার পাড়াটি কিন্তু মোটেই সুবিধার নয়। তোমার আগের বাড়িতে যারা এসেছেন তারা তো ঠিকানা বললেনই না, অধিকন্তু ঠাট্টা করে বললেন–বস্তিটস্তির ভেতর খুঁজে দেখুন, পেয়ে যাবেন। গলাটা একটু নিচু করে চোখ ইশারায় আশেপাশের লোকগুলোকে দেখিয়ে বলল, এঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, শুধু মুচকি হেসে বলে দিলেন–ডাকাডাকি করুন, পাওনাদার না হন তত বেরিয়ে আসবে। হতো আমার পাড়া–।
কথাটা চাপা দেবার জন্যে বললাম, এসো, এক কাজ করা যাক। সামনেই বলরাম বোসের ঘাট। দুপুরবেলা, এখন লোকজন কেউ নেই। চল না, ঐখানে বসেই কথাবার্তা বলি।
খুব খুশি হল না মুখুজ্যে। দুজনে গিয়ে ঘাটের ডান দিকের উঁচু সিমেন্টের চাতালটার উপর বসলাম। একটু চুপ থেকে বললাম, মুখুজ্যে, প্রকাণ্ড বটগাছের আড়ালে বসে এতদিন বাইরের ঝড়ঝাঁপটার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানতে পারিনি। দুনিয়াটাকে ভাবতাম রঙিন স্বপ্নে ভরা। সেই দুনিয়ার ছায়াছবির নায়ক হবার স্বপ্ন দেখতাম ছেলেবেলা থেকে। ঝড়ে পড়ে গেছে বটগাছ, সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে খসে পড়েছে রঙিন স্বপ্নের ঠুলি।
কী একটা বলতে যাচ্ছিল মুখুজ্যে। বাধা দিয়ে বললাম, কথাগুলো শেষ করতে দাও আমাকে। আমার বাবা টাকাকড়ি কিছুই রেখে যাননি, রেখে গেছেন একরাশ দেনা। সে দেনা শোধ করতে হলে বস্তিতে বাস করা ছাড়া আমার অন্য রাস্তা খোলা নেই। কথা শেষ করে ভাটায় চড়া পড়া মরা গঙ্গার দিকে চেয়ে রইলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, মুখুজ্যে একটু লজ্জায় পড়ে গেছে। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্যে একটু পরে আমি বললাম, তারপর? কী কথা বলবে বলছিলে?
যেন বেঁচে গেল মুখুজ্যে, বলল, একসেলেন্ট! চমৎকার পার্ট হয়েছে তোমার কালপরিণয়ে। এডিটিং শেষ করে কাল রাত্রের শো-এর পর এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে দেখা হল ছবিটা। রুস্তমজী, বজরজী, জাহাঙ্গীরজী, নরেশদা, গাঙ্গুলীমশাই, সবাই দেখেছেন। সবাই একবাক্যে তোমার সুখ্যাতি করলেন। সামনের শনিবারে ক্রাউনে রিলিজ, যেও কিন্তু!
হেসে বললাম, এই ন্যাড়া মাথা নিয়ে?
–তাতে কী হল, একটা খদ্দরের গান্ধী-ক্যাপ পরে যেও। এবার আসল কথাটা শোন।
পকেট থেকে কঁচি সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা আমায় দিয়ে নিজে ধরাল একটা। আসল কথাটা শোনবার জন্যে মুখুজ্যের দিকে চেয়ে চুপ করে সিগারেট খেতে লাগলাম।
নিঃশব্দে সিগারেটে কয়েকটা সুখটান দিয়ে মুখুজ্যে বলল, শোন, কাল একবার স্টুডিওয় যেও। বিশেষ দরকার।
বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, ব্যাপার কী মুখুজ্যে?
–ব্যাপার গুরুতর! কাল সব বড় বড় আর্টিস্টদের ডাক হয়েছে স্টুডিওতে। আবার বললাম, ব্যাপার কী মুখুজ্যে?
বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার চালে মুখুজ্যে বলল, ভয়েস টেস্ট।
–ভয়েস টেস্ট! তার মানে?
–টকিতে কার গলা কীরকম আসে দেখে নেওয়া হবে। মাইক্রোফোনের কাছে চালাকি চলবে না। যাদের গলা ভাল রেকর্ড করবে না, তারা খতম।
ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, কালকে কার কার গলার টেস্ট নেওয়া হবে?
গড়গড় করে বলে গেল মুখুজ্যে, অহীন্দ্রবাবু, দুর্গাদাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নরেশদা, তুমি, নির্মল লাহিড়ী, হাঁদুবাবু, কার্তিকবাবু, জয়নারায়ণ মুখুজ্যে, আরও অনেক অভিনেতার। মেয়েদের মধ্যে তোমাদের নৌকাডুবির ব্যাচের শান্তি গুপ্তা, সুনীলা, তাছাড়া ললিতা দেবী, পেশেন্স কুপার আর তার তিন বোন, সীতা দেবী, ইন্দিরা দেবী, আরও একগাদা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে।
অবাক হয়ে বললাম,অ্যাংলো মেয়েগুলো কেন মুখুজ্যে? ওরাও কি বাংলা ছবিতে –।
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখুজ্যে বলল–হিন্দি হিন্দি! বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে ছবি হবে। ফিরিঙ্গিপাড়ায় গিয়ে দেখ ইংরেজি কিচিরমিচির নেই। মুন্সী রেখে সবাই উর্দু পড়তে শুরু করেছে–আলেফ বে পে তে–!
.
ফেল! ফেল করলাম ভয়েস টেস্টে। একা আমি নই, অনেকেই। অহীনদা, নরেশদা, গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, আরও ছোটখাটো অনেকে। ফুল মার্ক পেয়ে পাস করলেন দুর্গাদাস আর জয়নারায়ণ মুখুজ্যে। মেয়েদের সবাই পাস। ভীষণ দমে গেলাম। সবাক ছবির শুরুতেই এরকম অবাক হব ভাবতেও পারিনি। যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটকে রামের পার্টে বহুবার সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছি। তা থেকে একটা ইমোশান্যাল সিন অভিনয় করলাম নিষ্ঠুর মাইক্রোফোনের সামনে, কিছুই হল না। ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, নির্বাক গিরিবালা, কালপরিণয়ের সমস্ত নাম-যশ নিঃশেষে ধুয়ে মুছে দেবে নাকি ঐ এক ফোঁটা মাইক্রোফোন?
এক নম্বর ফ্লোরের পাশে নির্জনে একখানা বেঞ্চের উপর বসে আলোর আশায় অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বসে আছি, কোথা থেকে মনমোহন এসে হাজির। আমায় দেখতে পেয়েই হাসতে হাসতে গায়ের উপর পড়ে আর কী! কোনও রকমে ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিতেই হাত ধরে টানতে টানতে বলল, মজা দেখবি আয়। ঝঝের সঙ্গে বললাম, মজা দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই।
হাসি থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে ঝুঁকে মনমোহন বলল, ফেল করেছিস বুঝি?
হেসে ফেললাম। বললাম, পাশ করলেও তোর হাসি কানে মধু বর্ষণ করত না।
পাশে বসে পড়ে পান-দোক্তা মোড়া একটা কাগজ বার করল মনমোহন।
বললাম, যেখানেই কিছু একটা অঘটন ঘটার সম্ভাবনা, যাদুমন্ত্রে তোর আবির্ভাব। তা এবার মজার ব্যাপারের বিষয়বস্তুটি কী?
বোধহয় ভুলে গিয়েছিল, মনে করিয়ে দিতেই থু থু করে গালের পান-দোক্তা ফেলে দিয়ে হাসতে শুরু করল মনমোহন। ওরই মধ্যে একটু দম নিয়ে অতি কষ্টে বলল, তোর মৈনাক পর্বত ঘাড়ে করে জাল সাহেব এসেছে টেস্ট দিতে।
জাল-গুলজার কাহিনীর যবনিকা নির্বাক যুগেই পড়বে ভেবেছিলাম। সবাক যুগেও তার জের টানা হবে ভাবতে পারিনি। রীতিমত কৌতূহল হল, বললাম, চল মনু, এ কথা আগে বলতে হয়।
দুজনে ফ্লোরে ঢুকতে গিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। জাল সাহেবের হুকুম, কেউ ভেতরে থাকবে না। বহুদিনের পুরোনো ওড়িয়া সেটিং কুলি উছুবা দরজার সামনে গম্ভীরভাবে টুল পেতে বসে জাল সাহেবের হুকুম তামিল করছে। হতাশ ভাবে তাকালাম মনমোহনের দিকে। দুষ্ট বুদ্ধি মনমোহনের হাতধরা। পকেট থেকে আলাদিনের প্রদীপের মতো পান-দোক্তা মোড়া কাগজের ঠোঙাটা বার করে তা থেকে দুটো পান নিয়ে আশেপাশে চকিতে চোখ বুলিয়ে উছুবার হাতে গুঁজে দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল। নিমেষে উছুবার গোমড়া মুখ হাসিখুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা সন্তর্পণে প্রায় ইঞ্চিচারেক ফাঁক করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। আমাকে ইশারায় কাছে ডাকল মনমোহন, তারপর দুজনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সেই চার ইঞ্চি ফাঁকে। মনমোহন নিচে, আমি উপরে।
আকাশের রামধনুতে আর শিল্পীর তুলিতে যতগুলো রং নজরে পড়ে সবগুলো একসঙ্গে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে গুলজার বেগমের পোশাকে। পাঞ্জাবী পোশাক, কিন্তু এমন বিচিত্র রুচিহীন রঙের খেলা কদাচিৎ দেখা যায়। কয়েক মাস আগে চেয়ারে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম, আজ মনে হল গুলজার আরো লম্বা, আরো মোটা। ওর পাশে জাল সাহেবকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন হাতির পাশে নেংটি ইঁদুর। দেখলাম, গুলজার বেগম জাল সাহেবের দিকে কাত হয়ে কী যেন শোনবার চেষ্টা করছে, আর লাফানোর ভঙ্গিতে মুখ তুলে এক-একটা কথা ছুঁড়ে মারছে জাল সাহেব গুলজারের কানে। হাসি সামলানো কঠিন। আড়-চোখে মনমোহনের দিকে চাইলাম, ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। চিমটি কেটে সাবধান করে দিলাম।
ঘন্টা বাজল। এইবার টেস্ট নেওয়া হবে। বাইরে এক নম্বর ফ্লোরের দক্ষিণ কোণে ইলেকট্রিক ঘন্টা আর্তনাদ করে উঠে আশেপাশের সবাইকে সাবধান করে দিল কথা না কইতে বা কোনও আওয়াজ না করতে।
রুদ্ধ নিশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, শুরু হল টেস্ট। মোটা একখানা খাতা খুলে পাশ থেকে জাল সাহেব ইশারা করলেন গুলজারকে।
মেয়েছেলের গলায় একঙ্গে তানপুরার মতো চারটে আওয়াজের খেলা এর আগে শুনিনি। দুর্বোধ্য উর্দুতে বীররসের অভিনয়। চোখ পাকিয়ে দুহাতে ঘুষি বাগিয়ে গুলজার যেন কোনও অদৃশ্য আততায়ীর মৃত্যু পরোয়ানা জারি করছে। ডায়লগ আর শেষ হয় না, মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে জাল সাহেব কথার সূত্র ছুঁড়ে মারছেন ওর কানে। কিছুক্ষণ এই ভাবে চলার পর ঘন্টা বেজে উঠল। পাশের দরজা দিয়ে রেকর্ডার মিঃ লাইফোর্ড বেশ রাগতভাবে ওদের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কজনের ভয়েস টেস্ট নেওয়া হচ্ছে?
জাল সাহেব ইশারা করে গুলজার বেগমকে দেখিয়ে দিলেন।
প্রবলভাবে মাথা নেড়ে লাইফোর্ড বললেন, নো, আমি পরিষ্কার দুজনের গলা পাচ্ছি।
জাল সাহেব স্বীকার করবেন না, লাইফোর্ডও ছাড়বেন না। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতির উপক্রম। জাল সাহেবের ধারণা, চুরি করে আস্তে আস্তে যে কথাগুলো গুলজারকে প্রম্পট করেছেন সেগুলো রেকর্ড হতেই পারে না। ব্যাপার হয়তো আরও অনেক দূর গড়াত। শেষ পর্যন্ত দেখবার বা শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হল না। উছুবা তাড়াতাড়ি দরজার ফাঁক বন্ধ করে দিয়ে বলল, ফ্রামজী সাহেব আর দুজন সাহেবকে নিয়ে এদিকেই আসছেন।
একটু দূরে গিয়ে একখানা বেঞ্চিতে আমি আর মনমোহন বসলাম। একটু পরে ঘন্টা দিয়ে আবার শুরু হল টেস্ট। মনমোহনকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, তোর কী মনে হয়, গুলজার বেগম ভয়েস টেস্টে পাস করবে?
পান খেতে খেতে জবাব দিল মনমোহন, শিওর! এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করছিস?
হতাশভাবে বললাম, ঐ গলা যদি মাইকের উপযোগী হয় তাহলে আমাদের ফেল করিয়ে দিল কেন?
আবার শুরু হল মনমোহনের হাসি। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম। উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। সবাই ব্যস্ত। দাঁড়িয়ে দুদণ্ড বাজে গল্প করার সময় নেই কারো। উত্তরদিকে শুরু হয়েছে আরও একটা ফ্লোর, রাতদিন মিস্ত্রী খাটছে। শুনলাম, বিশেষজ্ঞরা এসে এক নম্বর ফ্লোর সবাক ছবি নেবার উপযুক্ত নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। ওখানে থাকবে আর. সি. এ. মেশিন, ক্যামেরা এবং আর সব যন্ত্রপাতি। মিস্ত্রিদের খটখটাখট আওয়াজ, কুলিদের হৈহা, তার মাঝে হঠাৎ বেজে উঠছে চুপ করবার ঘন্টা। দুতিন মিনিট সবাই চুপচাপ, আবার যে কে সেই। স্টুডিওটাকে মনে হল কুম্ভকর্ণ। এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, আজ ঘুম ভেঙে শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। আপনা হতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, ভাবলাম, বেল পাকলে কাকের কী? এই মুখর রাজ্যে সবাই জয়যাত্রার গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যাবে, আর আমি শুধু মূক দর্শক হয়ে রাস্তার একপাশে নিম্বলের হতাশের দলে পড়ে থাকব। তখনি মনে পড়ল, আমি শুধু একা নই, সঙ্গে বড় বড় বাঘ ভাল্লুকও আছে, তাদের যদি একটা ব্যবস্থা হয় তো আমারও হবে। জোর করে মনটাকে প্রফুল্ল রেখে বাড়ি চলে এলাম।
বলতে ভুলে গেছি যে, এরই মধ্যে ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দীপালি নাট্যসংঘের সঙ্গে কলকাতার কাছাকাছি তিন-চারটে জায়গায় অভিনয় করে এসেছি। শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, ধানবাদ, নৈহাটি–এই চারটে জায়গায় অভিনয় হল জয়দেব, সরলা, প্রতাপাদিত্য, কর্ণার্জুন। সঙ্গে প্রহসন রেশমি রুমাল, তুফানি, রাতকানা ইত্যাদি। এছাড়া নৃত্যগীতবহুল আলিবাবা আর বসন্তলীলাও চাহিদানুযায়ী অভিনয় হত। তখনকার দিনে একখানা পুরো পঞ্চাঙ্ক নাটকের সঙ্গে একখানা প্রহসন না হলে শ্রোতার মন ভরত না। আজকাল আড়াই ঘন্টা, বড় জোর তিন ঘন্টার বেশি অভিনয় হলে শ্রোতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়।