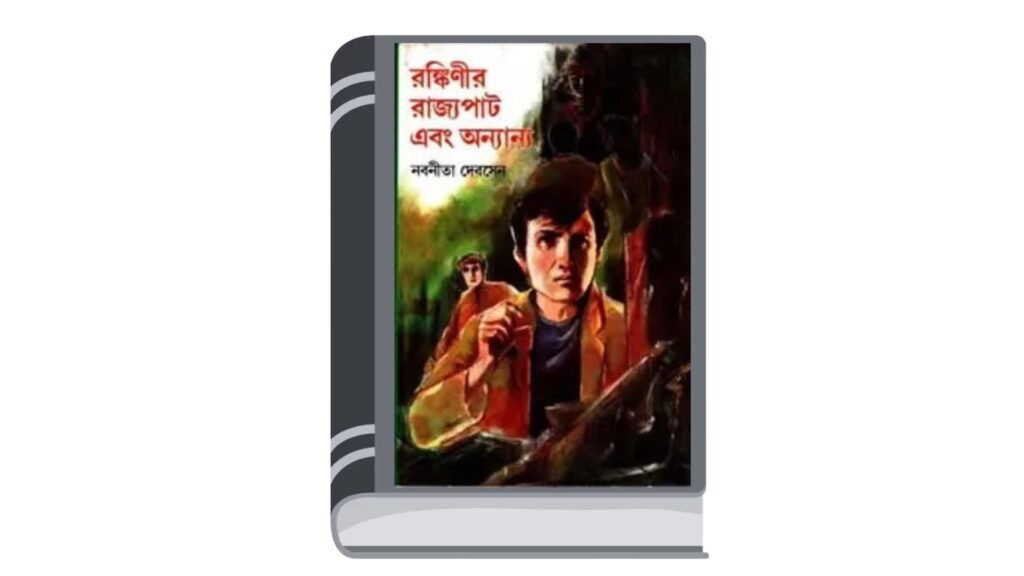দ্বিতীয় পর্ব : শালপিয়ালের বন
টুলকি
ঝাড়গ্রাম স্টেশনে কাকাবাবুদের টাটা সুমো ছিল এবং জিপগাড়ি নিয়ে শিবকাকাও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিল শুভ। সরোজকাকার ছেলে। একদম বাচ্চা, পুটুসেরই কাছাকাছি বয়েস হবে—কিন্তু দারুণ স্মার্ট। পুটুসের চেয়ে অল্প বড়—ক্লাশ ফাইভ। প্রথমে একটু একটু লজ্জা লজ্জা করছিল তার পরেই ভাব হয়ে যেতে কেবলই ধাঁধা জিজ্ঞেস করে। ওই সরোজকাকার ছেলে তো? অজস্র ধাঁধা জানে, বেশ মিষ্টি দেখতে, মেদিনীপুরে পড়ে। মনে হয় মেদিনীপুরটা মফঃস্বল হলেও শহরের মতনই। আমরা কলকাতাতে থাকি তো, বুঝতে পারি না। মনে করি কলকাতার বাইরে গেলে সবই বুঝি গ্রাম। কিন্তু তা তো নয়। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বহরমপুর, এসব তো শহর। মেদিনীপুর বেশ বড়সড় শহর বলেই মনে হচ্ছে। দুর্গাপুর, কি আসানসোলের মতন হবে বোধ হয়। আমরা শান্তিনিকেতন থেকে দুর্গাপুরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আসানসোলে, বার্নপুরে—টুলুমাসিদের বাড়িতে। বার্নপুরে খুব সুন্দর একটা গার্ডেন ছিল, একটা সাজানো পার্ক, রাত্রে আলো জ্বলে।
অবশ্য যেখানে এসেছি, এর কাছে কোনও পার্ক কোনও বাগান দাঁড়াতেই পারে না। প্রকৃতি এই অঞ্চলটাকে এত সুশ্রী করে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন। গাড়ির রাস্তার দু’ধারেই ঘন সবুজ শালবন। শালবনের মাঝখান দিয়ে কালো রাস্তায় পাতার ফাঁকে রোদ্দুর আছড়ে পড়ছে। রাস্তাটা আলোছায়ায় জালে জড়ানো। আমার এরকম রাস্তা খুব ভালো লাগে।
বুলটুর ‘এয়ার গান’ আনতে দেওয়া হয়নি বলে ও এখন ভয়ানক রেগে রয়েছে আমাদের সকলের ওপরে। আমিও মনে করি মা ডিড দ্য রাইট থিং।
কেন নির্দয় নিষ্ঠুরের মতো বন্দুক হাতে করে কারুর বনজঙ্গলে নিমন্ত্রণ রাখতে আসবে তুমি? পাখি শিকারের নেমন্তন্ন তো ছিল না, ছিল শুধু পিকনিকের। পিকনিক অহিংস, পাখি লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়া হিংস্র। বন্দুক টন্দুক এরকম শান্ত পরিবেশে একদম অচল। ও শুধু টেররিস্টদের হাতে মানায়। আর টেররিস্টদের মানায় না এই গ্রহের কোনোখানেই।
মা দারুণ লুচি আলুরদম আর হালুয়া এনেছেন। স্যান্ডউইচ স্পেশালিস্ট ছোটমা। হ্যাম অ্যান্ড চিজ স্যান্ডউইচ এনেছেন। পথে থেমে সেসব খাওয়া হবে। জেঠু বাবা—মা এবং ছোটমা নিজে লুচির দলে। বলটু, পুলকি, পুটুস এবং কাকুমণি স্যান্ডউইচের দলে—আমি দুদলেই! পথে থেমে এসব খাওয়া হবে। বুলটুর এসবে খুব উৎসাহ আছে অবশ্য। ফ্লাস্ক ভর্তি ঠাণ্ডা চকোলেট মিল্ক এসেছে। পুটুসের প্রিয়, আমাদেরও। জেঠুমণিরও। বাকিদের জন্য অন্য একটা ফ্লাস্কে গরম কফি। দুদিকেই শালবনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সত্যি অসম্ভব সুন্দর, শান্ত, এখানে এলে মনে হয় জগতে কোনো অশান্তি নেই, হিংসা নেই। অথচ এখানেও তো প্রচুর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটে। সন্ধ্যার পরে নাকি গাড়ি যেতেই দেয় না। পুলিশের এসকর্ট সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়ি যেতে পারে কনভয় করে—এই সব পথ দিয়ে। অথচ এখন দিনেদুপুরে কি অসাধারণ আবহাওয়া।
‘জনযুদ্ধ’ নামে নাকি সাধারণ গুণ্ডা বদমাশরাও এসব রাস্তায় ডাকাতি করে। শিবকাকা বলছেন, ওরা রাস্তার মাঝখানে গাছের গুঁড়ি ফেলে প্রাইভেটকার, এমনকি বাস পর্যন্ত আটকে দেয়। আর যাত্রীদের যথাসর্বস্ব লুটপাঠ করে নেয়। কখনও কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে টায়ার ফুটো করে দেয়। গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি, টেপ রেকর্ডার ঘড়িটরি তো বটেই। পরনের কাপড়জামা পর্যন্ত খুলে নেয়, এমন কি শীতের রাত্রে কনকনে ঠাণ্ডায় মানুষের গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত রাখে না ডাকাতগুলো। যেই করুক, লোকে বলে লোধারা করেছে। ওরা গরিব, ওরা খেতে পায় না। একটু খাবারের জন্য নাকি বিষাক্ত তীর মেরে খুন করে দিতে পারে। কিন্তু কেন? এত গরিব কেন?
এসব কথা শুনছি, আর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই নাকি আমাদের স্বাধীন দেশ।
পুলকি বলছে, ”দিদিভাই, আমাদের ফিরে গিয়েই লোধাদের সম্পর্কে পড়াশুনো করতে হবে।” ছোটমা বলেছিল, ”লোধা শুনলেই আমার তো চুনী কোটালের কথা মনে পড়ে। সে তো ছিল লোধাদের মেয়ে।” ওই চুনী কোটাল—ছোটমা যখন কলেজে তখন নাকি রোজ বেরুতো চুনী কোটালের ওপর অবিচারের কথা কাগজে।’ পুলকি আর আমি খুব worried এসব শুনে।
লোধাদের মধ্যেই বোধ হয় ওই শবরজাতিও পড়ে, যাদের নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী অনেক social work করেছেন। ওঁকে ওরা ওদের ‘মা’ বলে ডাকে শুনেছি। আমার আর পুলকির খুব ইচ্ছে একবার মহাশ্বেতা দেবীকে দেখতে যাবার। এখান থেকে ফিরেই চেষ্টা করব। কাকু নাকি ওঁর ছেলেকে চেনে। নবারুণ ভট্টাচার্য। কাকুই বলেছিল নিয়ে যাবে ওঁর কাছে, এবার যেতেই হবে। We can learn a lot about these লোধা শবর people from her—উনি বোধ হয় পুরুলিয়ার ওদিকে যেসব লোধারা থাকে, ওদের ‘মা’। এখান থেকে পুরুলিয়া খুব দূরে নয়—এইরকমই লালমাটি, কাঁকর পাথর, শালবন। ছোটো ছোটো টিলা। পুলকি বলছিল ওখানে ”ভালো পাহাড়” বলে একটা খুব সুন্দর রিসর্ট হয়েছে—একজন প্রবাসী বাঙালী কবির বানানো—তার সঙ্গে এই আদিবাসীদের development—ও জড়ানো আছে, education health etc. খুব জটিল একটা project মনে হয়।
এখানেও তেমনি কিছু করা যায়। অতটা জমি নিয়ে আমরা কী করব? এরা তো বলছে ওদের দিয়ে দিতে। বিক্রি করে দিতে। They are selling off the whole lot ours and theirs, সব জমিজমা বেচেবুচে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকবে। সকলেই মফঃস্বল ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতে চায়—মনে করে সেটাই উন্নতি। এখানে বাস করা নাকি খুব কঠিন হয়েছে সন্ত্রাসের জন্যে। ‘জনযুদ্ধ’ পার্টি তো আছেই। তারা সত্যি রাজনৈতিক বিদ্রোহী দল। আরও আছে চোরডাকাতের দল, যারা নিজেদের ওই ‘জনযুদ্ধ’ বলে চালাতে চায়। এরা আসলে কমন ক্রিমিন্যাল—শিবকাকা সব explain করছেন ওঁর নিজস্ব rough and tough, রুক্ষু শুক্ষু স্টাইলে। সাধারণ জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে এখনো ক্রাইম খুব বেড়েছে। বলতে বলতেই লক্ষ্য করি, গাড়িতে বন্দুক রয়েছে। জিপে বোধহয় আগে আগে পাহারাদারেরাই যাচ্ছে। শিবকাকা আমাদের সঙ্গে। ওটা নিশ্চয় ওঁর বন্দুক।
বুলটুও দেখেছে।
বুলটু লাফিয়ে উঠল—”ওটা রিয়্যাল গান? সত্যিকারের বন্দুক?”
শিবকাকা হেসে ফেললেন। ”এখানে কি খেলনার বন্দুক চলে রে ভাই? বন্দুকেরই খেলা চলছে যে সর্বক্ষণ!” শুনেই বুলটু অপ্রসন্ন চোখে মা’র দিকে তাকাল।
ভাবটা এই—কী? দেখলে তো? বন্দুকটা আনলে না—মা শান্তভাবে বললেন—”বুলটু তোমার airgun যে আনোনি, ভালোই করেছো—এসব জায়গায় সশস্ত্র হওয়াটাও বিপজ্জনক। নিরস্ত্র হওয়া আমাদের পক্ষে ভালোই।”
শিবকাকা বললেন, একদম ঠিক কথা। একবার নাকি সরোজকাকার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আসছিলেন—তাঁদের গাড়িটা শিবকাকাদের গাড়ির পিছু আসার কথা—কিন্তু অল্পবয়সীরা ছিল। তারা বলেছে তাড়াতাড়ি চালাও—ওরা এগিয়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে—গাড়ি এদিকে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। জঙ্গলমহল যাকে বলে—ওদের তখন ভয় হয়ে গেছে, ওরা দেখলো গাড়িতে বন্দুক দুটো নেই, কিন্তু তার খাপগুলো আছে।
ওরা করলো কি, খাপগুলোতে খবরের কাগজ ভরে, জানলার কাচের ওপর দিয়ে শুধু নলের ডগা দুটো বের করে রাখলো দুদিকে। বন্দুক দুটো তো সামনের গাড়িতে আছে যাদের ‘ফলো’ করে এদের যাবার কথা। এরা ভাবলো বন্দুকের নল বের করা আছে দেখলেই ডাকাতরা ভয় পাবে। রাত হয়ে গেছে—জন্তু জানোয়ার বেরুচ্ছে—যাই হোক ওরা তো পৌঁছে গেল ডাকাতের হাতে না পড়েই। কিন্তু পৌঁছানোর পরে সক্কলে ওদের খুব বকেছিলেন কেন ওরা নকল বন্দুকের নল উঁচিয়ে রেখেছিল! তখন ‘জনযুদ্ধ’ গোষ্ঠী তো বন্দুক সংগ্রহ করছে পুলিশ মারছে, জওয়ান মারছে, বন্দুক নিয়ে নেবে বলেই যারা আক্রমণ করছে—আর বোকার মতো তোমরা বন্দুক দেখিয়ে দেখিয়ে এলে? ওরা তোমাদের আক্রমণ করতোই, তারপরে বন্দুক নেই, ঠকে গেছে দেখলে, প্রাণে বাঁচতে না। ভাগ্যিস ওরা দেখতে পায়নি!
এই গল্পটা শুনে আমরা সবাই বুলটুর দিকে তাকালুম। বুলটু জানলা দিয়ে বনের শোভা নিরীক্ষণ করতে লাগলো।
আমাদের গাড়িতে বন্দুক আছে, কিন্তু প্রদর্শন করা অবস্থায় নেই। সামনের জিপ গাড়িতে নাকি বন্দুক আছে। এখানে এসব লাগে, আত্মরক্ষার জন্যে সকলেই সশস্ত্র থাকে বাড়িতে। ‘জনযুদ্ধ’ এখন ততটা বন্দুক কাড়ে না, ওদের যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র হয়ে গেছে বলে মনে হয়।
পুলকি
শিবমামা মানুষটাকে আমার সবচেয়ে কম পছন্দ হয়েছিল তিনজনের মধ্যে। বেশি কথা বলেন, বেশি বেশি স্মার্টনেস দেখান, উচ্চারণ কেমন অমার্জিত, চলন বলন সবই কেমন যেন। ওঁকে আমার ‘মামা’ ভাবতে ইচ্ছে করে না। কী করা, তিনিই এসেছেন আমাদের নিতে—শঙ্করমামার ওখানে কাজ আছে, আমাদের রিসিভ করবেন। আর সরোজমামার কালকে আসার কথা। উনি শনি—রবিবারে আসেন। কিন্তু মিতালীমামীমা শুভকে নিয়ে চলে এসেছেন, আমরা আসছি, তাই। দে আর অল ওয়েটিং ফর আস অ্যাট হোম।
শুভর সঙ্গে পুটুসের দিব্যি জমে গেছে। শুভ যে কেবল ধাঁধা বলে তা নয়, ও আবার ছড়া কেটে কথা বলে। যেমন পুটুস বলল—”এগুলো কী গাছ?”
উত্তরে শুভ বলল—
”এই বনের নাম শালবন,
ওই বনের নাম পিয়ালবন”।
—”পিয়ালবন? কই? কই? কোথায়?”
—”শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে
পিয়ালগাছ লুকিয়ে থাকে।”—
শুভর কথাবার্তা শুনে পুটুস কেন, আমরা তো সববাই থ’ হয়ে গেছি।
—”শুভ, তুমি এরকম ছড়া কাটতে শিখলে কার কাছে?”
ছোটমা আদর করে জিজ্ঞেস করতেই শুভ বলল—
—”কিল খাই চড় খাই
ছড়া কাটি ছড়া গাই।”
—”সে তো হল। কিন্তু শেখালো কে? তোমার টিচার কে?”
হেসে শুভ বলল,
”ছড়া কাটি ছড়া গাই
গুরুর নাম বলতে নাই!”
—সেকি, সেকি, সেকি?
শুভর ধাঁধাও খুব মজার মজার। কোনো কোনোটা বোঝা খুব দুষ্কর, মেজ মামীই কেবল ওর উত্তর দিতে পারেন, আমি বাবা পারি না। আমরা কেউ পারি না। শুভ বললো—
”তিন অক্ষর নাম আমার হই টক ফল প্রথম অক্ষর বাদ দিলে গাছের ডাল ধরি শেষে অক্ষর বাদ দিলে তোর পেট ভরি কী নাম আমার, তুই দু’মিনিটে বল।”
দুমিনিট তো দূরের কথা—আমরা তিন অক্ষরে তেঁতুল, আর আমড়া, এই দুটো ছাড়া টকফলই খুঁজে পেলুম না।
মেজমামী বললেন—”চালতা” ‘চা বাদ দিলে ‘লতা’, ‘তা’ বাদ দিলে ‘চাল’। শুভ খুব খুশি। মামী তখন বললেন, ”এই ধাঁধাটা তো আরও বাড়াতে পারা যায়। শেষ দুই অক্ষর বাদ দিলে—’চা’ হয়, তুমি নতুন ছড়া বানিয়ে ফ্যালো। ‘চা’ ঢুকিয়ে নাও।”
ভুরু কুঁচকে শুভ একটুক্ষণ ভাবলো? তারপর বললো,—”তিন অক্ষরে নাম মোর হই টক ফল প্রথম অক্ষর বাদ দিলে গাছের ডাল ধরি—
শেষ দু অক্ষর বাদ দিলে পাতায় গরম জল
শেষ অক্ষর বাদ দিলে তোর পেট ভরি—কী নাম আমার, তুই এক মিনিটে বল!”
এটা শুনে হই হই করে উঠলেন বড় মামু।
—”জিনিয়াস। জিনিয়াস! শুভ একটা জিনিয়াস!” মেজমামী, ছোটোমামীও খুব খুশি হলেন। শুভটা সত্যি খুব মজার। যেই বড়মামু ”জিনিয়াস”, বলে চেঁচাচ্ছেন শুভ বললো—
”জিনিয়াস” মিনিবাস।
নুন খাস, চিনি খাস।”
যেই সবাই হেসেছি, ও বলল—”আনি বানি জানি না জিনিয়াস মানি না!” আবার সববাই হেসে উঠলুম। শুভ তারপর বলল, ”জেঠুমণি, ‘জিনিয়াস’ মানে কী?” বুলটু ওকে শিখিয়ে দিয়েছে জেঠুমণি, মেজজেঠু, ছোটজেঠু বলতে। ওর বাড়িতে আছেন ওর জ্যাঠামশাই আর মেজজ্যাঠামশাই। জেঠু নেই কোনো।
—”জিনিয়াস মানে তুমি যা, তাই।”
—”যে ছড়া কাটতে পারে?” শুভর খুব সিরিয়াস মুখ।
—”শুধু ছড়াকাটা নয়। আরও অনেক রকমের জিনিয়াস হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, রবিশঙ্কর, অমর্ত্য সেন। সকলেই এঁরা জিনিয়াস।”
”জগদীশচন্দ্র বোস? সত্যজিৎ রায়?”
—”হ্যাঁ, ওঁরাও জিনিয়াস। ঠিক ধরেছো। এই তো বুঝে গেছ!”
—”তাহলে আমিও কেমন করে জিনিয়াস হবো? আমি তো কিছুই করিনি। ওঁরা প্রত্যেকে কত কী করেছেন। আমি তো ছোটো!” শুভ কাঁদোকাঁদো।
—”হ্যাঁ। একদিন নিশ্চয়ই হতে পারো। চেষ্টা করলেই তুমিও পারো ওঁদের মতো হতে। কিন্তু চেষ্টা করাটা খুব জরুরী। চেষ্টা করলেই দেখবে তুমি কী কী অবাক কাণ্ড ঘটাতে পারো এই পৃথিবীতে।”
শুভ চুপ করে শুনলো উত্তর দিল না।
খিদে পেয়ে গেছে সকলেরই। লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে শালবনেই একটা সুন্দর জায়গা দেখে গাড়ি থামানো হল। এখন জঙ্গলমহলেই আছি আমরা। লোধাশুলি মোড় থেকে ডানদিকে বেঁকে অবধি বড় বড় শালগাছ তার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সাঁওতালী গ্রাম—কীসব নাম—খুব সুইট, আমবনি, জামবনি, কলাবনি এইসব।
শালগাছের ফাঁকে মাটিটা খুব পরিষ্কার। লাল কাঁকড়ের পাথুরে মাটি, ধুলোকাদা নেই—আমরা শতরঞ্চি পেতে সবাই মিলে বসে পড়লুম, মেজমামী আর ছোটমা আমাদের লুচি, আলুরদম হালুয়া এবং স্যান্ডউইচ খাওয়ালেন, সুন্দর শালপাতার থালা এসেছিল কলকাতা থেকে। পাতাগুলো শালবনেই পড়ে রইলো আমরা যখন চলে গেলুম। বুলটু বলল, ”কে জানে, হয়তো এই বনেরই শালপাতা ওগুলো? আবার নিজের বনে ফিরে এলো!”—কথাটা কিছুই ভেবে বলেনি বুলটু। শালপাতা। আর শালবন—তাই দুটো মিলিয়ে দিয়েছে। আমার কিন্তু সত্যি সত্যি খুব ভালো লেগেছে ওর আইডিয়াটা। কোথায়, কোন পরদেশে চলে গিয়েছিল এই শুকনো শালপাতাগুলো, আবার নিজের ঘর বাড়িতেই ফিরে এসেছে! রি—ইউনিয়নের গল্প। এরকম তো ঘটছে এই মুহূর্তে আমাদেরও জীবনে—যে পরিবার টুকরো হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, পঞ্চাশ বছর পরে সেই পরিবারে আবার জোড়াতালি। তাপ্পি পড়লো।
বুলটু
স্টেশন থেকে আসবার পথে something happened today, which I didn’t like! শালবন দিয়ে আসবার সময়ে আমি স্পষ্ট গুলির শব্দ শুনেছি। প্রথমে একটা, তারপর দুটো। অনেক দূরে হতে পারে, কিন্তু গুলির শব্দ।
যেই বলছি—”বাবা, ঐ শোনো গুলির শব্দ!” শিবকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, ”আরে না, না, এখানে বন্দুকের শব্দ আসবে কোত্থেকে? তুমি ভুল শুনেছো।”
কাকু, দিদিভাই আর ছোটমাও বলল সঙ্গে সঙ্গে ওরাও শুনেছে। বাকিরা অন্যমনস্ক—শুনেছে সকলেই, কিন্তু ওটা যে গুলিরই আওয়াজ, না অন্য কিছুর আওয়াজ, অত জানে না।
শিবকাকা ভীষণ জবরদস্তি করতে থাকলেন যে, গুলির আওয়াজ হওয়া অসম্ভব।
আমার অবাক লাগছে—যদি হয়ই, তাতে কী? কলকাতাতে কি গুলির আওয়াজ শোনা যায় না? গুলির আওয়াজ ওটা ছিল না—এটা প্রমাণ করেই বা ওঁর কী উপকার? আর যদি বন্দুকের আওয়াজ হয়ও, তাতেই বা ওঁর কী ক্ষতি? নাথিং টু ডু উইথ আস অ্যাট অল!
শিবকাকার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, হি ওয়াজ ডিফেনডিং দ্য বোমা—গুলির শব্দ অন এ পার্সোনাল লেভেল বাট হোয়াই? নো বডি ওয়াজ বদার্ড অ্যাবাউট ইট। বনজঙ্গলে তো হতেই পারে গোলাগুলির শব্দ। ‘পোচার’ ঢুকেছে হয় তো? চোরাশিকারী!
সত্যি দারুণ জায়গাটা কিন্তু! বোথ বিউটিফুল অ্যান্ড মিস্টিরিয়াস। কলকাতাতে বসে ঠিক আন্দাজ পাওয়া যায়নি কত সুন্দর এই জঙ্গলমহল। মা ঠিকই বলেছিলেন এমন সুন্দর জায়গাতে গুলিগোলা বন্দুক চালানো খুব ugly—খুব কুৎসিত হত। এয়ারগান আনিনি ভালোই হয়েছে। ওই গুলির আওয়াজটা খুব ugly লাগলো। এখানে এসে তো আমরা সবাই এক্কেবারে spell bound! বাবা, জেঠুমণিরাও ভাবতে পারেননি এটা কতটা luxurious, কতটা ‘জমিদারী চাল’—এরই জায়গাতে আছে।—এখানে বড় বড় ইঁদারা খুঁড়ে এদের জলের সাপ্লাই—কিন্তু মস্ত একটা দিঘিও আছে এদের—নাম মনোমোহিনী। কি সুন্দর চওড়া বাঁধানো ঘাট। পাড়ার মেয়েরা জল নিয়ে যায় স্নান করে। আমাদের সুইমিং করতে অ্যালাউ করল—কিন্তু কেউ নামিনি, ভয়ে। অচেনা জল, অচেনা জায়গা, তাছাড়া কেউ তো সুইমিং কস্ট্যুম আনিনি। কিন্তু ঘাটেই স্নান করেছি আমরা। মেয়েরা fully clothed.—খুব মজা হয়েছে। আমি দিব্যি হাফপ্যান্ট পরে খালিগায়ে নেমে গেছি। পুটুসকে ছোটমা তো নামতেই দেয়নি। শুধু দিদিভাই আর পুলকি ওরা শর্টস আর গেঞ্জি পরে স্নান করল। তারপর বাবা—জেঠু—কাকু হৈ হৈ করে জলে নেমে গেলেন। মা, ছোটমা ওদের বাড়ির ‘কলঘরে’, অর্থাৎ বাথরুমে তোলা জলে স্নান করলেন। দিদিভাই গুল মেরেছিল, এখানে টয়লেট নেই—মাঠে যেতে হবে। খুব ভয়ে ভয়ে ছিল পুলকি। আমার অবশ্য কিছুই লাগেনি—if every one else is going, why can’t I? পুলকিটাই ঘাবড়ে গেছিল। কিন্তু এসে দেখছি নো প্রবলেম। দিব্যি টয়লেট আছে, শুধুই ইন্ডিয়ান স্টাইল, ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেট নেই। এইটুকু অসুবিধে। দিদিটা ইচ্ছে করে ভয় দেখিয়েছিল। নাকি সত্যিই ভেবেছিল, গ্রামট্রাম তো, জঙ্গলমহল নাম। টয়লেট থাকবে কেমন করে? যাই হোক উই আর রিল্যাক্সড। এরা রিয়্যালি নাইস পিপল। আমাদের তিনটে ভাইবোন আছে এখানে—বাসন্তী ইজ মাই এজ, এবারে স্কুল ফাইনাল দিয়েছে। ওর নাম জিজ্ঞেস করলে বলে বাসন্তী লাহিড়ী। অথচ ওকে সবাই ডাকে ‘শালফুল’ বলে। অনেক বেশি সুইট নাম—একদম নতুন। আর শালফুল তো আমরা দেখিওনি। Exotic ফুলের নাম, not like চাপা, জবা or Rose—শালফুলকে দেখতে খুব সুন্দর। But she is very shy দিদিভাই। পুলকি খুব চেষ্টা করছে ভাব করতে—I’m keeping my distance —একটা কুচো বাচ্চা আছে। লালা, সে কথা বলে না। সেও খুব shy মনে হচ্ছে। কিন্তু শুভ has made up for all these—যা মজার ছেলে। I’m admiring him like anything—ছড়া কেটে কেটে কথা বলে, আর endless supply of ধাঁধা আছে ওর কাছে। পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছি, শুভ বললো—
”দিঘির জলে, নাইবে বলে, সবাই চলে।” ছোটমা পুটুসকে ‘কলঘরে’ চান করাতে নিয়ে গেলেন বলে শুভ ছড়া কাটলো—”পুটুস! কলঘরেতে খুটুস, খুটুস/আমরা সবাই দিঘির জলে/ঝাপুস ঝুপুস ঝাপুস ঝুপুস”—শুনে ছোটমা হেসে বললেন, ”ঠিক আছে, কাল ও ঝাপুস ঝুপুস করবে’খন।”—
আমারও খুব ইচ্ছে করছে শুভর মতো করে ছড়া কাটতে but I can’t—may be পুলকি can—she is poet—পুলকি কবিতা টবিতা লেখে ও হয়তো পারবে—
আমাদের আরও দুজন cousin আছে মুন্টি আর বান্টি। কিন্তু ওরা আসেনি, ওরা এদিকে থাকে না। একজন বাঙ্গালোরে, আরেকজন ইন্দোরে। আমাদের দুজন পিসিমা আছেন, twin পিসিমা, গঙ্গা—যমুনা,—মুন্টি গঙ্গা পিসিমার মেয়ে, আর বান্টি যমুনা পিসিমার ছেলে। পিসিমারাও আসেননি। ওরা আমাদের চেয়ে ছোট, সিক্স সেভেনে পড়ে। ওই শুভই তাদের গল্প করছিল।
বাসন্তী, that is শালফুল আমারই বয়সী অথচ আমার সঙ্গে একদম কথা বলতে চায় না। ও সালোয়ার কামিজ পরে। জীনস, ট্রাউজারস নাকি পরেনি কখনো। দিদিভাই আর পুলকির জামা কাপড় দেখে ওর পছন্দ হয়নি মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করছিল দিদিভাইকে—”তুমি শাড়ি পরো না? কলেজে এইরকম কাপড়জামা পরেই যাও?”
এখানটায় ভীষণ rural mentality গ্রামই তো। গ্রামের মতন তো হবেই। আমি ইয়ার্কি মেরে বাসন্তীকে বললুম—”তেরা নাম কেয়া হ্যায়, বাসন্তী?” সবাই জানে শোলেতে আমিতাভ বচ্চনের ডায়লগ। মেয়েটা এত ক্যাবলা, কিছু বুঝল না। খেতে বসে কী জোরজবরদস্তি! ছাড়বেই না কাউকে সব কিছু ডবল ডবল করে থালাতে দিয়ে দিচ্ছে—কি ভীষণ waste! অথচ শুনলুম এখানকার লোধারা নাকি খাবারের জন্যে মানুষ খুন করে। মাছটার test দারুণ। খুব fresh। সবাই খুব ভালবাসছে শুনে শঙ্করকাকা বললেন ওগুলো সব বাড়ির পুকুরের মাছ, তাই অত fresh, কাল আমরাও যাবো মাছ ধরা দেখতে। ভাবা যায়? মাছটা ধরছে। ধরে এনে রান্না করে খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। আমি কখনও দেখিনি বাড়ির পুকুরের মাছ ধরে এনে সেটা দিয়ে ভাত খাওয়া। মাছ তো বাজার থেকে আসে। ”গঙ্গার ইলিশ” ও নাকি cold storage থেকে বের করা হয়। এখানে সবই fresh, fresh milk, fresh vegetables, fresh fruits, fresh air—no pollution—এমন সুন্দর জায়গায় জমিজমা আছে আমাদের? কেন বেচে দেবো? আমরা বেচবো না—আমি জেঠুমণিকে বলবো—আমাদের ইচ্ছে নয় জমি বিক্রি করা। এই তো জীবনে প্রথম আমরা জমি, গাছ, পুকুর এইসব দেখছি,—নিজেদের জমি! Why should we part with it? টুলকি—পুলকিরও তাই ইচ্ছে। একটা charming dreamland—a windfall—ওরাও চায় না এটা বিক্রি হয়ে যাক। আমরা অবশ্য বাবা—মার সঙ্গে কথা বলে দেখিনি—আগে তো সব মাপজোক হবে, আমাদের তার মধ্যে কোনো role নেই। আমরা পেয়ারাবাগানে, আতাবাগানে ঘুরতে যাব—আর? কাজুবাদামের বনে! এখানে প্রচণ্ড কাজুবাদাম হয়—ওরা যে আমাদের জন্য নিয়ে গিয়েছিল না, এক ব্যাগভর্তি কাজু, সেটা এখানকার। They grow it here—আমাদেরও নাকি নিজেদের ভাগেও কাজুবাদামের বন পড়েছে খানিকটা—শঙ্করকাকা বলছিল,—শিবকাকা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ”আগে জরিপ হোক”—ওর বোধ হয় ওটা দেবার ইচ্ছে নেই। I don’t like that man. আমরা বিকেলে বেড়াতে যাব—আমাদের নিয়ে যাবে ধনিয়া—সে এখানে খেতে কাজ করে, আমাদেরই বয়সী হবে। ধনিয়া মাহাতো। মাহাতোরা নাকি চাষবাস করে। ওদের জমিজমা থাকে, ওরা লোধাদের মতো দীনদরিদ্র হয় না। খুব নাকি ধূর্ত, চতুর হয় মাহাতোরা। শিবকাকা বলছিলেন। ধনিয়ার বাবা—ঠাকুর্দা সকলেই এবাড়ির খেতখামারে কাজ করেছে। এখনও করে। ওর কাকা, দাদারা সবাই মাহাতোদের ধূর্ত বলে নাম আছে এখানে। বাবা বললেন, বাঙালী আরও চতুর আর ধূর্ত। কি জানি?
ওঃ আসল কথাই বলা হয়নি।
We met our grandmother! আমাদের নতুন ঠাকুমার সঙ্গে আলাপ হল। Quite something! She looks much younger than her years—ওঁকে দেখতে বেশ young মতন—বুড়ি ঠাকুমার মতো একটুও না। রঙিন শাড়ি পরা, কালো চুলের খোঁপাতে একটা হলুদ ফুল গোঁজা। কি সুন্দর টল ফিগার—স্ট্যাচুয়েস্ক শাড়িটা অবশ্য শান্তিনিকেতনের মেঝেনদের মতো করে পরেন—ওঁকে দেখতেও! অনেকটা যেমন মেঝেনদেরই মতো। গড়নটা বাঙালীদের মতো নয়। She is very pretty through খুব সুন্দর দেখতে। আমরা তো আমাদের ঠাকুমাকে দেখে অবাক। ইঁদারা থেকে পেতলের বালতি করে জল তুলছিলেন। আমরা সবাই গিয়ে প্রণাম করলুম। শঙ্করকাকার, শিবকাকার মতোই রংটা কালো—কিন্তু She is pretty—মা—ছোটমাও বলছিলেন—ওঁর মুখখানা খুব মিষ্টি, ফিগারটাও দারুণ। বাংলাভাষা বলেন, সাঁওতালী accent—এ। আমাদের সবাইকেই খুব আদর করছেন উনি। জেঠুমণির জ্যাঠাইমা—সোজা কথা!
টুলকি
সোজা কথা!
কথায় কথায় ছড়া বানিয়ে ফেলছে এইটুকুনি বাচ্চা।
”বিকেলবেলায় কোথায় যাবো?
যেখানে গেলে পেয়ারা পাবো।”
”পেয়ারা পেড়ে করবো কী?
পেটের ভেতর ভরবো কি?”
এইসব বলছে। আর ধাঁধা। পুলকিকে ধরেছে ধাঁধার উত্তরের জন্য। শুভ জিজ্ঞেস করেছিল।
”—ভগবানের কেমন কল
গাছের মাথায় মিঠে জল”—
পুলকি যেই বলেছে ”ডাব!” ব্যাস।
Next ধাঁধা বলতে হবে। —বলো দেখি।
”ভগবানের এমন ভুল?
মাথা থাকতে মুখে চুল?”
উত্তর, ”গোঁফদাড়ি”—এবার বুলটু পেরেছিল—
কিন্তু পরেরটাতে হেরে গেল। পারল না।
”তিন অক্ষরে নামটি মোর মাটির নিচে বাড়ি।
শেষ অক্ষর ছেঁটে দিলে গাছে গাছে ঝুলি।
মাঝের অক্ষর ছেঁটে দিলে বাতাসে বুক ফুলি।
প্রথম অক্ষর কেটে দিলে ধপাস করে পড়ি।”
পুলকি ভেবে ভেবে এটাও বলতে পেরেছে—
—”পাতাল।” পাতা। পাল। তাল। কিন্ত শুভ এত স্মার্ট, এবার নিজে নিজেই বলল—”কিন্তু এটাকেও বড় করা যায়। সেই ‘চা’য়ের মতো, ‘পা’ হয়। দেখবে? দাঁড়াও ভাবছি।”—তারপরে নতুন ধাঁধা তৈরি হল—”শেষ দু’অক্ষর বাদ দিলেই ফের দাঁড়িয়ে পড়ি।” নতুন করে শেষ লাইন যুক্ত হল ধাঁধাতে।
উত্তর। ”পা”। মা এবারে খুব impressed. চটপট শিখে গেছে নতুন angle টা—
—আমিও খুবই impressed, খুব proudও, আমাদেরই ভাই তো। বড় হয়ে ও একটা স্পেশাল কেউ হবেই। হি ইজ ওনলি ইলেভন। এই বয়েসেই এত স্মার্ট!
জেঠুমণি—বাবা—কাকুমণিরা পিসেমশাইয়ের দেরিতে আসার জন্যে একটু বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছেন। ওঁরা চান সব কিছু clear থাকুক গোড়া থেকেই। পিসিমণির cell-এ ফোন করছিলেন।
কিন্তু ওঁদের পাঁচজনকে একসঙ্গে গিয়ে নতুন ঠাকুমা (ঐ নামেই ডাকা হবে নতুন ঠাকুমাকে)—কে ”জ্যাঠাইমা” বলে প্রণাম করতে দেখাটা একটা সারা জীবনের মনে রাখার মতো দৃশ্য। নতুন ঠাকুমাও ওঁদের চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। হাতের জলভরা বালতি নামিয়ে রেখে। খালি পা। পায়ে রুপোর মল। কানে একজোড়া হীরের ফুল। ঝকঝক করছে। হাতে মোটা সোনার বালা, গলায় মোটা সোনার বিছে হার। উনি কেন ইঁদারা থেকে পেতলের বালতি নিয়ে জল তুলছেন? আর কেউ নেই? স্নান করবেন, তাই। নিজের স্নানের জল এঁরা নিজেরাই তুলে নেন—এটাই দস্তুর। শুনে আমরা অবাক। এতগুলো কাজের লোক থাকতেও? মার, ছোটমার স্নানের জল অবশ্য এরাই তুলে দিয়েছে। ওঁদের তুলতে বলেনি। তিনবেলাই বারান্দায় চাটাই পেতে বসে পেতলের থালায় খাওয়া। শালপাতায় নয়। পেতলের থালা—গেলাস সব যেন সোনার মতো ঝকঝকে—মা বললেন, পেতল হয়তো নয়, কাঁসার বাসন হতে পারে।—কিন্তু বোঝা শক্ত। পেতল নয় সেটা বোঝা গেল, যখন পাতে টক দই দিল, তেঁতুলের আচার দিল। পেতলের পাত্রে এসব দিলে নাকি কলঙ্ক ধরে যায়। খাওয়া যায় না। আলাদা করে মাটির পাত্রে দিতে হয়। এখানে এসে বুঝতে পারছি গ্রাম্য হলেও এখানে অর্থের অনটন নেই—এঁরা নিজের হাতে কাজকর্ম করেন সেটা পছন্দ করেন বলেই। লোক নেই বলে নয়। মাঠে খেতে বাগানে বহু আদিবাসী লোক খাটছে এদের হয়ে। স্ত্রী—পুরুষ দুই—ই সমানতালে খাটে দেখছি এখানে। কি সুন্দর দেখতে এদের।
হঠাৎ পুলকি ঠাকুমাকেই জিজ্ঞেস করল—”আপনাকে কী বলে ডাকব? নতুন ঠাকুমা, না তিলফুল—ঠাকুমা? কেননা আমার দুটোই ভালো লাগছে।” উত্তরে উনি কি বললেন? উনি বললেন, ‘ঠাকুমাটা ছেড়ে দাও। আমার নাম তিলফুল। নাম ধরে তো কেউ আর ডাকে না—তোমরা ডাকবে তিলফুল বলেই। ছেলেবউ তো নাম ধরতে পারে না, ওরা ডাকুক জ্যাঠাইমা। তোমরা তো নাতিনাতিনী আমার ইয়ারবন্ধু। নাম ধরেই ডাকবে।” খুব আশ্চর্য মানুষটি। এখানে নাতিনাতনীরা কিন্তু ডাকে দাদী। নাম ধরে নয়। ঠাকুমাও নয়। আরও চেনা বাকি ছিল। খুব ভালো রান্না করতে পারেন। আমাদের সকলের জন্যে হরিণের মাংস রান্না করলেন। দু’দিন আগে হরিণ মেরে তার মাংস বাসি করা হয়েছে, তারপর রান্না। বাসি করে রান্না করলে নাকি অনেক বেশি স্বাদু হয় হরিণের মাংস। হরিণ মারা ব্যাপারটা এত নৃশংস এবং এত আপত্তিকর যে পুলকি আর আমি খেতেই পারলুম না। বুলটু বলল দারুণ খেতে। কারিটা অবশ্য মা আমাদের জোর করেই ভাত দিয়ে মেখে খাইয়েছিলেন। অপূর্ব কারি হয়েছিল। নতুন ঠাকুর্দা made the right choise সন্ন্যাস যদি ভাঙতেই হয় তো এমন মেয়েদের জন্যেই ভাঙা ভালো। মুনিঋষিরা যেমন তপস্যা ভাঙতেন। ব্যাপারটা জানতে হবে। বাবার জ্যাঠামশাই
১। কিসের জন্যে ঘর ছেড়েছিলেন? ধর্মের জন্য নয়। সন্ন্যাসের জন্য নয়। নতুন ঠাকুমাকে বিয়ে করবার জন্যেও নয়। তবে কিসের জন্য?
২। আর এখানে তিনি এলেন কেমন করে? এমন রাজ্যপাট প্রতিষ্ঠাই বা করলেন কীভাবে?
৩। নতুন ঠাকুমাকে বিয়ে করার পিছনে কী ছিল? ছিলেন তো হিমালয়ে। এলেন কেমন করে এই রাঙামাটির দেশে?
৪। এত কাছে রইলেন, একবারও গেলেন না ছোটভাইদের কাছে? সেটা অবশ্য চক্ষুলজ্জার দোষ হতে পারে।—”বিয়ে করেছি, সন্ন্যাস ছেড়েছি, গৃহী হয়েছি”, এসব খবর দিতে হয়তো তাঁর লজ্জা করেছিল।
৫। কিন্তু মার কাছেও প্রণাম করতে গেলেন না বৌ নিয়ে? বিয়ে তো ওঁর একটাই, বৌ তো একটাই। লজ্জার কী আছে? কর্তামা নিশ্চয় খুব খুশিই হতেন। তবে হ্যাঁ, যখন বিয়েটা করেছেন, তখন হয়তো কর্তামা আর নেই।
৬। কিন্তু এতবড় সংসার, এত লোকজন, এত জমিজমা, বাড়ি দেখেই বোঝা যায় বেশ ধনী লোক, এতসব উনি পেলেন কোথায়? উনি তো সন্ন্যাসী, টাকাকড়ি তো ছিল না, যে জলের দরে হলেও, প্রপার্টি কিনবেন। কোথা থেকে এল এত সম্পত্তি? V.Imp.question.
৭। ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী—এদের target খুব সহজেই হতে পারবে এরা। কিন্তু এরাও সর্বদা prepared—কখনও ওদের অন্যমনস্ক ধরতে পারবে না —as long as that শিবকাকা is their ready to jump—sharp quick like a wolf—জানি না কেন এই তুলনাটা মনে এল।
পেয়ারাবাগানে যাবার জন্যে পুটুস সবচেয়ে ব্যস্ত, কেননা ঐ একটাই গাছ, যাতে পুটুস চড়তে পারে। ছোটমা আমাকে বলে দিয়েছে পুটুসকে আগলাতে। জ্বর থেকে উঠেছে বলে।
শালফুল মেয়েটা খুব অদ্ভুত। ও সবে স্কুল ফাইনাল দিয়েছে, ছেলেমানুষ মেয়ে, বুলটুর সমান—অথচ হাবভাব যেন বড় ভারিক্কি। দেখতেও বেশ ভারিক্কি—খুব মিষ্টি মুখ, ওর মায়ের মতো। বড় কাকিমা বেশ গোলগাল বাঙালী মহিলা। পান জর্দা খান, হাসি হাসি মুখ, সাধারণ বাঙালী করে শাড়ি পরেন। ওঁরই কোলে ছোটো একটি ছেলে আছে। লালা—লালার বয়েস পাঁচ। শালফুলের ভাবখানা যেন সে—ই লালার মা। ওদের মা—ই বাড়ির গিন্নি—রান্নাঘরটা তিনিই দেখেন। ঠাকুমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।
লালাও থাকে তাঁর সঙ্গে। লালাটা খুব রোগা, ছোট্ট, লাজুক, কিন্তু সুইট দেখতে। পুটুসের সঙ্গে অল্প অল্প ভাব হয়েছে। শিবকাকার বৌ নেই। তিনি নাকি বাপের বাড়িতেই থাকেন, ধানবাদে। এখানে আসেন না। শিবকাকারও যাওয়া আসা নেই শ্বশুরবাড়িতে। আর সরোজকাকার বৌ মিতালী কাকিমা মেদিনীপুরের মিশন স্কুলে ফিজিক্স পড়ান। একদম আমাদের মায়ের মতোই শহুরে মেয়ে—তিনিই শুভর মা।
মিতালী কাকিমাকে ছোট কাকিমা বলতে বলা হচ্ছে কিন্তু আমরা অন্য কোনও নাম ভাবছি। পুটুস বলল—কুট্টি কাকিমা বললে কী হয়? ওর বন্ধু বুলার কুট্টিমাসি আছে। কুট্টিটা মন্দ না। সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে। মিতালী কাকিমা, সরোজকাকা—ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও কালচারাল ডিফারেন্স নেই। কিন্তু নতুন ঠাকুমা, শঙ্করকাকা, শিবকাকার সঙ্গে এমনকি বড়কাকিমার সঙ্গেও—আছে তফাত, কিছু কিছু। তফাতটা আমার অবশ্য ভালোই লাগছে। সবাই একরকম কেন হবো? অন্য অন্য রকমের হওয়াই তো ভালো। বেশ একগুচ্ছ রঙিন ফুলের তোড়ার মতো, কালারফুল ফ্যামিলি। সবাই মিলে একগুচ্ছ বোরিং রজনীগন্ধা হয়ে কীসের মজা?
টুলকি
আমরা চিলকিগড় বেড়াতে যাচ্ছি।
মা, ছোটমা যাচ্ছেন না, কিন্তু শালফুলের যাওয়াটা ‘ওকে’ করিয়ে দিয়েছেন। ও খুব খুশি হয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। লালা যাচ্ছে না। আমরা পাঁচজন, না, ছ’জন যাচ্ছি। সঙ্গে ধনিয়া আছে, আর ড্রাইভার সুখরামজী।
চিলকিগড়ের একটা হিস্ট্রি আছে।
কাকুরও ইচ্ছে ছিল যাবে। ক্যামেরা নিয়ে—ওখানে কাছাকাছি অনেক দেখবার জায়গা আছে। কিন্তু কাকু—ছোটোমা—বাবা—মা—জেঠুমণি—সরোজকাকা—কুট্টিকাকিমারা নিজেদের একটা প্ল্যান করেছেন—শিবকাকার বড় গাড়ি তাঁদের নিয়ে যাবে—সরোজকাকাদের একটা কী যেন প্রজেক্ট আছে, সেটা দেখতে যাচ্ছেন।
আমরা বেলা থাকতে থাকতে বেরুচ্ছি—জঙ্গলমহলে সন্ধ্যা নামবার আগেই ফিরে আসতে হবে—শঙ্করকাকার স্ট্রিক ইনস্ট্রাকশন আছে সুখরামজীকে। সূর্যডোবা চলবে না। সবকিছু দেখা হোক না হোক বাড়িতে ঢুকে পড়তে হবে। বাড়ি ফিরে এসে সূর্যাস্ত দর্শন করতে হবে—বাড়ির বাইরে কক্ষনো নয়।
শালডুংরি থেকে বেশি দূর নয় জামবনি। আর জামবনি থেকে আর একটুখানি যেতে হবে ডুলুং নদী পার হয়ে। শালবনের ভেতর দিয়ে, চিলকিগড়ের রাস্তা। এই চিলকিগড় জামবনির রাজাদের গড়, মানে কেল্লা। ডুলুং নদীর পাড়ে। একটা টিলার ওপরে চিলকিগড়। এই জঙ্গলমহল তাঁরাই শাসন করে এসেছেন। বছরের পর বছর। কিন্তু এঁরা কেউ এখানকার লোকাল লোক ছিলেন না—বনবাসী আদিবাসী সাঁওতাল, লোধা, শবর, মাহাতোদের কেউ নন রাজারা।—তাঁরা নিজেদের বংশতালিকায় নিজেদের বিদেশী বলে দাবি করেন, সকলেই রাজপুতানার লোক—স্থানীয় আদিবাসী জংলী মানুষ নন তাঁরা কেউ—এবং রাজবংশের প্রমাণ হিসেবে নিজেদের নামের সঙ্গে সিংহ যোগ করেন। এই অঞ্চলে অনেক রাজা, রাজবংশও একাধিক—কিন্তু প্রত্যেকেরই বংশলতিকার মূল গল্পটি এক।
এসব গল্প আমাদের কে বলেছে? ড্রাইভার সুখরামজী তিনি এখানকারই মানুষ। একজন মানুষ বনপথে যাচ্ছিল তীর্থ করতে পুরীতে শ্রীক্ষেত্রে পুণ্যলাভ করতে। যাত্রাপথের মধ্যেই হঠাৎ ঘটনাচক্রে রাজসিংহাসনে বসে গেল। রাজার হাতি নতুন রাজা খুঁজতে বেরিয়েছিল, এই তীর্থযাত্রীকে ধরে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এইভাবে রাজ্য পেলেন চিলকিগড়ের রাজা। ধলভূম, সিংভূমেও এইরকমই সব গল্প আছে, সুখরামজী বললেন, কিংবদন্তী শুনতে আমার খুব ভালো লাগে—অনেক কিছু জানাবোঝা যায়, একটা অঞ্চলের চরিত্র চেনা যায় প্রবাদ—প্রবচন আর কিংবদন্তী থেকে।
আমি মাঝে মাঝে ভাবছি হিস্ট্রি ছেড়ে দিয়ে অ্যানথ্রপলজি পড়তে ভর্তি হব। কিন্তু ইজিপ্টোলজিস্ট হতে গেলে নিশ্চয় হিস্ট্রি এবং অ্যানথ্রপলজি দুটো ভালো করে পড়তে হবে। এসব কথা বলছি, পুলকি হঠাৎ বলল—”তুই খালি ঈজিপ্ট ঈজিপ্ট করিস কেন রে দিদিভাই? আমাদের দেশের ঐতিহ্য কি কম ইম্পর্ট্যান্ট? কতটুকু জানিস তুই ভারতবর্ষের ইতিহাস? ”ইন্ডিয়ার মেয়ে, ইন্ডোলজি জানবি না, ঈজিপ্টোলজি পড়বি!” এই জঙ্গলমহলে এসে আমার সত্যি মনে হচ্ছে ”বিপুলা এ ধরণীর কতটুকু জানি?”
এখানে যে কতরকমের নতুন জিনিস আবিষ্কার করছি! পুলকি হয়তো ঠিকই বলেছে, আমি ঈজিপ্ট নিয়ে পড়াশুনো করবার আগে এনশ্যেন্ট ইনডিয়ান হিস্ট্রি খানিকটা জেনে নিলে পারি। কিন্তু এই ট্রাইবাল কালচারের জন্যে অ্যানথ্রপলজি পড়া ভিন্ন গতি নেই। খুব দুঃখী চেহারা হয়েছে গড়টার। এককালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে চুয়াড় বিদ্রোহ হয়েছিল, তার কেন্দ্র ছিল এই জঙ্গলমহল। এখানে এই চিলকিগড়ের গোটা আবহাওয়াটাই, কেমন থমথমে। নিস্তব্ধ। কেমন গা ছমছম করা। ঐ যে, নরবলি হতো, গা ছমছম করবে না?
সুখরামজী প্রচুর গল্প জানেন। ওই কপালে রাজচিহ্ন দেখে হাতি ধরে নিয়ে গিয়ে রাজা করে দেওয়ার গল্পটাই শুধু নয়—এই বনে পথ হারালে, কপালে বলির পশুর চিহ্ন দেখে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলিও দেওয়া হত রঙ্কিণীদেবীর সামনে। চিলকিগড়ের দেবী সাবিত্রী। তাঁর মন্দির আছে। আর মন্দির আছে কনকদুর্গার। দেবীদের মধ্যে উনিই এখানে সবচেয়ে বড়। বনদেবীও বটেন, রাজবাড়ির কুলদেবতাও বটেন। তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্করী রঙ্কিণীদেবী; তাঁর আশীর্বাদে ভিখারি রাজা হয়। তাঁর অভিসম্পাতে রাজা ভিখিরি হন। তাই নরবলিটা প্রধানত তাঁর সামনেই হত—তিনি রাখলে আছি, না রাখলেই গেছি। দারুণ জাগ্রতদেবী রঙ্কিণী—এখন আর নরবলি হয় না। তবু পশুবলি হয়। কনকদুর্গার মন্দির দেখে আমরা নেমে আসছি, সূর্য যেন পশ্চিমে ঢলে পড়ছে? কনকদুর্গা নাম, কেননা এই দুর্গামূর্তিটি সোনার গয়নায় ঢাকা। কিন্তু কেউ ছুঁতে সাহস করে না—ডাকাতরা জানে স্পর্শমাত্রেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে কালকেউটে—ছোবল মারবে একেবারে মাথায়। কোনো ওঝা আর সে বিষ নামাতে পারবে না। কালকেউটের গর্তে রোজ দুধ ঢালা হয়—এবং প্রায়ই খাদ্যও রেখে আসা হয়—ডিম, মুরগি, মাংসের টুকরো। শালবনের একটা জায়গা একটু সাফসুতরো করে নিয়ে। সেখানে রঙ্কিণীর মন্দির করা হয়েছে। মন্দির মানে একটা শালগাছের গুঁড়ির কাছে এক ঢিবিতে মাটির তৈরি টেরাকোটার হাতিঘোড়া মানত দেওয়া হয়েছে। ওটাই রঙ্কিণীদেবীর মন্দির। সেখানে একটা টাটকা রক্তমাখা হাড়িকাঠ আছে। যখনই যাও দেখবে তাতে টাটকা রক্ত লেগে আছে, অথচ গ্রামের কেউ ওখানে পশুবলি দেয়নি অনেক বছর। ওরা বলে রঙ্কিণীদেবী নাকি নিজের বলি নিজেই ধরে আনেন। মানুষকে এনে দিতে হয় না। বেশ, আত্মনির্ভরতা সব সময়েই ভালো। দেবদেবীদের পক্ষে তো সেইটেই স্বাভাবিক। হোয়াই শুড দে ডিপেন্ড অন আস? মরট্যাল বিইংস?
বুলটু
আমি আমার ডিজিটাল ক্যামেরাটা নিয়েছি। পুলকি রাগ করছে খুব, পিসিমণি ওকে ভিডিওক্যামেরাটা দেয়নি বলে। কাল পিসিমণি ওটা সঙ্গে আনবে। তখন পুলকি ছবি তুলবে।
ডুলুং নদীটা ভারি সুন্দর—কিরকম একটা যেন মালার মতো বেঁকে গিয়ে যেন চিলকিগড়টাকে ঘিরে রয়েছে। মন্দিরগুলো বনজঙ্গলের মধ্যে হলেও ঠিক জঙ্গলের মধ্যে নয়। কনকদুর্গার ঐ নাম নাকি প্রচুর সোনাদানার গয়না ছিল বলে। এখন নেই। থাকলেই ”জনযুদ্ধ” গোষ্ঠীর কাজে লেগে যেত। অথবা চোর ডাকাতদের। এখানে মন্দিরের কোনও প্রোটেকশনের বন্দোবস্ত দেখতে পাইনি সেদিন। অবশ্য মন্দিরের আবার প্রোটেকশন কি! ঠাকুরদেবতারা নিজেরাই নিজেদের দেখাশুনো করবেন। নিজেদের রক্ষা করতে না পারলে আর ভক্তদের রক্ষা করবেন কেমন করে?
বাবা—মারা যে আলাদা আলাদা ঘুরছেন, সেটা আমার খুব পছন্দ হচ্ছে—ইন ফ্যাক্ট, ওঁরা এখনও দেখেননি চিলকিগড়। সেদিন ঝাড়গ্রামের মল্লরাজার রাজবাড়িটাড়ি দেখতে গেছিলেন। ওদিকটায় আবার আমাদের যাওয়া হয়নি এখনও। যাবো, সুখরামজী ইস ভেরি গুড—সর্বত্র নিয়ে যাবে, সব দেখাবে বলেছে। শালফুলকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথাটা অবশ্য এখনও কাউকে বলা হবে না। যদি বাধা দেওয়া হয়। তাহলে, আমরা ঠিক করে ফেলেছি ওকে হাইজ্যাক করব। পিসেমশাইয়ের গাড়িতে আরও একজন—কাকুমণি বলছিল বেশি ভিড় হলে বাবাকে নিয়ে কাকুমণি ট্রেনে চলে যাবে। কিন্তু বাবা বলছিলেন অতগুলো বাচ্চা আর মেয়েদের নিয়ে জেঠুমণি আর পিসেমশাইকে ছেড়ে দেওয়াও ঠিক নয়। রাস্তাঘাট এ অঞ্চলে ভালো নয়।
পিসিমণিরা কালই এসে যাবে। তখন আরও মজা হবে। ভিডিওক্যামেরাটাও আসবে।
এইখানেও আমাদের দু’জন পিসিমা আছে, তারা খুব দূরে দূরে থাকে বলে আসেনি। তাদের বাচ্চাদের এখন স্কুল খোলা। ওদের দেশে পুজোর ছুটি হয় না। তাই আলাপ হল না বান্টি আর মুন্টির সঙ্গে।
ওদের ফোটো দেখেছি অবশ্য, নতুন ঠাকুমার ঘরে একটা অ্যালবাম আছে, নতুন ঠাকুমা যত্ন করে অ্যালবাম দেখিয়ে সকলকে চিনিয়ে দিয়েছেন। নতুন ঠাকুরদারও ছবি আছে তাতে—অনেকটা জেঠুমণির মতোই দেখতে। কোলে একটা বাচ্চা—শঙ্করকাকা। ছবিতে বান্টিকে আমার মতোই দেখতে বলে আমার তো মনে হচ্ছে, দিদিভাই বলছে, না। শুভর মতও না ওর নিজের মতো। আর মুন্টিকে অনেকটাই পুলকির মতো দেখতে—বোন বলে বোঝা যায়। দিদিভাই বলছে। তাও না ওই দুজনেরই পোনি—টেল আছে, দুজনেই গোলগাল, আর চশমা পরা। তাই ওপর ওপর আমার মনে হচ্ছে মিল রয়েছে। আসলে নাকি আলাদারকম চেহারা। কি জানি? But I must say what a great discovery. A whole new branch of the family and so many cousins! আর জমিজমা? সেও তো অনেক! সবই তো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। মাপজোক শুরু হয়ে গেছে—একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। বনের মধ্যে একটা অঞ্চলে লোকাল জরিপকারীরা যেতে চাইছে না। বলছে ওখানটা ভুতুড়ে। এখানে আশেপাশে যারা originally থাকতো, সবাই বাসা ছেড়ে উঠে গেছে অন্যত্র, এত ভূতের উপদ্রব।
শুনেই তো আমরা সকলে মহা উত্তেজিত all of us want to investigate it! ওইখানেই যেতে হবে! সুখরামজী কিন্তু বাদ সাধল। সে ওখানে গাড়ি নিয়ে যাবে না। গাড়ি permanently damage করে দেবে harmful ভূতেরা। ওরা নাকি বহু পুরনো ভূত, আগেকার ডাকাতদের হাতে মরে যাওয়া সব মানুষ। ওদিকে কেউ গেলেই Revenge নিতে তেড়ে আসে। ওখানে কেউ যায় না তাই। রাত্রে তো যাবেই না। দিনের বেলাতেও অনাসৃষ্টি করে। নানারকমের শব্দ করে ভূতেরা তীব্র শিস দ্যায়, গাছপালা ভেঙে দেয়, জীবজন্তুদের মেরে ফ্যালে—প্রবল অত্যাচার করে তারা।
পুলকি
আমরা একটু হাঁটতে বেরিয়েছি। অপূর্ব শালমহুয়ার বন দিয়ে যাচ্ছি আমরা। বিউটিফুল। শালবন মানে শুধুই শালগাছ তো নয়, মহুয়াবনও। তার সঙ্গে আরও পিয়ালবন। পিয়ারশাল, মহুয়া, কুড়চি, করম, কঙিলা—কতরকমের নাম গাছগুলোর—আর বুনো কলাগাছের ঝাড়, বুনো বাঁশঝাড়—হাতিরা এইসব খেতে আসে—এই বনে নাকি হায়েনা বেরোয় মাঝে মাঝে—আগে খুবই বেশি ছিল, শুনেছি এখন হায়েনার জাতটা পৃথিবীতে কমে আসছে। সুখরামজী বলছে, নদীর ধারে ভিজে মাটিতে নাকি হায়েনারও পায়ের ছাপ দেখা যায়, হাতির পায়ের ছাপ তো দেখা যায়ই, এমনকি বাঘের পায়ের চিহ্নও পড়ে থাকে। আর ‘ডুংরি’ মানে টিলা। পিয়ালডুংরি, মহুলিয়া, কি সুন্দর সব গ্রামের নাম। এখানে সব অন্য অন্য ফুল—আমাদের চেনা ফুলগুলো এখানে ফোটে না। Exotic, সত্যি সত্যি। কিন্তু সুখরামজী বলেছে একটা দারুণ বিলিতি গোলাপবাগিচাও আছে এখানে। একজন বাঙালীবাবুর প্রপার্টি। ঘোষালবাবু তাঁর নাম। আগে ছিল এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবের। এখন ওঁদের। সেটাও একদিন দেখাতে নিয়ে যাবে আমাদের।
এখানে দেখছি দু’রকম লোক থাকে।
কেউ কেউ খুব ধনী, জমিজায়গা নিয়ে লোকজন খাটিয়ে আরামসে আছে। কেউ কেউ খুব গরিব, নিজস্ব কিছুই নেই। পরিশ্রম করে বেঁচে আছে। এরা পরিশ্রম করে। অন্যরা আরামে থাকে। কলকাতাতে এটা এভাবে বুঝতে পারিনি। এখানে মাঝামাঝি বলে কিছু নেই। ঠিক সেই মেভিসভ্যালে ইউরোপের মতন যেন।
জমিদার আর প্রজা Lord আর Serf খুব অদ্ভুত।
এদিকে গ্রামবাসীদের একটা রেগুলার ঝামেলা তো আছেই ধনিয়া বলছিল, দলমা পাহাড় থেকে হাতির দল নেমে এসে খেতখামার নষ্ট করে দেয়। ধান খেয়ে ফেলে, কলাগাছ খেয়ে ফেলে, ঘরবাড়ি মাড়িয়ে দেয়। পিষে ফেলে, মানুষকেও, যদি বাধা দিতে যাও। এই হাতির দল পাগল নয়, মাতাল নয়, ভুখা। তারা খিদের চোটে নিচে নেমে আসে। গ্রামে গ্রামে তাণ্ডব চালায়। বনে এখন খাদ্য নেই।
হাতির তাণ্ডবের সঙ্গে এরা পরিচিত। সেজন্যে গ্রাম ছেড়ে পার্মানেন্টলি পালায় না কেউই। কিন্তু ভূতের উৎপাতটা অন্যরকমের। অলৌকিক উৎপাত। ভুতুড়ে উৎপাত। এ অঞ্চলে নরবলিও তো কম হয়নি এককালে। নিরীহ পথিকদের ভুলিয়ে ধরে এনে বলি দেওয়া হয়েছে। শুধু রাজারই নয়, ডাকাতদেরও দেবী রঙ্কিণী। একরকমের কালী। সেইসব মৃত আত্মারা জেগে উঠে বনের এই অংশটাতে ঘোরাফেরা করে। সুখরামজীও বলেছে ওদিকে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাবে না। এতগুলো বাচ্চাকে ভূতের উপদ্রব দেখাতে কিছুতেই নিয়ে যাবে না সে। খুব বেশি রিস্কি হয়ে যাবে। ভূতেদের চ্যালেঞ্জ করতে নেই। ভগবানকেও না। আমরা তো মানুষ, শুধু মানুষকেই তাই চ্যালেঞ্জ করা যায়। ভূতেদের ঘাঁটাতে হয় না।
এদিক ওদিক ঠিক আছে, সুখরামজী না হয় আমাদের নিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না—কিন্তু জরিপ করবার লোকগুলো যাবে না কেন? ভূতেরা কি তাদের জমিজমার teritorial rights বিষয়েও এত কনসাস? সূচ্যগ্র ভূমি মাপতেও দেবে না মানুষদের? এ আবার কি? জরিপের লোকেরা বলল, ডুংরির ওপর ওরা উঠবে না। ‘রঙ্কিণীর থানের’ ওদিকটাতেই ওরা যাবে না। মাপে যা লেখা আছে, তাই মেনে নিন।
”সরকারী চাকরি করে তারা। জমি জরিপ করাই ওদের কাজ। জরিপ করবে না মানে? দেখলুম বড়মামু, মেজমামু, ছোটমামু তিনজনেই ক্ষেপে লাল। শঙ্করমামা, শিবমামা কিন্তু শান্তভাবে ওঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে এটা তো শহর নয়, এটা জঙ্গলমহল, এখানে নিয়মকানুন একটু আলাদা। সরোজমামা কোনো পক্ষে কিছুই বলছে না। কুট্টিমামী, ছোটমা আর মামীমা নিজেরা কীসব বলাবলি করছিলেন বড়মামাদের থেকে আলাদা হয়ে। বুলটু আমাকে বলল ”বাড়ি চল তোর তিলফুলকে জিজ্ঞেস করি। নতুন ঠাকুমা মনে হয় মানুষটা খুব সেন্সিবল।”
ওরা কিন্তু কেউ ‘তিলফুল’ ডাকছে না, দিদিও না, পুটুসও না। দিদিভাই বলল, ”দাঁড়া! বাবাদের আগে ব্যাপারটা বুঝতে দে। কথায় কথায় নতুন ঠাকুমাকে জ্বালাস না।”
”জ্বালাবার কী আছে? শি মে নো মোর দ্যান দ্য রেস্ট অব দেম।”
কিন্তু আমারও ইচ্ছে করছিল না বাড়ি ফিরতে। তাছাড়া শালফুল বলল এই সময়টায় উনি একটু ঘুমোন। শালফুলও বলল বনের ওপাশটায় সত্যিই যাওয়া বারণ। ওরাও কখনও ওদিকে যায় না। কাঠুরেরাও ভীষণ সব মুশকিলে পড়েছে ওখানে কাঠ কাটতে গিয়ে। শুভ ছড়া কাটলো,—
”এটা কিন্তু ভূতের রাজার রাজ্য নয়।
এখানে অন্য রকম কাণ্ড হয়
এই ভূতেরা পাজী ভূত
মারে, ধরে, কিম্ভূত—
বর—টর কিছুই দেবে না
ধরলে পড়ে ছেড়ে দেবে না—
এই ভূতকে যে ভয় পায় না
মরণকেও সে ভয় পায় না।”
ওরে বাবা! এরকম কেস? এত খারাপ? একেবারে মরে যাওয়ার মতো ভুতুড়ে কীর্তিকলাপ এদের? কেলেঙ্কারি। হঠাৎ—প্রচণ্ড জোরে একটা কী যেন জিনিস শিস দিয়ে শোঁওও করে এসে হুউস করে আমাদের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, তীরের মতো। হাউইয়ের মতো। মাথার ভেতরে ঝন ঝন করে উঠল—হাউই? সে তো ওপরে উঠবে—এটা তো হরাইজনটালি গেল…
না। এখানে হাউই কোথায়? বনের মধ্যে?
অবশ্য দেওয়ালী সামনেই। হয়তো গ্রামে কোথাও বাজী—বারুদ ছাড়তেই পারে। এখানেও দেওয়ালী হয়। কালীপুজো হয় মন্দিরে। কিন্তু এটা তো গ্রাম নয়। আমরা তো গ্রামে নেই। আমরা তো জঙ্গলে। এমন সময়ে দূরে কোথায় ঠিন ঠিন ঠিন ঠিন ঠিন ঠিন করে একটা ঘণ্টা একটানা বাজতে শুরু করে দিল। শব্দটা বাড়ছে কমছে, বাড়ছে কমছে। মাথার মধ্যে ঝিন ঝিন করছে। পুটুস দিদিভাইকে আঁকড়ে ধরল ”বাঁড়ি যাঁবো।” আমরাও ভাবলুম হোকগে দিনের বেলা দুপুর বেলা—ভূতেরা তো দুপুরেও বেরোয়— We know so little about these supernatural beings …তার চেয়ে কেটে পড়াই ভালো। সরু ঘণ্টিটা কানের মধ্যে বেজেই চলেছে ঝিন ঝিন ঝিন—অসহ্য—
কাল রাত্রে একটা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেছে। এই আশপাশের গ্রামগুলো ভয়ে কাঁপছে। পিয়াশালডুংরি গ্রামে রাতে হাতি নেমেছিল। গ্রাম তছনছ করে দিয়েছে হাতির দল। বাড়িঘর মাড়িয়ে ভেঙেছে। কলাবাগাত্র তো খেয়েইছে, পুরো ধানখেত সাবাড় করে দিয়েছে overnight! একরাত্রে যে এমন তাণ্ডব সম্ভব, চোখে না দেখলে জানতেও পারতুম না। এসে অবধি শুনছি, দলমা পাহাড় থেকে হাতিরা এসে অত্যাচার করে মাঝে মাঝে। সেটার রেঞ্জ যে এতখানি, এত ক্ষতি করতে পারে ওরা। গ্রামের লোকের খাবার ধান, শোবার জন্য মাথার ছাদ, সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, গোয়ালঘর ভেঙে দিয়েছে, গরুগুলো ভয় পেয়ে গেছে, গ্রামসুদ্ধু যেন প্রলয় ঘটে গেছে এমনভাবে ভেঙে পড়েছে। ছোট্ট পুকুরের জলটুকু পর্যন্ত ঘেঁটে কাদাকাদা করে দিয়েছে ওরা, জলে নেমে খেলা করেছে না কি করেছে কে জানে। গ্রামের লোকেরা তিলফুলের কাছে এসেছিল, হেলপ চেয়ে। সরকারী সাহায্য তো আসতে অনেক দেরি হবে। এটা আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে। এরা কিন্তু শঙ্করমামা, শিবমামার কাছে আসেনি। সোজা ‘মা’—র কাছে এসেছে। ‘তিলফুল’কে ওরা সবাই ‘মা’ বলে ডাকে—খুব ভালোবাসে বলে মনে হল। তিনফুলও সঙ্গে সঙ্গে ওদের জন্য কত বস্তা যেন চাল, ডাল, সবজিটবজি পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। গোরুর গাড়ি করে সেসব রিলিফের জিনিসপত্র অলরেডি যেতে শুরু করেছে। এস্টেটের একজন ডাক্তারবাবু আছেন। তিনিও গেছেন ওষুধপত্তর নিয়ে ওই গরুর গাড়িতে। একটা ক্রাইসিস হলে তিলফুল কীভাবে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়েন, সেটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমরা সবাই।
আর অবাক হয়েছি শিবমামাদের অদ্ভুত ইনডিফারেন্সেও। বড়মামা খুব ডিস্টার্বড হয়ে বলতে গেছেন, ”তাই তো, আমাদেরও তো কিছু করা উচিত”। শিবমামা বললেন—”দূর দূর, বড়দা, ছেড়ে দিন তো? ওদের জন্য যত করবেন ওরা ততই পেয়ে বসবে। চেনেন না তো ওদের? মার কথা ছেড়ে দিন। মার একটা অসম্ভব উইকনেস আছে গ্রামের লোকদের জন্যে। ওরাও সেটা জানে। তার পুরো অ্যাডভান্টেজ নেয়। দেখছেনই তো।”
থতমত খেয়ে তখন বড়মামু বললেন, ”পুলিস টুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে তো?”
শঙ্করমামা উত্তর দিলেন—”সেসব ওদের বলতে হবে না। বছর বছর তো লেগেই আছে এই হাতির অত্যাচার। আজ এই গ্রামে হল, তো কাল ওই গ্রামে হাতির দল নামে। পাহাড়ে ওদের খাদ্য কমে গিয়েছে কিনা, গাছ কেটে নিয়ে। ওদেরও উপায় থাকে না। কী করবে? খাদ্য সংগ্রহ করতে আসে। আগে কিন্তু এমন হত না—আমাদের ছোটবেলাতে হাতিরা এমন গ্রামে নামতো না। কেবল দু’একবার পাগলা হাতি, মানে দলছুট, একা হাতি এসে গোল বাধিয়েছে—তাদের মারতে শহর থেকে শিকারীরা আসতো। ওদের স্বভাব খুব ভয়ঙ্কর হয়, খুনে হয়ে যায় কিনা? কিন্তু এরা ভূখা হাতির পাল, পাগলা হাতি নয়। এদের মারতে হয় না, তাড়িয়ে দিতে হয়। শিবে একবার গুলি করেছিল,—তাতে কেলেঙ্কারি। খেপে উঠে হাতির পাল চতুর্গুণ লোকসান করে। মানুষ পিষে দিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে গুলিগোলা বন্ধ। গ্রামের লোকদের খুব ক্ষতি হয়।”
শঙ্করমামার কথার মধ্যে একটা সিমপ্যাথি ছিল। হাতিদের প্রতিও গ্রামের লোকেদের প্রতিও। But শিবমামা সাউন্ডেড ভেরি ক্রুয়েল অ্যান্ড হার্টলেস—তিলফুলকে সবচেয়ে ভালো লাগলো। বুলটু সাইকেল নিয়ে পিয়াশালডুংরিতে গেছিল ড্যামেজের পরিমাণ দেখতে। আমারও যেতে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম মানুষের দুঃখ দেখা আমি সহ্য করতে পারি না। তাই আমি যাইনি। তাছাড়া সাইকেল চালাতে পারি না। আমাকে ক্যারি করতে হত। দিদিভাই পারে, কিন্তু যায়নি। ওখানে তো আমাদের কিছু করার নেই। দেখতে গিয়ে কার কী উপকার? যদি কোনো help লাগতো নার্সিং etc. তখন দিদিভাই আমাকে নিয়ে চলে যেত। শালফুলও আসতো। কিন্তু usually ওরা নিজেরাই সব পারে—মানুষ আহত হয়নি কাল কোনো। ওনলি প্রপার্টি।
শালফুল বলছিল হাতির অত্যাচারও অনেক সময়ে ভূতেদের দ্বারা organized হয়। তাই এর পরে গ্রামের লোকেরা রঙ্কিণীর পুজো দেয়। ভূতেরা তাঁর কথা শোনে। মহামারীও তাঁর কথা শোনে। হাতিরাও শোনে হয়তো।
শালফুলকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে। এখানে থেকে থেকে ও ভীষণ supersitious হয়ে গেছে। ওর মনটাকে মুক্ত করা দরকার। বুদ্ধিমতি মেয়ে সায়েন্সে এত ভালো, বলছে তো জয়েন্ট দেবে, টাউন প্ল্যানিং আর্কিটেকচার পড়বে, তাকে এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে চলবে? আমরা কোথায় দেশকে কুসংস্কারমুক্ত করবো—তা না আমরাই যদি নিজেরা ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি, তাহলে দেশের উন্নতি হবে কেমন করে?
প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদী দলকে একবার এইখানে নিয়ে আসতে হবে। এদের বোঝাতে হবে, কুসংস্কার কী, কেন। They need to be enlightened, হাতি কখনও ভূতে পাঠায়?