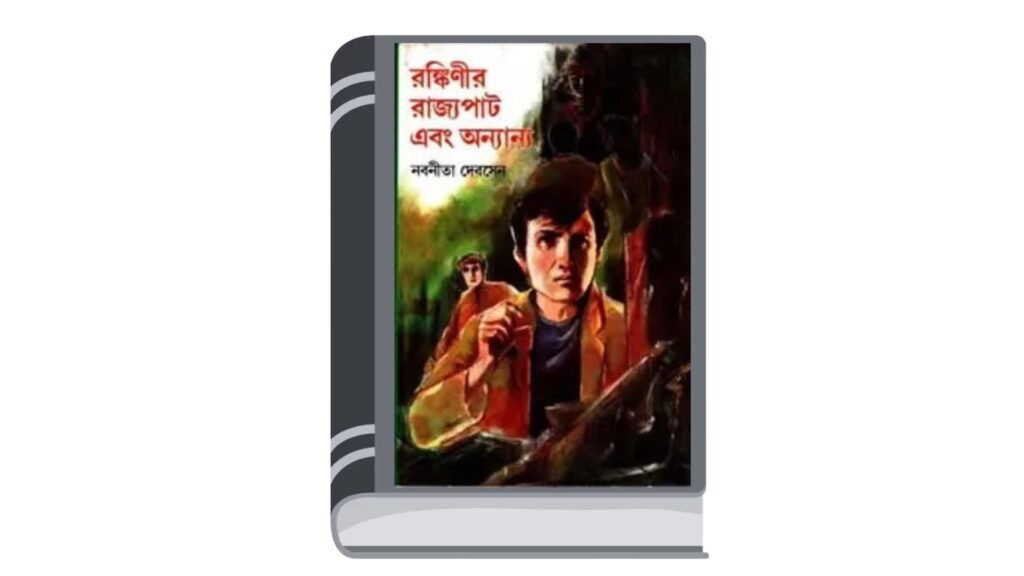তৃতীয় পর্ব : রঙ্কিণীর রাজ্যপাট
টুলকি
পিসেমশাই সমেত পিসিমণি এসে গেছেন। ওঁদের মিটিং বসেছে। আমি বুঝতে পারছি পুরো ব্যাপারটা যেমন সহজ মনে হচ্ছিল, ততটা সহজ নয়। বাবা জেঠুমণিকে বলছিলেন—”এরা আমাদের এনেছে ঠিকই, কিন্তু জমি দান করতে নয়। জমি বিক্রি করাতে। আমরা সই করে না দিলে ওই জমি ওরা আইনত বিক্রি করতে পারবে না। ওদের প্রোমোটার ঠিক করা হয়ে গেছে, জমি কেনবার লোক ঠিক। আমাদের অংশের টাকাটা আমাদের দিয়ে দেবে বলছে—”
—”যতটা দেবে, জেনে রেখো তার চেয়ে ঢের বেশি গুণ আমাদের প্রাপ্য। ওরা সব টাকাটা ঠিকমতো কক্ষণো দেবে না আমাদের।” কাকু বলে উঠল। জেঠু বাধা দেন—
—”তা কেন, ওরা তো আমাদেরই ভাই। ওরা তো আমাদের না ডেকে মিথ্যে মিথ্যে জালসইও করে দিতে পারতো? আমরা কি জানতেও পারতুম?”
—”না। সেটা পারতো না। জ্যাঠাইমা আছেন না? উনি না থাকলে ওরা নিশ্চয়ই সেটাই করত। এখন মুখরক্ষা না করলে নয়, তাই তোমাদের ডেকে এনেছে”—মা হঠাৎ বলে ওঠেন।
ঠিক তো।
ঠিক তো।
সকলেরই মনে পড়লো ঠিক কথা।
জ্যাঠাইমা তো রয়েছেন। তিনি যেরকম মানুষ দেখছি, তাঁকে সব ঠিক ঠিক কথাই বলতে হয়। তিনি সব জানেন।—জেঠুমণি, বাবার existence বিষয়ে সচেতন তিনি। অর্থাৎ তাঁর জন্যেই আমাদের whole lot কে lot ধরে আনতে হয়েছে এদের। জ্যাঠাইমা না থাকলে এরা আমাদের ডাকতো না।
কাকু বলল—”তোমরা কি জানো জমিজমাগুলো বেচে দেওয়া হচ্ছে কাকে, কেন?”
না, কেউ জানি না। কাকু জানে। কাকু কেমন করে জানল কে জানে? ও একা একা ঘোরে, চায়ের দোকানে আড্ডা মারে, ও বাইরে থেকে খবর সংগ্রহ করেছে। অনেক খবর।
—”একটা বড় মাড়োয়ারি কোম্পানিকে বেচা হবে। এখানে হোটেল হবে, রিসর্ট হবে, একটা নয়, অনেক। শিবপ্রসাদ তো ব্যবসাদার। ওঁর ধানকলও আছে, কিন্তু ট্রাকের বিজনেসটাই আসল। ইটভাটাও আছে একটা। SP লেখা ইটগুলো সব ওরই তৈরি করা।”
—”তবে তো খুব ধনী মানুষ সে।”
—”হ্যাঁ, ধনী—শংকরপ্রসাদও কম ধনী নন। এত কাজুবাগান, এত বনসম্পদ—প্রচুর কাঠ বিক্রির বিজনেস এঁদের—ট্রাকে করে কাঠ যায়—”
—”কাঠ? গাছকাটা বারণ না?”
—”কিছু গাছ কাটা বারণ, কিছু গাছ কাটা অ্যালাউড। এদের প্রচুর চন্দন গাছ আছে। সেগুলো কাটা নিষিদ্ধ। তার অংশ কেটে কেটে বিক্রি করে এরা। চন্দনগাছের সবটা থেকেই চন্দনকাঠ ঘষা যায় না নাকি। খানিকটা থেকে ওটা হয়। তাছাড়া চন্দনকাঠের গুঁড়ো বেচে।”
—”বাপরে! তুই এত খবর এনেছিস সৌম্য?”
—”খবরের কাগজে কাজ করি, দাদা! ফোটোগ্রাফার বলে কি জার্নালিস্ট নই?”
—”শোনো সৌম্য, তুমি সাবধানে থাকবে—এত খবর জেনে ফেলা তোমার উচিত হয়নি—” হঠাৎ কথা বলে উঠলেন পিসেমশাই। তারপর কী মনে করে হঠাৎ উঠে চট করে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে টর্চটা ফেললেন। টর্চটা ফেলেই দেখা গেল একটা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। আড়ি পাতছিল। আমাদের ঘরের কথাবার্তা শুনছিল।
বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকার যেন আরও ঘন হয়েছে অজস্র জোনাকি উড়ছে বলে।
লোকটি সেই অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।
আমাদের একটা আলাদা বাংলো দিয়েছেন কাকাবাবুরা। ওঁরা নিজেরা থাকেন পুরনো দোতলা বাড়িতে। মস্ত বড় উঠোন। উঠোনে ইঁদারা। উঠোনের অন্যদিকে বাথরুম। আরেকদিকে রান্নাঘর। মেন বিল্ডিংয়েই থাকেন তিনভাই। সরোজকাকার ঘরটা আছে, যদিও তিনি থাকেন মেদিনীপুরে। নতুন ঠাকুমার ঘর ওপরে। দোতলায়। সেখানে তিনটে ঘরই তাঁর। বাকিটা ছাদ। কিন্তু শোবার সময়ে ছাড়া প্রায় সবটা সময়েই নতুন ঠাকুমা নিচের তলায়, দালানেই থাকেন। রান্নাঘরে যান, সবজির বাগানে খবরদারি করেন, পুকুরের মাছ ধরার খবরদারি করেন। দালানে ঠাকুমার একটা চওড়া খাটিয়া আছে। নতুন ঠাকুমার তক্তাপোষ পছন্দ নয়। ওই বাড়িতে আরও ঘর আছে—কিন্তু আমাদের একটা পুরো বাড়িই দিয়ে দিয়েছেন কাকাবাবুরা। বাথরুম, রান্নাঘর, সব আছে। উঠোন, ইঁদারা, সব আছে। এটাই নাকি ওদের আউট হাউস। গেস্ট হাউস। এটাও দোতলা, আটটা ঘর আছে। আমরা পাঁচটা ভরে ফেলেছি। জেঠুমণি আর বুলটু, আমি আর পুলকি, কাকুমণিরা তিনজন, বাবা—মা। পিসিমণিরা দুজন। পাঁচটা ঘর ভর্তি। একটা ঘর বেতের সোফা সেট দিয়ে বৈঠকখানা ঘরের মতো সাজানো, সেটা ড্রইংরুম। আর ছাদে দু’খানা ঘরে তালাচাবি। ইলেকট্রিক আছে সর্বত্র। আমরা বৈঠকখানায় বসে কথা বলছিলুম। হঠাৎ পিসেমশাইয়ের কী মনে হল যে উনি বাইরে বেরুলেন—সেটা আমরা বুঝতে পারিনি।
পিসেমশাই বললেন উনি একটা শব্দ শুনেছিলেন। সেটা জন্তুও হতে পারতো, মানুষও। তাই টর্চ ফেলেছিলেন। ঐ যে মানুষটা ছুটে পালালো। তাকে কে এখানে পাঠিয়েছিল? কেন?
সমস্ত আবহাওয়াটা হঠাৎ পালটে গেছে। আগের সেই ”পিকনিক পার্টি”র মনোভাব আর নেই, শুধু পুটুস আর শুভ খুব খেলছে। পুটুসকেও ছড়া কাটতে শেখাচ্ছে শুভ। আজ পুটুস সকালে বলেছে—
”খাব না দুধু। খাব না দুধু,
বেড়াব শুধু, বেড়াব শুধু।”
শুনে ছোটমা ওকে বকবেন কি। হেসেই অস্থির আমরা। পুটুসের খুব উৎসাহ হয়েছে বাংলা পড়তে লিখতে—এতদিন কিছুতেই বাংলা পড়তে চাইতো না। শুভ বলেছে ছড়াগুলো মনে করে লিখে ফেলতে। পুটুস আরও ছড়া বানিয়েছে, শুভর দেখাদেখি।
”বনে বনে ঘুরি
রোদ্দুরে পুড়ি।”
আমরা যত আনন্দ করছি ও তত উৎসাহ পাচ্ছে। কিন্তু ওটাই কেবল ভালো খবর। Otherwise ভালো নয়। In general সকলের মন ভারী—কেউ বুঝতে পারছে না আমাদের policy কী হওয়া উচিত। আমরা আমাদের অংশ বেচতে চাই না—সেটা এখনও ওদের জানানো হয়নি। পিসেমশাই মনে করছেন সেটা dangerous হবে। ওটা কলকাতায় গিয়ে জানাবো। এখন মাপজোখ হয়ে যাক, দামটাম ঠিক হোক। তারপর চলে যাবো।
মাঝেমাঝেই পিসেমশাইকে বারান্দায় গিয়ে ফোন করতে দেখছি। রাগ করে পিসিমণি বলছেন ক্লায়েন্টদের হাত থেকে এখানেও রক্ষা নেই! সত্যি ল’ইয়ার হলে এত ব্যস্ত থাকতে হয়? আমাদের অংশটা না পেলে ওদের একসঙ্গে অনেকখানি জমি পাওয়া হচ্ছে না, তাছাড়া কাজুবাগানটা টুকরো হয়ে যাচ্ছে—এছাড়া আমাদের জমিতেই ‘ডুংরি’টা আছে একটা টিলা—তার ওপরে ওরা হোটেল করবে বলে ঠিক করেছে। ওই ‘ডুংরি’তেই সেদিন যাচ্ছিলাম, যাওয়া হল না। শালফুল বলছিল ওখানে যাওয়া বারণ—ভূতটুতের উপদ্রব আছে। তা ভূতের বাসায় ওরা হোটেল কবার কথা ভাবছে কেমন করে? ডুংরিটার চুড়োয় একটা ছোটো, ভাঙা মন্দির আছে। সেখানেও যাওয়া বারণ। সেখানেই নাকি নরবলি হত। ওটা রঙ্কিণী দেবীর থান ছিল। এখন আর কেউ যায় না, পুজোআচ্চাও হয় না। ওই মন্দিরটা পরিত্যক্ত। শালফুল ভীষণ বাধা দিল বুলটুকে, বুলটু জেদ ধরেছিল সাইকেল নিয়ে যাবে। সাইকেলের দরকার নেই, হাঁটাপথই, এই তো একটুখানি রাস্তা। আমরা একদিন চলে যাব লুকিয়ে। কাল রাত্রে হঠাৎ বুলটু ডেকে দেখালো, অদ্ভুত একটা দৃশ্য। মনে হচ্ছে যেন ঐ ভাঙা মন্দিরটা থেকেই একটা আলোর মতো আভা বেরুচ্ছে—মন্দিরটা তো রাতের অন্ধকারে অস্ত যায় ফের ভোরের সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়। আজ কেন মন্দিরটার একটা আবছা—ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে? ওর পিছনেও আলো জ্বলছে। আমরা ঠিক করলুম পরের দিন যাবো। মন্দিরের ব্যাপারটা বুঝতে হবে। After all ওটা তো আমাদেরই জমিতে। আমাদের জানা উচিত আলোটা বেরুলো কোথা থেকে? শালফুলকে দেখালুম ডেকে। শালফুল বললো, মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আপনিই একটা ভুতুড়ে আলো বেরোয় ওদিকে—ঐজন্যেই তো কেউ যায় না। মাঝে মাঝে ঘণ্টাও তো বাজে! অথচ মন্দিরে ঘণ্টা আলো, কিচ্ছু নেই। শালফুল একটুও বিচলিত নয়, ঐরকম আলোটালো সবাই দেখেছে এখানে। ওটা মানুষের নয়, দেবতারও নয়, অপদেবতার আলো। ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতেও নেই। আগে ঐ মন্দিরে নরবলি হত, ওখানে তাদেরই সব দীর্ঘনিশ্বাস ঘুরে বেড়ায়—কখনো আলো হয়ে, কখনো ঘণ্টার শব্দ হয়ে।
১। কে এসেছিল আড়ি পাততে?
২। মন্দিরে আলো জ্বলে কেন? এ দুটোর উত্তর জানতে হবে।
টুলকি
কাল মন্দিরের ঐ আলোটা দেখার পর থেকে—There are more things in heaven & earth Horatio, then your জেঠুমণির এই কথাটা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। সেদিন উনি এই লাইনটা ‘কোট’ করেছিলেন হ্যামলেট থেকে, এরা যখন ভূতপ্রেতের কথা বলছিল, আর কাকুমণি ছোটমা পিসিমণি সকলে মিলে বাধা দিচ্ছিল। পিসেমশাই চুপচাপ সব শোনেন। কিছু কমেন্ট করেন না। মা—ও মোটামুটি তাই—কিন্তু মা পরে নিজের মতামত বলেন। পিসেমশাই তাও বলেন না। বাবা সাধারণত জেঠুমণির সঙ্গেই থাকেন। এবারে বাবা চুপচাপ ছিলেন।
এরা বলছিল একটা অংশ নতুন করে জরিপ হবে না কেননা ওইদিকে জরিপের লোকেরা যাবে না। যাবে না, কারণ আগে শেষবার যেবার ওই অঞ্চল জরিপ করা হয়েছিল, সেই কাজে যারা যারা গিয়েছিল, তাদের তিনজনেই অদ্ভুত একটা না একটা দুর্ঘটনায় তার পরে পরেই মারা গেছে। সেই জরিপের হিসেবটা আছে, সেই মতোই ম্যাপ তৈরি হয়েছে। কিন্তু নতুন করে জরিপ করতে যেতে এরা রাজি হচ্ছে না—ওই অঞ্চলটুকু বাদ দিয়ে বাকিটা করবে।—”কিন্তু ওটা যে আমাদের জমির মধ্যেই পড়ছে—আমাদের জমিটা জরিপ করানোই তো উদ্দেশ্য”—কাকু বলল।
—”কিন্তু ওটা যে রঙ্কিণীর ডুংরি, ওর চারপাশের বনেও প্রবল ভূতের উৎপাত—আজ পর্যন্ত চলছে—স্থানীয় বাসিন্দারা কেউই তো ওদিকে যাবে না!—কলকাতা থেকে জরিপের লোক আনাতে পারেন—কিন্তু সরকারী জরিপের হিসেব তো প্রাইভেট কোম্পানি দিয়ে হবে না। সেটাই মুশকিল।”
শঙ্করকাকা চুপ করে শিবকাকার কথা শুনছিলেন। এবার বললেন—
—”ফরেস্টের লোকদের বললে হয় না, শিবে?”
শিবকাকা ফেটে পড়লেন।
—”কী যে বলো তুমি দাদা! ফরেস্টের লোকরাই তো আরও ভয় দেখাচ্ছে, যত ভূতের গল্প তো ফরেস্টের থেকেই ছড়ায়—ওদের তো যত ভূতের এক্সপিরিয়েন্স ঘটে—ওরাই তো যাতায়াত করে ওইখানে, কাজের চাপে, বাধ্য হয়ে—তাছাড়া ঐ আরজু মুণ্ডা—”
কাকু বলল—”আচ্ছা এখানে তো প্রচুর চোরাশিকারী আছে। চোরা কাঠকারবারিও আছে নিশ্চয়—তারা ভূতের ভয় পায় না?”
বিরক্ত মুখে শিবকাকা বললেন—”দেখুন, চুরিচামারি করতে বেরুলে আর প্রাণের ভয় রাখলে চলে না—ভূতপ্রেতের ভয় তো নয়ই—আরে পুলিসের গুলির ভয়ই পাচ্ছে না তারা, —হুঁ—ভূতের ভয় পাবে!”
আমার ওদের কথাগুলো কিরকম অদ্ভুত লাগছিল। ”ভূতের গল্প ছড়ায়” মানে? ওগুলো কি তবে বানানো গল্প? ”ফরেস্টের লোকেরাই আরো ভয় দেখাচ্ছে”, না ভূতেরা? আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে—এদের কথাবার্তায় আমি বেশ কিছু flaws পাচ্ছি—যুক্তিতে গলদ পাচ্ছি—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না শিবকাকার argument সত্যি বলে। বিশেষত, ”ওরা পুলিসের গুলিকেই ভয় পায় না তো ভূতপ্রেতকে ভয় পাবে—” এই সেনটেন্সটায় বেশ বোঝা গেল শিবকাকা নিজে পুলিসের গুলিকে ঢের বেশি ভয় পান ভূতপ্রেতের চেয়ে। তবে ওরা এই ভূতপ্রেতের ব্যাপারটা ভেঙে দিচ্ছেন না কেন? Explane করছেন না কেন? ওই ভাঙা মন্দিরটার চারিপাশের বনজঙ্গলেই ভূতের আড্ডা—নরবলির আত্মারা ওঁৎ পেতে থাকে, নতুন নতুন বলি ধরবে বলে। ব্যাপারটা সুখরামজীর কাছে শুনেছি আমরা।
—”আচ্ছা দিনেরবেলায়, জরিপের পার্টি গেলে, হঠাৎ ভূতেরা অ্যাটাক করবে কেন?” সাহস করে বলেই ফেলি কথাটা।
—”অ্যাটাক তো করবে না। কাজটাজ চুকে গেলে তারপরে বাড়ি ফিরে ওরা এক এক করে মরবে। কেউ রক্তবমি করে। কেউ গাড়ি চাপা পড়ে,—আরেকজন যেন কেমন করে মরেছিল, দাদা?”
—”পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে।” শঙ্করকাকা বললেন খুব দুঃখী মুখে। ”বিনু মহাতো।”
—”এই! এটাই মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে মরলে তো অন্য কথা ছিল। তখন—তখন কিছুই ঘটেনি। দিব্যি শান্তিমতো মাপজোক হয়ে গেল। মাসখানেক পর থেকে দুর্ঘটনাগুলি শুরু হল। যিনি লিডার ছিলেন প্রথমে তিনিই রক্তবমি করে মারা গেলেন। দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। চিতল সোরেন আর বিনু মাহাতো—তারাও একে একে দুর্ঘটনায় মরল। তারপর থেকে কেউ ওই দিকটায় যায় না।”
—”নাঃ চোরাশিকারীরাও যায় না। না কাঠ চুরি করতে, না জন্তু মারতে।” শঙ্করকাকা স্পষ্ট গলায় এবারে বললেন—”শিবে বলছে, ‘পুলিসকে ভয় পায় না, ওরা ভূতকে ভয় পাবে কেন’—সেটা বাকি জঙ্গলমহলের জন্যে ঠিক। কিন্তু এই এরিয়া, রঙ্কিণীর ডুংরির আশপাশের এরিয়ার জন্যে ঠিক নয়। এখানে তো পুলিসও আসবে না। পুলিসের প্রাণে ভয় নেই? এখানে পুলিসও পা দেয় না, চোরও না।”
”কি আশ্চর্য। পুলিসও আসে না?”
—”কেন, পুলিস বুঝি মানুষ নয়? তার প্রাণের ভয় নেই? সে বউবাচ্চা নিয়ে ঘর করে না? শেষকালে ওই আরজু মুণ্ডার মতন হোক?”
—”সেটা আবার কে?”
—”ঐ একজন চৌকিদার। ফরেস্টের লোক ছিল। সে পাহারা দিতে এইদিকে এসেছিল। বনের মধ্যে তার তো কাটা মুণ্ডু পাওয়া গেলই। তার ঘরে বৌ ঘুমুচ্ছিল, বাচ্চা কোলে নিয়ে—দেখা গেল তাদেরও মুণ্ডু কাটা!”—
—”ঈ—শ—শ…”
—”আর ফরেস্টের চৌকিদাররা কেউ রঙ্কিণীর থানে চৌকি দেয় না। তাদের কিছু বলাও তো যায় না। ওই মৃত্যুগুলোর কোনো সুরাহা হয়নি আজ পর্যন্ত। ভুতুড়ে মৃত্যুর আর সুরাহা কী হবে?”
এইসময় জেঠুমণি বলেছিলেন—There are more things is heaven & earth Horati ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি এখনও দু’দিকে পা দিয়ে আছি—বেশিটাই disbelief। বেশিটাই ভূতে অবিশ্বাস। কিন্তু কাল আলোটা দেখার পরে একটু ভয়—ভয়ও করছে, mysterious লাগছে—কেন এমন হবে? সত্যিই তো। জঙ্গলমহলের আর কোথাও তো এরকম হচ্ছে না? শুধু রঙ্কিণী দেবীর থানেই? Why?
পুলকি
আমাদের একবার দিনে দিনে ঘুরে আসতে হবে ঐ রঙ্কিণীর ডুংরি থেকে।
একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে হবে।
আমাদের তো যাবার দিন এসে যাচ্ছে। দেরি না করে আজই যাব। আজ আবার বড়রা অন্য কোনদিকে যাচ্ছেন—আমরা নিজেরা freely চলে যেতে পারবো। আমাদের তিনজনেরই ইচ্ছে we’ll go after lunch কিন্তু শালফুল যেতে দিতেই রাজি হচ্ছে না আমাদের। শুভ আর পুটুসকেও তো রেখে যাওয়া যাবে না—”লালার সঙ্গে থাকো” বললে ওরা থাকবে না। এটাই মুশকিল। দেখি কী হয়। শালফুলই প্রবলেম। শালফুল ভয় পাচ্ছে। ও তো এখানকার লোকাল মেয়ে—এখানকার সব সংস্কার ওকে জড়িয়ে রেখেছে। আমরা চেষ্টা করছি ছাড়িয়ে নিতে। ওকে কলকাতাতে পড়তে নিয়ে যেতে হবে। মিতালী কাকিমা ওকে মেদিনীপুরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু শিবকাকা মত দেননি। গোপনে গোপনে শুনতে পেলুম শিবকাকা ওর বিয়ে স্থির করেছেন, মস্ত এক প্রোমোটারের ছেলের সঙ্গে। যে এইসব, জমিটমি কিনছে রিসর্ট বানাবে বলে, তারই ছেলে। সে নাকি ধানবাদে কলেজে পড়ছে। শুনে অবধি আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। এই বিয়েটা ভাঙতে হবে। ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব। শালফুল বলছিল টাউন—আর্কিটেকট হতে চায়। বিয়ে দিয়ে দিলে ওর পড়াশুনো এখানেই শেষ। তাছাড়া ষোলো সতেরো বছরে বিয়ে তো এমনিতেও উচিত না,—আঠারো মিনিমাম।
অতি কষ্টে রাজি করানো গেছে শালফুলকে। শুভ, পুটুসকে রাখা গেল না—দলবলসুদ্ধুই যাত্রা—উপায় নেই। আমরা শালফুলকে বাদ দিয়ে নিজেরাই যেতে পারতুম, পুটুসকে শুভর সঙ্গে ওর কাছে রেখে। সেটাও যে আমাদের মনে হয়নি তা নয়।
কিন্তু দিদিভাই বলল—একযাত্রায় পৃথক ফল কেন?—ও তো আমাদেরই বোন—ওকেও সব কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে, সব রিস্ক শেয়ার করতে হবে। দিদি শালফুলকেও এইসব কথাই বলল। বলল,—”আমাদের ঈশ্বরের ওপরে বিশ্বাস আছে, ঈশ্বর ভালো লোকদের রক্ষা করেন।—মন্দদেরও ভয় তো করেন। জানি না—কিন্তু আমাদের রক্ষা করবেন। তুই তো ভক্তিমতী ভগবানে বিশ্বাসী, তবে কিসের ভয় তোর? আমরাই তো পুজোটুজো করি না—মনে মনে নির্ভর করি।”
শুভটা যা সুইট—অমনি বলে দিল—
—”ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি—রামলক্ষ্মণ বুকে আছেন, করবি আমার কী?” এই ছড়াটা আমরাও জানতুম—অনেকদিন শুনিনি, ভুলেই গিয়েছিলুম। শুভ খুব excited—আমাদেরই ভাই তো? পুটুসেরও এখন ছড়াকাটার নেশা ধরেছে।
আমি যেই বলেছি—”ঠিক দুকখুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা—” পুটুশ অমনি বলে উঠলো।
—”না না,
ঠিক দুকুখুর বেলা
ভূতের সঙ্গে খেলা”
—তৎক্ষণাৎ শুভ যোগ দিল
—”ভূতবাবাজী, গুড আফটারনুন—
খাবেন একটু, আমা আর নুন?”
বুলটু বলল—”ইয়ার্কি মারা বের করে দেবে, ভূত ধরবে যখন চেপে—হুঁ হুঁ—”
দিদিভাই এক ধমক দিল—”কী হচ্ছে কি? ওকে ভয় দেখাচ্ছিস? সঙ্গে না ও? তোর কোনো সেন্স নেই।”
অমনি শুভ ছড়া কাটলো—
—”সেন্স নেই মানে ননসেন্স
বুলটু দাদার গন কেস।”
ভারি চমৎকার লাগে ওর এই গুণটা। বেশ খানিকটা বনজঙ্গল পেরিয়ে টিলাটায় উঠতে হবে। টিলা বেশি উঁচু না। তবু ওখানে থেকে সূর্যাস্ত নিশ্চয় দারুণ দেখাবে। কিন্তু অতক্ষণ থাকা চলবে না—জঙ্গল দিয়েই ফিরতে হবে তো। ‘তিলফুল’ বলেই রেখেছেন—পাঁচটার মধ্যে বাড়ি!—তারপরে এদিক ওদিক ইচ্ছে হল কাছাকাছি যাও, সঙ্গে লোকজন নিয়ে।
কিন্তু আজকের যাওয়াটা সিক্রেট? ওটা বলেকয়ে যাওয়া যাবে না। কেউ পারমিশান দেবে না। আতাবাগানে যাচ্ছি, কি পেয়ারাবাগানে যাচ্ছি, এরকম একটা কিছু গুল দিয়ে যেতে হবে। White lies are okey ফিরে এসে সত্যি কথাটা বলে দেবো। এখন বলা মানেই যাওয়াটা ক্যানসেল হয়ে যাওয়া।
টর্চ নিচ্ছি চারজনে চারটে, ফোন নিচ্ছি দুটো। এখানে দুটোই রোমিংয়ে চলছে। টর্চ নিচ্ছি দিনেরবেলাতে কেননা জঙ্গলের মধ্যে ফেরার সময়ে যদি হুট করে অন্ধকার নেমে যায়?
বুলটু বলেছে—”দেখলি তো দিদিভাই তোরা এয়ারগানটা আনতে দিলি না? একটা safety measure হিসেবে থাকতো—”
দিদি বলল—”অহিংসা আমাদের মন্ত্র। বুদ্ধি, বিবেচনা আমাদের safety measure এটা মনে রাখবি।”
শালফুল বলল ও একটা দেশলাই নিয়েছে। অনেক সময়ে বনেজঙ্গলে একটু আগুন জ্বালানোর দরকার হয়, is signal others—লোকে তাই দেশলাইটাও সঙ্গে রাখে—টর্চে তো সেটা হবে না?
বুলটু
মন্দিরে পা দিয়েই চোখটা কেমন ধাঁধিয়ে গেল। হিলহিলে হলুদ এক চিলতে আলোয় যেন আরো বেশি অন্ধকার। ঘরটাতে ঢুকতেই হা হা হো হো করে হেসে উঠল কারা যেন!
চমকে পিছিয়ে এলুম সক্কলে।
দিদিভাই বলল, ”কে ওখানে?”
কেউ জবাব দিল না।
হো হো হা হা করে হেসেই কেউ যেন আমাদের মাথার ওপরে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে দরজা দিয়ে ভেসে বেরিয়ে গেল বাতাসের মতো। আমরা এ ওকে জাপটে ধরি।
হেসে শালফুল বলল,—”চামচিকে। ও কিছু না। ওরা থাকে এখানে।” ছোট্ট একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। খুব মিটমিটে আলো। কে বলেছে শূন্য মন্দির? ঐ তো দিব্যি প্রতিমা রয়েছে! শালফুলও একেবারেই অবাক।—”এ কি? মন্দিরে তো পুজো হয়!” অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে নিচু বেদীর ওপর দেবী প্রতিমা। ভয়ঙ্কর চেহারা। কালো পাথরে খোদাই করা দেবীমূর্তি। মাথায়, বুকে পিঠে জটা ঝুলছে। জটার চুড়ো বাঁধা রয়েছে কপালের ওপরে। দেবীর আটটা হাত। উপরের দুই হাতে একটা হাতি লুফছে। অন্যহাতে অস্ত্রশস্ত্র—কিছুই ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। সিঁদুরের চোটে দেবীমূর্তি ঢাকা পড়ে গেছেন। একটা কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। শিব? না শব? কে জানে। একটা লোক মোট কথা পায়ের নিচে শুয়ে। কালী ঠাকুরের মতোই দেখতে, তবে অনেক বেশি ভয়াল, ভয়ঙ্করী!
—”এখানে এই মূর্তিটা কী করে এল?” অত্যন্ত অবাক হয়ে শালফুল বলল,—’রঙ্কিণীর পূজা এমনিতে হয় শালগাছের গোড়ায়, মাটির হাতি ঘোড়া এইসব মূর্তি রেখে। ওইটেই ঠাকুর—ওখানেই ওরা বলি দেয়। মুরগী পাঁঠা। যে যা পারে—শুনেছি দেবীমূর্তি শুধু একা ধলভূমের রাজবাড়ির মন্দিরে আছে—রাজবাড়ির পুরোহিত পুজো করে। বাইরে কোথাও দেবীমূর্তি নেই। দেবীর ‘স্থান’ আছে অনেক, পুজো করেও সবাই—কিন্তু এরকম মূর্তিটুর্তি নেই।
—”কিন্তু মূর্তি তো চিলকিগড়ের মন্দিরেও থাকতে পারে না—ওটা তো ঘাটশিলায় নয়?” —পুলকি হঠাৎ বলল।
—”না, ঘাটশিলা হবে কেন? সে তো সুবর্ণরেখার পাড়ে। চিলকিগড় তো ডুলুং নদীর পাড়ে।”
—”এই দেবীমূর্তি তো কেবল ঘাটশিলাতেই আছে বলে জানি—জগতে আর কোথাও নেই? এখানেও এই মূর্তি আছে, চিলকিগড়ের এত কাছে অথচ স্কলাররা কেউ জানে না?”
—”কে বলল তোমাকে, মূর্তিটা কেবল ঘাটশিলাতেই আছে?”
—”আমি তো পড়ছিলুম, রঙ্কিণী দেবীর বিষয়ে। তোমাদের বাড়িতেই বাংলার লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে একটা বই আছে—সেটা ওলটাতে ওলটাতে দেখি ‘রঙ্কিণী দেবী’। বিভূতিভূষণের ”রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ” গল্পটা মনে পড়ে গেল, তাই রঙ্কিণী দেবীর ওপর লেখাটা পড়ছিলুম। সেখানে লিখেছে কনকদুর্গা মন্দিরের কাছেই রঙ্কিণী মন্দিরও আছে শালবনের মধ্যে—সেখানে একদা নরবলি হতো—কিন্তু পূর্ণ দেবীপ্রতিমা নেই। বিগ্রহ একমাত্র ঘাটশিলায় আছে। দু’এক জায়গায় মুণ্ডমূর্তি আছে, শুধু মুণ্ডুটা, রক্তমুখী, রক্তবর্ণা, নররক্তপিপাসু—”
—”চুপ কর! চুপ কর! পুলকি! শুনতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—চল বেরিয়ে যাই—আর এখানে নয়—” বলতে বলতেই হঠাৎ প্রদীপটা নিবে পুরো মন্দিরটা নিখাদ নিতল অন্ধকার হয়ে গেল। ভাগ্যিস পুটুসটাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি আমরা শুভর সঙ্গে। নইলে কেঁদে উঠত হয়তো ভয়ে—পুটুসটা এমনিতেই অন্ধকারে ভয় পায়। আমরা বেরুতে যাচ্ছি—দরজাটাতে চৌকো এক টুকরো আলো ভরা আকাশ আটকে আছে—হঠাৎ পায়ে কী যেন লেগে হোঁচট খেয়ে দিদিভাই পড়ে গেল। পুলকি শালফুল আমি—টর্চ জ্বেলে তিনজনেই ওকে তুলতে নিচে হয়েছি—হঠাৎ স্পষ্ট দেখতে পেলুম, প্রদীপটা যেখানে ছিল, সেখানে একটা গর্ত।—ঈশ! আমরা ধরে না ফেললে দিদিভাই এক্ষুনি পড়ে যেত ওই গর্তে! ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। গর্তটা কীভাবে এল? কোনো ট্র্যাপডোর খুলে ফেলেছি আমরা? নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কখন? কীভাবে? প্রদীপটা কি নিচে পড়ে গেল নাকি? গর্তের সিঁড়িতে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। পুলকি ফিসফিস করে—
—”দিদিভাই—সাবাধান। তোর পেছনেই একটা ট্রাপডোর খুলে গেছে, নিচে সিঁড়ি, গর্তের মধ্যে নেমে যাচ্ছে—”
দিদিভাই চমকে পিছনে ফিরল।
ঐ সময়ে বাইরে একটা চিৎকার। ভয়ার্ত আর্তনাদ।
শুভ চেঁচালো—”বড়দি!”
পুটুস চেঁচালো—”দিদিভাই।”
আমরা ছুটে বেরুতে গেলাম—পুলকির পা—টা পড়বি তো পড় সিঁড়ির গর্তেই পড়ে গেল। হাতের টর্চ নিবে গেল।
দিদিভাই দৌড়ে বেরিয়ে গেছে—শালফুল সমেত।
আমি চেঁচাই—”পুলকি!”
পুলকির উত্তরটা যেন অনেকদূর থেকে এল—”টর্চটা দেখা শিগগির!”
পুলকি
হঠাৎ পায়ের নিচে থেকে পৃথিবী সরে গেল।
গভীর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। ঈশ্বর—আমি কি তবে—আর পায়ের নিচে হঠাৎ মাটি। সিঁড়িটা পেয়ে গেছিল। মাটি! আর বুলটু চেঁচাচ্ছে আমার নাম ধরে। টর্চটা পড়ে গেছে।
আমিও চেঁচাই—”টর্চটা দেখা, শিগগির।”
কে জানে এখানে সাপখোপ কী না কী বসে আছে। ইঁদুর তো থাকবেই। যদি বিছে থাকে? হঠাৎ পড়ে গেছি, কিন্তু ব্যথা পাইনি। আশ্চর্য! এই তো বুলটু টর্চটা দেখাচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি শক্ত পাথরের মেঝেতে। টর্চের আলোয় সিঁড়িটা দেখেই উপরে উঠতে থাকি—খুব তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। আপনিই খুলেছে—আপনিই যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়? বুলটু হাত ধরে টেনে গর্ত থেকে বেরুতে সাহায্য করল। উঠে পড়েই দুজনে ছুটি বাইরে, মন্দিরে আর এক মিনিট নয়। আঃ—খোলা বাতাস। আর দিনের আলো!
আমার বুকের মধ্যে যে কিরকম করছে সেটা আমি ভাষাতে প্রকাশ করতে পারবো না—মৃত্যুর এত কাছে আগে কখনও আসিনি! কোনওরকমে বুলটু আর আমি পালিয়ে এসেছি। গর্তের মধ্যে আমার টর্চটা হাত থেকে পড়ে গেছে। খোঁজবার জন্য সময় নষ্ট করা সম্ভব ছিল না সেই মুহূর্তে। যদি আবার ট্র্যাপডোরটা আপনি আপনি বন্ধ হয়ে যেত? আমি তাহলে চিরজন্মের মতো থেকে যেতুম মাটির নিচের ওই অন্ধকূপে, বন্দিনী! যক্ষদের মতো। উঃ—
বেরিয়ে এসে দিদিভাই, শালফুল, শুভ, পুটুস—কাউকেই দেখতে পেলুম না। আমরা ডাকলুম—”দিদিভাই!” কোনও জবাব এল না। ”শালফুল।” বাইরে আলোভরা বিকেল—প্রথমে এতটা আলোয় চোখ ঝলসে গিয়েছিল—অন্ধকূপের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে। খুঁজতে খুঁজতে আমরা মন্দিরের ওপাশটাতে যাই—টিলার ঢালুর দিকে গিয়ে দেখি দিদিভাই, শালফুল, পুটুস আর শুভ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কুণ্ডলী পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুপটি করে। আমাদের ডাক শুনতে পায়নি। কী হয়েছে ওদের? ”দিদিভাই। পুটুস!” কাছে গিয়ে যা দেখলুম তাতে আমরাও স্ট্যাচু হয়ে যাই।—কতক্ষণ নিঃশব্দে কেটেছে জানি না, বুলটু হঠাৎ দিদিভাইয়ের হাত ধরে হাঁচকা টান মেরে বললো—
—”চলো, চলো, বাড়ি চলো, this is a dangerous place—চল পুটুসবাবু—ওসব আর দেখতে হবে না। ছিঃ! পুটুস আর শুভ, তাদের দিদিদের কোলে মুখ গুঁজে কাঠ হয়ে আছে। দিদিরাও তাদের জড়িয়ে ধরে স্ট্যাচু।
একটা হাড়িকাঠ। হাড়িকাঠে রক্ত। সামনেই একটা মানুষের মুণ্ডু গড়াচ্ছে মাটিতে—জটাধরা চুল—মুখটা উপুড় হয়ে আছে। কাটাঘাড়ে রক্ত। বাকি শরীর নেই।
—”কাল অমাবস্যা ছিল!” খুব আস্তে শালফুল বলল। প্রায় না শোনার মতো গলায়।
মনে পড়ে গেল—রঙ্কিণীদেবী তাঁর বলি নাকি নিজেই জোগাড় করেন।
টুলকি
কোনোরকমে শুভ আর পুটুসকে টানতে টানতে আমরা বাড়ি এলুম। তখন সূর্য ডুবুডুবু। শুভকে আর পুটুসকে পই পই করে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথায় গেছি কী দেখেছি কিছুই বলবে না। বনেজঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিলুম বলবে। সেটা মিথ্যে কথাও নয়। বনেজঙ্গলেই তো গিয়েছিলুম আমরা। মন্দিরটার প্রাঙ্গণও জংলী বুনো ঝোপঝাড়ে ভরা। ওপাশে, হাড়িকাঠের জায়গাটা কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন। আর ওখান থেকেই দেখতে পেয়েছি জঙ্গলের মাঝখানটা ন্যাড়া—খানিকটা জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করা। ছোট্ট খেলার মাঠের মতো। কিন্তু এদিকে তো মানুষে আসেই না। বড়রাই ঢোকে না, বাচ্চাদের খেলতে আসার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে কেন এই মাঠটা তৈরি করে রেখেছে? কারা খেলাধূলা করতে আসে এই খুদে মাঠে? মাঠটা তো আপনা থেকে গজিয়েছে বলে মনে হয় না, গাছটাছ কেটে কুপিয়ে ঐখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করা হয়েছে—হঠাৎ পুটুস বলল, ”দিদিভাই, ওদিকে ওটা কী। ওই মাঠের ধারে—”
—”কোনটা?”
—”ওই যে, বেলুনের মতোটা? উড়ছে, ওই যে?”
—তাকিয়ে দেখি মাঠের ওপাশে একটা খোঁটাতে বাঁধা একটা পাশবালিশের মতো লম্বাটে বেলুন উড়ছে—কমলা—রঙের বেলুন। এরকম বেলুনওয়ালা খুঁটি আমি আগেও দেখেছি। এয়ারপোর্টে এগুলো বাতাসের গতি মাপে, রানওয়ের ধারে থাকে। রানওয়ে? এয়ারপোর্ট? এখানে? এইটুকুনি এয়ারপোর্ট?
বাড়িতে ফিরে কোনোরকম গোলমালের মধ্যে পড়িনি—কেউ কিছুই জিজ্ঞেস করেনি—সময়মতো ফিরেছি বলেই সমস্যা হয়নি।
কিন্তু সমস্যা হয়েছে। প্রচণ্ড। আজ আমরা যা দেখেছি! শালফুল, পুটুস, শুভ আজ প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। আমিও কম ভয় পাইনি। same with পুলকি and বুলটু। আমরা প্রত্যেকেই terrified—কিন্তু at the same time, আমার মনে মনে mystery—টা একদিকে কমেছে, আর অন্যদিকে বেড়েছে। Airport—টা দেখবার পর আমার মনে একশোরকম প্রশ্ন উঠছে। অতটুকুনি রানওয়ে! অতটুকুনি airport ওটা নিশ্চয় হেলি—প্যাড। বড় প্লেন ওখানে নামতে পারে না। হেলিকপ্টার ওঠানামা করার জায়গা। তাহলে গ্রামের মধ্যে নয় কেন?
কেউ জানে না কেন? কখনও তো শুনিনি? হেলিকপ্টার অবশ্য দেখলুম না। কিন্তু abandoned বলেও মনে হয়নি। নিশ্চয় ব্যবহার করা হয় মাঝে মাঝে। যত্ন করা হয়। এখন আমার প্রশ্ন অনেক।
১। কে সেদিন আড়ি পেতেছিল? কেন?
২। কারা মন্দিরে আলো জ্বালে, পুজো দেয়?
৩। নরবলি যে এখন চলছে সরকারবাহাদুর কি জানেন?
৪। মন্দিরের ঐ গোপন ট্র্যাপডোর দিয়ে কোথায় যায়?
৫। হেলিপ্যাড কেন?
We must inform the police—দরকার হলে army আসুক—পুলিশ যদি ভূতের ভয়ে না আসে। নরবলি is murder—has to stop! এই অঞ্চলটা ভূতের হাতে নয়—আমার তো মনে হচ্ছে ডাকাতের হাতে।
আজ রাতে পুটুস হয়তো ভয় পাবে, সব কথা ছোটমাকে জানাতে হবে।
Infact বাবামাদের সব কথা খুলে বলাই উচিত। জানি না কোথায় কাদের আড্ডায় গিয়ে পড়েছিলাম আমরা। আরেকবার যেতে হবে। To investigate further—ভালো করে বড়দের সঙ্গে নিয়ে, in fact পুলিশফোর্স নিয়ে গিয়ে দেখতে হবে নরবলি কারা দিচ্ছে?—ঐ মুণ্ডুটা কার। ওর বডিটা কোথায় গেল?
এবং ওই trapdoor কী করে খুলল—ওই সুরঙ্গ সিঁড়ি দিয়ে কোথায় যায়? ওসব কবেকার জিনিস কে বানিয়েছে—historical importance থাকতে পারে—সুরঙ্গটা কে খুঁড়েছিল? কী জন্য? কোনখানে যাচ্ছে ওটা? আর ওই হেলিপ্যাড? আমার আর সন্দেহ নেই—after noticing the helipad, that we are in the middle of a huge conspiracy—মস্ত বিশাল কোনো ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়েছি আমরা—এখানে সামনে যা দেখছি—শুনছি তার চেয়ে যা দেখছি না, শুনছি না, সেটারই ওজন অনেক বেশি ভারী। ওই জমিজমার ownership. এই ভূতপ্রেত, ওই আড়িপাতা, spy—গিরি, প্রোমোটারদের জমি কেনা—বেচা, সবই জড়িত। May be trapdoor আর নরবলিও! Who knows? ঐ নরমুণ্ডুটা। আমাকে খুব ভাবাচ্ছে—where did the body go? অত তাড়াতাড়ি একটা গোটা মানুষের শরীর লুকিয়ে ফেলা যায় না।
নাকি শরীরটাই মুণ্ডু কেটে রেখে দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেছে? ভূতেরা সবই পারে।
ভূতই যদি থাকবে, তাহলে আমাদের ধরল না কেন? আমরা তো ভূতেরই খাদ্য। দুটি বাচ্চা ছিল, যারা ভূতে বিশ্বাসী—এবং শালফুলও, কিন্তু ভূতেরা were not interested in as—ধরেও নেয়নি, ভয়ও দেখায়নি। পুরো ignore করে গেল!
নাকি ওই নরমুণ্ড প্রদর্শনই ভয় দেখানো?
I suppose so!
রক্তাক্ত নরমুণ্ড বলির হাড়িকাঠের নিচে। দিনের বেলা। What can be more bizarre? Unbelievable! কিন্তু রক্তটা fresh ছিল না। কবে থেকে মুণ্ডুটা পড়ে আছে ওখানে? নাঃ, তা থাকবে না—হায়েনায় আর শেয়ালে আর বনবিড়ালে নিয়ে যেত। নাঃ আজই কাকু—ছোটমাকে বলতে হবে। টুলকি—পুলকি—বুলটুর গ্রুপ যথেষ্ট নয়। তারপর মা—বাবা। তারপর জেঠুমণি।
শালফুলকেও ডেকে বোঝাতে হবে। ওকে আমাদের আলোচনার মধ্যে রাখা উচিত। শুভকেও। কেউ ছোটো নয়—কেননা ওই দৃশ্য ওরা সকলেই দেখেছে। আর শুভ is very bright—নেমে এসে কী ছড়া কাটলো সে?
—”মন্দিরে আর যাবো না—
মুণ্ডু ফিরে পাবো না!”
‘ভয়’ একে বলে কি? ভয় হয় তো কিন্তু illogical নয়। ওর মনের জোরও অসাধারণ। শুভ আরও বলেছে—ফিরতে ফিরতে, আপনমনে, ছড়ায়—
”ওরে ওরে কাটামুণ্ডুর বডি
তোকে কোথাও দেখতে পাই যদি
একবারেতেই নেব চিনে
কাঁধের ওপর মুণ্ডু বিনে।”
তার মানে ওর মনটা খুবই বিচলিত। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকে ওটাকে প্রকাশ করছে। ভয়ের মধ্যে দিয়ে নয়। খুব আশ্চর্য মনের জোরে! ঐটুকু তো এগারো বছরের ছেলে!
পুটুস একটাও কথা বলেনি ফেরার পথে। ওর এই নিস্তব্ধতাটা আমার ভয় করছে। পুটুস খুব বেশিরকম ভয় পেয়েছে মনে হয়। শুভর ছড়াটড়া শুনেও নিজে ছড়া কাটেনি। চোখে ভাসছে রক্তমাখা হাড়িকাঠের সামনে রক্তমাখা কাটামুণ্ডুটা। ভাগ্যিস মুখটা মাটির দিকে ছিল, আমরা মাথার পিছনটুকু দেখেছি—মুখখানা দেখতে পেলে আরো ভয় করতো। কিন্তু What did they do with the body?
বাড়ি এসে পুটুস অদ্ভুত একটা কথা বলেছে কিন্তু। আমাকে পুটুস হঠাৎ বলল, —”ওই মুণ্ডুটা কি মাকালীর হাতে দেবার জন্যে কেটেছে? মাকালীর হাতে ঠিক ঐরকম মুণ্ডু থাকে, না দিদিভাই?”
কথাটা শুনেই আমার স্ট্রাইক করল। ওটা ঐ জটাচুলো কাটামুণ্ডুটা, সত্যিকার মুণ্ডু না হতেই পারে। How about a ‘কাটামুণ্ডু—পুতুল’? সত্যি সত্যি মাকালীর হাত থেকে যেমন ঝোলে? হতেই পারে What we saw was just a show! রক্ত তো fresh ছিল না—হয়তো ওটা একটা সাজানো ব্যাপার। কাল গেলেও এরকমই দেখা যাবে। দেখি, কাল আবার যাই—সদলবলে। দেখি কী হয়! আজ ওঁদের সার্ভে শেষ করে ওঁরা ফিরুন—তারপরে কথা হবে। ওখানে যে দেবীমূর্তিটা আমরা দেখেছি—পুলকি বলছে সেই মূর্তির বিষয়ে বইপত্রে কোনো mention নেই—আর এঁরাও তো বলেছেন ওখানে কোনো মূর্তি নেই। তবে ওটা এলো কেমন করে? প্রদীপ জ্বালছে কে? Who is lying here? আমরা তো স্বচক্ষে দেখে এসেছি মন্দিরে মূর্তি আছে। কালই আমরা শিবকাকাদের দেখিয়ে আনবো। কী কী প্রশ্ন আছে আমার, সবই ওঁদের জানাবো। ওখানে trapdoor—টাই বা হঠাৎ কেমন করে খুলে গেল? ওঁরা কি সত্যিই জানেন না, ওখানে সুড়ঙ্গপথ আছে? ওঁরা এখানকার বাসিন্দা! আশ্চর্য লাগছে।
কিন্তু শালফুল সত্যি জানতো না। শালফুল জানতো না মন্দিরে মূর্তি আছে। শালফুল জানতো না মন্দিরে নরবলি হয়। শালফুল ভীষণ nervous হয়ে পড়েছে। খুব ভয় পেয়েছে। শুভর চেয়েও অনেক বেশি। ওর ভয়টা সংস্কারের। পুটুস তো কথাই কইছে না। ওসব বলা বারণ বলেই বোধ হয়। বেচারীর shock লেগেছে। ওকে বলতে হবে মুণ্ডুটা আসলে মাটির ছিল। হোক, না হোক।
বুলটু
আমাদের আলোচনাসভাটা আজ ভালোই হয়েছে—শুধু আমাদের মিনিটে মিনিটে বাইরে গিয়ে spy search করতে হয়েছে—কাকুকে, আর আমাকে।
আজ spy ধরতে পারিনি। দোতলার ঘরে এসে কথা বলছি। বৈঠকখানাতে বসিনি। এঘরটার কাছে কোনও গাছটাছও নেই, এদিকে rainwater pipeও নেই—কাকু সব check করেছে—যেখানে spy বসে থাকবে।
সব বলেছি আমরা।
জেঠুমণি শকড—এবং মনে হল মাও, slightly, বাকিরা শকড নয়, excited—
সকলেরই মত ঐ মুণ্ডুটা real নয়, পুটুসের কথাটাই ঠিক, ওটা নিশ্চয় কালীমূর্তির হাতের মুণ্ডুই। জটামাথা কেন হবে নইলে? মুণ্ডুটা ঐ জন্যেই মাটিতে মুখ গুঁজে পড়েছিল। মুখ দেখলে তো বুঝতে পারবে, মাটির। ঘাড়ের রক্ত সব রঙ।
Helipad—এর সঙ্গে, কাকুমণি মনে করেছে trapdoor—এর কোনো যোগ আছে নিশ্চয়—সুড়ঙ্গ আছে। আমরা check করতে যাচ্ছি। আর এইসবের সঙ্গে আমাদের spy—এর যোগ।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে কীজন্যে ওরা ভূতের ভয় দেখিয়ে এতবছর ওদিকে মানুষজনকে ঘেঁষতে দেয়নি? কেউ তো জানেই না হেলিপ্যাডের অস্তিত্বের কথা, ওদিকে তো পুলিসেও যায় না নাকি। চোরাচালানীরাও যায় না। Spirit—কে ভয় পায় সবাই, গুলি দিয়ে যাদের মারা যাব না।—
কিন্তু ব্যাপারটা কী? শুভ বাড়ি গিয়ে কুট্টিকাকিমাকে বলে দিয়েছে মন্দির আর মুণ্ডুর কথা। সুড়ঙ্গ আর হেলিপ্যাডের কথা ও জানে না বলে বলেনি। কুট্টিকাকিমা তো ছুটে এসেছে মার কাছে। মা বলেছেন সব কথা। কিন্তু কাউকে বলতে বারণ করেছেন। আগে আমাদের investigation—টা হোক। কুট্টিকাকিমা বললেন তিনিও যাবেন সঙ্গে। শালফুল কিন্তু কাউকে কিচ্ছুটি বলেনি। শালফুল এবারে থাকবে। পুটুস আর শুভকে নিয়ে জেঠুমণি, বাবা—মা আর পিসিমণিও থাকবেন। পিসেমশাই, কাকুমণি, ছোটমা, কুট্টিকাকি আর কুট্টিকাকা যাবেন আমাদের তিনজনের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ জেঠুমণি এসে ঠিক করলেন আটজনের দল খুব বড়—চারজন ছেলে, দু’জন মেয়েই ঠিক। দুই কাকা এবং পিসেমশাই বললেন—এবারেও আমরা বাড়িতে কাউকে কিছু বলে যাব না—কুট্টিকাকাই তাঁর দাদাদের বলতে বারণ করলেন। বললেন তাঁদের এখনও কিছু জানাতে হবে না। পরে প্রয়োজন হলে বলা হবে। ওঁরা বারণ করে দিলে, আর তো যাওয়া যাবে না।—
আমরা দুটো ফোন নিলুম, পিসিমণি আর ছোটমার কাছে দুটা ফোন থাকলো। ওঁরা সবাই আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা করবেন যতক্ষণ না আমরা ঘুরে আসছি। রাত্রে নয়, আমরা এবারেও দিনে দিনেই যাবো, সকাল হলেই যাবো। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরবো। সেই ভালো।
ভোর ভোর বেরুবো ঠিক করেও সেই সূর্য উঠে গেল। কারণ পিসেমশাইয়ের ফোন। তাঁর একটা জরুরী ফোন আসবে সেটি না এলে উনি বেরুবেন না। কে জানে কোথায় network পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। আমাদের যতই ছটফটানি হোক পিসেমশাইকে তো কেউ কিছু বলতে পারি না—উনি বড় গম্ভীর মানুষ, কথা কম বলেন। ওঁকে ছেড়েও যেতে পারি না, উনি কিছুই চেনেন না।
শেষে এক সেকেন্ডের একটা ফোন এল, পিসেমশাইও আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওঁর এই ফোনাফুনির জন্যে পিসিমণি কেন যে এত রাগ করেন—এখানে এসেও এত ফোন—এখন বেশ বুঝতে পারছি।
কুট্টিকাকু বলছিল—”খুব strange happenings, একদম বিশ্বাস হচ্ছে না! শুভ যা যা দেখেছে বলল,—সে তো মারাত্মক! Unbelievable!”
—”সবাই দেখেছি আমরা।”
—”কিন্তু আমরা তো কখনও দেখিনি রে! আমরা এইখানেই খেলাধুলো করে বড়ো হলুম।”
—”কিন্তু ভূত তো দেখেছে সকলেই—এখানে সকলেই তো ভূতপ্রেতের অত্যাচারে উৎপীড়িত। সেটা তো দেখেছ?” পুলকি তর্ক জুড়ে দেয়।
কুট্টিকাকা তবুও বলতে লাগলো—”এ কিন্তু হতে পারে না—নিশ্চয় কোনরকম hallucination হয়েছে তোমাদের—এতসব নরবলির কাহিনী রঙ্কিণীদেবীর খড়্গটড়্গ চাদ্দিকে ভয়ানক সব কাহিনী শুনছে। পড়েছ তাই ওই পোড়া মন্দিরে অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে তোমরা imagine করেছো মূর্তিটুর্তি—ওসব কিসসু নেই—এই তো যাচ্ছি দেখতেই পাবে—”
—”পুলকি যে পড়ে গেল trapdoor—এর মধ্যে সেটাও imaginary?”
Trapdoor আর airport—এর কথা কুট্টিকাকা জানেন না। শুভ তো জানতো না। দেখেনি ও।
—”Trapdoor” ভীষণ অবাক কুট্টিকাকা। ”Trapdoor কোথায় পেলি আবার তোরা? নাঃ, রহস্য উপন্যাস পড়ে পড়ে তোরা ভীষণ imaginating হয়ে উঠেছিস—পাথরের মন্দির পাথরের মেঝে—এবড়োখেবড়ো, বিশ্রী—সেখানে আবার কোথায় trapdoor থাকবে?”
—”তুমি চল না তোমাকে দেখাচ্ছি—ওখানে নিশ্চয় টানেল আছে—আমরা আজ সেই টানেলটা investigate করব।”
”খবরদার! বুলটু, ওসব investigate ফেস করবার ধার দিয়েও যাবো না আমরা—এ হচ্ছে রঙ্কিণীর ডুংরি—যেমন আছে তেমনি থাক বাবা, বেশি ঘাঁটিয়ে কাজ নেই—মড়ক নামিয়ে দেবে দেশে”—
কুট্টিকাকার কথায় অবাক হয়ে পুলকি বলল ”No! You don’t believe in that রঙ্কিণীর খড়্গ story? রঙ্কিণীদেবী মড়ক নামাবেন কেন, শুধু মড়ক এলে warning দেন। ভালোই তো, তার সঙ্গে টানেল investigate করার কী যোগ? আমি যে গর্তে পড়ে গিয়েছিলুম সেখানে একটা বাতাস বইছিল—তাই মনে হয় ওর একটা দিকে opening আছে নিশ্চয়—গর্ত নয় সুড়ঙ্গ। টানেল। দেখতে হবে না কাদের সুরঙ্গ কোথায় যায়? আমার তো মনে হয়, হয় যাবে মল্লরাজার রাজবাড়িতে, নয় যাবে চিলকিগড়ে। রাজারাজড়াদের বৌ—ঝিরা হয়তো ওই পথ দিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে আসতো। গোপনে।
We must find out where it leads—”
—”পুলকি সোনা, ওসব dangerous games এখন না খেলাই ভালো। তোমরা দু’দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ। আনন্দ করে ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে যাও—সেধে সেধে উটকো ঝামেলায় জড়াতে যাবে কেন?”
—”ঝামেলা কেন হবে? তুমি তো বলছ সুড়ঙ্গও নেই, ট্র্যাপডোরও নেই। তবে তো মিটেই গেল।” বুলটু মন্তব্য করে—”ইনভেস্টিগেশন তো ওখানেই ফুরিয়ে যাবে। তোমার আর ভাবনা কিসের?” তবু কুট্টিকাকুকে মনে হল uncomfortable—হবেই তো! ছোটবেলার মন্দির!
সেদিন মন্দিরে মূর্তিটার একটা ছবি তুলে ফেলেছিলুম দিদিভাই উলটে পড়ার আগে—কিন্তু কাটামুণ্ডুর ছবি তোলার কথা মনেই আসেনি। এয়ারপোর্টটাও না। আজ ক্যামেরা নিয়েছি—যদি এখনও মুণ্ডু থাকে ছবি তুলবো। আজ কি আর থাকবে? বনের জন্তু—জানোয়ারে নিশ্চয়ই ওটা খেয়ে নিয়েছে overnight—উঃ, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!
বেচারী পুটুস! Hats off to শুভ, আবার ছড়া বানাচ্ছে কেমন! —ইয়ার্কি মারছে! —গান করছে, ”মুণ্ডু গেলে খাবোটা কী?” Strange guy প্রাণে ভয়ডর নেই। প্রথমে তো ভয়ে কাঠ হয়ে শালফুলের কোলে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখেই মনে জোর এসে গেল। আজও আসবার জন্যে জেদ করছিল, কুট্টিকাকার বকুনি খেয়ে থেমেছে। But I’m missing him—শুভটাকে আনলেই হত। He’s a sensible boy—entertaining too!
পিসেমশাই দেরি করে দিলেও, কেউ কিছু বলার নেই। পিসেমশাই সবচেয়ে চুপচাপ, সবচেয়ে গম্ভীর মানুষ। কাকু আর কুট্টিকাকু কাছাকাছি বয়েস—দুজনকে দেখলেই ভাই বলে বোঝা যায়। অদ্ভুত মিল আছে হাঁটাচলাতেও। আমরা রওনা হলুম। কুট্টিকাকু হঠাৎ বলল, ”বুলটুবাবু ক্যামেরা ট্যামেরা এনেছ নাকি সঙ্গে?”
কথার সুরটা আমার কেমন লাগলো, তাই সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললুম—”কেন গো? ক্যামেরা চাই?”
কুট্টিকাকু বলল, ”না, ওসব সঙ্গে না থাকাই ভালো। দামী জিনিসপত্তর, ঘড়ি, ক্যামেরা”—
—”ঘড়ি তো তোমার হাতেও রয়েছে।”
—”ভুল করে পরেই চলে এসেছি।”
—”কিছু হবে না কুট্টিকাকু। ভূতে কি ঘড়ি চুরি করবে? পরশু তো আমাদের কিছু হয়নি। Nobody bothered us! Neither ভূত nor robbers!
—”কিন্তু হাড়িকাঠের দৃশ্যটা—most strange story!”
—”ও বাবা! ওকথা থাক!”
—”ওই সুড়ঙ্গে ঢুকতেই হবে আজ” পুলকি বলল।
—”আমি ওর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু ভয়ের চোটে পালিয়ে এসেছি—ওটা explore করা হয়নি।”
—”ওসব সুড়ঙ্গ ফুড়ঙ্গে ঢুকে কাজ নেই পুলকি, কোথায় কী জীবজন্তু থাকে! সাপ তো থাকবেই, অন্য জন্তুও থাকতে পারে। সুড়ঙ্গের অন্য মুখটা কোথায়, তাও তো জানি না আমরা, কোনও জন্তু গুহা ভেবে বাস করতেই পারে ওর মধ্যে। না বাবা—আমি সুড়ঙ্গ explore করার বিপক্ষে। Its too dangerous!” কুট্টিকাকার reasoning গুলো ফেলে দেবার মতো নয়।
—”কিন্তু trapdoorটা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে খোলে, বন্ধ হয়—সেটা আজ জানতে হবে। তাছাড়া তোমরা তো এখনও বলছো মূর্তি নেই, আমরা কিন্তু মূর্তি দেখেছি। ভয়ংকরী। জটাজূটধারিণী—”
—”ভৈরবীমূর্তি। রঙ্কিণীর একটা ভৈরবী মূর্তি আছে”—পুলকি বলে।
—”কিন্তু সে তো এখানেই নেই, ঘাটশীলার মন্দিরে আছে।”
—”তাই তো পড়লুম বইতে”। পুলকি চেঁচায়। ”কিন্তু চলো না, কী দেখবে গিয়ে! মূর্তি রয়েছে, ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। নরবলি হচ্ছে—we saw it all!”
কুট্টিকাকু হাসলো। অবিশ্বাসের হাসি। হেসে হেসে কাকুমণির দিকে তাকাল। ভাবখানা এই—
—”দ্যাখো, এই বাচ্চারা কি ছেলেমানুষী করছে”।
কাকুমণি কিন্তু সেই হাসিতে যোগ দিলো না। কাকু বললো—”ওরা নিশ্চয়ই দেখেছে। চারজনে মিলে ভুল দেখতে পারে না। ওদের exaggerate করা স্বভাব নয়। খুব rational, cool-headed মেয়ে টুলকি—পুলকি দুজনেই। বুলটুটা ঠাণ্ডামাথা নয়, কিন্তু rational তো বটেই। শালফুলও ছিল। সেও তো দেখেছে। সবাই মিলে মিছে কথা বলছে কি? দেবীমূর্তি আছে। হাড়িকাঠ তো শুভও দেখেছে। কাটামুণ্ডুর ওপর ছড়া বানিয়েছে। শোনোনি?
—”মন্দিরে আর যাবো না/মুণ্ডু ফিরে পাবো না।”
—”ওইটাই উদ্দেশ্য, কাটামুণ্ডু ওখানে ফেলে রাখার।”
হঠাৎ পিসেমশাই বললেন, ”যাতে মন্দিরে কেউ না যায়—শুভর reaction—ই সবচেয়ে natural!”
কুট্টিকাকু কেমন একটা চোখে পিসেমশাইয়ের দিকে তাকান।
—”তার মানে?”
পিসেমশাই আর কিছু বলেন না। এগিয়ে যান। মন্দির সামনেই। আমরা এসে পড়েছি।
পুলকি
ভিতরে আজ প্রদীপ জ্বলছে না।
ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নয়, কেননা মন্দিরটা মাঝে মাঝে ভাঙা, ফাঁকফোঁকর দিয়ে আলো আসছে সামান্য। ভাঙা বেদী। টর্চগুলো জ্বলে উঠলো। কোনো মূর্তি নেই। প্রদীপ ট্রদীপ নেই।
সারা মেঝেয় উল্টোপাল্টা পাথরের টুকরো পড়ে আছে। হয়তো ভাঙা দেওয়ালের টুকরো।
কুট্টিমামা পিসেমশাইকে বললো—”কী দেখছেন? কী বললাম?”
সকলেই চুপ।
বুলটু চেঁচিয়ে ওঠে—”হতে পারে না। ইমপসিবল। কেউ মূর্তি সরিয়ে ফেলেছে। It was here!”
কুট্টিমামা বলে—”কেউ আসেনি বাবা এখানে তোমাদের পরে। তোমরাই তো last এসেছিলে।”
—”How do you know that?” বুলটু গোঁয়ারের মতো বললো। —”তুমি কি attendance খাতা রাখো? মন্দিরে কে কখন আসছে?”
টুলকির ঠাণ্ডামাথা? সে বললো—”কাকু, আমি বলছি, এখানে নিশ্চয়ই কোনো কারসাজি আছে—কোনো mystery নেই। We’ll find out what the trick is—Let’s try” বলেই মেঝের ছড়ানো পাথরগুলো নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দিল বসে পড়ে।
তাড়াতাড়ি কুট্টিমামা বললো—”ইসশ, ঐ পাথরগুলো কবে—এ থেকে পড়ে আছে! ওর নিচ থেকে বিছে সাপ বেরুবে—নাড়িস না! ফেলে দে, ফেলে দে! খুব বিপজ্জনক।”
কিন্তু দিদিভাই একটা একটা করে পাথর নাড়াচাড়া করছে—চাপ দিচ্ছে। হঠাৎ একটা পাথরে চাপ পড়তেই কুট্টিমামা নিজেই লাফিয়ে সরে গেল। কুটিমামার পায়ের নিচ থেকে গড়গড় করে উঠে আসছে একটা কিছু মেঝে ভেদ করে।
আস্তে আস্তে উঠে এলো দেবীমূর্তি। তার খানিক সামনে একটা পাথরের প্রদীপ। জ্বলছে না।
কুট্টিমামা চুপ। কেউই কিছু বলল না। মহাউৎসাহে আমরা তো আরও পাথর নাড়াচাড়া করছি—যদি trapdoorটা খুলতে পারি!
এদিকেই দিদিভাই হোঁটট খেয়েছিল না?
এই উঁচুমতো পাথরটাতেই লেগেছিল?
Let’s kick it—let’s see what happens!
আমি এক লাথি মারি উঁচু পাথারটায়।
অমনি হড়হড় করে মেঝে হাঁ হতে থাকে—প্রদীপসুদ্ধু পাথরটা নিচে নেমে যায়। আস্তে আস্তে সিঁড়ি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।
বুলটু নামতে যায়—ছোটমামু বলেন, ”দাঁড়া। সরোজকে আগে যেতে দে—এটা তো ওদেরই চেনা জায়গা।”
কিন্তু কুট্টিমামা নামতে রাজি নন। আর কাউকে নামতে দিতেও রাজি নন। হিংস্র জীবজন্তু, সাপখোপ এবং বিষাক্ত গ্যাসের ভয় পাচ্ছেন। বারণ করলেন আমাদেরও। বুলটু কি ভালো কথা শোনবার পাত্র? কথাবার্তা চলতে চলতেই সে নেমে গেল। কুট্টিমামা চটপট তার পিছু পিছু নামলেন এবার—টর্চ জ্বেলে। বাবা বললেন—”টুলকি—পুলকি আর আমি ওপরেই আছি—সৌম্য তুমি যাও।” ছোটমামুও নিচে নেমে পড়লো। বাবা কম কথার মানুষ বলেই বোধহয় বাবার কথা চট করে অমান্য করার অভ্যেস নেই কারুরই।
একটু পরেই নিচে একটা চীৎকার?
বুলটু চেঁচাচ্ছে—ARMS! ARMS! GUNS! TERRORISTS! ”
তারপরেই একটা আর্তনাদ।
সঙ্গে সঙ্গে একটা পেল্লায় ধমকানি। ফের সব চুপ।
একটু পরেই trapdoor দিয়ে কুট্টিমামাকে ঠেলতে ঠেলতে উপরে নিয়ে এলো ছোটমামু। কুট্টিমামার হাত দু’খানা তার পিঠের ওপর ঘুরিয়ে শক্ত করে ধরে রয়েছে ছোটমামু। ছোটমামু যে কুস্তি করে রবিঠাকুরের ছেলেবেলার স্টাইলে রোজ সকালবেলাতে, তা তো কুট্টিমামা জানতো না। পিছনে পিছনে বুলটু। টর্চ হাতে। ওকি! বুলটুর অন্য হাতে ওটা কী? টর্চ তো নয়?…পিস্তল? Real পিস্তল? কোথা থেকে পেলো? বুলটু ওটা কুট্টিমামার দিকেই তাক করে ধরে আছে। ”আমার gun কিন্তু loaded মনে রেখো, কুট্টিকাকা…” বুলটু বলল। বাবা ফোনে কাউকে কিছু instruction দিলেন।
ছোটমামু সজোরে জাপটে আছে কুট্টিমামাকে। বুলটু পিস্তলটা প্রায় বুকে ছুঁয়ে রেখেছে।
মিনিট কয়েকের মধ্যেই পুলিস ফোর্স মন্দিরে এসে পড়লো।—নিশ্চয় তারা ঘিরেই ছিল আমাদের already—নইলে এত দ্রুত আসতেই পারে না। তবে না পুলিস এদিকে আসতে ভয় পায়? কে ওদের খবর দিল?
বুলটু
কুট্টিকাকার কথা শুনবো না বলে মনস্থির করেছি। তাই আমি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলুম, যেই trapdoor—টা খুলে গেল,—টর্চ শক্ত করে ধরে—যাতে হাত থেকে পড়ে যায় না পুলকির মতো। নিচে নেমে দেখি, আরে, পুলকির টর্চটা তখনো মাটিতে পড়ে আছে। অর্থাৎ ইতোমধ্যে কেউ এখনও আসেনি এখানে—কেউ টের পায়নি এখানে আমরা এসেছিলুম। সিঁড়ির গর্তটা এখানেই শেষ। সুড়ঙ্গ শুরু হয়েছে ডাইনে। অন্ধকারে আমি সেদিকেই এগোতে থাকি। পিছনে পিছনে টর্চ নিয়ে কাকুমণি আর কুট্টিকাকা আসছেন। হঠাৎ কুট্টিকাকা ফিসফিস করে বললেন—
—”আর না! আমি গন্ধ পাচ্ছি—stop, stop right now!”
—”কিসের গন্ধ?”
—”বাস্তু সাপের। ঐ যে একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ, ওটাই তো সর্বনেশে। গোখরো সাপেদের meeting time—এর এই গন্ধ—এসময়ে সামনে যাকে দেখবে তাকেই ছোবল বসাবে—” বললেন কুট্টিকাকা।—”আমি যাচ্ছি ওপরে—”
—”কিন্তু”…কাকুমণি একটু ভেবে নিয়ে বললো—”ওটা তো তেমন মিষ্টি—মিষ্টি গন্ধ নয়? ওটা কীতপতঙ্গ মারবার ওষুধের গন্ধ। এরমধ্যে নিশ্চয় মানুষের বাস আছে। মশা বিছে, আরশোলা, মাকড়শা—এসব মারবার বিষের গন্ধ এটা। ট্রেনে আসবার সময়ে একটা বিক্রি করছিল বটে।”
—”এতে উইও যাবে। টিকটিকিও যাবে, বিছেও যাবে, মাকড়শাও যাবে—আর মানুষ, মানুষও—”
হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা insecticide—এরই গন্ধ—লেবু লেবু গন্ধ—ঠিকই তো? কাকুমণির কথায় মনে জোর পেয়ে গেলুম—কুট্টিকাকার কথায় কর্ণপাত না করে আমি এগোতে থাকি। হঠাৎ দেখি বাঁহাতে দেওয়ালের গায়ে মস্ত একটা কোটর। একটা ছোট ঘরের মতোই প্রায়—তাতে থাক থাক শেলফ। সেই শেলফে সারে সারে অস্ত্রশস্ত্র সাজানো। বন্দুক, মেশিনগান, পিস্তল, কার্তুজ সব। সব—বোমাও রয়েছে একধারে সাজানো—দেখে ভয়ের চেয়েও আমার আবিষ্কারের আনন্দই বেশি হল—আমি চেঁচিয়ে উঠি—”Arms! Arms! Terrorists কাকুমণি!”
তক্ষুনি কেউ পিছন থেকে আমার মুখে হাত চাপা দিল, পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে শক্ত গলায় বলল, ”একেবারে চুপ! নইলে শেষ করে দেব।” আর সঙ্গে সঙ্গে কুট্টিকাকা আর্তনাদ করে উঠল। আমার পিঠ থেকে বন্দুকও সরে গেল। আমি টুক করে পিছন ফিরে দেখি কাকুমণি কুট্টিকাকার হাত দুখানা শক্ত করে পিছনদিকে পিছমোড়া করে ধরে আছেন। পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেছে। Within seconds আমি পিস্তলটা তুলে নিই। কী হচ্ছে বোঝবার আগেই কুট্টিকাকু আরেকবার চেঁচায়—এবারে আর যন্ত্রণার আর্তনাদ নয়—”Help! Help!” চেঁচানি।
এবারে আমিই ওর পিস্তলটা ওরই পিঠে ঠেকিয়ে, বলি—”কুট্টিকাকা, shut up! or else—”
এবারে আর কুট্টিকাকা কোনও কথা বলে না। কাকুমণি ওর হাতে চাপ দিচ্ছে নিশ্চয়। কাকুমণি বলে, ”lets go back!”
আমি আরেকবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিই। থরে থরে অস্ত্র। পাণ্ডবরা যেরকম শমীবৃক্ষে অস্ত্র পেয়েছিল, এ যেন সেইরকম অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জায়গা। আমার মনে পড়ে গেল, পুরুলিয়াতে সাহেবরা, সেই যে পিটার ব্লিচ না কে যেন, এইরকম প্লেনে করে arms drop করত। ধরাও পড়েছিল। এটাও সাহেবদের ব্যাপার কিনা, কে জানে? Must be investigated further by the police—
কিন্তু কুট্টিকাকা?
কাকুমণি যে জিমন্যাস্ট এবং আমরা দুজনেই যে ক্যারাটে করি, —এসব খবর কুট্টিকাকা জানে না। জানলে হয়তো আসতেই দিত না। আমি পিছন থেকে টর্চের আলো ফেলছি—আর কুট্টিকাকাকে সিঁড়ি দিয়ে তাড়া দিয়ে উপরে তুলছে কাকুমণি। দুটো হাত পিছমোড়া করে পিছনে ধরে আছে বজ্রআঁটুনিতে—সেই হাত কুট্টিকাকার ছাড়ানোর উপায় নেই। দুটো হাতই মটমট করে ভেঙে যাবে তাহলে। পিঠে আমি ওরই পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে রেখেছি, ঠিক যেভাবে আমার পিঠে এক্ষুনি পিস্তল ঠেকিয়েছিল কুট্টিকাকা! আমরা উপরে উঠে আসছি আলোয়—ওপর থেকে টর্চ ফেলছে ওরা।
উঠে এসে দেখি পিসেমশাই তখনও ফোনে।
উঃ! এখানেও ক্লায়েন্ট? ম্যাড ম্যান! পুলকি আর দিদিভাই টর্চ ধরে আছে।
আমরা ওপরে উঠে আসতে আসতেই মন্দির ভরে গেল পুলিসে। তাদের হাতেই কুট্টিকাকাকে সমর্পণ করা হল।
কিন্তু পুলিশ এল কেমন করে?
এত তাড়াতাড়ি?
এখানকার পুলিস তো ভূতের ভয়ে এদিকে মোটে মাড়াবেই না। তবে এলো কেমন করে?
সব জানা গেল।
সবই পিসেমশাইয়ের ফোনে। ফোনই হিরো। সেই spy episode থেকেই সন্দেহ প্রবল হয়েছে পিসেমশাইয়ের। লালবাজারে inform করে দিয়েছেন—লোকাল নয়, বাইরে থেকে পুলিস ফোর্স এসেছে। তখন তো অস্ত্রশস্ত্রের কথা জানা যায়নি, তাহলে হয়তো মিলিটারিও নামানো যেত। এয়ারপোর্টের খোঁজটা পেয়েই পিসেমশাই ভয় পান। বড়সড় crime—এর সন্ধান পেয়েছিলেন তো তাই নির্ভয়ে পুলিস ডেকেছেন। কিছু না কিছু বেরুবেই উনি জানতেন। আর আজকে যে অত দেরি করে স্টার্ট করা হল—সেও ঐজন্যেই।
কাল ভোররাত্রে ঐ হেলিপ্যাডে পুলিসের হেলিকপ্টার নেমেছিল—পুলিসফোর্স এসে বনেজঙ্গলে লুকিয়ে মন্দির ঘিরে ফেলেছে—সেই খবরটি না নিয়ে, আমাদের সঙ্গে করে পিসেমশাই investigation—এ রওনাই হননি! আমাদের নিয়ে risk নেবেন না! পুলিসফোর্সের মোতায়েন হবার খবরের ফোনটি পেয়ে তবে আমাদের নিয়ে বেরিয়েছেন। ল’ইয়ার মানুষ, আটঘাট না বেঁধে কাজ করেন না।
এখন সব খবর শুনে বুঝলুম যে এদিকে কুট্টিকাকাও শিবকাকাদেরও খবর দিয়ে দিয়েছিল যে আমরা investigation—এ আসছি—তারাও জঙ্গলে তাদের আর্মড ফোর্স পাঠিয়েছিল, আমাদের ধরবে বলে। পুলিস তাদেরও সকলকেই গ্রেপ্তার করে ফেলেছে—including শিবকাকা and শঙ্করকাকা। শিবকাকা মন্দিরের পিছনেই ছিল, সুড়ঙ্গটার অন্য মুখে, যেখানটা এয়ারপোর্টের গায়ে। কিন্তু শঙ্করমামা এদিকে ছিলই না—তাকে ধরেছে খামারবাড়ি থেকে। তিনি বেচারী ধানখেতের পোকামাকড়ের খবরদারি করেছিলেন।
শিবকাকা I never liked, right from the beginning কিন্তু কুট্টিকাকা? খুবই অবাক হয়েছি—খুব shocked হয়েছি। ভাবতেও পারিনি he’ld be a part of a conspirancy of this order—দেশদ্রোহিতা তো? Illegal arms রাখা তো অনেকগুলো অপরাধের মধ্যে পড়ে—পিসেমশাই বলেছিলেন। এখানে বেশ জটিল পরিস্থিতি।
টুলকি
একজীবনে কত কী—ই ঘটে যায়। কত জীবনের রঙ লাগে। আমাদের এতটুকু জীবনে আমরা কত কিছু শিখে গেলুম। কত কিছু জেনে গেলুম এর মধ্যেই। একটা দীর্ঘ রহস্য—রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখা হয়ে যায় আমাদের এই ”লাহিড়ীবাড়ির রহস্য” নিয়ে। বুঝতে পারছি না কোথা থেকে শুরু করব।
প্রথমে বলি কীভাবে সেদিনকার মন্দির expedition সমাপ্ত হল।
পুলিসফোর্স এসে মন্দিরেই কুট্টিকাকাকে গ্রেপ্তার করলো। ওদিকে জঙ্গলে শিবকাকাকে। আর বাড়িতে অলরেডি শঙ্করকাকাকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ? গোপন অস্ত্রাগার তৈরি, ষড়যন্ত্র, সেখানেই বিদেশীরা হেলিকপ্টারে করে অস্ত্র রেখে যেত। শিবকাকা ট্রাকে করে সেসব বিলি করতেন।
১। শিবকাকার ধানকল আর ট্রাকের ব্যবসা কিছুই নয় অস্ত্রটাই আসল। তবে তিন ভাই—ই এর মধ্যে যুক্ত হয়ে পড়েছেন কিনা, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।
২। কুট্টিকাকার ব্যাপারটাই বোঝা কঠিন। এমনিতে এত ভালোমানুষ—উনি অস্ত্র ব্যবসায়ে আছেন, এটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যেটা আমাকে ছোটমা বলছেন সেটা বিশ্বাস হয়—সম্ভবত উনি বিপ্লবী ‘জনযুদ্ধ’ গোষ্ঠীর উপদেষ্টা সমিতির সদস্য—উনি হয়তো জনযুদ্ধের জন্য এখান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেন। —এটা হতেও পারে। সবই জানা যাবে একে একে। এই তো সবে শুরু। কুট্টিকাকা যে বুলটুর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়েছিলেন, সেটা তো সত্যি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।
৩। শঙ্করকাকা বেচারী সবচেয়ে ভালোমানুষ। ইনোসেন্ট বলেই মনে হচ্ছে। ব্যাপার স্যাপার দেখে সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেছেন। মনে হচ্ছে ভায়েরা ওঁকে কিছুই জানায়নি অস্ত্রশস্ত্রের কারবারের ব্যাপারে। টাকাকড়ির ভাগও নিশ্চয় দিত না। বড়কাকিমা, শালফুল সবাই ভেঙে পড়েছে। শঙ্করকাকার স্বপক্ষে কোনো কথাই বলছেন না।—”জয়েন্ট প্রপার্টি—সকলেই দায়ী।” এই কথা বলে উনি যে অপরাধ করেননি, তারও দায় স্বীকার করে নিচ্ছেন। পিসেমশাই এতে বেশ upset—I think he is going to do something positive about getting him out—জেঠুমণিও বোঝাচ্ছেন শঙ্করকাকাকে। তাঁর বেরিয়ে আসা উচিত। তাঁর মাকে, স্ত্রীকে, ছেলেমেয়েকে—ছোটভায়ের বৌ—ছেলেকে তাঁকেই তো দেখতে হবে। তিনি নিজেকে নির্দোষ বলুন। তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করা শক্ত হবে না। সত্যিই তো উনি বিন্দুমাত্র জানতেন না। ভাইরাও ওঁকে জড়াবে বলে মনে হয় না। বেচারী বড় কাকিমা। শালফুল আর লালটুকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন। আমরা তো ভেবেছিলুম শালফুলকে কলকাতায় নিয়ে যাব পড়াতে—এখন সে মাকে ছেড়ে যেতে চাইবে কি? তবে বিয়েটা ভেঙে গেল এটাই সুখবর। ওই প্রোমোটার আর প্রোমোটারের ছেলে—এখন সকলেই ধানবাদের জেলে। অন্য একটা গূঢ় অপরাধে ধরা পড়েছে। শিবকাকা কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন শালফুলের মতো মিষ্টি মেয়েটাকে! কেবল নিজের বিজনেসের সুবিধে হবে বলে! মানুষ যে কতটা স্বার্থপর হতে পারে, শিবকাকা তারই burning example, জ্বলন্ত উদাহরণ, বাবা। I’m very impresed indeed with নতুন ঠাকুমা। Gutsy lady—ছেলেদের গ্রেপ্তারিতে।
৪। নতুন ঠাকুমা একেবারেই ভেঙে পড়েননি। বলছেন, অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হয়। সে আমার ছেলেই হোক আর যে—ই হোক। নিয়মিত নিজের কাজকর্ম যথারীতি করে চলেছেন—গরুর দুধ দোয়ানো থেকে বেগুন খেতে পোকার ওষুধ দেওয়া পর্যন্ত। আশ্চর্য মহিলা, সত্যি! পুলকির ওঁর একটা বন্ধুত্ব হয়েছে। পুলকিকেই উনি ওঁর জীবনের সব গল্প বলেছেন। বাবার জ্যাঠামশায়ের গল্প। কেমন করে সন্ন্যাসী মানুষটি এসে ওঁকে বিয়ে করলেন, একেবারে একটা বনবালাকে? কেমন করেই বা ওঁরা এত জমিজমা সম্পত্তি পেলেন। সেও একটা রূপকথা? Another novel! পুলকি বলেছে লিখবে।
৫। আপাতত জানা গেছে, ট্রাকের কাঠের নিচে, সারা ভারতবর্ষে Terrorist-দের বন্দুক সাপ্লাই করতো শিবকাকার transport কোম্পানি। ভূতের ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছিল গ্রামের লোকজনদের, আর ঘুষ দিয়ে পুলিসের আর জরিপের লোকেদের। ওই কাটা মুণ্ডুটা মাটিরই ছিল আমরা চেক করেছি। হাড়িকাঠেও রক্ত মাখানো আছে। রক্তের কেসই নয়! দেবীমূর্তিটা বানিয়েছে অবিকল ঘাটশিলার মূর্তির নকলে, কপিকল করে লাগিয়েছে। ওখানে ধরে নিয়ে এসে ওরা বিদেশীদের ভয় দেখাতো। আপনি প্রতিমা উঠে আসতো—তারপর নরমুণ্ড দেখাতো—দেবীমূর্তি দেখাতো, ভয় পাইয়ে কাজ হাসিল করিয়ে নিত। বিদেশীরাও খুব ভীতু হয় দেখছি। সংস্কারাচ্ছন্ন হয়। বিদেশী তুকতাক জাদুটোনায় তাদের ভয়। যা জানে না, বোঝে না, মানুষ তাকে ভয় পায়। শিবকাকা তাদের কীভাবে ভয় দেখাতে হয় জানতো। শিবকাকাই যত নষ্টের মূল।
আমাদের ডাকাডাকি করতে সত্যিই চায়নি ওরা। নতুন ঠাকুমাই জোর করে বলেছেন—”আমি বেঁচে থাকতে থাকতে উইলের সুবন্দোবস্ত করে যেতে চাই।”
মায়ের কথার ওপরে কথা বলে না ছেলেরা। অতএব খোঁজো খোঁজো, লাহিড়ী বংশধরেরা কোনখানে।
জমির একটা বড়ো অংশ প্রোমোটারকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছিল অনেকগুলি হোটেল আর রিসর্ট বানানোর জন্যে। কিন্তু কাজুচাষের ব্যাপারটা তার বাইরে রাখতে চাইছিলেন নতুন ঠাকুমা। ওর মধ্যে যেমন ওদেরও জমি আছে আমাদেরও আছে কাজুবাগানের ভাগ। সেটা বোঝাবুঝি হয়ে যাওয়া ভালো। এখন তো সবই গোলমাল হয়ে গেল। রিসর্ট করছিল যে, সে নিজেই জেলে। জমি বেচা এখন অথৈ জলে চলে গেল। শালফুলের বিয়েও। শঙ্করকাকার এইটেতেই উৎসাহ ছিল—উনি শুধু এইটার কথাই জানতেন যে হোটেল, রিসর্ট হবে, টাউনশিপ হবে। অস্ত্রাগারের সংবাদ তাঁর অজানা ছিল। যেমন অজানা ছিল দেবীমূর্তি, কাটামুণ্ডুর অস্তিত্ব। বড়কাকিমা আর শালফুলকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল। এখন থাক। শঙ্করকাকা ছাড়া পাবেন নিশ্চয়ই—তার পরে আমরা শালফুলকে কলকাতাতে নিয়ে আসবো।
কুট্টিকাকিমার জন্যেও খুব কষ্ট হচ্ছে। কিছুই জানতেন না বেচারী ‘জনযুদ্ধের’ সঙ্গে কুট্টিকাকার যোগাযোগের কথা।
তাই দৌড়ে এসেছিলেন মায়ের কাছে শুভর মুখে নরমুণ্ডের খবর পেয়ে। শুভ আর কুট্টিকাকিমা মেদিনীপুরে ফিরে যাচ্ছেন, স্কুল খুলে যাবে দুজনেরই। ভাইদের জন্য মামলা লড়ালড়ি যা কিছু সেসব হবে এখান থেকেই। কোম্পানি করবে। উকিল টুকিল আছে। কুট্টিকাকিমা খুব আপসেট। প্রচণ্ড শক পেয়েছে। শুভও তাই। ছড়ার নদীটা শুকিয়ে গেছে।
জেঠুমণিরও খুব মনখারাপ। আশাতীত আনন্দের একটা glorious family reunion—এ আসছেন ভেবেছিলেন। যা ঘটলো সেটাও আশাতীত। আশাতীত লজ্জার। দুঃখের। ওদের এখন কী হবে? বাবা—মা জেঠুমণিকে বোঝাচ্ছেন। এত মনখারাপ কেন? এতদিন তো এরা ছিল না। শেষে নতুন ঠাকুমা ওঁকে ডেকে পাঠালেন।
জেঠুমণি অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলেন। যাবার আগে নতুন ঠাকুমাকে প্রণাম করে বললেন, ”জ্যাঠাইমা, আপনি তো একবারও এই ছেলের কাছে আসেননি। একবার চলুন। দেখবেন কত অল্প জায়গার মধ্যে একটুও সবুজ না দেখেও কত ঠাসাঠাসি করেও আমরা কেমন আনন্দে আছি। আমাদের যেমন বেশি বেশি কিছুই নেই, তেমনি চাহিদাও নেই। আপনার খুব ভালো লাগবে অল্প দু’একদিনের জন্যে গেলে। বেশিদিন বলবো না, বন্ধ ঘরে প্রাণ হাঁপিয়ে আসবে আপনার। তবুও ডাকছি, কলকাতা শহরটা একবার চোখে দেখবেন না? আপনার শ্বশুরবাড়ির দেশ?”
নতুন ঠাকুমা বললেন—”যাবো বইকি। ছেলে এত আদর করে ডাকছে, যাব না? আগে এদের ঝুটঝামেলা মিটুক? এখন তো সবদিক সামলাতে হবে আমাকেই।”
পুলকি
বড়মামু, মেজমামু, ছোটমামু—তিনজনেই একসঙ্গে তিলফুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা। ফ্যাবুলাস উওম্যান। তিলফুল সত্যিই খুব আশ্চর্য মেয়ে। উই আর ফ্রেন্ডস নাউ—আমরা দুজন বন্ধু। তিলফুল আমার চেয়ে পঞ্চাশ বছরের বড়ো হতে পারে, বাট শি ইজ আ ইয়ং উওম্যান অ্যাট হার্ট। অ্যান্ড ভেরি স্ট্রং। অ্যান্ড ভেরি অনেস্ট টুউ। তাই ওর ছেলেরা ওর কাছে ট্যাঁ ফোঁ করতে পারে না—অনেস্টির নিজস্ব একটা জোর আছে। শক্তি আছে। Goodness—এরও একটা নিজস্ব power আছে। তিলফুলকে দেখে সেটা বুঝতে পেরেছি। All her strength comes from goodness. যখন পুলিস—জেলহাজত—আইন—অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তুলকালাম, বাড়িময় যখন ওই প্রবল কেলেঙ্কারি চলছে, তারমধ্যেই হঠাৎ তিলফুল একদিন আমাকে বললেন, খুব মনখারাপ করে—”অপরাধ তো শুনেছি রক্তে খেলা করে। তাই লোধাদের ক্রিমিন্যাল জাতি বলে। ওদের বাবার তো রক্তে অপরাধ ছিল। যাবে কোথায়? ছেলেদের কী দোষ?”
—”তার মানে?” —আমি অবাক। তিলফুল depressed বলে আমি ওঁর কাছে কাছে থাকছিলুম, গানটান শোনাচ্ছিলুম। দিদিভাই শালফুল আর লালটুর মার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে। বুলটুও শুভর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। But they left in a hurry—কুট্টিমামিমা wanted to get out of here—উনিও সবচেয়ে বেশি hurt হয়েছেন—কুট্টিমামার ব্যাপার স্যাপার কিছুই জানতেন না কুট্টিমামী। সত্যি কি অদ্ভুত কাণ্ড, এই বিপ্লব—টিপ্লব। আমি কোনও সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করি না। বিপ্লবে বিশ্বাস করি, সেটা হবে চিন্তাভাবনার বিপ্লব। মার্কস, গান্ধী এঁরা বিপ্লবী। রবীন্দ্রনাথও তো রাখীবন্ধন করেছিলেন—he too was a বিপ্লবী in his own way—violence—এ বিশ্বাস করি না আমি। মানবতাবোধ এবং অস্ত্রশাস্ত্র, হানাহানি, একসঙ্গে যায় না। স্ত্রীপুত্রের কাছে অসৎ হয়ে কিসের বিপ্লব হচ্ছে?
কি আশ্চর্য!
তিলফুলও তাই বলছিলেন। লোধা—শবরদের নিয়মে ওরা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে দূর থেকে খাবার জন্যে জীবজন্তু যেমন শিকার করে, মানুষও নাকি মারতো তেমনি করে সেদিন পর্যন্ত। খাদ্যের লোভেই। তিলফুলের এই তীর ছোঁড়া ভীষণ খারাপ লাগতো যখন ছোটো ছিলেন, বেশ বুনো—বুনোই ছিল তখন ওঁদের আদিবাসী উপজাতির গোষ্ঠীটা। এখন আর নেই। এই ভূসম্পত্তিও ওঁর ছিল না। উনি তো যাযাবর জাতির মেয়ে। অন্য একজনের—একজন মাহাতোর—সম্পত্তি ছিল এটা। তিলফুলকে সে—ই দান করে গেছে—স্নেহে, ভালোবেসে। এর মালিক আসলে রঘুপতি মাহাতো। মাহাতোরা চাষবাস করে। মাহাতোদের জমিজমা থাকে। সাহেবরা কিনে নিয়েছিল অনেকটাই ওদের কাছ থেকে। রঘুপতি মাহাতোর খুব নামডাক ছিল। এই অঞ্চলের সর্দার ছিল সে—রাজার মতনই জোর তার জঙ্গলমহলে।
সেই রঘুপতি একবার ট্রেনে করে কোথায় যাচ্ছিল, যখন কলেরায় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে, ট্রেনেই একজন সাধু ছিলেন—তিনি ওকে অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। রঘুপতিকে গ্রামে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন তিনি। ওঁকে হাতেপায়ে ধরে নিজের গ্রামে আশ্রম করে থাকতে বলে। সবাই তাঁকে এটা ওটা কিছু না কিছু দেয়, সেবা করে। লোধাদের তো কিছুই নেই। তারা গরিব। তাদের মেয়েটি ওঁর রান্নাবান্না করত, ঘরদোর পরিষ্কার করে দিত। আস্তে আস্তে কী যে হল, সন্ন্যাসী সন্ন্যাস তাগ করে সেই লোধা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলেন। সন্ন্যাসী রীতিমতো ইংরাজী জানেন—জঙ্গলমহলে শিক্ষিত লোক কেউ তো ছিল না—তিনি থেকে যেতে রঘুপতি মাহাতোর অনেক সুবিধা হল। রঘুপতির ছেলেপিলে ছিল না—নিঃসন্তান। রঘুপতি মহানন্দে নিজে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীকে বর সাজিয়ে তিলফুলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন আর সম্পত্তি দান করলেন কন্যাকে যৌতুক হিসেবে। বাকিটা বড়দাদু নিজের চেষ্টায়, ব্যবসাবুদ্ধিতে বাড়িয়েছেন। এত জমিজমা সবটা তিলফুলের যৌতুকে পাওয়া জমি নয়, কাজুবাদামের মস্ত বাগানটা সবটাই যৌতুকের অংশ,—আর ঐ সুন্দর সোনাঝুরি বনটাও তিলফুলের। আর অনেকটা শালমহুয়ার জঙ্গলও।
—”তা এতে অপরাধের কী আছে? রঘুপতি মাহাতোর ট্রেনে কলেরার মতো ভীষণ অসুখ করেছিল, সন্ন্যাসী তার সেবা করেছেন এ তো মহাপুণ্য—এতে অপরাধ কিসের?”
তিলফুল মাথা নাড়লেন।
অপরাধটা সেখানে নয়।
অপরাধ তার অনেক বছর আগে। সন্ন্যাসী হবার আগে। উনি ওঁর বাবার সঙ্গে প্রবল ঝগড়া করে, মার গয়নার বাক্সটা চুপিচুপি চুরি করে পালিয়ে এসেছিলেন। সুরাটে হীরের ব্যবসা করে ভেবেছিলেন বড়লোক হয়ে দুগুণ ফেরত দেবেন। কিন্তু ব্যবসা ডুবে গেল—গয়নাগাঁটিও খতম। ওঁদের বাবা মারা গেলে—খবর রাখতেন সবই—বড় দাদু আর ঘরে ফিরলেন না। মনের কষ্টে, লজ্জায় সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।
বাবা মারা যাবার পরেও লজ্জায় মা—কে মুখ দেখাতে পারেননি। মায়ের মৃত্যুর পরেই ছোটভাইয়ের কাছে গেছেন। গিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর চুরির খবর কোনোদিনই কেউ কিচ্ছু জানতে পারেনি।
বড়দাদু পালিয়ে যাবার পরে গয়নার কথাটা তাঁর মা কাউকেই কিছু বলেননি। গয়নাচুরির ব্যাপারটা অনেক পরে ঘটেছে বলে জানিয়েছিলেন তাঁর মা। ছেলেকে চোর বলে জানতেও দেননি পৃথিবীকে।
সন্ন্যাসী অবস্থায় তিনি বাড়িতে ফিরেছিলেন আমাদের দাদু—ঠাকুমার কাছে। তখন তাঁর মা, বাবার ঠাকুমা আর ছিলেন না। মাকে মুখ দেখাননি উনি লজ্জায়। এত বড় চুরি করে তাঁর জীবন শুরু—এসব কলঙ্কের কথা তিনিই পরে তিলফুলকে জানিয়ে গিয়েছেন। ছোটভাইকে সম্পত্তির পঞ্চাশভাগই দেবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। তার মায়ের যথাসর্বস্ব তো তিনিই চুরি করে পালিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওই ত্রিশেরই হিসেব করেছিলেন—এবং কাজুবাগানের পঞ্চাশভাগ।
তিলফুল স্পষ্ট করে এসব কাহিনী আমাকে বলছিলেন দুপুরবেলায় মাদুরের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে জাঁতি দিয়ে হরিতকি কাটতে কাটতে। এখানে আমলকির আর হরিতকিরও প্রচুর গাছ আছে।
আমার কাছে তো টেপরেকর্ডার ছিল না। কিন্তু আমার ফোনটাতে খানিকটা টেপ করা যায়। এসব কথা আমি টেপ করতে চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু হল না ঠিকমতন। তাই যা যা তিনি বলছিলেন, আমার ঘরে ফিরে এসেই নোট করে ফেলেছি—best I forget something! খবরটা দিদিভাইকে বুলটুকে না বলা পর্যন্ত প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে। কী যে করি!
তিলফুল আমাকে ওঁর জীবনের অনেক গল্প বলেছেন—এটা আমি ওদের বলেছি। কিন্তু কী গল্প, সেটা বলিনি। কী করে যে বলব?—একথা তিলফুল আর আমি ছাড়া জগতে কেউ জানে না। তিলফুল বলেছেন—বড় ঠাকুর্দা যে সন্ন্যাসী হবার আগে তাঁর মায়ের গয়নার বাক্স চুরি করে সুরাটে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেইসব কথা কোনদিনই তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের জানাননি। আমাকেই প্রথম বললেন। বলতে বলতে তিলফুলের চোখ দিয়ে জল অঝোরে পড়ছিল। ছেলেরা জানে না যে তাদের বাবা চুরি করেছিলেন। তারা যে অপরাধ করেছে, সেটা সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বেই করেছে। বাবার অপরাধের কাহিনীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, লোভে।
কিন্তু তিলফুল ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছেন। ভেবেচিন্তে পিসিমণিদের খবর দিয়েছেন, তাঁর যমজ মেয়ে গঙ্গা—যমুনাকে। তাঁরা দু’একদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন। আমরা যখন চলে যাবো, তখন তাঁরা থাকবেন তিলফুলের কাছে।
এখন আমি কী করি?
দিদিভাইকে বলি? বুলটুকে? মাকে? বাবাকে? নাকি বড়মামুকে বলবো? He is the eldest of us all—মনস্থির করতে পারছিলুম না। সমাধান তিলফুলই করলেন। কী করে টের পেলেন?
—”তুই এখানে এখনই কাউকে কিছু বলিস না। কলকাতায় ফিরে যা, গিয়ে বলে দিস। ওটা জানার পরে ছেলেরা হয়তো আমার দিকেও তাকাতে লজ্জা পাবে—”
আমিও তাই ডিসাইড করেছি, এখনই বলব না। তিলফুলের এই কাহিনীতে আমাদের অনেক প্রশ্নের বকেয়া উত্তর মিলে যাচ্ছে।
১। কেন উনি মায়ের ছবি নিয়ে সন্ন্যাসী হতে গেলেন?
উঃ—কেননা উনি সন্ন্যাসী হতে যাননি, হীরের ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন সুরাটে।
২। কেন ছবিটা আধখানা ছেঁড়া?
উঃ—কেননা উনি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেই চলে এসেছিলেন—হয়তো পরে আধখানা রেগেমেগে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।
৩। সন্ন্যাসী কেমন করে শবর লোধাদের মেয়েকে বিয়ে করল?
৪। কেমন করেই বা এত ভূসম্পত্তি পেলেন?
তিলফুলের গল্পে আমাদের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। কলকাতায় যাই, গিয়ে ওদের সব জানাবো।
এদের টাটা সুমো নয়।
এবারে আমাদের কোয়ালিসেই ফিরছি আমরা। একটু ঠেসাঠেসি করে। বড় বড় চার বস্তা (বস্তা মানে huge সব প্লাস্টিকের ব্যাগ আর কি) ভর্তি করে কাজুবাদাম দিয়েছেন মা—দের চার ভাইবোনকে তিলফুল। ঝুড়িভর্তি ফল। আতা, পেয়ারা। পেঁপে, কলা, নারকেল। গরমকালে নাকি আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, জামরুল সব পাঠাবেন। গোলাপজামের গাছও দেখলুম অনেকগুলো আছে বাগানে। পুকুরের মাছও দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গন্ধ হবে, ice নেবার জায়গা নেই বলে নিতে রাজি হলেন না বড়মামু।
তিলফুলের মন—কেমন করছে। বড্ড দুঃসময়ের মধ্যে ওঁকে ফেলে যাচ্ছি আমরা। বাবা বলছেন তিনি তিলফুলের লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্সটা দেখবেন। বড়কাকার ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই দেখবেন। বাকি দু’জনের দায়িত্ব নিতে পারবেন না।
শালপিয়ালের বন মহুয়ার গন্ধ পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে। মন কেমন করছে—কিন্তু আবার আসবো তো। তিলফুল বলে দিয়েছেন পৌষপার্বণে আসতে। ‘নাওয়াই’ মানে নবান্ন হবে, তারপর ‘সোহরায়’ পরব। আর সংক্রান্তির দিনে আছে ‘টুসু’ পরব। মকরস্নান হবে, তখন মেলা বসবে—সারারাত্রি টুসুর গান গাওয়া হবে—”মেদিনীপুরে দেখ্যে আইলম/সোনার টুসু যায় চলে/হায়রে হাতে নাইরে পইসা/লিতম টুসু দর কর্যে।” গানটা শিখে ফেলেছি শালফুলের কাছে। এবছরেও কি মেলা বসবে?
—”কর্তারা দোষ করেছেন, তাঁদের তাই পুলিসে ধরেছে। তাই বলে কি গ্রামের মানুষের পালাপার্বণ আটকে থাকবে?” তিলফুল বললেন—”তা তো হয় না, তোরা চলে আসবি, নাচ দেখবি, গরু খেলা দেখবি, মেলার সময় ফুর্তি করবি!”
বড়মামু বলছিলেন আসতে আসতে—
—”জীবন যে অনেক বড়ো, জ্যাঠাইমার কাছে সেটাই শিক্ষণীয় ছিল। অনেক শিখলুম এই বয়সে—”
তা তো ওঁদের অনেকটা জানা বাকি আছে এখনও। কলকাতায় গিয়ে বলবো।
আকাশে গুমগুম শব্দ শুনে সকলেই চমকে মুখ তুলে তাকাই। না, হেলিকপ্টার নয়, অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন, রঙ্কিণীদেবীর রাজ্যপাট ছাড়িয়ে। অচেনা কোনো দেশের দিকে।
***