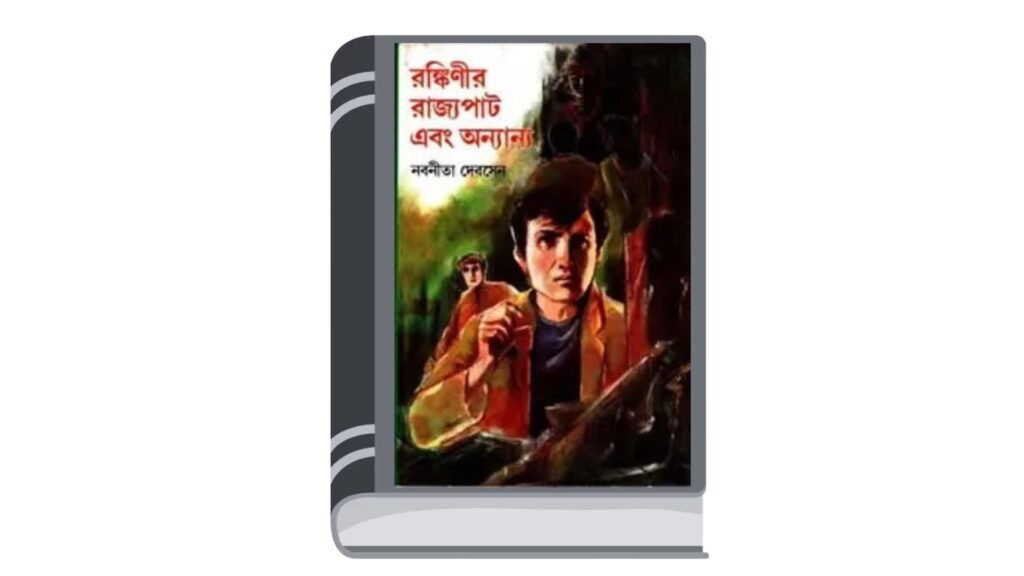লোভী চাষীর গল্প – নবনীতা দেবসেন
লোভী চাষীর গল্প
এক গ্রামে দুই ভাই থাকত। তারা ছিল চাষী। তাদের মা—বাপ ছিল না। দুই ভাই একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে রাঁধে বাড়ে খায়। একসঙ্গে মাঠে চাষ করে। কিছুদিন পরে, দাদার বিয়ে হল। বউ এসে বললে, তোমার ছোটো ভাইয়েরও তো বউ আসবে। সে এসেই বলবে, তার আলাদা রান্নাঘর চাই। তার চেয়ে এখনই আমাদের আলাদা আলাদা বাড়িতে থাকা ভালো। আলাদা আলাদা মাঠে চাষ করা ভালো।
দুই ভাইয়ের মাঠ আলাদা হয়ে গেল। দুই ভাইয়ের রান্নাঘর আলাদা হয়ে গেল। মাঠে যখন ধান বোনার সময় হল, ভাই গেল দাদার কাছে বীজধান চাইতে। গোলা তো তখনও আলাদা হয়নি। দাদা বললে বউকে, ‘ভাইকে বীজধান দিয়ে দিও তো বউ!’
এদিকে বউটা ছিল সত্যি দুষ্টু। সে একদম পছন্দ করত না ছোটো ভাইকে। সে দুষ্টুমি করে করল কী, ধানগুলো আগে সেদ্ধ করে নিয়ে তারপরে ভাইকে দিল মাঠে বুনতে। সেদ্ধ করা ধানে কিন্তু আর ক্ষেতে গাছ হয় না! ভাই তো জানে না তাকে সেদ্ধ করা বীজধান দিয়েছে তার বউদি। মাঠে ধান গাছই হল না! কেবল একটিমাত্র ধান ভুল করে হাঁড়িতে পড়েনি, ধামাতেই লেগে ছিল, তাই মাত্র একটি ধানগাছ জন্মাল।
ছোটোভাই খুব পরিশ্রমী—সে ওই একটা গাছকেই খুব যত্ন করতে লাগল সারাদিন ধরে। ওর যত্নে ভালোবাসায় ধানের চারাটি বেড়ে উঠতে উঠতে, বেড়ে উঠতে উঠতে, সত্যিই একটি গাছ হয়ে গেল আর তাতে যে ধানের শিষটা ধরল, তা বটগাছের মতো ছড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পুরো খেতটাকে ছায়া করে ফেলল। (আরেকটু হলেই সে দাদার ক্ষেতেও ছায়া দিয়ে ঢেকে দিত, ধান আর হত না!) এতবড়ো ধানের শিষ কেউ দেখেনি। ধান কাটার সময় হল, ছোটোভাই ধান গাছে উঠে কুড়ুল দিয়ে ধানের শিষটা কাটল। ধানের শিষটা মাটিতে পড়বামাত্র, ছোটভাই তখনও গাছ থেকে নামেনি, একটা বিশাল বড়ো ঈগলপাখির মতো পাখি এসে সেটা ঠোঁটে তুলে নিয়ে উড়ে গেল।
”আরে আরে আরে—’ ভাইটি ছুটল পাখির পিছু পিছু—পাখি যায় আকাশে আকাশে চাষী যায় মাটিতে মাটিতে। এমন করে চাষী পৌঁছে গেল এক্কেবারে সাগরতীরে। এবারে পাখিটি নেমে এল।
মানুষের গলায় চাষীকে বলল, ‘এই একটা ধানের শিষ দিয়ে তোমার আর কী হবে? এই সমুদ্রে সোনা রুপোর দ্বীপ আছে। আমি তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি? সেখানে গিয়ে তুমি এই ধানের দাম নিয়ে নিয়ো? ধানটা আমার খুব দরকার।’
চাষী তখন পাখির পিঠে উঠে বসল। পাখি বললে, ‘চোখটা বন্ধ করো দেখি? নইলে ভয় পাবে, পড়ে যাবে।’
চাষী চোখ বুজে ফেলল শক্ত করে। জোরে জোরে বাতাস কেটে পাখি উড়ে চলেছে—আর সেই বাতাসের প্রবল শব্দ শোঁ শোঁ করে চাষীর কানের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে—ওদিকে নিচে উত্তাল সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে—চাষী শক্ত করে পাখির ঘাড়ের কাছটা জড়িয়ে রইল। যেন একটা প্রবল ঝড়ের ভিতরে উড়ে যাচ্ছে সে—ভয়ে বুক ঠাণ্ডা—এমন সময়ে পাখি বলল, ‘চোখ খোলো, এসে গেছি। নেমে পড়ো।’ বলতে বলতে পাখি শোঁ করে নেমে এসেছে একটা মস্ত বড়ো পাথরের ওপরে।
চাষী চোখ খুলল। দেখল ততক্ষণে রাত্তির নেমে এসেছে। কিন্তু রাত্রি নামলে কী হবে—দিনের আলোর মতো ঝলমল করছে চারিদিক—সোনার আর রুপোর নুড়ির টিবি বিছিয়ে রয়েছে দ্বীপময়। সেই সোনা—রুপোর ঝলকানিতেই আলো হয়ে আছে দ্বীপটি!
ছোটোভাইকে পাখি বললে, ‘এই তো, তোমার ধানের শিষের দাম নিয়ে নাও এখান থেকে।’
ভাইটি তখন দু’হাতে দু’মুঠো সোনার নুড়ি দিয়ে ধুতির খুঁটে বাঁধল।
‘ওতেই হবে?’
‘হ্যাঁ হ্যাঁ ঢের হবে—মোটে একটাই তো শিষ!’
‘খুব ভালো।’ পাখি বললে, ‘অল্প চাইলে আর কোনোদিন চাইতেই হবে না।’
তারপরে চাষীকে পিঠে তুলে নিয়ে পাখি তার বাড়িতে পৌঁছে দিল।
পৌঁছে ভাই দ্যাখে আবার ভোর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ তো স্বপ্ন নয়, তার খুঁটে বাঁধা আছে সোনা—রুপোর নুড়ি!
চাষী গেল হাটে। নতুন ধুতি কিনল, চাল, ডাল, ঘি, কিনল, আর কিনল আরেকটা মস্ত জিনিস, আরেকটি ধানক্ষেতের জমি, আর বীজধান। নতুন করে ধানক্ষেতে ধান বুনলো চাষী। প্রবল উৎসাহে খাটতে লাগল। দেখতে দেখতে পরিশ্রমের ফসল ফলল, বছর ঘুরতেই—রীতিমতো বড়োলোক হয়ে গেল সে।
ব্যাপার দেখে দাদা—বৌদির হিংসে হয়ে গেল। দাদা বললে, ‘তুই একদিন রাত্তির বেলায় কোথায় যেন চুরি ডাকাতি করতে গিয়েছিলি, ভোর বেলাতে ফিরলি সোনারুপো নিয়ে। আমরা সব জানি। তুই চোর। তোকে পুলিশে দেব।’
ভাই দাদাকে সব কথা বললে। শুনে বৌদি বললে, তুমি কেন পাখির কাছে যাও না? আমি আবার বীজধান সেদ্ধ করে দেব। কেবল একটি ধান এবার না হয় খেয়াল করেই বাঁচিয়ে রাখব। তুমি সেটি বুনবে। সারাবছর যত্ন করবে। তোমারও নিশ্চয় ওই রকম হবে।’ যেমন বলা তেমনি কাজ।
সেই ধানবৃক্ষ হল, তাতে একটিমাত্র শিষ যেন ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ল। কাটা—মাত্রই সেই পাখি এসে শিষটি ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে উড়ে গেল। দাদা তো মহাখুশি—সেও ছুটতে থাকে মাঠ পেরিয়ে পাখির পিছু পিছু। অবিকল আগের মতোই হল। তাকে নিয়ে পাখি সোনারুপোর দ্বীপে উড়ে চলল। চাষী সেখানে পৌঁছে দ্যাখে—বাঃ, নানান সাইজের সোনারুপোর পাথর আছে! ছোট ছোট নুড়িও আছে, উটের মতো বড়ো পাথরও আছে। আরও বড়ো পিপের মতো পাথরও রয়েছে। কোনটা নেবে? কেমন করেই বা নেবে? বড়োগুলো তো নেওয়া যাবে না! চাষী বেচারির লোভে মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে সোনা রুপো সবটাই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে না ভেবে হাপুসনয়নে কাঁদতে শুরু করে। পাখি তাড়া দেয়, ‘নাও নাও চটপট যা নেবে নিয়ে নাও—রাত যে কাবার হতে চলল।”
চাষীর বউ তাকে একটাই থলি দিয়ে দিয়েছিল সঙ্গে। চাষী তাতে যত পারে সোনারুপোর ইট ভরেছে, কিন্তু তাতে আর জায়গা নেই। তাই চাষী এখন কোঁচড়ে বাঁধছে।
পাখি বললে, ‘ঢের হয়েছে। আর না। বেশি বেশি লোভ ভালো নয়।”
কিন্তু চাষী বলল, ”আরেকটু দাঁড়াও, ধুতিটা খুলে তাতে করে সোনারুপো বেঁধে নিই পুঁটলি করে। অনেক নেওয়া যাবে।’
কিন্তু তক্ষুনি পুব আকাশে চোখ রাঙিয়ে উঁকি দিলেন সূয্যিদেব। আর ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল পাখিও। লোভী চাষীর আর ঘরেই ফেরা হল না। সে এখনও সোনারুপো গুনছে আর পুঁটলি বাঁধছে—দ্বীপান্তরে, একা—
অতি লোভ করলে নিজেরই ক্ষতি হয়। বেচারি লোভী চাষীর বউও একলাটি হয়ে গেল। তারও আর কেউ রইল না।
আহা গো, লোভ বড্ড মন্দ জিনিস।
কাকচরিত্র
বেলুনমামা এসেই এক—একটা গল্পো ফাঁদেন, তাই রুবাই—বুবাইয়ের খুব ভালো লাগে বেলুনমামা এলে। সেদিন বাড়িতে দারুণ হইচই চলছে। দাদাভাই শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা থেকে একটা বই কিনে এনেছে, তার নাম ‘কাকচরিত্র’। তাতে লেখা আছে কাক কোথায় বসলে মানুষের কী হয়। কবে, কখন, কতবার কা—কা ডাকলে আমাদের কী—কী হয়। অমাবস্যা রাত্রের তৃতীয় প্রহরে একটি সর্বসুলক্ষণা কাকিনী ধরে তার হৃৎপিণ্ড আস্ত বের করে নিয়ে পুড়িয়ে খেলে মানুষ নাকি বশীকরণ মন্ত্র শিখে যায়—তখন সে যা চাইবে তাই পাবে। যাকে যা করতে বলবে সে তাই করবে। দাদাভাই আর তার বন্ধুরা মিলে ওর ঘরে বসে বেজায় হুল্লোড় করছে। দাদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এক এক লাইন পড়ছে; আর বাকিরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে।
মা বললেন, ”ধুৎ! এসব এখনও হয়? ছ’টাকা দিয়ে শুধু শুধু এই বই কিনে আনলি? তার চেয়ে কিছু নতুনগুড়ের লবাৎ কিনলে কাজে দিত।”
”কেন, খারাপ কিসের? এত মজা হচ্ছে যে, তার বেলা? এটাই বা কম কী?” দাদাভাই তর্ক জুড়ে দেয় মা’র সঙ্গে।
মা ওদের জলখাবার খেতে টেবিলে আসতে বলছিলেন। বেলুনমামা অলরেডি সেখানে বসে রুবাই—বুবাইদের সঙ্গে চা জলখাবার খাচ্ছিলেন। ওরা উঠে গেলে দাদাভাইদের দল বসবে। বেলুনমামা বললেন, ”কাকচরিত্র? নাঃ, আজকাল আর ওসব কাকচরিত্র—ফরিত্র কোনও কাজ করে না। অবসোলিট হয়ে গেছে। আগে করত।”
গল্পের গন্ধ পেয়েই রুবাই সোজা হয়ে বসেছে। এক চুমুকে গ্লাসের দুধ শেষ। ”আগে কীরকম করে কাজ করত গো বেলুনমামা? বশীকরণ হত?”
বেলুনমামা অদ্ভুত করে হেসে বললেন, ”কেন হবে না? বশীকরণ তো আজও হয়। এখনও হয়। আকচারই হচ্ছে। ওই সবের একাল—সেকাল নেই। ওরে, বশীকরণের কি একটা মন্তর? সহস্রটা! কাকচরিত্রেরটা তো ভীষণ কঠিন। ওতে রক্তারক্তি ব্যাপারও আছে। কত সহজ, সরল, সুন্দর উপায় আছে বশীকরণের। লোকে সেসব জানলে তো?”
”কেউ জানে না বেলুনমামা? ওই তো, বইটা যারা পড়বে তারাই জেনে যাবে তো?”
”না রে বুবাই, আমি ওই বটতলার চটিবই পড়ে বশীকরণ শেখার কথা বলছি না। তবে হ্যাঁ, কাকেরা সোজা পাত্র নয়। কাকেরা খুব জ্ঞানী। ওরা অনেক কিছু জানে। ভুশুণ্ডিকাকের নাম শুনেছিস তো? সর্বজ্ঞ কাক। হনুমান, বিভীষণ, অশ্বত্থামা, এদের মতো ভুশুণ্ডিকাকও অমর। আসল কাকচরিত্রের বশীকরণ মন্তর—টন্তর সব ওই একা ভুশুণ্ডিকাকই জানে। এ কি আমাদের ছাদে বসে যারা কা—কা করে, তাদের কম্মো?”
বুবাইয়ের ধৈর্য ধরছে না, ”কিন্তু ওই ভুশুণ্ডিকাকের বাসাটা কোথায় বেলুনমামা? তার সঙ্গে দেখা হবে কেমন করে?”
”ভুশুণ্ডিকে কেমন দেখতে? এমনি কাকের মতোই? নাকি তার মাথায় পাকাচুল আছে?”
রুবাইয়ের আর একটু ডিটেলের দিকে নজর। ”ওকে আমরা চিনতে পারব কেমন করে?”
বেলুনমামা বললেন, ”ভুশুণ্ডিকাককে চেনা খুব সোজা। আমার সঙ্গে তো অনেকবার দেখা হয়েছে। দেখলেই প্রণাম করবি, হাতজোড় করে বলবি, ”দাদুভাই, প্রণাম।’ দেখবি, ভুশুণ্ডিদাদু তোদের ‘থা—ক, থা—ক’ বলে কেমন সুন্দর আশীর্বাদ করবেন, ডানা নেড়ে নেড়ে।”
”কিন্তু কাকে প্রণাম করব? চিনব কেমন করে? সব—কাকাই তো একরকম দেখতে। বুড়োকাক আর ছোটকাকে তফাত বুঝতে পারি না তো?” রুবাই—বুবাই সমস্যায় পড়ে যায়।
”ভুশুণ্ডি তো বুড়ো হয় না রে, সে চিরতরুণ, এই আমার মতো।” বেলুনমামা তাঁর একমাথা রং করা কালো চুল নেড়ে দেখান। বেলুনমামা যে সত্যি—সত্যি মায়ের দাদা, সেটা বিশ্বাস হয় না। কী সুন্দর দেখতে, যেন ছোটভাই।
হইহই করে দাদাভাইরা খাওয়ার ঘরে চলে এসেছে বইসমেত। ওরা এখনও হাসছে। ”পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করতে হলে কী করতে হবে?” ঝান্টুদা জিজ্ঞেস করল, ”ওতে আছে?”
”দাঁড়া, দেখি, এই যে।” দাদাভাই পড়তে শুরু করে, ”কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে সূর্য অস্ত যাইবার পনেরো মিনিট পরে একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত কাক ধরিয়া তাহার গলায় লাল সুতার একটা তাগা বাঁধিয়া দিন। সুতাটি সাতটি গিট দিয়া বাঁধিবেন। এবারে কাকটিকে খাচায় পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিন। রোজ সকালে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া দু’ফোঁটা মধুর সঙ্গে দু’ফোঁটা চা পাতার রস মিশাইয়া কাকটিকে খাওয়াইবেন। এইভাবে তিনদিন তিনরাত্রি গত হইলে খাঁচা হইতে কাক বাহির করতঃ গলার সুতা খুলিয়া লইয়া কাকটিকে উড়াইয়া দিন। এবারে সুতাটি নিজের ডান হাতের কবজিতে ( যদি বাঁ হাতে লেখেন, তবে বাম কবজিতে) বাঁধিয়া লউন। এইবার পরীক্ষায় বসিলে আপনার সাফল্য লাভ হইবেই হইবে।”
”যদি একাধিক পরীক্ষা থাকে তবে প্রতিটি পরীক্ষার জন্য এক—একটি পৃথক কাক চাই। এবং প্রতিটির সহিত একই ক্রিয়া কর্তব্য। সাতটি পত্র পরীক্ষা দিলে, সাতটি খাঁচা ও সাতটি কাক লাগিবে। হিসেবমতো তিনদিন পরপর কিন্তু কাকগুলিকে উড়াইয়া দিতে হইবে। এই প্রণালী অতি সরল।”
দাদাভাই পড়ছে, আর দাদার বন্ধুদের সঙ্গে মা—ও হাসতে শুরু করেছেন। বেলুনমামা কিন্তু একটুও হাসছেন না। সেই দেখে, বই খুলে দাদা বলল, ”বেলুনমামা, তোমার বাড়িঅলার সঙ্গে মামলা চলছিল না? জিতবেই জিতবে, যদি এই পলিসিটা ফলো করো। মন দিয়ে শোনো। ”যে কোনও মঙ্গলবার অপরাহ্ণবেলায় সূর্যাস্তের পূর্বেই আটার রুটির টুকরার সহিত গাওয়া ঘি ও কাশীর চিনি মাখিয়া ছোট—ছোট মণ্ড বানাইয়া একটি কাককে খাওয়াইতে থাকুন। সম্ভব হইলে একটি চেনা—পরিচিত কাককেই খাওয়ানো ভালো। যেদিন কোর্টে যাইবেন, ওই কাকের পিঠের একটি পালক তুলিয়া পকেটে করিয়া লইয়া যাইবেন। সেইটি অপর পক্ষের উকিলের গায়ে বুলাইয়া দিতে হইবে। মামলায় আপনার জিৎ সুনিশ্চিত করিতে আরও একটি কাজ বাকি, আপনার শত্রুর বাঁ পকেটে পালকটি গুঁজিয়া দিবেন। এর ফলে শত্রুপক্ষ মামলা তুলিয়া লইবে। অথবা রায় আপনারই পক্ষে যাইবে।—কি বেলুনমামা, আছে তোমার কোনও চেনাপরিচিত কাক? যে তোমাকে পিঠের পালক প্রেজেন্ট করবে?”
বেলুনমামা দাদাভাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন দু’মিনিট। তারপর বললেন, ”আচ্ছা। ওই যে রুবাই—টুবাইকে বলছিলুম, ভুশুণ্ডিকাক। তিনি আছেন। চাইলেই পিঠের পালক দিয়ে দেবেন। কিন্তু আটার রুটি কি ছোঁবেন তিনি? আতপচাল ছাড়া চলে না তো?”
দাদাভাই হেসে উঠল, ”নাঃ, সত্যি বেলুমামার তুলনা নেই! বেলুনমামা জিন্দাবাদ!”
ঝান্টুদাটা আরও পাজি, সে বলে ওঠে, ”আর ভুশুণ্ডিমামা? ভুশুণ্ডিমামা দি গ্রেট জিন্দাবাদ।”
”ও তোদের জিন্দাবাদের অপেক্ষা করে না ঝান্টু। ভুশুণ্ডিকাক নিজেই তো চিরজীবী, ওর মৃত্যু নেই।”
”ও বাবা! মৃত্যু নেই এমন কাকের কি পালক খসে? নিশ্চয়ই খসে না, বেলুনমামা। তুমি অন্য কাক ধরো। পালকটা খুব জরুরি কিনা?”
”ও কাকচরিত্র—ফরিত্র পড়ে আজকাল আর কিসসু হয় না, আমি একবার চেষ্টা করেছিলুম ছেলেবেলায়। তোদের মতো বয়সে।—সে এক কেলোর কীর্তি হয়েছিল।” বেলুনমামা চায়ে চুমুক দিলেন আয়েস করে।
দাদাভাইয়ের দল এবার চমৎকৃত।
”তুমি চেষ্টা করেছিলে? কী চেষ্টা? সত্যি—সত্যি ধরেছিলে? কাক ধরতে পেরেছিলে?”
”না পারার কী আছে? কাকেরা জাতপেটুক। ওরা যতই বুদ্ধিমান হোক, ফাঁদে পা দিয়ে দেয় ঠিক। ওই যে আছে, লোভে পাপ, পাপের মৃত্যু। তা হলে বলি? বলেই ফেলি। শোন আমার বশীকরণ শেখার গল্প। আমারও একটা ‘কাকচরিত্র’ বই ছিল। এমনি চটিবই নয়, ট্রেনে আর মেলায় ফিরিকরা বই নয়। রীতিমত কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে কেনা মরক্কো লেদারে বাইন্ডিং করা, সোনারজলে মলাটে লেখা, ‘কাকচরিত্রম’। তাতে সবই সংস্কৃতে মন্ত্র লেখা ছিল—নো বাংলা গুরুচণ্ডালী জালিয়াতি। সে ছিল আসল কাকচরিত্রম। দুটো—একটা শ্লোক এখনও মনে আছে আমার—ধর, কাকেরা কোন সময়ে কী করলে তার তাৎপর্য কী হতে পারে। ধর, যদি অষ্টম দণ্ডে, মানে আটটার সময়ে ঈশান কোণে কাক হা—হা ধবনি করে, তবে কী হয়? ‘অষ্টম দণ্ডে ঐশ্যাণ্যাং হাহা রবো যদা রটতি/কাকস্তদা মরণবার্তাং কথয়তি।’ বুঝলি তো? তা হলে কাক মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে। ওই যে, মরণবার্তাং কথয়তি। আবার যদি, ‘নবম দণ্ডে ব্রহ্মস্থানে যাযা রবো যদা রটতি/কাকস্তদা প্রার্থনাবার্তাং কথয়তি।’ অর্থাৎ সকাল ন’টার সময়ে মাথার তালুর উপরে কাক যদি এসে যাঃ যাঃ বলে ডাকে, তা হলেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়, মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এসব পড়তে হয় জানতে হয়, বুঝলি? অমন বটতলার বই পড়লে কিসসু শেখা যায় না।”
”তোমার মনস্কামনা পূরণ হয়েছিল, বেলুনমামা? মাথার তালুর উপরে কাক এসে যাঃ যাঃ বলে ডেকেছিল?”
”কোথায় আর ডাকল বল? মাথার উপর কাক উড়ে এলে আমরাই তো তাকে যাঃ যাঃ বলে তাড়িয়ে দিই। কাক আর যাঃ যাঃ বলার চান্স পাচ্ছে কখন? মাথার উপরে যদি তিনি কম্মো করে দেন, সেই ভয়েই তো সবাই আগে তাকে তাড়াবে। তার মনস্কামনা পূরণের সুযোগই মিলবে না বেচারি কাকের।”
”তুমি যে বললে কাক ধরেছিলে, জাল পেতে ধরেছিলে বুঝি?”
”কাক ধরেছিলুম তো বলিনি! বলেছিলুম, কাক না—ধরতে পারার কী আছে? কাকগুলো জাতপেটুক। ওদের লোভ দেখিয়ে জালে আটকে ফেলা খুব সহজ। যতই বুদ্ধি থাকুক, ওরা ভুল করে ফাঁদে পা দিয়েই ফেলে প্রথমবার। দ্বিতীয়বার আর জীবনে দেবে না অবশ্য।”
”তুমি জানলে কেমন করে? তুমি দেখেছ?”
”দেখিনি। অমনি করেই তো ভুশুণ্ডির সঙ্গে আলাপ। ওই কাকচরিত্রম পড়ে, বশীকরণ শিক্ষা করব বলে আমি ছাদে পাখি ধরার জাল পেতে রেখেছি, কাক ধরব। জালে চড়াইপাখি, পায়রা, শালিক, এমনকি বুলবুলি পাখি পর্যন্ত ধরা পড়ছে, টিয়া, ময়না কিচ্ছু বাকি নেই। কিন্তু নো ক্রো! আমি পাখিদের ধরছি আর ছেড়ে দিচ্ছি। পাখিকে বন্দি দেখতে আমার ভালো লাগে না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় বিপুলবপু একটি দাঁড়কাক জালে ধরা পড়ল। দাঁড়কাক কলকাতা শহরে বেশি দেখা যায় না। আমি তো ভয়ে—ভয়ে কাছে গেছি। বিশাল চেহারা, খুব গম্ভীর, রাশভারী হাবভাব, আর কী কালো কুচকুচে, তেলচুকচুকে গা। দেখলেই বুকটা কেমন—কেমন করে। ওই কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো নয়। আমাদের পাতিকাকেরা বেশ ঘরোয়া দেখতে, গলা—বুকটা ধূসর, স্বভাবটা ছটফটে, সাইজেও ছোট। ইনি তেমন নন। আমার দিকে যেই ঘাড় কাত করে লাল—লাল চোখে তাকাল, আমার বুক ছমছম করে উঠল। মোটাগলায় কাক বললে, ‘ক্কঃ ক্বিম?’ অর্থাৎ ‘কী? ব্যাপারটা কী?’
”ভয়ে—ভয়ে আমি বললুম, ‘এবারে আপনার গলায় আমি সাতপাক দিয়ে একটা কালো সুতো বাঁধব। তাতে চোদ্দটা গেরো দেব। তারপর আপনাকে গঙ্গাজলে নাইয়ে, শুদ্ধ করে, আপনার গায়ে রক্তচন্দন আর সিঁদুর লেপন করব। এখন মোটে বেলা পাঁচটা, এখন কিছু করার নেই, ঠিক রাত বারোটা বাজলে আমার এই কাঁচা আম ছাড়ানোর ছুরিটা দিয়ে আপনার হৃৎপিণ্ড বের করে এনে অঙ্কের স্যারের বাড়ির সদর গেটের সামনে পুঁতব। তারপর আপনার বাকি শরীরটুকু কোনও নির্জন পরিচ্ছন্ন জায়গায়, মানে আমাদের বাগানে পুঁতে রেখে রোজ সেখানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসব, পরপর তেরো রাত্তির। আর হাজারবার করে এই বশীকরণ মন্ত্রটা জপ করব, ‘ওঁ হ্রীং ক্লীং অঙ্কস্যারং বশীকরণং ভবতু ওঁ স্বাহা!’ তা হলে চোদ্দদিনের দিন অঙ্কস্যারের সুমতি হবে, আমাকে পাশ নম্বর দিয়ে দেবেন।
দাঁড়কাক সব শুনে বলল, ”ক্কক?” অর্থাৎ ‘ব্যস? এই?’ তারপরে জালের মধ্যেই একটা ঠ্যাং একটু তুলে আমাকে ভরসা দেওয়ার মতো করে বলল, ‘ক্কক্কেন ক্কাক্কিম্ ক্কক্কম্ ক্কক্কঃ!’ আমি দিব্যি বুঝতে পারছি ও কী বলছে। বলছে ‘ব্যস, এই জন্য তুমি আমাকে মারবে? প্রাণিহত্যার পাপ করবে? আমি তো তোমাকে এমনিতেই পাশ করিয়ে দিতে পারি। এত কষ্ট করতে যাবে কেন?’ দাঁড়কাকটা মনে হল হাসছে, ‘ক্কক্ক্যাঃ ক্কক্ক্যাঃ’ বলে। আমি বললুম, ‘কেমন করে আপনি আমাকে পাশ করিয়ে দেবেন?’
”কাক বলল, ‘তোমার মাথায় বুদ্ধি বাড়িয়ে দিয়ে। যাতে তোমার অঙ্ক কষায় মন বসে যায়। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। দেখবে, ঠিক তোমার অঙ্ক পরীক্ষার সময়ে আমি আসব।’ আমার কীরকম মনে হল, একেই ওই সুন্দর আমকাটা ছুরিটা দিয়ে খুনখারাপি করার ইচ্ছে ছিল না—ইন ফ্যাক্ট খুনখারাপি করারই ইচ্ছে ছিল না—তাই কাকের অনুরোধ পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলুম।
”দাঁড়কাক বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দিলেই দেখবে তোমার অঙ্ক কষায় মন বসে গেছে। এসব জাদুটোনার দরকার হবে না। কেবল পড়ার টেবিলে বসে এই মন্ত্রটা আওড়াবে, আর অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে, তা হলেই অঙ্কস্যারকে বশীকরণ করা হয়ে যাবে—এই আমি শ্রীশ্রীমহাভুশুণ্ডিকাক তোমাকে বর দিচ্ছি।”
”আমি তো জাল থেকে ওর পা ছাড়িয়ে দিলুম। ভুশুণ্ডিকাক বললেন, ‘আমার হৃৎপিণ্ডটি তুমি কেটেকুটে বের করতে পারতে না, বৎস। ওটি অজর, অক্ষয়। নন—ব্রেকেবল। ইনডেস্ট্রাকটিবল। আমার হৃদিভঙ্গও হয় না। হৃৎপিণ্ড উৎপাটনও করা যায় না। তোমার বৃথা অনেক পরিশ্রম হত। বরং মন দিয়ে অঙ্ক কষো গে। দেখবে জলের মতো সরল হয়ে গেছে।’ এই বলে উড়ে গেলেন শ্রীশ্রীমহাভুশুণ্ডিকাক। আমিও আর কখনও ‘কাকচরিত্রম’ বইটা ছুঁইনি। তোরাও ফেলে দে।”
”তোমার অঙ্কের রেজাল্ট কেমন হয়েছিল বেলুনমামা? তোমার অঙ্কস্যার কী বললেন?”
”আমার খাতা দেখে তো অঙ্কস্যারের চক্ষু ছানাবড়া। ফুল মার্কস, একশোয় একশো! তোদের মাকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখ না—”
”মা, মা! বেলুনমামা অঙ্কে ভালো ছিলেন, না খারাপ?”
মা রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলেন, ”অঙ্কে? কেন রে? তোদের মামা স্কুল ফাইনালেও অঙ্কে ফুল মার্কস পেয়েছিল—বলছে বুঝি অঙ্কে কাঁচা ছিল? ছোট্ট থেকে মেজদা ম্যাজিকের মতো অঙ্ক কষে ফেলত।”
বেলুনমামা চোখ টিপে বললেন, ”ওই তো, শুনলি। ওটা কিন্তু ভুশুণ্ডিকাকের বরটা পাওয়ার পরবর্তী ঘটনা। তার পরবর্তী ঘটনা তোর মা জানে না—ছোট ছিল তো? সেটা বড়দাকে জিজ্ঞেস করিস!” বলে বেলুনমামা মাছের চপে কামড় বসালেন।
হইহই করে দাদাভাই এতক্ষণে বলল, ”কী বোকা রে তোরা? অঙ্কে কাঁচা হলে কেউ ফিজিক্সের প্রফেসর হতে পারে? বেলুনমামার মতো?”
বুড়োবুড়ি আর দুষ্টু মোড়ল
এক বুড়ো আর তার বুড়ি বনের মধ্যে বাস করতো। তাদের কুঁড়েঘরের মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ছে, তাদের পাতার ছাউনিটুকু এখানে ওখানে খসে খসে পড়ছে, তাদের শুকনো ঘাসপাতা জ্বালানো উনুনে মাটির হাঁড়িতে বুনো কচু সেদ্ধ হয়। বুড়ি পুকুর থেকে সুষনি—কলমি শাক তুলে আনে মাঝে মাঝে। একটু একটু ভাতও তো খাবে? সেজন্যে টাকা চাই, বাজারে যেতে হবে। বুড়ো—বুড়ি বনের শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে বাণ্ডিল বেঁধে বাজারে নিয়ে যায় বিক্রি করতে। অল্প বয়সে বুড়ো ছিল কাঠুরে। এখন আর সে কাঠ কাটতে পারে না। বনের গাছ কাটা বারণ—গাছ কাটলে মা বসুমতীর কষ্ট হয়, আকাশে আগুন ছোটে, নদীর জল ফুরিয়ে যায়—কাঠুরে বুড়ো তাই কাঠকুড়ুনি বুড়ো হয়েছে।
একদিন ওদের কিছু শুকনো ডালপালা জোটেনি—এদিকে ঘরে চাল নেই—কী হবে? বুড়ো তার কুঠার নিয়ে বেরুল কাটার মতন একটা গাছ খুঁজতে। যদি একটা বাজে—পোড়া পোকায় ধরা গাছ পাওয়া যায়। খুঁজতে খুঁজতে একখানা গাছ পাওয়া গেল। বাজ পড়ে তার মুণ্ডুটা উড়ে গেছে। বুড়ো যেই কুড়ুলখানা তুলে ধরেছে, গাছ বলে উঠলো, ‘আমাকে কেটো না, সবাই ভাবে আমি মরে গেছি, কিন্তু আমি মরিনি গো! চেয়ে দ্যাখো, দুখানি ছোটো ছোটো পাতা গজিয়েছি আবার!’
বুড়ো ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখে, তাই তো? শুকনো—টুকনো পোড়াঝোড়া গাছটাতে এই তো বেরিয়েছে একটি কচিডাল, তাতে দুই সবুজ সবুজ কচিপাতা! বুড়োর খুব মায়া হল। আহা, জ্যান্ত তো? সে গাছটি না কেটেই ফিরে চললো।
হঠাৎ শোনে গাছ তাকে পিছন থেকে ডাকছে, ‘কাঠুরে ভাই, ও কাঠুরে ভাই, শুনে যাও।’ ডাক শুনে বুড়ো কাঠুরে আস্তে আস্তে গাছের কাছে ফিরে এলো। গাছ তখন বললে, ‘আমার কোটরের মধ্যে একটা জালা আছে, সেটা তোমাকে দিলুম। নিয়ে যাও, তোমার কাজে লাগবে।’
কাঠুরে মস্তবড়ো জালাটি পিঠে করে বাড়িতে নিয়ে এলো। বউকে বললো, ‘বউ, এটা বেশ ঝেড়ে—ঝুড়ে পরিষ্কার করে দাও, হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে আসি। যা পাবো, তাতে চাল, তেল চিনি সবই কেনা যাবে।’
বুড়ি তখন খুব যত্ন করে জালাটি পরিষ্কার করতে বসলো। মস্ত বড় ভেতরটা ঝাঁট দেবে বলে ঝাঁটা নিয়ে যেই বুড়ি ঢুকেছে, হঠাৎ হাত থেকে ঝাঁটাটি পড়ে গেল। অমনি দ্যাখে ম্যাজিক। ঝাঁটার পরে ঝাঁটাতে জালার ভেতরটি ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর ঝাঁটা জড়ো হল। বুড়ো—বুড়ি হাটে গিয়ে ঝাঁটা বেচতে শুরু করলো। তাদের পেটে এখন আলুভাজা, ডাল, ভাত। মাছের ঝোলও হয় মাঝে মাঝে। সুখেই ছিল দুজনে—একদিন বুড়োর হাত থেকে একটা রুপোর টাকা জালার মধ্যে পড়ে গেল। অমনি—ওরে বাববা, এ কি কাণ্ড? জালাটা যে রুপোর টাকাতে ভর্তি হয়ে উঠেছে? দেখতে দেখতে জালা ভরে টাকা মেঝেতে উপচে পড়লো।
বুড়ো—বুড়ি মহানন্দে থাকে। ফলের দিনে ফল খায়, গুড়ের সময়ে গুড় খায়, মাছ কেনে, মাংস কেনে, খাট—বিছানায় ঘুমোয়, কাঁসার থালাতে খায়। গ্রামের লোকেরা ভাবে বুড়ো—বুড়ির হল কী? আর তো ঝাঁটা বেচতে আসে না? বুড়ো—বুড়ি মরলো নাকি? তারা খোঁজ করতে এসে দ্যাখে বুড়ো—বুড়ি মনের সুখে বসে ব্যাটারি চালিত টিভি দেখছে। তাদের আর মাটির কুটির নেই, পাকা বাড়ি। বুড়ির গায়ে বেগমবাহার শাড়ি, বুড়োর পরনে ফরাসডাঙার ধুতি। গ্রামের লোকদের আদর—যত্ন করে চা খাওয়ালো, মিষ্টি খাওয়ালে বুড়ি।
গ্রামের মোড়ল ভাবলো এত টাকা—কড়ি এলো কোথা থেকে? এরা তো ছিল হদ্দ গরিব মানুষ, বুনো কচু—সেদ্ধ খেয়ে থাকতো। চালে খড় ছিল না, ঘরের মধ্যে বৃষ্টি পড়তো। ব্যাপার কী?
তখন বুড়ো বললে, ‘সবই ওই জালার জন্যে। ওই মরা গাছটাকে কাটতে গিয়ে জালাটা পেয়েছিলুম ওর কোটরে। গাছ মরেনি, আমরাও বেঁচে আছি। গ্রামের যার যত টাকা লাগবে আমাদের এসে বললেই আমরা দিয়ে দেবো। জালার টাকা ফুরোয় না। তোমাদের আর কোনো চিন্তা নেই।’
কিন্তু গ্রামের মোড়ল মানুষটি অত সরল সোজা নয়, তাছাড়া তার ছিল একটু লোভী স্বভাব। বুড়ো—বুড়ির জালাভর্তি টাকা দেখে মনে লোভ হল, সে ভাবলো জালাটা চুরি করবে। কিন্তু অত বড়ো জালাটা নিয়ে যাবে যে, সবাই তো দেখে ফেলবে। তাহলে আর চুরি করা হবে না। তাছাড়া টাকাভর্তি জালাটা তো বেদম ভারী, ওটা পিঠে তোলাই যাবে না। তার চেয়ে টাকা—পয়সা ঢেলে রেখে শুধু জালাটাই নিয়ে যাওয়া ভালো, পরে তো আপনা—আপনি ভর্তি হয়েই যাবে। দরকার হলে, মোড়ল ভাবলো, বুড়ো—বুড়িকে মেরেই ফেলবে। তা না হলে জালা নেবে কেমন করে?
বুড়ো—বুড়ি যেই রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছে, মোড়ল এসে জালা খালি করতে শুরু করলো।
এদিকে জালাটি কিন্তু বুড়ো—বুড়িকে চিনে ফেলেছে। তাই, মোড়ল জালা খালি করছে দেখেই সুড়ুৎ করে ফাঁকা করে ফেললো নিজেকে।
মোড়ল শূন্য জালা পিঠে নিয়ে গ্রামে চললো। পথে একটা মিনি বেড়াল তাকে জিজ্ঞেস করলে, ‘মোড়লমশাই, মোড়লমাশাই, তোমার পিঠে কী?’
মোড়ল বললে, ‘জালা নিয়ে গ্রামে যাচ্ছি , ভরবো গাওয়া ঘি!’
একটু পরে এক প্যাঁচা গাছের ওপর থেকে ডেকে বললে, ‘মোড়লমশাই, মোড়লমশাই, তোমার পিঠে কী?’
মোড়ল বললে, জালা নিয়ে গ্রামে যাচ্ছি, ভরবো গাওয়া ঘি!’
প্যাঁচার বুদ্ধিও খুব প্যাঁচালো। সে মিনি বেড়ালের মতো বোকা নয়। তার কী মনে হলো সে মোড়লের পিছু পিছু উড়তে উড়তে চললো।
প্যাঁচাকে যেতে দেখে বেড়ালও সঙ্গে সঙ্গে চললো পা টিপে টিপে, বেড়ালরা যেমন যায়। নিঃশব্দে। মোড়ল বাড়ি গিয়ে জালাটি দালানে নামিয়ে রাখতেই একটা ইঁদুর লাফিয়ে জালার মধ্যে পড়েছে। আর যাবে কোথায়? বেচারি মোড়লের ঘি খাওয়া উড়ে গেল, দেখতে না দেখতে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার নেংটি ইঁদুরে ভর্তি হয়ে যেতে লাগলো জালা। কাণ্ড দেখে তো প্যাঁচা আর মিনিবেড়াল সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো নেমন্তন্ন খেতে। দুজনেই ইঁদুর ধরতে এক্সপার্ট—তারা ইঁদুর ধরছে, ইঁদুর মারছে, আর মনের আনন্দে ইঁদুর খাচ্ছে। খেতে খেতে তাদের পেট ভরে গেল। তখন তারা বনে ফিরে গিয়ে তাদের যত আত্মীয়—স্বজন, বন্ধু—বান্ধব, সক্কলকে নেমন্তন্ন করে এলো—যত খুশি ইঁদুর খাবার নেমন্তন্ন।
অত ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে ওদিকে মোড়লের বউ তার বাচ্চাদের নিয়ে মায়ের কাছে পালিয়ে বেঁচেছে—ইঁদুরের রাজত্ব চলেছে, ঘরে যা পাচ্ছে তাই কেটে কুচি কুচি করছে ইঁদুরের দল। মোড়ল ভয়ে উঠোনের কাঁঠালগাছে চড়ে বসে রইলো।
এদিকে দলে দলে বেড়াল আসতে লাগলো মোড়লের বাড়িতে, আর রাত পড়তেই ঝাঁকে ঝাঁকে প্যাঁচা। বেড়াল—প্যাঁচাতে—ইঁদুরে এমন প্রবল ঝাপটা—ঝাপটি শুরু হয়ে গেল যে তাদের ঠেলাঠেলিতে জালাটাই ভেঙে গেল। য্যাঃ!!
বেড়াল আর প্যাঁচারা এতদিনে মোড়লের বাড়ির সব ইঁদুর খেয়ে শেষ করে এনেছে। জালা তো নেই, তাই আর নতুন ইঁদুর তৈরি হচ্ছে না। কিন্তু ভয়ের চোটে মোড়ল এখনও সেই কাঁঠালগাছেই বসে আছে—নেমে আসবেই বা কোথায়? তার কি আর ঘরবাড়ি বলে কিছু বাকি আছে? তার বই—খাতা, কাপড়—জামা, বিছানা—বালিশ, চাদর—মাদুর, ছাতা—লাঠি যা কিছু ছিল সবই ইঁদুরের রেজিমেন্ট এসে কুচি কুচি করে ফেলেছে—তার আর কিছুই নেই। মোড়ল দুষ্টু লোক, সে লোভ করে বুড়ো—বুড়ির জিনিস চুরি করেছিল, তাদের মেরেও ফেলবে ভেবেছিল, তাই তার এমন শাস্তি হল। মন্দ কাজ করলে, মন্দ ভাবনা ভাবলে ঈশ্বর তাকে এমনি করে শিক্ষা দেন।
আর কাঠুরে বুড়ো—বুড়ি? তাদের ঘরের কোণে এখনও ঢিবি হয়ে পড়ে রয়েছে অগুনতি টাকা—তাদের কোনোই অভাব নেই। গাঁয়ের লোকেরা কেউ এসে চাইলে, আদর করে তাদেরও অভাব মিটিয়ে দেয় তারা। জালা নাইবা থাকলো, বুড়ো—বুড়ি আর কোনোদিন গরিব—দুঃখী হয়ে যাবে না। সবাইকে নিয়ে দিয়ে—থুয়ে বাঁচলে, ঘরের লক্ষ্মী ফুরোয় না।