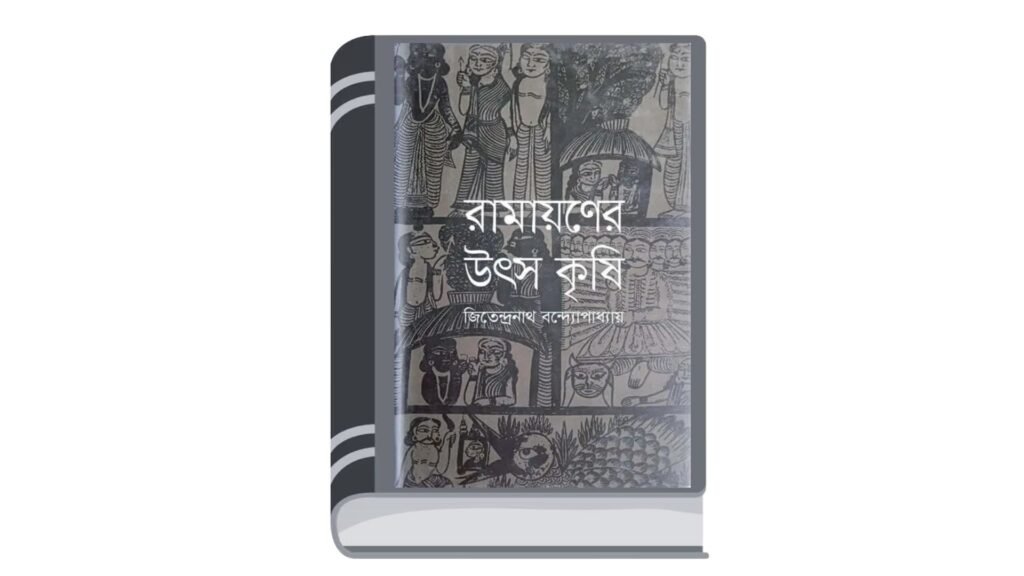০৭. কৃষিশ্ৰী সীতা – সপ্তম প্রকরণ
০৭. কৃষিশ্ৰী সীতা – সপ্তম প্রকরণ
বাল্মীকি ‘পৌলস্ত বধ’ তথা ‘রামায়ণ’ রচনা শেষ করে বেদবিশারদ ও গন্ধৰ্বসংগীতাভিজ্ঞ লবকুশকে শিক্ষাদান কালে বলেছেন,—
কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্ৰত॥ ৭ (১.৪.৭)
অর্থাৎ ‘পৌলস্ত বধ’ কাব্যে রামের অয়নসহ সীতার মহৎ চরিত্র বিবৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে সীতার পরিচয় বসুন্ধর তথা সীরখাত অর্থাৎ হলরেখ।
ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের সাতান্ন সূক্তের ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋকে আছে—
“অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্ব
যথা নঃ সুভগামসি যথা নঃ সুফলামসি। (ষষ্ঠ ঋক্)
ইন্দ্ৰঃ সীতাং নি গৃহ্নাতু তাং পূষা অনু যচ্ছতু
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুক্তরাং সমাম। (সপ্তম ঋকৃ)
অর্থাৎ হে তরুণী সীতে! সুভগে হও তোমাকে বন্দনা করি যেন আমাদের সুভোগে এস যেন আমাদের সুফলে এস ৷ ইন্দ্র কর্তৃক গৃহীত সীতার নিখিল, তাকে পূষা অনুসরণ করে যাচ্ছেন, সে আমাদের পয়ম্বতী উত্তরোত্তরকালে সমান দোহনীয়।” (১) ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একশো পঁচিশসূক্তে দ্বিতীয় ঋকে অদিতি নক্ষত্র সম্পর্কে উল্লেখ আছে “আমি সোমের আহন্ সংযুক্ত তিথি, আমি ধারণ করি ত্বষ্টা নক্ষত্রকে পৃষণ নক্ষত্রকে এবং ভগ নক্ষত্রকে। আমি দাত্রী হবিৰ্বাহী দ্যুতিদ্রব্যের আমাকে সুপ্রাপ্ত যাযাবর জ্যোতিষ্কের সুঅন্বিত।” ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে : “একদা যজ্ঞহীন দেবতার অদিতিকে বললেন, তুমি যজ্ঞ বলে দাও। অদিতি বললেন, ‘তথাস্তু, যজ্ঞের আবর্তন আমার শীর্ষদ্বয়ে আরম্ভ ও শেষ হোক।‘ এ আখ্যানের জ্যোতিষীক অর্থ একদা সায়ন বৎসরের আরম্ভ ও শেষ দু্যতিদ্বয়াত্মক অদিতি বা পুনর্বসু নক্ষত্রে হোত।”(২) যজ্ঞ অর্থ বর্ষ। ঋগ্বেদে যজ্ঞ অর্থ কর্ম বা জীবনবহনোপায়।
উপরোক্ত বক্তব্য অনুসরণে সহজেই বলা যায় পণ্ডিতগণের হিসাব মত আনুমানিক খৃঃ পূঃ ছয় হাজার বছর আগে পুনর্বসু নক্ষত্রে অমাবস্যা তিথিতে পুরাতন বৎসরের শেষ হত এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী শুক্লা প্রতিপদ হতে নতুন বৎসরের গণনা প্রচলিত ছিল। ঐ দিন যজ্ঞকৰ্মও অনুষ্ঠিত হত।
যদি মিথুন রাশিতে (অদিতি) পুনর্বসু নক্ষত্রর মধ্যভাগে বাসন্ত-বিষুব হয়, তাহলে (তুষ্ট) চিত্রা নক্ষত্রর দ্বিতীয় পাদে দক্ষিণায়ন (আপঃ) পূর্বাষাঢ় নক্ষত্রর শেষপাদে শারদ-বিষুব এবং (পূষণ) রেবতী নক্ষত্রর শেষপাদে উত্তরায়ণ অনুষ্ঠিত হবে।
ঋগ্বেদের উক্ত ঋকের ‘ভগম্’ শব্দটিকে ভগ অর্থাৎ পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র না ধরে আপঃ অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রর ইংগিত গ্রহণ করলে তৎকালীন অয়ন ও বিষুবস্থান সুস্পষ্ট হয়। ভগ অর্থ যোনি এবং যোনি অর্থ জল। জল অর্থাৎ আপঃ (পূর্বাষাঢ়া) নক্ষত্র সম্পর্কে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তে ষোড়শ ঋকে উল্লেখ আছে “হে মাতৃস্নেহধারী মধুসঞ্চারিণী জল, তুমি অধ্বর্যুদের যজ্ঞাভিমুখে জয়দাত্রীরূপে প্রবাহিত হয়েছে।”(৩) মিথুন ও ধনু উভয় রাশির নক্ষত্রগুলি ছায়াপথে নিমজ্জমান। অতএব ভগ নক্ষত্র বলতে এক্ষেত্রে আপঃ নক্ষত্রর ইংগিত গ্রহণ করা অসংগত হয় না।
অদিতি অর্থে পুনর্বসু নক্ষত্র; অন্য অর্থ অবিচ্ছিন্ন, ভূমি, পৃথিবী। বিষুবকালে দিন ও রাত্রি সমান হয়। ঐ নক্ষত্রে বৎসরের শেষ ও শুরু। এত কিছুর সমন্বয়ে ঋগ্বেদে অদিতি নক্ষত্রকে উপলক্ষ করে মূলতঃ পৃথিবীর মূর্তিময়ী স্বরূপ সীতার বন্দনাই করা হয়েছে। সীতার এই প্রথম আবির্ভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
শিকার, বনজসম্পদ আহরণ, আয়াসসাধ্য কৃষিকাজ এবং পশুপালন যাদের মুখ্য জীবিকা তাদের কাছে বসন্ত ঋতু শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় গম যব ইত্যাদি রবিফসল ঘরে ওঠে। লক্ষণীয় যে একদা বৈদিক-যজ্ঞে যবচূর্ণের পিষ্ঠকের প্রচলন ছিল। এই পিষ্ঠকের নাম পুরোডাশ। সুতরাং বাসন্তবিষুবতে সীতার ভূয়সী স্তুতিতে তৎকালীন মানব সমাজের জীবিকার আভাষ পাওয়া যায়।
সীতা ঋগ্বেদে ধরিত্রীর মূর্তিময়ী সত্বা, শুক্লযজুর্বেদে লাঙ্গলপদ্ধতি, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে সাবিত্রী, পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ইন্দ্ৰপত্নী এবং রামায়ণে রামপত্নী। অথর্ববেদের কৌশিকসূত্রে (১৪৭) সীতাকে বলা হয়েছে ‘পর্জন্যপত্নী হরিণী’। পর্জন্য মেঘাধিপতি ইন্দ্র। শব্দটির অর্থ শব্দায়মান মেঘ, গর্জন্মেঘ, মেঘশব্দ, মেঘ। ‘হরিণী “শব্দটি মৃগী অর্থে পাই অর্বাচন বৈদিকে। শব্দটির মূল পুংলিঙ্গরূপ ‘হরিৎ’ ঋগ্বেদে স্ত্রীলিঙ্গরূপেও ব্যবহৃত ছিল বিশেষণ হিসাবে (ঘোড়ার রং)। প্রজাপতির গল্পের রোহিৎ এই হরিণীর সঙ্গে তুলনীয়।”(৪) রোহিৎ এবং লোহিত শব্দদ্বয় সমার্থক। রোহিণী নক্ষত্র লোহিতবর্ণ, হরিৎবর্ণও বলা যায়। সুতরাং কৌশিকসূত্রে সীতাকে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত করা হয়েছে।
ঋগ্বেদে সীতার স্তুতিকাল বাসন্ত-বিষুবতে। বেদে ইন্দ্রর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। ইন্দ্র দ্বাদশাদিত্যের এক আদিত্য। ‘আদিত্য’ শব্দটি পুংলিঙ্গ ও দ্বিবচনান্ত হলে অর্থ হয় অদিতিদেবতার পুনর্বসু নক্ষত্র। সুতরাং ঋগ্বেদে সীতার সঙ্গে ইন্দ্রর উল্লেখ করে পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব নির্দেশ করা হয়েছে।
পরবর্তীকালে সূর্যর অয়নচলনহেতু বাসন্ত-বিষুব পশ্চিমদিকের নক্ষত্রগুলিতে সরে এলে এবং কালক্ৰমে দ্বাদশ রাশি সংশ্লিষ্ট দ্বাদশ মাসের সূর্যকে দ্বাদশ আদিতে বিভাগ ও নামকরণ করা হলে পূর্বসূত্র অনুসারে মনে হয়, বাসন্ত-বিষুব কালের সূর্যকে ইন্দ্র নামেই আখ্যাত করা হয়। এজনাই হয়ত বৃষরাশিতে জ্যৈষ্ঠমাসে বাসন্ত-বিষুব অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে এই মাসের সূর্যকে ‘ইন্দ্র’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে কারণে যে নক্ষত্র বা যে মাসের শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন মানুষের ধ্যানে ছিল সেই নক্ষত্র ও মাসের সঙ্গে ‘ইন্দ্র’ নামটি যুক্ত করে নিয়েছিল। “লোকমান্য তিলক প্রমাণ দিয়েছেন খ্রীষ্টের অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব হত। সেকালে চান্দ্র-অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যর জ্যেষ্ঠ নক্ষত্রে অবস্থান কালে শারদবিষুব হতে বৎসর গণনার রীতি ছিল।”(৫)
এখানে লক্ষণীয় যে এই সময় শারদ-বিষুব অর্থাৎ শরৎকাল প্রাধান্য লাভ করেছে। বর্ষার পর শরৎ ঋতুতে কৃষিকর্মের ফলাফল স্পষ্ট হয়। অতীতের সীতার ধ্যানধারণার সঙ্গে এবার কৃষিকাজ জড়িয়ে গিয়েছে। হয়ত ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার কারণে এবং নভঃমণ্ডলের বৃহত্তম নক্ষত্র জ্যেষ্ঠার গুরুত্ব মেনে নিয়ে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রেরও নামকরণ হয়েছিল ইন্দ্র।
খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে যজুর্বেদের কালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হত। এই কালে সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গলপদ্ধতি নির্ধারণ করে সীতার স্বরূপকে স্থিরনিশ্চয় করা হয়।
সীতাকে ইন্দ্রপত্নী এবং পর্জন্যপত্নী আখ্যা দিয়ে সীতার সঙ্গে মেঘবর্ষণ দেবতার সম্পর্ক স্থাপন করে প্রথমে ইন্দ্র এবং পরে পর্জন্য নাম ব্যবহার করে ইন্দ্রর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু ইন্দ্রর স্বরূপ প্রায় অপরিবতিত থাকলেও সীতার চারিত্রিক ব্যাপ্তি সংকুচিত করা হয়েছে। যে সীতার উদ্ভব হয়েছিল পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুবতে বর্ষশেষ ও বর্ষ আরম্ভ উভয়ের সন্ধিক্ষণে পৃথিবীর সর্ব-জীবধাত্রী স্বরূপ হিসাবে, সেই সীতা কয়েক হাজার বছর পরে কৃষিভিত্তিক সমাজ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরখাতে সীমিত হয়ে মেঘবর্ষণ-দেবতার পত্নীরূপে বন্দিতা হয়েছে। রামায়ণের কালে বসুন্ধরার কন্যা হিসাবে আমরা তাকে পেয়েছি। এখানে সীতা জনকের পালিত-কন্যা ও রামের পত্নী। এই সীতাকে কেন্দ্র করে বাল্মীকির ‘রামায়ণ’ কাব্য।
রামের ক্ষেত্রে যেমন জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রর সমাবেশ বিবৃত হয়েছে, সীতার ক্ষেত্রে কোন সময়েই তার বিশদ উল্লেখ নাই। কিন্তু সীতার জন্মকাহিনী অনুসারে সীতাকে হলরেখ হিসাবে সহজেই চেনা যায়।
রাম ও লক্ষণের সাহায্য নিয়ে বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম আশ্রমে সিদ্ধিলাভ করার পর দুই ভাইকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে না গিয়ে উত্তরে মিথিলায় জনকের যজ্ঞে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌছুলে জনক বিশ্বামিত্রকে স্বাগত জানিয়ে বললেন যে তার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হতে আর মাত্র দ্বাদশদিন বাকি। তারপর জনকের পুরোহিত শতানন্দ বিশ্বামিত্রর অতীত ইতিহাস সকলকে অবগত করলেন। পরদিন প্রভাতে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটলে বাল্মীকি জনককে অনুরোধ করলেন রাম ও লক্ষ্মণকে তার নিকট রক্ষিত ধনুটি দেখাতে। তখন জনক ধনুর ইতিহাস বর্ণনা করলেন। অতীতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর মহাদেব যজ্ঞভাগ হতে তাকে বঞ্চিত করার কারণে এই ধনুর দ্বারা দেবতাগণের শিরচ্ছেদ করার ভীতিপ্রদর্শন করায় দেবতাগণ মহাদেবকে স্তবে তুষ্ট করলেন তখন মহাদেব শান্ত হয়ে এই ধনু দেবতাগণকে অর্পণ করেন। দেবতাগণ নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাতকে এই ধনু ন্যাসম্বরূপ রাখতে দিয়েছিলেন।
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্ব্বজে বিভৌ।
অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্ৰং লাঙ্গলাদুখিত ততঃ॥ ১৩
ক্ষেত্ৰং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্ৰুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবৰ্দ্ধত মমাত্মজা॥ ১৪
বীৰ্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুখিতাং তাতু বৰ্দ্ধমানাং মমাত্মজাম্॥ ১৫ (১.৬৬.১৩-১৫)
অতঃপর একদিন ক্ষেত্রকর্ষণকালে লাঙ্গলমুখে এক কন্যার উদ্ভব হল। যেহেতু ক্ষেত্র পরিচর্যাকালে এই কন্যার আবির্ভাব ঘটে সেকারণে কন্যার নাম সীতা। সীতার বিবাহ ব্যাপারে জনক পণ করেছিলেন, যে এই ধনুৰ্ভঙ্গ করতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিবাহ দেবেন। রাম অবলীলাক্রমে ধনুর মাঝখানে ধরে জ্যা আরোপ করে ভেঙ্গে দিলেন।
ধনু কাহিনীতে অসামঞ্জস্য রয়েছে।
প্রথমতঃ; বিশ্বামিত্র দশরাত্রর জন্য মাত্র রামলক্ষ্মণকে তার নিজের কার্যোদ্ধারের কারণে দশরথের নিকট হতে চেয়ে এনেছিলেন। কার্যসিদ্ধির পর অযোধ্যায় না ফিরে মিথিলায় যাওয়া কি অস্বাভাবিক নয়?
দ্বিতীয়তঃ; ধনুর সঙ্গে সীতার বিবাহ বিষয়টি যখন জড়িয়ে আছে জানা গেল, তখন বিশ্বামিত্র দশরথের পূর্ব মতামত না নিয়ে কেন রামকে ধনু প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন?
তৃতীয়তঃ; রাম সীতার বিবাহের প্রাক্কালে জনক তার বংশের যে তালিকা পেশ করেছিলেন সেই অনুসারে দেবরাত নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র নয়, সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ।(৬)
চতুর্থতঃ; মহাদেব প্রদত্ত ধনু দেবতাগণ ন্যাসস্বরূপ দেবরাতের নিকট রেখেছিলেন। সুতরাং ঐ ধনু ভেঙ্গে নষ্ট করার অধিকার জনক কোথায় পেলেন? এই ধনু প্রসঙ্গে আবার অন্যত্র বলা হয়েছে মহাযজ্ঞে বরুণ তুষ্ট হয়ে ধনু প্রদান করেছিলেন।
মহাযজ্ঞে তদী তস্য বরুণেন মহাত্মনা।
দত্তং ধনুৰ্বরং প্রত্যা তুণী চাক্ষষ্যসায়কেী॥ ৩৯ (২.১১৮.৩৯)
সাধুর ছদ্মবেশে রাবণ পঞ্চবটী বনে সীতাকে হরণ করতে এসে সীতার পরিচয় জানতে চাইলে সীতা প্রসঙ্গক্ৰমে জানান বিবাহের পর বারো বৎসর শ্বশুরকুলে বাস করার পর ত্রয়োদশবর্ষে তিনি রামের সঙ্গে বনবাসে আসেন। তখন তার বয়স আঠারো এবং রামের বয়স পঁচিশ।
উযিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকুণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী॥ ৪
তত্ৰ ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্ৰভুঃ।
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ॥ ৫
* * *
মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সী পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে॥ ১০ (৩.৪৭.৪-৫, ১০)
বারো বৎসর শ্বশুরকুলে বাস করার কথা অশোকবনে বন্দিনী সীতা হনুমানের সাক্ষাৎকারের সময়েও ব্যক্ত করেছিলেন।
সমা দ্বাদশ ত্যাহং রাঘবস্য নিবেশনে।
ভুঞ্জান মানুষান ভোগান সৰ্বকামসমৃদ্ধিনী॥ ১৭
ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষবাকুনন্দনম্।
অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্ৰমে॥ ১৮ (৫.৩৩.১৭-১৮)
এই তথ্য অনুসারে সীতা আঠারো বছর বয়সে রামের সঙ্গে বনে গমন করেন। অতএব ছয় বছর বয়সে সীতার বিবাহ হয়েছিল। সাবালিকা না হলে স্বয়ম্বর সভায় বিবাহ হয় কি? আত্রির আশ্রমে সীতা নিজেই অনসূয়াকে বলেছিলেন তার পতিসংযোগসুলভ বয়স হলে তার বাবা তনয়ার জন্য ধর্মতঃ স্বয়ম্বরসভা স্থির করেন।(৭)
সুতরাং ধনুকাহিনীর সঙ্গে মূলতঃ মানবী সীতার সম্পর্ক নাই। এই সীতা কৃষিশ্রী। সীতার জন্মকাহিনীতেও তার সীরখাত-স্বরূপ সুস্পষ্ট।
জনক শব্দের সাধারণ অর্থ জন্মদাতা। বসুন্ধরার বুকে কৃষক হলকর্ষণ করলে সীতার উদ্ভব হয়। সুতরাং কৃষক হলেন জনক, সীতার পিতা, যদিও সীতার মাতা বসুন্ধরার সঙ্গে কৃষকের কোন যৌন সম্পর্ক নাই। অগ্নিপরীক্ষাকালে সীতা একথা ব্যক্ত করেছেন।(৮)
জনকের আসল নাম সীরধ্বজ, অর্থাৎ কৃষক জনক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে পৃথিবী শাসন করতেন। ক্ষত্র ও ক্ষেত্র শব্দ দুটি সমার্থক ধরলে কৃষিকাজের ইংগিত পাই। যদি স্বতন্ত্র অর্থ ধরা হয় তাহলে সীতার সূত্র ধরে বলা যায় একটি কৃষি নির্ভরশীল অঞ্চলের প্রধান ছিলেন ‘জনক’ উপাধিধারী বংশের সীরধ্বজ, যিনি যথাসময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম হলকর্ষণ করে কৃষিকাজের শুভারম্ভ ঘোষণা করতেন।
পুরাণে কালপুরুষ নক্ষত্র নিয়ে নানা কাহিনীর বিস্তার। দক্ষযজ্ঞ বিনাশক মহাদেবের জ্যোতিবিজ্ঞান-স্বরূপ হল কালপুরুষ নক্ষত্রও পুনর্বসু নক্ষত্র হল সেই ধনু। পাঁচ তারা বিশিষ্ট পুনর্বসু নক্ষত্রটি ধনুরাকৃতি। একদা মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হত। পরবর্তীকালে অয়নচলন হেতু বাসন্তবিষুব মৃগশিরা নক্ষত্রর পরিবর্তে রোহিণী এবং আরও পরে কৃত্তিকা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হয়। বিষুবর নক্ষত্র পরিবর্তনের ঘটনাকে উপলক্ষ করে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কাহিনী। দক্ষর কল্পনাও কালপুরুষ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। কালপুরুষ নক্ষত্রর শীর্ষস্থ তিনটি তারা নিয়ে দক্ষর ছাগমুণ্ড কল্পনা।(৯) বাসন্ত-বিষুব যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে, তখন কালপুরুষ নক্ষত্রের ভূমিকা গৌণ। একারণে ধনু জনক বংশের পূর্বপুরুষের নিকট ন্যাসস্বরূপ প্রদান। কালক্ৰমে অয়নচলন হেতু বাসন্ত-বিষুব আরও পশ্চাদগামী হলে পুনর্বসু নক্ষত্র পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে। কারণ তখন সূর্য কর্কটরাশিতে প্রবেশ করলে শ্রাবণ মাস বৰ্ষাঋতুর প্রথম মাস হিসাবে গণ্য হত। অতএব পুনর্বসু নক্ষত্রর শেষপাদে সূর্য এলে আগামী বর্ষার আশায় কৃষিকাজের প্রস্তুতি শুরু হত। কৃষিকাজের এই প্রস্তাবনাই হল জনকের যজ্ঞ।
আমরা জানি দক্ষিণায়নাদি দিবস হতে বর্ষা ঋতু গণনা করা হয়। রামায়ণের কালে গ্রীষ্মঋতুর দ্বিতীয় মাস আষাঢ়ে সূর্য যখন পূনর্বসু নক্ষত্রে তখন সূর্যর প্রখর তাপে আবহমণ্ডলের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে মেঘবাহী উত্তর-পূর্বমুখী বায়ুপ্রবাহ বৰ্ষাঋতুর আগমন ত্বরান্বিত করে। বায়ুমণ্ডলের এই গভীর নিম্নচাপের স্থান পূরণই হল ধনুৰ্ভঙ্গ ৷ ধনু অর্থ চাপ।
বিশ্বামিত্রর সঙ্গে জনকের সাক্ষাৎকারের দিন যজ্ঞের দ্বাদশ দিবস বাকি ছিল। রাম যেদিন ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করে ধনুৰ্ভঙ্গ করেন তার একাদশতম দিনে জনকের যজ্ঞ শেষ হয়, অর্থাৎ চাষের প্রাথমিক কাজ বীজতলা সম্পূর্ণ হয়। ঐদিন দক্ষিণায়নাদি। পৃথিবী এই সময় রসসিক্ত হয়, একারণে তিন দিন হলকর্ষণাদি নিষিদ্ধ। এই সূত্রে অম্বুবাচীর সঙ্গে দক্ষিণায়নাদির সম্পর্ক টানা যায়।
এখানে ধনুর মধ্যভাগ অর্থে পুনর্বসু নক্ষত্রর মধ্যভাগ ধরা হলে সূর্য তখন রাশিচক্রের ৮৬° ৪০’ (ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়)। বাকি এগারে দিনে সূর্য আন্দাজ দশ অংশ পূর্বগামী হয়ে ৯৬° ৪০” (ছিয়ানৱই অংশ চল্লিশ কলায়) পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থান করবে। অতএব রামায়ণের কালে ঐ সময় দক্ষিণায়নাদি।
কিন্তু দেবরাত কে?
দেবরাত অর্থে দেব রক্ষিত যেখানে। দেব অর্থ মেঘ। সুতরাং দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কাহিনীতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে পুষ্যা নক্ষত্রে দৃক্ষিণায়নাদি হলে পুনর্বসু নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে বায়ুমণ্ডলে যে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হবে, সেই তথ্যকে দেবরাতের নিকট ন্যাসম্বরূপ ধনু প্রদান বলা হয়েছে। সুতরাং দেবরাত শব্দের মধ্যেও পুনর্বসু নক্ষত্র এবং দক্ষিণায়নাদির ইংগিত আছে। অতএব ধনুকাহিনীর মধ্যে রামায়ণের কালের দক্ষিণায়ন স্থানটির নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সম্পাতি রহস্য অধ্যায়েও বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। বিশ্বামিত্রর সিদ্ধাশ্রম কাহিনীর বিশ্লেষণ কালে পুনরায় এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। এখানে লক্ষণীয় যে জনক বিশ্বামিত্রর নিকট যজ্ঞ শেষের সময়কাল উল্লেখ করেছেন, কোন তিথি নক্ষত্রর নাম করেননি। তাছাড়া রাম অহল্যাকে উদ্ধার করে বিশ্বামিত্রর সঙ্গে মিথিলায় উপনীত হন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় রামের ধনুৰ্ভঙ্গ পর্যন্ত “বিদেহ বা ‘বৈদেহ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। একবার মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে ‘বৈদেহোমিথিলাধীপঃ’ (১.৬৫.৩৯)। এখানে মিথিলাপতি বৈদেহ বলে উভয় শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য টান হয়েছে মনে করি। কিন্তু দশরথের জনক গৃহে আগমন উপলক্ষে ‘মিথিলা’ শব্দটি ব্যবহার না করে সকল সময় ‘বিদেহ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বিদেহ অর্থ বিগত দেহ, অর্থাৎ একদা ছিল।
এই শব্দে অবশ্যই বৈদিক কালের পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদির ইংগিত করা হয়েছে। দশরথ বিদেহ রাজ্যে পৌঁছানোর পর সীতার বিবাহ প্রসঙ্গে জনক মঘা ইত্যাদি নক্ষত্রর উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণায়নাদির প্রায় একমাস পরে পুরোদমে বর্ষা নামে, চাষের কাজও চলে দুততালে। তখন বারিধারার সূত্রে মেঘদেবতা রাম ও কর্ষিত জমি সীতা একটি সত্তায় যেন পরিণত হয়। সামাজিক জীবনে বিবাহবদ্ধনে আবদ্ধ হয়ে নর ও নারী ‘অর্ধনারীশ্বর’ ভাবে অবস্থিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করে। এজন্যই নৈসর্গিক ঘটনাকে প্রকাশ করতে রামায়ণে ভগ নক্ষত্রে রামসীতার বিবাহ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই রীতিতে রামায়ণে প্রায়শঃ রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে।
বর্ষারম্ভের পূর্বেই জমি চাষ করে বীজতলা তৈরী করতে হয়। তখন জমিতে বীজের অংকুরোদগম করার মত জলের প্রয়োজন। যেহেতু সীতাকে রূপকে মানবী-সত্তা দেওয়া হয়েছে, সেকারণে বর্ষার পূর্বমুহূর্তের সরখাতের পর্যায়কে সন্তান ধারণোপযোগী রজঃস্বলা যুবতী হিসাবে প্রকাশ করতে হবে। নতুবা বর্ষার জলস্পর্শে সীরখাত (সীতা) বীজ হতে চারা উৎপাদন করবে কিভাবে?
সীতার স্বয়ম্বরসভা হয়েছিল।
কর্ষিত জমি ত সকল সময়ের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু গ্রীষ্মঋতুর শেষে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ ভেদ করতে একমাত্র উত্তর-পূর্বমুখী মেঘ-বাহিত বায়ুপ্রবাহ সক্ষম। এই মেঘবর্ষণের দরুণ শস্যক্ষেত্রের শ্ৰীবৃদ্ধি, সীতার কৃষিশ্ৰী স্বরূপ। সুতরাং সীতার ভর্তী হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র মেঘদেবতার। রাম এই মেঘবর্ষণের দেবতা। মেঘের উৎপত্তি সূর্যর প্রখর উত্তাপে। সূর্যর বার্ষিকগতির দ্বারা মেঘের গমনাগমন নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মেঘদেবতা সূর্যরই আরেকটি স্বরূপ। সূর্যর এক নাম বিষ্ণু। রাম বিষ্ণুর অর্ধাংশ এবং সূর্যবংশীয়।
অতএব কৃষিশ্ৰী সীতা বিবাহের পূর্বেই পতিসংযোগসুলভ বয়স প্রাপ্ত হয়ে স্বয়ম্বর সভায় পতিলাভ করেছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না।
ধনুর সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক টানা হয়েছে। বরুণ জলের দেবতা। সুতরাং বর্ষারম্ভর সঙ্গে সম্পর্ক টানা যায়। অপরদিকে শতভিষা নক্ষত্রর বৈদিক নাম বরুণ। পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদি হলে শতভিষা (বরুণ) নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হয়। এই প্রাচীন তথ্য নিদেশের কারণে বরুণের সঙ্গে ধনুর সম্পর্ক দেখানে হয়েছে। অতএব আপাতঃ দৃষ্টিতে যা অসামঞ্জস্য মনে হয়েছিল, সেগুলি সবই রহস্য।
ধনুৰ্ভঙ্গের পর জনক বিশ্বামিত্রর অনুমতি নিয়ে রামের বিবাহ বিষয়ে দশরথের সম্মতি লাভার্থে অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করলেন। তিন রাত্রি অতিবাহিত করে চতুর্থ দিবসে দূতগণ অযোধ্যায় পৌঁছে দশরথের নিকট সকল ঘটনা পেশ করল। পরদিন দশরথ যাত্রা করে পথে চার দিবস অতিক্রান্ত করে বিদেহরাজ্যে উপস্থিত হলেন। তখন জনক দশরথকে জানালেন,—কাল প্রভাতে এই যজ্ঞের অবসানে আপনি বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন করুন।
পরদিন প্রভাতে বিশেষ দৃত পাঠিয়ে জনক সাঙ্কাশ্যা নগরী হতে ভ্রাতা কুশধ্বজকে নিয়ে এলেন। এখানে কিন্তু কুশধ্বজ কন্যাদ্বয় সহ বিদেহরাজ্যে এসেছিলেন এমন কোন ইংগিত দেওয়া হয়নি।
তারপর বিশ্বামিত্রর মতানুসারে দশরথের নির্দেশে বসিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের গুণকীর্তন করলেন। নিজ বংশের বর্ণনা পেশ করার পর জনক তিন সত্য করে তার দুই কন্যাকে সম্প্রদানের অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়ের উল্লেখ করলেন না।
মঘা হাদ্য মহাবাহে তৃতীয়দিবসে প্রভো।
ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু॥ ২৪ (১.৭১.২৪)
অর্থাৎ অদ্য মঘা নক্ষত্র, সুতরাং তৃতীয় দিবসে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে আপনি বৈবাহিক কাজ সম্পাদন করুন।
তখন বসিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্ৰ জনককে বললেন কুশধ্বজের দুই কন্যাকেও দশরথের পুদ্ধেয় ভরত ও শত্ৰুঘ্নর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হোক। অতএব স্থির হল একই দিনে চারজনের বিবাহ হবে।
উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ॥ ১৪ (১.৭২.১৪)
অর্থাৎ পরশুদিন ফল্গুনী-নক্ষত্র হবে, সুতরাং ঐদিন বিবাহে প্রশস্ত, যেহেতু মনীষীরা বিবাহ বিষয়ে ভগদৈবত ফল্গুনী-নক্ষত্রের প্রশংসা করে থাকেন। সেই মত দশরথের চারিপুত্রের সঙ্গে সীরধ্বজের দুইকন্যা ও কুশধ্বজের দুই কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হল।
এই বিবরণে ধনুৰ্ভঙ্গের পর দূতগণের অযোধ্যা গমন ও দশরথের বিদেহরাজ্যে আগমনের মধ্যে জনকের যজ্ঞ সমাপনের এগার দিনের হিসাব ঠিক আছে মনে হবে। কিন্তু আসলে কুশধ্বজ প্রসংগ টেনে ঘটনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে। সুতরাং দশরথের উপস্থিতিতে ঘোষিত বিবাহের দিন সূর্য পূর্ব-ফলুনী নক্ষত্রে এবং চন্দ্র উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে।
বিবাহের প্রস্তাবনায় কাহিনী রহস্যপূর্ণ।
যজ্ঞান্তে পরদিন প্রভাতে জনক দূত পাঠিয়ে সাঙ্কাশ্যা নগরী হতে কুশধ্বজ্ঞকে আনিয়েছিলেন। সাঙ্কাশ্যা অর্থে সাদৃশ্যযুক্ত, সমভাবাপন্ন। সাঙ্কাশ্যা নগরীর প্রাক্তন রাজা সুধম্বাকে বধ করে সীরধ্বজ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সেখানে অধিষ্ঠিত করেছেন। সুধম্বা অর্থে শ্রেষ্ঠ ধানুকী।
রামায়ণ কালের পূর্বে মৃগশিরা নক্ষত্রে এবং পরে রোহিণী নক্ষত্রে যখন বাসন্ত-বিষুব ছিল, তখন পূর্ব-ফলুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদি হত। সুতরাং বৈদিককালের দক্ষিণায়নাদির সূত্র ধরে পূর্ব-ফলুনী নক্ষকে সাঙ্কাশ্যা বলা হয়েছে। দক্ষিণায়নাদিতে বায়ুমণ্ডলে গভীর নিঃ চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলশ্রুতি বর্ষাগম। এই তথ্যের ইংগিত সাঙ্কাশ্যা নগরীর প্রাক্তন নৃপতি সুধম্বা, শ্রেষ্ঠ ধানুকী। যেমন, রামায়ণের কালে রাম। প্রাকৃতিক ঘটনা একই, শুধু মাত্র কালের ব্যবধান। রামায়ণকালের ভাদ্র মাস ঘোর বর্ষাকাল, অতএব সাঙ্কাশ্যা৷ তখন কুশধ্বজ অর্থাং ঘোর বর্ষার অধীন। সুতরাং কাহিনীকে অর্থাৎ দক্ষিণায়নাদি পুনর্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্র হতে পূর্ব ও উত্তর-ফলুনতে নিয়ে আসা হয়েছে।
উপরোক্ত শ্লোকে ‘ভগ’ শব্দের প্রয়োগে সূর্যর সিংহরাশিতে ভগ অর্থাৎ পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থান বুঝতে হবে। পূর্ব-ফল্গুনীর বৈদিক নাম ভগ। সিংহরাশিস্থ ভাদ্র মাসের আদিত্যর নামও ভগ।
রামসীতার বিবাহদিনে সূর্য পূর্ব-ফল্গুনীর শেষ পাদে, চন্দ্র উত্তর-ফল্গুনীতে। তিথি অমাবস্যা; শুক্ল প্রতিপদও হতে পারে। বৈদিক কালে পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্য এলে বর্ষাকাল সংক্রান্ত হলকর্ষণ জাতীয় উৎসব হত মনে হয়। সেই স্মৃতি অনুসারে রামায়ণের কালেও হয়ত ঐ সময় মেঘদেবতা ও বসুন্ধরা কন্যার বিবাহ জাতীয় কোন উৎসব পালন করা হত। সেই ইংগিত রামায়ণে রামসীতার বিবাহ উপলক্ষে রাখা হয়েছে।
দ্বিতীয়তঃ, সাঙ্কাশ্যা, সুধম্বা এবং কুশধ্বজকে কাহিনীর মধ্যে জড়ানোতে বলা যায় দক্ষিণায়নাদিতে বৰ্ষাঋতু গণনা করা হলেও পুরোপুরি বর্ষ নামে এক মাস পরে। সুতরাং শ্রাবণ বৰ্ষাঋতুর প্রথম মাস হলেও আকাশের মেঘ এবং পৃথিবীর কর্ষিত জমির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে ভাদ্রমাসে। একারণে আনুষ্ঠানিক বিবাহের ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হয়েছে সূর্য যখন ভগ (ভাদ্র) মাসে ভগ (পূর্ব-ফল্গুনী) নক্ষত্রে।
তৃতীয়তঃ, পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রর শেষপাদে অমাবস্যা হলে কর্কটরাশিতে দুইটি অমাবস্যা হওয়ার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে শ্রাবণ মাস অবশ্যই মলমাস হবে। অতএব শুভানুষ্ঠান শুদ্ধ শ্রাবণমাসে হতে হবে।
এই মলমাসের ইংগিত বিশ্বামিত্র কাহিনীতেও আছে। বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ সমাপনের কারণে দশরাত্রর জন্য দশরথের নিকট হতে রামকে চেয়ে নিয়েছিলেন। এখানে ‘রাত্র’ শব্দে মাসকে ইংগিত করা হয়েছে। তাহলে সেই বৎসরে মলমাস থাকায় এগারে মাসে বৎসর পূর্ণ হয়। অতএব রাম যে মাসে অযোধ্যা ত্যাগ করেন সেই মাস এবং মলমাস বাদ দিয়ে দশমাস গণনা করলে বৎসরের হিসাব মেলে।
সুতরাং পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষরে সূর্যর অবস্থানকালে সীতার বিবাহ উল্লেখ করে বৈদিক যুগের দক্ষিণায়নাদি কাল এবং রামায়ণের কালের কোনও এক বৎসরের মলমাস উভয়ের ইংগিত দেওয়া হয়েছে। বিশ্বামিত্রর সঙ্গে রামের অযোধ্যা ত্যাগ কালে রামের বয়স ছিল ঊনষোড়শ। উন শব্দটি ব্যবহার করে উন বৎসরের ইংগিত দেওয়া হয়েছে।
এবিষয়ে এখনও একটি সংশয় থাকে।
সীতা হরণের উদ্দেশ্যে রাবণ মারীচকে সাহায্য করার অনুরোধ করলে মারীচ রামের শৌর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একদা সে যখন মহাবিক্রমে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করছিল তখন তার ভয়ে ভীত হয়ে বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন দশরথ জানান রামের বয়স ঊনদ্বাদশ বৎসর মাত্র।
ঊনদ্বাদশবর্ষোহয়মকৃতাস্ত্রশচ রাঘবঃ।
কামস্তু মম তৎ সৈন্যং ময়া সহ গমিষ্যতি॥ ৬ (৩.৩৮.৬)
বিশ্বামিত্রর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত দশরথ রাজী হয়ে রামকে নিয়োগ করলে বিশ্বামিত্র সেই দিনই তার যজ্ঞ সমাধা করেন। মারীচ যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য রামকে উপেক্ষা করে ধাবিত হলে রাম শরাঘাতে মারীচকে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। এই প্রসঙ্গে তাড়কাবধ অথবা জনকের যজ্ঞের কোন উল্লেখ নাই। উপরন্তু বিশ্বামিত্র যেদিন রামকে প্রার্থনা করেন সেই দিনই যজ্ঞ সমাধা করেন।
অদ্য রক্ষতু মাং রামঃ পর্ব্বকালে সমাহিতঃ।
মারীচান্মে ভয়ং ঘোরং সমুৎপন্নং নরেশ্বরঃ॥ ৪ (৩.৩৮.৪)
অর্থাৎ বিশ্বামিত্র দশরথকে বলছেন; “ মারীচ হইতে আমার অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে; অতএব অদ্য আমি যখন যজ্ঞ করিব, রাম তখন আমাকে রক্ষা করুন”।
কিন্তু পূর্বকাহিনীতে অযোধ্যা ত্যাগের পর যজ্ঞস্থলে পৌঁছুতে বিশ্বামিত্র রামকে নিয়ে একাধিক রাত্র পথে রাত্রিবাস করেছিলেন।
রামের জন্ম চৈত্রমাসে, রবি মেষরাশিতে। অতএব রামের দ্বাদশ বৎসর পূৰ্ণ হতে তখনও রাশিচক্লের এক-চতুর্থ অর্থাৎ একভাগ কম। তাহলে সূর্য তখন মকররাশিতে, যখন রাম মারীচকে বিতাড়িত করেছিলেন।
মনে হয় রামের ঊনদ্বাদশ বৎসর বয়সে মারীচ অর্থাৎ দীপ্তি সম্পন্ন কোন ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল। সেই ধূমকেতুটি পুনরায় চার বৎসর পরে রামের ঊনষোড়শ বৎসরে দেখা গিয়েছিল। এটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল সীতাহরণের প্রাক্কালে। মনে হয় রামায়ণের কালে এই ধূমকেতুটি মানুষের মনে বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি করেছিল।
ঊনদ্বাদশ শব্দে বারে বৎসর পূর্ণ হতে তিন মাস বাকি আছে।
‘ঊনষোড়শ’ শব্দে ঊন বৎসর অর্থাৎ মলমাস সমন্বিত বৎসর বুঝানো হয়েছে। ঊন শব্দটি দুই ক্ষেত্রে দুই অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।
মানবী সীতার অস্তিত্ব স্বীকার করলে বলা যায় রামের দ্বাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর বিবাহ হয়েছিল। তখন সীতার বয়স ছয় বৎসর মাত্র। চার বৎসর পরে সীতা ঋতুমতী হলে দ্বিতীয়-বিবাহ হয়।(১০) উভয় বিবাহের ক্ষেত্রেই হয়ত পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ঐতিহাসিক ঘটনাকে রহস্যাবৃত করার কারণে রামের ঊনষোড়শ বর্ষের উল্লেখ করে মানবী সীতাকে কৃষিম্বরূপ সীতার সঙ্গে একাত্মা করা হয়েছে।।
বিবাহ বাসর ছাড়া সীতার তিন বোনের কোন ভূমিকা সমগ্র রামায়ণে নাই। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং এদের কোন মানবিক সত্তা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এঁদের কৃষিচরিত্র অনস্বীকার্য। হলকর্ষণের পর সীতার উদ্ভব। সীরখাত সমন্বিত কর্ষিত জমি উর্মি সমন্বিত। এই অবস্থাকে ঊর্মিলা বলা হয়েছে। একারণে ঊর্মিলা সীতার কনিষ্ঠ। ক্ষেত্রের এই উভয়বিধ অবস্থার সৃষ্টি হয় কৃষকের হাতে। এজন্য সীতা ও ঊর্মিলা সীরধ্বজের কন্যা। কর্ষিত জমির সঙ্গে মেঘবর্ষণ দেবতার সম্পর্ক। কিন্তু বর্ষণের প্রকাশ বারিধারায়। বারিবিন্দু প্রথম স্পর্শ করে কর্ষিত জমির উর্মির উর্ধ্বপীঠ। এজন্য ঊর্মিলা লক্ষণের স্ত্রী। বর্ষাকালে জমির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তখন জমির মাটি মণ্ডে পরিণত হয়। এই অবস্থার প্রকাশ ভরত ও মাণ্ডবীর বিবাহ। শ্ৰুতকীর্তি অর্থ বিখ্যাত, শ্ৰুতযশাঃ। শত্রুঘ্ন অর্থ শত্ৰুনাশক। কর্ষিত জমির সার্থকতা ফসল উৎপাদনে। ক্ষেত্র হতে এই ফসল প্রাপ্তিকে নির্দেশ করছে শত্রুঘ্ন ও শ্রুতকীর্তির বিবাহ। বিনা জলে জমির মাটি মথিত হয় না এবং ফসল উৎপাদিত হতে পারে না। এজন্য এঁর দুইজনে কুশধ্বজের কন্যা।
সুতরাং ধনুৰ্ভঙ্গ এবং সীতার বিবাহ উভয় প্রসঙ্গে সীতার কৃষিসত্তা খুবই স্পষ্ট।
রামায়ণে আছে সীতা লক্ষ্মীর অংশজাতা। রাবণকে বধ করে লংকা জয়ের পর রাম সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করায় সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। সে সময়ে ব্রহ্মা রামকে বলেন;
সীতা লক্ষ্মীর্ভবান বিষ্ণুদেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ॥ ২৭ (৬.১১৯.২৭)
অর্থাৎ, সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনিই সেই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু।
ঋগ্বেদে কৃষ্ণ অর্থে রাম শব্দটির ব্যবহার আছে (১০।৩৩ সায়ন)। হরিকে কি ভাবে মহাসমরে লাভ করা যায় রাবণ যখন এই চিন্তা করছিলেন তখন সনৎকুমার প্রসঙ্গক্ৰমে বলেছিলেন;
তস্য পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মীঃ সীতেতি বিশ্রুত।
দুহিতা জনকস্যৈষা উত্থিত বসুধাতলাৎ॥ ২৩ (৭.৪৪.২৩)
অর্থাৎ, তাঁহার (রামের) পত্নী মহাভাগ৷ লক্ষ্মী সীতা নামে বিখ্যাত৷ হবেন,—সেই জনকনন্দিনী সীতা বসুধাতল হতে সম্ভূতা হবেন।
নারদ সনৎকুমারের নিকট রাবণের ক্রিয়াকলাপ জ্ঞাত হয়েছিলেন। নারদের নিকট যেমনটি জেনেছেন, অগস্ত্য সেই রকম বর্ণনা রাম অযোধ্যার রাজা হলে তাকে শুনিয়েছিলেন।
সীতা লক্ষ্মীর্মহাভাগা সম্ভূতা বসুধাতলাৎ।
ত্বদর্থমিয়মুৎপন্ন জনকস্য গৃহে প্রভো॥ ৫৩ (৭.৪৬.৫৩)
অর্থাৎ, মহাভাগ লক্ষ্মীই ধরিত্রীসম্ভূতা সীতা, তিনি তোমার (রামের) জন্য জনকগৃহে উৎপন্ন হন। সকল শ্ৰী সম্পদ সৌভাগ্যর দেবী লক্ষ্মী। সুতরাং লক্ষ্মীস্বরূপ সীতা অবশ্যই কৃষিশ্রী। বাল্মীকি সীতার এই লক্ষ্মীসত্তার প্রত্যক্ষ প্রস্তাবনা প্রথম করেছেন লংকা জয়ের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে। অনেকে মনে করেন রামায়ণে এই ঘটনাটি প্রক্ষীপ্ত। কিন্তু সীতার কৃষিসত্তা স্বীকার করে নিলে এই ঘটনাকে প্রক্ষীপ্ত বলার কারণ নেই।
অতীতে কৃষিবিজ্ঞান যখন আজকের মত উন্নত হয়নি, সেকালে বসন্তঋতুতে চাষোপযোগী ভূখণ্ডের বনে আগুন লাগানো হত। বর্তমান কালেও অরণ্য অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। একে বলে ঝুম চাষ। আগুনে বন পরিষ্কার হলে দুই এক পশলা বৃষ্টির পর সেই জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। ছাইগুলো সারের কাজ করে। তারপর বর্ষার চাষ।
আগেই বলেছি রামায়ণে কৃষিভিত্তিক রামকথার পটভূমিকায় রহস্যে ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং ঐতিহাসিক মানবী সীতার ক্ষেত্রে বলা যায় বাল্যকালে তার বিবাহ হয়েছিল।
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্॥ ১৬ (৬.১১৮.১৬)
অর্থাৎ, বাল্যকালে শাস্ত্রানুসারে আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, তাহাও আপনি দেখিলেন না।
সুতরাং বিবাহকালে মানবী সীতা ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকা হওয়া অস্বাভাবিক নয়, স্বয়ম্বর নিশ্চয়ই হয়নি। বিবাহের বারো বৎসর পরে সীতার বয়স যখন আঠারো তখন ঐতিহাসিক রামচন্দ্র বনবাসে গমন করেন এবং সীতার প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন৷ লংকা জয়ের পর রামসীতার মিলনের পূর্বে সীতার অগ্নিপরীক্ষা (অগ্নিতে প্রবেশ নয়) হয়েছিল বসন্তঋতুতে। এক্ষেত্রে মানবী সীতা ও কৃষিশ্ৰী সীতাকে একটি সত্তায় ব্যক্ত করে রহস্য সৃষ্টি করা হয়েছে।
সীতা যখন লংকার অশোকবনে বন্দিনী, হনুমান সেখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে রামকে প্রদানের জন্য হনুমান অভিজ্ঞান প্রার্থনা করলে সীতা রামকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য চিত্ৰকূটে অবস্থানকালে বায়স ঘটনাটি বিবৃত করে হনুমানের হাতে চূড়ামণি প্রদান করেন।
এষ চূড়ামণিদিব্যে ময় সুপরিরক্ষিতঃ।
এতং দৃষ্টা প্রহৃষ্যামি ব্যসনে ত্বামিবানস্ব॥ ৭
এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান ময়া তে বারিসম্ভবঃ।
অতঃপরং ন শক্ষামি জীবিতুং শোকলালসা॥ ৮ (৫.৪০.৭-৮)
অর্থাৎ, আমি এ পর্যন্ত এই মনোহর চূড়ামণি সর্বতোভাবে রক্ষা করেছি। বিশেষতঃ তোমাকে দর্শন করলে যে প্রকার আনন্দ লাভ হয়, আমি ইহা দেখে সেরূপ আনন্দলাভ করছি। এই মনোহর সামুদ্র রত্নটি তোমার প্রত্যাভিজ্ঞানের জন্য প্রেরণ করলাম, তুমি শীঘ্র না এলে শোকনিবন্ধন উৎকণ্ঠায় প্রাণরক্ষা করতে পারব না।
রাম এই চূড়ামণি দেখে শোকে অভিভূত হয়ে বললেন,—
মণিরত্নমিদং দত্তং বৈদেহ্যাঃ শ্বশুরেণ মে।
বধুকালে যথাবদ্ধমধিকং মুর্দ্ধি শোভতে॥ ৪
অয়ং হি জলসম্ভূতো মণিঃ প্রবরপূজিতঃ।
যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শক্রেণ ধীমতা॥ ৫ (৫.৬৬.৪-৫)
অর্থাৎ, ধীমান ইন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হয়ে এই দেবপূজিত জলজাত রত্ন, যজ্ঞকালে জনককে দান করেন। আমার শ্বশুর জনকরাজ, সীতার শিরোভূষণের জন্য বিবাহকালে আমার পিতার নিকটে এটা সমর্পণ করেছিলেন। বৈদেহী এই মণির শোভাবর্ধনের নিমিত্ত সর্বদা মস্তকে ধারণ করতেন।
এই কাহিনীতে ‘ইন্দ্র’ শব্দে যজুর্বেদ অনুসারে বর্ষণদেবতাকে ইংগিত করছে। জমিতে বীজ বপনের পর ভূগর্ভস্থ জলের সংস্পর্শে বীজের অংকুরোদগম হয়। পরবর্তীকালে বৃষ্টিপাত হলে অংকুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে চারায় বা গাছে পরিণত হয়।
সীতার চূড়ামণি অংকুরিত বীজের প্রতীক। সীতা আঁচলের ভিতর হতে চূড়ামণি বের করেছিলেন। বীজের অংকুরোদগম হয় মাটির তলায়। উপরের আচ্ছাদনের মাটিকে সীতার বস্ত্রাঞ্চল কম্পন করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলকে সমুদ্র কল্পনা করে চূড়ামণিকে সমুদ্রজাত বলা হয়েছে।
সীতা হনুমানকে বারংবার একমাস কাল জীবিত থাকার কথা জানিয়ে ছিলেন।(১১) দক্ষিণায়ন কালে মেঘ সঞ্চারিত হয়ে বর্ষা সমাগম না ঘটলে বীজ অংকুরে নষ্ট হলে সীতার অর্থাৎ কর্ষিত জমির কৃষিশ্ৰী সত্তা বিঘ্নিত হয়। একারণে একমাস সময়কাল বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।
সুতরাং অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ ঘটেছিল বর্ষাঋতুর প্রথম মাসে, অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষে। বৰ্ষাঋতু শেষ হতে আর তখন একমাস বাকি।
অশোক বনে হনুমান বন্দিনী সীতার সন্ধান পেয়েছেন। এমন সময়
রাবণের আগমন। হনুমান বৃক্ষ মধ্যে শত শত পুষ্প এবং পত্রের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন। এটা বৰ্ষাঋতুর ইংগিত। তখন বৃক্ষাদি পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়। রাবণ এখানে অনাবৃষ্টির প্রতীক।
পরবর্তীকালে সীতার সম্মুখবর্তী হওয়ার প্রাক্কালে হনুমান শিংশপা বৃক্ষের (শিশু গাছ) পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে ইক্ষ্বাকু বংশের গুণকীর্তন করে সীতার বিশ্বাসভাজন হন। বর্ষাকালে শিশুগাছ পত্ৰশোভিত হয়। সুতরাং হনুমান গুপ্তচরবৃত্তি করতে লংকায় গিয়ে বৰ্ষাঋতুতে প্রথম সীতাকে দেখতে পান এবং পরে সাক্ষাৎকার।
রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করার কিছুকাল পরে লোক অপবাদ কারণে সীতাকে গঙ্গার অপর তীরে নির্বাসনে পাঠান। সীতা তখন গর্ভবতী। বাল্মীকি সীতাকে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন। ইতিমধ্যে রাম শত্রুঘ্নকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে লবণ-বধের জন্য মথুরায় পাঠান। শত্ৰুঘ্ন মথুরার পথে বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রি বাস করেছিলেন। সেই শ্রাবণের মধ্যরাত্রে লবকুশ জন্মগ্রহণ করেন।
যামেব রাত্ৰিং শত্রুঘ্নঃ পণশালাং সমাবিশৎ।
তামেব রাত্ৰিং সীতাপি প্রসূত দারকদ্বয়ম্॥ ১
ততোহদ্ধরাত্রসময়ে বালক মুনিদারকাঃ।
বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখুঃ সীতায়াঃ প্রসবং শুভমৃ॥ ২ (৭.৭৯.১-২)
অর্থাৎ, শত্রুঘ্ন যে রাত্রিতে বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করেন, সেই রাত্রিতেই সীতাদেবী দুটি পুত্র প্রসব করেন। মুনিপুত্রগণ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে বাল্মীকির নিকট এই শুভ সংবাদ নিবেদন করলেন।
কতকগুলি সাগ্রকুশ মধ্যভাগে কাটলে তার অগ্রভাগ কুশমুষ্টি এবং অধোভাগ লব বলে উক্ত হয়। বাল্মীকি ঐ কুশ ও লব বৃদ্ধাদের হাতে দিয়ে বললেন, যে আগে জন্মেছে তাকে কুশমুষ্টি এবং কনিষ্ঠকে লব দিয়ে সম্মার্জন করে। এই অনুসারে পুত্রদ্বয়ের কুশ ও লব নাম হয়।
শত্ৰুঘ্ন নিজের কুটিরে শুয়ে সব শুনলেন এবং চিন্তা করতে করতে শ্রাবণ মাসের সুদীর্ঘ নিশা কেটে গেল।
ব্যতীত বার্ষিক রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্ৰম॥ ১৩ (৭.৭৯.১৩)
সীতার পুত্র প্রসব সম্পর্কে ‘দারক’ শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ।
দারক অর্থ বিদারক, ভেদক, দুঃখনাশক, পুত্র। সুতরাং ‘দারক’ শব্দটি ব্যবহার করে বাল্মীকি একদিকে মানবী সীতার যমজ পুত্র প্রসব এবং অপরদিকে সীরখাতে বীজ হতে চারার আবির্ভাব উভয় ইংগিত রেখেছেন। কৃষিবিজ্ঞান অনুসারে বীজ হতে চারার আবির্ভাবের দুটি স্তর আছে। প্রথম অংকুরোদগমটিকে বলে বীজ-মূল যা পরবর্তীকালে শিকড়ে পরিণত হয়। দ্বিতীয় স্তরটির নাম ভ্রূণমুকুল, যা পরবর্তীকালে কাণ্ডে পরিণত হয়। এই দুটি স্তরকে যথাক্ৰমে কুশ ও লব নামে বাল্মীকি অভিহিত করেছেন।
শ্রাবণের রাত্রি, বর্ষার রাত্রি। রামায়ণের কালে শ্রাবণ বর্ষাঋতুর প্রথম মাস। সুতরাং জমিতে তখন বীজ হতে চারা উৎপন্ন হয়।
শত্ৰুঘ্ন লবণকে বধ করে মথুরাতে রাজধানী স্থাপন করে এক সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তোলেন। বারো বছর সেখানে বসবাসের পর রামকে দেখার বাসনায় শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় রওনা হন। পথিমধ্যে পনের দিন অতিবাহিত করে বাল্মীকি আশ্রমে রাত্রিবাসকালে আড়াল হতে কুশলবের মুখে রামায়ণ গান শোনেন।
সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছচ্ছত্বা শত্রুঘ্নণাসনম্।
নিবেশনঞ্চ শত্রুঘ্নঃ শ্রাবণেন সমারভৎ॥ ৮
স পুরা দিব্যসংকাশো বর্ষে দ্বাদশমে শুভে।
নিবিষ্ট শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়ঃ॥ ৯ (৭.৮৩.৮-৯)
অর্থাৎ, শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাস হতে পুরী (মথুরা) প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলেন। শুভ দ্বাদশ বৎসরের প্রারম্ভে সেই সুচারু নগর নির্মিত হল।
ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুঘ্নো রামপালিতাম্।
অযোধ্যাং চবমে গন্তুমল্পভূত্যবলানুগঃ॥ ১
ততো মন্ত্রিপুরোগাংশ্চ বলমুখ্যান্নিবৰ্ত্ত্য চ।
জগাম হয়মুখ্যেন রথানাঞ্চ শতেন সঃ॥ ২
স্ব গত্বা গণিতান্ বাসান্ সপ্তাষ্টৌ রঘুনন্দনঃ।
বালীক্যাশ্রমমাগত্য বাসং চক্লে মহাযশীঃ॥ ৩ (৭.৮৪.১-৩)
অর্থাৎ, দ্বাদশ বৎসরের পর কতিপয় অনুচর সঙ্গে নিয়ে রামপালিত অযোধ্যা নগরে যেতে বাসনা করলেন।
শত্ৰুঘ্ন মথুরা হতে যাত্রা করে পনের দিনের পর বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। লবণ বধের সময় বাল্মীকি আশ্রম হতে শত্ৰুঘ্ন সাতদিনে মথুরা পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এবার অযোধ্যার পথে মথুরা হতে বাল্মীকি আশ্রমে পৌছুতে পনের দিন অতিবাহিত হল। শত্রুঘ্ন মথুরার জনপদ স্থাপন করলেন, অথচ অযোধ্যার সঙ্গে যোগাযোগের পথ উন্নত করলেন না; এটা সমর্থনযোগ্য নয়। সুতরাং এই পনের দিনের উল্লেখ লক্ষণীয়।
শ্রাবণ মাসের মধ্যরাত্রে কুশলবের জন্ম হয়। এখানে ‘রাত্র’ শব্দটিতে নিশা এবং মাস দুই ই বুঝানো হয়েছে। মাস অর্থে ’রাত্র’ শব্দের ব্যবহার রামায়ণে অন্যত্র দেখা যায়। সুগ্ৰীবকে কিস্কিন্ধ্যারাজ্যে অধিষ্ঠিত করে রাম লক্ষ্মণ সহ বৰ্ষাঋতু প্রস্রবণগিরি-গুহায় কাটিয়েছিলেন।
ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশাল যুক্তমারুতা।
অস্যাং বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরামেরিন্দম্॥ ৬ (৪.২৭.৬)
অর্থাৎ, সুমিত্ৰানন্দন! এই গিরিগুহা পরম রমণীয় এবং বিস্তৃত, ইহাতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়, সুতরাং বর্ষার কয়েক মাস এস্থানে কাটাবো।
অতএব লবকুশের জন্ম হয়েছিল শ্রাবণ মাসের (নিশ্চয়ই চান্দ্র মাসে) পনের তারিখ এবং শত্রুঘ্ন যেদিন পুনরায় বাল্মীকি আশ্রমে আসেন, সেদিন লবকুশের বারো বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে দুই দফাতেই শত্ৰুঘ্ন সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। বাস্তবে, ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে, বাল্মীকির আশ্রমে সীতার অবস্থান এবং লবকুশের সত্য পরিচয় শত্রুঘ্নর নিকট অনিবার্য রাজনৈতিক কারণে গোপন রাখা হয়েছিল। এই কাহিনীতে একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে লবকুশ বারো বৎসর বয়স হতেই রামায়ণ গানে শিক্ষা গ্রহণ করেন।
সীতার একটি পূর্বকাহিনী আছে।
রাবণ ধরণীতলে ভ্রমণকালে হিমালয় পর্বতের নিকটস্থ বনে উপনীত হয়ে বিচরণ কালে কৃষ্ণজিনজটাধারিণী তপস্যারতা বেদবতীকে একাকিনী দেখে কামমোহিত হয়ে কন্যার পরিচয় জানতে চাইলে বেদবতী বললেন, “অমিতপ্রভ বৃহস্পতিসূত ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। সতত বেদাভ্যাসী কুশধ্বজের নিকট হতে বাংময়ী বেদ (কন্যা, মূর্তি) উৎপন্ন হয়। সুতরাং পিতা আমার বেদবতী এই নাম রাখেন। আমার পিতার ইচ্ছা ছিল বিষ্ণু তাঁর জামাতা হবেন। এজন্য আমাকে অন্য কাউকে দান করার ইচ্ছা নাই জেনে বলগর্বিত দৈত্যপতি শম্ভু কুপিত হয়ে অবশেষে নিশাকালে সুপ্ত অবস্থায় আমার পিতাকে বধ করে। আমার শোকার্ত মাতা পিতার দেহ আলিঙ্গন করে অগ্নিতে প্রবেশ করে। পিতার বাসন পূর্ণ করার জন্য আমার এই তপস্যা। সেই বিষ্ণু নারায়ণই আমার পতি।”
বেদবতীর পরিচয় পেয়েও তাকে লাভ করার বাসনায় রাবণ তার হাতের অগ্রভাগ দিয়ে বেদবতীর কেশ স্পর্শ করেন। রাবণের এই আচরণে নিজেকে ধর্ষিতা মনে করে বেদবতী রাবণকে অভিসম্পাত দিয়ে অনলে প্রবেশ করেন।
সৈষা জনকরাজস্য প্রসূত তনয়া প্রভো।
তব ভাৰ্য্যা মহাবাহো বিষ্ণুস্ত্বং হি সনাতনঃ॥ ৩৫
পূর্ব্বং ক্রোধহতঃ শত্রুর্যয়াসৌ নিহতস্তয়া।
উপাশ্রয়িত্ব শৈলাভস্তব বীর্য্যামমানুষম্॥ ৩৬
এবমেবা মহাভাগা মৰ্ত্তোযুৎপৎস্যতে পুনঃ।
ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদ্যামগ্নিশিখোপমা॥ ৩৭
এষা বেদবতী নাম পূর্বমাসাং কৃতে যুগে।
ত্রেতাযুগমনুপ্রাপ্য বধাৰ্থং তস্য রক্ষসঃ।
উৎপন্ন মৈথিলকুলে জনকস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৮ (৭.১৭.৩৫-৩৮)
অর্থাৎ, “সেই বেদবতী জনকরাজের কন্যারূপে জন্ম লইয়া তোমার (রামের) ভাৰ্য্যা হইয়াছেন এবং তুমিই সেই সনাতন বিষ্ণু পূর্বে বেদবতীর ক্ৰোধ দ্বারা যে শত্ৰু নিহত হইয়াছিল এক্ষণে সেই বেদবতীই তোমার অমানুষ বলের আশ্রয় লইয়া সেই শৈলাভ রিপুকে বধ করিয়াছেন। সেই মহাভাগ৷ বেদিমধ্যস্থা অগ্নিশিখার ন্যায় ভবিষ্যৎকালে পৃথিবীতে হলমুখ দ্বারা কর্ষিত ভূমিমধ্য হইতে এইরূপ বারবার উৎপন্ন হইবেন। পূর্বকালে সত্যযুগে ইহার বেদবতী নাম ছিল, ত্রেতাযুগ প্রাপ্ত হইয়া ইনি রাক্ষসকুলের বধের নিমিত্ত মৈথিলকুলে মহাত্মা জনকের কন্যারূপে জন্ম লইয়াছেন।”
বেদবতীর অস্তিত্ব ছিল সত্যযুগে। ঋগ্বেদের কালকে সত্যযুগ মনে করা যেতে পারে। সেকালে পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব হত। তখন কৃষিকাজ গৌণ কর্ম ছিল। বর্ষায় যে অঞ্চল জলে ডুবে যায়, শরতের পর হতে সেখানে ডাঙ্গা জেগে ওঠে। ঐ নরম পলিমাটিতে ছিটিয়ে ধান ও অন্য শস্য বোনা হয়। এই ধান বসন্তঋতুতে ঘরে ওঠে। নীবার বা উড়ি ধান বিলে বা জলায় আপনিই হয়। ধান পাকলে অল্প বাতাসে উড়ে যায় বা ঝরে পড়ে। এই ধানের অগ্রভাগে শূঁয়া থাকে এবং তুঁষের রং কালো।
এই কাহিনীর বেদবতী সহজাত ধানের রূপক। তুষের রং-এর ইংগিত রয়েছে ‘কৃষ্ণাজিন’ শব্দে এবং জটা তথা কেশের অগ্রভাগ অর্থে ধানের শুঁয়া। ধান পাকার সময় হলে শুঁয়া প্রথমে বিবর্ণ হয়।
বৃহস্পতির পৌরাণিক কাহিনী হল এর জন্ম পুষ্যা নক্ষত্রে। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি পুষ্টিবৰ্ধক (১।১৮।২) এবং ওষধি সমূহের জনক (১০।৯৭।১৫)। স্থান বিশেষে ঋগ্বেদে বৃহস্পতিকে অগ্নি বলা হয়েছে (২।১, ৩।২৬)(১২)।
অগ্নি অর্থাৎ তেজঃ-রশ্মিতে মেঘের উৎপত্তি। সুতরাং বৃহস্পতি-সূত কুশধ্বজ মেঘবর্ষণ দেবতা।
বর্ষায় বিল খাল জলে ভরে যায়, জলাজমি ডুবে থাকে। বর্ষান্তে জমিতে সহজাত ধান উৎপন্ন হয়। বেদ অর্থ বিষ্ণু; অর্থাৎ জল। জলের বাগ্ময়ী স্বরূপ সহজাত ধান, এজন্য নাম বেদবতী।
দৈত্যপতি শম্ভু মূলতঃ কালপুরুষ নক্ষত্র। মৃগশিরা নক্ষত্রে মিথুন রাশিতে সূর্য প্রবেশ করলে তৎকালে বসন্ত ঋতুতে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাম্পের ভাগ কমে যায়। অনুরূপ, ভূখণ্ডে জলস্তর নীচে নামতে থাকে। এই দুই অবস্থার রূপক শম্ভুর কুশধ্বজকে হত্যা এবং শোকে তার পত্নীর অনলে প্রবেশ।
বেদবতীর বিষ্ণু তথা নারায়ণকে পতি হিসাবে লাভের বাসনা অর্থে সহজাত ধানের অমরত্ব কামনা। কিন্তু রৌদ্রতাপ হেতু ফসল পাকে। রাবণ অর্থে রাবিতলোকত্ৰয়, অর্থাৎ লোকবাসীকে যে কাদায়। সুতরাং প্রখর সূর্য ধরা যায়। রাবণের কেশম্পর্শ তারই ইংগিত। রামায়ণে ‘রাবণ’ শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা ইষ্ট নষ্ট করে তাই রাবণ।
ত্রেতা যুগে অর্থাৎ দক্ষিণায়নাদি যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের পরবর্তী পুষ্যা নক্ষত্রে তখন কৃষিচর্চার প্রসার হেতু চাষের উন্নতি হওয়ায় যা ছিল সহজাত, তাই সীরখাতে বপন করে ফসল তোলার প্রাধান্য হেতু বেদবতীর জনকদুহিতাসীতারূপে আবির্ভাবের বর্ণনা। সুতরাং বেদবতী উপাখ্যান সীতার কৃষি চরিত্রটি দৃঢ়তর করছে।
রামায়ণের সীতা চরিত্রের মূল অংশগুলি বিশ্লেষণ করার পর চরিত্রটির কৃষিসত্তা যেমন সুস্পষ্ট হয়, তেমনি সীতার একটি মানবিক সত্তাকেও স্বীকার করে নিতে হবে।
সীতার এই দুই সত্তাকে একীভূত করে বাল্মীকি রহস্যর সৃষ্টি করেছেন। মনে করি, এই সঙ্গে সীতার আরও একটি সত্তা মিশে রয়েছে। সেটি হল লক্ষ্মীস্বরূপী-সীতার রাজশ্ৰী স্বরূপতা।
সীতা প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সীতাহরণের কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি। সত্যই কি সীতা নাম্নী কোন মানবী ঐতিহাসিক রামচন্দ্রর পঞ্চবটী আশ্রম হতে অপহৃতা হয়েছিলেন? মনে হয় না। অপহৃতা সীতা এখানে মানবদেহী রামের ভাগ্যশ্রী তথা রাজ্যশ্রী৷ লংকাপতি রাবণ মারীচকে দিয়ে রামলক্ষ্মণকে বিভ্রান্ত করে দূরে পাঠিয়ে রামের পঞ্চবটী অধিকার করেছিলেন। ফলে রামচন্দ্র রাজহারা হয়েছিলেন। পরে রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যার সুগ্ৰীবের সহায়তায় লংকা জয় করে সেই রাজশ্ৰীকে পুনরুদ্ধার করেন।
সীতাহরণ কাহিনীর মধ্যে রহস্যে জ্যোতিবিজ্ঞান তথ্যও ব্যক্ত করা হয়েছে। যে নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে প্রথম হলকর্ষণ করা হত, সেই নক্ষত্রকে সীতার জন্মনক্ষত্র ধরা যায়। উক্ত নক্ষত্রে গ্রহণ এবং একাধিক বৎসর অনাবৃষ্টির ইংগিত সীতাহরণ কহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে।
অনুরূপ, চিরকুট পাহাড়ের বায়স কাহিনী। এই কাহিনীতে ইন্দ্রপুর বায়স শনিগ্রহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। রামের বনবাস কালের কোনও এক সময়ে সীতার জন্ম নক্ষত্রে চন্দ্রর অবস্থানকালে শনিগ্রহের প্রবেশ এবং সেই অংশ হতে উক্ত গ্রহের গতির দিক পরিবর্তন শুরু। শনিগ্রহ বছরে বারো অংশ অতিক্রম করে। সুতরাং এক নক্ষত্র অতিক্রম করতে তেরো মাস কয়েকদিন সময় লাগে। দ্বিতীয় দফায় বক্ৰী গতিতে পুনরায় উক্ত নক্ষত্রকে স্পর্শ করে আবার মার্গী হয়। কাল নির্ধারণ জন্য এই জ্যোতিষ তথ্যটি রূপকে বর্ণনা করা হয়েছে। এবিষয়ে স্বতন্ত্র প্রকরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
এই সুদীর্ঘ আলোচনায় ঋগ্বেদের কাল হতে সীতার কৃষিশ্ৰী স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। ঋগ্বেদের কালে ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে দক্ষিণায়নাদিতে বর্ষ সমাগমে ধরিত্রী জীবধাত্রীরূপ হয়ে উঠত। বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে অরণ্য তার সম্পদ উজার করে দিত পরবর্তী ঋতুগুলিতে। এখানে সীতা মুখ্যতঃ বসুন্ধর।
পরবর্তীকালে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠলে সীতার ব্যাপকতর স্বরূপকে সংকুচিত করে কৃষিগ্রীতে রূপান্তরিত করা হল। তখন সীতা হল সীরখাত, মেঘবর্ষণ দেবতার পত্নী। সীতার কৃষিশ্রী-সত্তা রামায়ণের মূল উপজীব্য। এই আবরণের অন্তরালে বাল্মীকি ঐতিহাসিক তথ্য রহস্যে ব্যক্ত করেছেন। রামায়ণে সীতাকে বারংবার রোহিণী নক্ষত্রর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রামায়ণের কালে বৃষরাশিতে রোহিনী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মের প্রথম মাস। বৰ্ত্তমানকালেও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে দেখেছি কৃষিজীবিরা রোহিণী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল রয়োদশীতে ‘রোণীপরব’ উদ্যাপন করে। রোহিণী শব্দের অপভ্রংশ রোণী। অতি সাধারণ পরব, প্রায় বৈশিষ্ট্যহীন। কিন্তু পরবের ধরণ অনুসরণ করলে বুঝা যায় এর সঙ্গে কৃষিকাজ আরম্ভের যোগ রয়েছে। এ ছাড়াও ঐ অঞ্চলের চাষীরা সূর্য রোহিণী নক্ষত্র অতিক্রম করে গেলে ইতিমধ্যে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে অনাবৃষ্টি ও অনাবাদ আশংকা করেন। রোহিণী নক্ষত্র নিয়ে কৃষিজীবিদের এই ধ্যানধারণা অবশ্যই প্রাচীন যুগের স্মৃতি বহন করছে।
যাইহোক আপাতঃদৃষ্টিতে সীতার সঙ্গে তিনটি নক্ষত্রর যোগসূত্র টানা যায়। রোহিণী, পুনর্বসু ও পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র।
রামায়ণের অন্যান্য কাহিনী পর্যালোচনা কালে এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে। রামায়ণে বিভিন্ন ধরণের তথ্য এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে একটি মাত্র তথ্যকে সুস্পষ্ট করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য তথ্যগুলির প্রসঙ্গও উপস্থিত হয়। কৃষিশ্রী সীতার আলোচনার ক্ষেত্রে তাই মানবী সীতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি, যদিও রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের মানবিক সত্তা উদ্ঘাটনের জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।