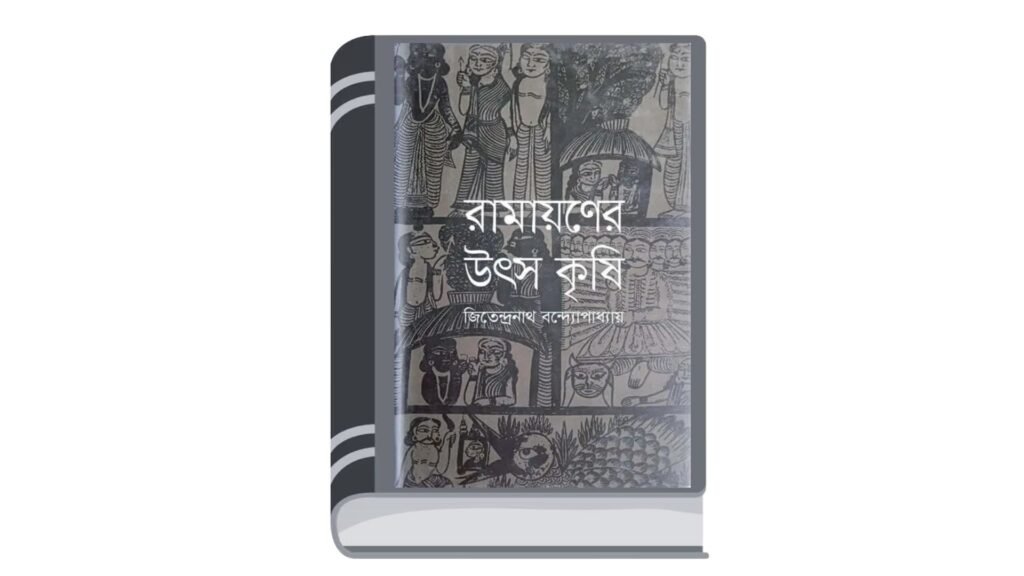০৮. ইক্ষ্বাকু বংশ – অষ্টম প্রকরণ
০৮. ইক্ষ্বাকু বংশ – অষ্টম প্রকরণ
রামায়ণের মূল কাহিনীতে তিনটি বংশের প্রাধান্য,—ইক্ষ্বাকু বংশ, জনক বংশ এবং এই দুই বংশের সংযোগসাধনকারী কুশ বংশ।
মেঘ-দেবতা রামের বংশ তালিকায় ব্রহ্ম তথা মহাশূন্য হতে প্রাণ তথা উদ্ভিদ জগতের আবির্ভাবের বিভিন্ন স্তরগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। জনক বংশে বীজ হতে পুনরায় বীজের উদ্ভবের প্রতিটি পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে। কুশ বংশে অল্পকথায় শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশ পাওয়া যায়।
এখানে স্মরণ রাখতে হবে একই শব্দ দ্বারা চিহ্নিত একটি চরিত্র সেই শব্দের বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একটা উদাহরণ রাখা যেতে পারে। বেদে ‘রঘু’ শব্দটি সূর্যর প্রতিপদ। দশরথ এবং রাম রাঘব নামে পরিচিত, অর্থাৎ সূর্য তথা সূর্য-সঞ্জাত। সুতরাং দশরথ শব্দে সূর্য, দশদিক, ঋতুচক্ৰ, গুচ্ছধর্মী উদ্ভিদ ইত্যাদি বুঝানো যায়। অপরদিকে ব্যক্তি দশরথের অপর নাম অতিরথ; অর্থাৎ বিশেষ বলবান পুরুষ। অতএব রামায়ণের ঐতিহাসিকতা যখন স্বীকার করা হবে তখন দশরথকে একজন রাজচক্রবর্তী হিসাবে গণ্য করতে হয়। কাহিনীতে প্রয়োজন বোধে এই সকল অর্থে ‘দশরথ’ শব্দটি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ চরিত্রটি পরিবেশিত হয়েছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে একটি চরিত্র মনে হলেও আসলে একাধিক তথ্যের রূপক।
ইক্ষ্বাকু বংশ ‘সূর্যবংশ’ নামে পরিচিত, অর্থাৎ সূর্য হতে উদ্ভূত। রামায়ণে এই বংশের রাজনবর্গের তালিকা কয়েক ধরণের পাওয়া যায়, ফলে বিভ্রান্তি রয়েছে। যেমন অম্বরীষকে কখনও বলা হয়েছে নাভাগের পুত্র, কখনও মান্ধাতার পুত্র, কখনও বা প্রশুশ্রুকের পুত্র। সুতরাং রামসীতার বিবাহ বাসরে বৈবাহিক রীতি অনুসারে উভয় পক্ষের যে বংশ-পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল, আলোচনায় সেই বংশানুক্ৰম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়; কারণ বিবাহ একfট উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। তাছাড়া রামসীতার বিবাহকে ভিত্তি করে রামায়ণের কৃষিস্বরূপ চিত্রটি সহজবোধ হয়। আসরে ইক্ষ্বাকু বংশের বিস্তারিত তালিকা পেশ করেন কুলগুরু বসিষ্ঠ। আর জনকবংশের উল্লেখ করেন সীতার পিতা সীরধ্বজ স্বয়ং।
ইক্ষ্বাকু বংশের তালিকা হল :– ১। ইক্ষ্বাকু ২। কুক্ষি ৩। বিকুক্ষি ৪। বাণ ৫। অনরণ্য ৬। পৃথু ৭। ত্রিশংকু ৮। ধুন্ধুমার ৯। যুবনাশ্ব ১০। মান্ধাতা ১১। সুসন্ধি ১২। ধ্রুবসন্ধি (এঁর এক ভাই ছিলেন, তার নাম প্রসেনজিৎ) ১৩। ভরত ১৪। অসিত ১৫। সগর ১৬। অসমঞ্জ ১৭। অংশুমান ১৮। দিলীপ ১৯। ভগীরথ ২০। ককুৎস্থ ২১। রঘু ২২। কল্মাষপাদ ১৩। শঙ্খণ ২৪। সুদর্শন ২৫। অগ্নিবৰ্ণ ২৬। শীঘ্ৰগ ২৭। মরু ২৮। প্রশুশ্রুক ২৯। অম্বরীষ ৩০। নহুষ ৩১। যযাতি ৩২। নাভাগ ৩৩। অজ ৩৪। দশরথ ৩৫। রাম এবং লক্ষ্মণ। লক্ষণীয় যে এক্ষেত্রে ভরত ও শত্রুঘ্নর কোন উল্লেখ নাই। (১)
ইক্ষ্বাকুর জন্মদাতা মনু, মনুর পিতা সূর্য। সূর্যকে উৎপন্ন করেন কশ্যপ। কশ্যপের পিতা মরীচি হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্ৰহ্ম স্বয়ং নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত; তিনি মায়াসমন্বিত পরব্রহ্ম হতে উদ্ভূত। অতএব ব্রহ্ম হতে রাম পর্যন্ত মোট একচল্লিশ জনের নাম পাওয়া যায়। এদের অনেকের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। উপরন্তু অনেক নামের সঙ্গে নানা পুরাণে নানা কাহিনী জড়িয়ে আছে, যেগুলোর সঙ্গে এই তালিকার সামঞ্জস্য নাই। যেমন যযাতির কাহিনী; শমিষ্ঠা ও দেবযানীকে নিয়ে। সেখানে নাভাগর প্রসঙ্গ নাই; হরিশচন্দ্র ও তার পুত্র রোহিতাশ্ব এই তালিকায় বাদ পড়েছে। সুতরাং এই তালিকায় প্রদত্ত নামগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কালে অনেক নামের সঙ্গে জড়িত বহুল প্রচলিত কাহিনী প্রয়োজনবোধে বর্জন করতে হবে। কারণ সেসব কাহিনীর মূল অন্যত্র, হয়ত একই নামের অন্য ব্যক্তি বিশেষের অথবা স্বতন্ত্র তথ্যের রূপক হতে পারে। পরবর্তীকালে নামসাদৃশ্য হেতু একটি সত্তার কাহিনী হয়ে উঠেছে।
দেখা যায় এই বংশ ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত। সুতরাং এই বংশ তালিকায় মহাকাশ বিজ্ঞান তথা সৃষ্টির রহস্য জড়িয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সৃষ্টির এই ক্ৰমবিকাশ কিভাবে ঘটল প্রথমে দেখে নিলে সুবিধা হবে।
মহাকাশের কোটি কোটি তারাজগতের একটিকে নাম দেওয়া হয়েছে ছায়াপথ। এই ছায়াপথের প্রায় দশ পনের হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি নগন্য নক্ষত্র আমাদের প্রাণদায়ী মহান সূর্য। কোটি কোটি বছর আগে এই সূর্যর দেহ হতে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে কালক্ৰমে সৌরজগতের গ্রহ সমুহের সৃষ্টি। এই গ্রহগুলির তৃতীয়টি আমাদের জীবনধাত্রী পৃথিবী। বিজ্ঞান বলছে মহাকাশের যেখানে গ্রহ নক্ষত্র কিছুই নাই, নাই সূক্ষানুসূক্ষ্ম কোন বস্তু, সেই নিরবিচ্ছিন্ন মহাশূন্যের ঘোর তমিস্রা ভেদ করে অজ্ঞাতঅস্তিত্ব কোন উৎস হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটি যুগ্মরশ্মি। এই যুগ্মরশ্মি তার চলার পথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি করছে সূক্ষানুসূক্ষ্ম কণিকা। কল্পনা করা যায় না এমন দুরন্ত গতিতে ছুটতে ছুটতে সেই কণিকা ও রশ্মির সংঘর্ষে উদ্ভূত হচ্ছে পরমাণুর সূক্ষাতিসুক্ষ বস্তু যা ক্ৰমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে হতে মহাকাশের তারাজগতে রূপায়িত হয়েছে। কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্রপুষ্ট একটি তারাজগতে অহরহ চলছে নক্ষত্রের সৃষ্টি, নক্ষত্রের স্থিতি এবং নক্ষত্রের মৃত্যু। এই ত্ৰিদশা-সমন্বিত তারাজগতের বর্তমানে প্রায় স্থিতাবস্থা প্রকৃতির একটি নক্ষত্র হল সূর্য-যে সূর্য নয়টি গ্রহের সাহচর্যে সৃষ্টি করেছে নিজস্ব সৌরজগৎ।
যে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর মানুষ চাঁদ জয় করে অন্য গ্রহে পদাপণের চেষ্টা করছে, সেই পৃথিবী তার আবির্ভাবের ঊষালগ্নে ছিল বিপুল বিস্তৃত অনিলপুঞ্জ মাত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে সেই অনিলপুঞ্জ একটা নিদিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছিল, যে ঘুর্ণনকে আজকের বিজ্ঞানে বলা হয় বার্ষিক গতি। এই বার্ষিক গতি ছাড়াও সেই অনিলপুঞ্জর নিজস্ব অক্ষোপরি একটা গতি সৃষ্টি হয়েছিল, যার আজকের পরিভাষা আহ্নিক গতি। সেই অনিলপুঞ্জেই আজকের পৃথিবীর সকল কার্যকারণ বর্তমান ছিল। ঘুর্ণির ফলে অনিলপুঞ্জটি ঘনীভূত হতে হতে তাপ বিকীরণ শুরু করে। ঘনীভবন এবং তাপ হ্রাস হেতু আলোক-সমন্বিত অনিলপুঞ্জতে সূক্ষাণুগুলির পরমাণু ও অণু এবং বস্তু পর্যায়ে রূপান্তর আরম্ভ হয়। সৃষ্ট সকল বস্তুই অনিলপুঞ্জর আহ্নিক গতির রীতিতে সংক্রামিত হয়ে একই রীতিতে পশ্চিম হতে পূর্বে ঘুর্ণিত হতে থাকে। নিদিষ্ট রীতি ও ক্ৰমে বাধা বস্তুগুলি অনিলপুঞ্জটির মেরুদণ্ডকে (মেরুরেখা বা অক্ষরেখা) কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে নিরাকার হতে সাকার অবস্থার দিকে এগিয়ে চলে। বহু কোটি বছর ধরে এই রূপান্তরের ফলে অনিলপুঞ্জটি বতুলাকার ধারণ করে, উপরিভাগটিও কঠিনীভূত হয়। রূপান্তরিত সেই অনিলপুঞ্জ, যা আমাদের আদিম পৃথিবী, তখনও তাপবিকীরণ ও দেহসংকোচন করে চলেছে : এখনও করছে। বস্তু বা পদার্থর পরমাণুগুলি সংযোজিত হয়ে বিভিন্ন মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব ঘটাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ তারতম্য অনুসারে কোনটা কঠিন, কোনটা তরল আবার কোনটা অনিল অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। এমনিভাবেই একদিন পৃথিবীপৃষ্ঠের কোথাও অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী, কোথাও সুগভীর খাদ সৃষ্টি হল। সৃষ্টি হল হিমবাহ, অন্তরীক্ষের জল-অণুগুলি আকস্মিক তাপহ্রাসে সরাসরি কঠিনতা লাভ করল। সূর্যদেহ হতে বিচ্ছুরিত কণিকাস্রোত এবং মহাজাগতিক রশ্মিগুলির পৃথিবীর পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ায় বাধা সৃষ্টি করে উদ্ভূত হল হাইড্রোজেন বলয়, চৌম্বক রশ্মিজাল, পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুস্থ অধিকর্ষ। সৃষ্ট হল আবহমণ্ডল, আবির্ভাব ঘটল মেঘের, মেঘ হতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় জলে পূর্ণ হল সুগভীর খাদগুলি, দুরন্ত বেগে শিলাময় পাহাড় হতে নামল জলধারা, মহাসমুদ্র স্থায়ী আসন পাতল পৃথিবীর বুকে। জলের ঘর্ষণে আবহমণ্ডলের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় তাপ-তারতম্য প্রভৃতি বিভিন্ন যোগাযোগে জন্ম নিল মৃত্তিকা। এত সব পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে দেহসংকোচনের দরুণ বার বার ভূপৃষ্ঠের চেহারার বদল হল। এসব ঘটনার কোন্টা আগে কোন্টা পরে অথবা সবই একসঙ্গে কিনা বলা শক্ত।
সেই দ্রুত পরিবর্তনশীল জড় পৃথিবীর মহাসমুদ্রে একদিন প্রাণের ম্পন্দন জাগল; আদি প্রাণের আবির্ভাব ঘটল, বিজ্ঞান পরিভাষায় যার নাম প্রটোপ্লাজম (প্রাণকোষ)। মোটামুটি ছয়টি জড় উপাদানে গঠিত প্রটোপ্লাজম নিজ দেহকে বহুধা বিভক্ত করে নিমেষে মহাসমুদ্রে দুধের সর পড়ার মত বিস্তৃত হয়ে গেল। তার পর একদিন, জল ও বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত উপাদানগুলিতে তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটবে না বুঝতে পেরেই হয়ত প্রটোপ্লাজম এক নতুন পথ ধরল, যা হল সালোকসংশ্লেষের (Photo Synthesis) দ্বারা সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেহ ধারণ। আবির্ভাব ঘটল ‘ক্লোরোফিল’ এর, উদ্ভিদজগতের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ভূ-পৃষ্ঠের জলে স্থলে শুরু হল উদ্ভিদের রাজত্ব। পাশাপাশি আবির্ভূত হল প্রাণী; জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী এবং সকলের শেষ ধাপে চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীব,— মানুষ। সেও আজ লক্ষ কোটি বছর আগেকার কথা। আদিম মানুষ পশুসংসৰ্গ ছেড়ে আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের জন্য পাথরের হাতিয়ার বানাতে শিখল। দল বাঁধল, দল বেঁধে আদিম পৃথিবীর বুকে বিচরণ শুরু করল এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত। অতি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহদের সেই প্রব্রজা প্রবৃত্তি বুঝিবা আজও মানুষের রক্তে মিশে আছে। ধীরে ধীরে মানুষ বুদ্ধির গোড়ায় শান দিয়ে কুঠারের সঙ্গে ধনুক তুলে নিল, বনের পশু হত্যা না করে পোষ মানিয়ে পশু প্রজননের সূত্র ধরে অল্প আয়াসে আহার সংস্থানের ব্যবস্থা করল। আরেকটু এগিয়ে নিছক প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর করে না থেকে ফসল ফলানোর কৌশল আয়ত্ব করে নিয়ে মানুষ জন্তু পর্যায় হতে সম্পূর্ণ নিজের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করল। ঘর বাঁধল, পরিবারের বন্ধন মানল, সমাজ গড়ে তুলল।
স্থূলভাবে এই হল মহাশূন্য হতে পৃথিবী এবং পৃথিবীর বুকে মানব সমাজ গড়ে ওঠার কাহিনী। এই বক্তব্যের বহু তথ্য সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে নানা ধরণের মতবাদ আছে। এখানে শুধু একটা মোটামুটি কাঠামো তুলে ধরা হল ইক্ষ্বাকু বংশের বিশ্লেষণের পটভূমিকা হিসাবে। আদিমকাল হতে মানুষ সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে প্রাচীন ধ্যান-ধারণারও রদবদল ঘটেছে। সুতরাং আজকের সৃষ্টি-তত্ত্বের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে অমিল হলেও রামায়ণের কালের মানুষের এ সম্পর্কে নিজস্ব একটি কল্পনা নিশ্চয়ই ছিল। এই আলোচনাও সেকারণে যুক্তি দিয়ে সেই কল্পনার তথ্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস।
সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিটি ধাপের একটা করে নাম দিলে কেমন হয়?
যেমন যুগ্মরশ্মি এবং তারাজগৎ সৃষ্টির মধ্য পর্যায়ে পরবর্তী সৃজনের কার্যকারণতাকে বলা যেতে পারে ব্রহ্মা, কেননা সেই পর্যায় নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত, অথচ মায়া-সমন্বিত পরব্রহ্ম; অর্থাৎ যুগ্মরশ্মি হতে উদ্ভূত। এই ব্ৰহ্মা হতে তারাজগৎ, যার নাম মরীচি; বর্তমানকালে এমন একটি তারাজগৎকে বলা হয় ছায়াপথ (Milky way)!
মরীচি–মৃ (নাশ করা)+ঈচি অপাতনে, যে (অন্ধকার) নাশ করে; কিরণ।
তারাজগৎ বস্তু-সমন্বিত আলোকরশ্মি ছাড়া আর কি?
তারাজগতের বিশেষ একটি অংশে প্রায়-স্থায়িত্ব-সম্পন্ন একটি নক্ষত্র আছে যার নাম সূর্য। সুতরাং সূর্য তারাজগতের যে বিশেষ অংশ হতে সৃষ্ট সেই অংশের নাম কশ্যপ। কশ্যপ,—কশ (শব্দ করা)+য (কৰ্ম্মে) = কশ্য— পা (পান করা) + ড কর্তৃ। কশ্য অর্থে মদ্য ধরে শব্দটিতে বুঝান হয়েছে যে, যিনি মদ্যপান করেন। শব্দময় এই অর্থও করা চলে। মহাশূন্য শব্দহীন নয়, সুতরাং যেখানে নক্ষত্র সৃজন হচ্ছে সেই শব্দময় স্থানের নাম কশ্যপ।
তারাজগতের ‘কশ্যপ’ স্থানের একটি নক্ষত্র আমাদের সূর্য।
সূর্যর পুত্র মনু। মন্ (জ্ঞান, মনন, পূজা, গর্ব, সস্তাবন, ধারণ, মান) + উ কর্তৃ। মনু শব্দটিতে মূলতঃ বুঝানো হয়েছে যে পরবর্তীকালে প্রাণের যে বিকাশ হবে, সূর্যদেহে সেরকম মনন বা ক্রিয়ার সবেমাত্র উন্মেষ ঘটছে।
মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। শব্দটি ইষ্ (ইচ্ছা, গমন, পুনঃ পুনঃ করণ) ধাতু নিষ্পন্ন। সুতরাং ইক্ষ্বাকু অর্থে সূর্যদেহ হতে ভবিষ্যত গ্রহের বিচুতির কারণে পুনঃ পুনঃ স্পন্দন অবস্থা।
ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষি। অর্থ হল জঠর অভ্যন্তর। অর্থাৎ, স্পন্দনের নিদিষ্ট রূপ।
এরপর বিকুক্ষি। কাহিনী অনুসারে একে ইক্ষ্বাকু বিসর্জন দেন। বি (নাই) কুক্ষি (জঠর মধ্য, অভ্যন্তর) (মধ্যে)। বিমুক্ষি শব্দে বুঝানো হয়েছে যে ইক্ষ্বাকু অর্থাৎ স্পন্দনের বিচ্যুতি। মাতৃগর্ভে শিশুর ভ্রূণ ভিন্নদেহী হলেও মাতৃদেহে সংলগ্ন থাকে, এই গর্ভস্থ সন্তানের অস্তিত্ব যেমন মাতা আপন সত্তা জেনেও ভ্রূণের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে, অথচ ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত মাতার দেহেরই একটা অংশ হিসাবে লীন হয়ে থাকে এমত অবস্থাকে বিকুক্ষি পর্যায় বলা যায়। যথা সময়ে মাত সন্তান প্রসব করে অর্থাৎ আপনাকে যথাযথ ঠিক রেখে আপন দেহজাত একাংশকে বিসর্জন দেয়।
বিসর্জনের পর সন্তানের স্বাতন্ত্র্য পরিচয়, তখন নাম হল বাণ। বন্ (শব্দ করা, গমণ করা, ব্যপ্ত হওয়া) ধাতু নিপন্ন বাণ শব্দের অর্থ শর, তীর, অগ্নি, আগুনের আঁচ, শব্দ, ধ্বনি, বন্য প্রভৃতি। সুতরাং সূর্যদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বিরাট শব্দময় রশ্মি-সমন্বিত অবস্থাকে বাণ বলা হয়েছে।
বাণের পর অনরণ্য। ন (নাই) অরণ্য (বন, নিবিড়, ঘন) যার। অঘন তেজোময় বিরাট এক অনিলপুঞ্জ সূর্যদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘূর্ণিত হচ্ছে। সেই বিশাল বিস্তৃত স্থূল মহৎ অনিলপুঞ্জ, পরবর্তীকালে যা পৃথিবী নামক গ্রহে পরিচিত হয়, তার নাম পৃথু। পৃথুর কাহিনীতে আছে এঁর স্ত্রীর নাম অর্চি। ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং লোকহিতার্থে গোরূপা ধরিত্রীকে দোহন করেছিলেন। মর্তে ইনি প্রথম রাজা এবং এঁর নামানুসারে ধরার নাম পৃথ্বী। অর্চি অর্থ কিরণ। অশ্বমেধ যজ্ঞ অর্থ রশ্মি বিচ্ছুরণ গোরূপ ধরিত্রী অনিলপুঞ্জ-ময় অতীত পৃথিবী। মর্তে প্রথম রাজ অর্থে অনিলপুঞ্জটির আপন কক্ষপথে স্বতন্ত্র বিচরণ।
অতএব কাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত অর্থ দাঁড়ায় সূর্যদেহে প্রথম স্পন্দনের নাম মনু। স্পাদনের তীব্রত বাড়লে ইক্ষ্বাকু। সূর্যদেহের চারিদিকে একটি বলয়ের আবির্ভাব ঘটলে কুক্ষি। বলয়টি মূল দেহ হতে বিচুত হলে বিকুক্ষি। বিচ্যুত বলয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাব ধারণ করলে বাণ স্বতন্ত্র বলয়টির অঘনীভূত অবস্থা অনরণ্য। বলয়টি রূপান্তরিত হয়ে পিণ্ডাকার ধারণ করলে পৃথু। এই আদিম পিওটি প্রথম হতেই সূর্যকে কেন্দ্র করে আপন কক্ষপথে রশ্মি বিচ্ছুরণ করতে করতে আবতিত হতে লাগল।
এরপর ত্ৰিশংকু। এর সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বিখ্যাত কাহিনীটি এই আলোচনার অন্তর্গত হবে না। কেন না সেই ত্ৰিশংকু হরিশ্চন্দ্রর পিতা। যদিও বিশ্বামিত্রর ক্ষমতার বিবরণ কালে এই কাহিনীর অবতারণা হয়েছে, কিন্তু সেখানে হরিশচন্দ্রর উল্লেখ নাই। এজন্য ত্ৰিশংকুকে এই পর্যায়ে অন্য দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করতে হবে।
ত্ৰিশংকু-টি (তিন) শংকু (শঙ্ক, ভয়, ত্রাস) যাহার। শংকু শব্দটি শনক্ (ভয় সংশয়) ধাতু নিষ্পন্ন। পৃথু নামক অনিলপুঞ্জটিতে তিন ধরণের ক্রিয়া শুরু হল; ষেমন আবর্তন বা গতি, তাপ বিকীরণ এবং দেহসংকোচন যেন ভয় হতে এইগুলির উদ্ভব, তাই নাম হল ত্ৰিশংকু।
এবার ধুন্ধুমার; অপর নাম কুবলয়াশ্ব বা কুবলাশ্ব। ধুন্ধ অর্থ ধূম বা ধোঁয়া ধুন্ধুমার অর্থ সোরগোল, কোলাহল, হৈ চৈ। কুবলয়াশ্ব,-কুবলয় (কু অর্থাৎ পৃথিবীর বলয় রুপ বা পদ) + অশ্ব (রশ্মি)। ত্ৰিশংকু অবস্থার অনিলপুঞ্জটিব আকৃতি যখন পদ্মফুলের মত, রশ্মি বিচ্ছুরণ তখন পাপড়ি সদৃশ। অথবা রশ্মি ও কণিকার অর্থাং ধোয়ার বলয়-সমন্বিত। এই ধোঁয়া বা রশ্মি পদার্থে পরিণত হওয়ায় আগামী দিনের পৃথিবীর আবির্ভাব। সুতরাং ধুন্ধুমার।
এরপরে যুবনাশ্ব। যুবন (তারুণ্য) + অশ্ব (রশ্মি)। ধূম্রাচ্ছাদিত অনিলপুঞ্জটি তখন জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করেছে।
তারপর মান্ধাতা। বিখ্যাত মান্ধাতা পিতা যুবনাশ্বর বামপার্শ্বদেশ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। মান্ধাতার প্রচলিত কাহিনী এখানে গ্রহণ করা হবে না, কারণ সেই কাহিনীর মান্ধাতার পুত্রের নাম মুচুকুন্দ বশিষ্ঠ প্রদত্ত বংশ তালিকানুসারে মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি।
মান্ধাতা-মাম্ (আমাকে)—ধে (পান করা) + তৃন্ কর্তৃ। অথবা, মাম্ (আমাকে) ধাতা (ধারক, নির্মাণকৰ্তা)।
ঘূর্ণন, তাপ বিচ্ছুরণ এবং দেহসংকোচন দরুণ জ্যোতির্ময় অনিলপুঞ্জটির পৃষ্ঠদেশ কঠিনতা লাভ করতে আরম্ভ করে; কারণ তখন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের অণুগুলির অবস্থান্তর ঘটতে শুরু করেছে। এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে। অনিল, তরল ও কঠিন পদার্থ সমন্বিত যুবনাশ্ব পিওটির আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতির কারণে গতিধর্ম অনুসারে ভারী বস্তুগুলি প্রথমতঃ বামদিকে জমা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ পৃথিবীর উভয় গতি পশ্চিম হতে পূর্বে। তারপর ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কাঠিন্যের পাশাপাশি রয়েছে তরল পদার্থ, যা পৃথিবীর কঠিন পিঠের নিম্নাংশকে আবৃত করে রেখেছে। যত কেন্দ্রবিন্দুর দিকে যাওয়া যায় বস্তু সকল সেখানে অনিল অবস্থায়। পিণ্ডাকার পৃথিবীর এই অবস্থান্তর প্রকাশের কারণে মান্ধাতার বামপার্শ্বদেশ হতে জন্ম। পৃথিবীর আদিমতম অবস্থার নাম মান্ধাতা হওয়ায়, প্রাচীনকাল বলতে বলা হয় ‘মান্ধাতার আমল’।
তিন অবস্থাপ্রাপ্ত পদার্থময় পৃথিবীতে যে সহাবস্থান অবস্থা চলেছে, সেই পর্যায়ের নাম সুসন্ধি। সু (উৎকৃষ্ট) সন্ধি (মিলন) যাহাতে। সুসন্ধি সংজ্ঞায় পৃথিবীর দুই প্রকার আবর্তন, তাপহ্রাস এবং দেহসংকোচন মধ্যে যে সামঞ্জস্য ঘটেছে তাই বুঝানো হয়েছে।
সুসন্ধির পরে ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুব অর্থ স্থির, অপরিবর্তনীয়। বিস্তরের পদার্থময় পৃথিবীর আকৃতি এবং প্রকৃতির পরিবর্তন হেতু বার্ষিকগতি ও আহ্নিকগতির প্রতিনিয়ত যে তারতম্য ঘটছিল তা এখন একটি নিদিষ্ট নিয়মে ও কক্ষপথে সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই ধ্রুবসন্ধি পর্যায়ে পৃথিবীদেহ হতে কিছু অংশ বিচ্যুত হয়ে স্বাতন্ত্র্যলাভ করে এবং পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে থেকে নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তিত হতে থাকে। এই নবসৃষ্ট বস্তুটি প্রসেনজিৎ তথা চন্দ্র উপগ্রহ। প্রসেন শব্দে পৃথিবীকে বুঝানো হয়েছে, তাকে জয় করেই যেন চন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য।
ধ্রুবসন্ধির ভাই প্রসেনজিৎ। প্রসেন (প্রকৃষ্ট সেনা যার) তাহাকে যিনি জয় করেন। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রের সৃষ্টি কিভাবে তা এখনও স্থিরিকৃত হয়নি। হয়ত আদিমতম কোনও এক কালে কোন ধূমকেতুর আকর্ষণে পৃথিবীর সামান্য অংশ বিচুত হয়ে এই উপগ্রহের সৃষ্টি। রামায়ণের কালে এ নিয়ে কোন কল্পনা থাকা বিচিত্র নয়।
তারপরের আবির্ভাব ভরত। ভূ (পোষণ, ধারণ, ভর্জন, ভৎর্সনা) ধাতু নিষ্পন্ন। অর্থ তন্তুবায়, ক্ষেত্র। শব্দটির বানান ‘ভরৎ’ ধরলে অর্থ হয় ধারণকারী। এই অবস্থায় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেহ কাঠিন্য হেতু উচ্চাবচ আকার ধারণ করেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের বিস্তর-পদার্থের সংঘট্টে যৌগিক পদার্থসমূহের আবির্ভাবের দরুণ বায়বীয় তথা অনিল মণ্ডলর সৃষ্টি। বিভিন্ন অনিল পদার্থে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ যখন ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে প্রায়অন্ধকার, তখন নাম হল অসিত। ন (নাই) সিত (শ্বেত) অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ, আলোহীন, মেঘাচ্ছন্ন।
পৃথিবীর এই অসিত পর্যায়ের পরের অবস্থাকে বলা হয়েছে সগর। গর (বিষ, বৈপরীত্য)এর সঙ্গে বর্তমান। ইনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বিমাতা গর্ভ নষ্ট করার জন্য বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি গরলসহ ভূমিষ্ট হন। সগর সম্পর্কে এই কাহিনী ছাড়াও আরেকটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে এর অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র চুরি করে নিয়ে গিয়ে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে রেখে এসেছিলেন। এই কপিল মুনির ক্ৰোধে সগরের শতপুত্র ভস্মীভূত হয়। পৃথিবীর জড় রাজত্বে প্রাণের আবির্ভাব নিশ্চয়ই বিপরীত-ধৰ্মী। অপরদিকে প্রাণের ক্ষেত্রে বিষতুল্য পরিবেশে আদি প্রাণের আগমন গরলসহ ভূমিষ্ট হওয়ার সামিল। কপিল শব্দের একটি অর্থ অগ্নি। অন্তরীক্ষের (ইন্দ্র) তেজ ভূমণ্ডলে অগ্নি নামে খ্যাত। অঙ্গার, উদযান, যবক্ষারজান, অম্লজান, গন্ধক আর যে কোন একটি উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট প্রাণকোষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোষটির কেন্দ্রবিন্দু—যা তেজ বা অগ্নি-সমন্বিত। এই প্রাণকোষ হয়ত অনিল পদার্থর মত বায়বীয় মণ্ডল অথবা অন্তরীক্ষে অবস্থান করে। তরল জলের অভাবে প্রাণকোষের বিস্তার ঘটে না। প্রসঙ্গটি সহজবোধ করার জন্য বলা যায় বাতাসে অবস্থিত এক প্রকার বিশেষ জীবাণু দুধের মত উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সেই দুধে বংশবিস্তার করে দুধকে দই-এ রূপান্তরিত করে। প্রাণকোষের ক্ষেত্রেও অতীতে এই রকম ধারণা পোষণ করা বিচিত্র নয়।
কপিল শব্দের আর একটি অর্থ কুক্কুর।
কুক্কুর-কুক্ (কুক্ষি, উদর) কুর (শব্দ)। অর্থাৎ পৃথিবীর উদরে (অভ্যন্তরে) যে শব্দশক্তি (স্পন্দন বা তরঙ্গশক্তি) ভাবার্থে মাধ্যাকর্ষণ, যা সকল বস্তুকে পৃথিবীর দিকে টানে।
ফলে বস্তুর পলায়ন-প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় পথিবীতে তাদের নানা রূপান্তর। এই রূপান্তর বা বন্ধনকে রূপকে বলা হয়েছে কপিলক্ৰোধে শত পুত্র ভস্মীভূত। এখানে ভস্মীভূত অর্থে রূপান্তরিত ধরতে হয়।
পৃথিবীর এই অবস্থার কালে অতি প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন (উদ্যান) অণুর নিঃসরণ শুরু হয়েছিল, এই ক্রিয়াকে বলা হয়েছে সগর তার পুত্র অসমঞ্জকে উচ্ছৃংখলতার জন্য ত্যাগ করেন। অসমঞ্জ অর্থ অসদৃশ, অসংগত, অনুপযুক্ত। এই নিঃসরিত হাইড্রোজেনকে ধরে রাখতে না পারলে পথিবীতে কোনদিন প্রাণের আবির্ভাব ঘটত না। পৃথিবীর উর্ধ্বমহলে অন্তরীক্ষে হাইড্রোজেন বলয় সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য।
তাই অসমঞ্জর চেয়ে তার পুত্র অংশুমানের প্রাধান্য বেশী। অংশুমান অর্থ কিরণ বিশিষ্ট, প্রভাবশালী। মাধ্যাকর্ষণ তার ছড়িয়ে দেওয়া অদৃশ্য কিরণে সকল বস্তুকে পৃথিবী অভিমুখে ধরে রেখেছে।
এই সঙ্গে আরও একটি ক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, তা হল চুম্বক-রশ্মিজাল, যা সূর্যদেহজাত প্রোটিন-কণিকা-স্রোত প্রভৃতিকে সরাসরি পৃথিবী-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়তে বাধার সৃষ্টি করল। এই চুম্বক-রশ্মি পথিবীর অভ্যন্তর হতে যেমন বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তেমনি মহাজাগতিক রশ্মিগুলিকেও বহুলাংশে শোষণ করে নিচ্ছে। তাই পথিবীর এই অবস্থার নাম দিলীপ; শব্দটি দল (ভেদ, বিকাশ পাওয়া) ধাতু নিষ্পন্ন।
দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগ শব্দের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, শক্তি, যোনি প্রভৃতি বহু অর্থ। ইনি শৈশবে মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলেন। অষ্টবক্ৰ মুনির বরে উত্তমাঙ্গ হন। কপিলের শাপে ভস্মীভূত পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ধারাথে গোকৰ্ণ তীর্থে বহুকাল তপস্যা করে গঙ্গাকে ভূমণ্ডলে এনেছিলেন। এই পর্যায়ে দিলীপ নামক পথিবীর আবহমণ্ডলে জলের সঞ্চার।
গোকৰ্ণ,–গো (রশ্মি), + কর্ণ (প্রসারতা); অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, যেখানে জলকণা অণু অবস্থায় বিদ্যমান। পথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের মূলে জল, সুতরাং অন্তরীক্ষের জল-অণু আগামী দিনে যে ঐশ্বর্য নিয়ে এল তাই ভগীরথ। কাহিনীতে গঙ্গা জলের প্রতীক।
সঞ্চারমান বিশাল মেঘপুঞ্জকে বলা হয়েছে ইন্দ্রের ককুদ। বজ্র বিদ্যুতের সংঘর্ষে মেঘ হতে বৃষ্টি ঝরে। তাই বলা হল ককুৎস্থ। এর অন্য নাম পুরঞ্জয়। ইনি বিষ্ণুর পরামর্শে মহাবৃষভরূপী ইন্দ্রর ককুদে চেপে যুদ্ধে অসুর দমন করেন। সেজন্য নাম হয় ককুৎস্থ। অর্থাৎ, জলকণাময় বিস্তৃতদেহী মেঘপুঞ্জে বিদ্যুৎ সংযোগে যে রুপান্তর; বৃষ্টিপাতের পূর্বাবস্থা। সূৰ্যঃ (ইন্দ্র) বৃষরাশিতে সঞ্চরণকালে নভঃ-মণ্ডলে মেঘের আবির্ভাব হত ঋগ্বেদকালে। পুরঞ্জয়; পুর (দেহ, নগর) বা পুর (প্রবাহ, জলরাশি)—জি (জয় করা) খশ্ কর্তৃ।
ককুৎস্থর পুত্র রঘু। রঘ্ (গমন করা) + কু (পথিবী) কর্তৃ। অন্তরীক্ষের মেঘ হতে পথিবীর বুকে বারিধারা নেমে এল। কঠিন নিষ্প্রাণ পথিবীপষ্ঠের খাদগুলিতে জল জমে মহাসমুদ্রের সৃষ্টি হল, অন্য দিকে তাপহ্রাসজনিত আকস্মিক পরিবর্তনে জল অণু হতে সরাসরি পর্বতচূড়ায় হিমবাহরও সৃষ্টি। এই অবস্থার নাম কল্মষপাদ। অর্থ অগ্নি বিশেষ, শ্বেতকৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত। কলুষ-কল্গমন করা) ক্কিপ কর্তৃ = কল (যে গমন করে)। মস্ (হানি করা) + আ-কর্তৃ = মাস (যে অন্যকে নট করে)। সুতরাং তেজ বা অগ্নির রূপান্তর বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ সংস্পর্শে মেঘ বিদারণ হেতু চরাচরে জলবর্ষণ। অপরদিকে হিমবাহর মধ্যে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। এজন্য বলা হয়েছে অগ্নিবিশেষ কল্মাষপাদ। তাপ সৃষ্টি হয় বলেই হিমবাহ বিগলিত জলধারা নদীতে রূপান্তরিত হয়; যেমন গঙ্গানদীর উৎস গোমুখী।
কল্মাষপাদের পর শঙ্খণ। শব্দটি শম্ (শান্তভাব, দমন, উপশম, নিবৃত্তি) ধাতু নিপন্ন। হিমবাহ হতে উদ্ভুত জলীয় বাষ্পর দরুণ পৃথিবীর যে রূপ তাকেই বলা হয়েছে শঙ্খণ। রৌদ্রতেজে হিমবাহ হতে যে বাষ্প উর্ধ্বে উঠে যায়, তার নীচের দিকটা শঙ্খর মতই সরু ও পেটমোট এবং দক্ষিণ বা বামাবর্তে সেই বাম্পের উর্ধ্বগতি। অথবা, বলা যায় যে, মেঘমণ্ডলে তখন ঘন ঘন বজ্রধ্বনি উঠছিল, সেই শব্দময় পৃথিবী চিহ্নিত হয়েছে শঙ্খণ নামে।
অন্তরীক্ষের মেঘসন্টার, হিমবাহ ও তদুদ্ভূত শঙ্খাকার বাষ্প এবং শিলাময় ভূখণ্ডে পৃথিবী তখন অপরূপা। সুতরাং এই পর্যায়ের নামকরণ হয়েছে সুদর্শন।
এই সুদৰ্শন-পৃথিবীর উপর সূর্যর আলো পতিত হয়ে যে শোভা ধারণ করেছে তার নাম অগ্নিবৰ্ণ।
পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে উচ্চভাগ হতে নিম্নভাগে নেমে আসা জলস্রোতের সঙ্গে অন্তরীক্ষ হতে আদি প্রাণকোষ পৃথিবীর মহাসমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে তরিৎ গতিতে যে বংশ-বিস্তার করল, ‘শীঘ্ৰগ’ শব্দে সেই ক্রিয়া বুঝান হয়েছে।
জলস্রোতে পাহাড়ের ধ্বস ভেঙ্গে পাথর গুড়িয়ে জলবায়ুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার জন্ম হলেও পৃথিবী তখনও উদ্ভিদহীন, তথা প্রাণহীন। সুতরাং বলা হয়েছে মরু।
এরপরে প্রশুশ্রুক। প্র (প্রকৃষ্ট) শুশ্ৰু (শ্রোতা) যে, শুশ্রু শব্দটি শ্র (শ্রবণ, গতি) ধাতু নিষ্পন্ন। মহাসমুদ্রে যে প্রাণকোষ (প্রটোপ্লাজম) সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রাণ এখন বংশ বিস্তারের উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে মহাসমুদ্রে এবং জলসিক্ত স্থলে শৈবাল-এর সৃষ্টি করল। শৈবাল (Algae) এর নাম দেওয়া হয়েছে প্রশুশ্রুক।
শৈবাল এবং মস্ (Bryophyta) পর্যায়ের মাঝে ছত্রাক (Fungus) | ক্লোরোফিল-সৃজন-শক্তিহীন বস্তুটির আকার গোলাকার বা ছাতার মত। ‘ছত্রাক’ পর্যায়ের নাম অম্বরীষ। অর্থ অন্তরীক্ষ, ভর্জনপার, নরক বিশেষ। ভাজনাখোলা শব্দময় (যার বৃদ্ধি বা গতি আছে তাই শব্দময়) এবং ছাতার আকার। অপরদিকে জল হতে উৎপন্ন অর্থে নরক ধরলে ছত্রাকের সৃষ্টিকর্তা প্রাণকোষ জল হতে উদ্ভূত। তৃতীয়তঃ, ছত্রাকে যে জীবাণু থাকে সেটির আদি বিচরণক্ষেত্র অন্তরীক্ষ।
এবার নহুষ। শব্দটি নহ্ (বন্ধন) ধাতু নিষ্পন্ন। নহুষের ত্ৰৈলোক্যর রাজা হওয়া এবং অগস্ত্য মুনির শাপে অজগররূপ ধারণ করা, এই উপাখ্যানটি চন্দ্র বংশীয় আয়ুর পুত্র নহুষের ধরে নিয়ে এই আলোচনায় টান হল না, যেমনটি বাদ দেওয়া হয়েছে অম্বরীষ-শূনঃশেফ কাহিনী। নহুষ হল মস্ পর্যায়। পাকাবাড়ীর ছাদের কার্নিশে মখমলের মত নরম সবুজ ঘন সন্নিবিষ্ট শেওলা জাতীয় যে উদ্ভিদ দেখা যায় তাকে মস্ বলে। ঘন সন্নিবেশের দরুণ নহ ধাতুজ ‘নহুষ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
নহুষের পুত্র যযাতি। য (বায়ু)—যা (যাওয়া) +তি কর্তৃ; অর্থাৎ, যা বায়ুতে গমন করে।
মস্ পর্যন্ত উদ্ভিদের বিস্তার আছে, কিন্তু উচ্চতা নাই, অর্থাৎ উর্ধ্বদিকে বৃদ্ধি পেয়ে বায়ুমণ্ডল আবৃত করে না।
কিন্তু মস্ এর পর ফার্ণ (Ptcrid০phyta) জাতীয় উদ্ভিদ উচ্চতায় তালগাছের মতও হয়। আদিম পৃথিবীর ফার্ণ হয়ত আরও বড় ছিল। ছোট বা বড় যাইহোক ফার্ণ প্রথম বায়ুতে গমন করল।
যযাতি-দেবযানি-শমিষ্ঠার একটি সুন্দর গল্প আছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু যেহেতু সেই যযাতির পুত্র হিসাবে নাভাগর নাম উল্লেখ নাই, সে কারণে ঐ কাহিনী আলোচনার গণ্য হল না।
ফার্ণ এর পরের ধাপে পাইন (Gymnosperm) অনাবৃতবীজ উদ্ভিদ। এই পর্যায়ে প্রথম উদ্ভিদজগতে বীজের আবির্ভাব ঘটে। এই বীজের কোন আবরণ নেই, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। বাতাস এবং কীটপতঙ্গ দ্বারা স্ত্রী পুরুষ সম্মেলনে বীজের প্রজনন ক্ষমতা সৃষ্ট হয়। বীজ পাকার পর ঝরে পড়ে গাছ হয়। এই প্রসঙ্গে শৈবাল ইত্যাদির প্রজনন পদ্ধতিটা জেনে নেওয়া যেতে পারে। কোষ বিভাজন দ্বারা শৈবালের বংশবৃদ্ধি। শৈবাল পিচ্ছিল বস্তু; মূল, পাতা বা কাণ্ড নাই। মস্-এর পাতা ও কাও আছে, কিন্তু মূল নাই; তবে মূলের মত একটি অংশ আছে। তাকে বলা হয় রাইজয়েড (Rhyzoide)। মসের কাণ্ডের মাথায় একটি আধার (Capsul) তৈরী হয়, সেই আধারে দানার মত একটি বস্তুর, যাকে বলা হয় স্পোর (Spore), দরুণ বংশবৃদ্ধি ঘটে। উভলিঙ্গের মত বৈশিষ্ট্য। পাইনের অনাবৃত বীজ, যার স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদ সুস্পষ্ট এবং বংশবৃদ্ধির দরুণ স্ত্রী পুরুষের মিলন প্রয়োজন।
এই অনাবৃত বীজ উদ্ভিদ পর্যায়কে বলা হয়েছে নাভাগ। না অর্থ পুরুষ, অর্থাৎ পুরুষের ভাগ বা ভূমিকা যেখানে সুনিদিষ্ট।
নাভাগর পুত্র অজ। অর্থ খাঁটি, ঠিক, আদৎ।
অজ শব্দের অন্য অর্থ শস্য বিশেষ, বিষ্ণু ইত্যাদি।
অনাবৃত বীজে উদ্ভিদজগতের যে অপূর্ণতা ছিল, তা সুষ্ঠুরূপ পেল আবৃত বীজ উদ্ভিদ (Angiosperm)-এর আবির্ভাব ঘটায়।
এই পাঁচ জাতীয় উদ্ভিদ এবং এদের পরস্পরের সংযোগে উদ্ভূত সংকর উদ্ভিদ ভূমণ্ডল আছন্ন করে প্রাণের জয়যাত্রার সহায়ক হয়েছে। এই আবৃতবীজ উদ্ভিদ পর্যায় যে সত্যরূপ তাকে ‘অজ’ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।
অজর পুত্র দশরথ। দশ অর্থ সংখ্যা-বিশেষ (১০), দশবাচক যথা হস্তাঙ্গুলি, বহুবচন বোধক শব্দ। রথ অর্থে কায়, চরণ, বেতসলতা। সুতরাং দশরথ অর্থে বহুচরণ বিশিষ্ট।
তৃণ পর্যায় উদ্ভিদ হতে শস্য উৎপাদক উদ্ভিদের (যথা ধান, গম, যব ইত্যাদি যাদের একটি চারা হতে অনেকগুলি কাঠি বা ডাটা আবির্ভত হয়) উদ্ভবকে বলা হয়েছে দশরথ। এই জাতীয় উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম একবীজ-পত্রী (Monocotyledon) |
এখানে বলা প্রয়োজন দশরথ শব্দটি নানা অর্থে প্রয়োগ করা যায়। যেমন সূর্য, অন্তরীক্ষ, নভঃমণ্ডল, ঋতুচকু ইত্যাদি। শব্দটি বিভিন্ন অর্থে রামায়ণে ব্যবহত হয়েছে রূপকের স্বার্থে। রাম লক্ষণের পিতা দশরথ অর্থ অন্তরীক্ষ; কৌশল্য-কৈকেয়ী-সুমিত্রার পতি দশরথ অর্থে ঋতুচক্ৰ।
ইক্ষ্বাকু বংশের নামের তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট উপকাহিনী বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টি-তত্ত্বের সঙ্গে যে মিল দেখানো হয়েছে তা কি খুব কষ্টকল্প মনে হয়?
অনেক নামের সঙ্গে জড়িত বহুল প্রচারিত কাহিনীগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে এই আলোচনা হতে, তার মূল কারণ বিবাহবাসরে বসিষ্ঠর প্রদত্ত বংশ তালিকাকে অনুসরণ করায় অথবা রামায়ণে উল্লেখ না থাকার দরুণ অথবা রামায়ণে আছে, কিন্তু বসিষ্ঠ প্রদত্ত বংশ তালিকার সঙ্গে গরমিল। রামায়ণে রামের বিশেষণ হিসাবে এই বংশতালিকার তিনজন মাত্র প্রাধান্য পেয়েছে, ককুৎস্থ, রঘু এবং দশরথ। ককুৎস্থ শব্দটি মেঘের দ্যোতক। রঘু শব্দে গমনকারী; মেঘ গমন করে, বারিবিন্দু মেঘ হতে পৃথিবীতে আগমন করে। দশরথ শব্দে ঋতুচক্র, যা মেঘের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করে।
সুতরাং ইক্ষ্বাকু বংশ তালিকায় সৃষ্টি-রহস্য বিবৃত হলেও রামের মেঘস্বরূপ প্রকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ নাম তথা পর্যায়গুলোকে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে; উপরন্তু ঐ সকল শব্দের অর্থ ধরা যায় সূর্য। রামায়ণ, বিশেষ করে কাহিনীতে বিশ্বামিত্ৰ যতক্ষণ জড়িয়ে আছেন মূলতঃ তখন ক্ষত্রায়ণ বা কৃষিবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার সম্পর্ক ঘনিষ্টতম, সুতরাং মৃত্তিকার উৎস জানা প্রয়োজন ছিল। শুধু মৃত্তিক নয়; জলের উৎপত্তি, আবহমণ্ডল সৃষ্টি, পৃথিবীর বার্ষিক ও আহিক গতির সুনিদিষ্ট আবর্তন, পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌরশক্তি ছড়িয়ে পড়ার সামঞ্জস্য, অন্তরক্ষমণ্ডলের (বা সৌরশক্তির) সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং উদ্ভিদজগতের আবির্ভাব এগুলোও জানতে হবে। ইক্ষ্বাকু বংশে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের শুধু মাত্র ইংগিত রয়েছে। সে কারণে এই গুলির বিস্তৃত আলোচনার জন্য অন্য কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে রামায়ণে এবং সেগুলিকে নিদিষ্ট করে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।
ইক্ষ্বাকু বংশে সৃষ্টির শুরু হতে আবৃত-বীজ উদ্ভিদের আবির্ভাব পর্যন্ত বলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে প্রাণকোষ হতে আরেকটি ধারায় প্রাণীজগতের আবির্ভাব ঘটেছে সে কথার কোন উল্লেখ নাই। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার দরূণ এবং উদ্ভিদজগৎ পর্যন্ত বংশতালিকা শেষ হওয়ার কারণেই দাবী করা চলে ‘রামায়ণ’ মূখ্যতঃ ক্ষত্রবিজ্ঞান।
একথা মেনে নিলেও কোনক্রমেই বলা যায় না যে রামায়ণ ইতিহাস নয়।
হাজার হাজার বছর আগে তৎকালীন ধ্যানধারণার ভিত্তিতে যিনি
ক্ষত্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি এত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন, তিনি শুধু কুশলী ভাষাবিদ বা পালাকার নন, অত্যন্ত ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কবে এবং কোথায় প্রথম শস্যজাত তৃণের সন্ধান পেয়ে মুখের গ্রাস সহজলভ্য করার জন্য ‘রামায়ণ’ আয়ত্ব করেছিলেন—এই তথ্য খুঁজে দেখার দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণের।