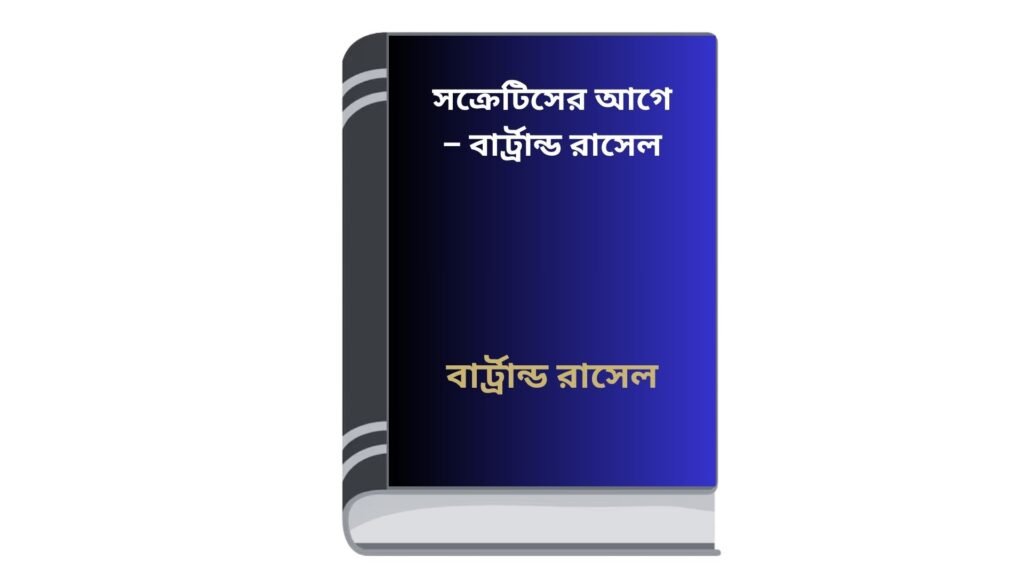০১. গ্রিক সভ্যতার অভ্যুদয়
সক্রেটিসের আগে – বার্ট্রান্ড রাসেল
১. গ্রিক সভ্যতার অভ্যুদয়
পুরো ইতিহাসে গ্রিক সভ্যতার আকস্মিক অভ্যুদয়ের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার মতো কঠিন বিষয় আর নেই। সভ্যতা গঠনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার অধিকাংশই ইতোমধ্যে মিসর ও মেসোপটেমিয়ায় বিদ্যমান ছিল হাজার বছর ধরে এবং সেখান থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু উপাদানের অভাব তত দিন পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল যত দিন গ্রিকদের কাছ থেকে তা পাওয়া বাকি ছিল। শিল্প ও সাহিত্যে গ্রিকদের অর্জন সম্পর্কে সবাই অবগত, কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে তারা যা করেছে তা বেশ ব্যতিক্রমী। গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শন তাদেরই আবিষ্কার। নিছক ঘটনাপঞ্জির বদলে ইতিহাস রচনা করে তারাই প্রথম। উত্তরাধিকার-সূত্রে চলে আসা গোঁড়ামির বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে তারা স্বাধীনভাবে বিশ্বজগতের প্রকৃতি ও জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করত। গ্রিসে যা কিছু ঘটেছে তা এতই বিস্ময়কর যে খুব সাম্প্রতিককাল আগেও গ্রিক মনীষা সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে গিয়ে লোকজনকে বিমূঢ় আর হতবুদ্ধি হতে হয়েছে। কিন্তু গ্রিসের ঘটনাবলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব, আর তা করার কাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশ উপযোগীও বটে।
থেলিসকে দিয়ে দর্শনের শুরু। একটি ঘটনা থেকে সৌভাগ্যক্রমে থেলিসের সময়কাল নির্দেশ করা যায়। সেটি হচ্ছে, তিনি একটি সূর্য/চন্দ্রগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, জ্যোতির্বিদদের মতে তা ঘটেছিল ৫৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাহলে, দর্শন ও বিজ্ঞান-যা শুরুতে পরস্পর থেকে পৃথক ছিল না-তার সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে। কিন্তু সে সময়ের আগে গ্রিসে ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে কী ঘটেছিল? এই প্রশ্নের যেকোনো উত্তর আংশিকভাবে অনুমাননির্ভর হতে বাধ্য। তবে সুখের কথা, বর্তমান শতাব্দীতে প্রত্নতত্ত্ব থেকে আমাদের অনেক বেশি জ্ঞান লাভ হয়েছে, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল না।
খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ সালের দিকে মিসরে লেখার কৌশল আবিষ্কৃত হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে মেসোপটেমিয়াতেও তা ঘটে। প্রত্যেক দেশেই লেখা শুরু হয় কোনো লক্ষ্যবস্তুর ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে। ছবিগুগলো দ্রুত পরিচিত ও রীতিসিদ্ধ হয়ে ওঠে এবং একটি সময়ে শব্দ বোঝাতে আইডিওগ্রাম ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে ওঠে, যেটা চীন দেশে এখনো প্রচলিত আছে। হাজার হাজার বছরে এই কষ্টসাধ্য পদ্ধতিটি উন্নীত হয় বর্ণমালার ব্যবহারে লেখার পদ্ধতিতে।
মিসর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাথমিক উন্নতি সাধিত হয় নীল, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর বদৌলতে। নদীগুলোর কারণে সেখানে কৃষিকাজ ছিল খুব সহজ ও উৎপাদনশীল। স্পেনীয়, মেক্সিকো এবং পেরুতে যা দেখতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রাচীন মিসরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে। ঈশ্বরসুলভ একজন রাজা থাকত, তার ক্ষমতা হতো একচ্ছত্র ও অসীম। মিসরে সেই ছিল সব ভূমির মালিক। বহু-ঈশ্বরবাদী একটি ধর্ম ছিল। সে ধর্মে ছিল একজন সর্বোচ্চ দেবতা অর্থাৎ সর্বেশ্বর। সর্বেশ্বরের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক হতো বেশ ঘনিষ্ঠ। একটি সামরিক আর একটি পুরোহিত সম্প্রদায় থাকত। রাজা যদি দুর্বল হতো বা কোনো কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ত, তাহলে পুরোহিত সম্প্রদায় প্রাইই রাজক্ষমতা দখল করে নিত। যারা ভূমি চাষ করত তারা ছিল রাজা, অভিজাত সম্প্রদায় বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের অধীনস্ত দাস।
মিসরীয় ধর্মতত্ত্ব ও ব্যাবিলনীয় ধর্মতত্ত্বের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। মিসরীয়দের মধ্যে মৃত্যুচিন্তাই ছিল প্রধান ও প্রকট। তারা বিশ্বাস করত, মৃত ব্যক্তির আত্মা পাতালপুরীতে নেমে যায়, সেখানে ওসিরিস তাদের ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করে। তারা মনে করত আত্মা শেষ পর্যন্ত আবার দেহের মধ্যে ফিরে আসে। এই বিশ্বাস থেকে তারা মৃতদেহকে নষ্ট না করে মমি বানিয়ে সুন্দর সুন্দর কবরের মধ্যে রেখে দিত। বিভিন্ন রাজার উদ্যোগে অনেক পিরামিড তৈরি হয় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষ ও তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুর দিকে। ওই সময়ের পর থেকে মিসরীয় সভ্যতা ক্রমশই গাধা হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ভবিষ্যৎ প্রগতিকে অসম্ভব করে তোলে। খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ সালে হিকসোস নামক সেমিটীয়রা মিসর অধিকার করে নেয়। তারা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে মিসর শাসন করে। মিসরে তারা কোনো স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়নি, কিন্তু সেখানে তাদের উপস্থিতি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে মিসরীয় সভ্যতার প্রসারে নিশ্চয়ই সহায়ক হয়ে থাকবে।
মিসরের চেয়ে ব্যাবিলনিয়া ছিল অধিকতর সামরিকসুলভ। প্রথম দিকে সেখানকার শাসকরা সেমিটীয় ছিল না, ছিল সুমেরীয়। সুমেরীয়দের আদি পরিচয় অজানা। তারা লেখার কীলকাকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। বিজয়ী সেমিটীয়রা সেটা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। একটি সময় ছিল যখন অনেক স্বাধীন নগরী ছিল, আর তারা সব সময় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। কিন্তু একটি সময় আসে যখন ব্যাবিলন হয়ে ওঠে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য নগরীর দেবতারা হয়ে পড়ে ব্যাবিলনের দেবতা মারডকের অধীন। মারডক এমন একটি অবস্থান অর্জন করে যা পরবর্তীকালে গ্রিক দেবমণ্ডলীতে জিউসের অবস্থানের মতো। একই ধরনের ব্যাপার ঘটে মিসরেও, তবে তা আরো বেশ কিছু সময় আগে। অন্যান্য প্রাচীন ধর্মের মতো মিসর এবং ব্যাবিলনিয়ার ধর্মগুলোও ছিল মূলত উর্বরতা পূজা।
পৃথিবী ছিল স্ত্রী, সূর্য পুরুষ। ষাঁড় গরুকে সাধারণত পুরুষ উর্বতার মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করা হতো; সর্বত্রই ষাঁড়-দেবতার দেখা পাওয়া যেত। ব্যাবিলনে স্ত্রী দেবতাদের মধ্যে মৃত্তিকা দেবী ইশতারের স্থান ও মর্যাদা ছিল সবার উপরে। পশ্চিম এশিয়াজুড়ে এই মহামাতার পূজা করা হত বিভিন্ন নামে। গ্রিক ঔপনিবেশিক শাসকরা এশিয়া মাইনরে যখন ইশতারের মন্দিরগুলো দেখতে পায় তখন তারা তার নাম দেয় আরটেমিস এবং তারা সেখানকার বিদ্যমান ধর্ম গ্রহণ করে। ডায়ানা অব এফেসিয়ানস-এর আদি উৎস ছিল এটাই। খ্রিস্ট ধর্ম তাকে রূপান্তরিত করে কুমারী মেরিতে। এফেসাসে একটি পরিষদ ছিল যারা আমাদের লেডির (যিশুমাতা মেরিকে বোঝানো হচ্ছে) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঈশ্বরমাতা অভিধানটিকে বৈধতা দান করে। যেখানে কোনো সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ধর্ম খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের আদিরূপ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সেখানে দেবতা বা দেবী রাষ্ট্রের সহযোগী হয়ে উঠেছে এবং তারা যে কেবল প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করত তা-ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা বিজয় নিশ্চিত করত। একটি ধনী পুরাহিত সম্প্রদায় নীতি-আচার ও ধর্মকে বিশদভাবে প্রণয়ন করে সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সেগুলোকে একটি দেবতামণ্ডলীর সঙ্গে মিলিয়ে নিত।
রাজ্যশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার মধ্য দিয়ে দেবতারা নৈতিকতার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হতো। বিধানদাতারা বলত, তারা তাদের বিধানগুলো পেয়েছে দেবতার কাছ থেকে। তাই তারা দাবি করত, সাম্রাজ্যের আইন বা বিধান হচ্ছে ঐশ্বরিক, পবিত্র জিনিস। তাই সে-আইন ভঙ্গ করা পাপ। আজ পর্যন্ত জানা দণ্ডবিধিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি (খ্রি.পূ. ২০৬৭-২০২৫)-এর দণ্ডবিধি। রাজা হাম্মুরাবি দাবি করতেন দেবতা মারডক তাকে ওই দণ্ডবিধিটি দান করেছিল। প্রাচীনকালজুড়ে ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে।
মিসরীয় ধর্মে পরকালের চিন্তা প্রধান। কিন্তু ব্যাবিলনিয়ার পরকাল নয়, ইহকালের সুখ-সমৃদ্ধির কথাই বেশি ভাবা হতো। জাদু, তন্ত্রমন্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে বেশি উন্নত ছিল ব্যাবিলনিয়াতে এবং প্রধানত ব্যাবিলনের মাধ্যমেই এই জিনিসগুলো পরবর্তী প্রাচীন যুগে প্রাধান্য লাভ করেছিল। ব্যাবিলন থেকে কিছু জিনিস এসেছে যেগুলো বিজ্ঞানের অন্তর্গত। যেমন-দিন-রাত্রিকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করা, বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করা ব্যাবিলনেই আবিষ্কৃত হয়। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের বেলায় তারা একটি চক্র আবিষ্কার করে, যার ভিত্তিতে নিশ্চয়তার সঙ্গে চন্দ্রগ্রহণের পূর্বাভাস দেওয়া যেত এবং সূর্যগ্রহণের সম্ভাব্যতা নির্দেশ করা যেত। দেখা যায়, পরবর্তীকালে থেলিস এই ব্যাবিলনীয় জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন।
মিসর ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতাগুলো ছিল কৃষিভিত্তিক এবং তার চারপাশের জাতিগুলোর সভ্যতা ছিল মূলত পশুপালনভিত্তিক। বাণিজ্য-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়, প্রথমে বাণিজ্য ছিল পুরোপুরি সমুদ্রভিত্তিক। খ্রিস্টপূর্ব প্রায়। ১০০০ সাল পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি। যেসব জাতির নিজ নিজ অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধাতু ছিল না তারা তা সংগ্রহ করত হয় বাণিজ্য, নয় দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে। দস্যুবৃত্তি ছিল একটি সাময়িক কূটকৌশল। যেসব স্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল সেখানে বাণিজ্য অধিকতর লাভজনক হয়ে ওঠে। বাণিজ্যক্ষেত্রে ক্রিটি দ্বীপ ছিল অগ্রপথিক। খ্রি.পূ. ২৫০০ থেকে খ্রি.পূ. ১৪০০ সাল পর্যন্ত এগারো শতাব্দী ধরে ক্রিটি দ্বীপে এক উন্নত শিল্পসভ্যতা ছিল, ইতিহাসে তা মিনোয়ান সভ্যতা (Minoan Civilization) নামে খ্যাত। ক্রিটীয় শিল্প-সংস্কৃতির যা কিছু আমাদের কাল অবধি টিকে রয়েছে তার নিদর্শনগুলো থেকে তাদের আনন্দোচ্ছল, এমনকি বেশ বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপনের ইঙ্গিত মেলে, যা মিসরীয় মন্দিরগুলোর ভয়গম্ভীর চেহারা থেকে খুবই আলাদা।
স্যার আর্থার ইভান্স ও অন্যদের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের আগ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা ছিল না। এটি ছিল একটি সমুদ্র-উপকূলীয় সভ্যতা। হিসোসদের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত এই সভ্যতার সঙ্গে মিসরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মিসরীয় চিত্রাবলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মিসর ও ক্রিটি দ্বীপের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল, ক্রিটীয় নাবিকদের মাধ্যমে তা চলত। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের দিকে সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল। মনে হয় ধর্মের দিক থেকে ক্রিটির সাদৃশ্য ছিল সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের সঙ্গে, আর শিল্পকলার দিক থেকে মিসরের সঙ্গে, যদিও ক্রিটির শিল্পকলা ছিল খুব মৌলিক ধরনের, তাতে চমৎকার জীবনবাদিতা ছিল। ক্রিটির সভ্যতার কেন্দ্রে ছিল তথাকথিত মিনোসের প্রাসাদ বা Palace of Minos। তার অবস্থান ছিল নসস (Knosos) নামক স্থানে। ক্রিটির প্রাসাদগুলো ছিল খুবই মনোমুগ্ধকর। সম্ভবত খ্রি.পূ. ১৪০০ শতাব্দীতে গ্রিক আগ্রাসীদের হাতে সেগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ক্রিটির ইতিহাসের কালপঞ্জি পাওয়া যায় মিসরে আবিষ্কৃত ক্রিটির জিনিসপত্র থেকে। এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আগাগোড়াই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর ওপর নির্ভরশীল।
ক্রিটির অধিবাসীরা একজন অথবা সম্ভবত কয়েকজন দেবীর পূজা করত। দেবীদের মধ্যে যিনি ছিলেন সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে তাকে বলা হতো প্রাণিকুলের মালকিন। তিনি ছিলেন সম্ভবত একজন শিকারি মহিলা এবং তিনিই সম্ভবত ধ্রুপদী আরটেমিস দেবীর উৎস। দৃশ্যত তিনি একজন মাতাও ছিলেন। প্রাণিকুলের মালিকরা ছাড়া যে একমাত্র পুরুষ দেবতা ছিলেন, তিনি এই দেবীর যুবক পুত্র। মিসরীয়দের মতো ক্রিটির অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসেও পরজীবন ছিল এমন প্রমাণ খেয়াল করা যায়। মিসরীয়দের মতো তারাও বিশ্বাস করত যে পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। তবে সামগ্রিকভাবে তাদের শিল্পকলার নিদর্শনগুলো থেকে মনে হয় তারা মোটের ওপর হাসি-খুশি, প্রাণোচ্ছল মানুষ ছিল। বিষণ্ণ পরকালীন চিন্তার ছাপ তাদের মধ্যে খুব একটি ছিল না। ক্রিটি দ্বীপে ষাঁড়ের লড়াই বেশ জনপ্রিয় ছিল। ষাঁড়-লড়াইয়ে নারী ও পুরুষ লড়য়ারা সমান রকম দৈহিক পারদর্শিতা দেখাত।
স্যার আর্থার ইভান্স মনে করেন, ক্রিটিতে ষাঁড়ের লড়াই ছিল একধরনের ধর্মীয় উৎসব, যারা এ লড়াইয়ে অংশ নিত সমাজে তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো হতো। তবে স্যার আর্থার ইভান্সের এই মত সর্বজনস্বীকৃত হয়নি। আমাদের কাল অবধি যেসব চিত্রকলা টিকে রয়েছে সেগুলো গতি আর বাস্তবতায় পরিপূর্ণ। ক্রিটির অধিবাসীদের একটি রৈখিক হস্তলিপি ছিল, কিন্তু তার অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নিজেদের মধ্যে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত, তাদের নগরগুলো প্রাচীরবেষ্টিত ছিল না। এটা নিঃসন্দেহে এ কারণে যে তাদের ভূখণ্ড ছিল সমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত।
ধ্বংসের আগে মিনোয়ান সংস্কৃতি ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের প্রসার লাভ করে। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপে সে সংস্কৃতি সেখানে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে এই সভ্যতা মাইসেনিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। এটা জানা যায় রাজা-বাদশাদের সমাধি আর পাহাড়-চূড়ায় অবস্থিত দুর্গগুলোর নিদর্শন থেকে, যাতে যুদ্ধের ভয় বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে, যা কিনা ক্রিটি দ্বীপে ছিল না। সমাধি এবং দুর্গগুলো উভয়ই ধ্রুপদী গ্রিসের মানসে ছাপ ফেলেছে। এর আগেকার শিল্পকলার নিদর্শনগুলো-যেগুলো মিনোয়ান প্রাসাদগুলোতে পাওয়া যায়-হয় মূলত ক্রিটির কর্মনৈপুণ্যের লক্ষণ বহন করে, নয়তো সেগুলো ক্রিটি দ্বীপের লোকদেরই কর্মকুশলতার নিদর্শন। আর কাহিনি-উপকথার মধ্য দিয়ে মাইসেনীয় সভ্যতাকে দেখলে তাই পাওয়া যায়, যা আমরা হোমারের মারফতে পাই।
মাইসেনীয়দের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানা যায় না। তারাই কি সেই সভ্যতার ধারক ছিল যা ক্রিটির অধিবাসীরা অধিকার করে নিয়েছিল? তারা কি গ্রিক ভাষায় কথা বলত? অথবা তারা কি আরো পূর্ববর্তী প্রাচীন কোনো স্থানীয় জাতি ছিল? এইসব প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। তবে এমন প্রমাণ মিলেছে যা এ ধরনের সম্ভাব্য উত্তর সরবরাহ করে যে, তারা সম্ভবত এক বিজয়ী জাতি ছিল যারা গ্রিক ভাষায় কথা বলত এবং ওই প্রমাণ থেকে অন্ততপক্ষে এমনটা মনে করা যায় যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত শ্রেণিগুলো ছিল উত্তর থেকে আগত সোনালি চুলের আগ্রাসীর দল, যারা তাদের সঙ্গে করে গ্রিক ভাষা নিয়ে এসেছিল। গ্রিকরা গ্রিস দেশে এসেছিল পরপর তিনটি ধারায়। প্রথমে এসেছিল আয়োনিয়ান (lonians) নৃগোষ্ঠী, তারপর আকিয়ান (Achaeans) এবং সবশেষে ডরিয়ান (Dorian) নৃগোষ্ঠী। আয়োনীয়রা যদিও ছিল বিজয়ী আগ্রাসনকারী, তবু তারা বেশ ভালোভাবে ক্রিটির সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল, যেমনটা পরবর্তীকালে রোমানরা গ্রহণ করেছিল গ্রিসের সভ্যতাকে। কিন্তু আয়োনীয়রা বাধাগ্রস্ত হয়, তাদের অধিকাংশকে উৎখাত করে পরবর্তী আগ্রাসী আকিয়ানরা। বোঘাজ-কুই নামক স্থানে প্রাপ্ত হিটাইট ফলক থেকে জানা গেছে, খ্রিস্টপূর্ব ১৮ শতকে আকিয়ানদের এক বিশাল সংগঠিত সাম্রাজ্য ছিল। আয়োনীয়রা, অর্থাৎ ডরিয়ানরা বস্তুত সেটাকে ধ্বংসই করে ফেলে। যেহেতু পূর্ববর্তী দখলদাররা মিনোয়ান সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল সে জন্য ডরিয়ানরা তাদের পূর্বসূরিদের মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্মকে পরিত্যাগ করেনি, তারা তা সংরক্ষণ করেছিল। মাইসেনীয় ধর্ম টিকে ছিল বিশেষত নিম্নশ্রেণির লোকদের মধ্যে এবং ধ্রুপদী গ্রিসের ধর্ম ছিল মূলত দুটোর মিশ্রণ। আসলে ধ্রুপদী দেবীদের অনেকেরই উৎস ছিল মাইসেনীয়।
যদিও উপরের বিচারকে সম্ভবপর বলেই মনে হয়, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা জানি না, মাইসেনীয়রা আসলেই গ্রিক ছিল কি না। আমরা যা জানি তা হলো, তাদের সভ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে। যখন তাদের সভ্যতার পরিসমাপ্তি ঘটে তখন ব্রোঞ্জের জায়গা দখল করে নিয়েছে লোহা এবং আরো জানি যে, কিছুকালের জন্য সমুদ্রের আধিপত্য চলে গিয়েছিল ফিনিসীয়দের হাতে। মাইসেনীয় যুগের শেষের দিকে এবং এ যুগ শেষ হবার পর-উভয় কালে দখলদারদের কিছু অংশ সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং কৃষিজীবী হয়ে ওঠে। আর তাদের কিছু অংশ আরো অগ্রসর হয়ে প্রথমে এশিয়া মাইনরের দ্বীপগুলোতে, তারপর সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি পৌঁছে। সেখানে তারা নগর পত্তন করে এবং সমুদ্র-উপকূলীয় বাণিজ্যকে জীবিকা হিসেবে নেয়। এসব উপকূলীয় নগরীতেই গ্রিকরা তাদের সভ্যতার জন্য নতুন নতুন গুণগত অবদান রাখে। এথেন্সের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় পরবর্তী সময়ে, এ ক্ষেত্রে এথেন্স নৌশক্তির সহযোগিতা লাভ করে।
গ্রিসের মূল ভূখণ্ড পাহাড়ি এবং এর ব্যাপক অঞ্চল অনুর্বর। অবশ্য অনেক উপত্যকা ছিল যেখান থেকে সহজেই সাগরে পৌঁছানো যেত। কিন্তু উপত্যকাগুলো পাহাড়-পর্বত দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাতে করে স্থলপথে যোগাযোগ সহজ ছিল না। এসব উপত্যকায় ছোট ছোট জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সাধারণত সমুদ্রের কাছাকাছি কোনো নগরকে কেন্দ্র করে তারা বসবাস করত। তাদের জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। এ রকম পরিবেশে এটা খুব স্বাভাবিক ছিল যে জনগোষ্ঠীগুলো সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, তাদের নিজেদের ভূখণ্ডের সম্পদে তাদের চাহিদা আর মেটে না, তখন তাদের অনেকেই সাগরের দিকে অগ্রসর হয়। মূল ভূখণ্ডের নগরগুলো প্রায়ই এমন সব স্থানে তাদের কলোনি স্থাপন করে যেখানে উপজীবিকা ছিল মূল ভূখণ্ডের চেয়ে সহজতর। এইভাবে ইতিহাসের একেবারে শুরুর যুগে এশিয়া মাইনর, সিসিলি ও ইতালির গ্রিকরা মূল ভূখণ্ডের গ্রিকদের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল।
গ্রিসের বিভিন্ন অংশের সামাজিক ব্যবস্থাগুলো ছিল খুবই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। স্পার্টায় একটি ক্ষুদ্র অভিজাত সম্প্রদায় ছিল যারা জীবনযাপন করত অন্য জাতির দাসদের শ্রমের ওপর নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষি অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল মূলত চাষী। তারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজেদের জমি চাষাবাদ করত। কিন্তু যেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল সেসব অঞ্চলে স্বাধীন নাগরিকরা দাসদের কাজে খাঁটিয়ে ধনী হতে থাকে। পুরুষ দাসদের তারা খাটাত খনিতে আর নারী দাসদের খাটাত বস্ত্রশিল্পে। আয়োনিয়াতে এই দাসরা ছিল চারপাশের বর্বর জনগোষ্ঠী, যাদেরকে অধিকার করে নেওয়া হয় যুদ্ধে। সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাভাজন নারীদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে গ্রিক সমাজ জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ কমে যায়, অবশ্য স্পার্টায় ও লেসবস-এ ছাড়া।
গ্রিসের সব অঞ্চলের বিকাশের মধ্যে একটি বেশ সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। বিকাশ ঘটেছিল প্রথমে রাজতন্ত্র থেকে অভিজাততন্ত্রে, তারপর স্বৈরতন্ত্র আর গণতন্ত্র বদলাবদলি করে। মিসর ও ব্যাবিলনিয়ার রাজাদের মতো গ্রিসের রাজারা নিরঙ্কুশ বা অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। তাদের পরামর্শদাতা হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠদের একটি পরিষদ থাকত। রাজারা প্রচলিত নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করলে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেত না। স্বৈরতন্ত্র বলতে অবধারিতভাবে মন্দ শাসন বোঝত না, তা ছিল কেবল একজন মানুষের শাসন যার ক্ষমতার দাবি উত্তরাধিকারভিত্তিক ছিল না। গণতন্ত্র বলতে বোঝাত সব নাগরিকের শাসন, তবে দাস-দাসী ও নারীদের নাগরিক বলে গণ্য করা হতো না। মেডিসির মতো প্রথম দিকের স্বৈরশাসকরা ক্ষমতা লাভ করে ধনিক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ধনী সদস্য হিসেবে। প্রায়ই তাদের সম্পদের উৎস ছিল সোনা ও রুপার খনির মালিকানা। মুদ্রা প্রস্তুতকরণ শুরু হবার পর থেকে সোনা-রুপা আরো বেশি লাভজনক হয়ে ওঠে। মুদ্রা তৈরির শিল্প প্রথম আসে আয়োনিয়ার পার্শ্ববর্তী লিডিয়া থেকে। এই শিল্প প্রথম আবিষ্কৃত হয় ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সামান্য আগে।
বাণিজ্য আর দস্যুবৃত্তির মধ্যে শুরুতে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। গ্রিকদের কাছে বাণিজ্য বা দস্যুবৃত্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলগুলোর একটি ছিল লেখার কৌশল অর্জন। যদিও মিসর ও ব্যাবিলনিয়ায় হাজার বছর ধরে লেখার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং আয়োনিয়ার ক্রিটীয়দেরও একটি হস্তলিপি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল-যা এখন গ্রিক ভাষারই একটি ধরন বলে জানা গেছে-তবু গ্রিকরা সঠিক কোন সময় থেকে বর্ণমালা ব্যবহার করে লেখার কৌশল অর্জন করেছিল তা জানা যায়নি। বর্ণমালার সাহায্যে লেখার কৌশলটা তারা শিখেছিল ফিনিসীয়দের কাছ থেকে। সিরিয়ার অন্যান্য অধিবাসীদের মতো ফিনিসীয়দের ওপরও মিসর এবং ব্যাবিলনিয়ার প্রভাব ছিল। আয়োনিয়া, ইতালি ও সিসিলিতে গ্রিক নগরীগুলোর উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত উপকূলীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে ফিনিসীয়দেরই প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। চতুর্দশ শতকেও ইখনাতনের (Ikhnaton) চিঠিপত্র লেখার সময় সিরীয়রা ব্যাবিলনীয় কিউনিফর্মই ব্যবহার করত। কিন্তু টায়ার এর হিরাম (৯৬৯-৯৩৬ খ্রি.পূ.) ব্যবহার করত ফিনিসীয় বর্ণমালা, যার বিকাশ ঘটেছিল সম্ভবত মিসরীয় হস্তলিপি থেকেই। শুরুর দিকে মিসরীয়রা শুধু ছবির মাধ্যমে লিখত। ক্রমান্বয়ে ছবিগুলো সর্বজনীনতা লাভ করতে থাকে এবং সবার দ্বারা ব্যবহৃত হতে হতে রীতি লাভ করে এবং একেকটা ছবি একেকটা শব্দাংশ বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে (অঙ্কিত বস্তুর নামের প্রথম শব্দাংশ)। এভাবে অবশেষে একেকটা বর্ণ বা অক্ষর তৈরি হয়। অক্ষর তৈরির নিয়মটা ছিল এ রকম : A ছিল একজন Archer, যে একটি ব্যাঙ মেরেছিল। গ্রিকরা তাদের ভাষার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো করে বর্ণমালা পরিবর্তন করে নিয়েছিল। শব্দ তৈরিতে শুধু ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারের বদলে গ্রিকরা তাতে স্বরবর্ণ যোগ করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনাটি সাধন করেছিল। লেখার এই সুবিধাজনক পদ্ধতি অর্জনের ফলে গ্রিক সভ্যতা যে ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত হয়েছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।
হেলেনিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখযোগ্য ফসল ছিলেন হোমার। হোমার সম্পর্কে সবকিছুই অনুমাননির্ভর। তবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত একটি মত আছে যে, হোমার নামে কোনো একজন ব্যক্তি ছিল না, বরং এ নামে পরিচিত ছিলেন বেশ কয়েকজন কবি, আগে-পরে বিভিন্ন সময়ে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। যারা এই ধারণায় বিশ্বাসী তাদের হিসেবে ইলিয়াড এবং অডেসি রচনা সম্পূর্ণ হবার মাঝখানের সময়গত দূরত্ব দুই শত বছর। কেউ কেউ বলেন খ্রি.পূ. ৭৫০ থেকে খ্রি.পূ. ৫৫০ সাল পর্যন্ত আবার অন্য অনেকে মনে করেন, অষ্টম শতকের শেষ নাগাদ হোমার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। হোমারীয় কবিতাগুলো বর্তমান রূপে এথেন্সে এনেছিলেন পেইসিস্ট্রাটাস। পেইসিস্ট্রাটাস গ্রিসে রাজত্ব করেন ৫৬০ খ্রি.পূ. থেকে ৫২৭ খ্রি.পূ. পর্যন্ত (মাঝখানে কিছু সময় বিরতিসহ)। তার সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে এথেনীয় যুবসম্প্রদায় হোমারের রচনা মুখস্থ করত এবং তা ছিল তাদের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রিসের কিছু কিছু অংশে, বিশেষভাবে স্পার্টায়, আরো কিছুকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত হোমারের মর্যাদা একই রকম ছিল না।
পরবর্তী-মধ্যযুগের প্রণয়-প্রার্থনা ধরনের রোম্যান্সগুলোর মতো হোমারীয় কবিতাগুলোতে একটি সভ্য অভিজাত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারকে নিচ ও ইতর ভেবে উপেক্ষা করা হয়। এই কুসংস্কারগুলো এখনো জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে। অনেককাল পরে এগুলোর কিছু কিছু আবার বেরিয়ে এসেছে। নৃবিজ্ঞানের সহায়তায় অনেক বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হোমার সেকেলে ছিলেন না, ছিলেন একজন সংস্কারক বা সংশোধনকারী, প্রাচীন পুরাণগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যাদানকারী অষ্টাদশ শতকের র্যাশনালাইজারদের মতো। অলিম্পীয় দেবতারা-যারা ছিলেন হোমারের মধ্যে ধর্মের প্রতিফলন-হোমারের যুগে বা তার পরের যুগেও শুধু গ্রিকদের মধ্যেই পূজনীয় ছিলেন না। গণধর্মের মধ্যে অন্য অনেক অন্ধকার ও অসভ্য উপাদান ছিল। সেগুলো গ্রিক মনীষা দ্বারা কোণঠাসা হয়ে থাকত, কিন্তু দুর্বলতা বা আতঙ্কের মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওঁৎ পেতে থাকত। হোমার যেসব বিশ্বাসকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, অবক্ষয়ের যুগে সেগুলো টিকে ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে, ধ্রুপদী যুগ জুড়ে সেগুলো আধা বিলুপ্তির অবস্থায় ছিল। এই তথ্য অনেক বিষয়েরই ব্যাখ্যা হাজির করে, অন্যভাবে যা সঙ্গতিহীন বা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। আদি ধর্মগুলো কোথাও ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না, ছিল গোত্রীয় ব্যাপার। গোত্র বা উপজাতির মঙ্গলার্থগুলোকে এগিয়ে নেবার জন্য চিত্তাকর্ষক নানা ধরনের জাদুবিদ্যা দ্বারা কিছু বিশেষ কৃত্যানুষ্ঠান চলত। বিশেষভাবে উর্বরতা, গাছপালা, পশু ও মানুষের কল্যাণের জন্য এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হতো। দক্ষিণায়নের দিন সূর্যের শক্তি যাতে ফুরিয়ে না যায় সে জন্য সূর্যকে সাহস যোগানো হতো। বসন্ত আর ফসল কাটার ঋতুতেও যথাযথ অনুষ্ঠান করা হতো। এগুলো প্রায়ই এমন ছিল যাতে ব্যাপক সমষ্টিগত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যে উত্তেজনার মধ্যে ব্যক্তি-মানুষ তার বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্তি পায় এবং নিজেকে তার পুরো গোত্রের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে। পৃথিবীজুড়েই ধর্মীয় বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধাপে পৌঁছে পবিত্র পশু আর মানুষকে আনুষ্ঠানিকভাবে হত্যা করা বা বলি দেওয়া হতো এবং তাদের ভক্ষণ করা হতো। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই ধাপ এসেছিল বিভিন্ন সময়ে। বলি দেওয়া মানুষের মাংস ভক্ষণের চেয়ে বেশি দিন স্থায়ী ছিল নরবলির ধর্মীয় রীতি। ঐতিহাসিক যুগ শুরুর দিকেও গ্রিসে তা বিলুপ্ত হয়নি। এরূপ নির্দিষ্ট দিক বাদ দিয়ে উর্বরতা-প্রার্থনার কৃত্যানুষ্ঠানগুলো গ্রিসে ছিল একটি সাধারণ ব্যাপার। নির্দিষ্টভাবে এলিউসীয় গুহ্য ধর্মানুষ্ঠানগুলো তাদের প্রতীকধর্মিতার দিক থেকে মূলত ছিল কৃষিভিত্তিক।
স্বীকার করতেই হবে, হোমারের মধ্যে ধর্ম ব্যাপারটা খুব একটি ধার্মিকতাপূর্ণ নয়। তার রচনায় দেবতারা আগাগোড়াই মানবসুলভ। মানুষের সঙ্গে দেবতাদের পার্থক্য শুধু এই যে, দেবতারা অমর এবং অতিমানবিক নানা ক্ষমতার অধিকারী। নৈতিক দিক থেকে এ ব্যাপারে কিছুই বলার নেই। তারা যে কীভাবে এতটা সম্ভ্রম বা ভয় উদ্রেক করতে পারত তা বোঝা কঠিন। হোমারের কাব্যগুলোর কোনো কোনো অংশে-যেগুলো মনে হয় পরের দিকে রচিত-দেবতাদেরকে ভলতেরীয় অশ্রদ্ধার সঙ্গে দেখানো হয়েছে। সেই অর্থে খাঁটি ধর্মীয় অনুভূতি হোমারে পাওয়া যায় না। ধর্মীয় অনুভূতি যা তার মধ্যে খেয়াল করা যায়, তা অলিম্পিয়াসের দেবতাদের চেয়ে নিয়তি, প্রয়োজন, পরিণতি-এ রকম সব অস্পষ্ট ছায়াময় বিষয়ের সঙ্গেই বেশি সম্পর্কিত। এমনকি হোমারের রচনায় বর্ণিত জিউসও এই বিষয়গুলোর অধীন ছিলেন। পুরো গ্রিক চিন্তায় নিয়তি বা ভাগ্যের একটি বড় প্রভাব ছিল এবং এটা সম্ভবত বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর প্রতি বিশ্বাসের উৎসগুলোর অন্যতম।
হোমারের দেবতারা ছিল একটি বিজয়ী অভিজাত সম্প্রদায়ের দেবতা। যারা বস্তুত ভূমি চাষ করত। ওইসব দেবতা তাদের উর্বরতার দেবতা ছিল না। গিলবার্ট মুরে যেমনটি বলেন: অধিকাংশ জাতির দেবতারা দাবি করে যে তারা বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। অলিম্পীয় দেবতারা এ রকম দাবি করে না। তারা যা করেছে তা হলো বিশ্বকে জয় করা…আর যখন তাদের রাজ্যজয় সম্পন্ন হয়ে গেছে তখন তারা কী করে? তারা কি দেশ শাসনে আছে? তারা কি কৃষিকাজ চালাচ্ছে? তারা কি বাণিজ্য ও শিল্প করছে? মোটেই না। কেন তাদেরকে কোনো সৎ কাজ করতে হবে? তারা রাজস্ব আয়ের ওপর জীবনযাপনকেই বেশি সহজ মনে করে, আর যারা রাজস্ব পরিশোধ করে না তাদের ওপর বজ্রপাত ঘটানোই তাদের কাছে অধিকতর সহজ কাজ। তারা একেকজন বিজয়ী গোষ্ঠীপতি, একেকজন রাজকীয় বোম্বেটে। তারা যুদ্ধ করে, আনন্দোৎসব করে, আনন্দ-ফুর্তি আর পানভোজনে দিন কাটায়। তারা ক্রীড়ামোদে গা ভাসায়, সঙ্গীত রচনা করে, তারা আকণ্ঠ পান করে আর সেই খোঁড়া কর্মকারের প্রতি অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে, যে তাদের খেদমতে নিয়োজিত। নিজেদের রাজাকে ছাড়া তারা কখনো আর কাউকে ভয় পায় না। শুধু প্রেমে আর যুদ্ধক্ষেত্রে ছাড়া তারা কখনো মিথ্যা বলে না।
হোমারের মানুষ-বীরদেরও স্বভাব-আচরণ খুব একটি ভালো নয়। তাদের নেতৃস্থানীয় পরিবার হলো হাউস অব পেলোপস। কিন্তু সুখী পারিবারিক জীবনের একটি আদর্শ দাঁড় করাতে এ পরিবার সফল হয়নি।
এ বংশের এশীয় প্রতিষ্ঠাতা তানতাবোস তার কর্মজীবন শুরু করেন দেবতাদের বিরুদ্ধে এক সরাসরি আক্রমণের মধ্য দিয়ে। কেউ কেউ বলেন তিনি দেবতাদের নরমাংস খাইয়ে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার পুত্র পেলোপসের মাংস দেবতাদের খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। পেলোপস অলৌকিকভাবে প্রাণ ফিরে পেলে নিজের অকর্মটা সম্পন্ন করেন। তিনি পিসার রাজা অনৌমাওসের সঙ্গে রথচালনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন রাজার রথচালক মারটিলিসের পরোক্ষ সহায়তায়। পেলোপস মারটিলিসকে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে রথচালক মারটিলিস যদি তাকে সহায়তা করেন তাহলে তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু পেলোপস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার পর মারটিলিসকে পুরস্কার না দিয়ে বরং সাগরে নিক্ষেপ করেন। এরপর এর অভিশাপ পুরুষান্তরে বর্ষিত হয় তার পুত্র আট্রেয়াস আর থায়েস্টেসের ওপর। গ্রিক ভাষায় সে অভিশাপের নাম ate, যার অর্থ অপরাধের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। থায়েস্টেস তার ভাইয়ের স্ত্রীকে প্ররোচিত করে পরিবারের ভাগ্য চুরি করতে সক্ষম হয়। সেই ভাগ্য হলো সেই বিখ্যাত সোনালি পশমের ভেড়া। আর আট্রেয়াস সে জন্য তার ভাইয়ের নির্বাসনের ব্যবস্থা পাকাঁপোক্ত করে, তারপর তার সঙ্গে মিটমাট করার অজুহাতে ফিরিয়ে আনে এবং তার নিজেরই ছেলেমেয়েদের মাংস তাকে খাওয়ায়। তারপর এই অভিশাপের উত্তরাধিকারী হয় আট্রেয়াসের পুত্র আগামেনন। আগামেনন এক ধর্মের পাঁঠা হরিণ হত্যা করে আরটেমিসকে প্রতারিত করে, দেবীকে তুষ্ট করার জন্য নিজের কন্যা এফিজেনিয়াকে বলি দেয় ও তার নৌবহরের জন্য ট্রয়ে যাওয়ার একটি নিরাপদ রাস্তা পেয়ে যায় এবং পরিশেষে তার অবিশ্বস্ত স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রা ও তার প্রেমিক আইগিস্থসের হাতে খুন হয়। আইগিস্থস থায়েস্টেসের একজন বেঁচে যাওয়া পুত্র। আগামেননের পুত্র অরেস্টেস পরিণামে পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয় তার মা ও মায়ের প্রেমিক আইগিসকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে।
পূর্ণাঙ্গ একটি অর্জন হিসেবে হোমার ছিলেন আয়োনিয়ার ফসল, অর্থাৎ হেলেনিক এশিয়া মাইনর ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোর। হোমারের কবিতাগুলো বর্তমান রূপে স্থিতি লাভ করে খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে। গ্রিক বিজ্ঞান, দর্শন এবং গণিতও শুরু হয় ওই শতাব্দীতেই। একই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন অনেক ঘটনা ঘটছিল। কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, জরআস্তর (জরথুস্ত্র)-যদি তাদের অস্তিত্ব সত্য হয়ে থাকে-সম্ভবত এই শতাব্দীরই মানুষ ছিলেন। কেউ কেউ বলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সম্রাট সাইরুস পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, আর সে শতাব্দীর শেষের দিকে আয়োনিয়ার গ্রিক নগরীগুলো, যাদেরকে পারসিকরা একটি সীমিত স্বায়ত্তশাসনের অনুমতি দিয়েছিল, তারা একটি অসফল বিদ্রোহ করে। দারিউস সেই বিদ্রোহ দমন করেন আর সেসব গ্রিক নগরীর সেরা সেরা লোকজন নির্বাসিত হয়। এই যুগের কয়েকজন দার্শনিক ছিলেন উদ্বাস্তু। হেলেনিক জগতের তখন পর্যন্ত মুক্ত এক নগরী থেকে অন্য নগরীতে তারা ঘুরে বেড়াতেন। আর তখন পর্যন্ত যে সংস্কৃতি আয়োনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা তারা অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে দেন। যেসব জায়গায় তারা ঘুরে বেড়াতেন সেখানে সদয় আচরণ পেতেন। জেনোফেন, যিনি খ্যাতি লাভ করেন ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে, তিনি ছিলেন উদ্বাস্তু দার্শনিকদের অন্যতম। তিনি বলেন, এটা এমন একটি ব্যাপার ছিল যাকে বলতে হয় শীতকালে আগুনের পাশে উত্তম খাদ্য গ্রহণের পর মিষ্টি সুরা পান করতে করতে নরম গদিতে শুয়ে হলুদ মটর দানা চিবানো : কোন দেশ থেকে এসেছেন, কত বয়স আপনার, জনাব? যখন মিডির আবির্ভাব ঘটেছিল, তখনই বা কত বয়স ছিল আপনার…? সালামিস আর প্লটেয়ার যুদ্ধে গ্রিসের অবশিষ্ট অংশ স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এ দুই যুদ্ধের পর আয়োনিয়া কিছু সময়ের জন্য মুক্ত হয়েছিল।
অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল গ্রিস। একটি করে নগরী আর সেটিকে ঘিরে কিছু কৃষি-অঞ্চল নিয়ে রাষ্ট্রগুলো গঠিত ছিল। গ্রিক দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে সভ্যতার স্তর খুবই ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। শুধু অল্পসংখ্যক নগরীই পুরো হেলেনিক সিদ্ধিতে অবদান রাখতে পেরেছিল। স্পার্টা, যার সম্পর্কে পরে আমার অনেক কিছু বলার থাকবে, গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামরিক দিক থেকে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে নয়। করিন্থ ছিল ধনী ও সমৃদ্ধিশালী। সেটা ছিল এক বিরাট বাণিজ্যিক কেন্দ্র, কিন্তু বড় বড় ব্যক্তিত্বের মানুষ করিন্থে খুব বেশি ছিল না। তারপর ছিল খাঁটি কৃষিজীবী গ্রামীণ সম্প্রদায়, প্রবাদতুল্য আর্কেডিয়ার মতো নগরীর লোকেরা আর্কেডিয়াকে স্বপ্নসুখাচ্ছন্ন, শান্ত সমাহিত একটি স্থান বলে কল্পনা করত। কিন্তু আর্কেডিয়া আসলে ছিল প্রাচীন বর্বরতাপূর্ণ, বিভীষিকায় পরিপূর্ণ একটি জায়গা।
অধিবাসীরা হারমেস এবং পান-এর উপাসনা করত। তাদের মধ্যে উর্বরতা-পূজার অজস্র রকমফের ছিল। এসব উপাসনায় প্রায়ই একটি চৌকোনা খুঁটি দেবতার মূর্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কৃষকরা এত দরিদ্র ছিল যে তারা ষাড়ের মালিক হতে পারত না, তাই ছাগী ছিল তাদের কাছে উর্বরতার প্রতীক। যখন খাদ্যদ্রব্য খুব দুর্লভ হয়ে উঠত তখন পান-এর মূর্তিকে পেটানো হতো। (চীন দেশের কোনো কোনো প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে একই ধরনের রীতি এখনো প্রচলিত আছে।) কথিত ওয়্যার-উলফদের একটি পোত্র ছিল, যারা সম্ভবত নরবলি দিত এবং স্বজাতি মাংস ভক্ষণ করত। মনে করা হতো যে, কেউ যদি বলি-দেওয়া মানুষের মাংসের স্বাদ গ্রহণ করে তাহলে সে ওয়্যার-উলফ বনে যায়। নেকড়ে-জিউসের একটি পবিত্র গুহা ছিল; সে-গুহার ভেতরে কারোর ছায়া সৃষ্টি হতো না। আর যে সেই গুহায় প্রবেশ করত, এক বছরের মধ্যেই তার মৃত্যু হতো। ধ্রুপদী যুগেও এইসব কুসংস্কার সক্রিয়ভাবে প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, দেবতা পান-এর প্রকৃত নাম ছিল পাওন (Paon)। শব্দটির অর্থ যে খাওয়ায় বা রাখাল। পারস্য যুদ্ধের পর খ্রি.পূ. পঞ্চম শতকে এথেন্সের লোকেরা যখন পান বা পাওনের উপাসনার রীতি গ্রহণ করে নেয়, তখন তার আরেকটি উপাধি অর্জিত হয়, যা আরো বেশি পরিচিত। সেটার ইংরেজি অর্থ দাঁড়ায় All-God, বাংলায় সর্বেশ্বর।
ধর্ম শব্দটি আমরা যেভাবে বুঝি তার অনেকটাই প্রাচীন গ্রিসে ছিল বলে মনে হয়। এটা অলিম্পীয়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না, ছিল ডায়োনিসাস বা বাক্কাসের সঙ্গে। বাক্কাস বা ডায়োনিসাস সম্পর্কে আমাদের খুব স্বাভাবিক ধারণা যে, তিনি মদ এবং মাতলামির এক কুখ্যাত দেবতা। তার উপাসনা থেকে এক গভীর মরমিবাদের সৃষ্টি হয়েছে, সেই মরমিবাদ অনেক দার্শনিকের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে, এমনকি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের রূপায়ণের মধ্যেও এর একটি অংশ রয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় এটা ঘটেছে তা বেশ লক্ষণীয় এবং যিনি গ্রিক চিন্তার বিকাশ অধ্যয়ন করার ইচ্ছা রাখেন তাকে অবশ্যই তা বুঝতে হবে।
ডায়োনিসাস বা বাক্কাস ছিলেন মূলত একজন গ্রেসীয় দেবতা। থ্রেসীয়রা গ্রিকদের চেয়ে অনেক কম সভ্য ছিল, গ্রিকরা তাদেরকে বর্বর মনে করত। সব আদিম কৃষিজীবীদের মতো গ্রেসীয়দেরও উর্বরতা-পূজা করার ধর্ম ছিল এবং তাদের একজন দেবতা ছিলেন যিনি উর্বরতা যোগাতেন। তার নাম ছিল বাক্কাস। বাক্কাসের আকার মানুষের মতো ছিল, না ষাঁড়ের মতো ছিল তা কখনোই জানা যায়নি। থ্রেসীয়রা যখন বিয়ার তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করে তখন তারা মাদকতাকে স্বর্গীয় ব্যাপার মনে করত এবং বাক্কাসকে ভক্তি করত। পরে, যখন তারা আঙুরলতার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং মদপান শেখে, তখন বাক্কাসের প্রতি তারা আরো ভালো ধারণা পোষণ করতে থাকে। সাধারণভাবে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে কাজ বাক্কাস করতেন সেটার চেয়ে আঙুর উৎপাদন আর মদ-সৃষ্ট স্বর্গীয় উন্মাদনা সৃষ্টির কাজ তাদের কাছে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।
বাক্কাস-পূজা কখন থ্রেস থেকে গ্রিসে চলে আসে তা জানা যায়নি। তবে মনে হয়, সেটা ঘটেছিল ঐতিহাসিক যুগ শুরু হবার ঠিক প্রাক্কালে। গ্রিসের গোড়া ধার্মিকরা বাক্কাস-পূজার প্রতি ছিল বিরূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাক্কাস উপাসনায় অনেক বর্বর উপাদান ছিল। যেমন-বন্য পশুকে টুকরো টুকরো করে কেটে পুরোটাই কাঁচা খাওয়া হতো। বাক্কাস-পূজার মধ্যে নারীবাদের একটি কৌতূহলোদ্দীপক উপাদান ছিল। বয়স্কা মহিলারা এবং অবিবাহিত তরুণীরা বড় বড় দল বেঁধে উন্মুক্ত পাহাড়ে সারা রাত নৃত্য করত, এই নৃত্য তাদের মনে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের তীব্র অনুভূতি জাগাত। তাদের এই অনুভূতি ছিল প্রধানত আধ্যাত্মিক এবং অংশত মদপানজনিত। এই রীতি তাদের স্বামীদের অসন্তুষ্ট করত, কিন্তু তাদের স্বামীরা ধর্মের বিরোধিতা করার সাহস পেত না। ধর্মীয় উপাসনার এই রীতির সৌন্দর্য ও বর্বরতা বর্ণিত হয়েছে ইউরিপাইডিসের Bacchae শীর্ষক রচনায়।
গ্রিসে ডায়োনিসাস-পূজার সিদ্ধিতে অবাক হবার কিছু নেই। দ্রুত সভ্যতা অর্জনকারী সব সম্প্রদায়ের মতোই গ্রিকদের বা অন্তত তাদের কিছু অংশের মধ্যে আদিম-এর প্রতি একধরনের অনুরাগ গড়ে উঠেছিল। সমকালীন বা প্রচলিত নৈতিকতা দ্বারা বেঁধে-দেওয়া জীবনের চেয়ে তাদের বেশি ঝোঁক ছিল প্রবৃত্তিতাড়িত, প্রবল আবেগপ্রবণ জীবন-পদ্ধতির প্রতি। যে নারী বা যে পুরুষ অনুভূতির টানে নয়, নেহায়েত প্রচলিত আচার-ব্যবহারের দায়ে সভ্য হতে বাধ্য হয়েছে, তার কাছে যৌক্তিকতা বা বুদ্ধি-বিবেচনা বিরক্তিকর। সদগুণকে সে মনে করত একটি বোঝা, দাসত্ব। এ থেকে তার প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিই আমাদের আলোচনায় বিশেষ স্থান পাবে। তবে প্রথমে অনুভূতি ও আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু বলে নেওয়া প্রয়োজন।
অসভ্য মানুষ থেকে সভ্য মানুষকে যা পৃথক করে তা হলো মূলত পরিণামদর্শিতা বা দূরদর্শিতা, অথবা আরেকটু বিশদভাবে বললে, পূর্বচিন্তা। ভবিষ্যতের সুখ বা আনন্দের খাতিরে সে বর্তমানের কষ্ট সহ্য করতে রাজি, যদি সেই ভবিষ্যৎ-সুখ অনেক দূরবর্তীও হয়। এই অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে কৃষির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী শীতকালে খাদ্য পাবার জন্য কোনো পশু বা বর্বর মানুষ বসন্তকালে কাজ করে না। শুধু মৌমাছির মধুসগ্রহ আর কাঠবিড়ালীদের বাদাম লুকিয়ে রাখার মতো খাঁটি প্রবৃত্তিগত কাজগুলোই এর ব্যতিক্রম। এসব ক্ষেত্রে কোনো পূর্বচিন্তা কাজ করে না। মানুষের ক্ষেত্রে কেবল সে রকম কাজের প্রতিই একটি প্রত্যক্ষ প্রণোদনা থাকে যে কাজ পরবর্তী সময়ে উপকারী বা ফলদায়ী প্রমাণিত হয়। সত্যিকারের পূর্বচিন্তা কেবল তখনই উদ্রেক হয় যখন একজন মানুষ প্রবৃত্তিগত প্রণোদনা ছাড়াই একটি কিছু করে, কারণ বুদ্ধি তাকে বলে দেয় যে ভবিষ্যতে কোনো একসময়ে এই কাজের কিছু সুফল সে পাবে। শিকারে কোনো পূর্বচিন্তার প্রয়োজন হয় না, কারণ তা আনন্দদায়ক। কিন্তু ভূমিকৰ্ষণ খাটুনির কাজ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনা থেকে তা করা যায় না।
সভ্যতা প্রণোদনাকে নিয়ন্ত্রণ করে কেবল পূর্বচিন্তার দ্বারাই নয়, যে পূর্বচিন্তা একধরনের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ। আইন, সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রণোদনা। সভ্যতা প্রণোদনার নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে বর্বরতা থেকেই, তবে সেই নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্তির ভূমিকা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে, শৃঙ্খলা ও নিয়মের ভূমিকা বেড়েছে। কিছু কিছু কাজ অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং সেগুলো সম্পাদনের দায়ে শাস্তির বিধান হয়েছে। আর কিছু কিছু কাজ আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিমূলক না হলেও দুষ্টকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যারা এসব দুষ্টকর্ম করে সমাজ তাদের ভালো বলে না, প্রত্যাখ্যান করে।
সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আসে নারীদের অধীনস্ত করার রীতি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি দাস শ্রেণির উৎপত্তি ঘটে। একদিকে সম্প্রদায়ের অভীষ্টগুলো ব্যক্তির ওপর আরোপিত হওয়ায়, অন্যদিকে নিজের জীবনকে পুরো সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখার অভ্যাস অর্জন করায় সে আরো বেশি করে তার বর্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করতে থাকে। এটা বেশ পরিষ্কার যে, এই প্রক্রিয়া অনেক দূর পর্যন্ত চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একজন কঞ্জুস ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। কিন্তু সে রকম চূড়ান্ত পর্যায়ে না গিয়েও দূরদর্শিতার কারণে জীবনের অনেক শ্রেষ্ঠ জিনিস হারাতে হতে পারে। ডায়োনিসাসের উপাসক দূরদর্শিতার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে। দূরদর্শিতা মানুষের অনুভূতির যে তীব্রতা নষ্ট করে দেয়, শারীরিক বা আধ্যাত্মিক নেশাগ্রস্ততার মধ্যে তা ফিরে পাওয়া যায়। নেশাগ্রস্ত হয়ে মানুষ জগৎকে আনন্দে আর সৌন্দর্যে ভরপুররূপে দেখতে পায় এবং প্রাত্যহিক চিন্তাকুলতার কারাগার থেকে তার কল্পনা হঠাৎ মুক্তি লাভ করে। যাকে উৎসাহ বা উদ্দীপনা বলা হতো, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পূজারি বা উপাসকের ভেতরে ঈশ্বরের প্রবিষ্ট হওয়া, বাক্কাসের আচার অনুষ্ঠানগুলো সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করত। ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে পেয়ে পূজারি মনে করত সে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। মানবসভ্যতার অর্জনগুলোর মধ্যে যেগুলো শ্রেষ্ঠ তার অধিকাংশের সঙ্গে নেশাগ্রস্ততার কিছু উপাদান জড়িত (আমি বলতে চাই, মানসিক নেশাগ্রস্ততা, অ্যালকোহল-সৃষ্ট নেশাগ্রস্ততা নয়), আবেগ দ্বারা নেশাগ্রস্ততাকে খানিকটা হটিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে। বাক্কাসীয় উপাদান ছাড়া জীবন হয়ে পড়ত নিরানন্দ; আবার এইসব উপাদানপূর্ণ জীবন বিপজ্জনক। দূরদর্শিতা বনাম আবেগ-এমন একটি দ্বন্দ্ব যা ইতিহাসজুড়ে চলে আসছে। তবে এটা এমন কোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নয়, যাতে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে।
চিন্তার জগতে সংযমী বা মিতাচারী সভ্যতা মোটামুটি বিজ্ঞানের সমার্থক। কিন্তু নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মানুষকে পরিতুষ্ট করতে পারে না। মানুষের আবেগ, শিল্পকলা এবং ধর্মও প্রয়োজন। বিজ্ঞান জ্ঞানের সীমারেখা টেনে দিতে পারে, কিন্তু কল্পনার সীমা টানা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়। পরবর্তীকালের দার্শনিকদের কারো কারো মতো গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন প্রাথমিকভাবে বৈজ্ঞানিক, কেউ কেউ প্রাথমিকভাবে ধার্মিক। পরবর্তীরা, অর্থাৎ ধর্মপ্রবণ দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাক্কাসের ধর্মের কাছে বেশ ঋণী। এটা বিশেষভাবে প্লেটোর ক্ষেত্রে এবং তার মাধ্যমে সংঘটিত পরবর্তী বিকাশগুলো-যা শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে সঞ্চারিত হয়েছে-সেসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
ডায়োনিসাস-পূজার আদি রূপটি ছিল বর্বর এবং নানাভাবে বিকর্ষক ও বীভৎস। সেই আদি রূপ যে দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছিল তা নয়, বরং অর্ফিয়ুস কর্তৃক আরোপিত এর আধ্যাত্মিক রূপটির দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেটা ছিল আত্মনিরোধী, কৃচ্ছ্ববাদী এবং শারীরিক নেশাগ্রস্ততার পরিবর্তে মানসিক নেশাগ্রস্ততা। অর্ফিয়ুস একটি অনুজ্জ্বল কিন্তু আগ্রহব্যঞ্জক চরিত্র। কেউ কেউ মনে করেন তিনি একজন বাস্তব মানুষ ছিলেন, আবার কেউ কেউ মনে করেন তিনি ছিলেন একজন দেবতা, বা একজন কাল্পনিক বীর। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, তিনিও বাক্কাসের মতো থ্রেস থেকে আগত। কিন্তু তিনি (বা তার নামের সঙ্গে জড়িত ধারাটি) ক্রিটি দ্বীপের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অর্ফিক মতবাদগুলোর মধ্যে অনেক বিষয় আছে, যেগুলোর প্রাথমিক উৎস মিসরীয় বলে মনে হয় এবং এটা নিশ্চিত যে, মিসর গ্রিসের ওপর প্রভাব ফেলেছিল প্রধানত ক্রিটির মাধ্যমে। বলা হয়ে থাকে অর্ফিয়ুস ছিলেন একজন সংস্কারক, যাকে টুকরো টুকরো করে কেটেছিল বাক্কাসের গোড়া উপাসক মায়েনাড়রা। পৌরাণিক উপকথার প্রাচীন ভাষ্যগুলোতে সঙ্গীতের প্রতি অর্ফিয়ুসের আসক্তির কথা ততটা সুবিদিত ছিল না, যতটা হয়েছে পরবর্তীকালে। প্রাথমিকভাবে তিনি ছিলেন একজন পুরোহিত ও দার্শনিক। অর্ফিয়ুসের শিক্ষা (যদি আসলেই এ কথা সত্য হয় যে বাস্তবে তার। অস্তিত্ব ছিল) যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, অর্ফিয়ুসবাদীদের শিক্ষা কিন্তু বেশ পরিচিত। তারা ছিলেন আত্মার দেহান্তরে বিশ্বাসী। তারা এই শিক্ষা দিতেন যে, পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে মৃত্যুর পর তার আত্মার অনাদি আনন্দ লাভ করতে পারে অথবা চিরন্তন বা সাময়িক নির্যাতনের শিকার হতে পারে। তাদের লক্ষ্য ছিল বিশুদ্ধ বা পবিত্র হওয়া। সেটা তারা করার চেষ্টা করতেন অংশত শুদ্ধিকরণ কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে, অংশত দূষণীয় কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। তাদের মধ্যে যারা ছিলেন সবচেয়ে কট্টর তারা কোনো প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করতেন না। তবে ধর্মীয় আচার ও সংস্কারবশত তারা তা খেতেন শুধু কিছু কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে। তারা মনে করতেন মানুষের কিছু অংশ পার্থিব আর কিছু অংশ স্বর্গীয়। শুদ্ধ জীবনযাপনের ফলে স্বর্গীয় অংশটি বৃদ্ধি পায় আর পার্থিব অংশটি লোপ পায়। এভাবে শুদ্ধ জীবনযাপন করতে করতে পরিশেষে একজন মানুষ বাক্কাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় এবং তখন তাকে একজন বাক্কাস বলে অভিহিত করা হয়। একটি বিশদ ধর্মতত্ত্ব ছিল, যা অনুসারে বাক্কাসের জন্ম হয়েছিল দুইবার। একবার তার মাতা সিমিলি থেকে, আরেকবার তার পিতা জিউসের ঊরু থেকে।
ডায়োনিসাস-পুরাণের অনেক রকম ভাষ্য আছে। সেগুলোর একটিতে বলা হয়, ডায়োনিসাস জিউস এবং পারসিফোনির পুত্র। যখন তিনি নিতান্ত বালক, তখন টাইটানরা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং শুধু তার হৃৎপিণ্ড ছাড়া সব মাংস খেয়ে ফেলেছিল। কেউ কেউ বলে সেই হৃৎপিণ্ড জিউস দিয়েছিলেন সিমিলিকে। অন্যরা বলে জিউস নিজেই তা গলাধঃকরণ করেন। এ দুয়ের যেটাই ঘটে থাকুক না কেন, তা থেকেই ডায়োনিসাসের দ্বিতীয় জন্ম ঘটে। মনে করা হয়, বাক্কাসের উপাসকরা বন্য পশুদের টুকরো টুকরো করে কেটে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করত টাইটানদের হাতে ডায়োনিসাসের টুকরো টুকরো হবার সেই ঘটনা উদযাপনের জন্য। এক অর্থে সেই বন্য পশুকে দেবতার প্রতিমূর্তি মনে করা হতো। টাইটানদের জন্ম পৃথিবীতে, কিন্তু দেবতাকে ভক্ষণ করার ফলে তাদের মধ্যে স্বর্গীয় দ্যুতি আসে। সে জন্যই মনে করা হতো মানুষ অংশত পার্থিব, অংশত স্বর্গীয় এবং বাক্কাসীয় কৃত্যানুষ্ঠানগুলোতে মানুষকে প্রায়-সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় করে তোলার চেষ্টা চলত।
একজন অর্ফিক পুরোহিতের মুখ দিয়ে ইউরিপাইডিস একটি স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন, যা এ ব্যাপারে ইঙ্গিতবহ–
টায়ার বংশোদ্ভূত প্রভু ইউরোপার,
জিউস-জাত, পদতলে তোমার।
ক্রিটির শত নগরী,
সেই নিস্প্রভ সমাধি থেকে খুঁজছি তোমাকে।
সমাধির ছাদ বাঁকানো আর খোদাই-করা কড়ির,
শ্যালিব-ইস্পাত আর বুনো ষাঁড়ের শোণিতে
সাইপ্রেস কাঠের নিখুঁত জোড়ে সুদৃঢ়। এক বিশুদ্ধ স্রোতধারায়
আমার দিন গেল। সেবক আমি
ঈদীয় জোভের শাগরেদ,
যেখানে মধ্যরাতে বিহার করে জাগ্রেউস, বিহার করি আমি
আমি সয়েছি তার বজ্রচিৎকার;
পূর্ণ করে লোহিত রক্তাক্ত ভোজ
ধারণ করে মহামাতার পর্বতাগ্নি
আমি হয়েছি মুক্ত, অভিধা পেয়েছি
একজন বাক্কাস বর্মাচ্ছাদিত পুরোহিতদের।
শুভ্র বিশুদ্ধ পোশাকে নিজেকে করেছি অমল
মনুষ্যজন্মের কালিমা আর শবাধারের কাদা থেকে,
আর চিরতরে নির্বাসিত করেছি আমার ওষ্ঠ থেকে
সব মাংসের স্পর্শ, যেখানে জীবন ছিল।
বিভিন্ন সমাধিতে কিছু অফিক ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। পরজীবনে পথ খুঁজে পেতে হলে কী করতে হবে, নিজেকে পরিত্রাণের উপযুক্ত প্রমাণ করার জন্য কী বলতে হবে। ইত্যাদি সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে নির্দেশনা লেখা রয়েছে সেসব ফলকে। ফলকগুলো ভাঙা এবং অসম্পূর্ণ, সেগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি সম্পূর্ণ (প্যাটেলিয়া ফলক), তাতে এ রকম কথাবার্তা লেখা রয়েছে–
হাডেস ভবনের বাম পাশে তুমি একটি ঝরনা-কূপ দেখতে পাবে,
তার পার্শ্বে এক শ্বেত সাইপ্রাসবৃক্ষ দণ্ডায়মান।
ঝরনা-কূপটির নিকটবর্তী হয়ো না।
আরো একটি ঝরনা-কূপ দেখতে পাবে স্মৃতি হ্রদের পাশে,
সেখান থেকে শীতল পানি নির্গত হচ্ছে, তার সম্মুখে প্রহরীরা আছে।
তুমি বলো : মর্ত্য ও তারকাময় স্বর্গের এক সন্তান আমি;
কিন্তু আমার বংশ (শুধুই) স্বর্গের। তোমরা নিজেরাই তা জানো।
আর দেখো, তৃষ্ণায় আমি কাতর ও মৃত্যুপথযাত্রী। শিগগির আমাকে স্মৃতি-হ্রদ থেকে প্রবাহিত শীতল পানি এনে দাও।
তখন তারা নিজেরাই তোমাকে সেই পবিত্র ঝরনা-কূপ থেকে পানি পান করতে দেবে,
অতঃপর অপরাপর বীরদের মধ্যে তুমি কর্তৃত্ব লাভ করবে…।
অন্য একটি ফলকে লেখা রয়েছে : স্বাগতম, তোমরা যারা যন্ত্রণা সয়েছ…তোমরা মানুষের উর্ধ্বে উঠে দেবতা হয়েছ। আরো একটি ফুলকে বলা হচ্ছে : সুখী আর আশীর্বাদধন্যরা শোনো, তোমরা নশ্বর না হয়ে দেবতা হবে।
মৃতের আত্মাকে যে ঝরনা-কূপ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করা হয়েছে সেটি লিথি (Lethe) বা বিস্মৃতি আনে। অন্য ঝরনা-কূপটি মেমোসাইনি (Mnemosyne), এর অর্থ স্মরণ বা স্মৃতি। পরলোকে আত্মাকে পরিত্রাণ পেতে হলে বিস্মৃত হওয়া চলবে না, বরং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি স্মৃতিশক্তি অর্জন করতে হবে।
অর্ফিকরা ছিল এক আত্মনিরোধী, কৃছুবাদী গোষ্ঠী। মদ তাদের কাছে ছিল একটি প্রতীকমাত্র, যেমনটি পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় সংস্কারে হয়েছে। তারা যে মাদকতা কামনা করত তা ছিল উদ্দীপনার মাদকতা, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের মাদকতা। তাদের বিশ্বাস ছিল সাধারণ উপায়ে যে মরমি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, এই উপায়ে তা লাভ করা সম্ভব। গ্রিক দর্শনে এই মরমিবাদী উপাদান প্রবেশ করেছে পিথাগোরাসের হাত ধরে, যিনি ছিলেন অফিজিমের একজন সংস্কারক, যেমনটি অর্ফিয়ুস ছিলেন ডায়োনিসাসের ধর্মের একজন সংস্কারক। পিথাগোরাস থেকে অর্ফিক উপাদানগুলো প্রবেশ করেছে। প্লেটোর দর্শনে আর প্লেটো থেকে তা প্রবেশ করেছে পরবর্তীকালের যেসব দর্শন কিছু না কিছু মাত্রায় ধর্মীয় ছিল সেসবের অধিকাংশতে।
যেখানেই অফিজিমের প্রভাব ছিল সেখানেই বাক্কাসীয় উপাদানগুলো নিশ্চিতভাবে ছিল। সেগুলোর একটি ছিল নারীবাদ, পিথাগোরাসে নারীবাদের উপাদান ছিল যথেষ্ট পরিমাণে এবং প্লেটোতে নারীবাদ এত পরিমাণে ছিল যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সম্পূর্ণ সম-অধিকার দাবি করেছিলেন। পিথাগোরাস বলেন, লিঙ্গ হিসেবে নারী প্রকৃতিগতভাবে অধিকতর পবিত্র। বাক্কাসীয় উপাদানগুলোর আরেকটি ছিল তীব্র আবেগের প্রতি অনুরাগ। গ্রিক ট্র্যাজেডিগুলোর জন্ম হয়েছে ডায়োনিসাসের আচার অনুষ্ঠানাদি থেকে। বিশেষত, ইউরিপাইডিস অর্ফিজিমের দুই প্রধান দেবতাকে ভক্তি করতেন। তারা হলেন ডায়োনিসাস ও এবোস। শীতল, আপনভোলা, শান্ত স্বভাবী, সদাচারী ব্যক্তির জন্য তার কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তার ট্র্যাজেডিগুলোতে দেখা যায়, এই ধরনের চরিত্রগুলো পাগল হয়ে যায়, অথবা কোনো না কোনোভাবে অধর্মাচারের শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর তাদেরকে দুঃখ-যন্ত্রণায় ফেলেন।
গ্রিকদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, তারা প্রশংসনীয় রকমের সৌম্য-শান্ত, তারা আবেগের বশবর্তী না হয়ে আবেগ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারত এবং আবেগের মধ্যকার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারত, কিন্তু নিজেরা ছিল শান্ত ও অলিম্পীয় মেজাজের। এটি খুবই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। সম্ভবত হোমার, সফোক্লিস এবং অ্যারিস্টটলের ক্ষেত্রে এটা সত্য হতে পারে, কিন্তু এটা সেইসব গ্রিকের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সত্য নয় যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাক্কাসীয় বা অর্ফিক উপাদানগুলো দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এলিউসিসে, যেখানে এথেনীয় রাষ্ট্রধর্মের সবচেয়ে ঐশ্বরিক অংশ গঠিত হয়েছিল এলিউসীয় গুহ্যাচার থেকে, সেখানে একটি স্তোত্র গাওয়া হতো, যার বাণীগুলো এ রকম–
উচ্চে দুলিয়ে সুরাপাত্র তোমার,
উন্মত্ত উল্লাসে
এলিউসিসের পুষ্পময় উপত্যকায়
এসো হে-বাক্কাস, পিয়ান, স্বাগতম।
ইউরিপাইডিসের বাককেতে মায়েনাদের কোরাসে কাব্য ও বর্বরতার সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়, যা কিনা শান্ত স্বভাবের একেবারেই বিপরীত। তারা একটি বন্য পশুকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে সেখানেই, তখনই, একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলে–
যখন পবিত্র ছাগশিশুর চামড়া লেগে থাকে
আর সবকিছুই ভেসে যায় উড়ে যায়
তখন ছোটার ক্লান্তিতে বেহুশ হয়ে পড়া
কী আনন্দ কী আনন্দ তখন পাহাড়ে
স্রোতস্বিনী রক্তপ্রবাহের আনন্দে
ছিঁড়ে ফেলা পাহাড়ি ছাগলের রক্তে
বন্য পশুর ভয়ঙ্কর ক্ষুধার গৌরবে
যেখানে পাহাড়ের চূড়া ধরে ফেলে দিনকে
সেই ফ্রিজিয়ান আর লিডিয়ান পাহাড়ে পাহাড়ে
হে ব্রোমিওস, পথ দেখাও।
পর্বতচূড়ায় মায়েডদের নৃত্য কেবল উন্মত্তই ছিল না, তা ছিল সভ্যতার বোঝা আর দায়িত্ব-কর্তব্য-যত্ন-সতর্কতা থেকে অমানবিক সৌন্দর্যের জগতে, হাওয়া আর তারকাদের মুক্ত জগতে পলায়নস্বরূপ। অপেক্ষাকৃত কম উত্তেজনার মেজাজে তারা একটি গান গাইত–
তারা কি আবার আসবে আমার কাছে, আবার কখনো
সেই সব দীর্ঘ, দীর্ঘ নৃত্য?
যে-সব নৃত্য চলত সারা রাত ধরে, অনুজ্জ্বল তারাগুলো মিলিয়ে না যাওয়া অবধি?
কণ্ঠে কি আমি শিশিরের স্পর্শ পাব? চুলে লাগবে হাওয়ার পরশ?
নিষ্প্রভ প্রান্তরে আমাদের শুভ্র পদরাজি কি দ্যুতিময় দেখাবে?
হরিণশাবকের পাগুলো হারিয়ে গেছে হায়! সবুজ বনে,
একাকী, ঘাসে আর সৌন্দর্যে
শিকারির শিকার হয়ে লাফাবে না আর, কোনো ভয় আর নেই তার।
আর তার ফাঁদে পড়ার ভয় নেই, নেই কোনো মারাত্মক চাপ।
একটি কণ্ঠস্বর তবুও ভেসে আসে,
একটি কণ্ঠস্বর, একটি ভয়, ডালকুত্তাদের ছুট,
ওহ্ জান্তব শ্রম, দুর্ধর্ষ ক্ষিপ্রতা,
নদী আর উপত্যকা বেয়ে ধেয়ে চলা
হে ঝাক্ষিপ্র পদযুগল, এ কি হর্ষ, না আতঙ্ক?
মানুষের উৎপাতহীন, নির্জন, প্রিয় এই দেশে,
যেখানে ধ্বনিত হয় না কোনো কণ্ঠ, ছায়াচ্ছন্ন সবুজের মাঝে
বনভূমির ছোট ছোট জীব বাস করে অলক্ষ্যে।
গ্রিকরা সৌম্য-শান্ত ছিল এই কথাটির পুনরাবৃত্তি করার আগে ইউজিন ওনিলের একটি নাটকে ফিলাডেলফিয়ার ম্যাট্রনদের এ রকম আচরণের কথা ভেবে দেখার চেষ্টা করুন। ডায়োনিসাসের আদি উপাসকদের চেয়ে অর্ফিকরা কোনোভাবেই বেশি শান্তশিষ্ট নয়। একজন অর্ষিকের কাছে এ জগতে জীবন হচ্ছে যন্ত্রণা, ক্লান্তি আর একঘেয়েমি। তাদের মতে, আমরা এমন এক চক্রে বাঁধা যা জন্ম আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীনভাবে ঘুরে চলেছে। আমাদের সত্যিকারের জীবন স্বর্গে, কিন্তু আমরা বাঁধা পড়ে আছি পৃথিবীর মাটির সঙ্গে। শুদ্ধি, ত্যাগ আর কৃচ্ছসাধনাপূর্ণ জীবনযাপনের দ্বারাই কেবল আমরা সেই চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং পরিশেষে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের পরমানন্দ লাভ করতে পারি। যেসব মানুষের কাছে জীবন সহজ ও আনন্দদায়ক এটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না। এটা অনেকটাই সেই নিগ্রো ধর্মসঙ্গীতের মতো, যেখানে বলা হয়–
যখন আমি ঘরে পৌঁছুব
তখন আমার সব সমস্যার কথা ঈশ্বরকে বলব।
গ্রিকদের সবাই নয়, কিন্তু তাদের এক বিরাট অংশ ছিল তীব্র আবেগপ্রবণ, অসুখী। তাদের মধ্যে ছিল যুক্তিবুদ্ধি আর আবেগের লড়াই। তাদের মধ্যে স্বর্গের কল্পনা আর নরক সম্পর্কে সচেতন আত্মপ্রত্যয়ের দ্বন্ধ ছিল। তাদের একটি নীতিবাক্য ছিল, কোনো কিছুতেই বাড়াবাড়ি কোরো না। কিন্তু বাস্তবে তাদের সব কিছুতেই ছিল বাড়াবাড়ি-বিশুদ্ধ চিন্তায়, কাব্যকলায়, ধর্মে এবং পাপকর্মে। যখন তাদের মধ্যে আবেগ আর যুক্তিবুদ্ধির মিলন ঘটেছে তখন তারা মহৎ সব কর্ম করাতে পেরেছে। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে তারা যেভাবে বদলে দিয়েছে, শুধু আবেগ বা শুধু যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তা করা কখনোই সম্ভব ছিল না। পুরাণে তাদের প্রত্নপ্রতিমা অলিম্পীয় জিউস নয়, বরং প্রেমিথিউস, যে স্বর্গ থেকে আগুন এনেছিল এবং তার পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল চিরন্ত ন যন্ত্রণা।
সামগ্রিকভাবে গ্রিকদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ব্যাপারে উপরে যা বলা হলো, অর্থাৎ, গ্রিকদের যে শান্তশিষ্ট বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা একটি একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত গ্রিসে প্রবণতা ছিল দুটি। একটি আবেগ-প্রবণতা : ধর্মীয়, মরমি, পরজাগতিক প্রবণতা। আর অন্যটা হাসি-খুশি, অভিজ্ঞতাবাদী, যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী এবং বিচিত্র রকমের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী প্রবণতা। দ্বিতীয় প্রবণতাটি লক্ষ করা যায় হেরোডটাসের মধ্যে। একেবারে গোড়ার দিকের আয়োনীয় দার্শনিকদের মধ্যেও তা ছিল। একটি পর্যায় পর্যন্ত অ্যারিস্টটলও তাই। অফিজম বর্ণনা করার পর বেলক বলেছেন
ইহজগৎকে অস্বীকার করে বাস্তব জীবনকে পরকালে স্থানান্তরিত করার সর্বজনগ্রাহ্য যে-একটি বিশ্বাস ছিল তাকে অতিক্রম করার মতো যথেষ্ট যৌবনময় প্রাণশক্তির অধিকারী ছিল গ্রিক জাতি। তাই অর্ফিক মতবাদ সীমাবদ্ধ ছিল অজিমে দীক্ষিত একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে, রাষ্ট্রধর্মের ওপর তার প্রভাব ছিল না বললেই চলে। এমনকি এথেন্সের মতো স্থানের জনগোষ্ঠী, যারা তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মাচারে গুহ্য ধর্মানুষ্ঠানগুলো উদ্যাপনের রীতি গ্রহণ করেছিল এবং তাকে আইনগত সুরক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অর্ফিক মতবাদের প্রভাব ততটা ছিল না। অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের এক ধর্মতাত্ত্বিক পোশাকে তা গ্রিক জগতে বিজয় অর্জন করেছিল, কিন্তু তার জন্য পুরো এক হাজার বছর সময় লেগেছিল।
এই বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত মনে হয়, বিশেষ করে এলিউসীয় গুহ্য ধর্মানুষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে, যেগুলো অর্ফিক মতবাদ দ্বারা পরিপূর্ণ। ব্যাপক অর্থে বললে, যাদের মেজাজ ও মনোভঙ্গি ছিল ধর্মীয় তারাই অফিঁজমের দিকে ঝুঁকেছে আর যুক্তিবাদীরা অৰ্কিজমকে ঘৃণা করেছে। ১৮ শতকের শেষ ও ১৯ শতকের শুরুর দিকের ইংল্যান্ডের মেথডিজম। বা পদ্ধতিবাদের সঙ্গে অজিমের মর্যাদার তুলনা করা যেতে পারে।
একজন গ্রিক তার পিতার কাছে কী শিক্ষা লাভ করত তা আমরা কমবেশি জানি। কিন্তু একেবারে শৈশবের দিনগুলোতে একজন গ্রিক তার মায়ের কাছ থেকে কী ধরনের শিক্ষা লাভ করত তা সম্পর্কে আমরা জানি খুব অল্পই। পুরুষরা যে সভ্যতা থেকে আনন্দ লুটত, নারীরা তার আলো থেকে বেশ বঞ্চিত ছিল। এমন হতে পারে যে, শিক্ষিত এথেন্সবাসিরা, এমনকি তাদের সর্বোত্তম যুগেও, আচরণগত দিকে সচেতন মানসিক প্রক্রিয়ায় যত যুক্তিবাদীই হোক না কেন, ঐতিহ্যগতভাবে একেবারে শৈশব থেকেই চিন্তাপদ্ধতি ও অনুভবের এমন একটি আদিম ধরন তাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল যা সংকটময় মুহূর্তগুলোতে সর্বদাই জয়ী হয়েছে। এই কারণে গ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোনো সরল বিশ্লেষণ যথার্থ হবে বলে মনে হয় না।
সাম্প্রতিককালের আগে পর্যন্ত গ্রিক চিন্তায় ধর্মের, বিশেষ করে অন-অলিম্পীয় ধর্মের প্রভাব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। জন হ্যারিসনের প্রলেগোমেনা টু দি স্টাডি অব গ্রিক রিলিজিয়ন গ্রন্থে সাধারণ গ্রিকদের ধর্মে আদি ও ডায়োনিসাসীয় উপাদান, দুটোর কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এফএম কর্নফোর্ড-এর ফ্রম রিলিজিয়ন টু ফিলোসফি গ্রন্থে দার্শনিকদের ওপর ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে গ্রিক দর্শনের শিক্ষার্থীদের অবগত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তার অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অথবা তার নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলো সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করা যায় না। আমার জানা মতে, সবচেয়ে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে জন বার্নেটের আরলি গ্রিক স্টাডিজ গ্রন্থটিতে, বিশেষ করে বইটির বিজ্ঞান ও ধর্ম শীর্ষক অধ্যায়টিতে। বার্নেট বলেন, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হেলাসজুড়ে যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সৃষ্টি হয় তা থেকে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটি বিরোধ দাঁড়িয়ে যায়; আয়োনিয়া থেকে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হতে হতে পশ্চিমে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা ঘটতে থাকে। তিনি বলেন, উপমহাদেশীয় হেলাসের ধর্ম বিকশিত হয়েছে আর্জেনিয়ার ধর্মবিকাশের ধরন-প্রক্রিয়ার চেয়ে খুবই আলাদাভাবে। নির্দিষ্ট করে প্রেস থেকে আগত ডায়োনিসাস-পূজা, যার কথা হোমারে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তাতে জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গির বীজ ছিল। থ্রেসীয়রা নিজেরা কোনো উচ্চমানের দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিল এ কথা বলা নিশ্চিতই ভুল হবে। তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, গ্রিকদের আধ্যাত্মিক পরমানন্দের বিষয়টির অর্থ ছিল এই যে, আত্মা কেবল সত্তার একটি ক্ষীণ প্রতিরূপ নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু এবং আত্মা যখন দেহের বাইরে যায়, কেবল তখনই তার প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায়…।
মনে হয় গ্রিক ধর্ম যেন সেই পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছিল, প্রাচ্যের ধর্মগুলো ইতমধ্যে যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। বিজ্ঞানের উত্থান ছাড়া আর কিসের দ্বারা সেই প্রবণতা প্রতিহত হয়েছিল তা দেখতে পাওয়া কঠিন। সাধারণভাবে বলা হয়, প্রাচ্য ধরনের ধর্ম থেকে গ্রিকরা রক্ষা পেয়েছিল এই জন্য যে তাদের কোনো পুরোহিততন্ত্র ছিল না। কিন্তু এ রকম বলার অর্থ দাঁড়ায় কারণকে কার্য হিসেবে ধরে নেওয়া, অর্থাৎ এতে ভুল করা হয়। পুরোহিততন্ত্র অন্ধবিশ্বাস তৈরি করে না, যদিও ইতমধ্যে সৃষ্ট বা বিদ্যমান অন্ধবিশ্বাসকে তা জিইয়ে রাখে। কিন্তু বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে প্রাচ্যের জাতিগুলোর মধ্যে কোনো পুরোহিততন্ত্র সে অর্থে ছিল না। গ্রিসকে রক্ষা করেছে তার বৈজ্ঞানিক ধারাগুলো যতটা, পুরোহিততন্ত্রের অনুপস্থিতি ততটা নয়।
নতুন ধর্ম-যা এক বিবেচনায় নতুন, অন্য বিবেচনায় মানবজাতির মতোই পুরাতন-তার বিকাশের সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে অফিক সম্প্রদায়গুলোর গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যত দূর দেখতে পাই, সে সম্প্রদায়গুলোর আদি নিবাস ছিল অ্যাটিকা, কিন্তু তারা অসাধারণ দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতে। তারা প্রথমত ছিল ডায়োনিসাসের উপাসক গোষ্ঠী, কিন্তু তারা আলাদা ছিল দুটি দিক থেকে, যা গ্রিক নাগরিকদের মধ্যে ছিল নতুন বিষয়। তাদের কাছে ধর্মীয় কর্তৃত্বের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো ঐশী প্রত্যাদেশ এবং তারা সংগঠিত হয়েছিল কৃত্রিম সম্প্রদায় রূপে। যেসব কাব্যে তাদের ধর্মতত্ত্ব রয়েছে সেগুলোর উৎস অর্ফিয়ুস, এই অর্ফিয়ুস নিজে থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন হাডেস-এ এবং পরজগতে দেহ থেকে মুক্ত আত্মাকে ঘিরে যেসব ভয়ানক বিপদ-আপদ রয়েছে সেসব অতিক্রম করে যাবার পথে তিনি এক নিরাপদ দিগনির্দেশক।
বার্নেট আরো বলছেন, অর্ফিক ধর্মবিশ্বাসগুলোর সঙ্গে প্রায় একই সময়কার ভারতে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসগুলোর একটি চমৎকার সাদৃশ্য আছে; যদিও তিনি মনে করেন যে, তখন এ দুই দেশের মধ্যে কোনো যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। এরপর তিনি orgy বা উদ্দাম পানভোজনোৎসব শব্দটির মূল অর্থের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। অর্ফিকরা এই শব্দটিকে ধর্মদীক্ষার অনুষ্ঠান বোঝাতে ব্যবহার করত। এই উপায়ে তারা বিশ্বাসীর আত্মাকে শুদ্ধ করত এবং জন্মের চক্র থেকে তাকে মুক্ত করতে চাইত। আমরা যাকে গির্জা বা church বলি, তার প্রতিষ্ঠা করে অর্ফিকরা, অলিম্পীয় ধর্মের পুরোহিতরা তা করেনি। গির্জা মানে ধর্মীয় সম্প্রদায়, লিঙ্গ-বর্ণ নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সে সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারত। তাদেরই প্রভাব থেকে জীবনযাপনের একটি বিধান বা পথ হিসেবে দর্শনের সৃষ্টি।