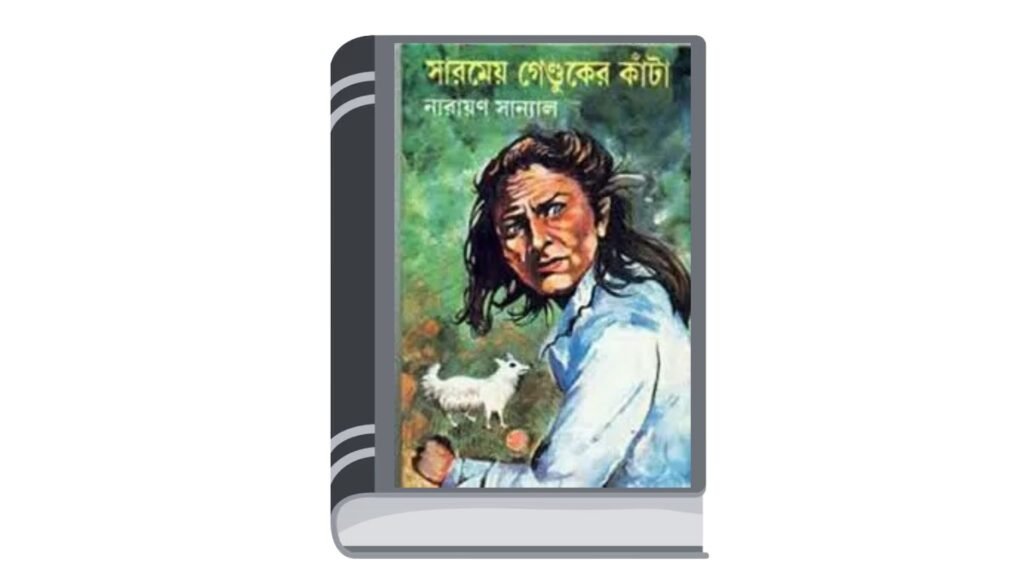সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা – ৫
৫
ওরা কোনও ঘুমের ঔষুধ ওঁকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছিল কিনা জানেন না। টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা উনি অঘোরে ঘুমিয়েছেন। তারপর আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল একটা পরিচিত শব্দে :
ঘৌ-ঘৌ নয়, কুঁই-কুঁই।
চোখ দুটি খুলে গেল বৃদ্ধার। লক্ষ হল পাশেই বসে আছে মিনতি। বসে বসেই ঘুমাচ্ছিল সে ঘাড় গুঁজে। ফ্লিসির কুঁই-কুঁইটা তারও কানে গেছে। চট করে উঠে দাঁড়ালো সে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরেই সদর-দরজা খোলার শব্দ। তারপর মিনতির চাপা কণ্ঠস্বর : হতভাগা! বাঁদর। কর্ত্রীর এখন-তখন, আর তুই সারারাত পাড়া বেড়াচ্ছিস!
পামেলার সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা; কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। ওঁর মনে পড়ে গেল—মাসের মধ্যে পাঁচ-সাত দিন তিনি নিজে যেমন নৈশবিহার করে থাকেন, তেমনি ফ্লিসিও করে। তফাৎ; এই, উনি নৈশবিহার সারেন মরকতকুঞ্জের ভিতরে, ফ্লিসি বাইরে। তফাত এই, গৃহকর্ত্রী সে জন্য আদৌ লজ্জিতা নন, ফ্লিসি সলজ্জ।
এতক্ষণে বৃদ্ধার মনে পড়লো—দুর্ঘটনার পর থেকে কিসের যেন একটা অভাব বোধ করছিলেন তিনি! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বাড়িশুদ্ধ সবাই জড়ো হয়েছিল, কিন্তু একটা অতি পরিচিত সারমেয়র গর্জন তিনি শুনতে পাননি। তার মানে ফ্লিসি বাড়িতে ছিল না। থাকলে, সবার আগে সেই পাড়া মাথায় তুলতো!
কিন্তু! তা কেমন করে হয়? বলটা তাহলে কেমন করে…
মনে পড়ে গেল সুরেশের কথাটা। উনি সিঁড়ির নিচে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন আর সুরেশ রবারের বলটা উঁচু করে দেখিয়ে বলছে, এইটার জন্যেই বড়পিসির পা হড়কেছিল।
তাই কী?
সেই খণ্ডমুহূর্তের কথাটা মনে করতে চেষ্টা করলেন পামেলা। পতনের পূর্বমুহূর্তটা। না, পায়ের তলায় নরম রবারের বলটার কোনও স্পর্শের স্মৃতি তাঁর নেই। তাহলে হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন কী করে? কেন? না, পিছন থেকে কেউ তাঁকে ঠেলা দেয়নি। ত্রিসীমানায় তখন কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। না, পায়ের তলায় রবারের বলটাও ছিল না। তাহলে?
ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। আশ্চর্য! অপরিসীম আশ্চর্য!
ওঁর স্পষ্ট মনে আছে, রাত্রে সায়মাশের পর, সবাই যে যার ঘরে চলে যাবার পর তিনি আর মিনতি দোতলায় উঠে আসেন। সরযূ এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে টেবিলটা যখন সাফা করছে তখনো তিনি নিচে হলঘরে। ওঁর স্পষ্ট মনে আছে, সরযূ চলে যাবার পর মিনতি সদর বন্ধ করলো। ওঁরা দুজনে দোতলায় উঠে এলেন। তখন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ওঁর নজরে পড়েছিল রবারের বলটা সিঁড়ির নিচে পড়ে আছে। নিচে অর্থাৎ দোতলায় নয়। ঠিক মনে পড়ছে না, উনি কি মিন্টিকে বললেন বলটা সরিয়ে রাখতে? নাকি বলবেন ভেবেছিলেন? বলেননি? সে যাই হোক, বলটা উপরে উঠে এল কী করে? ফ্লিসি মুখে করে আনতে পারে না; কারণ তার আগেই রাতের মতো সদর দরজা বন্ধ হয়েছে। ফ্লিসি নিশ্চয়ই তার আগেই বেরিয়ে গেছে। এই শেষ রাত্রে ফিরলো! তাহলে কে বলটাকে উপরে নিয়ে এসেছিল। আদৌ এসেছিল কি?
না আসেনি। সুরেশের ডিডাকশানটা ভুল। পতনজনিত দুর্ঘটনার হেতু ঐ রবারের বলটা নয়। বল নয়, কলার খোসা নয়, পিছন থেকে ঠেলাও কেউ দেয়নি, তাঁর মাথাও ঘুরে ওঠেনি—তাহলে তিনি পড়ে গেছেন কী করে? কেন?
হঠাৎ একটা নিরতিশয় আতঙ্কের আভাস পেলেন যেন। আতঙ্কেরই শুধু নয়, নিরতিশয় গ্লানির, লজ্জার।
তাই কি?
না, এখন নয়। এখন তাঁর স্নায়ু দুর্বল। শরীর অবশ। কিন্তু কথাটা ভুললেও চলবে না। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে তাঁকে। সুসময়ে। একটু সামলে উঠেই।
৬
সতেরই এপ্রিল। দশটা দিন কেটে গেছে ইতিমধ্যে।
বাড়ি ফাঁকা। সবাই চলে গেছে যে যার পরিচিত গণ্ডিতে।
এবার এই বাহাত্তরের ঘাটে এসে ওঁকে আর সেই ক্লান্তিকর ঘ্যানঘ্যানটা শুনতে হয়নি : হ্যাপি বার্থ ডে টু য়ু! অনিমন্ত্রিত এসেছিলেন দুজন। শুভেচ্ছা জানাতে। পিটার দত্ত আর ঊষা বিশ্বাস।
জন্মদিনের সন্ধ্যায় তিনি শয্যাশায়ী।
ওরা চারজনই—সুরেশ, টুকু, হেনা আর প্রীতম মরকতকুঞ্জে থেকে যেতে চেয়েছিল। সেবা-শুশ্রূষা করতে। গৃহকর্ত্রী সম্মত হননি। সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বুড়ির যেন ভদ্রলোকের এককথা : চিরটা কাল একলা-একলা কাটিয়েছি। ফাঁকা বাড়ি না হলে আমি শান্তি পাব না। আসিস, তোরা আবার আসিস, কিন্তু তার আগে আমাকে একটু সামলে নিতে দে।
অতিথিরা বিদায় হবার পর প্রথম কয়েকটা দিন পামেলা শুধু চিন্তা করেছেন। ডক্টর পিটার দত্ত ওঁকে বারণ করেছেন চিন্তা করতে, বলেছেন, মনটা প্রফুল্ল রাখতে। কারণ ইতিমধ্যে ওঁর রক্তচাপটা—যেটা এতদিন কোনও বেয়াড়াপানা করেনি—নানারকম অবাধ্যতা শুরু করেছিল। ডাক্তার দত্তের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা একটু অন্য ধরনের। দু’জনেরই সত্তরের ওপরে, দু’জনে দু’জনকে চেনেন পঞ্চাশ-ষাট বছর। ডাক্তার দত্তের চোখে যুবতী পামেলার সেই মোহিনী মূর্তিটা আজও মুছে যায়নি। তিনি বাল্যবান্ধবীকে নাম ধরেই ডাকতেন। বলেছিলেন, এগারোটা সিঁড়ির ধাপ গড়িয়ে পড়লে আর একখানা হাড় ভাঙতে পারলে না পামেলা, ইটস শিয়ার ডিসগ্রেস! আশ্বাস দিতেন, কিচ্ছু হয়নি তোমার। পরের সপ্তাহেই আবার নিচে নামবে তুমি, আগেকার মতো আমাকে নেমন্তন্ন করে নিজে হাতে বানানো পাম-কেক খাওয়াবে!
ওঁর অসুখটা এবার সারছে না শুধু ঐ দুশ্চিন্তায়। ঘটনার পারম্পর্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিদিনই ঊষা বিশ্বাস এসে দেখা করে গেছেন, ফুলের তোড়া হাতে। তাঁকেও কিছু মন খুলে বলতে পারেননি। এ-কথা কি মন খুলে বলার? তবে ব্যবস্থা নিয়েছেন। আজ সকালেই। কলকাতায় ওঁর অ্যাটর্নি প্রবীর চক্রবর্তীকে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করছেন, দু-চারদিনের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন। কিন্তু তাতে ভবিষ্যৎকেই শুধু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, অতীতটা উদ্ঘাটিত হবে না। অথচ বিগত ঘটনার রহস্যজালটা ভেদ করতে না পারলে তিনি যে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছেন না। কেমন করে এমনটা হল? একতলা থেকে কী ভাবে রবারের বলটা দোতলায় উঠে গেল? যদি না গিয়ে থাকে—যায়নি বলেই তাঁর ধারণা, কারণ সেই বিশেষ খণ্ড-মুহূর্তে পায়ের তলায় একটা নরম রবারের বলের স্পর্শটাকে কিছুতেই স্মরণে আনতে পারছিলেন না তিনি। তার একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত…’
হঠাৎ বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। অসতর্ক মুহূর্তে বলে উঠলেন : জগদানন্দ সেন।
মিনতি শুয়ে ছিল মাটিতে মাদুর পেতে। উঠে বসে বললে, কিছু বললেন মা?
—হ্যাঁ, আমার চিঠি লেখার সরঞ্জামটা নিয়ো এসো তো মিন্টি। আর ঐ সঙ্গে টেলিফোন ডাইরেক্টারিটা।
একটু পরেই ফিরে এল মিনতি হুকুম তামিল করে।
হাত বাড়িয়ে সব কিছু নিলেন। কিন্তু আবার নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন যেন। ওঁর মনে পড়ে গেছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের জগদানন্দ সেন পরলোকগমন করেছেন। জগদানন্দই ওঁকে বলেছিলেন সেই বিচিত্র বিচক্ষণ ব্যারিস্টারটির কথা। ক্রিমিনাল-সাইডের ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল। যিনি জগদানন্দের কেসটা জিতিয়ে দিয়েছিলেন, ফাঁসীর আসামী জগদানন্দকে মুক্ত করেছিলেন এবং কে তাঁর ভাইপো যোগানন্দকে হত্যা করেছিল তা খুঁজে বার করেছিলেন! তার চেয়েও বড় কথা, জগদানন্দের কী একটা পারিবারিক অত্যন্ত গোপন সমস্যা এমনভাবে সমাধান করেছিলেন যাতে-কেউ কিছু জানতে পারেনি। কী যেন নাম ব্যারিস্টারটির? কিছুতেই মনে পড়ল না। জগদানন্দের বাড়িতে টেলিফোন আছে, হয়তো জগদানন্দের নাতনিকে টেলিফোনে পাওয়া যায় কিন্তু মরকতকুঞ্জে টেলিফোন রাখা আছে একতলার হল-ঘরে। উনি প্রায় উত্থানশক্তি-রহিতা। মিনতির দ্বারা একাজ হবে না। নাঃ! নামটা ওঁকে মনে করতে হবেই। আপাতত মিনতিকে বললেন, থাক, এখন চিঠি লিখবো না। এগুলো রেখে এসো।
মিনতি হুকুমের চাকর। আবার সেসব সরঞ্জাম রেখে এল নিচের ঘরে। হয়তো এখনি কর্ত্রী আবার চিঠি লিখতে চাইবেন, তাহলেও জায়গার জিনিস জায়গায় থাকবে, এই হচ্ছে মরকতকুঞ্জের আইন
চিঠির সরঞ্জাম যথাস্থানে রেখে ফিরে এসে মিনতি বললে, বই-টই পড়বেন? কোনও গল্পের বই এনে দেবো?
—লাইব্রেরি থেকে কিছু বই এনেছো? কই দেখি?
—হ্যাঁ, মা এনেছি। আপনি যেগুলোর নাম লিখে দিয়েছিলেন তার একখানাও পাইনি। দাশুবাবু নিজে থেকেই এই গোয়েন্দা বইটা দিল। বললে, খুব জমাটি বই।
—দাশু তো বলবেই। ও শুধু গোয়েন্দা গল্পের বইই পড়ে। কী নাম বইটার?
—দাঁড়ান, এনে দেখাই। আমার ঘরে আছে। ‘কিসের কাঁটা’ যেন—পি. কে.বাসু গোয়েন্দা সিরিজের…
—দ্যাটস্ ইট! প্রায় লাফিয়ে উঠে বসেন পামেলা জনসন।
মিনতি চমকে ওঠে। সে নিজে গোয়েন্দা বইয়ের পোকা। কিন্তু কর্ত্রী ডিটেকটিভ বই কদাচিৎ পড়েন। লাইব্রেরীয়ান দাশুবাবু প্রায় জোর করেই এ বইখান গছিয়ে দিয়েছে। বলেছে, নিয়ে যান, আপনার তো ভাল লাগবেই, ম্যাডামেরও দারুণ লাগবে।
মেরীনগরে অনেকে পামেলা জনসনকে ‘ম্যাডাম’ বলে।
মিনতি বলে, নিয়ে আসি তাহলে?
—শ্যিওর! শুভস্য শীঘ্রং! এখনই বখেড়া চুকিয়ে দিতে চাই।
মিনিট পাঁচেক পরে মিনতি নিজের ঘর থেকে লাইব্রেরির বইটা নিয়ে এল। তার মাঝামাঝি পড়া শেষ হয়েছিল। কিন্তু কর্ত্রী যখন ‘দ্যাটস ইট’ বলে অমন লাফিয়ে উঠেছেন, তখন তিনিই আগে পড়ুন।
বইখানা নিয়ে সে ফিরে এলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন পামেলা।
—এ কী? ইডিয়ট্! বইটা নিয়ে আসতে কে বললো তোমাকে? আমার চিঠি লেখার প্যাডটা চাইলাম না আমি? প্যাড, কলম, কুইক্
মিনতি কোনক্রমে সামলে নেয় নিজেকে। আবার নিচে যেতে হয় তাকে। নিয়ে আসতে হয় লেখার সরঞ্জাম। হাত বাড়িয়ে সেগুলি গ্রহণ করে পামেলা বলেন, তোমার গোয়েন্দা গল্পের বইটার মাঝখানে একটা ‘চুলের কাঁটা’ গোঁজা আছে। তার মানে তুমি ওটা আধাআধি পড়েছো! কারেক্ট?
মিনতি স্বীকার করে।
—দ্যাটস্ অল রাইট। বইটা নিয়ে যাও। ঘণ্টাখানেক পরে আমার হরলিক্সটা নিয়ে এস। আর শোন, এই এক ঘণ্টার মধ্যে কেউ যেন আমাকে ডিসটার্ব না করে। বুঝলে?
ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে মিনতি চলে যাচ্ছিল। তাকে ফিরে ডাকলেন আবার : শোন মিনতি আবার এসে নতনেত্রে দাঁড়ায়, আদেশের অপেক্ষায়।
—এখনি তোমাকে গালমন্দ করেছি বলে রাগ করনি তো?
মিনতি লজ্জা পায়। মাথা নেড়ে জানায়—সে কিছু মনে করেনি।
—দ্যাটস্ আ গুড গোর্ল! বকে কে? বকে মা! কারণ মা ভালবাসে। নয় কি? যাও।
নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয় মিনতি মাইতি। পামেলার কথাটা তার মনে লাগে। কর্ত্রী মাঝে মাঝে খেঁকিয়ে ওঠেন বটে; কিন্তু মনটা তাঁর সাদা। মিনতিকে ভালও বাসেন। ভালবাসা জিনিসটা মিনতি বড় একটা পায়নি। তিন কুলে তার কেউ নেই। শৈশবেই বাপ-মাকে হারিয়েছে। থাকার মধ্যে আছে এক খুড়তুতো দাদা—সে তো খোঁজ খবরই নেয় না। সৌভাগ্যই বলতে হবে—ঝি-গিরি করতে হচ্ছে না তাকে। ভদ্রঘরের মেয়েটিকে কর্ত্রী একটা সম্মানজনক উপাধি পর্যন্ত দিয়েছেন : মিন্টি ওঁর ‘সহচরী’।
লেটার-প্যাডটা টেনে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিখানি লিখতে বসেন এবার। নামটা নিতান্ত ঘটনাচক্রে মনে পড়ে গেছে ওঁর : বাসু, প্রসন্নকুমার, বার-অ্যাট-ল। টেলিফোন গাইড খুলে তাঁর নিউ আলিপুরের ঠিকানাটাও পেয়ে গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগল ড্রাফটা ছকতে। অনেক কাটাকুটির পর মনে হল বক্তব্যটা পরিষ্কার হয়েছে। এবার ধরে ধরে ফেয়ার কপি তৈরি করলেন। চিঠির মাথায় তারিখ বসালেন : 17.4.70। প্ৰথমে ড্রাফটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন এবার। একটি খাম বের করে চিঠিখানা ভরলেন, নাম ঠিকানা লিখে টিকিট সাঁটলেন। খামটা বন্ধ করে ঘড়িটা একবার দেখলেন। মিনতির হরলিক্স নিয়ে আসার সময় হয়েছে। না, মিনতি মাইতির হাতে চিঠিখানা ডাক বাক্সে ফেলতে পাঠানো যাবে না। মিনতি গোয়েন্দা গল্পের পোকা। তাকে জানানো চলবে না—ব্যারিস্টার পি.কে. বাসুকে তিনি একটি চিঠি লিখছেন। বিকালে সরযূ যখন ঘর মুছতে আসবে তখন তার হাতে চিঠিখানা ডাকে পাঠাবেন বরং। আপাতত ওটা তোশকের নিচে লুকানো থাক।
৭
এতক্ষণে আমরা আবার সেই উনত্রিশে জুন তারিখে ফিরে যেতে পারি। অর্থাৎ সেই যেদিন বাসু-সাহেব মিস্ পামেলা জনসনের চিঠিখানি পেলেন।
জাগুলিয়ার মোড় পার হয়ে আমাদের গাড়িটা যখন মেরীনগরের খোয়া-বাঁধানো সড়কে এসে পড়ল তখন বেলা এগারোটা। পাকা রাস্তা থেকে এই খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় মাইল-খানেক ভিতরে মেরীনগরের বসতি। বাসু-সাহেব পথ-চলতি একজনকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন ‘মরকতকুঞ্জটা কোন দিকে
গায়ে ফতুয়া, চোখে নিকেলের চশমা, লোকটা সোজা কথায় জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলো : আপনারা?
এটাই রেওয়াজ। সর্বকালে। সে আমলে এর জবাবে বহিরাগতরা গ্রামবাসীকে জানাতো : ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অথবা…অর্থাৎ নিজের জাত। নাম বা নিবাসের প্রসঙ্গ পরে আসতো। এ যুগে ঐ প্রশ্নটির জবাবে বহিরাগতকে বলতে হয় : কংগ্রেস, সি.পি.এম. অর্থাৎ…নিজের জাত। নাম বা নিবাসের প্রসঙ্গ পরে আসবে।
বাসু-সাহেব কোনও জবাব দেবার বদলে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিলেন।
বস্তুত ‘মরকতকুঞ্জটা খুঁজে বার করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হল না। মেরীনগরে সেটা আগ্রার তাজমহল।
গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে দূর থেকে নজর হল—দ্বিতলের জানালাগুলি বন্ধ। লাল ইঁটের টাক্-পয়েন্টিং করা প্রকাণ্ড প্রাসাদ—দুর্গ যেন। বাগানটা কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা। গেট তালাবন্ধ। সেখানে একটি নোটিস বোর্ড-বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে : এই বাড়ি বিক্রয় করা হইবে।
নোটিসে কলকাতার একটি নামকরা রিয়াল এস্টেট এজেন্টের নাম লেখা আছে এবং তারপরের লাইনে : ‘স্থানীয় ক্রেতারা মেরীনগরের অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরসের শ্রীভবানন্দ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারেন।’
সেই স্থানীয় দালালটির টেলিফোন নাম্বারও লেখা আছে।
তখনই অন্তরীক্ষ থেকে শ্রুত হল এক সারমেয় গর্জন। অচিরেই আবির্ভাব ঘটল তার—কাঁটাতারের ওপারে। সাদা ধবধবে একটা স্পিৎজ। তবে অনেকদিন তাকে স্নান করানো হয়নি বলে গায়ের রঙটা ধূসর হয়ে গেছে। কাঁটাতারের এপারে আমরা, ওপারে সে। আমাদের কথা সে কানেই তুললো না। এক নাগাড়ে বলে গেল, কে বট তোমরা? কী চাও? এগিয়ে এসো না কাছে?
ত্রিসীমানায় লোকজন নজরে পড়ল না। মনে হলো বাড়িতে কেউ নেই।
বললুম, এবার কী করবেন? কিছুই তো নজরে পড়ছে না।
—একেবারে কিছুই পাইনি বল না কৌশিক। অন্তত ‘সারমেয়’কে পেয়েছি, তার ‘গেণ্ডুক’-এর দেখা না পেলেও। চল, দেখা যাক অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরস্টা কোথায়
গির্জাটা গণ্ডগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। তাকে ঘিরে কিছু দোকানপাট। অনন্ত ভ্যারাইটি স্টোরও খুঁজে পেতে খুব কিছু অসুবিধা হল না। মনিহারি দোকান। বোধ করি মালিক জমি-বাড়ির দালালিও করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত মালিক অনুপস্থিত। দোকানে বসেছিল সতের-আঠারো বছরের একটি ছোকরা। স্পোর্টস গেঞ্জি, চোঙা প্যান্ট। খদ্দের পাতি ত্রিসীমানায় নেই। বুঁদ হয়ে সে একখানা সিনেমা পত্রিকা পড়ছিল।
বাসু-সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন, ভবানন্দবাবু আছেন?
ছেলেটি মুখ তুলে তাকিয়েও দেখল না। বললে, না।
—কোথায় গেছেন তিনি? কখন ফিরবেন?
—জান্নে।
—ভগবান দত্ত তোমার কে হন?
এতক্ষণে ছেলেটি মুখ তুলে তাকায়। প্রতি প্রশ্ন করে, কেন বলুন তো: সে খোঁজে আপনার কী প্রয়োজন?
বাসু-সাহেব জবাব দেবার আগেই ঝন্ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বইটা উবুড় করে কাউন্টারের উপর রেখে ও এগিয়ে গেল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল, “হ্যালো!…না নেই…জান্নে, আই মীন, কখন ফিরবেন বলতে পারছি না…কী বললেন?…সেসব বাবা জানে…হ্যাঁ বলবো, ফিরে এলে আপনাকে ফোন করতে বলবো? কী? কে. পি. চ্যাটার্জী? হ্যাঁ! কে. পি. চ্যাটার্জী, শুনেছি। কত নম্বর?…হ্যাঁ, হ্যাঁ, 46-5126! অ্যাঁ? 47? ও, আচ্ছা 47-2156! ফাইভ-সিক্স নয়, সিক্স-ফাইভ? অল রাইট? 47- 2165! ….না, না লিখে নেবার দরকার নেই, আমার মনে থাকবে। থ্যাঙ্কু। বলবো।”
টেলিফোনটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললো, কী বলছিলেন যেন?
—মরকতকুঞ্জে একটা নোটিসে বলা হয়েছে যে, ভবানন্দ দত্ত মশাই….
ও! মরকতকুঞ্জ কিন্তু বাবা তো নেই। আপনারা ওবেলা আসবেন।
বাসু-সাহেব জানালেন যে, ঐ বাড়িটা কিনবার ইচ্ছা নিয়ে আমরা কলকাতা থেকে আসছি। এখানে থাকি না যে, ও-বেলায় আবার আসতে পারবো। জানতে চাইলেন, তুমি বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে?
—আমি? মরকতকুঞ্জ? হ্যাঁ, শুনেছি ওটা বিক্রি হবে। তা সেসব কথা বাবা জানে। আপনারা ওবেলা আসবেন।
—তুমি কখনও ঐ বাড়িটার ভিতরে গিয়েছো? মালিকের নামটা জানো?
—আমি? মরকতকুঞ্জে? হ্যাঁ গিয়েছি—কতবার! কিন্তু সেসব কথা বাবা জানে। আপনারা বিকালবেলা আসবেন….
নিতান্ত সৌভাগ্য আমাদের, তখনই একটি সাইকেল চেপে এসে হাজির হলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সাইকেলটা লক করে এগিয়ে এসে বললেন, কী চাই স্যার?
—আমরা ভবানন্দ দত্ত মশায়ের খোঁজে…
—আমিই। বলুন স্যার?
—মরকতকুঞ্জের সামনে একটা নোটিস বোর্ড দেখলাম…
—হ্যাঁ, আসুন। ভিতরে আসুন। মাঝ-সড়কে দাঁড়িয়ে ওসব কথা আলোচনা করা যায় না।
দোকানের পিছনে আর একখানি ঘর আছে। ভদ্রলোক পথ দেখিয়ে সেখানে আমাদের বসালেন। গুদাম ঘরই। তবে খানতিনেক চেয়ার আছে, একটা চৌকিও। তিনি নিজে চৌকিতে উঠে বসলেন। বললেন, কলকাতা থেকে আসছেন নিশ্চয়? ঐ গাড়িতে?
—হ্যাঁ। আমরা শুনেছি, এই মেরীনগরে একটা বেশ বড় বাড়ি বিক্রি হবার সম্ভাবনা আছে। মরকতকুঞ্জ। আপনি নাকি তার হক-হদিশ সব জানেন….
—ঠিক কথা! শুধু ‘মরকতকুঞ্জ’ নয়, অনেকগুলি বাড়ির সন্ধান জানি আমি। কাঁচড়াপাড়ায়, হরিণঘাটায়, কল্যাণীতে। বিভিন্ন দামের, বিভিন্ন মাপের –
বাসু পাইপটা ধরালেন। বললেন, আমরা একটু নির্জনতা খুঁজছি। কাঁচড়াপাড়া বা কল্যাণীতেই যদি হবে, তবে খাশ কলকাতা কী দোষ করল?
—ঠিক কথা, ঠিক কথা। সে হিসাবে ‘মরকতকুঞ্জ’ আইডিয়াল প্রপার্টি। তবে প্রকাণ্ড বাড়ি, সংলগ্ন জমিও অনেক। দামটা নম্যাচারলি বেশিই হবে-
—পছন্দ হলে দামে হয়তো আটকাবে না। ‘প্রকাণ্ড’ মানে কত বড়? ক-তলা বাড়ি? ক-খানা ঘর?
ভদ্রলোক সে-কথার জবাব না দিয়ে হাঁকাড় পাড়লেন, খোকা, মরকতকুঞ্জের ফাইলটা নিয়ে আয় তো।
দোকান থেকে সেই ছোকরা একটা ফাইল এনে বাবাকে দিলো। একটা কাগজের টুকরো দেখে দেখে বলল, ইয়ে হয়েছে…একটু আগে কলকাতা থেকে সাম পি. কে. ব্যানার্জি তোমাকে ফোন করেছিলেন। কী একটা বায়নানামার ব্যাপারে।
ভবানন্দের ভ্রূ যুগল কুঁচকে গেল। বললেন, পি.কে. ব্যানার্জি? ঠিক চিনতে পারছি না তো। কোন জমির বায়নানামার?
—জান্নে। উনি ওঁর টেলিফোন নম্বরটা দিয়েছেন। বলেছেন, তোমাকে রিং-ব্যাক করতে : 45-6521.
ভবানন্দ একটা কাগজে নাম্বারটা টুকে নিয়ে ফাইলটা খুলতে থাকেন।
বাধা দিয়ে বাসু সাহেব বলেন, কলকাতার সাম মিস্টার কে.পি. চ্যাটার্জির একটা টেলিফোন আসার কথা ছিল কি?
অবাক হয়ে ভবানন্দ বলেন, হ্যাঁ, একটা বায়নানামার ব্যাপারে। আপনি কী করে জানলেন?
—সে কথা থাক। ফোনটা তাঁকেই করবেন। তাঁর নাম্বার বোধহয় 47-2165! ভবানন্দ তাঁর ‘খোকা’র দিকে তাকাতেই ছেলেটি সুট করে আড়ালে সরে গেল। মরকতকুঞ্জের যাবতীয় তত্ত্ব-তালাশ লেখা আছে ফাইলে। দ্বিতল বাড়ি। কোন তলায় ক’খানা ঘর, কত কত মাপের, সব খবর। আউট-হাউসের বিবরণ ও প্ল্যান। সংলগ্ন
বাসু-সাহেব পাকা হিসাবীর মতো সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে বললেন, গৃহকর্তা কি বাড়িটা আপাতত ভাড়া দিতে রাজি হবেন, মাস ছয়েকের জন্য? তাহলে এখানে বসবাসের সুবিধা-অসুবিধা বোঝা যেত।
—আজ্ঞে না। ভাড়া দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। স্রেফ বিক্রি।
—বাড়িটা কি বারে বারে হাতবদল হয়েছে?
—আদৌ না। একহাতেই বরাবর আছে। তৈরী করেছিলেন একজন বিলাতী কেতার বাঙালী ক্রিশ্চিয়ান – যোসেফ হালদার—বস্তুত এই মেরীনগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ছেলে-মেয়েরাই থাকতো এখানে। চারটি মেয়ে, একটি ছেলে। একে একে সকলেই স্বৰ্গত হয়েছে। শেষ মালিক ছিলেন মিস্ পামেলা জনসন। তিনি গত হয়েছেন মাস দুয়েক আগে—
বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বললেন, ব্যাপারটা তো ঠিক বোধগম্য হল না দত্ত মশাই। যোসেফ হালদারের অবিবাহিতা মেয়ের নাম—মিস্ পামেলা জনসন?
দত্ত মশাই হাসলেন, বললেন, আপনি যে উকিল-ব্যারিস্টারের মত সওয়াল-জবাব শুরু করলেন মশাই। তবে হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। মিস্ পামেলা জনসনের মায়ের নাম ছিল মেরী জনসন। মায়ের উপাধিটাই গ্রহণ করেছিলেন ম্যাডাম পামেলা।
—বুঝলাম। তা মিস্ পামেলা জনসনও তো গত হয়েছেন বলছেন। সেক্ষেত্রে বর্তমান মালিক কে?
–মিস মিনতি মাইতি।
—আই সি। তিনি পামেলার বোনঝি না ভাইঝি? না, ভাইঝি হলে মাইতি হত না।
—দুটোর একটাও নয়। তিনি ছিলেন পামেলার ‘সহচরী’—ইংরেজি কেতায় যাকে বলে ‘কম্পানিয়ান’। তাঁকেই বাড়িটা দিয়ে গেছেন ম্যাডাম। এখন সেই মিনতি মাইতিই ঐ প্রপার্টির মালিক। সমস্ত সম্পত্তি ঐ সহচরীকেই দিয়ে গেছেন মিস্ পামেলা জনসন।
—বুঝেছি। পামেলার কোনও ভাইপো-ভাইঝি অথবা বোনপো-বোনঝি ছিল না।
-–না, তা নয়, ছিল। কিন্তু তাদের কাউকেই উনি প্রপার্টিটা দিয়ে যাননি। উইল করে সব কিছুই দিয়ে গেছেন ঐ সহচরীকে।
বাসু বেঁকে বসলেন এবার। আমরা যদি প্রপার্টিটা কিনি সেই আত্মীয়-স্বজনেরা আবার মামলা মোকদ্দমা করবে না তো?
—মাপ করবেন স্যার। এবার কিন্তু আপনার এ-কথাটা উকিলের মতো হল না। মিনতি মাইতি প্রবেট নিয়েছে। মালিক বনেছে। এখন যদি সে সম্পত্তিটা রেজিস্ট্রি করে বিক্রয় করে তাহলে কে বাধা দিতে আসবে?
—আমরা বাড়িটা একবার দেখতে যেতে পারি?
–পারেন। অবশ্যই পারেন। এখনই দেখতে যাবেন, না লাঞ্চের পরে?
—বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। দু’টি খেয়ে নিই কোথাও ধরুন আমরা যদি আড়াইটে নাগাদ দেখতে যাই?
—তাই যাবেন। ও বাড়িতে টেলিফোন আছে। আমি খবর দিয়ে রাখছি। মিনতি মাইতি অবশ্য কলকাতায়, কিন্তু চাকর-বাকরেরা আছে। তারই ঘুরিয়ে দেখাবে। আপনারা কোথায় লাঞ্চ সারবেন?
—আপনি স্থানীয় লোক। সাজেস্ট করুন।
—মেরীনগরে সবচেয়ে ভাল হোটেল : ‘সুতৃপ্তি’–ঐ সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমি বলি কি, কাঁচড়াপাড়ায় চলে যান। এটুকু পেট্রল পোড়ানো সার্থক হবে। ‘সুতৃপ্তি’তে আর যাই পান, তৃপ্তি পাবেন না।
বাসু জানতে চাইলেন, মরকতকুঞ্জের দামটা কত হতে পারে আন্দাজ দিতে পারেন?
—ভবানন্দ প্রায় কানে কানে বললেন, দু-দুটি পার্টি ইতিমধ্যেই বাড়িটা দেখে গেছেন—একজন রিটায়ার্ড বিগ্রেডিয়ার, একজন রিটায়ার্ড জজ। দুজনেরই পছন্দ হয়েছে। যে কোনও একজন দর দিলেই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাবে কিন্তু। গোপনে বলি, মিনতি মাইতি বাড়িটা ঝেড়ে দেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। বেশি দরদাম করবে বলে মনে হয় না। তাই আমার পরামর্শ, পছন্দ হলে একটা ‘অফার’ দিয়ে যান। মিনিমাম ‘অফার’ই দেবেন, একটু দরদাম করে—সেই যাকে বলে ‘আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক’ গোছের একটা রফা করে দেওয়া যাবে। আমাকে কোনও কমিশন দিতে হবে না। আমি ও তরফ থেকে তা পাবো!
বাসু একটু সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন। বললেন, সেই ‘সহচরী’ ভদ্রমহিলা এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন, বলুন তো মশাই। ভুতুড়ে বাড়ি-টাড়ি নয় তো?
—আরে না, না। সেসব কিছু নয়। মিনতি মাইতি অত বড় বাড়ি নিয়ে কী করবে? চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, তিন কুলে কেউ নেই—বাড়িটা বিক্রি করে সে ঝাড়া হাত-পা হতে চায় আর কি।
বাসু আবার বলেন, শুনুন দত্তমশাই! বাড়িটা কিনলে আমিও কমিশন দেব আপনাকে। খোলাখুলি বলুন তো—ও বাড়িতে কোনও খুন-জখম, আত্মহত্যা-ফত্যা হয়েছে কখনও।
ভবানন্দ আবার ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, আমি চল্লিশ বছর এই মেরীনগরের বাসিন্দা। মা-কালীর নামে দিব্যি করে বলছি, আমার জ্ঞানত সেরকম কোনও দুর্ঘটনা ওখানে ঘটেনি।
–পামেলা জনসন কীভাবে মারা যান? স্বাভাবিক মৃত্যু?
—বিলকুল। বাহাত্তর বছর বয়স হয়েছিল ম্যাডামের। শেষ তিন-চার বছর ভুগছিলেন জনডিস্-এ। তাতেই মারা যান মাসদুয়েক আগে।
—ঠিক আছে। আগে বাড়িটা তো দেখি। তারপর আপনার সঙ্গে কথা হবে।
—একটু চা-টা খাবেন না?
—থ্যাঙ্কু। না। লাঞ্চের আগে চা খেলে খিদেটা নষ্ট হবে।
বাসু-সাহেব গাত্রোত্থান করতেই ভবানন্দ বললেন, আপনার নামটাই জানা হয়নি স্যার, যোগাযোগের একটা ঠিকানা—
—আমার নাম কে. পি. ঘোষ। ইন্ডিয়ান নেভিতে ছিলাম। রিটায়ার করেছি। আগে বাড়িটা দেখি। মোটামুটি পছন্দ হলে আবার আসব। ঠিকানা, ফোন নম্বর আর আমার ‘অফার’ দিয়ে যাব।
—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে।
৮
অনন্ত স্টোরস্ থেকে বেরিয়ে এসে আমি প্রশ্ন করি, এবার কোথায়? ব্যাক টু ক্যালকাটা?
–সে কি! আড়াইটেয় ‘মরকতকুঞ্জ’ দেখতে যাবার কথা বললাম না?
–সে তো রিটায়ার্ড নেভাল অফিসার কে.পি.ঘোষ বলেছেন আপনার তাতে কী?
—কিন্তু যে জন্যে আসা, তা তো এখনো সুসম্পন্ন হয়নি কৌশিক।
—আবার কী? শুনলেন না— আপনার ক্লায়েন্ট মিস্ পামেলা জনসন মারা গেছেন?
—এক্সজ্যাক্টলি।
যে ভঙ্গিতে উনি ঐ একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন, তাতে একটু ঘাবড়ে যাই। গুছিয়ে নিয়ে বলি, মানে…আমি বলতে চাইছি—মিস্ পামেলা জনসন যে-কথা আপনাকে জানাতে চাইছিলেন তা আর জানা যাবে না। কী তাঁর সমস্যা ছিল তা যখন জানা যাবে না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে এ পার্টটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে!
—কী সহজে তুমি বলতে পারলে কথাটা! শুনে রাখো কৌশিক! পি.কে.বাসু যতক্ষণ না কোনও সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়েছে বলে মেনে নিচ্ছে ততক্ষণ তা শেষ হয়ে যায় না— ওঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তবু অন্তিম যুক্তিটা আবার দাখিল করি, কিন্তু যেহেতু আপনার ক্লায়েন্ট
—এক্সজ্যাক্টলি! কৌশিক— এক্সজ্যাক্টলি! সবচেয়ে দামী কথাটাই তুমি বারে বারে বলছ, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থটা প্রণিধান না করে!
আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। রুখে উঠি, কী বলতে চান আপনি? পামেলার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়? শুনলেন না ভবানন্দ দত্তের কথা— জনডিসে ভুগে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মারা গেছেন, নিতান্ত পরিণত বয়সে?
—ভবানন্দ তো একথাও বলেছিল যে, একজন বিগ্রেডিয়ার আর একজন হাইকোর্টের জজ বাড়িটা কিনবার জন্য মুখিয়ে আছে। সেকথা বিশ্বাস করেছিলে তুমি? ভবানন্দ যুধিষ্ঠির?
এ কথার কী জবাব? বলি, তাহলে কি কাঁচড়াপাড়ার কোনও রেস্তোরাঁয়…..
—না। আমরা ঐ ‘সুতৃপ্তি’তেই মধ্যাহ্ন আহার সারবো। ভবানন্দের ও-কথাটা অবশ্য মানি যে, সেখানে ‘তৃপ্তি’ পাব না; কিন্তু এই সুবাদে মরকতকুঞ্জ সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ
হয়ত সংগ্রহ করা যাবে। এসো।
অগত্যা।
‘সুতৃপ্তি’ একটি ছোট্ট রেস্তোরাঁ। এত বেলাতেও কেউ কেউ খাচ্ছে। আমরা দূরতম একটা পর্দা-ঘেরা কেবিনে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই একজন মাঝবয়সী ‘বয়’ এসে জিজ্ঞাসা করলো, কী খাবেন স্যার? ভাত?
বাসু বলেন, না। কী কী পাওয়া যাবে বল তো ঠিক। মুরগি হবে?
—হবে, কিন্তু একটু দেরী হবে স্যার। আধঘণ্টা লাগবে।
—তা হোক। আমাদের তাড়া নেই। টোস্ট নিয়ে এসো, আর স্যালাড। মুরগির রোস্ট বানাও। নাও, তোমার টিপ্স্টা আগাম নাও দিকিন–বাসি মাল চালিও না।
লোকটা পাঁচ টাকার নোটখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বললে, সুতৃপ্তিতে বাসি মাল পাবেন না স্যার। অন্তত আপনাকে সব টাটকা জিনিসই সার্ভ করবো। কলকাতা থেকে আসচেন বুঝি?
—হ্যাঁ। অর্ডারটা দিয়ে ঘুরে এসো দিকিন। কথা আছে।
লোকটা গেল আর এলো। বললে, বলুন স্যার?
–তোমাকে বেশ চালাক-চতুর লাগছে। শোন, আমরা ঐ মরকতকুঞ্জটা কিনতে এসেছি, মানে যদি পছন্দ হয়—
—জানি, আন্দাজ করেছি। এখনই অনন্ত স্টোরস্ থেকে বার হলেন, না?
—হ্যাঁ। ও বেলায় বাড়িটা দেখবো। পছন্দ হলে মেরীনগরেরই বাসিন্দা হয়ে যাব। এখন দু’চারটে খবর বল দেখি। এখানে ভাল ডাক্তার আছে?
—আছেন স্যার। ডাক্তার পিটার দত্ত। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। সত্তরের ওপর বয়স। অতি বিচক্ষণ।
—মরকতকুঞ্জ বাড়িটার মালিক কে এক মিস্ মাইতি, নয়?
—আজ্ঞে হ্যাঁ। বর্তমানে সেই হচ্ছে ছপ্পড়ফোড় মালকিন!
—’ছপ্পড়ফোঁড় মালকিন’ মানে?
লোকটা একই কথা আবার জানালো। প্রাক্তন মালকিন মিস্ পামেলা জনসন তাঁর নিকট আত্মীয়দের বঞ্চিত করে একেবারে শেষ সময়ে বাড়িটা দিয়ে যান তাঁর সহচরীকে। রীতিমত উইল করে।
—মিনতি মাইতি বোধ হয় দীর্ঘদিন ওঁর সেবাযত্ন করেছে?
—মোটেই নয়। মাত্র তিনবছর সে এই চাকরিতে বহাল ছিল।
—মাত্র তিন বছর! শুধু বাড়িটাই দিয়ে গেছেন, নগদ-টগদ দেননি নিশ্চয়—
আমি লক্ষ করেছি, কারও পেট থেকে খবর বার করতে হলে তাকে প্রতিবাদ করার সুযোগ দিতে হয়। ভবানন্দের কাছ থেকেই আমরা জেনেছি যে পামেলা তাঁর সবকিছুই নির্ব্যঢ় স্বত্বে দান করে গেছেন তাঁর সহচরীকে। বাসুমামু সেটাই করোবরেট করাতে চান; কিন্তু তিনি এমনভাবে প্রশ্ন রাখছেন যাতে বক্তা একটা প্রতিবাদের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রেও তাই হল। লোকটা সোৎসাহে বলল, আপনার ভুল ধারণা স্যার! উইলটা যখন পড়ে শোনানো হচ্ছিল তখন নাকি সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। বুড়ি থাকত খুব সাধাসিধে—কিন্তু তার কোম্পানির কাগজই নাকি ছিল সাত লক্ষ টাকার!
—বল কী হে! এ যে রূপকথার গল্প! বুড়ির আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না বুঝি?
আবার প্রতিবাদের সুযোগ : এখানেও ভুল হল আপনার। ছিল; ভাইপো, ভাইঝি আর বোনঝি। বোনঝি হেনা অবশ্য একজন সর্দারজীকে বিয়ে করেছে—বুড়ির রাগ হতেই পারে! কিন্তু ভাইপো সুরেশ, আর ভাইঝি স্মৃতিটুকুকে কেন যে উনি এভাবে বঞ্চিত করে গেলেন তার কোনও হদিশই কেউ বাতলাতে পারল না আজও।
বুড়ি মারা গেল কিসে?
—ঐ যে, ন্যাবারোগে। দু’তিন বছর ধরেই ভুগছিলেন। ডাক্তার দত্ত চেষ্টার ত্রুটি করেননি। বুড়ি শুধু সেদ্ধ খেত—ভাজা-টাজা একদম নয়।
* * * *
সুতৃপ্তিতে মধ্যাহ্ন আহার সেরে মামু বললে, চল চার্চটা দেখে আসি। এখনও দুটো বাজেনি। অগত্যা চার্চ দেখতে যেতে হল। রোমান ক্যাথলিক চার্চ। গথিক শৈলীর সঙ্গে ইন্ডো-স্যারানেসিক শৈলীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বাসুমামু সেসব নজর করলেন বলে মনে হয় না। উনি প্রবেশ করলেন সংলগ্ন সিমেটারিতে। পকেট থেকে নোটবই বার করে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। দু-একটা টুম্ব-স্টোনের তারিখ লিখে নিলেন খাতায়—যোসেফ হালদার, মেরী জনসন, সরলা এবং শেষমেশ মিস্ পামেলা জনসন :
SACRED
TO THE MEMORY OF
PAMELA HARRIET JOHNSON
DIED MAY 1.1970
“THY WILL BE DONE”
হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, পয়লা মে! চিঠি লিখেছিলেন সতেরই এপ্রিল। আর আজ উনত্রিশে জুন আমি তাঁর চিঠিখানা পেলাম। বুঝলে? সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার।
আমি বুঝলাম—সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার!
অর্থাৎ বাসুমামু যতক্ষণ না সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখে শান্ত হচ্ছেন ততক্ষণ আমাকে তার লগে-লগে থাকতে হবে। এই জুন মাসের খর-রৌদ্রতাপ অগ্রাহ্য করে!
মরকতকুঞ্জের বাগানের গেটে-এ এবার আর তালা ঝুলছে না। গাড়ি থামিয়ে আমরা এগিয়ে যেতেই একটি হিন্দুস্থানী লোক ওপাশ থেকে এগিয়ে এল। আউট-হাউস থেকে। গেট খুলে সসম্ভ্রমে বললে, আইয়ে সা’ব।
—তোম কৌন?
–ম্যায় ছেদিলাল সা’ব। বাগিচাকে দেখভাল করতে থে।
আউট হাউসের জানলা থেকে একটি অবগুণ্ঠনবতীকে দেখা গেল, ঘোমটা তুলে দুটি কাজলকালো কৌতূহলী চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত ছেদিলালের ঘরওয়ালী।
গেট থেকে আমরা তিনজনে প্রাসাদটির দিকে অগ্রসর হওয়ামাত্র ভেতর থেকে শোনা গেল পরিচিত সারমেয় গর্জন : কে বট তোমরা? ভেবেছ, আমাকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছে বলে যা ইচ্ছে নিয়ে পালাবে। সেটি হচ্ছে না…
ছেদিলাল বললে, ডরিয়ে মৎ সা’ব, ফিসি কিছু বোলবে না। বহু! আচ্ছা কুত্তা।
সদর দরজা খুলে একটি প্রৌঢ় বিধবা এগিয়ে এসে যুক্ত করে নমস্কার করে বললেন, আসুন। ভবানন্দবাবু টেলিফোনে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, আপনারা আড়াইটের সময় আসবেন।
বাসুমামুর সেই একই ট্যাকটিক্স! ‘আপনি ব্যক্তিটি কে?’–এই সিধাসাদা প্রশ্নটা না করে এমনভাবে সাজালেন যাতে বক্তা একটা প্রতিবাদের সুযোগ পায়, আপনিই বুঝি মিস্ মিনতি মাইতি?
—আজ্ঞে না। আমি শান্তি, মিস জনসনের পাচিকা ছিলাম। মিস্ মাইতি কলকাতায় থাকে। আসুন, ভিতরে আসুন। আমাকে ‘তুমিই বলবেন।
এবার সব জানলা খোলা। প্রচুর আলো-হাওয়া। ঘরদোর ঝক্ঝক্ তক্তক্ করছে। বাড়ির দেখভাল যারা করে তারা কাজে ফাঁকি দেয় না, এটা বোঝা যায়
এটা বৈঠকখানা, ড্রইংরুম আর কি।
প্রাচীনযুগের আসবাবপত্র। ভারী পর্দা। কাঁচের আলমারিতে শৌখিন পোর্সেলিনের পুতুল। প্রকাণ্ড ফুলদানি, ফুল নেই অবশ্য। বাসু-সাহেব প্রশংসা করলেন গৃহসজ্জার! বললেন, খুব ঝক্ঝক্-েতক্তকে করে সাজিয়ে রেখেছ তো?
–আমি নয়। ঘর-দোর ঝাড়-পৌঁছ করে সরযূ—ঐ ছেদিলালের বউ।
–আমি যদি বাড়িটা কিনি, তোমরা তিনজনে এখানে থেকে যাবে তো?
শান্তি একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। একটু ভেবে নিয়ে বলে, ছেদিলালেরা কী করবে তা ওদেরকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি আর চাকরি করব না। ম্যাডাম আমাকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেছেন, তারই সুদে আমার দিব্যি চলে যাবে। তবে লোকজন আপনি পেয়ে যাবেন। আমি বিশ্বস্ত লোক জোগাড় করে দেব।
—তা তোমার ম্যাডাম তো দু-মাস হল গত হয়েছেন, তুমি যদি আর চাকরি নাই করবে তাহলে এখানে পড়ে আছ কেন?
—মিস্ মাইতির অনুরোধে। ও বলল, গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে, এবার বাড়িটা বিক্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তা তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই, আমি রাজি হয়ে গেছি।
একটা জিনিস বাসুমামু খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমার নজরে পড়ছিল। মিনতি মাইতি আজ লক্ষপতি। কিন্তু মেরীনগরে কেউ তাকে তার প্রাপ্য সম্মানটা দিচ্ছে না। ভবানন্দ, সুতৃপ্তির বয় এবং এখন এই শান্তি—কেউই মিনতির প্রসঙ্গে ‘আপনি’ বলছে না। বোধ করি সেজন্যই মিনতি এই প্রাসাদটা জলের দামে বিক্রি করে কলকাতায় চলে যেতে চায়। কলকাতায় একটা মানুষের মর্যাদা তার আর্থিক সঙ্গতিতে।
কুকুরের গর্জনটা তীব্রতর হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। বাসুমামু আমাকে বললেন, কৌশিক, তুমি বসে পড় তো ঐ চেয়ারটায়। নিজেও বসলেন তিনি। শান্তিকে বললেন, এবার খুলে দাও কুকুরটাকে। ও আসুক। আমাদের শুঁকে দেখে শান্ত হোক।
শান্তি বলল, ঠিক বলেছেন। বাইরের লোক বসে থাকলে ও কখনও তেড়ে যায় না।
শান্তি কুকুরটাকে বন্ধনমুক্ত করে দিতেই সে তীরবেগে ছুটে এল। এখন আর সে ডাকছে না। আমাদের জুতো আর প্যান্ট ভাল করে শুঁকে দেখল। বাসুমামু একটা হাত বার করে বললেন, শুঁকে দ্যাখ্! এখনও চিকেন রোস্টের গন্ধ লেগে আছে।
কুকুরটা সত্যিই ওঁর হাতটা ভাল করে শুঁকে দেখল।
—কী নাম ওর? কত বয়স?
—ওর নাম ফ্লিসি। মাসছয়েক বয়স। ভারি বুদ্ধিমান। কাউকে কখনও কামড়ায়নি। ওর একমাত্র রাগ শুধু পোস্টম্যানের উপর। কেন যে পোস্টম্যানকে দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে, জানি না।
বাসুমামু বলেন, হেতুটা কিন্তু সহজবোধ্য। শোন, বুঝিয়ে বলি। তোমাকে বিচার করতে হবে কুকুরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সে দেখেছে বাড়িতে দু’জাতের লোক আসে। একদল চোর-ডাকাত। তাদের ও কিছুতেই ঢুকতে দেবে না বাড়িতে। চোর-ডাকাত ও চেনে না, দেখেনি—কিন্তু ওর ‘জিন’-এ আছে বংশানুক্রমিক নির্দেশ। স্পিৎজ হচ্ছে জার্মান শিকারী কুকুর। শত্রুকে মোকাবিলা করার নির্দেশ ওর রক্তে মজ্জাজাত। দ্বিতীয় আর এক জাতের মানুষ বাড়িতে আসে-যাকে সাদরে আহ্বান করা হয়। বসতে দেওয়া হয়। তারা গৃহস্বামীর বরণীয় ব্যক্তি। তাদের তেড়ে যেতে নেই। ওর সারমেয় দৃষ্টিতে পোস্টম্যান এমন একটা লোক যে, প্রায় প্রতিদিনই এসে বেল বাজায়—কিন্তু যাকে কোনওদিনই ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বসতে বলা হয় না। দোর থেকে তাকে বিদায় করা হয়। ফলে পোস্টম্যান হচ্ছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি!
শুধু শান্তি নয়, আমার কাছেও ব্যাখ্যাটা যুক্তিপূর্ণ মনে হল। বেশ বোঝা গেল কুকুরটা শান্তির প্রিয়। আমরা যে তাকে ভালবেসেছি এতে শান্তি খুশি হয়ে ওঠে, বলে, ওর দারুণ বুদ্ধি। বল নিয়ে এমন খেলে-
—গেণ্ডুক?
শান্তি বোধহয় ‘গেণ্ডুক’ শব্দটার অর্থ জানে না। বললে, না স্যার, গেণ্ডুক নয়, রবারের বল।
—কই দেখি! বলটা দেখি। ফ্লিসির কেরামতিটা দেখা যাক।
শান্তি একটু অবাক হল। তবু বৃদ্ধ খরিদ্দারের এই অহৈতুকী কৌতূহল চরিতার্থ করল সে। টানা ড্রয়ার থেকে রবারের বলটা বার করতেই সচকিত হয়ে উঠল ফ্লিসি। লাফাতে লাফাতে উঠে গেল সিঁড়ির মাথায়। শান্তি বলটাকে উপর দিকে ছুঁড়তেই লাফ দিয়ে লুফে নিল ফ্লিসি। বার তিনচার খেলাটা দেখিয়ে বলটাকে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।
ফ্লিসি শান্ত হয়ে সোফার নিচে শুয়ে পড়ল। শান্তি বললে, এ খেলাটা কিন্তু বেশ বিপজ্জনক।
—বিপজ্জনক! কেন? বিপদ কিসের?
—একবার সিঁড়ির মাথায় বলটাকে রেখে দিয়েছিল ফ্লিসি। তখন গভীর রাত। ম্যাডাম কী কারণে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন। ঐ বলে পা পড়তে এক্কেবারে নিচে গড়িয়ে পড়েন। ডাক্তার দত্ত বলেন, তাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারতো।
—সর্বনাশ! হাড়গোড় ভেঙেছিল নাকি?
—না! নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে। দিন সাতেকের মধ্যেই সামলে নিয়েছিলেন।
—অনেকদিন আগের কথা নিশ্চয়?
সেই একই ট্যাকটিক্স। শান্তি প্রতিবাদ করে, না, স্যার! অতি সম্প্রতি। তারিখটা পর্যন্ত আমার মনে আছে। এ বছরের ছয়ই এপ্রিল। কারণ তার পরদিনই ছিল ওঁর বাহাত্তরতম জন্মদিন। আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই হাজির—তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। জন্মদিন তো মাথায় উঠলো।
—ভগবান রক্ষা করেছেন! বেচারি ফ্লিসি জানেও না কত বড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। তা অত রাত্রে বৃদ্ধা নিচেই বা আসছিলেন কেন? একা-একা নিশ্চয়?
—হ্যাঁ একা-একাই! ব্যাপার কি জানেন, ম্যাডামের ঘুম না হওয়ার রোগ ছিল— ঐ যে ইনস্মিয়া না কি— যেন বলে। মাসের মধ্যে পাঁচ-সাত রাত তিনি ঐভাবে সারা বাড়ি পায়চারি করতেন। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো শেষ রাতে ঘুমোতে যেতেন। কিছুতেই ঘুমের ওষুধ খেতে চাইতেন না। সে যা হোক, আপনাদের আবার কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। আসুন ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।
নিচেকার ঘরগুলো দেখা শেষ হলো। তারপর উপরের ঘরগুলি। নিচে ড্রইং, ডাইনিং, স্টোর, কিচেন, প্যান্ট্রি, বাড়তি গেস্টরুম। শয়নকক্ষগুলি সবই দ্বিতলে—তাদের সব গালভারি নাম। মাস্টার্স বেড রুম, ওক-রুম, দোলনা ঘর ইত্যাদি।
সিঁড়ি দিয়ে আমরা দ্বিতলে উঠে আসি। ফ্লিসি কোনও আগ্রহ দেখালো না। একতলায় সোফার তলায় সে নিদ্রা দিচ্ছে। ধাপে ধাপে আমরা উপরে এসে পৌঁছাই। শেষ ধাপে পা দিয়ে বাসু-সাহেবের হাত থেকে কী যেন পড়ে গেল। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন সেই জিনিসটা। কিছুই নয়, ওঁর গাড়ির চাবিটা। একে একে ঘরগুলি দেখলাম। বাসু-মামুর কী খেয়াল হলো, বললেন, এই ওক-রুমটার মাপ নিয়ে দেখতো কৌশিক। আমার বুককেসগুলো সব আঁটবে কিনা পরখ করে দেখতে চাই।
পকেট থেকে তিনি বার করলেন একটা গোটানো স্টীল-টেপ, নোটবই আর কলম। আমি আর শান্তি দেবী ঘরটার মাপ নিলাম, উনি নোটবইতে লিখে নিলেন। মাপ নেওয়া শেষ হলে নোটবইটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, দেখ তো, মাপ ঠিক লেখা হয়েছে?
তাকিয়ে দেখি, নোটবইতে মাপ লেখা নেই আদৌ। বরং লেখা আছে ‘কোনও ছুতায় শান্তিকে একতলায় নিয়ে যাও। আমি মিনিট-পাঁচেক একা একা এখানে থাকতে চাই। শোন, ফোনটা নিচে আছে। সেই অজুহাতে শান্তিকে সরিয়ে নাও।
নোটবইটা ফেরত দিয়ে বলি, মাপ ঠিকই আছে। দুটো বুককেসই ধরে যাবে। তারপর শান্তির দিকে ফিরে বলি, এখান থেকে অনন্ত স্টোর্সে একটা ফোন করা যাবে? আমরা ফিরবার পথে ভবনান্দবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।
—কেন যাবে না। আমি ফোন করে বলে দেব? কটার সময়?
—না চলুন, আমিই যাই। দু-একটা কথা জানাবার আছে। আমাদের অ্যাড্রেসটাও দেওয়া হয়নি।
—বেশ তো, আসুন।
শান্তিদেবীর পিছন-পিছন আমি নিচে নেমে এলাম। টেলিফোনে কী বলবো, মনে মনে ছক্তে ছক্তে। সৌভাগ্য আমার, ভবানন্দ দোকানে নেই। তাঁর পুত্রটি ফোন ধরলো, বাবা কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন প্রভৃতি প্রতিটি প্রশ্নের জবাবেই তার ভদ্রলোকের-এক-এক কথা : জান্নে।
টেলিফোন নামিয়ে ‘হলে’ ফিরে এসে দেখি বাসুমামু নিচে নেমে এসেছেন। হল-কামরার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আত্মসমাহিত ভাবে।
আমাদের দেখে হঠাৎ শান্তিকে বলে ওঠেন, সিঁড়ির মাথা থেকে উল্টে পড়ে গিয়ে মিস্ জনসন নিশ্চয়ই একটা মানসিক আঘাত পান, শারীরিক তো বটেই। তিনি কি তখন ঐ ফ্লিসি আর তার বল-এর কথা কিছু বলেছিলেন?
শান্তি রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। বলে, আপনি কেমন করে জানলেন? হ্যাঁ, বিকারের ঘোরে প্রায়ই বলতেন ফ্লিসি আর তার বলের কথা। এমনকি মৃত্যুর আগে, মানে ঘণ্টাখানেক আগে তাঁর শেষ কথাটিও ছিল ঐ। তখন অবশ্য তিনি ঘোর বিকারে আবোল-তাবোল বকছিলেন। তাঁর শেষ কথা : ফ্লিসি… তার বল… চীনের মাটিতে ফুল দামি…’
—চীনের মাটিতে ফুল দামি!’ –তার মানে কী?
—কোনও মানে নেই! ও তো ঘোর বিকারের মধ্যে বলা কথা!
বাসু-সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাইপটা ধরিয়ে বললেন, আর একবার উপরে যেতে পারি কি? আমি ঐ মাস্টার্স বেডরুমটা আর একবার দেখতে চাই।
—আসুন না। দেখুন—
শান্তিদেবী পথ দেখিয়ে আবার দ্বিতলে আমাদের নিয়ে এলেন। গৃহকর্ত্রীর শয়নকক্ষে। বাসু-সাহেব দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা কাচের আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে কিছু শৌখিন পোর্সেলিনের খেলনা সাজানো। তার মাঝখানে একটি কাচকড়ার ফুলদানি। তাতে একটা বিচিত্র ছবি। রুদ্ধদ্বারের সামনে বসে আছে একটি কুকুর—নিচে লেখা : “Out all night and no key! ‘
বাসু-সাহেব বললেন, বিকারের ঘোরে তোমার কর্ত্রী ‘চীনের মাটিতে ফুল দামি বলেননি। হয়তো বলেছিলেন, ‘চীনেমাটির ফুলদানি…..’
শুধু শান্তি নয়, আমিও অবাক হয়ে যাই। বলি, একথা কেন বলছেন?
—মিস জনসন এ ঘরে থাকতেন। ঐ ফুলদানির ছবিটার কথা তাঁর মনে পড়েছিল। ওতে একটা ভিক্টোরিয়ান রসিকতার আভাস আছে। পোষা কুকুরটা বাড়ির বাইরে অভিসারে গেছিল আর তারপর সারা রাত বাড়ি ঢুকতে পারেনি। হয়তো ফ্লিসির ঐ জাতের বদভ্যাস আছে, তাই নয়?
শেষ প্রশ্নটা শান্তি দেবীকে। সে স্বীকার করলো, হ্যাঁ, মাসের মধ্যে দু-এক রাত সে পালিয়ে যেতো, সারা রাত বাইরে কাটাতো। ভোর রাতে ফিরে এসে বাড়ির সামনে কুঁইকুঁই করছিল। মিস্ মাইতি চুপিসাড়ে নেমে এসে সদর-দরজা খুলে ওকে ভিতরে আনে-
–চুপিসাড়ে? কেন? চুপিসাড়ে কেন?
—হ্যাঁ। পাছে কর্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। ফ্লিসির এই বাইরে যাওয়াটা ম্যাডাম একেবারে পছন্দ করতেন না। তাই মিস্ মাইতি আমাদের বারণ করে দিয়েছিল—আমরা যেন ওঁকে না জানাই যে দুর্ঘটনার রাত্রে ফ্লিসি সারারাত বাড়িতে ছিল না।
—আই সি! উনি খুব হিসাবী ছিলেন, তাই নয়?
—হ্যাঁ রোজ হিসাব রাখতেন। প্রতিদিন রাতে শোবার আগে দিনের খরচ লিখে রাখতেন। আবার কোনো কোনো বিষয়ে খুব ভুলো মানুষ ছিলেন তিনি। চিঠিপত্র লিখে পোস্ট করতে ভুলে যেতেন। এই তো দিন তিন-চার আগে আমি ওঁর তোশকের নিচে থেকে একটা চিঠি উদ্ধার করি। চিঠি লিখে, খাম বন্ধ করে, ঠিকানা লিখে তোশকের নিচে গুঁজে রেখেছিলেন।
ম্যাজিশিয়ান যে কায়দায় পকেট থেকে খরগোশ বার করে দেখায় প্রায় সেই ক্ষিপ্রতায় বাসু-সাহেব তাঁর পকেট থেকে একটি খাম বার করে বললেন, এই চিঠিখানা কি?
শান্তিদেবী বজ্ৰাহত হয়ে গেলেন।
—আপনি, আপনিই সেই পি.কে.বাসু?
—হ্যাঁ, তুমি আমার নাম শুনেছো?
—শুনেছি। কাঁটা-সিরিজের অনেক গল্পে—
—শোনো শান্তি। এই চিঠিতে মিস্ পামেলা জনসন আমাকে একটি গোপন তদন্ত করতে বলেছিলেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্য, চিঠিখানা তিনি সময়ে ডাকে দিতে ভুলে যান। তুমি এটা শুক্রবারে পোস্ট করেছো, আর আজ সোমবার আমি তা পেয়ে এখানে ছুটে এসেছি। ইতিমধ্যে মিস্ জনসন মারা গেছেন। আমি বুঝে উঠতে পারছি না, এক্ষেত্রে তদন্তটা আমার পক্ষে চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য কি না।
শান্তি একটু ভেবে নিয়ে বললে, আমি জানি স্যার, ব্যাপারটা কী! মানে কী বিষয়ে তিনি আপনাকে তদন্ত করতে বলতেন। কিন্তু সেসব তো চুকেবুকেই গেছে—
—কী বিষয়ে তদন্ত? তুমি কতটা কী জান?
—সামান্য ব্যাপার। পাঁচখানা একশ টাকার নোট চুরি যায়। কে নিয়েছে তা আমরাও আন্দাজ করেছিলাম, ম্যাডামও করেছিলেন, কিন্তু সে সময় আত্মীয়-স্বজনে ভরা বাড়িতে—
—কী ব্যাপার খুলে বল দিকিন?
শান্তি জানালো কীভাবে নোটগুলো খোয়া যায়। কাকে যে সন্দেহ করা হয়েছিল সে-কথা সে স্বীকার করল না কিছুতেই। বারে বারে একই কথা বলল—এ তদন্তের এখন আর কোনও মানে হয় না।
মরকতকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে বলি, মামু! এতক্ষণে আপনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন নিশ্চয়?
—হ্যাঁ, কৌশিক। আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।
—বাঁচা গেল। তাহলে কাল বাদে পরশু আমরা গোপালপুর যাচ্ছি? সব সমস্যা মিটে গেছে। ‘সারমেয় এবং তার গেণ্ডুক’–কেন চিঠিখানি ডেলিভারি হতে দু-মাস লাগল, কী তদন্ত তিনি আপনাকে করতে দিতেন, ইত্যাদি, প্রভৃতি! এবার কী? সোজা কলকাতা?
—না! তদন্ত আমার শেষ হয়নি এখনো।
মাঝ-সড়কেই দাঁড়িয়ে পড়ি, মানে! এই যে বললেন, আপনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন?
—তাই বলেছি। আমার স্থির সিদ্ধান্ত : মিস্ পামেলা জনসনের দুর্ঘটনার মূলে আর যাই থাক—’ফ্লিসি নামক সারমেয় এবং তার রক্তবর্ণের গেণ্ডুক’ নেই।
—তার মানে?
—তার মানে, আমি এমন একটি তথ্য জানি, যা তুমি জানো না এখনো —হুঁ! সেটা কী?
—মরকতকুঞ্জে কাঠের সিঁড়িতে, দোতলার ল্যান্ডিং-এর শেষ ধাপের কাছাকাছি স্কার্টিং-এ একটা পেরেক পোঁতা আছে! ধাপ থেকে নয় ইঞ্চি উঁচুতে!
ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কিছুই বোঝা গেল না। উনি অত্যন্ত গম্ভীর! বলি, বেশ তো! না হয় তাই আছে। তাতে কী হল?
–প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে একটা পেরেক পোঁতার কী হেতু থাকতে পারে?
—হাজারটা হেতু থাকতে পারে।
—তার একটা অন্তত আমাকে শোনাও। ল্যান্ডিং-এর কাছাকাছি, শেষ ধাপের সই-সই, দেওয়ালের দিকে, ধাপ থেকে নয় ইঞ্চি উঁচুতে পেরেক পোঁতার একটি সম্ভাব্য হেতু। শুধু তাই নয়, পেরেকের মাথাটা ভার্নিশ-করা, যাতে সহজে নজরে না পড়ে।
—আপনি কী বলতে চান? কে, কেন পুঁতেছে আপনি জানেন?
—’কে’ পুঁতেছে জানি না। ‘কেন’ পুঁতেছে জানি।
— কেন?
—সে রাত্রে ও বাড়িতে একাধিক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন যাঁরা বুড়ির মৃত্যু কামনা করছিলেন। কারণ বুড়ি তখনো দ্বিতীয় উইলটা করেনি। সকলেই তাঁর ওয়ারিশ। তারা জানতো, বুড়ি সারারাত পায়চারি করে। দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসে। বুড়িকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার সবচেয়ে সহজ পন্থা বাড়িসুদ্ধ সবাই শুয়ে পড়ার পর সিঁড়ির শেষ ধাপে আড়াআড়িভাবে একটা টোন সুতো বা তার বেঁধে দেওয়া। রেলিং-এর দিকে বাঁধাটা সহজ, কিন্তু দেওয়ালের দিকে সেটাকে শক্ত করে বাঁধতে হলে ওয়াল-বোর্ড এর গায়ে একটা পেরেক পুঁতে দিতে হবে। সহজে সেটা যাতে নজরে না পড়ে তাই তার মাথাটা ভার্নিশ করে দিতে হবে। আর ‘সারমেয় গেণ্ডুকটিকে সিঁড়ির ধাপে রেখে দিতে হবে।
—মাই গড! কী বলছেন আপনি?
—ইয়েস! এছাড়া ওখানে ঐ পেরেকের অস্তিত্বের আর কোনও ব্যাখ্যা নেই। মিস্ পামেলা জনসন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। পতনজনিত মৃত্যু হলে যা ঘটতো না, তাই ঘটলো। উনি ভাবতে বসলেন। দুর্ঘটনা ঘটে ছয় তারিখে, উনি চিঠি লেখেন সতেরো তারিখ। পাক্কা দশটা দিন তিনি শুধু ভেবেছেন, আর ভেবেছেন। হয়তো স্মরণে আনবার চেষ্টা করেছেন পতনের পূর্বমুহূর্তে পায়ের তলায় রবারের বলের স্পর্শের স্মৃতিটা। মনে পড়েনি—এ আমার আন্দাজ—শুতে যাবার আগে সারমেয় গেণ্ডুকটি তিনি ড্রয়ারে তুলে রেখেছিলেন। সেটা কেমনভাবে সিঁড়ির মাথায় এল—মাথায় না হলেও পাদদেশেই, এটা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফ্লিসি আনেনি—কারণ ফ্লিসি সেরাত্রে বাইরে ছিল। বোধ করি শেষ রাত্রে তার কুঁইকুঁই উনি স্বকর্ণে শুনেছেন—এটাও আমার আন্দাজ—তার তাতেই মৃত্যু সময়ে ওঁর মনে পড়েছে চীনে মাটির টবের ঐ ছবিটার কথা!
—হতে পারে, হতে পারে! কিন্তু—
—ভেবে দেখো, কৌশিক, চিঠিতে ভদ্রমহিলা বারে বারে বলেছেন গোপনতার কথা, বলেছেন, ‘বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করিতে আমার মন সরিতেছে না’—নিজের পরিবারে এই রকম একটা ডেলিবারেট মার্ডারার আছে একথা মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। অথচ আর কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাচ্ছিলেন না ঐ ‘সারমেয়-গেণ্ডুক’ সমস্যার। হয়তো বাকি যে-কটা দিন বেঁচে ছিলেন তার ভিতর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে সেই বিশেষ শয়তানটিকে তিনি চিহ্নিত করে যেতে পারেননি—কিন্তু সে যে ঐ দলে আছে, এটা স্থির নিশ্চয় বুঝেছিলেন। তাই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে।
আমি বলি, হয়তো তাই। কিন্তু এখন আর কী-করার আছে মামু?
—অনেক-অনেক কিছু! গোটা রহস্যটা উদ্ঘাটিত করতে হবে আমাকে। জানতে হবে–প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর হত্যাকারী কি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা করেনি?
আমি বাধা দিয়ে উঠি, নিশ্চয় নয়। উনি মারা গেছেন জনডিসে।
উনি আমার কথায় কর্ণপাত না করে বলে চলেন, জানতে হবে, মিস্ মাইতি কেন ‘চুপিসাড়ে’ ফ্লিসিকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিল, কেন সবাইকে বারণ করেছিল-কর্ত্রী যেন না জানতে পারেন, ফ্লিসি সে-রাত্রে বাড়িতে ছিল না।
—তার মানে আপনি কি বলতে চান…
—আমি কিছুই বলতে চাই না কৌশিক—এই স্টেজে—আমি শুধু শুনতে চাই; কিন্তু এ-কথাও তো ভুললে চলে না যে, সম্পত্তিটা লাভ করেছে মিস্ মিনতি মাইতি। যে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল ফ্লিসির অভিসার-বার্তা গোপন রাখতে! নয় কি?
আবার সব গুলিয়ে গেল আমার।
৯
নাটকের পরবর্তী দৃশ্য ডাক্তার পিটার দত্তের ডেরা।
—চল, দেখি তিনি কী বলেন। কী রোগে মিস্ জনসন ফৌত হলেন। একাধিক ব্যক্তি বলেছে রোগটা ‘জনডিস’–এই রোগে জীবনের শেষ তিনবছর কাবু ছিলেন বৃদ্ধা। কিন্তু সেকথা বাসুমামুকে বলতে যাওয়া বৃথা, কারণ আমি প্রমাণ করতে পারবো না যে, বক্তারা ধর্মপুত্র নয়। ডক্টর দত্ত থাকেন মেরী নগরে, কিন্তু তাঁর ক্লিনিকটি কাঁচড়াপাড়ায়। একটি পুরোনো আমলের ফোর্ড গাড়ি আছে; তাই চেপে তাঁতের মাকুর মতো তিনি এই পাঁচ-সাত মাইল পথ পাড়ি দেন নিত্যি ত্রিশদিন। নিজেই ড্রাইভ করেন। এখন বেলা চারটে, গেছো-দাদা কোথায় আছেন তা জানা নেই। মামু বললেন, টি-টাইম হয়ে গেছে; চল, সুতৃপ্তিতে গিয়ে এক-এক কাপ চা সেবন করা যাক। আর সেখান থেকে টেলিফোনে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যাবে। ডাক্তার মানুষ—চেম্বারে এবং বাড়িতে টেলিফোন থাকবেই।
ফিরে এলাম সুতৃপ্তিতে। হ্যাঁ, মামুর ডিডাকশান নির্ভুল—ডক্টর দত্তের চেম্বারে এবং বাড়িতে টেলিফোনের কানেকশন আছে! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সুতৃপ্তিতে তা নেই। তা হোক, আমাদের সেই চালাক-চতুর বয়টি জানালো ডাক্তার সাহেব চেম্বারে যান সন্ধ্যা ছয়টায়। অর্থাৎ এখন তাঁকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে। ওঁর বাড়ির পথ নির্দেশ দিয়ে দিল এবং ঐ সঙ্গে আরও কিছু সংবাদ পরিবেশন করলো।
ডাক্তার পিটার দত্ত সত্তরের উপর। কাঁচড়াপাড়ায় ওঁর ডাক্তারখানাটি বাস্তবে ক্লিনিক, প্যাথলজিক্যাল ইনভেস্টিগেটিং সেন্টার। রক্ত ও মলমূত্রাদির পরীক্ষা করা হয়, এক্স-রের ব্যবস্থাও আছে। দত্ত-সাহেব নিজে হাতে সব কিছু করেন না, বেতনভুক কর্মচারী আছে। উনি প্র্যাকটিসই করেন, শুধু সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টা-দুয়েক চেম্বারে গিয়ে বসেন। এই প্রসঙ্গে উঠে পড়লো ডাক্তারবাবুর দক্ষিণ হস্তের কথা—ডাক্তার নির্মল দত্তগুপ্ত। অল্প বয়স, মেধাবী। ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে—তবে রোগীপত্র দেখে না—সে নাকি ডাক্তারসাহেবের পরীক্ষাগারে কী সব পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে। বাসু মামু আকৃষ্ট হলেন যখন লোকটা বললো, ঐ নির্মল ডাক্তারের সঙ্গেই স্মৃতিটুকুর বিবাহ পাকা হয়ে আছে।
—তাই নাকি? তুমি কী করে জানলে?
—একথা কে না জানে? অ্যাত্তটুকুন শহর—সবাই সবার নাড়ির খবর রাখে।
—তাই বুঝি? তা মিস্ জনসনের চিকিৎসা ঠিক কে করতেন? ডাক্তার দত্ত, না কি নির্মল দত্তগুপ্ত?
—না স্যার। বুড়ি সেদিকে ট্যাটন। পিটার দত্তের প্রেসক্রাইব করা ওষুধ ছাড়া আর কিছু খেতো না।
—তার মানে?
লোকটা সামলে নিল নিজেকে। বললে, মানে ঐ আর কি।
সবাই সবার নাড়ির খবর রাখে! তার মানে কি ঐ লোকটাও আন্দাজ করেছিল, মিস্ জনসন শেষ জীবনে আতঙ্কগ্রস্তা হয়ে পড়েছিলেন? স্বীকার করলো না সে কথা।
ডাক্তার দত্ত বাড়িতেই ছিলেন। কলবেল বাজাতে তিনি নিজেই দ্বার খুলে আমাদের বললেন, ইয়েস? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়্যু?
বাসু-সাহেব হাত তুলে নমস্কার করলেন। বললেন, প্রথমেই বলে রাখি ডক্টর দত্ত, বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সাক্ষাৎ করতে এসেছি কোনও প্রফেশনাল কারণে নয়।
—শুনে সুখী হলাম। হ্যাঁ, আপনাদের দুজনের স্বাস্থ্যই ভাল। অসুখের লক্ষণ কিছু দেখছি না।
—আপনার সঙ্গে দু’চারটে কথা বলার আছে। যদি সময় না থাকে…
—বিলক্ষণ! আমার যথেষ্ট সময় আছে। আসুন, ভিতরে এসে বসুন। কলকাতা থেকে আসছেন? সোজা গাড়িতে?
—আজ্ঞে হ্যাঁ।
—আমার সঙ্গে দেখা করতে?
—আজ্ঞে না। আপনার কথা জেনেছি মেরীনগরে পৌঁছে।
আমরা ওঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসি। গৃহস্বামী ফ্যানটা খুলে দিয়ে বসলেন। বলেন, এবার বলুন?
আমার নাম টি. পি. সেন। আমি একজন সাংবাদিক–ফ্রি-লাগ জার্নালিস্ট আর কি। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমি যোসেফ হালদারের একটি জীবনী লিখছি। তাই এসেছিলাম এখানে। মরকতকুঞ্জে গেছিলাম–কী আপসোসের কথা! কেউ কিছু বলতে পারছে না। আপনি মেরীনগরের একজন ‘প্রাচীন সম্মানীয় সিটিজেন, তাই…
ডাক্তার দত্ত আকাশ থেকে পড়লেন। আমিও। মুহূর্তকাল পূর্বেও আমি অনুমান করতে পারিনি যে, রিটায়ার্ড নেভাল অফিসার কে. পি. ঘোষ ইতিমধ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন টি- পি. সেন-এ! ডাক্তার দত্তের বিস্ময় অন্য জাতের। কোনওক্রমে বলেন, এ তো আজব কথা শোনালেন মশাই! অফ্ অল পার্সেন্স আপনি এতদিন পরে যোসেফ হালদারের জীবনী লিখতে বসেছেন কেন? ব্যাপারটা কী?
—উনি বিদেশ থেকে বিদেশী স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন একথা নিশ্চয় জানেন; কিন্তু তাঁর পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে আপনার?
—আদৌ না। উনি কোন দেশ থেকে এসেছিলেন তাই তো জানে না কেউ?
—না! কেউ জানে না। উনি বোধ হয় 1914-এ ভারতে ফিরে আসেন? নয়? তা হবে। হ্যাঁ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে, এটুকুই শুনেছি।
—আপনি ‘কোমাগাতামারু’ নামটা শুনেছেন?
—‘কোমাগাতামারু’? হ্যাঁ, মনে পড়ছে—একটি জাপানী জাহাজের নাম। কী যেন হয়েছিল?
—আজ্ঞে, হ্যাঁ। জাহাজটিতে চেপে অনেক পাঞ্জাবী শিখ আমেরিকা আর কানাড়া থেকে ভারতে ফিরে আসে। ‘এমিগ্রেশন’ আইন পাশ করে ঐ শিখ শ্রমজীবীদের ধনেপ্রাণে মেরে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। জাহাজটা যখন বজবজে এসে নোঙর করল তখন বৃটিশ পুলিস চাইলো সবাইকে বন্দী করতে। স্পেশাল ট্রেনে করে বন্দীদের পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু সর্দার গুরুজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে কলকাতার দিকে রওনা দেয়। বাধা দিল পুলিস। শুরু হয়ে গেল লড়াই। গদর-বিপ্লবীরা ঐ শিখ যাত্রীদের কিছু পিস্তল সরবরাহ করেছিল—কিন্তু রাইফেলের সঙ্গে পিস্তলের লড়াই চলে না। বহু শিখযাত্রী হতাহত হল। পুলিসের পক্ষেও দু’জন বৃটিশ অফিসার এবং তিনজন পুলিস মারা যায়। যাত্রীদের ষাটজনকে গ্রেপ্তার করে পাঞ্জাবে পাঠানো হয়; কিন্তু গুরুজিৎ সিং পালিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে পালিয়ে যান। যার মধ্যে একজনের নাম যোসেফ হালদার।
—মাই গড! কিন্তু আপনিই তো বললেন যে, ঐ জাহাজের যাত্রীরা ছিল নিঃস্ব। সেক্ষেত্রে যোসেফ হালদার অত সম্পদ পেলেন কী করে?
—ডক্টর দত্ত! সেটাই আমার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু! কিন্তু ব্যাপারটা মোস্ট কনফিডেনশিয়াল!
সেটা সহজেই বোঝা যায়! তা বেশ, আপনি কী জানতে চান বলুন? আমি যোসেফ হালদারকে ছেলেবেলায় দেখেছি। তিনিই এই মেরীনগরের প্রতিষ্ঠাতা। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মেরীনগরের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে একজন। যোসেফ হালদারের বড় মেয়ে পামেলা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। আমরা একসঙ্গেই পড়াশুনা করেছি মিশনারি স্কুলে। সে আমার বাল্যবান্ধবী।
—যোসেফের সন্তানাদি কী?
ডক্টর দত্ত হালদার-পরিবারের নানান তথ্য পরিবেশন করতে থাকেন। আমার পক্ষে সেসব কথা দ্বিতীয়বার বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ পাঠককে আমি তা ইতিপূর্বেই জানিয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে ডক্টর দত্ত বললেন, মরকতকুঞ্জে পুরোনো কাগজপত্র আপনি কিছুই খুঁজে পাবেন না। পামেলার মৃত্যুর পর মিন্টি সব বাজে কাগজপত্র ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে।
বাসু-মামু ন্যাকা সাজলেন, মিন্টি কে?
ফলে আবার শুনতে হল একই ক্লান্তিকর ইতিহাস। সেই সূত্র থেকে মামু প্রশ্ন করবার সুযোগ পেলেন সুতৃপ্তিতে একটা গুজব শুনলাম, অবশ্য গুজবে কান না দেওয়াই উচিত—ওঁর শেষ জন্মদিনে নাকি আত্মীয়স্বজনেরা সবাই জড়ো হয়েছিল, তখনই হয়তো কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়ে থাকবে যেজন্য দ্বিতীয় উইল না করে-
—না না! অপ্রীতিকর ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি। পামেলা সে রকম মেয়ে ছিল না। হলে, আমি খবর পেতাম–মেরীনগর ছোট্ট জায়গা। ওর বাড়ির ঝি-চাকরেরা সেকথা রটিয়ে বেড়াত। তাছাড়া পামেলার মৃত্যুর দিন-সাতেক আগে আমি একটি ট্রেইনড নার্সকে বহাল করেছিলাম। মৃত্যু সময়েও সে ছিল। তেমন কিছু ঘটে থাকলে আমি আশার কাছে খবর পেতাম।
—আই সি! তাহলে সেই সহচরী— কী যেন নাম— হাঁ মিনতি মাইত—সেই হয়তো সুযোগ বুঝে কর্ত্রীকে দিয়ে নতুন একখানা উইল বানিয়ে নিয়েছে! বাহাত্তর বছরের একটি মৃত্যুপথযাত্রিণীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে-
কথাটা শেষ করতে দিলেন না ডক্টর দত্ত। মাঝপথেই বলে ওঠেন, আপনি ওদের দুজনের একজনকেও চেনেন না, তাই একথা ভাবতে পারছেন। পামেলা জনসনকে আমি ষাট বছর ধরে চিনতাম। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সই করানোর ক্ষমতা দুনিয়ায় কারো নেই। দ্বিতীয়ত মিন্টি মাইতি একটা নিটোল গবেট—নিনকপূপ! বুঝেছেন? তার মাথায় নিরেট গোবর। এমন একটা পরিকল্পনার কথা তার মাথাতেই আসবে না।
বাসু বললেন, দুনিয়ায় কত রকম রহস্যই তো অনুদ্ঘাটিত থেকে যাচ্ছে। আর তা নিয়ে আমাদের কেন মাথা-ব্যথা বলুন?
—বটেই তো, বটেই তো!
—আপনি ঐ তিনজনের ঠিকানা আমাকে দিতে পারবেন? সুরেশ, স্মৃতিটুকু আর হেনার?
—বৃথা চেষ্টা! ওরা পুরোনো কথা কিছুই জানে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। আপনি বরং আর এক কাজ করতে পারেন। ঊষা বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সে এখানেই থাকে। পামেলার বান্ধবী। পারলে সে হয়তো কিছু বলতে পারবে।
ঊষা বিশ্বাসের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বাসু বললেন, হয়তো তাঁর কাছে সুরেশ বা হেনার ঠিকানাটা পেয়ে যাব।
—সুরেশ বা হেনার ঠিকানা না দিতে পারলেও টুকুর ঠিকানাটা বোধ হয় আপনাকে দিতে পারবো। নির্মল জানে।
—নির্মল কে?
সুতৃপ্তিতে শ্রুত সন্দেশটি করবরেটেড হল। ডাক্তার দত্ত তাঁর চেম্বারে ফোন করলেন, কিন্তু নির্মল দত্তগুপ্তকে পাওয়া গেল না। ও-প্রান্ত থেকে ওঁকে জানালো—কী একটা জরুরি প্রয়োজনে নির্মল সাইকেলে চেপে ওঁর কাছেই আসছে।
ডক্টর দত্ত বললেন, মিনিট পাঁচ-দশেকের মধ্যেই নির্মল এসে যাবে। একটু বসে যান।
তাই এল নির্মল দত্তগুপ্ত। বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স। স্মার্ট, সুদর্শন। পিটার দত্ত তার সঙ্গে সাংবাদিক টি. পি. সেনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেন-মহাশয় যোসেফ হালদারের জীবনী লিখতে ইচ্ছুক একথা শুনে তার চোখ কপালে উঠলো। ‘কোমাগাতামারুর প্রসঙ্গটা উল্লেখিত না হওয়ায় ব্যাপারটা হয়তো তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল। আমাদের দুজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, সুরেশের ঠিকানা আমি জানি না। তবে টুকুর ঠিকানা জানি, সে নিশ্চয় তার দাদার পাত্তা জানে।
নির্মল একটি কাগজে স্মৃতিটুকুর ঠিকানা লিখে বাড়িয়ে ধরল। মামু তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গাত্রোত্থান করলেন।
বাইরে বেরিয়ে এসে আমি বললুম, মামু, ‘কোমাগাতামারু’ সম্বন্ধে আপনি যেসব ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার্স বললেন, তা সত্যি?
—শিওর! ডক্টর দত্ত দু-চারদিনের ভিতরেই লাইব্রেরি থেকে বই এনে ভেরিফাই করবে। আমাকে সন্দেহ করেছে বলে নয়, মেরীনগরের প্রতিষ্ঠাতার কোনও হক-হদিশ পাওয়া যায় কিনা যাচাই করতে। আমি যা বলেছি তা ঐতিহাসিক সত্য। তবে ঐ—ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন সামান্য একটু ভেজাল থাকে, এখানে তেমনি আছে যোসেফ হালদারের নামটা।
—হঠাৎ দুইয়ে দুইয়ে চার বানিয়ে ফেললেন কী করে?
—যেহেতু যোসেফ হালদার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে ভারতে ফিরে এসেছিলেন, এ খবরটা শুনলাম।
—ডক্টর দত্ত আপনাকে সন্দেহ করবে না কেন বললেন?
—সন্দেহ করার কী আছে? এমনটা তো নিত্যি ঘটছে। একদল গণ্ডমূর্খ আর একদল গণ্ডমূর্খের জীবনী ক্রমাগত লিখছে।
আমি হেসে ফেলি। বলি, মামু! কথাটা কিন্তু আপনার নিজের তরফে ‘কমপ্লিমেন্টস্’ হলো না।
বাসু-মামু চকিতে আমার দিকে চাইলেন। বললেন, উল্টোটাও হলো না। আমি যোসেফ হালদারের জীবনী আদৌ লিখছি না। সেটা লিখছে টি. পি. সেন।
আমি বলি, কিন্তু ডাক্তার দত্তগুপ্তের চোখে আমি যে দৃষ্টি দেখেছি তাতে আশঙ্কা হয়, সে আপনাকেই সন্দেহ করছে, টি. পি. সেনকে নয়!
—ও ছোকরা স্বভাবগতভাবে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত।
—তা যেন হলো। অতঃ কিম্?
—আর অবিশ্বাসীদের কাছে নয়। এবার আমাদের লক্ষ্যস্থল : ঊষা বিশ্বাস।