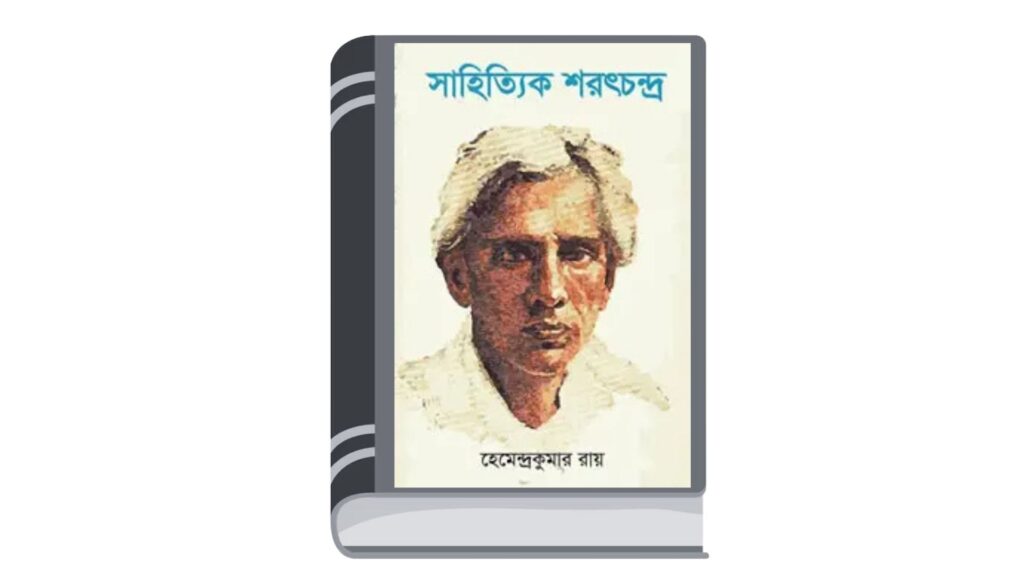মধ্যকাল (১৮৯৭–১৯১৩)
আমরা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকেই অল্পের মধ্যে যতটা সম্ভব ভালো করে দেখতে চাই। কিন্তু এখন আমরা শরৎচন্দ্রের জীবননাট্যের যে-অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে দারিদ্র্যের বেদনা, মানসিক অস্থিরতা, পিতৃশোক ও জীবনের লক্ষ্যহীনতা প্রভৃতির জন্যে কাতর এমন একটি মানুষকেই বেশি করে দেখতে পাই, যার মধ্যে সাহিত্যপ্রতিভা ছাইচাপা আগুনের মতো প্রায়-নিস্ক্রিয় হয়ে আছে। এর প্রথম দিকটায় মাঝে মাঝে অনুকূল হওয়ায় ছাই উড়ে আগুনের দীপ্তি বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কলমের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে তুলে দেননি বটে, কিন্তু তারপরেই তার লেখাটেখা বহুকালের জন্যে ধামাচাপা পড়ে। এই সময়টায়—তার নিজের কথায়—শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন যে, কোনওকালে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন।
বাংলাদেশের আর কোনও সাহিত্যিক এমন দীর্ঘকাল সাহিত্যকে ভুলে থেকে আবার সহসা আত্মপ্রকাশ করে পরিপূর্ণ মহিমায় সকলকে অবাক করে দিতে পারেননি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর তুলনা দুর্লভ। এমন সাহিত্যিকের অভাব নেই, যারা প্রথম জীবনে অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও জনতার অভিনন্দন পেয়ে আচম্বিতে সাহিত্যধর্ম ত্যাগ করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন, আর দেখা দেননি। যেমন ফরাসি কবি Arthur Rimband; তার সতেরো বছর বয়সের সময়ে সারা ফ্রান্স তাকে অতুলনীয় প্রতিভাবান বলে অভ্যার্থনা করেছিল, কিন্তু সাহিত্যসমাজের দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে কলম ছুড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি সরে পড়লেন; চলে গেলেন একেবারে আবিসিনিয়ায়; এবং বাকি জীবন ব্যবসায়ে মেতে আর কবিত্বের স্বপ্ন দেখেননি।
কিন্তু আমরা একজন কবিকে জানি, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যার তুলনা করা চলে। তিনিও জাতে ফরাসি, নাম Paul valery। বিশ বৎসর বয়সে কবিযশোপ্রার্থ হয়ে পারি শহরে এলেন। তার অসাধারণ কবিত্ব দেখে জনকয়েক রসিক সাহিত্যিক তাকে খুব আদর করতে লাগলেন। কিন্তু Valery কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করলেন যে, শরীরী মানুষের পক্ষে কবিত্বের চেয়ে অভাবের তাড়না ও পেটের দায় হচ্ছে বড়ো জিনিস। তিনি ছিলেন Stephane Malarme-র মতন সেই শ্রেণীর কবি, কবিতা পড়ে লোকে সহজে বুঝতে পেরে সুখ্যাতি করলে র্যারা খুশি হতেন না! সুতরাং কবিতা লিখে অন্নসংগ্রহের উপায় নেই দেখে Valery হঠাৎ একদিন ডুব মারলেন।…বছরের পর বছর যায়, Valery-র কোনও পাত্তা নেই। যে দু চারজন কবিবন্ধু তাঁকে ভোলেননি তাঁরা অবাক হয়ে ভাবেন, কবি নিরুদ্দেশ হয়েন কোথায়? অদৃশ্য না হলে এতদিনে না জানি তার কত যশই হত! কিন্তু কেউ খবর পেলে না যে, Walery তখন কোনও ব্যবসায়ীর সেক্রেটারিরূপে অজ্ঞাতবাস করছেন এবং অবসরকালে করছেন কাব্যের বদলে গণিতবিজ্ঞানের চর্চা!
সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কেটে গেল! তারপর আচম্বিতে একদিন ফরাসি সাহিত্যক্ষেত্রে কবি Valery-র পুনরাবির্ভাব! এখন তিনি আধুনিক ফরাসি সাহিত্যে একজন অমর কবিরূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর এক টুকরো কবিতার নমুনা হচ্ছে এই
The Universe is a blemish
In the purity of Non-being.
শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে অতটা না মিললেও, ফরাসি গল্প ও উপন্যাস লেখক গী দে মোপাসার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। ফ্লবেয়ারের অধীনে অপূর্ব ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল অপ্রকাশ্যে শিক্ষানবিসি করে মোপাসা একটিমাত্র গল্প নিয়ে প্রথম যেদিন আত্মপ্রকাশ করলেন, বিখ্যাত হয়ে গেলেন সেই দিনই। তারপর মাত্র দশ-বারো বৎসর লেখনী চালনা করেই মোপাসাঁ নিজের বিভাগে বিশ্বসাহিত্যে আজও অমর এবং অদ্বিতীয় হয়ে আছেন!
সাধারণত যেসব উদীয়মান সুলেখক হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিয়ে কার্যাস্তরে মন দেন, দীর্ঘকাল পরে কলম ধরলেও অনভ্যাসের দরুন আর তারা ভালো লিখতে পারেন না। সেই জন্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে এসব লেখকের পুনরাগমন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর একজন লেখককে আমরা বহুকাল পরে উৎসাহিত করে কলম ধরিয়েছিলুম। যে-বৎসরে যমুনা’ পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের বিন্দুর ছেলে প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরেই এবং ওই কাগজেই আমরা প্রকাশ করেছিলুম তার একাধিক রচনা। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার পুনরাগমন সফল হল না। অথচ পুরাত ‘ভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি যখন সাহিত্যসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তখন সকলেই জানত, তিনি একজন খুব বড়ো লেখক হবেন। আমরা তার নাম করলুম না, কারণ তিনি হয়তো এখনও ইহলোকেই বিদ্যমান।
কিন্তু আগেই দেখিয়েছি, শরৎচন্দ্র ওই-শ্রেণীর লেখকদের দলে গণ্য হতে পারেন না। সমসাময়িক সাহিত্যসমাজ থেকে নির্বাসিত ও জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি লেখনীত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার চিন্তাশীল মন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেনি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের— বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের—রচনা বরাবরই তার বুভূক্ষু মস্তিষ্কের খোরাক যুগিয়েছে। অর্থাৎ তিনি কলমই ছেড়েছিলেন, সাহিত্যকে ছাড়েননি। মন ছিল তার সক্রিয়। এবং মনই করে সাহিত্যসৃষ্টি।
সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যখন থেকে মানুষ শরৎচন্দ্রে পরিণত হতে বাধ্য হলেন, তার তখনকার কার্যকলাপ খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে। বেশি কথা বলবার মালমশলাও আমাদের হাতে নেই।
নানাকারণে তাদের আত্মসম্মানে বারংবার আঘাত লাগায় পিতার সঙ্গে ভাগলপুর ছেড়ে শরৎচন্দ্র খঞ্জরপুর, তারপর অন্যান্য জায়গায় যান—চাকরির সন্ধানে। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ ছিল, তিনি সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী! বই পড়তে ভালোবাসেন, লেখার অভ্যাস আছে, নকশা আঁকেন, ফুলের মালা গাথেন, অথচ টাকা রোজগার করতে পারেন না! শ্বশুরবাড়িতে তাই গরিব ও বেকার জামাইয়ের আর ঠাই হল না। এবং সংসারে এইটেই স্বাভাবিক। ভাগলপুরের আত্মীয়-আলয়ে মতিলাল ও শরৎচন্দ্রের অনেক নির্যাতনের কাহিনি আমরা শুনেছি, কিন্তু এখানে তার উল্লেখ করে কাজ নেই। তার পরের কথা শ্ৰীমতী অনুরূপা দেবীর ভাষাতেই শুনুন। তখন হাতে-লেখা খাতায় বা মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি রচনা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন
‘হঠাৎ একদিন আমার স্বামীর মুখে শুনিলাম, সেই অপ্রকাশিত লেখার লেখক মজঃফরপুরে আমাদের বাসায় অতিথি। আমি সে সময় ভাগলপুরে। আমার স্বামী আমার মুখেই ইতিপূর্বে শরৎবাবুর লেখার প্রশংসা শুনিয়াছিলেন, তাই নাম জানিতেন। মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তার খুব শখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন, ‘একটি বাঙালি ছেলে অনেক রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায় অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারি বলেই পরিচয় দিলেন; কিন্তু লোকটি বাঙালিই, একদিন গান শুনবে? নিয়ে আসব তাকে?’
‘বাড়িতে সন্ধাবেলা এক একদিন গান-বাজনার আসর বসিত। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসে, ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়িতে অতিথিরূপে এখানেই ছিলেন। কি জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু তখন তাহার অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতোই ছিল। সে সময় তিনি কিছু নূতন রচনা না করিলেও তাহার যে ফুটনোন্মুখ প্রতিভা তাঁহার মধ্যে অপেক্ষা করিয়ছিল তাহা তাঁহার ব্যবহারকেও অনেকখানি সৌজন্যমণ্ডিত এবং আকর্ষীয় করিয়া রাখিত। শ্ৰীযুক্ত শিখরনাথবাবু এবং তাহার বন্ধুবৰ্গ তাহার সহিত কথাবার্তায় বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহার পরিচয় এখনকার লেখক শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ পরিচিত লোকও অবগত নন। অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিখরবাবুর বাড়ি থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যান। এই মহাদেব সাহুই ‘শ্ৰীকান্তের’ কুমার সাহেব তাহাতে সন্দেহ নাই। মজঃফরপুর হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও শরৎচন্দ্র শিখরনাথবাবুকে বার কয়েক পত্র দিয়াছিলেন। তাহার পর আর বহুদিন তাহার সংবাদ জানা যায় নাই। পরে শ্ৰীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রমুখাৎ শুনি তিনি বৰ্মা চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যে সেখানে তাহার মৃত্যুসংবাদও রটিয়াছিল।’
অসাধারণ মানুষ শরৎচন্দ্রের তখনকার যে-ছবিটি কল্পনায় আসছে, তা হচ্ছে এই রকম। একটি রোগাসোগা কালো যুবক, চোখে শ্রান্ত স্বপ্নবিলাসের ছাপ আছে, চেহারায় ও কাপড়েচোপড়ে পারিপাট্য নেই, লাজুক অথচ মিষ্টভাষী, মাঝে মাঝে সাহিত্য-আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, খোসগল্পেও সুপটু, কিন্তু ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগলে হন বজের মতন কঠিন, আত্মপরিচয় দিতে নারাজ, সর্বাঙ্গে ফোটে আলাভোলা বৈরাগ্যের ভাব, পরদুঃখে কাতর, পরসেবায় তৎপর, সুকণ্ঠ, বাঁশি ও তবলায় দক্ষ এমন একজন মানুষ যে সকলের প্রিয় হয়ে উঠবেন, এটা আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু একে অপমান করতে গেলে সাহসীকেও আগে ভাবতে হয়!
মহাদেব সাহুর কাছে কাজ করবার সময়ে শরৎচন্দ্রের শিকারেরও শখ হয়। অবসরকালে প্রায়ই তিনি বন্দুক হাতে করে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রের মনের কোথায় খানিকটা যে ক্ষত্রিবীর্য ছিল, সেটা পরেও লক্ষ করা গেছে। যখন রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, সেই পরিণত বয়সেও পকেটে তিনি ধারালো বড়ো ছোরা রেখে পথে বেরিয়েছেন। একথা সত্য কি না জানি না, তবে কেউ কেউ লিখেছেন শরৎচন্দ্ৰ নাকি সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি করেই রেঙ্গুনের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কাহিনি আমরা শরৎচন্দ্রের মুখে শুনিনি। তবে সশস্ত্র থাকবার দিকে তার একটা ঝোক ছিল বরাবরই। বৃদ্ধবয়সেও—ছোরা ত্যাগ করলেও—এমন এক ভীষণ মোটা লগুড় হাতে নিয়ে নিরীহ বন্ধুদের বৈঠকখানায় এসে বসতেন, যার আঘাতে বন্য মহিষও বধ করা যায়!
১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় আসেন। কলকাতার ভবানীপুরে থাকতেন র্তার সম্পর্কে মামা উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি বিচিত্রা সম্পাদক শ্ৰীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা। হিন্দি কাগজপত্র অনুবাদ করবার জন্যে তার একজন লোকের দরকার হয়েছিল। ভাগিনেয় শরৎচন্দ্র সেই কাজটি পেলেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতৃদেব স্বৰ্গারোহণ করেন। তখনও তার পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করবারও সময় আসেনি। চির-গরিব বাপ, ছেলেকেও দেখে গেলেন দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত পরাশ্রিত অবস্থায়। অথচ এমন ছেলের জন্মদাতা তিনি।
এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প আছে। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো সম্পর্কে-মামা, অথচ বন্ধুস্থানীয় কারুর কারুর শখ হয়েছিল তাঁরা একটি হারমোনিয়াম কিনবেন। অথচ সকলেরই ট্যাঁক গড়ের মাঠ। অতএব সকলে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলেন। বক্তব্যটা এই; তুমি আমাদের একটা গল্প লিখে দাও, আমরা সেটা কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠাব। পুরস্কার পেলে আমাদের হারমোনিয়াম কেনবার একটা উপায় হয়! দেখা যাচ্ছে, তখনই ওঁদের মনে ধারণা ছিল যে, শরৎচন্দ্র গল্প লিখলে সেটি পুরস্কৃত হবেই।
শরৎচন্দ্রের তখন নাম হয়নি। এবং তিনিও তখন নিজের লেখাকে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না। তবু নিজের নামে প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠাতেও তার আত্মসম্মানে বাধে। তাই সকলের সুদৃঢ় অনুরোধে সেইদিনই তাড়াতাড়ি ‘মন্দির’ নামে একটি গল্প লিখতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু লেখকরূপে নাম রইল শ্ৰীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের।
গল্পটি প্রতিযোগিতায় হল প্রথম এবং এই হল আত্মীয়-সভার বাইরে শরৎপ্রতিভার প্রথম সফল পরীক্ষা ও প্রথম গৌরবজনক আত্মপ্রকাশ! কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার আগে ওই মন্দিরই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের শেষ-রচনা!
শুনেছি, ভবানীপুরেও আত্মীয়-আলয়ে শরৎচন্দ্র নিজের মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণ বলে মনে করতে পারেননি—প্রায়ই প্রাণে তার আঘাত লাগত। শেষটা নিতান্ত মনের দুঃখেই তিনি আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সাগর পার হয়ে গেলেন একেবারে অজানা দেশ রেঙ্গুনে। এত দেশ থাকতে ওই সুদূর প্রবাসে গেলেন যে তিনি কোন ভরসায়, সেটা প্রথম দৃষ্টিতে রহস্যময় বলেই মনে হয়। তবে শুনেছি, তার আত্মীয়-সম্পৰ্কীয় ও রেঙ্গুনপ্রবাসী স্বর্গীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু হঠাৎ এসে তার পথ থেকে এ বান্ধবটিকেও সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বিশ্বাস, এই দুঃসময়ে শরৎচন্দ্র কোনও আত্মীয়হীন দেশে গিয়ে নূতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মনে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব ছিল না, সেটা বলা বাহুল্য। তার উপরে তার ভিতরে ছিল শিল্পীর ভাবপ্রবণতা। সাধারণ লোকের মতো আত্মীয়-বন্ধুদের অবহেলা অনায়াসে সহ্য করবার ক্ষমতা তার মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। আগে তার মতো অনেক বেকার দরিদ্রই যেতেন ব্রহ্মদেশে ভাগ্যান্বেষণে। নিজের দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিয়ে তিনিও যখন সেই পথ অবলম্বন করে রেঙ্গুনে গিয়ে হাজির হন, তার সম্বল ছিল নাকি মাত্র দুই টাকা! এবং ওই দুই টাকা ফুরিয়ে যেতেও দেরি লাগেনি। তখন রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালিরা কিছুদিন শরৎচন্দ্রের অভাব মেটালেন, কারণ লোকের স্নেহ-শ্রদ্ধা আকর্ষণ কুরতে পারতেন তিনি খুব সহজেই। তারপর সওদাগরি অফিসে তার সামান্য মাহিনীর একটি চাকরি জুটল। তার তখনকার অসহায় অবস্থার পক্ষে সেই কাজটিও বোধ করি যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল!
কিছুদিন পরে তিনি ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেলের অফিসে একটি কাজ পেলেন। এখানে চাকরি ছাড়বার আগে তার মাহিনী একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।
এই রেঙ্গুন-প্রবাসের সময়ে শরৎচন্দ্রের মনের বৈরাগ্য বোধহয় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কারণ তার সংসারী হবার সাধ হল এবং তাঁর সে সাধ পূর্ণ করলেন শ্ৰীমতী হিরন্ময়ী দেবী। কিন্তু এর আগেই তিনি একটি মেয়েকে কুপাত্রের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে বিবাহ করে নিজের মহত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই বিবাহের ফলে লাভ করেছিলেন একটি পুত্রসন্তান। কিন্তু দুৰ্দান্ত প্লেগ এসে তাদের সেই সুখের সংসার ভেঙে দেয় এবং শরৎচন্দ্র হন আবার একাকী!
আমাদের এক নিকট-আত্মীয় রেঙ্গুনে ডাক্তারি করেন। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তারই মুখে শুনেছি, রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালি-সমাজে শরৎচন্দ্র খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। গানে-গল্পে তিনি সকলকেই মোহিত করতেন। সেখানে গান, গল্প, বইপড়া, ছবি আঁকা আর চাকরি ছাড়া তার জীবনের যে আর কোনও উচ্চ লক্ষ্য আছে বাহির থেকে দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারত না। শরৎচন্দ্রের এই আর একটা বিশেষত্ব ছিল; মনে মনে নিজেকে তিনি যত আলাদা করেই রাখুন, বাহিরে আর দশজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যেতে পারতেন। এ বিশেষত্ব রঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, সাধারণ মানুষ তাকে দূর থেকে নমস্কার করত। রবীন্দ্রনাথও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারেন না। শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসী বন্ধু শ্ৰীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার অধুনালুপ্ত ‘বাঁশরী’ পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম ‘ব্ৰহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র’। ওই লেখাটিতে ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ গল্পের সঙ্গেই শিল্পী বা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বিশেষ সম্পর্ক নেই বলে কেবল গল্পের খাতিরে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতরে তাদের আর টেনে আনা হল না।
তবে শরৎচন্দ্রের জীবনীকথা হিসাবে, ব্রহ্মদেশের দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। যদিও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে সাধ্যমতো আত্মগোপন করে চলতেন, তবু অবশেষে রসিক লোকেরা তাকে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তার ফলে বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সভ্যদের প্রবল অনুরোধে শরৎচন্দ্রকে আবার অস্ত্র ধরতে হয়। তিনি ‘নারীর ইতিহাস’ নামে সুবৃহৎ এক প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রকাশ্য সভায় লেখাটি তার পড়বার কথা ছিল এবং সভার মধ্যিখানে শরৎচন্দ্র ছিলেন চিরদিনই কাপুরুষ’—মসীবীর হলেই যে বাকবীর হওয়া যায় না তারই মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। অতএব প্রবন্ধটি সভার জন্যে বাসায় রেখে, লেখক পড়লেন কোথায় সরে! যা-হোক প্রবন্ধটি সভায় পঠিত হয় এবং শরৎচন্দ্রের নামে ধন্য-ধন্য রব পড়ে যায়!
শরৎচন্দ্র বরাবরই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন বলে তার রেঙ্গুনের বাসাতেও ছোটোখাটো একটি মূল্যবান পুস্তকালয় স্থাপন করেছিলেন। হঠাৎ বাসায় আগুন লেগে সেই সযত্নে সংগৃহীত পুস্তকাবলীর সঙ্গে তার রচিত একাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও তার অঙ্কিত চিত্রের প্রশংসিত নমুনা প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যায়।
শরৎচন্দ্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নব নব গীত শুনে রেঙ্গুনের বাঙালিরা আনন্দে মেতে উঠতেন—বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতিতেও তার দক্ষতা ছিল অপূর্ব কবি নবীনচন্দ্র সেন নিজের সংবর্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্রের কষ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীত শুনে তাকে নাকি রেঙ্গুন-রত্ন বলে সম্বোধন করেছিলেন।
রেঙ্গুন-প্রবাসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা হচ্ছে এই: ওখানে গিয়েছিলেন তিনি অজ্ঞাতবাস করতে, কিন্তু ওখান থেকেই হল তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। সে কথা বলবার আগে আর একটি দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শরৎচন্দ্রের ‘রামের সুমতি’, ‘পথনির্দেশ’, ‘বিন্দু ছেলে’, ‘নারীর মূল্য’, ‘চরিত্রহীন’ প্রভৃতি আরও অনেক শ্রেষ্ঠ রচনার জন্ম এই রেঙ্গুনেই। সেজন্যেও তার সাহিত্যজীবনে রেঙ্গুনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং রেঙ্গুন আশ্রয় না দিলে বাংলার শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্যতাড়িত জীবন কোন পথে ছুটত, সেটাও মনে রাখবার কথা।
শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে, কলকাতায় তার অজ্ঞাতে তখন এক কাণ্ড হল। শ্ৰীমতী সরলা দেবী তখন ভারতী’র সম্পাদিকা এবং শ্ৰীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় থেকে তার নামে কাগজ চালান। সৌরীন্দ্র জানতেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাবার সময়ে তার রচনাগুলি রেখে গেছেন শ্ৰীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। সৌরীন্দ্রমোহন সুরেনবাবুর কাছ থেকে ছোটো উপন্যাস ‘বড়দিদি’ আনিয়ে তিন কিস্তিতে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্রের মত নেওয়া হল না, কারণ তাদের হয়তো সন্দেহ ছিল যে, মত নিতে গেলে গল্প ছাপা হবে না। এটা ১৩১৪ সালের কথা।
শ্ৰীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন
‘এই বড়দিদি সম্পর্কে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ কাহিনি আছে। বড়দিদি যখন ভারতী’তে প্রকাশিত হয় তখন নবপর্যায় বঙ্গদর্শন চলছিল এবং তার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতী’তে বড়দিদির প্রথম কিস্তি পাঠ করে বঙ্গদর্শনের কার্যাধ্যক্ষ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজের কাগজ বঙ্গদর্শনের দাবি অগ্রাহ্য করে ভারতী’তে লেখা দেওয়ার অপরাধে গুরুতরভাবে তাকে অভিযুক্ত করেন। অপরাধ মোচনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তা হয়েছে, কখনও হয়তো ওরা কবিতা-টবিতা সংগ্রহ করে রেকে থাকবে, প্রকাশ করেছে।’ শৈলেশচন্দ্র চক্ষু বিস্ফোরিত করে বললেন, ‘কবিতা-টবিতা কী বলছেন মশায়? উপন্যাস! কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ তো অবাক! বললেন, উপন্যাস কী বলছ শৈলেশ? উপন্যাস লিখলামই বা কখন আর ভারতীতে প্রকাশিত হলই বা কেমন করে? তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভুল করছ। পকেটের মধ্যে প্রমাণ বর্তমান তবু বলবেন ভুল করছ? বিরক্তিগম্ভীর মুখে পকেট থেকে সদ্য প্রকাশিত ‘ভারতী’ বার করে বড়দিদির পাতাটি খুলে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে স্থাপন করে শৈলেশবাবু বললেন, ‘নাম না দিলেই কী এ আপনি লুকিয়ে রাখতে পারেন? এখনও কি অস্বীকার করছেন?’ শৈলেশচন্দ্রের অভিযোগের প্রাবল্যে ঔৎসুক্যবশতই হোক অথবা বড়দিদির প্রথম দু-চার লাইন পড়ে আকৃষ্ট হয়েই হোক, রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সমস্ত লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করলেন, তারপর বললেন, ‘লেখাটি সত্যিই ভারী চমৎকার—কিন্তু তবুও আমার বলে স্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ লেখাটি সত্যই অন্য লোকের।’ রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শৈলেশচন্দ্র ক্ষণকাল নির্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর অস্ফুটম্বরে বললেন, আপনার নয়? এ অবশ্য প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের আকারে বিস্ময় প্রকাশ করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই অনাবশ্যক প্রশ্নের মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন।
বড়দিদি প্রথম প্রকাশের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পেরেছিল বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু যাঁরা লেখার পাকা কারবারি, তারা এই নূতন লেখকটির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে দেখে, শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে কৌতুহলী দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। সেসব দৃষ্টি শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে পারলে না। এবং শরৎচন্দ্রও জানলেন না যে, তার জন্যে কোথাও কোনও কৌতুহল জাগ্রত হয়েছে (এখানে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। পরে শরৎচন্দ্রের নাম যখন দেশব্যাপী, তখন একমাত্র ‘পরিণীতা’ ছাড়া আর কোনও উপন্যাসেরই বড়দিদির মতন এত বেশি সংস্করণ হয়নি।)
তিনি তখন কেরান। তিনি তখন সংসারী। এমনকী জীবনযাত্রার দিক দিয়েও তিনি তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। দুর্লভ সরকারি চাকরি করেন, ক্রমেই মাহিনা বাড়বার সম্ভাবনা. আহারের ভয় আর নেই। গল্পরচনা অকেজোর কাজ, তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?
শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে যে দুচারজন নবীন সাহিত্যযশোপ্রার্থী তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তারা মাঝে মাঝে প্রবাসী বন্ধুর কথা ভাবেন। যে দু-চারজন সাহিত্যিকের বড়দিদি ভালো লেগেছিল, তাদের চোখে শরৎচন্দ্রের আর কোনও নূতন লেখা এসে পড়ল না, তারা বড়দিদির কথাও ভুলে গেলেন। নব্য বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব প্রতিভা যে মগের মুল্লুকে অজ্ঞাতবাস করছে এমন সন্দেহ তখন কেউ করতে পারেনি।