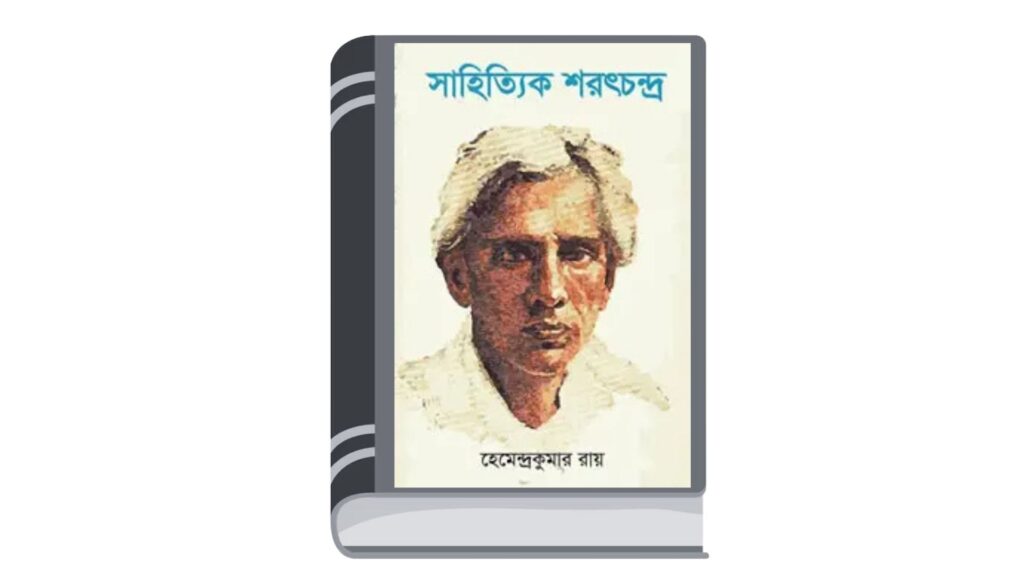পরিশিষ্ট – শরতের ছবি
পঁচিশ বছর আগেকার কথা। সাহিত্যের পাঠশালায় আমার হাতমকশো তখন শেষ হয়েছে বোধহয়। ‘যমুনা’র সম্পাদকীয় বিভাগে অপ্রকাশ্যে সাহায্য করি এবং প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ বা কবিতা কিছু না-কিছু লিখি। …একদিন বৈকালবেলায় যমুনা অফিসে একলা বসে বসে রচনা নির্বাচন করছি। এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগ ও নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উষ্কপুষ্ক চুল, একমুখ দাড়ি-গোফ, পরনে আধ-ময়লা জাম-কাপড়, পায়ে চটি জুতো। সঙ্গে একটি বাচ্চা লেড়ী কুকুর।
লেখা থেকে মুখ তুলে শুধোলুম, কাকে দরকার?
—যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।
—ফণীবাবু এখনও আসেননি।
—আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বসব কি?
চেহারা দেখে মনে হল লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।
প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে শ্ৰীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুককে দেখেই সসন্ত্রমে ও সচকিত কষ্ঠে বললেন, এই যে শরৎবাবু! কলকাতায় এলেন কবে? ওই বেঞ্চিতে বসে আছেন কেন?
আগন্তুক মুখ টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, ওঁর হুকুমেই এখানে বসে আছি।
ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, সে কী! হেমেন্দ্রবাবু, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেননি?
অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে স্বীকার করলুম, আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী?
শরৎচন্দ্র সকৌতুকে হেসে উঠলেন।
এই হল কথাসাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কিন্তু তার সঙ্গে অন্য পরিচয় হয়েছিল এর আগেই। কারণ ‘যমুনা’য় আমার কেরানী গল্প পড়ে তিনি রেঙ্গুন থেকে আমাকে উৎসাহ দিয়ে একখানি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন। তারপরেও আমাদের মধ্যে একাধিকবার পত্র-ব্যবহার হয়েছিল। তার দু-একখানি পত্র এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছি।
উপর-উক্ত ঘটনার সময়ে শরৎচন্দ্রের নাম জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত না হলেও, ‘যমুনা’য় ‘রামের সুমতি’, ‘পথনির্দেশ’ ও ‘বিন্দুর ছেলে’ প্রভৃতি গল্প লিখে তিনি প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরও বছর-ছয়েক আগে ‘ভারতী’তে তার বড়দিদি প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যসমাজে অল্পবিস্তর আগ্রহ জাগিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর যশের ভিত্তি পাকা করে তুলেছিল, ওই তিনটি সদ্য-প্রকাশিত গল্পই—বিশেষ করে ‘বিন্দুর ছেলে’। তার অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস ‘চরিত্রহীনে’র পাণ্ডুলিপি তখন অশ্লীলতার অপরাধে বাংলাদেশের কোনও বিখ্যাত মাসিকপত্রের অফিস থেকে বাতিল হয়ে ফিরে এসে ‘যমুনা’য় দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তার প্রথমাংশ পাঠ করে আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে বিপুল আগ্রহ। তার চন্দ্রনাথ ও নারীর মূল্যও তখন ‘যমুনা’য় সবে সমাপ্ত হয়েছে। তবে তখনও শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার মতো আর বেশি কিছু ছিল না। রেঙ্গুনে সরকারি অফিসে নব্বই কী একশো টাকা মাহিনায় অস্থায়ী কাজ করতেন। অ্যাকাউন্টেন্টশিপ একজামিনে পাস করতে পারেননি বলে তার চাকরি পাকা হয়নি। শুনেছি, বর্মায় গিয়ে তিনি উকিল হবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বর্মি ভাষায় অজ্ঞতার দরুন ওকালতি পরীক্ষাতেও বিফল হয়েছিলেন। এক হিসাবে জীবিকার ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা তার পক্ষে শাপে বর হয়েই দাঁড়িয়েছিল। কারণ সরকারি কাজে পাকা বা উকিল হলে তিনি হয়তো আর পুরোপুরি সাহিত্যিকজীবন গ্রহণ করতেন না।
শরৎচন্দ্র প্রত্যহ ‘যমুনা’-অফিসে আসতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি তার অকপট বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য হলুম। তার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সে পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়নি। সে সময়ে যমুনা-অফিসে প্রতিদিন বৈকালে বেশ একটি বড়ো সাহিত্য-বৈঠক বসত এবং তাতে যোগ দিতেন স্বর্গীয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় গল্পলেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কবি, গল্পলেখক ও ‘সাধনা’-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক শ্ৰীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি শ্ৰীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যিক শ্ৰীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্ৰীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ঔপন্যাসিক শ্ৰীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যরসিক শ্ৰীযুক্ত হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়, ‘মৌচাক’-সম্পাদক শ্ৰীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার, ঔপন্যাসিক (অধুনা চলচ্চিত্র-পরিচালক) শ্ৰীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আনন্দবাজারের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম শ্ৰীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রকর ও চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্ৰীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক শ্ৰীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও ‘ভারতবর্ষে’র ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্ৰীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আরও অনেকে, সকলের নাম মনে পড়ছে না। ‘যমুনা’র কর্ণধার ফণীবাবুর কথা বলা বাহুল্য। পরে এই আসরেরই অধিকাংশ লোককে নিয়ে সাহিত্যসমাজে বিখ্যাত ‘ভারতী’র দল গঠিত হয়। অবশ্য ‘ভারতী’র দলের আভিজাত্য এ আসরে ছিল না—এখানে ছোটো-বড়ো সকল দলেরই সাহিত্যিক অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেতেন। অসহিত্যিকেরও অভাব ছিল না। এখানে প্রতিদিন আসরে আর্ট ও সাহিত্য নিয়ে যে আলোচনা আরম্ভ হত, শরৎচন্দ্রও মহা উৎসাহে তাতে যোগ দিতেন এবং আলোচনা যখন উত্তপ্ত তর্কাতর্কিতে পরিণত হত তখনও গলার জোরে তিনি কারুর কাছে খাটো হতে রাজি ছিলেন না—যদিও যুক্তির চেয়ে কষ্ঠের শক্তিতে সেখানে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতেন শ্ৰীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত সেখানে যেমন অসঙ্কোচে ও স্পষ্টভাষায় প্রকাশ পেত, তার কোনও রচনার মধ্যেও তা পাওয়া যাবে না। সময়ে সময়ে আমরা সকলে মিলে শরৎচন্দ্রকে রীতিমতো কোণঠাসা করে ফেলেছি, কিন্তু তিনি চটা-মেজাজের লোক হলেও তর্কে হেরে গিয়ে কোনওদিন তাকে মুখভার করতে দেখিনি; পরদিন হাসিমুখে এসে আমাদেরই সমবয়সী ও সমকক্ষের মতন আবার তিনি নূতন তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদীয়মান সাহিত্যিকরূপে অক্ষয় যশের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান সেদিনকার সেই শরৎচন্দ্রকে যিনি দেখেননি, আসল শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারা তার পক্ষে অসম্ভব বললেও চলে। কারণ গত বিশ বৎসরের মধ্যে তার প্রকৃতি অনেকটা বদলে গিয়েছিল। সাহিত্যে বা আর্টে একটি অতুলনীয় স্থান অধিকার করলে প্রত্যেক মানুষকেই হয়তো প্রাণের দায়ে না হোক, মানের দায়ে ভাব-ভঙ্গি-ভাষায় সংযত হতে হয়।
শত শত দিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গলাভ করে তার প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষত্ব আমার কাছে ধরা পড়ছে। শরৎচন্দ্রের লেখায় যেসব মতবাদ আছে, তার মৌখিক মতের সঙ্গে প্রায়ই তা মিলত না। তিনি প্রায়ই আমাদের উপদেশ দিতেন, সাহিত্যে দুরাত্মার ছবি কখনও এঁকো না। পৃথিবীতে দুরাত্মার অভাব নেই, সাহিত্যে তাদের টেনে না আনলেও চলবে। আবার—পুণ্যের জয় পাপের পরাজয় দেখবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর মৃত্যু দেখিয়েছেন, এটা বড়ো লেখকের কাজ হয়নি। উত্তরে আমরা বলতুম, কেন, আপনিও তো দুরাত্মার ছবি আঁকতে ক্রটি করেননি। আবার আপনিও তো কোনও কোনও উপন্যাসে নায়িকাকে পাপের জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বেশি শাস্তি দিয়েছেন? কিন্তু এ প্রতিবাদ তিনি কানে তুলতেন না। উপবীতকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন না, কৌলীন্যগর্ব তার যথেষ্ট ছিল। ‘ভারতী’র আসরে একদিন শ্ৰীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় পইতা নেই দেখে তিনি খাপ্পা হয়ে বললেন, ও কী হে চারু, তোমার পইতে নেই! চারুবাবু হেসে বললেন, শরৎ পইতের ওপরে ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না। শরৎচন্দ্র আহত কণ্ঠে বললেন, ‘না, না, বামুন হয়ে পইতা ফেলা অন্যায়।’ রবীন্দ্রনাথের উপরে শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, যখন-তখন বলতেন, ওঁর লেখা দেখে কত শিখেছি! কিন্তু আত্মশক্তির উপরেও ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। ‘যমুনা’র পরে ওই বাড়িতেই নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় ‘মর্মবাণী’র কার্যালয় স্থাপন করেন এবং আমি ছিলুম তখন ‘মর্মবাণী’র সহকারী সম্পাদক। ‘যমুনা’র আসরে আমার যেসব সাহিত্যিক বন্ধু আসতেন, এই নূতন আসরেও তাদের কারুরই অভাব হল না, উপরন্তু নূতন গুণীর সংখ্যা বাড়ল। যেমন স্বর্গীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ। তিনি মাঝে মাঝে নিজের নূতন রচনা শোনাতে আসতেন। এবং ‘মানসী’রও দলের একাধিক সাহিত্যিক এখানে এসে দেখা দিতেন। এই ‘মর্মবাণী’র আসরে বসে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, সবুজপত্রে রবিবাবু ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস লিখছেন, তোমরা দেখে নিয়ো, আমি এইবার যে উপন্যাস লিখব, ‘ঘরে-বাইরে’র চেয়েও ওজনে তা একতিলও কম হবে না। প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রবল প্রতিবাদ করে বললেন, ‘যে উপন্যাস এখনও লেখেননি, তার সঙ্গে ঘরে-বাইরের তুলনা আপনি কী করে করছেন?’ কিন্তু শরৎচন্দ্র আবার দৃঢ়স্বরে বললেন, ‘তোমরা দেখে নিয়ো!’ এই উক্তিতে কেবল শরৎচন্দ্রের আত্মশক্তিনির্ভরতাই প্রকাশ পাচ্ছে না, তার সরলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, খুব সম্ভব শরৎচন্দ্রের পরের উপন্যাসের নাম ছিল ‘গৃহদাহ’—যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কোনও একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট ছায়া আছে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির নকলে চরিত্র অঙ্কন করেছেন, একখানি পত্রে সরল ভাষায় সে-কথা স্বীকার করতেও কুষ্ঠিত হননি। এই সরলতা ও অকপটতার জন্যে শরৎচন্দ্রের অনেক দুর্বলতাও মধুর হয়ে উঠত।
হয়তো এই সরলতার জন্যেই শরৎচন্দ্র যে-কোনও লোকের যে-কোনও কথায় বিশ্বাস করতেন। কারুর উপরে তাকে চটিয়ে দেওয়া ছিল খুবই সহজ। যদি তাকে বলা হত, শরৎদা, অমুক লোক আপনার নিন্দা করেছে, তাহলে এ-কথার সত্যাসত্য বিচার না করেই তিনি হয়তো কোনও বন্ধুর উপরেও কিছুকালের জন্যে চটে থাকতেন এবং নিজেও কষ্ট পেতেন। তারপর হয়তো নিজের ভুল বুঝে ভ্রম সংশোধন করতেন। মাঝে মাঝে কোনও কোনও দুষ্টু লোক এইভাবেই তাকে রবীন্দ্রনাথেরও বিরোধী করে তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনওবারেই এই সব অসৎ চক্রান্ত সফল হয়নি।
আমি এখানে খালি ব্যক্তিগতভাবেই শরৎচন্দ্রকে দেখতে ও দেখাতে চাইছি, কারণ এই সদ্যগত বৃহৎ বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে এখন ব্যক্তিগত কথা ছাড়া অন্য কথা মনে আসছে না, আসা স্বাভাবিকই নয়। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি বা সাহিত্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ করবার কোনও ইচ্ছাই এখন হচ্ছে না। তবে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করলে মন্দ হবে না। আজকাল অনেক তথাকথিত সাহিত্যিক নিজেদের অভিজাত বলে প্রচার করে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার জন্যে হাস্যকর চেষ্টা করেন। তাঁরা লেখেন ও বলেন বড়ো বড়ো কথা। কিন্তু সাহিত্যের এক বিভাগে অসাধারণ হয়েও শরৎচন্দ্র কোনওদিন এই সব ময়ূরপুচ্ছধারীর ছায়া পর্যন্ত মাড়ননি। নিজেকে অতুলনীয় ভেবে গর্ব করবার অধিকার তার যথেষ্টই ছিল, কিন্তু মুখের কথায় ও অসংখ্য পত্রে তিনি বারবার এই ভাবটাই প্রকাশ করে গেছেন যে—আমি লেখাপড়াও বেশি করিনি, আমার জ্ঞানও বেশি নয়, তবে আমার লেখা লোকের ভালো লাগে তার কারণ হচ্ছে, আমি স্বচক্ষে যা দেখি, নিজের প্রাণে যা অনুভব করি, লেখায় সেইটেই প্রকাশ করতে চাই। ইনটেলেকচুয়াল গল্প-টল্প কাকে বলে আমি তা জানি না..এখনকার অভিজাত সাহিত্যিকরা লোককে ধাক্কা মেরে ধাপ্পা দিয়ে চমকে দিয়ে বড়ো হবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতো যারা যথার্থই শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী, তারা বড়ো হন বিনা চেষ্টায় হাওয়ার মতো অগোচরে বিশ্বমানুষের প্রাণবস্তুতে পরিণত হয়ে। জোর করে প্রেমিক বা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। পরের প্রাণে আশ্রয় খুঁজলে নিজের প্রাণকে আগে নিবেদন করা চাই। তুমি অভিজাত সাহিত্যিক, তুমি হচ্ছ সোনার পাথর-বাটির রূপান্তর! যশের কাঙাল হয়ে সাগ্রহে লেখা ছাপাবে, অথচ জনতাকে ঘৃণা করবে। অসম্ভব।
‘যমুনা’-অফিসে শরৎ ও তার ভেলু কুকুরকে নিয়ে আমাদের বহু সুখের দিন কেটে গিয়েছিল। ওই ভেলু কুকুরকে অনাদর করলে কেউ শরৎচন্দ্রের আদর পেত না—কারণ শরৎচন্দ্রের চোখে ভেলু মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল না, বরং অনেক মানুষের চেয়ে ভেলুকে তিনি বড়ো বলেই মনে করতেন। আর ভেলুও বোধ হয় সেটা জানত। সে কতবার যে আমাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে আদর জানিয়েছে, তার আর সংখ্যা হয় না। এবং তার এই সাংঘাতিক আদর থেকে শরৎচন্দ্রও নিস্তার পেতেন না। আমাদের সুধীরচন্দ্র সরকারের ছিল ভীষণ কুকুরাতঙ্ক, ভেলু যদি ঘরে ঢুকল সুধীর অমনি এক লাফে উঠে বসল টেবিলের উপরে। ভেলুকে না বাঁধলে কারুর সাধ্য ছিল না সুধীরকে টেবিলের উপর থেকে নামায় এবং শরৎচন্দ্রেরও বিশেষ আপত্তি ছিল ভেলুকে বাঁধতে—আহা, অবোলা জীব, ওর যে দুঃখ হবে! হোটেল থেকে ভেলুর জন্যে আসত বড়ো বড়ো ঘৃতপক্ক চপ, ফাউল কাটলেট। ভেলুর অকালমৃত্যুর কারণ বোধহয় কুকুরের পক্ষে এই অসহনীয় আহার এবং ভেলুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের যে শোকাকুল অশ্রুস্নাত দৃষ্টি দেখেছিলুম, এ-জীবনে তা আর ভুলব বলে মনে হয় না।
‘যমুনা’-অফিসে শরৎচন্দ্র অনেকদিন বেলা দুটো-তিনটের সময়ে এসে হাজিরা দিতেন, তারপর বাসায় ফিরতেন সান্ধ্য-আসর ভেঙে যাবারও অনেক পরে। কোনও কোনওদিন রাত্রি দুটো-তিনটেও বেজে যেত। সে সময়ে তার সঙ্গে আমরা তিন-চারজন মাত্র লোক থাকতুম। বাইরের লোক চলে গেলে শরৎচন্দ্র শুরু করতেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা কাহিনি। বেশি লোকের সভায় আলোচনা (conversazione) ও তর্ক-বিতর্কের সময়ে শরৎচন্দ্র বেশ গুছিয়ে নিজের মতামত বলতে পারতেন না বটে, কিন্তু গল্পগুজব করবার শক্তি ছিল তার অদ্ভুত ও বিচিত্ৰ—শ্রোতাদের তার সুমুখে বসে থাকতে হত মন্ত্রমুগ্ধের মতো। একদিন এমন কৌশলে একটি ভূতের গল্প বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্রে একলা বাড়ি ফিরতে ভয় পেয়েছিলেন। সেই গল্পটি পরে আমি আমার ‘যকের ধন’ উপন্যাসে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছিলুম বটে, কিন্তু তার মুখের ভাষার অভাবে তার অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি রাত্রেই আসর ভাঙবার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাড়ি ফিরতুম আমি, কারণ তিনি তখন বাসা নিয়েছিলেন আমার বাড়ির অনতিদূরেই। সেই সময়ে পথ চলতে চলতে শরৎচন্দ্র নিজের হৃদয় একেবারে উন্মুক্ত করে দিতেন এবং তার জীবনের কোনও গুপ্তকথাই বলতে বোধ হয় বাকি রাখেননি। এইভাবে খাঁটি শরৎচন্দ্রকে চেনবার সুযোগ খুব কম সাহিত্যিকই পেয়েছেন এবং আরও বছর-কয়েক পরে তার সঙ্গে আলাপ হলে আমার ভাগেও হয়তো এ সুযোগলাভ ঘটত না। এও বলে রাখি, শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে উঠেছিল— much familiarity brings contempt,এ প্রবাদ সব সময়ে সত্য হয় না।
একদিন সকালবেলায় মা এসে বললেন,
‘ওরে, তোর পড়বার ঘরে কে এক ভদ্রলোক এসে গান গাইছেন—কী মিষ্টি গলা?’ কৌতুহলী হয়ে নীচে নেমে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখি, শরৎচন্দ্র কখন এসে আমার পড়বার ঘরে ঢুকে গালিচার উপরে ঠেলান দিয়ে শুয়ে নিজের মনে গান ধরেছেন এবং সে গান শুনতে সত্যই চমৎকার! আমাকে দেখেই তিনি মৌন হলেন, কিছুতেই আর গাইতে চাইলেন না! তারপর আরও কয়েকবার আমার নীচের ঘরে তাঁর গানের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়েছি, আড়ালে থেকেও শুনেছি, কিন্তু যেই আমাকে দেখা অমনি তার ভীরু কণ্ঠ হয়েছে বোবা! অথচ তার সঙ্কোচের কোনওই কারণ ছিল না, তাঁর গানে ওস্তাদি না থাকলেও মাধুর্য ছিল যথেষ্ট এবং সঙ্গীত-সাধনা করলে তিনি নাম করতেও পারতেন রীতিমতো।
শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে বাস করতেন, তখন প্রতিদিন আর তার দেখা পেতুম না বটে, কিন্তু আমাদের অন্যান্য আসরে তার আবির্ভাব হত প্রায়ই। কিন্তু তার সম্বন্ধে সমস্ত গল্প বলতে গেলে এখানে কিছুতেই ধরবে না, অতএব সে চেষ্টা আর করলুম না। তিনি পানিত্ৰাসে যাবার পর থেকে তার সঙ্গে আমার দেখা হত ন-মাসে ছ-মাসে, কিন্তু যখনই দেখা হত বুঝতে পারতুম যে, আমার কাছে তিনি সেই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়সের যুবক ও পুরাতন শরৎচন্দ্রই আছেন। অতঃপর তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে গল্প বলে এবারের কথা শেষ করব।
একদিন আমাদের এক আসরে বসে শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক টানছেন, এমন সময়ে অধুনালুপ্ত ‘বিদূষক’ পত্রিকার সম্পাদক হাস্যরসিক শ্ৰীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের আবির্ভাব। ‘বিদূষক’-সম্পাদক এই শরৎচন্দ্রকে কথায় হারাতে কারুকে দেখিনি এবং খোঁচা খেলে তিনি নিরুত্তর থাকবার ছেলেও ছিলেন না। ‘বিদূষক’-সম্পাদককে অপ্রস্তুত করবার কৌতুকের লোভে শরৎচন্দ্র বললেন, এসো বিদূষক শরৎচন্দ্র। শরৎ পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিলেন, কী বলছ ভাই ‘চরিত্রহীন’ শরৎচন্দ্র? এই কৌতুকময় ঘাত-প্রতিঘাতে নিরুত্তর হতে হল ‘চরিত্রহীন’ প্রণেতাকেই।
একদিন বিডন স্ট্রিটের মোড়ে এক মণিহারির দোকানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কী কিনতে গিয়েছি। হঠাৎ তিনি বললেন, ‘হেমেন্দ্র, তুমি কিছু খাও!’ আমি বললুম, ‘এই মণিহারির দোকানে আপনি আবার আমার জন্যে কী খাবার আবিষ্কার করলেন?’—‘কেন,অনেক ভালো ভালো লজেনচুস রয়েছে তো!’—‘বলেন কী দাদা,আপনার চেয়ে বয়সে আমি অনেক ছোটো বটে,কিন্তু আমাকে লজেনচুস-লোভী শিশু বলে ভ্রম করছেন কেন?’ শরৎচন্দ্র মাথানেড়ে বললেন, ‘নাহে না,তুমি বড়ো বেশি সিগারেট খাও! ও বদ-অভ্যাস ছাড়ো। হয় তামাক ধরো, নয় লজেনচুস খাও!’ দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি শরৎচন্দ্রের এ আদেশ পালন করতে ইচ্ছা হয়নি।
শরৎচন্দ্র ভেলুকে কী রকম ভালোবাসতেন তারও একটা গল্প বলি। একদিন কোনও এক ভক্ত এক চাঙরি প্রথম শ্রেণীর সন্দেশ নিয়ে গিয়ে তাকে উপহার দিলেন। ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সামনে সন্দেশগুলি রাখলেন, ভেলু ছিল তখন তার পাশে বসে। সন্দেশ দেখে ভেলু রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠল। এবং শরৎচন্দ্রও ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভেলুর উৎসাহিত মুখে এক-একটি সন্দেশ তুলে দিতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, চাঙারি একেবারে খালি! যে ভদ্রলোক এত সাধে ভেট নিয়ে গিয়েছিলেন, সন্দেশের এই অপূর্ব পরিণাম দেখে তার মনের অবস্থা কী রকম হল, সেকথা আমরা শুনিনি।
একদিন শরৎচন্দ্র এসে বিরক্তমুখে বললেন, নাঃ, শিবপুরের বাস ওঠাতে হল দেখছি!’—
‘কেন শরৎদা, কী হল?’—‘আর ভাই, বলো কেন, ভেলুর জন্যে আমার নামে আদালতে নালিশ হয়েছে, পাড়ার লোকগুলো পাজির পা-ঝাড়া’—‘সেকি, ভেলু কী করেছে?’—‘কিছুই করেনি ভাই, কিছুই করেনি! একটা গয়লা যাচ্ছিল পাড়া দিয়ে, তাকে দেখে ভেলুর পছন্দ হয়নি। তাই সে ছুটে গিয়ে তার পায়ের ডিম থেকে শুধু ইঞ্চি-চারেক মাংস খুবলে তুলে নিয়েছে!’—‘অ্যাঃ, বলেন কী, ইঞ্চি-চারেক মাংস?’—‘হ্যাঁ, মোটে এক খাবল মাংস আর কী! এই সামান্য অপরাধেই আমার ওপরে হুকুম হয়েছে, ভেলুর মুখে ‘মাজল’ পরিয়ে রাখতে হবে! ভেলুর কী যে কষ্ট হবে, ভেবে দাখো দেখি!’
সারমেয়-অবতার ভেলুর এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছি। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরের বাড়িতে, সেই সময়ে এক সকালে টেক্সোবাবু এলেন টেক্সোর টাকা আদায় করতে। বাইরের ঘরে টেক্সোবাবু তার তল্পিতল্পা নিয়ে বসলেন। ভেলু এক কোণে আরাম করে শুয়ে আছে—যদিও তার অসন্তুষ্ট দৃষ্টি রয়েছে টেক্সোবাবুর দিকেই। শরৎচন্দ্র টেক্সোর টাকা দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। টেক্সোবাবুর কাজ শেষ হল—তিনিও নিজের টাকার তল্পির দিকে হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেলু ভীষণ গর্জন করে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কারণ ভেলুর একটা স্বভাব ছিল এই, তার মনিবের বাড়িতে বাহির থেকে কেউ কোনও জিনিস এনে রাখলে সে কোনও আপত্তি করত না, কিন্তু বাড়ির জিনিসে হাত দিলেই তার কুকুরত্ব জেগে উঠত বিষম বিক্রমে! সুতরাং টেক্সোবাবুর অবস্থা যা হল তা আর বলবার নয়! তিনি মহা-আতঙ্কে পিছিয়ে পড়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। একেবারে চিত্রাপিতের মতো—কারণ একটু নড়লেই ভেলু করে গোঁ-গোঁ! দুই-তিন ঘণ্টা পরে মান-আহারাদি সেরে শরৎচন্দ্র আবার যখন সেখানে এলেন, টেক্সোবাবু তখনও দেওয়ালের ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন! বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের পুনরাবির্ভাবে টেক্সোবাবুর মুক্তিলাভের সৌভাগ্য হল!
মনোমোহন থিয়েটারে চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্রের প্রথম বই ‘আঁধারে আলো’ দেখানো হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমিও গিয়েছি। একখানা ঢালা বিছানা পাতা ‘বক্সে’ শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে আমিও আশ্রয় পেলুম। ছবি দেখানো শেষ হলে দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের এক পাটি তালতলার চটি অদৃশ্য হয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও পাটি পাওয়া গেল না। তখন শরৎচন্দ্র হতাশ হয়ে অন্য পাটি বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললুম, এক পাটি চটি নিয়ে আর কী করবেন, ওটাও এখানে রেখে যান। শরৎচন্দ্র বললেন, ‘ক্ষেপেছো? চোরবেটা এইখানেই কোথায় লুকিয়ে বসে সব দেখছে! আমি এ-পাটি রেখে গেলেই সে এসে তুলে নেবে। তার সে সাধে আমি বাদ সাধব,—শিবপুরে যাবার পথে হাওড়ার পুল থেকে চটির এই পাটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেব!’ তিনি খালি পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।
পরদিনই ‘বক্সে’র তলা থেকে তালতলার হারানো চটির পাটি আবিষ্কৃত হল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের হস্তগত অন্য পাটি তখন গঙ্গালাভ করেছে এবং সম্ভবত এখনও সলিল-সমাধির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।
রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন আর্ট ও সাহিত্যের আসর ‘বিচিত্রা’র অধিবেশন হচ্ছে প্রতি সপ্তাহেই এবং প্রতি অধিবেশনের পরেই খবর পাওয়া যাচ্ছে, অমুক অমুক লোকের জুতা চুরি গিয়েছে। আমরা সকলেই চিন্তিত, কারণ ‘বিচিত্রা’র ঢালা আসরে জুতা খুলে বসতে হত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছেঁড়া, পুরানো জুতার আশ্রয় নিলেন, কেউ কেউ জুতা না খুলে ও হলে না ঢুকে পাশের বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করলেন এবং আমরা অনেকেই জুতার দিকেই মন রেখে গান-বাজনা ও আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলুম। শরৎচন্দ্র এই দুঃসংবাদ শুনেই খবরের কাগজে নিজের জুতোজোড়া মুড়ে বগলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে বসলেন— সেদিন আসরে লোক আর ধরে না। ইতিমধ্যে কে গিয়ে চুপি চুপি বিশ্বকবির কাছে শরৎচন্দ্রের গুপ্তকথা ফাঁস করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মুখ টিপে হেসে শুধোলেন, শরৎ, তোমার কোলে ওটা কী? শরৎচন্দ্র মাথাচুলকোতে চুলকোতে বললেন, ‘আজ্ঞে, বই!’ রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ?’ শরৎচন্দ্র লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারেন না!
বছর-আড়াই আগেকার কথা। প্রায় বৎসরাবধি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তখন আমি আমার নতুন বাড়িতে এসেছি, শরৎচন্দ্র এ-বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত জানেন না। একদিন দুপুরে তিনতলার বারাদার কোণে বসে রচনাকার্যে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে একতলায় পরিচিত কষ্ঠে আমার নাম ধরে ডাক শুনলুম। আমার দুই মেয়ে গিয়ে আগন্তুকের নাম জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর এল, ওগো বাছারা, তোমরা আমাকে চেনে না, তোমরা যখন জন্মাওনি তখন আমি তোমাদের পুরনো বাড়িতে আসতুম, তোমার বাবা আমাকে দেখলে হয়তো চিনতে পারবেন!’এ যে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর—আজ কুড়ি-বাইশ বছর পরে শরৎচন্দ্র অযাচিতভাবে আবার আমার বাড়িতে! বিশ্বাস হল না—তিনি আমার এ-বাড়ি চিনবেন কেমন করে? কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়েই দেখলুম, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন সত্য-সত্যই শরৎচন্দ্ৰ—তার পিছনে কবি-বন্ধু গিরিজাকুমার বসু সবিস্ময়ে বললুম, ‘শরৎদা, এতকাল পরে আমার বাড়িতে আবার আপনি!’ শরৎচন্দ্র সহস্যে বললেন, ‘হ্যাঁ হেমেন্দ্র। গিরিজার সঙ্গে যাচ্ছিলুম বরানগরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, তাই তোমার কাছেই এসে হাজির হয়েছি!’ আমি সানন্দে তাকে তিনতলার ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললুম, ‘এ যে আমার পরম সৌভাগ্য দাদা, এ যে বিনা মেঘে জল!’ ‘কোথায় রবীন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমি! এ যে হাসির কথা?’ তারপর অবিকল সেই পুরাতন কালে অবিখ্যাত শরৎচন্দ্রের মতোই নানা আলাপ-আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তিনি আবার বিদায় গ্রহণ করলেন।
শরৎচন্দ্র শেষ যেদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, আমার দুইমেয়ে শেফালিকাও মুকুলিকার কাছে বলে গিয়েছিলেন, শোনো বাছা, এসব সিগারেট ফিগারেট আমার সহ্য হয় না। আমার জন্যে যদি গড়গড়া আনিয়ে রাখতে পারো, তাহলে আবার তোমাদের বাড়িতে আমি আসব!’ তার কিছুদিন পরে রঙ্গালয়ে ‘চরিত্রহীনে’র প্রথম অভিনয় রাত্রে আমার মেয়েরা তার কাছে গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল, কই, আপনি তো আর এলেন না? শরৎচন্দ্র বললেন, ‘আমার জন্যে গড়গড়া আছে?’—‘হাঁ! শুনে তিনি সহস্যে অঙ্গীকার করলেন, ‘আচ্ছা, এইবারে তবে যাব!’ কিন্তু এখন আর তার সে-অঙ্গীকারের মূল্য নেই। তবু শোকাতুর মনে ভাবছি, তার গড়গড়া তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র তো আর এলেন না? হায়, স্বর্গ থেকে মর্ত্য কতদূর?