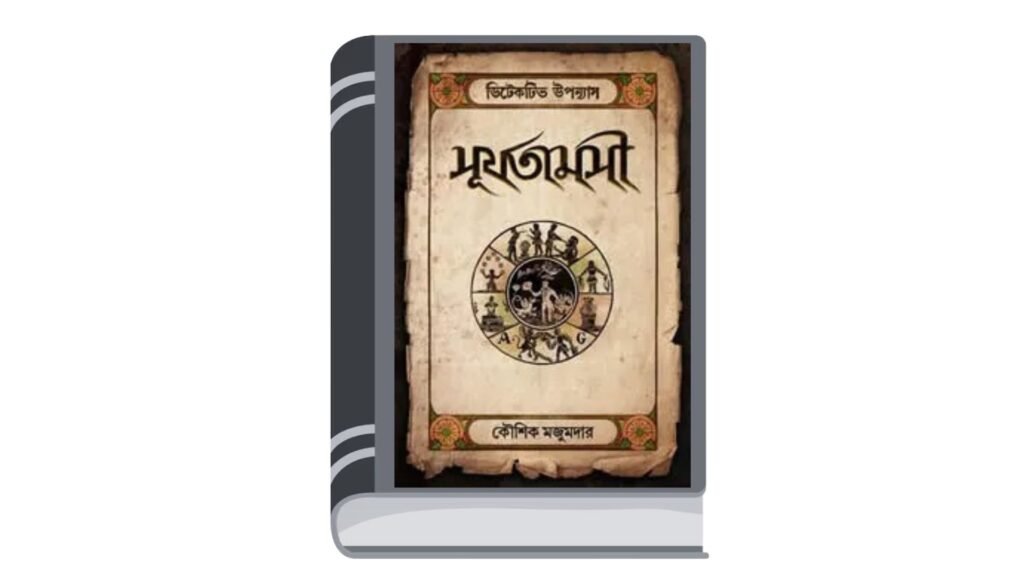তুর্বসুর কথা
। এক।
সেদিন রাতে দেবাশিসদার চিঠি পেয়ে প্রথমেই ভাবলাম অফিসারকে একবার ফোন করি। তারপরেই মনে হল দেবাশিসদা বারণ করেছেন। এই তল্লাশি আমাকে একাই চালাতে হবে। এই চিঠির কথা আপাতত কাউকে বলা যাবে না। পরদিন বলার মতো ঘটনা একটাই ঘটেছিল। যদিও সেটা বেশ ভয়াবহ। আমি আর অফিসার মুখার্জি দুজনে গেছিলাম চন্দননগর গ্রন্থাগারে। বিরাট গ্রন্থাগার। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক সদাশয়, যদিও পুলিশ দেখে একটু ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। দেবাশিসদার খুনের কথাটা খবরের কাগজে এখনও না এলেও লোকমুখে ওঁর কানে এসেছে। দু-একবার কথা বলতে বলতে ঠোঁট দিয়ে জিভ চেটে নিলেন দেখতে পেলাম। একটু হেঁ হেঁ করে আমাদের জানালেন দেবাশিসদা প্রায়ই আসতেন এখানে। অনেক সময় প্রায় সারাদিন বসে পড়াশোনা করতেন। কারও সঙ্গে খুব বেশি আলাপ ছিল না। তবে তাঁর কোনও এক অনুগামী ছিল। লাইব্রেরিয়ান তাঁর নাম জানেন না। দেবাশিসদাও বলেননি। শুধু কয়েকবার বই ইস্যু করার সময় বলেছেন, “যাই, এটা পড়ে আমার চ্যালাকে জ্ঞান দেওয়া যাবে।”
“আপনার কথাই তো বলেছিল বলে মনে হয়, কি মশাই?” জিজ্ঞেস করলেন অফিসার।
“আর কেউ নেই বলছেন?”
“থাকলেও এখনও খোঁজ পাইনি। কেন, আপনি কাউকে জানেন?”
মাথা নাড়লাম। জানি না। বললাম, “কী কী বই উনি সেই চ্যালার জন্য ইস্যু করেছেন মনে আছে?”
“দাঁড়ান, ইস্যু রেজিস্টার দেখি”, বলে ভদ্রলোক একটা গাবদা খাতা বার করলেন। তাতে সব সদস্যদের নাম আর তাঁরা কবে কী বই ইস্যু করিয়েছেন তা লেখা। দেবাশিস গুহ-র নামের নিচে শেষ যে কটা বইয়ের নাম দেখলাম, তাতে দুটো ‘চন্দননগরের ইতিহাস’, একটা ‘ব্যান্ডেল চার্চের ইতিহাস’, ‘বাংলার পুলিশের ইতিহাস’, ‘দারোগার দপ্তর’, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ তো ছিলই, সঙ্গে ছিল বেশ কিছু ম্যাজিকের বই। সেই প্রাচীন ব্ল্যাক ম্যাজিক, তন্ত্র মন্ত্র থেকে হুডিনি অবধি। জাদুকর গণপতির ওপর শেষদিকে ওঁর বেশ আগ্রহ হয়েছিল। তাঁর জীবনী, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর ‘বাঙ্গালীর সার্কাস’, অজিতকৃষ্ণ বসুর ‘জাদুকাহিনী’ সহ প্রচুর ম্যাজিকের বই পড়ছিলেন। আর একটা ম্যাগাজিনের বেশ কিছু সংখ্যা তিনি রিডিং সেকশানে বসে পড়ে নোট নিয়েছিলেন। নাম ‘ম্যান, মিথ অ্যান্ড ম্যাজিক’। যে তিনটে ইস্যু তিনি পড়তে নিয়েছিলেন, একটার বিষয় ফ্রি ম্যাসন, একটার বিষয় লিং-চি, আর অন্যটা বেশ অদ্ভুত, এডগার অ্যালান পো। পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনির লেখক এই সিরিজে জায়গা পেলেন কী করে, সেটাই মাথায় এল না। আমি লাইব্রেরিয়ানকে অনুরোধ করলাম ম্যাগাজিনগুলোর ফটোকপি করে দেওয়া সম্ভব কি না। একটু গাঁইগুঁই করে শেষে রাজি হলেন। সঙ্গে পুলিশ থাকার এই সুবিধে।
তবে অফিসার মুখার্জি অস্থির হয়ে উঠছিলেন। এখানে দেবাশিসদা কি কিছু লুকিয়ে রেখেছেন? রাখলে সেটা কি? শেষে তিনিই লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা এই দেবাশিসবাবু এখানে বসে যে বই পড়তেন, তাঁর কোনও নিজস্ব জায়গা ছিল?”
“ছিল বইকি! একেবারে পিছনে পুরোনো বইয়ের র্যাকগুলোর পিছনে ছোটো একটা টেবিল আছে। ওখানেই চেয়ার পেতে বসতেন। ওদিকটা বেশ নির্জন। কেউ যায়-টায় না। আলো একটু কম হলেও পড়াশোনার জন্য খাসা জায়গা।”
“উনি ছাড়া আর কেউ ওখানে বসেন না?”
“নাহ। যারা রেগুলার আসে, তারা জানে ওটা ওঁর জায়গা। টেবিলে ওঁর বই-ই রাখা থাকে। আমরা গোছাই না।”
“কেন?”
“আসলে একটু খেয়ালি টাইপ লোক ছিলেন তো, পড়তেন, নোট নিতেন। একবার গোছাতে গিয়ে কোনও বইয়ের মধ্যে রাখা ওঁর একটা নোট বোধহয় হারিয়ে যায়। খুব রেগে গেছিলেন। সেই থেকে ওঁকে জিজ্ঞাসা না করে ওঁর বই গোছাই না।”
“ওঁর পড়ার জায়গাটা দেখা যায়?” জিজ্ঞেস করলেন অফিসার মুখার্জি।
“হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই, কেন নয়?” বলে লাইব্রেরিয়ান (পরে নাম জেনেছিলাম সুজিত দত্ত) আমাদের নিয়ে গেলেন লাইব্রেরির মধ্যে দিয়ে। উঁচু উঁচু তাকে সারি সারি বই সাজানো। কিছু নতুন, বেশিরভাগই পুরোনো। গোলকধাঁধার মতো পথ। একেবারে শেষে দেওয়ালের ধারে এক কোনায় ছোট্ট একটা টেবিল পাতা। তাতে কিছু ম্যাজিক নিয়ে জিম স্টেইনমেয়ারের কিছু বই ছড়ানো, সেই তিনটে ম্যাগাজিন আর ছোট্ট একটা বাক্স। চামড়ার।
“এই বাক্সটা কীসের?”
“সেই আপনাকে বলছিলাম না, গোছানোর কথা। সেই থেকে উনি নিজের নোটপত্র যাবার আগে এই বাক্সে আটকে রেখে যেতেন, যাতে বই গোছালেও এটা কেউ না ধরে। এটার একটা নামও দিয়েছিলেন উনি, ‘প্যান্ডোরার বাক্স’।”
একেবারে দেবাশিসদাচিত নাম। স্বর্গ থেকে প্রমেথিউস আগুন চুরি করায় দেবরাজ জিউস মানবজাতির উপরে রেগে গিয়ে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য, হেফেথাসকে দিয়ে একটি মাটির নারী বানিয়ে তাঁকে জীবন দেন। নাম প্যান্ডোরা। প্যান্ডোরাকে তৈরি করার জন্য ভালোবাসার দেবী আফ্রোদিতিকে বেছে নেওয়া হয় মডেল হিসেবে। আফ্রোদিতি তাকে দেন সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-আকাঙ্ক্ষা। হার্মিস তাকে দেন চাতুর্য ও দৃঢ়তা, অ্যাপোলো সংগীত শেখান। প্রত্যেক দেবতাই তাঁদের নিজেদের সেরাটা দিয়ে সাজিয়ে তোলেন প্যান্ডোরাকে। অনেকটা আমাদের দেবী দুর্গার মতো। সবশেষে দেবরাজ জিউসের স্ত্রী হেরা প্যান্ডোরাকে উপহার দেন হেরার অনন্য বৈশিষ্ট্য, কৌতূহল। প্যান্ডোরাকে দেবতাদের তরফ থেকে উপহার হিসেবে পাঠানো হয় প্রমেথিউসের ভাই এপিমেথেউসের কাছে। প্যান্ডোরাকে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে যান এপিমেথেউস। এপিমেথেউস-প্যান্ডোরার বিয়েতে প্যান্ডোরাকে দেবরাজ জিউস উপহার দেন এক অপূর্ব বাক্স। নিষেধ করে দেন এটি খুলতে। দেবরাজ জিউসের নিষেধাজ্ঞা পরাস্ত হয় দেবরানি হেরার দেওয়া উপহার কৌতূহল-এর কাছে। বিয়ের উপহার একবার দেখতে প্যান্ডোরা বাক্সটি খোলামাত্র বাক্সবন্দি রোগ-জরা-হিংসা-দ্বেষ-লোভ-মিথ্যা ইত্যাদি সব স্বর্গীয় নীচতা ছড়িয়ে পড়ে মানুষের পৃথিবীতে, প্যান্ডোরা যখন বাক্সটা বন্ধ করতে পারে তখন শুধু আশা রয়ে যায় সেই বাক্সে। পৃথিবীর প্রথম ও একমাত্র সর্বগুণে গুণান্বিত মানবী পৃথিবীর জন্য নিয়ে আসে নারকীয় দুর্ভোগ। অনেক কিছুর মতো এটাও দেবাশিসদার থেকেই শোনা। কিন্তু কী আছে দেবাশিসদার এই বাক্সে? বাক্সটায় কোনও লক নেই। এঁটে বসানো। মুখার্জি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেন সেটাকে খোলার। পারলেন না। ডালাটা এঁটে বসা। আমায় দিয়ে বললেন, “একবার দেখুন তো, যদি খুলতে পারেন…” বলেই সুজিতবাবুকে নির্দেশ দিলেন ফটোকপিগুলো করিয়ে আনতে। সুজিতবাবু ভীতু মানুষ। একটু থতোমতো খেয়ে চলে গেলেন।
আমিও বেশ কয়েকবার টানাটানি করলাম। নাহ। বাক্স খোলা যাচ্ছে না। এটা খোলার কোনও কায়দা আছে। এ বাক্স সাধারণ বাক্স না। ম্যাজিশিয়ানরা এই ধরনের বাক্স ব্যবহার করেন। কায়দামতো না হলে খোলা অসম্ভব। আশেপাশে বেশ কটা কাগজ ছড়িয়ে আছে। তাতে হিজিবিজি নোট। তার থেকে একটা কাগজ উঠিয়ে মুখার্জি বললেন, “দেখুন তো এটা কী?” একটা তালিকা বানাচ্ছিলেন দেবাশিসদা। কিছু শব্দ চেনা, কিছু অচেনা। সেই তালিকায় লেখা— পো… তৈমুর… স্টেজে খুন… প্রিয়নাথ… ডালান্ডা হাউস… সাইগারসন???!!!… গণপতি… তারিণী… ডিরেক্টর।
“কিছু বুঝতে পারছেন?” মুখার্জি বললেন।
“নাহ। সাইগারসন আর ডিরেক্টর নতুন চরিত্র। আগে এঁদের কথা শুনিনি।” মিথ্যেই বললাম। ডিরেক্টরের কথা ছিল সেই চিঠিতে।
“এক কাজ করুন। আপনি এই লিস্টটা ফটোকপি করে নিয়ে যান। আর ওই ম্যাগাজিনগুলোও, যেগুলো আপনার জন্যেই উনি তুলেছিলেন। আমার নম্বর তো রইলই। যদি কিছু ক্লু পান, ফোন করে দেবেন। আমাদের হাজার কাজ মশাই, এই এক বিচিকাটা কেস নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। ওদিকে এঁর বউকেও তো ইন্টারোগেট করতে হবে। যদি কিছু জানেন… বলা যায় না মশাই কার কোথায় কী খার থাকে…”
“আর এই বাক্সটা?” বললাম আমি।
“এটা স্টেশনে নিয়ে যাই। ওখানে খোলার চেষ্টা করতে হবে। কী পেলাম আপনাকে জানিয়ে দেবখন। আপনি বরং একটা কাজ করুন, আপনার ফটোকপিগুলো হয়ে গেছে মনে হয়। নিয়ে আসুন, তারপর চলুন রওনা হই। অনেক বেলা হল।”
আমি ফটোকপি আনতে পা বাড়ালাম। মুখার্জি আবার সেই বাক্স খোলায় মন দিলেন। ফিরে এসে দেখি ভদ্রলোক দরদর করে ঘামছেন, তবু খোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
“কী বালের বাক্স মশাই, কিছুতেই খোলা যায় না… এ তো ভাঙতে হবে যা মনে হচ্ছে।”
“প্যান্ডোরার বাক্স ভাঙবেন না, কী বেরিয়ে আসে কে জানে।” একটু হেসেই জবাব দিলাম আমি।
“আপনার কাজ হয়ে গেছে?”
আমি হ্যাঁ বলতেই, উনি “লাস্ট ট্রাই, একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে” বলে বাক্সটাকে এবার উপর নিচে না খুলে লম্বালম্বি রেখে পাশাপাশি খোলার চেষ্টা করলেন। কী অবাক কাণ্ড! ক্লিক করে একটা শব্দ হল। প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেছে। বাক্সটা পাশাপাশিই খোলে। আর খুলতেই ভিতরের জিনিসটা আমাদের নজরে এল। প্রথমে প্লাস্টিক ফয়েলে মোড়া কালচে একটা বস্তু মনে হচ্ছিল। ভালো করে দেখতে বুঝলাম কালচে তরল শুকিয়ে এসেছে ততক্ষণে। ম্যাজিক বক্সে প্লাস্টিকের ভিতরে কোনও অজানা জাদুতে চলে এসেছে দেবাশিসদার খুনের সেই এভিডেন্সটা, যেটা কাল থেকে হন্যে হয়ে পুলিশ খুঁজছিল। দেবাশিসদার দেহ থেকে ছিন্ন অণ্ডকোশ।
। দুই ।
আজ প্রায় দশদিন হয়ে গেল দেবাশিসদা মারা গেছেন। খুন হয়েছেন। খুনের কোনও কিনারা হয়নি এখনও। কলকাতায় ফিরে সবার আগে থানা থেকে বাইকটা উদ্ধার করলাম। কিছু টাকা খসল। কিন্তু উপায় নেই। বাইক ছাড়া কোনও কাজ করা যাবে না। এখন আমি ভাড়াবাড়িতে। নিজের খাটে বসে আছি। আমার চারদিকে একগাদা কাগজের তাড়া। বেশিরভাগই ফটোকপির পাতা। যত পড়ছি, তত গুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। দেবাশিসদা কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধা ছিল। বলতে পারেননি। আর যখন বলতে গেলেন, সময় পেলেন না। তার আগেই খুন হয়ে যেতে হল তাঁকে। কী জানতেন দেবাশিসদা, যার জন্য এমন নৃশংসভাবে তাঁকে মরতে হল? খাটে বসে এইসবই ভাবছিলাম। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে অদ্ভুত একটা দেখনদারি আছে। কেউ যেন নেটফ্লিক্সের টিভি সিরিজের স্ক্রিপ্ট লিখবে বলে প্লট সাজাচ্ছে। একমাত্র ভিক্টোরিয়ান গোয়েন্দা গল্পে এসব ঘটে। আজকালকার খুনখারাপি বড্ড পানসে। আর এখানে পদে পদে ড্রামা, যে ড্রামার অন্যতম অভিনেতা দেবাশিসদা নিজেই। ধরলাম দেবাশিসদাকে কেউ খুন করতে এল, তিনি লুকিয়ে বাথরুমে এলেন। এখানে অন্য যে-কোনো মানুষ হলে কাউকে ফোন করে বলত, “ভাই বাড়িতে লোক ঢুকেছে, আমায় বাঁচা”, কিংবা সোজা পুলিশে ফোন করত। উনি সে পথে গেলেনই না। আমি, যে চন্দননগরে থাকিই না, থাকি কলকাতায়, তাকে…. না না, ফোন না, হোয়াটসঅ্যাপ করলেন। তাও ঝাপসা একটা ছবি। পুলিশ যাতে আমায় খুঁজে পায়, তাই কাগজের নিচে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিলেন, “তুর্বসু জানে।” সোজা কথা, মরার আগে বাঁশ দিয়ে গেলেন। কিন্তু কেন? আবার সেই লোকই আমাদের বাড়ি দেখার দালাল সেজে জেঠিমার থেকে চাবি নিয়ে আমায় চিঠি লিখলেন? ফোনে বা সাক্ষাতে বলতে কী হয়েছিল? যে লোক নিজের বউকে অন্য লোকের সঙ্গে শুতে বাধ্য করে, সে-ই আবার বউয়ের পিছনে গোয়েন্দা লাগায় কেন? তাঁর খুনিও আবার তেমনি। সরাসরি বুকে ছুরি বিঁধিয়ে খুন কর, তা না করে প্রাচীন চিনা পদ্ধতি বেছে নিল। এটা কি নাইট্যশালা নাকি? মাঝে মাঝে সিরিয়াসলি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে এগুলো বাস্তবে ঘটছে, আমি কোনও সিনেমার সেটে নেই। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেদিন লাইব্রেরিয়ান সুজিতবাবু বলতে পারেননি, কে আগের দিন ওই বাক্স ধরেছে। চন্দননগর লাইব্রেরিতে অনেকেই আসেন। আর ওটা এমন জায়গা, একটু চোখের আড়ালে গিয়ে যে কেউ ওই জিনিসটা বাক্সে রাখতে পারে। ঠিক এই জায়গায় একটু নাড়া খেলাম। যে কেউ? না বোধহয়। এমন একজন, যে জানে সেই বাক্স কেমন করে খুলতে হয়। আমার আর অফিসারের সেদিন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিল সেই বাক্স খুলতে, কিন্তু অপরাধী সে সময় পাবে কোথায়? তাকে খুব দ্রুত এই বাক্স খুলতে হবে। সুতরাং দুটো ব্যাপার পরিষ্কার। এক, সে বাক্স খুলতে জানে, দুই, সে জানত এখানে বাক্সটা রাখা আছে। আবার সেই নাটুকেপনা। দেবাশিসদার অণ্ডকোশ এমন কোনও দামি বস্তু না যে সেটাকে বাক্সে সংগ্রহ রাখতে হবে। কেন কাটল জানি না, যদি বা কাটল, সামনেই গঙ্গা। ভাসিয়ে দিলে কে টের পেত? তা না করে এভাবে করার মানে কী? কিছুই হিসেবে মেলে না, যদি না… মাথাটা ঘুরে উঠল যেন… যদি না খুনি কোনও মেগালোম্যানিয়াক সাইকো হয়। খুনের চেয়ে দর্শকাম, এই থিয়েটারি ঢং তার কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কেন বা কাকে খুন নয়, কীভাবে খুন করা হচ্ছে সেটাই তার কাছে চরম আনন্দের বিষয়। খুন তার কাছে খেলা। এ খেলায় সে মন্ত্রী। সে যে-কোনো দিকে যে-কোনো চাল দিতে পারে। আর আমরা সবাই… আমি, দেবাশিসদা, অফিসার মুখার্জি, সবাই তাঁর হাতের বোড়ে। আমরা শুধু এক ঘর এক ঘর করে এগোচ্ছি। সে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গোটা দাবার ছকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর বলছে, “দ্যাখো, আমায় দ্যাখো।” আমার হাড় শিরশিরিয়ে উঠল। এ কার সঙ্গে মরণখেলায় নামলাম? কিন্তু একবার যখন খেলা শুরু হয়েছে, এর শেষ না দেখে উপায় নেই। আমি পালাতে পারি, কিন্তু লুকাতে পারব না। খুনি আমার অজান্তেই আমার মন পড়া শুরু করে দিয়েছে। সে জানত আমি যাবই নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে। আমার জন্যেই সে সাজিয়ে রেখেছিল দেবাশিসদার অণ্ডকোশ। একমাত্র তাহলেই হিসেব মেলে। আর তা যদি হয়, আমি নিশ্চিত, এই উন্মাদ, মেগ্যালোম্যানিয়াক খুনির পরের টার্গেট আমি।
দরজায় টোকা পড়ল। খুব আস্তে আস্তে। আমি জানি উর্ণা এসেছে। উর্ণা আমার বাড়িওয়ালার মেয়ে। ঝকঝকে মাথা। আমার মতো ভ্যাদভ্যাদে আলুসেদ্ধমার্কা না। আগে আমাকে বিশেষ পাত্তা দিত না। নিজের মতো থাকত। একদিন গড়িয়াহাটে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে মার্কেটিং করতে গিয়ে ওর পার্স চুরি যায়। পার্সে মোবাইল, এটিএম কার্ড সব ছিল। পুলিশ গা করেনি। এদিকে কেঁদে কেঁদে মেয়ের অবস্থা খারাপ। কাকু মানে ওর বাবা বাধ্য হয়ে আমায় বলেছিলেন যদি কিছু করতে পারি। এখানে আমি কিছুটা ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছিলাম। ওই এরিয়া ভজাদার নখদর্পণে। ভজাদা লোকাল গুন্ডা, আবার পার্টিরও নেতা। ওর সঙ্গে পরিচয় ওর ভাইয়ের বউয়ের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে। বউটা ভালো। ভাই সন্দেহবাতিক। সে যাই হোক, ভজাদার নজরের বাইরে ওদিকের পাতাটাও নড়ে না। ওকে জানাতেই বলল, “ঠিক কোথায় হয়েছে বলতে পারবি ভাই?” জেনে নিয়ে বললাম। “আধ ঘণ্টার মধ্যে ফোন করছি”, বলে ফোন রেখে দিল ভজাদা। ঠিক চল্লিশ মিনিট বাদে ফোন এল, “তুই গড়িয়াহাটের পুরোনো বইয়ের দোকানগুলোর সামনে চলে আয়। এসে আমায় একটা ফোন করবি। আমি চলে আসব।” বাইক নিয়ে গিয়ে দেখি বেদুইনের সামনে ভজাদা দাঁড়িয়ে, হাতে একটা চটের থলে। “চল ভিতরে চল”, বলে বেদুইনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে টেবিলে বসেই দুটো ফিশ রোল অর্ডার দিল। তারপর টেবিলে ব্যাগ উপুড় করতেই আমার চক্ষুস্থির। খুব কম করেও গোটা দশেক লেডিস পার্স!
“সকাল থেকে এই হয়েছে, এবার তোর কোনটা বেছে নে।”
“মানে! তুমি এগুলো পেলে কোথায়?”
“উঁহুঁ উঁহুঁ… ওসব প্রশ্ন করবি না। আম খাবার দরকার আম খা, আঁটি গুনে কী করবি?”
“কিন্তু আমি জানব কী করে কোনটা?”
“খুলে খুলে দেখ তবে। এটিএম কার্ড তো আছে বললি।”
ভাগ্য ভালো দ্বিতীয় পার্সটা খুলতেই পার্সে উর্ণার প্রেসিডেন্সির আই কার্ড পাওয়া গেল। আমি আবার দেখতে যাচ্ছিলাম ভিতরের সবকিছু ঠিকঠাক আছে নাকি। ভজাদা ধমক দিল, “দেখার কিচ্ছু দরকার নেই। এই ভজহরি মুখুজ্জেকে যখন বলেছিস, কোনও ব্যাটার ক্ষমতা নেই একটা কাগজ এদিক-ওদিক করার। আর মেয়েদের পার্স দেখতে নেই জানিস না?”
থতোমতো খেয়ে পার্স বন্ধ করে রাখলাম।
“মেয়েটা কে? লাভার?”
“আরে না, না। তেমন কিছু না। বাড়িওয়ালার মেয়ে।”
ততক্ষণে রোল এসে গেছে। ভজাদা রোল চিবুতে চিবুতে মিটিমিটি হাসতে লাগল, “শোন ভাই, কিছু না থাকলে এমন সুন্দরী মেয়ের পার্সের জন্য তুই সেই নর্থ কলকাতা থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে চলে আসতি না। ফি নিবি না নিশ্চয়ই…”
“ধুসস, এর জন্য ফি নেওয়া যায় নাকি?”
“তাই তো, তাই তো। এরপরেও বলবি শুধুই বাড়িওয়ালার মেয়ে! বাড়িওয়ালার জন্য এমন পিরিত তো গোটা কলকাতা শহরে কারও নেই রে… তোর বাড়িওয়ালা তো মহা ভাগ্যবান!”
কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, “বাকি পার্সগুলোর কী হবে?”
“কেন, তোর লাগবে? দরকার? গোয়েন্দাগিরি ভালো চলছে না বুঝি? নিয়ে যা যেটা খুশি…”
আমি আর কথা বাড়ালাম না। ফিরে এসে উর্ণাকে পার্স দিতেই ছলছল চোখে একগাল হেসে সেই যে “থ্যাঙ্কিউ তুর্বসুদা” বলেছিল, সেই আমাদের প্রথম কথা। তারপর প্রায় বছরখানেক কেটে গেছে। এর মধ্যে তিনবার আমরা গোলদিঘির ধারে গিয়ে বসেছি। দুদিন ভিক্টোরিয়া গেছি। ওর বাবা-মা জানেন না। জানলে আমাকে এই বাড়ি ছাড়তে হবে। বাড়িতে আমরা অপরিচিতর মতো থাকি। আমার ঘরে সচরাচর ও আসে না। এলেও দরজায় খুব মৃদু টোকা মারে। ঠিক এখন যেমন মারছে।
উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। ও সাততাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। মুখে একটা চাপা হাসি।
“আরে! তুমি পাগল নাকি? এই ভরদুপুরে আমার ঘরে! তোমার মা জানতে পারলে আমাকে বাড়িছাড়া করবে।”
ফিক করে হাসল উর্ণা। হাসলে ওর আক্কেলদাঁতটা দেখা যায়। ওকে আরও সুন্দরী লাগে। ডানদিকের ভুরুটা তুলে বলল, “মা বেরিয়েছে। জয়া মাসির বাড়ি। আসতে দেরি হবে। আর বাবা তো অফিস… তাই দেখতে এলাম, আমাদের ভাড়াটিয়া মশাই কী করছেন…”
“তা বেশ করেছ। আজ টিউশানি নেই?”
“নাহ। কী ব্যাপার বলো তো? আমি কি তোমায় খুব বিরক্ত করছি? এসে থেকে তাড়াতে চাইছ! ওকে চললাম। বাই।”
“আরে না, না…” প্রায় ছুটে গিয়ে ওর হাত টেনে ধরি। “আমি তো চাই তুমি সারাক্ষণ আমার কাছেই থাকো।”
“খুব পাকা পাকা কথা শিখেছ, তাই না… সরো তো। খাটটা একেবারে কাগজের গাদা বানিয়ে রেখেছ তো। কী ব্যাপার, প্রেমপত্র লিখছ নাকি?”
“সেটাই বাকি আছে। অনুপমের কোট করছে একজন আর প্রেমপত্র লিখছি নাকি আমি! এগুলো একটা কেসের ব্যাপারে… তোমাকে দেবাশিসদার কথা বলেছিলাম?”
“কোন দেবাশিসদা?” পা নাচাতে নাচাতে উর্ণা বলল।
“সেই যে চন্দননগরে থাকেন। খুব বিদ্বান মানুষ। বউ ছেড়ে চলে গেছে…”
“হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলে মনে পড়ছে অল্প অল্প। তাঁর কেস?”
“তাঁরই বলতে পারো। তিনি খুন হয়েছেন।”
উর্ণা বেশ চমকে গেল। ওর ঠোঁটদুটো ছোটো, তাই হাঁ করলে একেবারে পারফেক্ট ইংরাজি ‘ও’ অক্ষরের মতো দেখায়। তেমনটাই দেখাচ্ছিল।
“বলো কী? কবে?”
“দিন দশেক হল। কিন্তু সমস্যা সেখানে না। দেবাশিসদা কিছু একটা গোপন খবর জানতে পেরেছিলেন। তাই তাঁকে খুন হতে হল। সেটা যে কী, তা বোঝার চেষ্টাই চালাচ্ছি।”
আমার কথা শুনতে শুনতে খাটের কাগজগুলো গোছাচ্ছিল উর্ণা। হঠাৎ প্রশ্ন করল, “তা গোপন খবরের সঙ্গে এডগার অ্যালান পো-র কী সম্পর্ক?”
দেখলাম ওর হাতে সেই ফটোকপি করে আনা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাগুলো। তাতে পো-র ছবি।
“আসলে মারা যাবার কিছুদিন আগেই দেবাশিসদা একটা তালিকা বানিয়েছিলেন। তাতে শুরুতেই পো-র নাম। পো-কে নিয়ে পড়াশোনাও করছিলেন যা জেনেছি। তাই লোকটাকে নিয়ে পড়ছিলাম।”
“ও। তা কী কী জানলে পো সম্পর্কে?”
“গ্রাহামস পত্রিকার সম্পাদক, প্রথম আধুনিক গোয়েন্দাকাহিনির লেখক, আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ দুঁপ্য-র স্রষ্টা, দারুণ সব ভয়ের গল্পের লেখক, আর… আর হ্যাঁ, মারা গেছিলেন রহস্যজনকভাবে।”
“মানে? কীভাবে?”
“১৮৪৯ সালের ৩ অক্টোবর বাল্টিমোরের এক রাস্তার ধারে প্রায় সংজ্ঞাহীন পো-কে খুঁজে পান জেকব ওয়াকার নামে এক ভদ্রলোক। গায়ে প্রবল জ্বর। বিড়বিড় করে ভুল বকছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চারদিন পর তিনি মারা যান। গায়ের পোশাক যেটা পরেছিলেন, সেটা ওঁর না। কার, তা কেউ জানে না। সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। যেন কোনও হিংস্র পশুর নখের দাগ। অজ্ঞান অবস্থাতেই বহুবার রেনল্ডস বলে কাউকে একটা ডাকছিলেন। সে যে কে, তাও কেউ জানে না। মারা যাবার আগে নাকি শেষ কথা বলেছিলেন, ‘লর্ড, হেল্প মাই পুয়োর সোল।’ কীভাবে তাঁর এই দশা হল আজও রহস্য। রহস্যের এখানেই শেষ না, মারা যাবার পর তাঁর সমস্ত মেডিক্যাল রেকর্ড, মায় ডেথ সার্টিফিকেট সমেত গায়েব হয়ে যায়। পো-এর মৃত্যুর আসল কারণ কেউ জানে না। শুধু নানারকম কথা প্রচলিত। কেউ বলে স্বয়ং শয়তানের কাছে তিনি আত্মা বন্ধক রেখেছিলেন। শয়তানই তাঁর আত্মা চুষে নিয়েছে। এইসব আগে জানতাম না। এই ম্যাগাজিনটা পড়ে জানলাম।”
“বাহহ… এত কিছু লেখা আছে, আর ভদ্রলোক যে দারুণ কবিতা লিখতেন সে কথা নেই?”
“জানতাম, কবিতাটাই তোমার আগে চোখে পড়বে… আছে। দ্য র্যাভেন নামে একখানা কবিতার কথাও আছে বটে।”
“ব্যস! এটুকুই? আর উনি যে তৈমুরের কাব্যগাথা লিখলেন সে বিষয়ে কিচ্ছুটি লেখেনি?”
সারা পৃথিবীটা যেন আমার চোখের সামনে টলে গেল এক নিমেষে। ‘তৈমুরের কাব্যগাথা’ এই শব্দগুলো উর্ণা জানল কীভাবে? ওর তো এসব কিচ্ছু জানার কথা না।
আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখে উর্ণা কিছু আঁচ করল। বলল, “বুঝিয়ে বলব?”
আমি উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু ওপরে নিচে মাথা নাড়লাম। এইসব সময়ে উর্ণার ভিতরের মাস্টারি ভাবটা জেগে ওঠে। খাটের ওপর দুই পা তুলে বাবু হয়ে বসে বলল, “শোনো তবে। ১৮২৭ সালের কথা। পো-এর তখন আঠেরো বছর বয়স। ইচ্ছে কবিতা লিখে জগৎজয় করবেন। কিন্তু পকেটে রেস্ত নেই। এদিকে বাপ-মা মারা যাবার পর যে অ্যালান পরিবার তাঁর দেখাশোনা করত, তারাও বলল এবার পথ দ্যাখো। বেচারা পো এডগার পেরি নামে আমেরিকার সৈন্যদলে যোগ দিলেন। কিন্তু কবিতা লেখার নেশা তখনও কাটেনি। তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন নিজের কবিতার খাতাখানা। বোস্টন হারবারে মাসিক পাঁচ ডলার মাইনাতে কাজ পেলেন পো। সেই টাকা জমিয়ে সেই বছরই তাঁর কিছু কবিতার সংকলন প্রকাশের জন্য কেলভিন এফ এস থমাসকে ধরলেন। চল্লিশ পাতার এই বই মাত্র পঞ্চাশ কপি ছাপা হয়েছিল। মূল কবিতাটা ৪০৬ লাইনের। লর্ড বায়রনের স্টাইল অনুকরণ করে এশিয়ার বিখ্যাত বিজেতা তৈমুরলং-এর কাব্যগাথা। বইয়ের নাম ‘Tamerlane and Other Poems’। সঙ্গে আরও কিছু কবিতা। পো-এর প্রথম প্রকাশিত বইতে নিজের নাম অবধি দেননি তিনি। ‘বাই এ বোস্টোনিয়ান’ নামে ছাপা হয়েছিল সে বই।”
“হুম। বুঝলাম। কিন্তু এ তো দুশো বছর আগের গল্প। আজকের দিনে এই বইয়ের গুরুত্ব কোথায়?”
“কী বলছ হে তুর্বসু রায়?” বাক্স রহস্যের সিধুজ্যাঠার স্টাইলে বলে উঠল উর্ণা। ফেলুদা ওর ফেভারিট ডিটেকটিভ। সব বই মুখস্থ। “সারা বিশ্বে এখন মাত্র বারো কপি এই বইয়ের হদিশ পাওয়া গেছে। শেষ জানা কপিটা ক্রিস্টির নিলামের দোকানে কত টাকায় বিক্রি হয়েছে জানো?”
আবার পাশাপাশি মাথা নাড়লাম।
গালে একটা ঠোনা মেরে দিয়ে উর্ণা বলল, “জানো না তো জানো কী ডিটেকটিভ সাহেব? ফেলুদা হলে ঠিক বলে দিত। পাঁচ কোটি টাকা বুঝলে, পাঁ-আ-চ কোটি”, বলে হাতের পাঁচটা আঙুল আমার চোখের সামনে মেলে ধরল।
“তার মানে আজকে যদি সেই বইয়ের আর-এক কপির সন্ধান পাওয়া যায়?”
“তাহলে আমাদের পরের তিন প্রজন্মকে আর কিছু করেকম্মে খেতে হবে না। হেসেখেলে চলে যাবে।”
এই ‘আমাদের’ কথাটা আমার কানে বড্ড মধুর শোনাল। গলাটা অদ্ভুত গম্ভীর করে এবার একেবারে সিধুজ্যাঠাকে কোট করল উর্ণা, “গোল্ডমাইন, ফেলু, গোল্ডমাইন।”
। তিন ।
—দেবাশিসদার সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ?
—২০১১-র ডিসেম্বরে। অহর্নিশ পত্রিকার একটা অনুষ্ঠান ছিল জীবনানন্দ সভাঘরে। সেখানে দেবাশিস এসেছিল বক্তৃতা দিতে। অসম্ভব সুন্দর বলেছিল। অনুষ্ঠান শেষে পত্রিকার সম্পাদককে বলে আমিই আগ বাড়িয়ে পরিচয় করি।
—কী নিয়ে বলেছিলেন?
—উনিশ শতকের কলকাতার মনোচিকিৎসা।
—তারপর?
—আসলে আমি তখন এম.এ. করছিলাম। ইতিহাসে। আমার স্পেশাল পেপার ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, তাই দেবাশিসের বক্তৃতা শুনতে গেছিলাম। শোনার পর যখন আরও জানতে চাই, ও আমাকে ওর চন্দননগরের বাড়ি যেতে বলে। আমরা ফোন নম্বরও এক্সচেঞ্জ করি।
—আপনি গেছিলেন?
—হ্যাঁ, পরের হপ্তাতেই। এক রবিবার করে। ও আমাকে অনেক মেটেরিয়াল দিয়েছিল। সেখান থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়।
—আর বিয়ে?
—তিন মাসের মধ্যে। যাকে বলে ঝট মাঙ্গনি, পট বিহা। তখন যদি বুঝতাম… আসলে বাবা মারা গেছিলেন, মাও দেখলেন ছেলে ভালো। বিয়ে হয়ে গেল। তবে ঘটা করে কিছু হয়নি, জাস্ট কোর্ট ম্যারেজ। আমার মা, এক বান্ধবী, আর দেবাশিসের এক বন্ধু সাক্ষী দিয়েছিল।
—বিয়েটা কোথায় হয়েছিল?
—কলকাতাতেই। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে আমার পরিচিত এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছেন। বাণী রায়। তিনিই বিয়ে দিয়েছিলেন।
—দেবাশিসদা তো স্টেট আর্কাইভে চাকরি করতেন?
—হ্যাঁ, শেক্সপিয়র সরণিতে।
—কাজটা ঠিক কী ছিল জানেন?
—খুব মামুলি কাজ। ১৯৮০ সাল থেকে স্টেট আর্কাইভ বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষ বা পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিজেদের আর্কাইভে রাখতে থাকে, অবশ্যই সে পরিবারের অনুমতি নিয়ে। দেবাশিস এই বিভাগেই কাজ করত।
—কত সাল থেকে কত সাল অবধি এই সংগ্রহ রাখা?
—১৮৫৯ থেকে ১৯৪৭, মানে ধরুন ওই সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে স্বাধীনতা অবধি।
—এখানে দেবাশিসদার কাজটা ঠিক কী ছিল?
—ধরুন কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি বা তাঁর পরিবার তাঁদের সংগ্রহ আর্কাইভে দিতে চান। তাঁরা ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনিই দেবাশিসকে দায়িত্ব দেন, দেখেশুনে, বেছে, ক্যাটালগ করতে…
—দাঁড়ান, দাঁড়ান… এই ডিরেক্টর কে?
-ওমা! উনিই তো সর্বেসর্বা। স্টেট আর্কাইভের মাথা…
—আচ্ছা, বুঝলাম। তারপর?
—দেবাশিস ওর কাজ নিয়ে খুব একটা উৎসাহী ছিল না কোনও দিন। বরং ও নিজের পড়াশোনা, লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি, এসবে ডুবে থাকতে ভালোবাসত অনেক বেশি। বলত চাকরিটা নাকি জাস্ট পেট চালানো আর বই কেনার টাকা জোগাড়ের জন্য। চাকরির সঙ্গে ওর মনের যোগ ছিল না কোনও দিনই। তবে ২০১২-র শেষদিকে অবস্থাটা বদলে যায়।
—কীরকম?
—কোনও এক পরিবার থেকে তাদের পুর্বপুরুষের কোনও সংগ্রহ আর্কাইভে দেবার জন্য আবেদন করা হয়। দেবাশিস যায় দেখতে। ফিরে এসে ওর চোখমুখের অবস্থা দেখার মতো। চোখ যেন জ্বলছে। কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেলেও মানুষ এমন করে না। এখনও মনে আছে, সেই রাতে ও এক সেকেন্ড দুই চোখের পাতা এক করেনি। সারারাত অস্থিরভাবে হেঁটে বেড়িয়েছে।
—কারণ কিছু বলেছিলেন? মানে আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?
—করেছিলাম। বলেছিল এমন একটা কিছু পেয়েছে, যাতে কলকাতার ইতিহাস বদলে যাবে চিরকালের মতো। কিন্তু শুধু তা নয়, আরও একটা জিনিস ছিল ওর চোখে, যেটা আগে কোনও দিন দেখিনি…
—কী সেটা?
—লোভ। ভয়ানক এক লোভ। আর সে লোভ জ্ঞানের লোভ না, অর্থের লোভ।
—সেটা কী করে বুঝলেন?
—নানা কথার মধ্যে বেশ কয়েকবার বলেছিল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর কষ্ট করে এই ছোট্ট বাড়িতে থাকতে হবে না। সব ঠিকঠাক চললে আমরা কোটিপতি হয়ে যাব।
—আপনি জিজ্ঞাসা করেননি, উনি কী পেয়েছেন?
—না, আমি আসলে ওর কথাগুলো সিরিয়াসলি নিইনি। ওর বইপত্রের ব্যাপারে অদ্ভুত একটা অবশেসন ছিল। বিশেষ করে রেয়ার বইপত্রের ওপরে। আর তা নিয়ে অবলীলায় মিথ্যে কথাও বলত। আনাড়ি কেউ এলেই দেখাত ওর কাছে নাকি আসল হ্যালহেডের ব্যাকরণ, রামধন স্বর্ণালঙ্কারের কাঠখোদাইয়ের বই আছে। প্রচুর দামি। আসল কথা হল ওগুলো সব ফ্যাক্সিমিলি। নকল। হাজার টাকাও দাম না। কিন্তু বলত। বলেই আনন্দ। আমি প্রায়ই ওর বই গুছিয়ে দিতাম। একটা কাগজের টুকরো অবধি ফেলতে দিত না। সব নাকি রেয়ার, কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হবে। এই কোটির গল্প বিয়ের পরে এত শুনেছি যে, সেবার আর খুব একটা পাত্তা দিইনি।
—তারপর?
—তারপর থেকেই ও কেমন বদলে যেতে থাকে। খিটখিটে হয়ে যায়। কোনও দিন তালাচাবির হ্যাবিট ছিল না। একটা মোটা লাল ফাইলে কীসব কাগজ এনে ড্রয়ারে লক করে রাখে। কী জিনিস জিজ্ঞেস করতে খেঁকিয়ে উঠেছিল।
—আপনার কী মনে হয়? এই পরিবর্তনের পিছনে কী কারণ থাকতে পারে?
—আমি জানি না, সত্যিই জানি না। তবে আমার মনে হয় এই মিডিওকার জীবন ওর পছন্দ ছিল না। ও চাইত খ্যাতি, অর্থ, ক্ষমতা। কিন্তু ওর চাকরিতে সে সুযোগ ছিল না। কোনওভাবে ওর কাছে সে সুযোগ আসে। শুধু তাই না, ওর অন্য একটা চাহিদাও ছিল, সেটা পরে জেনেছি।
—কী?
—মানে… ও রেগুলার রেড লাইট এরিয়ায় যাওয়া শুরু করল। বদলটা আগেই চোখে পড়ছিল, মনের ভুল ভেবে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু মেয়েরা বোঝে, জানেন… আমার প্রতি ওর ইন্টারেস্ট কমে যাচ্ছিল। রাতে আলাদা খাটে শুত।
—রেড লাইট এরিয়াটা জানলেন কী করে?
—ওর এক বন্ধু আমায় বলল। ফোন করে। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। পরে ও নিজে আমায় গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে দেখাল ওই পাড়া থেকে বেরোচ্ছে…
—কোন পাড়া?
—বেশ্যাপাড়া। তবে আমাদের এই চন্দননগরের বেশ্যাপট্টিতে নিয়মিত যেত খবর পেয়েছি।
—এই বন্ধুটির নাম কী?
—মাপ করবেন। বলা যাবে না। আসলে আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি নাম জানাব না।
—আপনি সরাসরি দেবাশিসদাকে প্রশ্ন করেননি? তিনি কেন এমন করছেন?
—অবশ্যই করেছি।
—তাতে উনি কী বললেন?
—প্রথমে চমকে গেল। ভাবতে পারেনি আমি জানতে পারব। তারপর বহুবার জিজ্ঞেস করল আমায় কে বলেছে? আমি নাম বলিনি। নাম জানার জন্য আমাকে অনেক চাপ দিয়েছে। মেরেওছে। বলিনি।
—কেন বলেননি?
—বলব কেন? তাহলে তো ও সাবধান হয়ে যাবে। আমিও আর খবর পাব না।
—যাই হোক, বলুন।
—বলার আর কী আছে? ও পাগলের মতো কিছু একটার পিছনে পড়ে ছিল। অন্য কোনওদিকে নজর ছিল না। আমার দিকেও না। একদিন বলতে গেলাম, যা বলল তাতে ওর সঙ্গে আর কথা বলার প্রবৃত্তি জাগেনি।
—কী বলেছিলেন?
—দেখুন, আপনি আমার চেয়ে ছোটোই হবেন। আমার বলতে বাধছে।
—বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমার অবস্থাটা বুঝুন। দেবাশিসদা খুন হয়েছেন। আমিও যে কোনও দিন খুন হয়ে যেতে পারি… এখন একটাই উপায় আমার কাছে। মরি কি বাঁচি, দেবাশিসদার খুনি আমাকে ধরার আগে, আমায় তাকে ধরতে হবে… আমাকে ছোটো ভাই ভেবেই বলুন…
—ও একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দেয়। বলে, ও নাকি আর আমার শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, যেহেতু আমি স্ত্রী আর আমার প্রতি ওর একটা দায়িত্ব আছে, তাই ওর এক বন্ধুর সঙ্গে আমি চাইলেই শুতে পারি। ওর কোনও আপত্তি নেই।
—আপনি কী বললেন?
—কী বলব? এক ঘণ্টার মধ্যে সুটকেস গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছি…
—দাঁড়ান, দাঁড়ান… কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম উনি আপনাকে ওঁর বন্ধুর সঙ্গে শুতে বাধ্য করেছিলেন। শুধু তাই না, তার ছবিও তুলে রেখেছিলেন?
—এ মা!! ছিঃ… এই হল মুশকিল। আপনার কাছে একটু ভুল খবর গেছে। আমাদের ডিভোর্সের কেসে এই প্রসঙ্গটা উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু ছবি-টবি… ছিঃ। কে বলেছে আপনাকে?
—সে তো বলা যাবে না ম্যাডাম। ধরে নিন তিনিও আমার বন্ধু।
—তবে তিনি যার থেকে শুনেছেন ভুল শুনেছেন, বা নিজেই বাড়িয়ে বলেছেন। ছবি-টবি কিছু ছিল না।
—তারপর আর কোনও দিন দেবাশিসদার সঙ্গে কথা হয়নি?
—না। প্রবৃত্তি হয়নি। কোন এক চ্যালা জুটিয়েছিল। প্রায়ই সে আসত ওর কাছে। রাতের বেলায়।
—তার নাম জানেন?
—জানি না। জানার ইচ্ছে হয়নি।
—আপনার বর্তমান স্বামী…
—সুতনু? ও বেচারা মাটির মানুষ। আইটি-তে কাজ করে। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।
—এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়?
—স্কুলের বন্ধু ছিল। তবে দারুণ কিছু না। আমার এই ঘটনার পর যখন সেপারেশান চলে, তখন ও আবার ফেসবুকে যোগাযোগ করল। প্রচণ্ড মেন্টাল সাপোর্ট দিয়েছিল। ওই সেপারেশনের সময়ই আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ডিভোর্সের পরে বিয়ে করে নিই। আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছেন…
—অভিনন্দন। কত মাস?
—পাঁচ হবে। আর কিছুদিন পর থেকে চলাফেরা রেস্ট্রিক্ট করে দেব। যাই হোক, আমি উঠি তবে? এই অবস্থায় এতদূর আসতাম না, নেহাত আপনি এমনভাবে বললেন, না করতে পারলাম না। ও হ্যাঁ, আর-একটা কথা জানিয়ে রাখি। আমার যখন সেপারেশান চলছিল, তখনও দেবাশিস আমায় শান্তি দেয়নি। আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিল। সে খবরও আমার কাছে আছে। লোকটাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু কী অদ্ভুত দেখুন, ও মারা গেছে, আমার দুঃখ হবার কথা, হাজার হোক এককালের স্বামী তো… কিন্তু একটুও দুঃখ হচ্ছে না জানেন… আপনি হয়তো আমাকে খুব বাজে টাইপের মহিলা ভাবছেন…
—এ মা! না না। তা কেন হবে? আপনার জায়গায় থাকলে যে কেউ এমনটাই করত। আপনি এসব ভাববেনই না। এখন আপনার শরীর ভালো না। মন খুশি রাখুন। আপনাকে এতটা কষ্ট দিলাম বলে সরি। কিন্তু অনেক অনেক ধন্যবাদ…
—না, না, ঠিক আছে ঠিক আছে… আচ্ছা আমি তো আপনাকে কোনও দিন দেখিনি। দেবাশিসের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কীভাবে, সে গল্পটা তো শোনা হল না?
—সে আর-একদিন বলব। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে… আপাতত জেনে রাখুন একটা কেসের ব্যাপারেই…
—আর একটা কথা—
—বলুন
—আমাদের এই দেখা করা নিয়ে কেউ যেন কিচ্ছু না জানে। আমার স্বামী আমাকে একটা নতুন জীবন দিয়েছেন। দেবাশিসের মৃত্যুর পর পুলিশ ফোন করেছিল, তাতেই ও একটু আপসেট। ও যদি জানে আমি আবার সেই জীবনকে রিলিভ করছি, তবে বড্ড দুঃখ পাবে। প্লিজ কাউকে বলবেন না। আপনি এত করে অনুরোধ করলেন, তাই এলাম।
—কথা দিচ্ছি দিদি, বলব না। আপনি চলে যান। শরবতের দাম আমি দিয়ে দেব।
প্যারামাউন্টে দুটো ডাব শরবতের দাম মিটিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। এবার যেতে হবে স্টেট আর্কাইভে। ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে।
। চার।
স্টেট আর্কাইভের ডিরেক্টরের দেখা পাওয়াটা আরও কঠিন হতে পারত, কিন্তু এখানে একটা সুবিধে হল। উর্ণার কোনও এক মাসিও নাকি ওখানেই কাজ করেন। উনিই আমার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিয়েছেন। শেক্সপিয়র সরণিতে বিরাট নীল-সাদা বিল্ডিং। তিনটেয় সময় দিয়েছিলেন। যেতে যেতে প্রায় সাড়ে তিনটে হয়ে গেল। ভেবেছিলাম ভদ্রলোক রেগে যাবেন, কিন্তু কার্ড দিয়ে ঘরে মুখ বাড়াতেই একগাল হেসে “আসুন আসুন” বলে ডেকে নিলেন। চা-ও অফার করলেন। বুঝলাম ওঁর কাজের চাপ এখন বেশি নেই।
“অরুণ, তুমি একটু বিশুকে চা দিয়ে যেতে বলো তো”, বলে আমার দিকে ফিরলেন ভদ্রলোক। বাইরে নেমপ্লেটে নাম দেখেছি। প্রশান্ত মজুমদার।
—আমাকে আপনার কথা শর্মিষ্ঠা বলল। ও কে হয় আপনার?
—সত্যি বলতে কী, আমার সঙ্গে পরিচয় নেই। আমার বাড়িওয়ালার আত্মীয় উনি।
—অ। তা আমি কীভাবে হেল্প করতে পারি?
—দেবাশিস গুহকে নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল।
—সে তো পুলিশ এসেছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জেরা করে গেছে। অফিসের অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছে। আবার আপনি কেন?
—আজ্ঞে আমার সঙ্গে পুলিশের কোনও বিরোধ নেই। আমরা একসঙ্গেই কাজ করছি ধরে নিতে পারেন। আসলে দেবাশিসদা আমার কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর খুনটা মেনে নিতে পারছি না। তাই আমিও…
—ওহহ। ভালো, ভালো। আমি আগে কোনও দিন কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ দেখিনি, জানেন! এত বছরে এই প্রথম। তা বলুন, কী জিজ্ঞাসা করবেন?
—২০১২ সালের শেষের দিকে দেবাশিসদাকে কোনও একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ পরীক্ষা করে আর্কাইভ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সংগ্রহটা কার বা কী, সেটা জানার উপায় আছে?
—২০১২? সে তো অনেকদিন আগের কথা। তখন তো আমি এই চেয়ারে ছিলামও না। ডিরেক্টর মিসেস সেনের রিটায়ার করার পর সামুইবাবু চার্জে ছিলেন…
—আপনি কিছুই বলতে পারবেন না?
—না, না, তা কেন? ২০১২-তে আমি তখন চিফ আর্কাইভিস্ট। দেবাশিসের সঙ্গে ভালোই আলাপ ছিল। কিন্তু অনেকদিন তো হয়ে গেল। দাঁড়ান…
বলেই আবার সেই অরুণ নামের লোকটিকে ডেকে বললেন ২০১২-১৩ সালের অ্যাকুইজিশান খাতা নিয়ে আসতে। বিশু ততক্ষণে চা দিয়ে গেছে। দুধ ছাড়া লাল চা। সেই চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মজুমদার সাহেব একটা কাষ্ঠহাসি হাসলেন।
—দেবাশিস ছেলেটা খারাপ ছিল না। প্রচুর পড়াশোনা করত। কাজ বুঝত। কিন্তু হাই অ্যাম্বিশান ছিল। প্রায়ই বলত, এসব ছেড়েছুড়ে একদিন ঠিক বেরিয়ে যাব দেখবেন মজুমদারদা। শেষের দিকে অবশ্য নিয়মিত অফিস করত না। লেটে আসত। আসলে ফ্যামিলিতে একটু প্রবলেম ছিল, জানেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তা বলে খুন হয়ে যাবে, সেটা কোনও দিন ভাবিনি। এই তো, খাতা নিয়ে এসেছে।
অরুণ বগলে মোটা একটা খাতা নিয়ে ঢুকে গেছে। ডিরেক্টর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “২০১২-র কোন মাস বলতে পারবেন?”
—শেষের দিকে, আপনি অক্টোবর থেকে দেখুন।
—অক্টোবর… অক্টোবরে কিছু নেই। নভেম্বর… নভেম্বর… হ্যাঁ এই তো, নভেম্বরের ৩০ তারিখ বেশ কিছু জিনিস অ্যাকোয়ার করা হয়েছে। এই যে দেবাশিসের সই। দাঁড়ান, ডিসেম্বরটাও দেখে নিই। নাহ… এটাই হবে… এই যে…
খাতায় তাকিয়ে আমি মাথামুন্ডু কিছু বুঝলাম না। সরকারি খাতা বোঝা আমার সাধ্য নেই। তাই খুব বিনীতভাবে বললাম, “যদি কোথা থেকে আর কী সংগ্রহ করা হয়েছিল বলেন…”
—হুঁ। এবার মনে পড়ছে। মলয় কৃষ্ণ দত্ত, মানে হাটখোলার দত্তবাড়ির বংশধর। বোধহয় সব বেচে দিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছিল। ঠাকুরদার বাবার কিছু জিনিস দিয়ে যেতে চেয়েছিল।
—হাটখোলার দত্ত মানে?
—আপনি হাটখোলার দত্তদের নাম শোনেননি! বিরাট বনেদি বংশ মশাই। আমি অত কিছু জানতাম না। দেবাশিসের থেকেই শুনেছি। চিঠিটা ওরা তখনকার ডিরেক্টরকে করেছিল। উনি আমাকে মার্কা করে দেন। আমার থেকে চিঠিটা দেখে দেবাশিস জানায় যে ও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অ্যাকুইজিশান করবে। তখনই এদের পরিবারের গল্প শুনি…
—কী গল্প?
—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাটনা গুদামের আমদানি-রপ্তানি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন দেওয়ান জগৎরাম দত্ত। উনিই হাটখোলায় এঁদের আদি বাড়িটা তৈরি করেন। তাঁর দাদু রামচন্দ্র দত্তও ছিলেন কোম্পানির মুৎসুদ্দি। রাজনৈতিক কারণে গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁকে খুন হতে হয়। ৭৮, নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে এঁদের আদি বাড়িকে কিছুদিন আগেও লোকে পাখিওয়ালা বাড়ি বলত। প্রচুর পাখি ছিল এই বাড়িতে। এঁদের আদিপুরুষ নাকি পুরুষোত্তম দত্ত। আদিশূরের আমন্ত্রণে কৌলঞ্চ থেকে বাংলায় আসেন। কলকাতার ইতিহাস রচয়িতা প্রাণকৃষ্ণ দত্তও এঁদের বংশেরই ছেলে। তবে বড়ো বংশে যা হয়, এখন হাজার হাজার শাখাপ্রশাখা। কেউ কারও খবর রাখে না। সবাই নিজের নিজের মতো বাড়ি করেছে। কেউ বিদেশে থাকে, কেউ অন্য রাজ্যে, তবে দুর্গাপুজোটা কিন্তু এখনও নিয়ম করে হয়। ২০০ বছরের পুরোনো দুর্গাপুজো। ভাসানের দিন নীলকণ্ঠ পাখি ছাড়ে… জানেন না?
—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে টিভিতে।
—ওই বাড়ি।
—ও। তা ইনি কোন জন? যার জিনিসপত্র অ্যাকোয়ার করা হল?
—ইনি এক আশ্চর্য মানুষ। আমাদের পোড়া দেশে নাম পেলেন না। ইনি ছিলেন সেসময়ের নামকরা ডাক্তার। ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্ত। মহেন্দ্রলাল সরকারের ছাত্র। প্রথমদিকে মেডিক্যাল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ বিভাগে কাজ করতেন। পরে নিজেই মানসিক রোগীদের নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর অধ্যবসায় ফল দেয়। প্রথমে দেশি পাগলদের জন্য তৈরি ডালান্ডা হাউসের দায়িত্বে তাঁকে দেওয়া হয়, পরে ভবানীপুরে সাহেবদের পাগলাগারদের সুপার হয়ে নাকি রিটায়ার করেছিলেন। তখনকার দিনে খুব কম নেটিভই এমন সুযোগ পেতেন।
—বাপরে! দারুণ ব্যাপার তো! তাঁর কী কী জিনিস অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল?
—দাঁড়ান দেখি। লিস্ট আছে। এই তো, একটা ছবির খাতা, বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই, একটা ভার্নাকুলার ম্যানুস্ক্রিপ্ট, আর মিসেলেনিয়াস…
—ভার্নাকুলার ম্যানুস্ক্রিপ্ট মানে?
—বাংলায় লেখা পাণ্ডুলিপি।
—কীসের ওপরে?
—তা তো লেখা নেই। যা আছে তাই বলছি।
—এগুলো কি খুব জরুরি? মানে বই বাদে যা যা বললেন…
—দাঁড়ান। সঙ্গে একটা নোটশিট আছে। তাতে লেখা আছে এগুলো কেন অ্যাকোয়ার করা হল। এই তো, ছবির খাতাটা হল তখনকার দিনে করা অ্যানাটমি স্টাডি, বইগুলো তো রেয়ার বুকস লেখা, ম্যানুস্ক্রিপ্টের নোটে কী লেখা আছে শুনুন, পড়ছি, “দি আননেমড ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইজ এ ক্রনিকল অফ নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পোলিশ ইনভেস্টিগেশান”, মানে উনিশ শতকের কোনও পুলিশি তদন্তের কাহিনি। পাশে আবার পেনসিল দিয়ে দেবাশিস কী যেন লিখেছে, অনাথ? দেখুন তো, ঝাপসা হয়ে গেছে।
আমি দেখলাম। পেনসিলের লেখা অনেক জায়গায় উঠে গেছে। যা দেখা যাচ্ছে তা হল ….anath!!
—আচ্ছা, এই মিসেলেনিয়াসে কী ছিল?
—দাঁড়ান, নোট দেখি। হ্যাঁ, এই যে লেখা আছে। ওল্ড মেডিক্যাল রিপোর্ট, অটোপ্সি রিপোর্ট, লেটারস অ্যান্ড সাম পেজেস অফ এ ডায়রি।
আমি ভিতরে ভিতরে তখন প্রায় কাঁপছি।
—কার ডায়রি, কিছু লিখেছে?
—নাহ। তবে বিখ্যাত কারও হবে। নইলে সংগ্রহে রাখা হল কেন?
—আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?
—আসলে তখনকার ডিরেক্টর সাহেব ওঁকে খুব ভালোবাসতেন। দেবাশিস সরাসরি ওঁকেই রিপোর্ট করত। আমি তাই আর নাক গলাইনি।
—ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?
—এই একটা ব্যাপারে আমি আপনাকে হেল্প করতে পারব না। সামুইবাবু গতবছর হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তার আগেই রিটায়ার করেছিলেন অবশ্য।
—একটা অনুরোধ। আমি ওই ম্যানুস্ক্রিপ্ট আর ডায়রির পাতাগুলো দেখতে চাই।
—তাহলে একটু সমস্যা আছে। আপনাকে একটা চিঠি করতে হবে। আমাকেই। আমি অ্যাপ্রুভ করে দিলে আমাদেরই কারও সঙ্গে গিয়ে আপনাকে দেখতে হবে। কিছু নোট করার হলে করবেন। কিন্তু নিতে পারবেন না।
—অনেক ধন্যবাদ। আমি এক্ষুনি চিঠি লিখে দিচ্ছি।
—দিন তবে। আর এই অরুণের সঙ্গে চলে যান। ও আপনাকে দেখাবে।
—শেষ প্রশ্ন। দেবাশিসদা কি আপনার কাছে কিছু গচ্ছিত রেখে গেছিলেন?
—আরে বাবা না বলেছি তো… ওঁর সঙ্গে এতটাও ঘনিষ্ঠতা ছিল না আমার। আমার কাছে গচ্ছিত রাখতেই বা যাবে কেন? আপনি অরুণের সঙ্গে যান। একটা চিঠি করুন। তারপর যা দেখার দেখে নিন। আমাকে একটু কাজ করতে হবে।
এরপর আর বসা যায় না। হঠাৎ মজুমদার সাহেবের মেজাজ বিগড়াল কেন কে জানে!
চিঠি লিখে পারমিশান আসতে আসতে আধা ঘণ্টা লাগল। অরুণ বলে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে চললেন অ্যানেক্স রুমে। সারি সারি আলমারি গাদাগাদি করে রাখা। এর কোনোটার মধ্যেই আছে জিনিসগুলো। অরুণবাবুর হাতে একটা কাগজ। তাতে আলমারি আর ফাইলের নম্বর লেখা। ভুলভুলাইয়ার মতো গলিঘুঁজি ঘুরে অবশেষে একটা আলমারির সামনে দাঁড়ালাম আমরা। আলমারির গায়ে একটা নম্বর সাদা পেন্ট দিয়ে লেখা। অরুণবাবু প্রথমে সেই নম্বর মেলালেন। তারপর “এই আলমারি” বলে চাবি দিয়ে খুলে “কোন মাস যেন, নভেম্বর, তাই তো?” বলে নিচের দিক থেকে বার করলেন বড়ো একটা কাঠের বাক্স।
পাশেই একটা টেবিল; তার ওপরে রেখে এবার কাগজের সঙ্গে বাক্সের নম্বর মেলালেন তিনি।
—এটাতেই আছে সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট আর ডায়রির কাগজ।
বাক্স খুলতেই সুন্দর ছোটো ছোটো হাতে লেখা খুব পুরোনো একটা কাগজের বান্ডিল দেখতে পেলাম। লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। বেশ মোটা। ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেলে প্রায় একটা উপন্যাসের সমান হবে। হাতে তুলে নিয়ে প্রথমেই একটু অদ্ভুত লাগল। কেন জানি না। আমি পড়তে শুরু করলাম। লেখা আছে—
“যে সকল রোমহর্ষণকারী হত্যাকাণ্ডের নায়ক স্থির হয় না, অথবা যে সকল মোকদ্দমার হত্যাকারী পলায়িত অথবা লুক্কায়িত থাকেন, ঈশ্বর জানেন কেন সেই সকল মোকদ্দমা সন্ধানের ভার আমারই হস্তে পতিত হয়। ভুল বলিলাম। পতিত হইত। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর সুনামের সহিত কলিকাতা ডিটেকটিভ পুলিশের কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিয়াছি। আজই আমি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। এতকাল যে সকল মোকদ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য হইয়াছি, তাহা অনেক সময় দারোগার দপ্তরে প্রকাশ করিতাম।”
মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল, “প্রিয়নাথের শেষ হাড়!”
প্রথম পাতা পড়ে দ্বিতীয় পাতা পড়তে যাব, সুতো দিয়ে বাঁধা। অরুণবাবু বেশ গাঁইগুঁই করছিলেন। সুতো খোলার নিয়ম নেই, যা দেখার তাড়াতাড়ি দেখুন, পাঁচটা বেজে গেছে, অফিস টাইম শেষ ইত্যাদি, কিন্তু আমি তেমন পাত্তা না দিয়ে একটানে খুলে ফেললাম সুতোর গিঁট। বোধহয় কিছু ভুল হয়েছিল। হাত ফসকে ঝরঝর করে পড়ে গেল পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো। কিন্তু এ কী! এতক্ষণে বুঝলাম শুরুতেই কেন অদ্ভুত লেগেছিল। প্রথম পাতা বাদে প্রতিটা পাতা একেবারে চকচকে নতুন, আর ধবধবে সাদা। গোটা বাক্সে আর কিচ্ছুটি নেই।