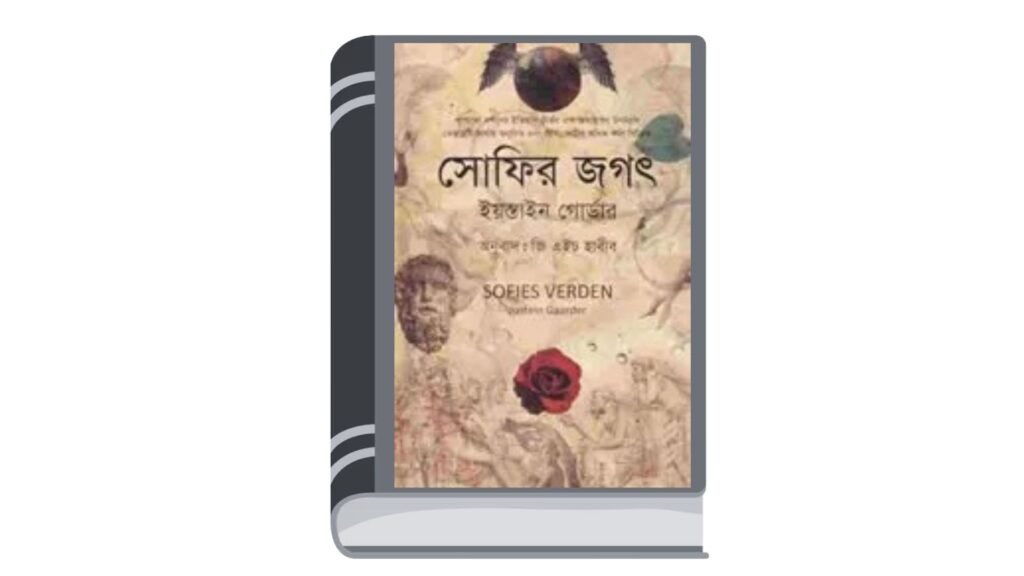১৫. মধ্য যুগ
১৫. মধ্য যুগ
…পথের কেবল খানিকটা যাওয়া আর ভুল পথে যাওয়া এক কথা নয়…
এক হপ্তা হলো অ্যালবার্টো নক্সের কোনো খবর নেই। লেবানন থেকেও কোনো পোস্ট কার্ড আসেনি, যদিও মেজরের কেবিনে পাওয়া সেই পোস্ট কার্ড নিয়ে সোফি আর জোয়ানা এখনো আলাপ করে। যারপরনাই ভয় পেয়েছিল জোয়ানা সেদিন, কিন্তু এরপর তেমন কিছুই আর না ঘটাতে সেই তাৎক্ষণিক আতংক মিইয়ে গেছে, ডুবে গেছে হোমওয়ার্ক আর ব্যাডমিন্টনের তলায়।
হিল্ডা-রহস্যের ওপর আলো ফেলবে এ-রকম কিছু সূত্রের আশায় অ্যালবার্টোর চিঠিগুলো বার বার করে পড়ল সোফি। এতে করে ধ্রুপদী দর্শন আত্মস্থ করার বেশ সুবিধে হয়ে গেল তার। ডেমোক্রিটাস আর সক্রেটিস কিংবা প্লেটো আর আরিস্টটলকে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করে চিনে নেয়ার কোনো সমস্যা। রইল না আর।
২৫ শে মে শুক্রবার সে তার মা বাড়ি ফেরার আগে ডিনারে তৈরি করছিলো। এটা বরাবরই তাদের শুক্রবারের ব্যবস্থা। আজ সে ফিশ বল আর গাজর দিয়ে ফিশ স্যুপ রান্না করছে।
বাইরে আবহাওয়াটা ক্রমেই ঝোড়ো হয়ে উঠছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাসেরোলটা নাড়ার সময় জানলার দিকে তাকাল সোফি। বার্চ গাছগুলো। শস্যমঞ্জরীর মতো দুলছে।
হঠাৎ কী যেন সে করে এসে লাগল উইন্ডোপেন-এ। ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে সোফি দেখল একটা কার্ড সেঁটে আছে জানলায়।
একটা পোস্টকার্ড। কাচের ভেতর দিয়েই পড়া যাচ্ছে: হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে, সোফি অ্যামুন্ডসেন।
ঠিক যা ভেবেছিল সে। জানলা খুলে কার্ডটা নিল সে। সেই লেবানন থেকে নিশ্চয়ই পুরো পথ উড়তে উড়তে আসেনি ওটা।
এই কার্ডটিতেও জুন ১৫-র তারিখ লেখা। স্টোভের ওপর থেকে ক্যাসেরোলটা নামিয়ে রাখল সোফি, তারপর বসল গিয়ে কিচেন টেবিল-এ। কার্ডটাতে লেখা:
প্রিয় হিল্ডা, কার্ডটা যখন তুই পড়বি তখনো তোর জন্মদিন থাকবে কিনা জানি না। আশা করছি থাকবে; অন্তত বেশ কিছু দিন পার হয়ে যাবে না। সোফির এক হপ্তা যে আমাদেরও এক হপ্তা হবে সে-রকম কোনো কথা নেই। আমি মিডসামার ঈভে বাড়ি আসছি, তখন ঘন্টার পর ঘন্টা গ্লাইডারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবো, হিল্ডা। মেলা কথা জমা হয়েছে আমাদের। ভালোবাসা নিস, তোর বাবা, যে কিনা ইহুদি, খ্রিস্টান আর মুসলিমদের মধ্যেকার হাজার বছরব্যাপী বিরোধের কথা ভেবে প্রায়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। নিজেকে আমার বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে এই তিনটে ধর্ম-ই শুরু হয়েছে আব্রাহাম থেকে। তাই আমার ধারণা তারা সবাই একই বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে। এদিকে কেইন আর অ্যাবেল এখনো পরস্পরকে বধ করা চালিয়ে যাচ্ছে।
পুনশ্চ: সোফিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিস, দয়া করে। বেচারী জানেও না। পুরো ব্যাপারটা কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে তুই সম্ভবত জানিস, তাই না?
.
মাথাটা টেবিলে রাখল সোফি একেবারে বিধ্বস্তের মতো। একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটার স্বরূপ তার একেবারেই জানা নেই। কিন্তু হিল্ডার সম্ভবত জানা আছে।
হিল্ডার বাবা যদি হিল্ডাকে বলে সোফিকে শুভেচ্ছা জানাতে, তার অর্থ দাঁড়ায় সোফি হিল্ডা সম্পর্কে যতটুকু জানে হিল্ডা সোফি সম্পর্কে তারচেয়ে বেশি জানে। ব্যাপারটা তার কাছে এতো জটিল বলে বোধ হলো যে সে আবার ডিনার তৈরি করায় মন দিল।
একটা পোস্টকার্ড, সেটা নিজে নিজেই এসে সেঁটে যায় রান্নাঘরের জানলায়। এর নাম দেয়া যেতে পারে বিমানডাক।
ক্যাসেরোলটা সে ফের স্টোভের ওপর বসাতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।
যদি বাবা হয়! সোফি মরিয়া হয়ে চাইল তার বাবা যেন বাড়ি আসে যাতে গত কয়েক হপ্তা ধরে যা ঘটেছে সে-সব সে বলতে পারে তাঁকে। কিন্তু দেখা যাবে ফোনটা আসলে জোয়ানা বা মা-র। সোফি ছোঁ মেরে ফোনটা তুলে নিল।
সোফি অ্যামুন্ডসেন, বলল সে।
আমি, ওপাশের কণ্ঠটা বলল।
তিনটে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল সোফি: ফোনটা তার বাবার নয়। কিন্তু গলাটা একজন পুরুষের আর গলাটা সে আগে শুনেছে কোথাও।
কে বলছেন?
অ্যালবাটো।
ওহহ।
কোনো কথা সরছিল না সোফির মুখে। সে চিনতে পারল এটা সেই অ্যাক্রোপলিসের ভিডিও-র গলা।
তুমি ঠিক আছে তো?
বিলক্ষণ।
এখন থেকে আর কোনো চিঠি নয়।
কিন্তু আমি তো আপনাকে কোনো ব্যাঙ পাঠাইনি!
আমাদের সামনা-সামনি দেখা হওয়া দরকার খুব। ব্যাপারটা বেশ জরুরি হয়ে উঠছে।
কেন?
হিল্ডার বাবা আমাদের কাছে এসে পড়ছে।
কীভাবে কাছে এসে পড়ছে?
সব দিক থেকে, সোফি। এবার আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
কীভাবে…?
কিন্তু মধ্যযুগ সম্পর্কে তোমাকে আমি বলার আগে তুমি খুব একটা সাহায্য করতে পারবে না। রেনেসাঁ আর সপ্তদশ শতাব্দীও কাভার করতে হবে আমাদের। বার্কলে একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র…
মেজরের কেবিনে তাঁর ছবিই তো ছিল, তাই না?
ঠিক। হয়তো আসল যুদ্ধটা হবে তার দর্শন নিয়েই।
আপনার কথায় একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব।
ব্যাপারটাকে আমি বরং ইচ্ছাশক্তির যুদ্ধ বলবো। আমাদেরকে হিল্ডার নজর কাড়তে হবে, তারপর তার বাবা লিলেস্যান্ডে আসার আগেই ওকে আমাদের দলে ভেড়াতে হবে।
কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।
হয়ত দার্শনিকরা তোমার চোখ খুলে দিতে পারবেন। আগামীকাল সকাল আটটায় সেন্ট মেরি গির্জায় দেখা করবে আমার সঙ্গে। তবে একা আসবে, মেয়ে।
এতো সকালে?
ক্লিক করে একটা শব্দ হলো টেলিফোনে।
হ্যালো?
রিসিভার রেখে দিয়েছেন উনি। ফিস স্যুপটা গরম হয়ে উপচে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সোফি দৌড়ে গিয়ে ক্যাসেরোলটা নামিয়ে রাখল স্টোভের ওপর থেকে।
সেন্ট মেরি-র গির্জা? পাথর দিয়ে তৈরি মধ্যযুগের একটা গির্জা ওটা। কনসার্ট আর খুবই বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের কাজেই কেবল ব্যবহার করা হয় গির্জাটা। গরমের সময় অবশ্য কখনো কখনো ট্যুরিস্টদের জন্যে খুলে দেয়া হয় ওটা। কিন্তু তাই বলে মাঝরাতে নিশ্চয়ই খোলা নেই গির্জাটা?
তার মা বাড়ি ফিরতে ফিরতে লেবানন থেকে আসা কার্ডটা সোফি অ্যালবার্টো আর হিল্ডার কাছ থেকে পাওয়া জিনিসের সঙ্গে রেখে দিয়েছে। ডিনারের পর জোয়ানার বাড়ি গেল সোফি।
তার বন্ধু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, খুবই বিশেষ একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।
জোয়ানা তার শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করার আগ পর্যন্ত আর কিছুই বলল না সে।
ব্যাপারটা একটু জটিল, সোফি আগের কথার খেই ধরে বলল।
খুলে বল।
মা-কে আমার বলতে হচ্ছে যে আমি আজ রাতটা এখানে থাকছি।
দারুণ!
কিন্তু ওটা আমি স্রেফ বলবোই শুধু, বুঝলি। আসলে আমি অন্য এক জায়গায় যাবো।
দ্যাটস্ ব্যাড। কোনো ছেলের সঙ্গে দেখা করবি বুঝি?
না, সেই হিল্ডা সংক্রান্ত ব্যাপার।
ছোট্ট করে শিষ দিয়ে উঠল জোয়ানা। কড়াভাবে তার চোখের দিকে তাকাল সোফি।
আজ সন্ধ্যায় আমি আসছি এখানে, বলল সে। কিন্তু সাতটার সময় আবার চুপিচুপি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যাপারটা সামলাতে হবে তোকে।
কিন্তু তুই যাচ্ছিস কোথায়? কী এমন ব্যাপার যা তোর না করলেই চলছে না?
দুঃখিত। আমি মুখ খুলতে পারছি না।
বাড়ির বাইরে ঘুমানোটা কখনোই কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেনি। প্রায় তার উল্টোটাই হয়েছে বরং। মাঝে মাঝে সোফির যেন মনে হয়েছে, বাড়িতে একা থাকাটা তার মা উপভোগই করেন।
ব্রেকফাস্ট করতে নিশ্চয়ই বাড়ি আসবি তুই? সোফি বেরুবার সময় কেবল এই মন্তব্যটা করলেন তিনি।
যদি না-ও আসি তুমি তো জানো-ই আমি কোথায় থাকবো।
এই কথাটা আবার সে বলতে গেল কেন? একটা খুঁত থেকে গেল।
সোফির সফরের শুরুটা অন্য যে-কোনো বারের বাইরে ঘুমনোর মতোই হলো, গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করল ওরা। একমাত্র তফাত্তা হোলো, শেষ পর্যন্ত ওরা যখন দুটোর সময় ঘুমোত গেল সোফি ঘড়িতে পৌনে সাতটায় এলার্ম দিয়ে রাখল।
পাঁচ ঘণ্টা পর সোফি যখন বাযারটা বন্ধ করছে, জোয়ানার ঘুম ভেঙে গেল তখন, অবশ্য নেহাতই অল্প সময়ের জন্য।
সাবধানে থাকিস, বিড়বিড় করে বলল সে।
সোফি রওনা হয়ে গেল। শহরের পুরনো অংশের বাইরের দিকটায় সেন্ট মেরি-র গির্জা। মাইল কয়েকের হাঁটা-পথ। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমোলে কী হবে, সোফির চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই।
পুরনো পাথুরে গির্জাটার প্রবেশপথের সামনে যখন এসে দাঁড়াল সে তখন প্রায় আটটা বাজে। বিশাল, ভারি দরজাটা খোলার চেষ্টা করল সোফি। দরজাটায় কোনো তালা নেই।
গির্জাটা যেমন পুরনো, সেটার ভেতরটাও ঠিক তেমনি নির্জন আর সুনসান। ঘষা-কাঁচের জানলাগুলোর ভেতর দিয়ে নীলাভ একটা আলো এসে বাতাসে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে ধূলিকণাকে দৃশ্যমান করে তুলছে। ধুলোগুলো মোটা কড়িকাঠের মতো এক জায়গায় জড়ো হয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে গির্জার ভেতরে। সোফি গির্জার মূল অংশের মধ্যেকার একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। অনুজ্জ্বল রঙে ছোপান ক্রশবিদ্ধ যীশুর একটা পুরনো মূর্তির নিচের বেদির দিকে তাকিয়ে রইল।
কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ করেই অর্গান বেজে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাবার সাহস হলো না সোফির। মনে হলো প্রাচীন কোনো স্তবগান, সম্ভবত মধ্য যুগের। ঘুরে তাকাবে নাকি? তার চেয়ে বরং কুশটার দিকে তাকিয়ে থাকাই স্থির করল সে।
তার পাশ দিয়ে আইল ধরে ওপরে উঠে গেল পদক্ষেপগুলো, সন্ন্যাসীর বাদামি পোষাক পরা একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সে। সোফি দিব্যি দিয়ে বলতে পারে ঠিক মধ্য যুগ থেকে উঠে এসেছেন সন্ন্যাসীটি।
একটু নার্ভাস বোধ করল সোফি, কিন্তু বুদ্ধি হারাল না। বেদিটার সামনে গিয়ে আধ পাক ঘুরলেন সন্ন্যাসীটি, উঠে পড়লেন সেটায়। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। মাথা নিচু করে সোফির দিকে তাকালেন, তারপর লাতিন ভাষায় তার উদ্দেশে বলে উঠলেন:
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper et in sæcula sæculorum. Amen.
কী যা তা বকছেন! সোফি চেঁচিয়ে উঠল।
তার গলা পুরনো পাথুরে গির্জার ভেতর প্রতিধ্বনি তুলল।
যদিও সে বুঝতে পারছিল যে সন্ন্যাসী লোকটি অ্যালবার্টো নক্স ছাড়া অন্য কেউ নন, কিন্তু তারপরেও ঈশ্বরের আরাধনার এই পবিত্রস্থানে এভাবে নিজে সে চেঁচিয়ে ওঠায় অনুতপ্ত বোধ করল সোফি। তবে কথা হলো সে আসলে নার্ভাস বোধ করছিল আর কেউ যখন নার্ভাস বোধ করে তখন সব ধরনের বিধি-নিষেধ অমান্য করাটা বড় স্বস্তিদায়ক।
শশশ! একটা হাত উঁচু করলেন অ্যালবার্টো, ঠিক যেমন পাদ্রীরা করেন যখন তারা সমবেত লোকজনকে শান্ত হতে বলেন।
মধ্য যুগ চারটার সময় শুরু হয়েছে, তিনি বললেন।
মধ্য যুগ চারটার সময় শুরু হয়েছে? বোকা বনে গিয়ে জিগ্যেস করল সোফি, অবশ্য এখন আর তার নার্ভাস লাগছে না।
হ্যাঁ, প্রায় চারটার সময়। আর তারপর পাঁচ, ছয়, সাতটা বাজল। কিন্তু মনে হলো সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। এরপর আট, নয়, দশ হবে। তারপরও সেটা মধ্য যুগ। তুমি হয়ত ভাববে একটা নতুন দিন শুরু হওয়ার সময় হয়েছে। বুঝতে পারছি, তুমি কী বলতে চাইছে। কিন্তু তা না হয়ে দিনটি রোববারই আছে। অসংখ্য রোববারের একটা লম্বা, অন্তহীন সারি। এরপর বাজবে এগারো, বারো, তেরো। এই সময়টাকে আমরা বলি হাই গথিক, ইউরোপের বড় বড় ক্যাথীড্রালগুলো এই সময়েই তৈরি হয়েছিল। তারপর, চৌদ্দটার কাছাকাছি সময়ে, অর্থাৎ বিকেল দুটোর সময় একটা কাক ডেকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হতে শুরু করল অন্তহীন মধ্য যুগ।
মধ্য যুগ তাহলে ছিল দশ ঘণ্টা, বলল সোফি। অ্যালবার্টো তাঁর সন্ন্যাসীর বাদামি আলখাল্লার ভেতর থেকে মাথাটা বের করে দিয়ে চোদ্দ বছর বয়েসী একটি মেয়েকে নিয়ে গঠিত তার ধর্মসভার দিকে তাকালেন।
প্রতিটি ঘণ্টা যদি একশো বছর হয় তাহলে তাই। আমরা ধরে নিতে পারি যীশুর জন্ম হয়েছে মধ্যরাত্রে। পল তার মিশনারী সফর শুরু করেছেন রাত সাড়ে বারোটার ঠিক আগে আর তার পনেরো মিনিট পর মারা গিয়েছেন রোমে। ভোর তিনটের দিকে খ্রিস্ট সম্প্রদায় একরকম নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো আর ৩১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তা রোমান সাম্রাজ্যে একটি স্বীকৃত ধর্মের মর্যাদা লাভ করল। সেটা সম্রাট কনস্টান্টিনের শাসনামল। খোদ হোলি এম্পেরর বা পবিত্র সম্রাটই বহুদিন পর তার মৃত্যুশয্যায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। ৩৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্ট ধর্ম গোটা রোমান সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম বলে স্বীকৃতি পেল।
রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল না?
পতন তখন শুরু হয়েছে সবে। সংস্কৃতির ইতিহাসে যত বড় বড় পরিবর্তন ঘটেছে তারই একটার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এখন। চতুর্থ শতাব্দীতে রোম দুদিক থেকেই হুমকির সম্মুখীন হতে শুরু করল, একদিকে বর্বররা উত্তর দিক থেকে গায়ের ওপর এসে পড়ছিল, অন্যদিকে ভেতর থেকেও শুরু হয়েছিল ক্ষয়। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে কন্সটান্টিন দ্য গ্রেট তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে কন্সটান্টিনোপল-এ স্থানান্ত রিত করলেন। কৃষ্ণ সাগরের মুখে অবস্থিত এই শহরটির পত্তন করেছিলেন তিনি ই। অনেকেই এই নতুন শহরটিকে দ্বিতীয় রোম মনে করত। ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল রোমান সাম্রাজ্য-রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল পশ্চিম সাম্রাজ্য আর নতুন শহর কন্সটান্টিনোপলকে রাজধানী হিসেবে রেখে একটি পূর্ব সাম্রাজ্য। ৪১০ খ্রিস্টাব্দে বর্বররা রোমে লুটতরাজ আর ধ্বংসযজ্ঞ চালায় আর ৪৭৬ এ গোটা পশ্চিম সাম্রাজ্য-ই ধ্বংস হয়ে যায়। ওদিকে পূর্ব সম্রাজ্য দাপটের সঙ্গেই। টিকে থাকে অনেক দিন, তারপর ১৯৫৩ সালে তুর্কীরা দখল করে নেয় কন্সটান্টিনোপল।
আর তখন সেটার নাম হয় ইস্তাম্বুল,তাই না?
ঠিক! আর ওই নামটাই এখনো আছে। আরেকটা তারিখও একটু মনে রাখতে হবে আমাদের আর সেটা হলো ৫২৯। এই বছরই খ্রিস্টানরা এথেন্সে প্লেটোর। একাডেমি বন্ধ করে দেয়। একই বছর প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত মঠভিত্তিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রথমটি– বেনেডিক্টিয় সম্প্রদায়। কাজেই খ্রিস্ট সম্প্রদায় কীভাবে গ্রীক দর্শনের মুখে কুলুপ এঁটে দিল তারই একটি প্রতীক হয়ে রইল ৫২৯ খ্রিস্টাব্দ। এরপর থেকে শিক্ষা, চিন্তা-ভাবনা এবং ধ্যান, ইত্যাদির একচেটিয়া এক্তিয়ার চলে গেল মঠগুলোর কাছে। ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে…
এই সময়গুলো দিয়ে অ্যালবার্টো কী বোঝাতে চাইছেন বুঝতে পারল সোফি। মধ্যরাত্রি ০, একটা হচ্ছে খ্রিস্টের জন্মের পর ১০০ বছর, ছটা খ্রিস্টের জন্মের পর ৬০০ বছর, চোদ্দটা হচ্ছে খ্রিস্টের জন্মের পর ১,৪০০ বছর…
অ্যালবার্টো বলে চললেন: মধ্য যুগ বলতে আসলে অন্য দুটো সময়ের মধ্যবর্তী সময়টাকে বোঝায়। রেনেসাঁ-র (Renaissance) সময়ই শোনা যেতে থাকে কথাটা। মধ্য যুগকে– সেটাকে অন্ধকার যুগ-ও বলা হতো– তখন প্রাচীনকাল আর রেনেসাঁ-র মাঝখানে ইউরোপে নেমে আসা এক হাজার বছরের দীর্ঘ একটা রাত হিসেবে দেখা হতো। মধ্যযুগীয় কথাটা ব্যবহৃত হয় অতি কর্তৃত্বপরায়ণ এবং অনমনীয় যে-কোনো কিছুকে বোঝাবার জন্য। কিন্তু এখন অনেক ইতিহাসবিদ-ই মধ্যযুগকে এক হাজার বছর স্থায়ী অংকুরোদগম আর ক্রমবৃদ্ধির সময় হিসেবে দেখে থাকেন। যেমন ধরো, স্কুল পদ্ধতির শুরু হয়েছিল মধ্য যুগেই। এই সময়ের গোড়ার দিকেই ভোলা হয়েছিল প্রথম কনভেন্ট স্কুলগুলো, তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে আসে ক্যাথড্রাল স্কুল। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্থাপিত হয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর সেখানে যে-সব বিষয় পড়ানো হতো সেগুলোকে নানান অনুষদ-এর অধীনে রাখা হয়েছিল, ঠিক যেমনটি করা হয় আজকের দিনে।
এক হাজার বছর সত্যিই খুব লম্বা সময়।
হ্যাঁ। তবে জনগণের কাছে পৌঁছাতে বেশ সময় লেগেছিল খ্রিস্ট ধর্মের। তাছাড়া, মধ্য যুগেই নানান শহর-নগর, নাগরিক আর লোকসঙ্গীত ও লোকগল্প নিয়ে গড়ে ওঠে নানান জাতি-রাষ্ট্র। মধ্যযুগ না থাকলে এতোসব রূপকথা আর লোকসঙ্গীত কী করে হতো বলো তো? এমনকী ইউরোপই বা কেমন হতো? একটা রোমান প্রদেশ, খুব সম্ভব। তারপরেও, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স কিংবা জার্মানী নামগুলো যে অনুরণন সৃষ্টি করে তা হলো অনন্ত অতল যে-জলধিকে আমরা মধ্য যুগ বলি ঠিক তাই। এই অথৈ জলে ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য চকচকে মাছ, যদিও সব সময় সেগুলোর দেখা মেলে না। স্মরি মধ্য যুগের লোক। সেন্ট ওলাফ আর শার্লামেন-ও তাই। রোমিও-জুলিয়েট, জোয়ান অভ আর্ক, ইভানহো, হ্যাঁমেলিনের বংশীবাদক এবং আরো শত শক্তিমান রাজপুত্র, জমকালো রাজা-মহারাজা, বীরধর্মব্রতী নাইট আর সুন্দরী রমণী, ঘষা-কাঁচের জানলার অজ্ঞাতপরিচয় নির্মাণকারী আর প্রতিভাবান অর্গান প্রস্তুতকারকের কথা তো না বললেও চলে। তারপরেও তো ফ্রায়ার, ক্রুসেড বা উইচদের কথা বলাই হয়নি।
পাদ্রীদের কথাও বলেননি আপনি।
হ্যাঁ, তাঁরাও আছেন। ভালো কথা, নরওয়েতে কিন্তু একাদশ শতাব্দীর আগে খ্রিস্ট ধর্ম আসেনি। তবে নর্ডিক দেশগুলো সব একসঙ্গে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। খ্রিস্ট ধর্মের উপরিতলের নিচে অখ্রিস্ট্রিয় বিশ্বাস-ও প্রচলিত ছিল আর এ-সব প্রাক-খ্রিস্টিয় উপাদানের অনেকগুলোই খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। যেমন ধরো, স্ক্যান্ডিনেভিয় বড়দিনের উৎসবে এই আজকের দিনেও অনেক খ্রিস্টিয় এবং প্রাচীন নর্স রীতিনীতি মিলেমিশে থাকে। এবং এক্ষেত্রে পুরনো সেই প্রবাদটা বেশ প্রযোজ্য: বিবাহিত লোকজনের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর চেহারা ধীরে ধীরে একই রকম হয়ে যেতে থাকে। ঠিক তেমনি ইউলিটাইড কুকি, ইউটিাইড পিগলেট আর ইউলিটাইড এইল প্রাচ্যের তিন জ্ঞানী ব্যক্তি আর বেথুলহেম-এর জাবনা-পাত্রের মতো চেহারা পেতে শুরু করে। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খ্রিস্টধর্ম-ই ধীরে ধীরে জীবনের প্রধান দর্শন হয়ে ওঠে। সেজন্যেই মধ্য যুগকে আমরা খ্রিস্টিয় সংস্কৃতির একটা ঐক্য বা সমন্বয় সাধনকারী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করে থাকি।
ব্যাপারটা তাহলে অতটা হতাশাজনক ছিল না?
৪০০ খ্রিস্টাব্দের পর প্রথম কয়েকটা শতকে সাংস্কৃতিক একটা অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। তবে রোমান সময়টা ছিল খুবই উঁচু মানসম্পন্ন সাংস্কৃতিক যুগ, যেখানে ছিল বড় বড় নগর, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, গণস্নানাগার; তাছাড়া জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্যের কথা তো বলাই বাহুল্য। মধ্যযুগের প্রথম কয়েক শতকে এই গোটা সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়ল। একই দশা ঘটল ব্যবসা-বাণিজ্য আর অর্থনীতির বেলাতেও। মধ্য যুগে লোকজন মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে পণ্যবিনিময় প্রথায় ফিরে গিয়েছিল। অর্থনীতিতে প্রচলিত হলো সামন্ত প্রথা (feudalism); এই সামন্ত প্রথায় অল্পসংখ্যক অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের হাতে জমির মালিকানা থাকত আর সার্ফ (serf) বা ভূমিদাসরা সেই জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রথম কয়েক শতকে জনসংখ্যাও হ্রাস পেয়েছিল বেশ। প্রাচীন যুগে রোমের জনসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষেরও বেশি। কিন্তু ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন রোমান রাজধানীর লোকসংখ্যা ঠেকল এসে ৪০,০০০-এ, আগের জনসংখ্যার স্রেফ এক ভগ্নাংশে। অর্থাৎ নগরটির সাবেক গৌরবের চিহ্ন নিয়ে আঁকাল সব স্মৃতিচিহ্নবাহী প্রাসাদ আর অট্টালিকার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তারই ভেতর ঘুরে-ফিরে বেড়াবার জন্যে রয়ে গেল তুলনামূলকভাবে অল্পসংখ্যক একটি জনগোষ্ঠী। তাদের নির্মাণ সামগ্রীর প্রয়োজন মেটাতো অগুনতি সব ধ্বংসাবশেষ। স্বাভাবিকভাবেই, এতে করে বর্তমান যুগের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নিদারুণ দুঃখ পেয়েছেন, প্রাচীন যুগের এ-সব স্মৃতিস্তম্ভ বা চিহ্নগুলোতে মধ্য যুগের মানুষেরা হাত না দিলেই বরং খুশি হতেন তারা।
কোনো কিছু ঘটে গেলে তারপর সে-সম্পর্কে জানাটা সহজ হয়।
রাজনৈতিক দিক দিয়ে অবশ্য চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকেই যবনিকা পতন ঘটে গিয়েছিল রোমান যুগের। সে যাই হোক, কালে রোমের বিশপ-ই রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে পোপ– লাতিন ভাষায় পাপা, যার অর্থ বাবা– উপাধি দেয়া হলো এবং কালক্রমে তাকে দেখা হতে লাগল পৃথিবীতে যীশু খ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসেবে। এভাবেই, মধ্য যুগের প্রায় পুরো সময়টাতে রোম-ই ছিল খ্রিস্ট ধর্মের রাজধানী। কিন্তু নতুন নতুন জাতি রাষ্ট্রের রাজা আর বিশপেরা ক্রমেই আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে তাঁদের কেউ কেউ গির্জার শক্তি ও সম্পদের বিরুদ্ধেও মাথা তুলে দাঁড়ালেন।
আপনি বললেন খ্রিস্টানরা এথেন্সে প্লেটোর একাডেমি বন্ধ করে দিয়েছিল। তার মানে কি এই যে গ্রীক দার্শনিকদের সবাই ভুলে গিয়েছিল?
পুরোপুরি নয়। অ্যারিস্টটল আর প্লেটোর কিছু লেখার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। কিন্তু প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপে রইল লাতিনিয় খ্রিস্টান সংস্কৃতি, রোমকে রাজধানী হিসেবে নিয়ে। পূর্ব ইউরোপে কন্সটান্টিনোপলকে রাজধানী হিসেবে নিয়ে রইল গ্রীক খ্রিস্ট সংস্কৃতি। এই নগরটি পরিচিত হলো সেটার গ্রীক নাম বাইজেন্টিয়াম (Byzantium) হিসেবে। সেজন্যেই আমরা বলি বাইজেন্টিয় মধ্য যুগ বনাম রোমান ক্যাথলিক মধ্য যুগ। অবশ্য উত্তর আফ্রিকা আর মধ্য প্রাচ্য-ও রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। মধ্য যুগে এই অঞ্চলটি আরবিভাষী অধ্যুষিত মুসলিম সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে ওঠে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ-এর মৃত্যুর পর মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা ইসলামের পতাকাতলে চলে যায়। এর কিছুদিন পর স্পেন-ও ইসলামি সংস্কৃতি বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম আর বাগদাদকে ইসলাম পবিত্র নগর হিসেবে গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে যে-বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষণীয় তা হলো আরবরা প্রাচীন হেলেনিস্টিক নগর আলেকজান্দ্রিয়া-ও জয় করেছিল। ফলে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের অনেকটাই আরবরা পেয়েছিল উত্তরাধিকারসূত্রে। গোটা মধ্য যুগ জুড়ে বিজ্ঞানের এই শাখাগুলোতে গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা আর চিকিৎসাশাস্ত্রে আরবরা শীর্ষস্থানে ছিল। এখনো আমরা আরবি সংখ্যা ব্যবহার করি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে আরবিয় সংস্কৃতি খ্রিস্টান সংস্কৃতির চেয়ে এগিয়ে ছিল।
আমি জানতে চাই গ্রীক দর্শনের কী হলো।
একটা নদীর কথা কল্পনা করো তো যেটা তিনটে ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে কিছু দূর চলার পর আবার এক বিশাল চওড়া নদীতে পরিণত হয়েছে।
করলাম।
বেশ, তাহলে তুমি এটাও বুঝতে পারবে কী করে গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতি বিভক্ত হয়ে তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বেঁচে রইল: পশ্চিমে রোমান ক্যাথলিক সংস্কৃতি, পুবে বাইজেন্টিয় আর দক্ষিণে আরবিয়। ব্যাপারটা অতিসরলীকরণ হয়ে যায়, তারপরেও এটা বলা চলে যে পশ্চিমে চলে এলো নব্য-প্লেটোবাদ, পুবে প্লেটো আর দক্ষিণে আরবদের কাছে অ্যারিস্টটল। কিন্তু এই তিন ধারাতেই সবগুলোরই কিছু না কিছু ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মধ্য যুগের শেষের দিকে এই তিনটি ধারাই এসে মিলিত হলো ইতালির উত্তরাংশে। আরবিয় প্রভাবটি আসে স্পেনের আরবদের কাছ থেকে, গ্রীক প্রভাব আসে গ্রীস আর বাইজেন্টিয় সাম্রাজ্য থেকে। এবার আমরা দেখতে পাই রেনেসা-র সূচনা পর্বটি, যা কিনা প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্জন্ম। এক অর্থে বলতে গেলে, প্রাচীন সংস্কৃতি অন্ধকার যুগটির পরেও টিকে গেল।
বুঝতে পারছি।
কিন্তু তাই বলে ঘটনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে কিছু ভেবে নেয়াটা উচিত হবে না। তার আগে আমরা মধ্য যুগের দর্শন নিয়ে কিছু কথা বলব। আমি আর এই বেদি থেকে কথা বলব না। নিচে নেমে আসছি।
ঘুম তেমন না হওয়াতে সোফির চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। অদ্ভুত সন্ন্যাসীটিকে সেন্ট মেরি-র গির্জার বেদি থেকে নেমে আসতে দেখে তার স্বপ্নের মতো মনে হলো।
বেদির রেইল-এর দিকে হেঁটে এলেন অ্যালবার্টো। মুখ তুলে তাকালেন প্রাচীন ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তিসহ বেদিটার দিকে, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে এলেন সোফির দিকে। তারপর তার পাশে উপাসকের জন্য সংরক্ষিত আসনে (pew) বসে পড়লেন।
ভদ্রলোকটিকে এতো কাছে দেখতে পেয়ে কেমন অদ্ভুত লাগল সোফির। মস্ত কাবরণ সহ তার আলখাল্লার ভেতর একজোড়া গভীর বাদামি চোখ দেখতে পেল সে। চোখ দুটো কালো চুল আর সুচালো দাড়িবিশিষ্ট একটি মধ্যবয়স্ক মানুষের। কে আপনি? ভাবল সোফি। কেন আপনি আমার জীবন এভাবে উল্টে দিলেন?
ধীরে ধীরে আমরা একে অন্যকে আরো ভালোভাবে জানবো, যেন সোফির মনের কথা পড়ে নিয়ে বললেন তিনি।
দুজনে যখন ঘষা-কাঁচের জানলার ভেতর দিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়া তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে আসা আলোর মধ্যে বসেছে, অ্যালবার্ট নক্স বলতে শুরু করলেন মধ্য যুগের দর্শনের কথা।
মধ্য যুগের দার্শনিকেরা এ-কথা প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে খ্রিস্ট ধর্ম সত্য, শুরু করলেন তিনি। প্রশ্ন ছিল কেবল এই যে, আমাদেরকে কি খ্রিস্টিয় প্রত্যাদেশ বিশ্বাস করতে হবে, নাকি খ্রিস্টিয় সত্যগুলোর দিকে আমরা আমাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে এগোতে পারবো। গ্রীক দার্শনিকেরা যা বলেছেন তার সঙ্গে বাইবেল-এর কথার সম্পর্ক কোথায়? বাইবেল আর প্রজ্ঞা মধ্যে কি কোনো বিরোধ আছে, নাকি বিশ্বাস আর জ্ঞানের সহাবস্থান সম্ভব? মধ্য যুগের দর্শনের প্রায় পুরোটা আবর্তিত হয়েছে এই একটি প্রশ্নকে ঘিরে।
অধৈর্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল সোফি। এ-সব কথা সে তাদের ধর্ম ক্লাশেই শুনেছে।
আমরা দেখব মধ্য যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত দুই দার্শনিক কীভাবে এই প্রশ্নের সঙ্গে বোঝাঁপড়া করেছেন এবং আমরা শুরু করবো সেন্ট অগাস্টিনকে (St. Augustine) দিয়ে, যার জন্ম ৩৫৪-তে মৃত্যু ৪৩০-এ। এই একজন মানুষের জীবনের দিকে তাকালেই প্রাচীন যুগের শেষ অংশ থেকে মধ্য যুগের প্রথম অংশে পর্বান্তরের চিত্রটি দেখতে পাবো আমরা। উত্তর আফ্রিকার ছোট্ট শহর তাগাস্তে-তে জন্মেছিলেন সেন্ট অগাস্টিন। ষোল বছর বয়েসে কার্থেজে গেলেন পড়াশুনা করতে। পরে তিনি রোম আর মিলান ভ্রমণ করেন এবং জীবনের শেষ অংশটা কাটান কার্থেজ থেকে মাইল কয়েক পশ্চিমের একটি ছোট্ট শহর হিপ্পো-তে। তিনি অবশ্য জন্মসূত্রে খ্রিস্টান ছিলেন না। বরং খ্রিস্টান হওয়ার আগে তিনি বেশ কিছু ধর্ম এবং দর্শন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন।
যেমন?
জীবনের কিছু সময় তিনি ছিলেন ম্যানিকিয় (Manichaen)। ম্যানিকিয়রা ছিল প্রাচীন যুগের শেষ পর্বের চরম বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাদের মতবাদের আদ্ধেক ধর্ম, আদ্ধেক দর্শন। তাঁরা বলতেন জগৎ ভালো আর মন্দ, আলো আর আঁধার, মন আর বস্তু, এই দ্বৈতবাদের তৈরি। মানবজাতি তার মন-এর সাহায্যে বস্তু জগতের ওপরে উঠে তার আত্মার মুক্তিলাভের জন্যে তৈরি হতে পারে। কিন্তু ভালো এবং মন্দের মধ্যেকার এই সুস্পষ্ট বিভাজন তরুণ অগাস্টিনের মনে কোনো শান্তি আনতে পারল না। তার মন পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে রইল আমরা যাকে মন্দ সংক্রান্ত সমস্যা (problem of evil) বলি তাই নিয়ে। এই কথাটির সাহায্যে আমরা বুঝাই মন্দ বা অশুভ কোথা থেকে এলো, এই প্রশ্নটি। একটা সময় তার ওপর স্টোয়িক দর্শন খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং স্টোয়িক মত অনুযায়ী ভালো এবং মন্দের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো বিভেদ নেই। তবে তিনি মূলত আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রাচীন যুগের শেষ পর্বের বাকি যে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন ছিল, নব্য-প্লেটোবাদ, সেটার প্রতি। এই সুবাদে, জগতে অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছুই যে স্বর্গীয় এই ধারণার সংস্পর্শে আসেন, তিনি।
তো, এরপর তাহলে তিনি নব্য-প্লেটোবাদী বিশপ হলেন বুঝি?
হ্যাঁ, তা বলতে পারো, তুমি। তিনি প্রথমে খ্রিস্টান হলেন, তবে সেন্ট অগাস্টিনের খ্রিস্ট ধর্ম ছিল অনেকটাই প্লেটোনিক ধারণা প্রভাবিত। কাজেই, সোফি, এই ব্যাপারটি তোমাকে বুঝতে হবে যে খ্রিস্টিয় মধ্য যুগে পা দেয়া মাত্রই আমরা। গ্রীক দর্শন থেকে একেবারে নাটকীয়ভাবে ভিন্ন কোনো কিছু পাবো না। গ্রীক দর্শনের অনেকটাই সেন্ট অগাস্টিনের মতো গির্জার পাদ্রীদের মাধ্যমে নতুন যুগে চলে এসেছিল।
তাহলে সেন্ট অগাস্টিন আধা খ্রিস্টান এবং আধা নব্য-প্লেটোবাদী ছিলেন বলছেন?
তিনি নিজে মনে করতেন তিনি শতকরা একশো ভাগ খ্রিস্টান, যদিও খ্রিস্ট ধর্ম আর প্লেটোর দর্শনের মধ্যে সত্যিকারের কোনো বিরোধ আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে প্লেটো আর খ্রিস্টিয় মতবাদের মধ্যেকার সাদৃশ্য এতোটাই পরিষ্কার যে তিনি ভাবতেন প্লেটো নিশ্চয়ই ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পর্কে জানতেন। সেটা অবশ্য ভীষণ অসম্ভব একটা ব্যাপার। আমরা বরং বলতে পারি সেন্ট অগাস্টিন-ই প্লেটোকে খ্রিস্টান বানিয়েছেন।
তাহলে খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করার পর তিনি দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন সব কিছুর দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়াননি?
না, তবে তিনি মন্তব্য করেছেন যে ধর্মীয় প্রসঙ্গে প্রজ্ঞার এক্তিয়ারের একটা সীমারেখা রয়েছে। খ্রিস্ট ধর্ম একটি স্বর্গীয় রহস্য, যা কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমেই বোঝা বা উপলব্ধি করা সম্ভব। তবে আমরা যদি খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস করি তাহলে ঈশ্বর আমাদের আত্মা এমনভাবে আলোকিত করবেন যাতে করে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত জ্ঞানলাভ করবো। সেন্ট অগাস্টিন উপলব্ধি করেছিলেন যে দর্শন কতদূর যেতে পারবে তার একটা সীমা রয়েছে। খ্রিস্টান হওয়ার পরেই কেবল তার আত্মা প্রশান্তি লাভ করেছিল। তিনি লিখেছেন, তোমার মধ্যে ঠাই না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আত্মা শান্তি পায় না।
আমি ঠিক বুঝতে পারছি না প্লেটোর ধারণা আর খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে কীভাবে মিল থাকতে পারে, সোফি আপত্তি জানাল। সেই শাশ্বত ভাবগুলোর কী হবে?
দেখো, সেন্ট অগাস্টিন এ-কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর এ-জগৎ শূন্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং এটা একটা বাইবেলিয় ধারণা। ওদিকে গ্রীকরা বরং এ-কথা বিশ্বাস করতেই পছন্দ করত যে জগৎ-এর অস্তিত্ব সব সময়ই ছিল। কিন্তু সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার আগে ভাবগুলো ছিল স্বর্গীয় মন-এর মধ্যে। কাজেই প্লেটোনিক ভাবগুলোকে তিনি ঈশ্বরের ওপর ন্যস্ত করলেন আর এভাবেই শাশ্বত ভাব সম্পর্কে প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গিকে রক্ষা করলেন।
এটা অবশ্য দারুণ বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে।
তবে ব্যাপারটা এদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে কী করে শুধু সেন্ট অগাস্টিন-ই নয়, অন্যান্য খ্রিস্টিয় পাদ্রীও পিছু ফিরে তাকিয়েছিলেন গ্রীক আর ইহুদি চিন্তাধারাগুলোকে এক করার জন্যে। এক অর্থে দুটো দুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অগাস্টিন মন্দত্ব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও নব্য-প্লেটোবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। প্লটিনাসের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন মন্দ হলো ঈশ্বরের অনুপস্থিতি। মন্দের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, এটা হলো এমন কিছু যা নেই। কারণ, ঈশ্বরের সৃষ্টি কেবল ভালোই, অন্য কিছু নয়। মন্দ আসে মানবজাতির অবাধ্যতা থেকে, অগাস্টিন তাই ভাবতেন। অথবা, তার কথায়, শুভ ইচ্ছা ঈশ্বরের কাজ; মন্দ ইচ্ছা ঈশ্বরের কাজ থেকে বিচ্যুত হওয়া।
তিনি কি এ-কথাও বিশ্বাস করতেন যে মানুষের আত্মা স্বর্গীয়?
হ্যাঁ এবং না। সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর আর জগতের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ বাধার প্রাচীর রয়েছে। এদিক থেকে তিনি প্রতিটি জিনিস-ই এক, প্লটিনাসের এই মতবাদকে অস্বীকার করে বাইবেলিয় মতকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। কিন্তু, তারপরেও তিনি এই ব্যাপারটিতে জোর দিয়েছেন যে মানুষ আধ্যাত্মিক প্রাণী। কিন্তু দেহটি বস্তুগত-আর তা রয়েছে বাস্তব জগতেই, যে-জগতকে মথপোকা আর মরিচা বিনষ্ট করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার একটি আত্মা-ও আছে যা ঈশ্বরকে জানতে পারে।
তা, আমরা যখন মারা যাই তখন আত্মার কী হয়?
সেন্ট অগাস্টিনের মতানুসারে, মানুষের পতনের পর গোটা মানবজাতিই পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তারপরেও ঈশ্বর ঠিক করেন যে বিশেষ কিছু লোককে নরকবাসের হাত থেকে রেহাই দেয়া হবে।
সেক্ষেত্রে তো ঈশ্বর ঠিক একইভাবে ইচ্ছে করলে সবাইকেই রেহাই দিতে পারতেন।
যদ্দূর জানা যায়, সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের সমালোচনা করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। এ-প্রসঙ্গে তিনি রোমানদের উদ্দেশে লেখা পলের চিঠির উল্লেখ করতেন: হে মনুষ্য, বরং তুমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিবাদ করিতেছ? নির্মিত বস্তু কি নির্মাতাকে বলিতে পারে আমাকে এরূপ কেন গড়িলে? কিম্বা কাদার উপরে কুম্ভকারের কি এমন অধিকার নাই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে একটি সমাদরের পাত্র আর একটা অনাদরের পাত্র গড়িতে পারে?
তো, ঈশ্বর তাহলে স্বর্গে বসে মানুষকে নিয়ে খেলা করে যাবেন? এবং যখনই তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টির ওপর অসন্তুষ্ট হবেন তখন সেটাকে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দেবেন?
সেন্ট অগাস্টিনের কথা হলো, কোনো মানুষই ঈশ্বরের ক্ষমার যোগ্য নয়। কিন্তু তারপরেও তিনি কিছু মানুষকে নরকভোগ থেকে রেহাই দেবেন বলে নির্বাচন করেছেন, কাজেই কে রেহাই পাবে আর না পাবে তা নিয়ে তার কাছে লুকোছাপার কিছু ছিল না। এটা পূর্ব নির্ধারিত। আমরা পুরোপুরি তাঁর করুণার অধীন।
অর্থাৎ এক অর্থে তিনি সেই পুরনো নিয়তিবাদেই ফিরে গেলেন।
হয়ত। তবে সেন্ট অগাস্টিন কিন্তু মানুষের নিজের জীবনের ব্যাপারে মানুষের দায়-দায়িত্বের ব্যাপারটি বাতিল করে দেননি। তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে আমরা নির্বাচিত স্বল্প সংখ্যকের মধ্যেই আছি এই ধারণার মধ্যেই বাঁচতে হবে আমাদের। আমাদের যে ইচ্ছার স্বাধীনতা (free will) আছে সে-কথা অগাস্টিন অস্বীকার করেননি। তবে আমরা কীভাবে জীবন যাপন করবো ঈশ্বর তা আগে থেকেই জানেন।
ব্যাপারটা কি একটু অন্যায় নয়? সোফি শুধালো। সক্রেটিস বলেছিলেন আমাদের সবার কাণ্ডজ্ঞান একই হওয়াতে আমাদের সবারই সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সেন্ট অগাস্টিন মানুষকে দুই দলে ভাগ করে ফেলছেন। এক দল রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, আরেক দল নরকভোগ করছে।
এদিক দিয়ে তোমার কথা ঠিক যে সেন্ট অগাস্টিনের ঈশ্বরতত্ত্ব এথেন্সের মানবতাবাদ থেকে বেশ দূরে সরে গেছে। তবে তিনি কিন্তু মানবজাতিকে দুটো দলে ভাগ করছেন না। তিনি স্রেফ মুক্তিলাভ এবং নরকভোগ সম্পর্কে বাইবেলের মতবাদের গণ্ডিকে বিস্তৃত করছেন। বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই ঈশ্বরের নগর (City of God)-এ।
শোনা যাক তাহলে।
ঈশ্বরের নগর বা ঈশ্বরের রাজ্য কথাটা এসেছে বাইবেল আর যীশু শিক্ষা থেকে। সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন মানবজাতির ইতিহাস ঈশ্বরের রাজ্য আর জগতের রাজ্য-র মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস। এই দুই রাজ্য আলাদা দুটো রাজনৈতিক রাজ্য নয়। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই এই দুই রাজ্য যুদ্ধ করে চলে যার যার আধিপত্য কায়েম করার জন্যে। তারপরেও, ঈশ্বরের রাজ্য কম বেশি সুস্পষ্টভাবে রয়েছে খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যেই আর জগতের রাজ্য রয়েছে রাষ্ট্রের মধ্যে, এই যেমন রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে, সেন্ট অগাস্টিনের সময়ই কিনা যার পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। গোটা মধ্য যুগ ধরেই গির্জা আর রাষ্ট্রের মধ্যে চলা শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ই এই ধারণাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। বলা হতে থাকল, গির্জার বাইরে কোনো মুক্তি নেই। সেন্ট অগাস্টিনের ঈশ্বরের নগর আর রাষ্ট্র অনুমোদিত গির্জা শেষ পর্যন্ত অভিন্ন হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে রিফর্মেশনের আগ পর্যন্ত এই ধারণার বিরদ্ধে কোনো প্রতিবাদ শোনা গেল না যে একমাত্র গির্জার মাধ্যমেই মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে।
সময় হয়ে আসছিল।
আমরা এটাও দেখতে পাব যে সেন্ট অগাস্টিন-ই এ-পর্যন্ত আমাদের দেখা প্রথম দার্শনিক যিনি ইতিহাস-কে দর্শনের ভেতর টেনে এনেছেন। ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বের বিষয়টি কোনো অর্থেই নতুন কিছু নয়। নতুন যেটা সেটা হচ্ছে অগাস্টিনের বিবেচনায় দ্বন্দ্বটা বা লড়াইটা হয়েছে ইতিহাসের ভেতর। সেন্ট অগাস্টিনের কাজের এই ক্ষেত্রে প্লেটো খুব একটা নেই। ওল্ড টেস্টমেন্টে আমরা ইতিহাসের সে সরলরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গির দেখা পাই তিনি বরং সেটা দিয়েই প্রভাবিত ছিলেন বেশি এই ধারণা দিয়ে যে ঈশ্বরের রাজ্য-র বাস্তবায়ন ঘটাতে ঈশ্বরের দরকার সমস্ত ইতিহাসটাই। মানুষের আলোকপ্রাপ্তি আর মন্দের বিনাশের জন্যেই ইতিহাস প্রয়োজন। অথবা সেন্ট অগাস্টিনের ভাষায়: স্বর্গীয় অন্তদৃষ্টি মানুষের ইতিহাসকে অ্যাডাম থেকে সময়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ে গেছে যেন সেটা একজন মানুষেরই গল্প, যে-মানুষটি ধীরে ধীরে শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পৌঁছোয়।
নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল সোফি। দশটা বাজে, বলল সে। শিগগিরই যেতে হবে আমাকে।
কিন্তু তার আগে তোমাকে মধ্য যুগের অন্য যে মহান দার্শনিক রয়েছেন তার কথা বলতে হবে। আমরা বাইরে গিয়ে বসি, কি বলল?
উঠে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো। দুই হাতের তালু এক করে আইল ধরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি প্রার্থনা করছেন বা কোনো আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তাকে অনুসরণ করল সোফি; তার মনে হলো এ-ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই।
.
সকালবেলার মেঘ ভেদ করে সূর্য এখনো বেরিয়ে আসেনি। গির্জার বাইরে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন অ্যালবার্টো। সোফি ভাবল এখন কেউ এলে সে কী না জানি ভাববে। এমনিতেই সকাল দশটার সময় গির্জার বেঞ্চির ওপর বসে থাকা-ই অস্বাভাবিক, তার ওপর যদি এক মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসী পাশে থাকে তাহলে তো কথাই নেই।
আটটা বাজে, শুরু করলেন অ্যালবার্টো। সেন্ট অগাস্টিনের পর কেটে গেছে প্রায় চারশো বছর, প্রচলন হয়েছে স্কুলগুলোর। এখন থেকে দশটা পর্যন্ত কনভেন্ট স্কুলগুলোরই একচেটিয়া আধিপত্য চলতে থাকবে। দশটা থেকে এগারটার মধ্যে প্রথম ক্যাথড্রাল স্কুলগুলো স্থাপিত হবে, তারপর দুপুরবেলা থেকে আসবে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এই সময়েই তৈরি হবে বিশাল বিশাল গথিক ক্যাথড্রালগুলো। এই গির্জাটাও ১২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তৈরি, এই সময়টাকেই বলে হাই গথিক যুগ। এই শহরের পক্ষে এরচেয়ে বড় ক্যাথড্রাল তৈরি করা সম্ভব হয়নি।
তার দরকারও পড়েনি, সোফি বলল। ফাঁকা গির্জা আমার একদম পছন্দ নয়।
তবে বড় বড় ক্যাথড্রাল কিন্তু শুধু বড় বড় জমায়েতের জন্যেই তৈরি হয় না। ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্যেও তৈরি করা হয়। আর তাছাড়া খোদ এই গির্জাগুলিই এক ধরনের ধর্মীয় প্রসিদ্ধির পরিচায়ক। সে যাই হোক, এই সময়টাতেই আরো একটা ঘটনা ঘটে, আমাদের মতো দার্শনিকদের কাছে যার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে।
অ্যালবার্টো বলে চলেছেন: স্পেনের আরবদের প্রভাব এই সময়টাতেই অনুভূত হতে শুরু করে। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে আরবরা অ্যারিস্টটলিয় ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিল এবং দ্বাদশ শতকের শেষ দিক থেকে আরব পণ্ডিতরা উত্তর ইতালিতে পা দিতে শুরু করেন অভিজাত সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। এভাবেই, অ্যারিস্টটলের অনেক লেখা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং গ্রীক আর আরবি ভাষা থেকে লাতিনে অনূদিত হয়। এভাবেই, নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি হয় প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে আর খ্রিস্টিয় প্রত্যাদেশ-এর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে যে-বিতর্ক চলছিল তাতেও নতুন করে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে অবশ্য অ্যারিস্টটলকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু কথা হচ্ছে লোকে কখন দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কথা শুনবে আর কখনই বা অনুসরণ করবে বাইবেলকে? বুঝতে পারছো তো?
মাথা ঝাঁকাল সোফি; সন্ন্যাসী বলে চললেন:
এই সময়ের সবচেয়ে মহান আর গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক হলেন সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস, (St. Thomas Aquinas), জন্ম তাঁর ১২২৫-এ মৃত্যু ১২৭৪-এ। রোম আর নেপলস্-এর মাঝখানো ছোট শহর অ্যাকুইনো-র লোক তিনি, তবে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। আমি তাঁকে দার্শনিক বলছি ঠিকই, কিন্তু তিনি আসলে ছিলেন ঈশ্বরতাত্ত্বিক। সে-সময়ে দর্শন আর ঈশ্বরতত্ত্ব-র মধ্যে সে-রকম বড় কোনো ফারাক ছিল না। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, অ্যারিস্টটল-এর ওপর অ্যাকুইনাস ঠিক সেভাবেই খ্রিস্টত্ব আরোপ করেছিলেন সেন্ট অগাস্টিন মধ্য যুগের প্রথমদিকে যেভাবে করেছিলেন প্লেটোর ওপর।
ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া হয়ে গেল না কি, যে-সব দার্শনিক যীশুর কয়েক শ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ওপর খ্রিস্টত্ব আরোপ করা?
সেটা অবশ্য তুমি বলতে পারো। তবে এই দুই মহান গ্রীক দার্শনিকের ওপর খ্রিস্টত্ব আরোপ করার অর্থ তাদের বক্তব্যকে কেবল এমনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাতে তা খ্রিস্টিয় মতবাদের পক্ষে হুমকিস্বরূপ হয়ে দেখা না দেয়। অ্যারিস্টটলের দর্শনকে যারা খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন অ্যাকুইনাস তাঁদের অন্যতম। আমরা বলি, তিনি বিশ্বাস আর জ্ঞানের মধ্যে এক অসাধারণ সমম্বয় সাধন করেছিলেন। কাজটা তিনি করেছিলেন অ্যারিস্টটলের দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করে আর তার কথায় অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস স্থাপন করে।
কিছু মনে করবেন না, গতরাতে আমি প্রায় ঘুমোইনি বললেই চলে, আমার মনে হয় ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে বলতে হবে আপনাকে।
অ্যাকুইনাস বিশ্বাস করতেন দর্শন বা প্রজ্ঞা আমাদেরকে যা শিক্ষা দেয় আর খ্রিস্টিয় প্রত্যাদেশ বা বিশ্বাস যা বলে তার মধ্যে কোনো বিরোধ থাকার কথা নয়। খ্রিস্ট ধর্ম আর প্রজ্ঞা প্রায় একই কথা বলে। কাজেই আমরা আমাদের প্রজ্ঞা ব্যবহার করে প্রায়ই এমন সব সত্যে উপনীত হই বাইবেলে ঠিক যা লেখা আছে।
কীভাবে? আমাদেরকে প্রজ্ঞা কি এ-কথা বলে যে ঈশ্বর ছদিনে এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, বা যীশু ছিলেন ঈশ্বর-পুত্র?
না, বিশ্বাসযোগ্য এ-সব তথাকথিত সত্যকথা কেবল বিশ্বাস আর খ্রিস্টিয় প্রত্যাদেশ-এর মাধ্যমেই উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু অ্যাকুইনাস বেশ কিছু প্রাকৃতিক ঈশ্বরতাত্ত্বিক সত্য কথায় বিশ্বাস করতেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন কিছু সত্যকে বোঝাতেন যা পাওয়া যায় খ্রিস্টিয় বিশ্বাস আর আমাদের সহজাত বা প্রাকৃতিক প্রজ্ঞা এই দুইয়ের মাধ্যমে। যেমন ধরো, এই সত্যটি যে ঈশ্বর আছেন। অ্যাকুইনাস বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরকে পাওয়ার দুটো পথ আছে। একটা পথ গেছে বিশ্বাস আর খ্রিস্টিয় প্রত্যাদেশের ভেতর দিয়ে, অন্যটি প্রজ্ঞা আর ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে দিয়ে। এই দুইয়ের মধ্যে বিশ্বাস আর প্রত্যাদেশের পথই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সঠিক, কারণ স্রেফ প্রজ্ঞার ওপর ভরসা করলে খুব সহজেই পথ ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। তবে অ্যাকুইনাস-এর বক্তব্য হচ্ছে অ্যারিস্টটলের মতো একজন দার্শনিক আর খ্রিস্টিয় মতবাদের মধ্যে বিরোধের কোনো অবকাশ নেই।
অর্থাৎ আমরা হয় অ্যারিস্টটল-এর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারি, নয়ত বাইবেলের ওপর।
মোটেই তা নয়। অ্যারিস্টটল কেবল খানিকটা পথ গিয়েছেন, কারণ খ্রিস্টিয় প্রত্যাদেশের কথা তার জানা ছিল না। কিন্তু পথের কেবল খানিকটা যাওয়া আর ভুল পথে যাওয়া এক কথা নয়। যেমন ধরো, এথেন্স ইউরোপে অবস্থিত বললে ভুল বলা হয় না। কিন্তু তাই বলে একেবারে ঠিক বলাও হয় না। কোনো বইতে যদি শুধু এ কথা লেখা থাকে যে এথেন্স ইউরোপে অবস্থিত তাহলে সেই সঙ্গে ভূগোলের একটা বই দেখে নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানেই তুমি সম্পূর্ণ সত্যটা পাবে যে এথেন্স দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ গ্রীসের রাজধানী। ভাগ্য ভালো হলে সেখানে অ্যাক্রোপলিস সম্পর্কেও দুএকটা কথা লেখা থাকতে পারে। থাকতে পারে সক্রেটিস, প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের কথাও।
কিন্তু এথেন্স সম্পর্কে প্রথমে যে-কথাটা বলা হয়েছিল সেটাতো সত্যি।
অবশ্যই! অ্যাকুইনাস প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সত্য রয়েছে মাত্র একটি। কাজেই অ্যারিস্টটল যখন আমাদেরকে এমন কিছু দেখান যাকে আমাদের প্রজ্ঞা সত্য বলে ঘোষণা করে তখন তার সঙ্গে খ্রিস্টিয় শিক্ষার কোনো বিরোধ থাকে না। প্রজ্ঞার সাহায্যে আর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর দেয়া প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আমরা সত্যের একটি দিকের কাছে সাফল্যের সঙ্গেই পৌঁছুতে পারি। উদাহরণ হিসেবে সেই ধরনের সত্যের কথা বলা যায় যে-সব সত্যের কথা অ্যারিস্টটল উল্লেখ করেছিলেন উদ্ভিদ আর প্রাণী-রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে। সত্যের আরেকটা দিক আমাদের কাছে উন্মোচিত করেন ঈশ্বর, বাইবেলের মাধ্যমে। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে সত্যের এই দুটো দিক একে অন্যের ওপর এসে পড়ে। বেশ কিছু প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ রয়েছে যে-ব্যাপারে বাইবেল আর প্রজ্ঞা ঠিক একই কথা বলে।
যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন?
একদম ঠিক বলেছ! অ্যারিস্টটলের দর্শনও একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা একটা আকারগত কারণ (forma cause)-এর অস্তিত্বের কথা অনুমান করেছিল, যে কারণ সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বা ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। কিন্তু তিনি ঈশ্বর এর বর্ণনা প্রসঙ্গে এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি। এ-ব্যাপারে আমাদেরকে বাইবেল আর যীশুর শিক্ষার ওপরই নির্ভর করতে হবে পুরোপুরি।
ঈশ্বর-এর অস্তিত্ব কি এতোটাই নিশ্চিত?
সেটা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু এমনকী আমাদের যুগেও মেলা লোক এই ব্যাপারে একমত হবেন যে মানুষের প্রজ্ঞা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খারিজ করে দেবার হিকমত একেবারেই রাখে না। অ্যাকুইনাস তো আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন অ্যারিস্টটলের দর্শনের সাহায্য নিয়েই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিতে পারেন।
নট ব্যড।
তিনি বিশ্বাস করতেন, আমাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা এ-কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে আমাদের চারপাশের সমস্ত কিছুর একটি আকারগত কারণ রয়েছে। বাইবেল আর প্রজ্ঞা, এই দুটোর মাধ্যমেই ঈশ্বর নিজেকে মানবজাতির কাছে প্রকাশ করেছেন। কাজেই বিশ্বাসের ঈশ্বরতত্ত্ব আর প্রাকৃতিক ঈশ্বরতত্ত্ব এই দুটোরই অস্তিত্ব রয়েছে। নৈতিক ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই একই কথা প্রযোজ্য। বাইবেল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় আমরা কীভাবে জীবনযাপন করবো বলে ঈশ্বর চান সে-বিষয়ে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে একটি বিবেক-ও দিয়েছেন যার সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিক ভিত্তিতে ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে পারি। কাজেই দেখা যাচ্ছে নৈতিক জীবনেরও দুটো পথ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে ঠিক সে-রকম ব্যবহার কর যে-রকম ব্যবহার তুমি অন্যের কাছে আশা কর, বাইবেলের এই কথা যদি আমাদের পড়া না-ও থাকে, তারপরেও আমরা জানি যে লোকের অনিষ্ট করা ঠিক নয়। এই ক্ষেত্রেও বাইবেলের অনুজ্ঞা পালন করাই শ্রেষ্ঠ পথ।
আমার মনে হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি, এবার বলল সোফি। ব্যাপারটা অনেকটা বজ্র-বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের মতো যা কিনা বিদ্যুচ্চমক দেখা আর বজ্বের শব্দ শোনার মিলিত ফল।
ঠিক বলেছো! অন্ধ হলেও লোকে বজ্রের শব্দ শুনতে পায়, কালা হলেও বিদ্যুচ্চমক দেখতে পায়। দেখা আর শোনা এই দুটো হলেই যে সবচেয়ে ভালো হয় সে-কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। তবে আমরা যা দেখি আর যা শুনি তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং একটা আরেকটাকে আরো পোক্ত করে।
বুঝেছি।
আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো যদি কোনো উপন্যাস পড়ো, এই যেমন জন স্টেইনবেক-এর অড় মাইস অ্যান্ড মেন…
আমি কিন্তু সত্যিই পড়েছি ওটা।
তো, তোমার কি মনে হয় না স্রেফ বইটা পড়েই তুমি লেখক সম্পর্কে খানিকটা জানতে পেরেছো?
আমি বুঝতে পারছি কেউ একজন নিশ্চয়ই লিখেছেন ওটা।
শুধু কি এটুকুই জানতে পেরেছো তুমি তাঁর সম্পর্কে?
মনে হয় আউটসাইডারদের প্রতি তার একটা সহানুভূতি আছে।
বইটা পড়ার সময়– যে-বইটা স্টেনবেক লিখেছেন– তুমি স্টেইনবেকের চরিত্র সম্পর্কেও খানিকটা জানতে পারো। কিন্তু তাই বলে তুমি লেখক সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনো তথ্য সেখানে আশা করতে পারো না। অড় মাইস এ্যান্ড মেন পড়ে তুমি কি বলতে পারবে বইটা লেখার সময় লেখকের বয়স কত ছিল? তিনি কোথায় থাকতেন বা তার ছেলেমেয়ে কটি ছিল?
নিশ্চয়ই না।
কিন্তু এসব তথ্য তুমি খুব সহজেই পেয়ে যাবে জন স্টেইনবেক-এর কোনো জীবনীতে। একমাত্র কোনো জীবনী বা আত্মজীবনীতেই তুমি ব্যক্তি স্টেনবেক সম্পর্কে আরো অনেক বেশি কিছু জানতে পারবে।
সে-কথা ঠিক।
ঈশ্বরের সৃষ্টি আর বাইবেল সম্পর্কেও কথাটা কম-বেশি সত্য। প্রাকৃতিক জগতে স্রেফ খানিকক্ষণ চলাফেরা করেই আমরা একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব টের পাই। খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে তিনি ফুল আর জীব-জন্তু ভালোবাসেন, না হলে সেগুলো তিনি তৈরি করতেন না। কিন্তু ব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে কেবল বাইবেল-এ বা ঈশ্বরের আত্মজীবনী-তে।
উদাহরণ দেবার বেলায় আপনার জুড়ি নেই।
হুম…
এই প্রথমবারের মতো অ্যালবার্টো কোনো জবাব না দিয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন।
এ-সবের সঙ্গে হিল্ডার কি কোনো সম্পর্ক আছে? সোফি জিগ্যেস না করে পারল না।
হিল্ডা বলে আদৌ কেউ আছে কিনা সেটাই তো জানি না।
জানি না। কিন্তু একটা কথা আমরা জানি যে, কেউ একজন হিল্ডা সম্পর্কে নানান সব প্রমাণ আমাদের চারপাশে রেখে যাচ্ছে। পোস্টকার্ড, রেশমি স্কার্ফ, একটা সবুজ ওয়ালেট, একটা মোজা…
অ্যালবার্টো ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে হিল্ডার বাবাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কতগুলো সূত্র তিনি আমাদের সামনে হাজির করবেন সে-ব্যাপারে। আপাতত আমরা যেটুকু জানি তা হচ্ছে কেউ একজন আমাদেরকে গাদা গাদা পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছে। সে যদি তার নিজের সম্পর্কে লিখে। জানাতো তাহলে ভালো হতো খুব। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরে আসব।
পৌনে এগারোটা বাজে। মধ্য যুগ শেষ হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।
অ্যারিস্টটলের দর্শন যে-সব জায়গায় খ্রিস্টিয় ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে মুখোমুখি হয়নি সেগুলোর ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলেই শেষ করবো আমি। এ-সবের মধ্যে আছে তার যুক্তিবিদ্যা, তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব (theory of knowledge) আর প্রাকৃতিক দর্শন (natural philosophy), গুরুত্বের দিক দিয়ে যেটা নেহাত কম নয়। এই যেমন ধরো, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে গাছপালা থেকে শুরু করে জীব-জম্ভ হয়ে মানুষ পর্যন্ত জীবনের একটা নিচু থেকে উঁচুর দিকে ওঠা স্কেলের কথা বলেছিলেন অ্যারিস্টটল?
সোফি মাথা ঝাঁকাল।
অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে এই স্কেল এমন এক ঈশ্বরের ইঙ্গিত দেয় যিনি এক ধরনের সর্বোচ্চ অস্তিত্ব তৈরি করেছেন। ঘটনা বা বস্তুগুলোর এই পরিকল্পনাকে খ্রিস্টিয় ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কঠিন কিছু নয়। অ্যাকুইনাসের বক্তব্য অনুযায়ী, উদ্ভিদ আর জীব-জম্ভ থেকে শুরু করে মানুষ, তারপর মানুষ থেকে দেবদূত আর শেষে দেবদূত থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত ক্রমেই ওপরে উঠে যাওয়া একটি অস্তিত্ব রয়েছে। জীব-জম্ভর মতো মানুষেরও দেহ আর সাংবদনিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ অস্তিত্ব রয়েছে। জীব-জন্তুর মতো মানুষেরও দেহ আর সাংবেদনিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিমত্তা-ও আছে যা তাকে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছে। দেবদূতদের সাংবেদনিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ এ ধরনের কোনো দেহ নেই, যে-কারণে তাদের রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত, তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা। মানুষের মতো তাদেরকে চিন্তা করতে হয় না; সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্যে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার হয় না। মানুষ যা জানে তা জানার জন্যে তাদেরকে ধাপে ধাপে এগোতে হয়নি। আর দেবতাদের যেহেতু কোনো শরীর নেই, তাদের মৃত্যুও নেই। তারা অবশ্য ঈশ্বরের মতো চিরস্থায়ী বা চিরন্তন নয়, তার কারণ ঈশ্বরই তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন কোনো এক সময়। কিন্তু তাদের এমন কোনো দেহ নেই যা থেকে এক সময় তাদেরকে বিদায় নিতে হবে আর তাই কখনো, মৃত্যু হবে না তাদের।
চমৎকার তো!
কিন্তু, সোফি, দেবদূতদের ওপর কর্তৃত্ব করেন ঈশ্বর। একটি একক সঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি সমস্ত কিছুই দেখেন এবং জানতে পারেন।
তাহলে তো তিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের।
হ্যাঁ, তা হয়ত তিনি পাচ্ছেন। তবে এখন নয়। সময় আমাদের কাছে যেমন ঈশ্বরের কাছে ঠিক তেমন নয়। আমাদের এখন ঈশ্বরের এখন নয়। আমাদের জীবনে বেশ কয়েক হপ্তা কেটে গেলে ঈশ্বরের কাছে যে তা সে-রকমই হবে এমনটি মনে করার কারণ নেই।
এ-তো বড় অদ্ভুত। আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল সোফি। নিজের মুখের ওপর একটা হাত চলে এলো তার। মাথা নিচু করে তার দিকে তাকালেন অ্যালবার্টো। সোফি বলে চলল, কাল আরেকটা কার্ড পেলাম হিল্ডার বাবার কাছ থেকে। তিনি অনেকটা এরকম কথাই লিখেছেন-সোফির কাছে এক হপ্তা বা দুই হপ্তা পার হলে আমাদের জীবনেও যে তাই হতে হবে এমন কোনো মানে নেই। কথাটা তো ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি যা বললেন ঠিক সে-রকমই।
সোফি দেখতে পেল বাদামি আলখাল্লার ভেতর অ্যালবার্টোর মুখে একটা চকিত জভঙ্গি খেলে গেল।
তার লজ্জা হওয়া উচিত।
সোফি ঠিক বুঝতে পারল না অ্যালবার্টো কী বোঝাতে চাইলেন কথাটা দিয়ে। তিনি বলে গেলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে অ্যাকুইনাস নারী সম্পর্কেও অ্যারিস্টটলেরই মত গ্রহণ করেছিলেন। তোমার হয়ত মনে আছে যে অ্যারিস্টটল মনে করতেন নারী হচ্ছে আসলে কম-বেশি অসম্পূর্ণ পুরুষ। তিনি আরো ভাবতেন সন্তানেরা কেবল বাবার বৈশিষ্ট্যই লাভ করে উত্তরাধিকার সূত্রে, কারণ নারী কেবল নিষ্ক্রিয় আর গ্রহীতা, অন্য দিকে পুরুষ সক্রিয় আর সৃজনশীল। অ্যাকুইনাসের মতে, এই দৃষ্টিভঙ্গি বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ বাইবেল বলে, অ্যাডামের পাঁজরের হাড় থেকেই নারীর সৃষ্টি।
ননসেন্স।
একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ১৮২৭ সালের আগ পর্যন্ত স্তন্যপায়ীদের ডিম আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই সম্ভবত এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে লোকে ভাবতো সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষই সৃজনশীল আর প্রাণদায়ী শক্তি। আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হল, অ্যাকুইনাসের মতে, কেবল প্রাকৃতিক-সত্তা হিসেবেই নারী পুরুষের চেয়ে হীনতর। নারীর আত্মা আর পুরুষের আত্মা সমান। স্বর্গে কোনো লিঙ্গভেদ নেই, নারী-পুরুষ একই সমান, কারণ সেখানে শারীরিক লিঙ্গ বৈষম্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।
সেটা খুব একটা স্বস্তিদায়ক কথা নয়। মধ্য যুগে কোনো নারী দার্শনিক ছিলেন?
মধ্য যুগে গির্জাশাসিত জীবনে ছিল পুরুষেরই আধিপত্য। তাই বলে যে কোনো নারী চিন্তাবিদ একেবারেই ছিলেন না তা নয়। তাদের মধ্যেই একজন হলেন বিঙ্গেন-এর হিল্ডাগার্ড (Hildegard of Bingen)…।
চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল সোফির।
তার সঙ্গে কি হিল্ডার কোনো সম্পর্ক আছে?
মেয়ের প্রশ্ন শোনো! হিল্ডাগার্ড ছিলেন রাইন উপত্যকার মানুষ, জন্ম ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১১৭৯-তে। নারী হওয়ার পরেও তিনি ছিলেন ধর্ম প্রচারক, লেখক, চিকিৎসক, উদ্ভিদবিদ আর প্রকৃতিবিদ। নারীরা যে প্রায়ই পুরুষের চেয়ে বেশি বাস্তববাদী, বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ছিল, এমনকী সেই মধ্য যুগেও, তারই একটি উদাহরণ তিনি।
কিন্তু হিল্ডা?
প্রাচীন খ্রিস্টিয় আর ইহুদি একটা বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর কেবল পুরুষই নন। তার একটা স্ত্রীসুলভ দিক বা মাতৃ-প্রকৃতিও (mother nature) রয়েছে। নারীদেরও ঈশ্বরের অনুরূপ করে তৈরি করা হয়েছে। গ্রীক ভাষায় ঈশ্বরের এই নারীসুলভ দিকটিকে বলা হয় সোফিয়া (Sophia)। সোফিয়া বা সোফি (Sophie) শব্দের অর্থ বিজ্ঞতা।
হালছাড়া ভঙ্গিতে মাথা ঝকাল সোফি। কথাটা কেউ তাকে কখনো বলেনি কেন? তাছাড়া, সে নিজেই বা জিগ্যেস করেনি কেন?
অ্যালবার্টো বলে চললেন: পুরো মধ্য যুগ জুড়েই ইহুদি এবং গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের কাছে সোফিয়া বা ঈশ্বরের মাতৃ-প্রকৃতির একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। পশ্চিমে তার কথা ভুলে গিয়েছিল সবাই। কিন্তু এরপরই এলেন হিল্ডাগার্ড। মহামূল্যবান অলংকার খচিত সোনালি বস্ত্র পরে সোফিয়া হাজির হলেন হিল্ডগার্ডের স্বপ্নে…।
উঠে দাঁড়াল সোফি। হিল্ডেগার্ডের স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন সোফিয়া…।
হয়ত আমি একদিন দেখা দেবো হিল্ডার স্বপ্নে।
ফের বসে পড়ল সে। এই তৃতীয়বারের মতো তার কাঁধে হাত রাখলেন অ্যালবার্টো।
ব্যাপারটা আমরা এক সময় অবশ্যই ভেবে দেখব। কিন্তু এখন একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছি। রেনেসা সম্পর্কে আলাপ করাবার জন্য তোমাকে খবর পাঠাবো আমি। হার্মেস তোমার বাগানে যাবে।
এই বলে উঠে দাঁড়ালেন অদ্ভুত সন্ন্যাসীটি, তারপরে হাঁটতে শুরু করলেন গির্জার দিকে। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল সোফি, ভাবছে হিল্ডাগার্ড আর সোফিয়া, হিল্ডা আর সোফির কথা। হঠাৎ করেই সে লাফ দিয়ে উঠে সন্ন্যাসীর আলখাল্লাপরা দার্শনিকের দিকে ছুটে গেল এই প্রশ্নটা করতে করতে:
মধ্য যুগে কি অ্যালবার্টো নামেও কেউ ছিলেন?
অ্যালবার্টো তার হাঁটার গতি ধীর করলেন খানিকটা, ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালেন, তারপর বললেন, অ্যাকুইনাসের একজন বিখ্যাত দর্শন শিক্ষক ছিলেন অ্যালবার্ট দ্য গ্রেট নামে…।
এই কথা বলে তিনি মাথা ঝাঁকালেন একবার, তারপর সেন্ট মেরি-র গির্জার দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
উত্তরটা খুশি করতে পারল না সোফিকে। সে তার পিছু পিছু গির্জায় গিয়ে ঢুকল। কিন্তু এখন সেটা একদম নির্জন। উনি কি মেঝে খুঁড়ে ঢুকে গেলেন নাকি?
গির্জা ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ম্যাডোনার একটা ছবি নজরে পড়ল তার। সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, তারপর ভালো করে তাকাল সেটার দিকে। হঠাৎ সে ম্যাডোনার এক চোখের নিচে এক ফোঁটা পানি আবিষ্কার করল। অশ্রু বিন্দু
দৌড়ে গির্জার বাইরে বেরিয়ে এলো সে, তারপর ছুটল জোয়ানার বাসার দিকে।