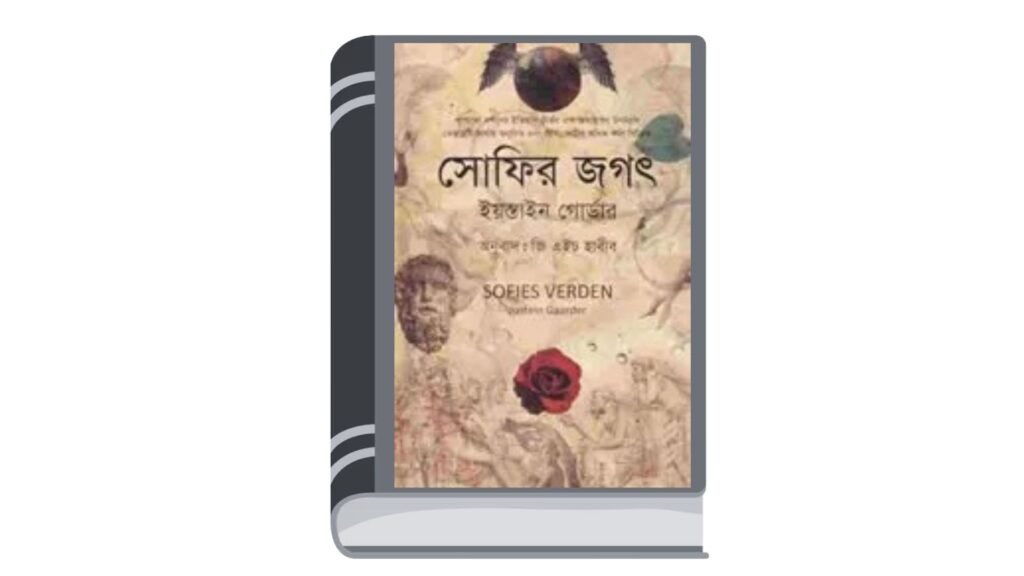১৭. বারোক
১৭. বারোক
…স্বপ্ন গড়া যা দিয়ে…
বেশ কদিন অ্যালবার্টোর আর কোনো সাড়াশব্দ পেল না সোফি, কিন্তু হার্মেসের দর্শনলাভের আশায় প্রায়ই বাগানে উঁকি মেরেছে সে। মাকে সে বলেছে কুকুরটা নিজেই নিজের পথ খুঁজে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল আর সেটার মালিক, পদার্থবিদ্যার এক প্রাক্তন শিক্ষক, সোফিকে তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। তিনি তাকে ঘোড়শ শতাব্দীতে জন্ম নেয়া বিজ্ঞান আর সৌরজগৎ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন।
জোয়ানাকে অবশ্য সোফি আরো অনেকটা বলল। অ্যালবার্টোর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, ডাকবাক্সের পোস্টকার্ড আর বাড়ি ফেরার পথে কুড়িয়ে পাওয়া দশ ক্রাউনের পয়সা, এগুলোর সবই তাকে বলল সে। হিল্ডাকে নিয়ে দেখা স্বপ্ন আর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সেই সোনার মূর্তিটার কথা অবশ্য চেপে গেল সে।
২৯ শে মে, মঙ্গলবার সোফি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে বাসন-কোসন ধুচ্ছিল। তার মা টিভির খবর শোনার জন্যে আগেই বসার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ওপেনিং থীমটা মিলিয়ে যাওয়ার পর রান্নাঘর থেকেই সে শুনতে পেল যে বোমার আঘাতে নরওয়েজিয় জাতিসংঘ বাহিনীর এক মেজর নিহত হয়েছে।
টেবিলের ওপর বাসন-কোসন মোছার কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে ছুটে চলে এলো সে বসার ঘরে। জাতিসংঘ বাহিনীর অফিসারটির মুখটা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দেখতে পেল সে দৌড়ে এসে, তারপরেই অন্য খবরে চলে গেল ওরা।
সোফি চেঁচিয়ে উঠল, না!
তার মা ঘুরে তাকালেন সোফির দিকে।
হ্যাঁ, যুদ্ধ বড়ো ভয়ংকর ব্যাপার!
কান্নায় ভেঙে পড়ল সোফি।
কিন্তু সোফি, অতোটা খারাপ কিছু তো দেখায়নি।
ওরা কি লোকটার নাম বলেছে?
বলেছে, কিন্তু আমার মনে পড়ছে না। তবে গ্রিমস্ট্যাডের লোক সম্ভবত।
লিলেস্যান্ড আর গ্রিমস্ট্যাড, একই তো হলো।
মোটেই না, কী যা তা বলছিস!
কারো বাড়ি গ্রিমস্ট্যাড-এ হলে সে কি লিলেস্যান্ডের স্কুলে যেতে পারে না?
সোফি কান্না থামিয়েছে, কিন্তু তার মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। চেয়ার থেকে উঠে টিভিটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।
এ-সব কী হচ্ছে, সোফি?
কিছু না।
আলবাৎ কিছু হচ্ছে। তোর একজন বয়ফ্রেন্ড আছে আর আমার সন্দেহ হচ্ছে সে তোর চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। এবার আমার কথার জবাব দে: লেবাননের কোনো লোককে তুই চিনিস?
না, ঠিক সে-রকম না…
লেবাননে থাকে এমন কারো ছেলের সঙ্গে তোর পরিচয় হয়েছে?
না, হয়নি। এমনকী তার মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়নি আমার।
কার মেয়ে?
তা জেনে তোমার দরকার নেই।
আমার মনে হয় আছে।
এবার বরং আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি। বাবা কেন কখনোই বাড়ি আসে না? সেটা কি এই জন্যে যে ডিভোের্স নেবার সাধ্য হয়নি তোমার? হয়ত তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে যার কথা আমি আর বাবা জানি তা তুমি চাও না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার নিজেরই প্রশ্ন আছে একগাদা।
আমার মনে হয় আমাদের দুজনের মধ্যে একটা আলাপ হওয়া দরকার।
তা হয়ত, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি খুব ক্লান্ত, আমি শুতে যাচ্ছি। তাছাড়া আমার। পিরিয়ড শুরু হয়েছে।
দৌড়ে নিজের ঘরে চলে গেল সোফি। তার মনে হলো সে কেঁদে ফেলবে।
বাথরুমের কাজ-টাজ সেরে সে যখন চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে, তার মা এসে ঢুকলেন সোফির শোবার ঘরে।
সোফি ভান করল সে ঘুমিয়ে পড়েছে, যদিও জানে তার মা সে-কথা বিশ্বাস করবেন না। সোফি এ-ও জানে যে তার মা জানেন যে সোফি জানে তার মা তা বিশ্বাস করবেন না। তারপরেও তার মা ভান করলেন তিনি বিশ্বাস করেছেন যে সোফি ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বিছানার এক প্রান্তে বসলেন তিনি, হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন মেয়ের চুলে।
এদিকে সোফি ভাবছে একই সঙ্গে দুটো জীবনযাপন করা কী কঠিন। দর্শন কোর্সটা কবে শেষ হবে সে-কথা চিন্তা করতে লাগল সে। হয়ত তার জন্মদিন আসতে আসতেই বা অন্তত পক্ষে মিডসামার ঈ-এ যখন হিল্ডার বাবা লেবানন থেকে ফিরে আসবেন তখন শেষ হবে কোর্সটা।
একটা বার্থ ডে পার্টি করতে চাই আমি, হঠাৎ বলে উঠল সে।
সে তো খুব ভালো কথা। কাকে কাকে দাওয়াত করবি?
অনেককে…। পিরবো না?
পারবি না কেন? আমাদের বাগানটা তো বেশ বড়। আশা করছি আবহাওয়া ভালো-ই থাকবে তখনো।
পার্টিটা আমি মিডসামার ঈ-এর সময় করবো কিন্তু।
বেশ তো, তাই হবে।
দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সোফি বলল, অবশ্য শুধু যে তার জন্মদিনটার কথা মাথায় রেখে তা নয়।
তা তো বটেই।
আমার মনে হচ্ছে গত কদিনে অনেক বড় হয়ে গেছি আমি।
সেটা তো ভালোই, তাই না?
ঠিক জানি না।
মাথাটা বালিশের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে কথা বলছিল সেফি। এবার তার মা বলে উঠলেন, সোফি, একটা কথা আমাকে তোর বলতেই হবে; তোকে এমন অস্থির, ভারসাম্যহীন লাগছে কেন ইদানিং।
তোমার বয়স যখন পনেরো ছিল তখন তুমিও এ-রকমই ছিলে না, বলো?
হয়তো। কিন্তু তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস আমি কী বলতে চাইছি।
হঠাৎ মায়ের দিকে মুখ ফেরাল সোফি। বলল, কুকুরটার নাম হার্মেস।
তাই?
অ্যালবার্টো নামের এক লোকের কুকুর ওটা।
আচ্ছা।
সেই ওল্ড টাউনে বাসা তাঁর।
কুকুরটার সঙ্গে তুই অত দূরে গিয়েছিলি?
এর মধ্যে তো বিপদের কিছু নেই।
তুই বলেছিস কুকুরটা প্রায়ই আসে এখানে।
বলেছি বুঝি?
একটু ভাবতে হলো তাকে এবার। যতটুকু সম্ভব ততটুকুই বলে ফেলতে চায় সে, কিন্তু তাই বলে সবটা বলা সম্ভব নয়।
তুমি তো বাড়িতে প্রায় থাকোই না, সাহস করে বলে ফেলল সোফি।
তা অবশ্য, নানান কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে।
অ্যালবার্টো আর হার্মেস বেশ কবার এসেছে এখানে।
কেন? ওরা কি এই বাসাতেও এসেছে?
একবারে একটা প্রশ্ন করতে পারো না বুঝি তুমি? এই বাসায় আসেনি। কিন্তু ওরা বনের মধ্যে হাঁটতে যায় প্রায়ই। এর মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্যজনক কিছু নেই?
না, না, তা নেই।
ওরা যখন হাঁটতে যায় তখন অন্য যে কারো মতোই আমাদের গেটটার পাশ দিয়ে চলে যায়। একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় কুকুরটার সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি। এভাবেই অ্যালবার্টোর সঙ্গে পরিচয় আমার।
সেই সাদা খরগোশ আর ওই সব ব্যাপার কী?
অ্যালবার্টোই বলেছিলেন আমাকে ওসবের কথা। উনি সত্যিই একজন দার্শনিক, বুঝলে? তিনি আমাকে সব দার্শনিকের কথা বলেছেন।
ওভাবে, বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?
তিনি আমাকে চিঠিও লিখেছেন। সত্যি বলতে কী, বেশ কিছু চিঠি লিখেছেন। কখনো কখনো তিনি সে-সব ডাকে পাঠিয়েছেন, কখনো আবার হাঁটতে যাওয়ার সময় আমাদের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে গেছেন।
তাহলে আমরা যে প্রেমপত্র নিয়ে আলাপ করেছিলাম তা এই।
তফাৎ হচ্ছে ওগুলো প্রেমপত্র ছিল না।
তো, তিনি কেবল দর্শনের কথাই লিখলেন?
হ্যাঁ, তুমি ভাবতে পারো! আট বছর স্কুলে পড়ে আমি যা জেনেছি তার কাছ থেকে আমি তার চেয়ে বেশি জেনেছি। এই, যেমন ধরো, তুমি কি জিওর্দানো ব্রুনোর কথা শুনেছো কখনো, যাকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? বা নিউটনের সার্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের কথা?
না, অনেক কিছুই আমার জানা নেই।
আমি বাজি ধরে বলতে পারি, পৃথিবী কেন সূর্যের চারপাশে ঘোরে সে-কথাও তোমার জানা নেই-অথচ এটা তোমারই গ্রহ।
তা, লোকটার বয়স কত?
আমার কোনো ধারণা নেই-পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে হয়ত।
কিন্তু লেবাননের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়?
এই প্রশ্নটা কঠিন হয়ে গেল। দ্রুত চিন্তা করল সোফি। সবচেয়ে সম্ভাব্য গল্পটাই বেছে নিল সে।
অ্যালবার্টোর এক ভাই জাতিসংঘ বাহিনীর মেজর। উনি লিলেস্যান্ডের লোক। হয়ত উনিই সেই মেজর যিনি মেজরের কেবিনে থাকতেন।
অ্যালবার্টো নামটা বেশ মজার, তাই না?
হয়ত।
শুনে তো মনে হয় ইটালিয়ান।
ইয়ে, দেখো, যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তার প্রায় সবই এসেছে হয় গ্রীস নয়ত ইটালি থেকে।
কিন্তু উনি কি নরওয়েজিয়ানে কথা বলেন?
ও, হ্যাঁ, ফ্লুয়েন্টলি।
আমার মনে হয় কি জানিস সোফি, তুই একদিন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন কর অ্যালবার্টোকে। সত্যিকারের কোনো দার্শনিকের সঙ্গে কখনো কোনোদিন দেখা হয়নি আমার।
দেখা যাক।
তোর বার্থ ডে পার্টিতেই দাওয়াত দে না ওঁকে? ভিন্ন প্রজন্মের কিছু লোকজন এক জায়গায় হলে মজাই হবে। তারপর ধর, আমিও না হয় যোগ দিলাম। আমি নিদেনপক্ষে সার্ভিং-এ সাহায্য করতে পারবো। কী, আইডিয়াটা কেমন, ভালো না?
উনি যদি আসেন। মোটের ওপর, আমার স্কুলের ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলার চাইতে আমি তার সঙ্গে কথা বলতেই ইন্টারেস্টেড বেশি। ব্যাপারটা স্রেফ এই…
কী?
না, মানে ওরা হয়ত ব্যাপারটা অন্যভাবে নেবে, ভাববে অ্যালবার্টো আমার নতুন বয়ফ্রেন্ড।
ভাবলে বলবি ব্যাপারটা আসলে তা না।
বললাম তো, দেখা যাক।
ঠিক আছে। আর, সোফি, কথাটা সত্যি যে ড্যাড আর আমার মধ্যে ব্যাপারগুলো সবসময় সহজ ছিল না বা এখনো নেই। কিন্তু তৃতীয় আরেকজন কখনোই ছিল না…
আমাকে ঘুমোতে হবে এখন। শরীরটা বেশ কয়েক জায়গায় ভীষণ খিচ ধরে আছে।
অ্যাসপিরিন দেব?
ঠিক আছে, দাও।
তার মা ওষুধ আর পানির গ্লাস নিয়ে ফিরে এসে দেখেন ঘুমে ঢলে পড়েছে সোফি।
***
৩১শে মে, বৃহস্পতিবার। স্কুলে বিকেলবেলার ক্লাসগুলোতে ছটফট করে মরেছে সোফি। দর্শন কোর্সটা শুরু করার পর থেকে কিছু কিছু বিষয়ে ভালো করছে সে। সাধারণত বেশিরভাগ কোর্সেই তার গ্রেড ভালো ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অংক ছাড়া বাকিগুলো আরো ভালো হতে শুরু করেছে।
শেষ ক্লাসটায় ওদের লেখা একটা রচনা দেখে ফেরত দেয়া হয়েছে। সোফি লিখেছিল মানুষ আর প্রযুক্তি নিয়ে। রেনেসাঁ, বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কার, প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর জ্ঞানই শক্তি-এই উক্তি যিনি করেছিলেন সেই ফ্রান্সিস বেকনকে নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গিয়েছিল সে। খুব সতর্কতার সঙ্গে সোফি উল্লেখ করেছিল যে প্রযুক্তিগত আবিষ্কারগুলো হওয়ার আগেই অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি এসে গিয়েছিল। এরপর সে তার সাধ্য অনুযায়ী এমন কিছু প্রযুক্তির কথা লিখেছিল যে-সব প্রযুক্তি সমাজের জন্য ততো ভালো নয়। মানুষ যা কিছুই করুক তাকে ভালো এবং মন্দ এই দুই কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে, এই মন্তব্য করে শেষ অনুচ্ছেদটা লিখেছিল সে। ভালো এবং মন্দ হচ্ছে একটি সাদা আর একটি কালো সুতো যা মিলে একটি দড়ি তৈরি হয়। মাঝে মধ্যে এই সুতো দুটো এতো ঘনভাবে জড়াজড়ি করে থাকে যে তাদের আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
সোফির শিক্ষক সোফির খাতাটা ফেরত দেয়ার সময় তার দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন।
সোফি এ পেয়েছে, সঙ্গে মন্তব্য: এ-সব কথা কোথা থেকে পেয়েছো তুমি?
তার শিক্ষক যখন ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন, সোফি একটা কলম বের করে তার এক্সারসাইজ খাতার মার্জিনে বড় বড় করে লিখল: আমি দর্শন পড়ছি।
ফের যখন খাতাটা বন্ধ করছে সে, সেটার ভেতর থেকে কী যেন একটা পড়ে গেল। লেবানন থেকে পাঠানো একটা পোস্টকার্ড:
প্রিয় হিল্ডা, তুই যখন এ-চিঠি পড়বি তার আগেই আমরা এখানে ঘটে যাওয়া একটা করুণ মৃত্যু সম্পর্কে ফোনে আলাপ করে ফেলবো। মাঝে মাঝে আমি ভাবি মানুষের চিন্তা-ভাবনা যদি আরেকটু ভালো হতো তাহলে যুদ্ধ এড়ানো যেতো কিনা। সম্ভবত দর্শনের ওপর একটা ছোটখাট কোর্স সন্ত্রাসের একটা ভালো প্রতিষেধক হতে পারে। জাতিসংঘের সংক্ষিপ্ত দর্শন গ্রন্থ নামের একটা বই বের করলে কেমন হয়, যে-বইয়ের একটা কপি বিশ্বের প্রতিটি নতুন নাগরিককে তার নিজের ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া হবে? জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এই প্রস্তাবটা রাখবো আমি।
ফোনে তুই বলেছিস নিজের জিনিস-পত্র দেখেশুনে রাখার ব্যাপারে তোর উন্নতি হচ্ছে। আমি তাতে খুশি হয়েছি, কারণ আমার জানামতে তুই ই হচ্ছিস পৃথিবীর সবচেয়ে অগোছালো প্রাণী। এরপর তুই বলেছিস, আমাদের মধ্যে শেষবার কথা হওয়ার পর থেকে একমাত্র যা তুই হারিয়েছিস তা হলো দশ ক্রাউন। আমি চেষ্টা করবো যেন ওটা ফিরে পাস তুই। যদিও আমি অনেক দূরে থাকি কিন্তু দেশে আমার এক সাহায্যকারী আছে। (পয়সাটা পেলে সেটা আমি তোর জন্মদিনের উপহারের সঙ্গে দিয়ে দেব।) ভালোবাসা নিস, বাবা, যার ধারণা সে এরিমধ্যে বাড়ি ফেরার দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।
.
কার্ডটা পড়া সোফি শেষ করেছে কেবল এই সময় শেষ ঘণ্টাটা বেজে উঠল। ফের তার মাথায় চিন্তা-ভাবনার ঝড় বইতে শুরু করল।
খেলার মাঠে অপেক্ষা করছিল জোয়ানা। বাড়ি ফেরার পথে সোফি তার স্কুলব্যাগ খুলে জোয়ানাকে দেখাল সদ্য পাওয়া কার্ডটা।
কবেকার পোস্টমার্ক দেয়া আছে ওটায়? জোয়ানা জিগ্যেস করল।
সম্ভবত ১৫ই জুনের…
না। দ্যাখ… ৫/৩০/৯০, লেখা আছে।
তার মানে গতকাল…লেবাননে সেই মেজরের মৃত্যুর পরের দিন।
লেবানন থেকে কোনো পোস্টকার্ড একদিনে নরওয়ে আসতে পারে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার, জোয়ানা বলল।
আর এই অদ্ভুত ঠিকানার কথা না হয় বাদই দেয়া গেল: হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে সোফি অ্যামুন্ডসেন, ফুরুলিয়া জুনিয়র হাই স্কুল…
তোর ধারণা ডাকে এসেছে চিঠিটা? তারপর টিচার স্রেফ ওটাকে তোর খাতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন?
নো আইডিয়া। সাহস করে ওটার কথা জিগ্যেস করব কিনা সে-বথাও বুঝতে পারছি না।
পোস্টকার্ডটা নিয়ে আর কোনো কথা হলো না ওদের মধ্যে।
মিডসামার ঈ-এ একটা গার্ডেন পার্টি দিতে যাচ্ছি আমি, সোফি বলল।
ছেলেদের নিয়ে?
কাঁধ ঝাঁকাল সোফি। সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গাধাদের ডাকার দরকার আছে কোনো, তুই বল?
কিন্তু তুই জেরেমি-কে ডাকবি নিশ্চয়ই?
তুই যদি চাস। ভালো কথা, আমি হয়ত অ্যালবার্টো নক্স-কে ডাকব।
নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়েছে তোর!
আমি জানি।
সুপারমার্কেট পর্যন্ত এসে ওরা যে যার পথ ধরার আগ পর্যন্ত এটুকুই কথা হলো দুজনের মধ্যে।
বাড়ি ফিরে সোফি প্রথমেই দেখল হার্মেস বাগানে আছে কিনা। যা ভেবেছে ঠিক তাই, ওই তো হার্মেস। আপেল গাছগুলোর চারপাশে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে।
হার্মেস!
এক সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুকুরটা। সোফি ঠিক জানে সেই এক সেকেন্ডে কী হচ্ছে। কুকুরটা তার ডাক শুনেছে, তার গলাটা চিনতে পেরেছে, তারপর সে ওখানে আছে কিনা তা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারপর সোফিকে আবিষ্কার করার পর তার দিকে ছুট দিল সে। শেষে, চার চারটে পা ঢাকের কাঠির মতো উঠতে আর পড়তে লাগল দ্রুত বেগে।
এক সেকেন্ডের মধ্যে এতো সব ব্যাপার সত্যিই অনেক কিছু।
কুকুরটা ছুটে এসে তার গায়ের ওপর পড়ল, লেজটা নাড়তে লাগল ভীষণ বেগে, লাফিয়ে উঠল সোফির মুখটা চেটে দেয়ার জন্যে।
হার্মেস; চালাক ছেলে! নাম, নাম্। না, না, এভাবে চাটিস না আমার সারা গা। শান্ত হ! এই তো!
বাড়ির ভেতর ঢুকল সোফি। ঝোপের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো শিয়ার্কান। অচেনা কারো ব্যাপারে বরাবরই সতর্ক ওটা। সোফি বেড়ালের খাবার বের করল, বাজারিগারের কাপটাতে বার্ডসীড ঢালল, কচ্ছপটার জন্য সালাদের। একটা পাতা বের করল, তারপর মায়ের জন্য একটা চিরকুট লিখে রাখল।
সে লিখল হার্মেসকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে সে, সাতটার মধ্যেই ফিরে আসবে।
শহরের ভেতর দিয়ে রওনা হলো দুজন। এইবার পকেটে কিছু টাকা নিতে ভুলল না সোফি। একবার ভাবল হার্মেসকে নিয়ে বাসে চড়বে কিনা, কিন্তু পরে ঠিক করল অ্যালবার্টোকে এ-ব্যাপারে জিগ্যেস করার আগ পর্যন্ত বরং অপেক্ষাই করা যাক।
হার্মেসের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল একটা জন্তু আসলে কী। একটা কুকুর আর একজন মানুষের মধ্যে তফাৎ কোথায়? অ্যারিস্টটলের কথা মনে পড়ে গেল তার। তিনি বলেছিলেন, মানুষ আর জীব-জন্তু দুই-ই প্রাকৃতিক জীবন্ত প্রাণী যাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। তবে মানুষ আর জীব-জম্ভর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে আর সেটা হলো মানবীয় প্রজ্ঞা।
ভদ্রলোক এতো নিশ্চিত হলেন কীভাবে?
অন্যদিকে ডেমোক্রিটাস কিন্তু মনে করতেন মানুষ আর জীব-জন্তু বরং একই রকম, কারণ দুই-ই পরমাণু দিয়ে তৈরি। তাছাড়া, মানুষ বা জীব-জন্তু কারোরই অমর আত্মা রয়েছে বলে মনে করতেন না তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আত্মাও পরমাণু দিয়ে তৈরি আর মানুষ মারা গেলে সে-সব পরমাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি-ই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি মনে করতেন মানুষের আত্মা তার মস্তিষ্কের সঙ্গে একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা।
কিন্তু আত্মা কী করে পরমাণু-র তৈরি হয়? আত্মা তো আর দেহের অন্য কোনো অংশের মতো নয় যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক একটা জিনিস।
ততক্ষণে মেইন স্কোয়্যার ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, কাছাকাছি চলে এসেছে ওল্ড টাউনের। ওরা যখন সাইডওয়াকটার সেইখানে চলে এসেছে যেখানে সোফি দশ। ক্রাউনের পয়সাটা পেয়েছিল, সোফির চোখ আপনা আপনিই চলে গেল অ্যাসফল্টের ওপর। আর সেখানেই, ঠিক যেখানে সে ঝুঁকে পড়ে পয়সাটা তুলে নিয়েছিল, সেখানেই একটা পোস্টকার্ড পড়ে থাকতে দেখল সে, ছবির দিকটা ওপরে রয়েছে সেটার। ছবিতে পাম আর কমলা গাছ শোভিত একটা বাগান দেখা যাচ্ছে।
ঝুঁকে পড়ে কার্ডটা তুলে নিল সোফি। হার্মেস গরগর করে উঠতে শুরু করল, যেন সোফির ওটা ধরাটা পছন্দ না তার।
কার্ডটাতে লেখা:
প্রিয় হিল্ডা, জীবনটা কাকতালীয় ঘটনার একটা লম্বা শেকল। এমনটা ঘটা অসম্ভব নয় একেবারে যে তোর হারানো দশ ক্রাউন ঠিক এখানেই পাওয়া গিয়েছিল। ক্রিস্টিয়ানস্যান্ডে যাওয়ার বাসের জন্যে অপেক্ষারত কোনো বৃদ্ধা মহিলা হয়ত লিলেস্যান্ডের স্কোয়্যারে পেয়েছিলেন ওটা। ক্রিস্টিয়ানস্যান্ড থেকে ট্রেনে চেপেছিলেন তিনি তাঁর নাতি-নাতনীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে, তার বেশ কয়েক ঘণ্টা পর দশ ক্রাউনটা তিনি এই নিউ স্কোয়্যারে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তো, এরপর এটা খুবই সম্ভব যে ঠিক সেই পয়সাটাই পরে সেদিন একটা মেয়ে তুলে নিয়েছিল বাসে করে বাড়ি যাওয়ার জন্যে ওটা তার আসলেই দরকার ছিল বলে। আর আসলেই যদি তাই হয়ে থাকে, হিল্ডা, তাহলে লোকে নিশ্চয়ই এ-কথা জিগ্যেস করবে সব কিছুর পেছনে ঈশ্বরের হাত রয়েছে কিনা। ভালোবাসা নিস, বাবা, মানসিক দিক দিয়ে যে কিনা লিলেস্যান্ডের ডক-এ বসে আছে। পুনশ্চ: আমি বলেছিলাম না তোর
সেই দশ ক্রাউন খুঁজে পেতে সাহায্য করব তোকে?
.
ঠিকানা যে-পাশে সেখানে লেখা আছে: হিল্ডা মোলার ন্যাগ, প্রযত্নে কোনো এক আকস্মিক পথচারী… ডাকঘরের সীলমোহর দেয়া আছে ৬/১৫৯০।
হার্মেসের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল সোফি। অ্যালবার্টো দরজা খুলতেই সে বলে উঠল,
পথ থেকে সরে দাঁড়ান। ডাকপিয়ন আসছে।
তার মনে হলো বিরক্ত বোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তার নিজের। সে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকছে দেখে সরে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো। হার্মেস আগের মতোই সেই কোট ঝোলানর খুঁটার নিচে গিয়ে শুয়ে পড়ল।
মেজর বুঝি আরেকটা ভিজিটিং কার্ড হাজির করেছে?
সোফি তার দিকে মুখ তুলে তাকাল, দেখল ভিন্ন একটা সাজের পোশাক পরে আছেন তিনি। লম্বা কোঁকড়া চুলের একটা উইগ আর ঢোলা ঢালা এক গাদা লেস লাগানো একটা ব্যাগি স্যুট পরেছেন তিনি। গলায় দৃষ্টিকটু রঙের রেশমি একটা স্কার্ফ পেঁচানো আর স্যুটের ওপর চাপিয়েছেন লাল রঙের একটা হাতাকাটা কোট। আরো পরেছেন সাদা মোজা আর পাকা চামড়ার বো লাগানো জুতো। পুরো পোশাকটা দেখে সোফির মনে পড়ে গেল তার দেখা চতুর্দশ লুই-এর রাজসভার ছবির কথা।
ক্লাউনের মতো দেখতে লাগছে আপনাকে! বলে কার্ডটা তার হাতে ধরিয়ে দিল সোফি।
হুম…আর যেখানে সে কার্ডটা ফেলে রেখেছিল সেখানে তুমি সত্যিই দশ ক্রাউন পেয়েছিলে।
ঠিক তাই।
প্রতিবারই আগের চেয়ে বেশি অভব্য হয়ে উঠছে লোকটা। কিন্তু হয়ত এটাই ভালো হচ্ছে।
কেন?
এতে করে তার মুখোশ খোলাটা সহজ হবে। কিন্তু এই কৌশলটা জমকালো আর রুচিহীন দুই-ই। এটার গা থেকে প্রায় সস্তা সুগন্ধীর গন্ধ বেরচ্ছে।
সুগন্ধী?
হ্যাঁ, তবে মার্জিত হতে চাইলে কী হবে, ওটার গন্ধ আসলে জঘন্য। দেখলে না লোকটা তার নোংরা নজরদারিকে কী ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানের সঙ্গে তুলনা করল?
কার্ডটা তুলে ধরলেন তিনি। তারপর সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তার মেজাজটা যাতে আরো বিগড়ে না যায় সেজন্যে সোফি স্কুলে তার খাতার ভেতর থেকে পড়া কার্ডটার কথা চেপে গেল।
চলো ভেতরে গিয়ে বসি। কটা বাজে?
চারটা।
আজ আমরা আলাপ করবো সপ্তদশ শতাব্দী নিয়ে।
ঢালু দেয়াল আর স্কাইলাইটঅলা বসার ঘরে চলে এলো ওরা। সোফি লক্ষ করল এর আগেরবার সে যে-সব জিনিস দেখেছিল সে-সবের কিছু কিছু সরিয়ে অ্যালবার্টো ভিন্ন কিছু জিনিস বের করে রেখেছেন।
কফি টেবিলের ওপর সাবেক কালের ছোট একটা বাক্সে নানান ধরনের চশমার কাঁচ রাখা আছে দেখতে পেল সে। তার পাশেই রয়েছে একটা ভোলা বই। দেখতে বেশ পুরনো।
ওটা কী? জিগ্যেস করল সোফি।
এটা আমার সবচেয়ে দামি সংগ্রহগুলোর মধ্যে একটা, ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দেকার্তের দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধের বই; এই বইতেই তাঁর বিখ্যাত রচনা ডিসকোর্স অন মেথডপ্রথমবারের মতো পাঠকদের সামনে হাজির করা হয়েছিল।
আর ওই ছোট্ট বাক্সটা?
ওটাতে আছে কিছু লেন্স বা চশমার কাঁচের একটা বিশেষ সগ্রহ। ওলন্দাজ দার্শনিক স্পিনোজা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে এই কাঁচগুলো পরিষ্কার করেছিলেন। অত্যন্ত দামি কাঁচ ছিল এগুলো। আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের মধ্যে এগুলোকেও ধরতে পারো তুমি।
এগুলো কতটা দামি সেটা সম্ভবত আমি আরো ভালো করে বুঝতে পারতাম যদি জানতাম তারা কে ছিলেন।
অবশ্যই। তবে প্রথমে, তারা যে-সময়ের লোক সেই সময়টা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করা যাক। তা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোসা না।
আগের সেই স্থানেই বসল দুজনে, সোফি বড় আর্মচেয়ারটায় আর অ্যালবার্টো নক্স সোফায়। দুজনের মাঝখানে কফি টেবিলটা, সেটার ওপর বই আর ছোট্ট বাক্সটা। অ্যালবার্টো পরচুলাটা খুলে রেখে লেখার ডেস্কের ওপর রেখে দিলেন।
আমরা এখন কথা বলতে যাচ্ছি সপ্তদশ শতাব্দী বা সাধারণত যে-সময়টাকে আমরা বারোক (Baroque) যুগ বলে থাকি সেই সময়টা নিয়ে।
বারোক যুগ? কী অদ্ভুত নাম।
বারোক শব্দটা এসেছে এমন একটা শব্দ থেকে যে-শব্দ দিয়ে অসমান আকার বা গঠনের মুক্তাকে বোঝানো হতো। বারোক শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মহীনতা, যা কিনা রেনেসাঁর সময়কার তুলনামূলকভাবে সহজ-সরল আর আরো বেশি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল তার প্রবলরকমের বৈপরিত্যপূর্ণ ধরন-ধারন নিয়ে। আসলে, পুরো সপ্তদশ শতাব্দী-ই বিশিষ্ট হয়ে আছে অসেতুসম্ভব বৈপরীত্যগুলোর মধ্যেকার টানাপোড়নের কারণে। একদিকে ছিল রেনেসাঁ-র নিরন্তর আশাবাদ আর অন্যদিকে অগুনতি মানুষ, যারা ধর্মীয় নিঃসঙ্গতা এবং আত্ম-স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে খুঁজে ফিরছিল একেবারে বিপরীত মেরুর এক জীবন। শিল্প এবং বাস্তব জীবন, এই দুইয়ের ভেতরেই আমরা আত্মপ্রকাশের আড়ম্বরপূর্ণ আর বর্ণবহল রূপ লক্ষ করি এই সময়টায়। ওদিকে আবার ঠিক একই সময়ে দেখা দিয়েছিল জগতের দিকে পিঠ ফেরানো মঠভিত্তিক আন্দোলন।
অন্য কথায় বলতে গেলে, উদ্ধত সব প্রাসাদ আর দূরবর্তী সব মঠ, এই দুই-ই।
হ্যাঁ, তা তুমি নিঃসন্দেহে বলতে পারো। বারোক যুগের একটি প্রিয় কথা ছিল, লাতিন ভাষায়, কার্পে দিয়েম (carpe diem), আজকের দিনের জন্যে বাঁচো। লাতিন আরেকটা কথাও লোকের মুখে মুখে ফিরত আর সেটা হলো মেমেন্তো মোরি (memento mori), মনে রেখো, মরতে তোমাকে হবেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে, একটা ছবিতে হয়ত খুবই বিলাসবহুল জীবনের চিত্র আঁকা হলো, কিন্তু তার পাশেই এক কোনায় ছোট্ট করে একে দেয়া হতো একটা খুলি।
অনেক অর্থেই, বারোক যুগ বিশিষ্ট হয়ে আছে অহং বা ভান-এর জন্যে। কিন্তু একই সময়ে, মুদ্রার অপর পিঠটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল অগুনতি মানুষ। তারা উদ্বিগ্ন ছিল বস্তুর ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে। অর্থাৎ এই বিষয়টি নিয়ে যে আমাদের চারপাশের সব সুন্দর জিনিস একদিন অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।
তা ঠিক। এ-কথা চিন্তা করলেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে যে কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়।
সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকেই তোমার মতো ভেবেছিল। বারোক যুগ রাজনৈতিক অর্থে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময়ও বটে। যুদ্ধে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল ইউরোপ। সবচেয়ে বাজে যুদ্ধটা ছিল তিরিশ বছরের যুদ্ধ, প্রায় গোটা মহাদেশ জুড়েই চলেছিল যুদ্ধটা ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সত্যি বলতে কী, এটা ছিল ধারাবাহিক কিছু যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ মাশুল আদায় করেছিল বিশেষ করে জার্মানীর কাছ থেকে। ফ্রান্স যে ধীরে ধীরে ইউরোপের প্রধানতম শক্তি হয়ে উঠেছিল তার জন্যে এই তিরিশ বছরের যুদ্ধ কম দায়ী নয়।
তা, যুদ্ধগুলো হয়েছিল কী নিয়ে?
যুদ্ধগুলো ছিল মূলত প্রোটেস্টান্ট আর ক্যাথলিকদের মধ্যে। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা-ও একটা অন্যতম কারণ ছিল।
অনেকটা লেবাননের মতো।
যুদ্ধ-বিগ্রহ বাদ দিলে, সপ্তদশ শতাব্দী ছিল শ্রেণী বৈষম্যের সময়। আমি নিশ্চিত করে জানি না ফরাসী অভিজাততন্ত্র বা ভার্সাই-এর রাজসভার কথা তুমি শুনেছ। কিনা। কিন্তু জাকজমক-এর প্রদর্শনীর জন্য ক্ষমতার প্রদর্শনীরও প্রয়োজন হয়। একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে বারোক যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে-সময়কার শিল্পকলা আর স্থাপত্যর মতোই ছিল অনেকটা। কারণ বারোক যুগের দালান-কোঠার বৈশিষ্ট্য-ই ছিল সেগুলোর অলংকারপূর্ণ কোনা-ঘুপচি আর ফাঁক-ফোকরগুলো। ঠিক একইভাবে, তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিশিষ্ট হয়ে আছে ষড়যন্ত্র, ফাঁদ আর গুপ্তহত্যার জন্যে।
সুইডিশ এক রাজাকে গুলি করে মারা হয়েছিল না থিয়েটারের মধ্যে?
তুমি বলছ তৃতীয় গুস্তাভের কথা; হ্যাঁ, আমি যে-ব্যাপারটি বোঝাতে চাইছি এটা তার একটা ভালো উদাহরণ বটে। অবশ্য গুস্তাভের গুপ্তহত্যা ঘটেছিল সেই ১৭৯২ তে, তবে তখনকার পরিস্থিতি কিন্তু পুরোপুরি বারোক যুগের মতোই ছিল। বিশাল একটা মাস্ক বল নাচে অংশ নেয়ার সময় নিহত হন তিনি।
আমি ভেবেছিলাম থিয়েটার দেখছিলেন তিনি তখন।
মুখোশ পরা সেই বল নাচ হচ্ছিল আসলে একটা অপেরা ঘরে। আমরা বলতে পারি, সুইডেন-এ বারোক যুগ-এর ইতি ঘটেছিল তৃতীয় গুস্তাভের সেই হত্যার মধ্যে দিয়ে। তার শাসনামলটা ছিল আসলে এক আলোকিত স্বৈরাচার-এর যুগ, যা কিনা প্রায় একশো বছর পূর্বেকার রাজ চতুর্দশ লুই-এর শাসনামলের মতোই একদম। তৃতীয় গুস্তাভ খুবই আত্মম্ভরি ধরনের লোক ছিলেন, ফরাসী সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা আর আচার-অনুষ্ঠান-এর ভক্তও ছিলেন। থিয়েটারও ভালোবাসতেন তিনি…
আর সেটাই মৃত্যু ডেকে আনল তাঁর।
হ্যাঁ, তবে বারোক যুগের থিয়েটার কিন্তু কেবলই একটা শিল্প মাধ্যম ছিল না। সেটা ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রতীক।
কিসের প্রতীক?
জীবনের, সোফি। সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবন একটা রঙ্গমঞ্চ এই কথাটা যে কতবার বলা হয়েছে আমার জানা নেই। তবে এ-কথা বলা যায়, প্রায়ই বলা হতো কথাটা। বারোক যুগই আধুনিক থিয়েটারের জন্ম দিয়েছিল, সেটার নানান ধরনের সিনারি আর থিয়েটারী কলাকৌশল সমেত। থিয়েটারে আসলে মঞ্চের ওপর একটা ইস্যুশন বা বিভ্রান্তি তৈরি করা হতো, শেষ পর্যন্ত যা এই ব্যাপারটিই প্রকাশ করতো যে মঞ্চের নাটকটি আসলে একটি মায়া ছাড়া কিছু নয়। এভাবেই থিয়েটার হয়ে ওঠে সাধারণভাবে মানবজীবনেরই একটি প্রতিফলন। থিয়েটার হয়ত দেখাল অহংকারই পতনের মূল এবং ফুটিয়ে তুলল মানুষের অনৈতিকতার এক নিষ্করুণ চিত্র।
শেক্সপীয়ার কি এই বারোক যুগের লোক ছিলেন?
১৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকেই তিনি তাঁর সবচেয়ে মহৎ নাটকগুলো লিখেছিলেন, কাজেই বলতে পারো তিনি তাঁর এক পা রেনেসা-য় অন্য পা বারোক যুগে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শেক্সপীয়ারের লেখায় জীবনকে প্রায়ই থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সে-রকম কিছু লাইন শুনতে চাও?
চাই।
তিনি তার অ্যাজ ইউ লাইক ইটনাটকে বলেছেন:
অল দ্য ওয়ার্ল্ডজ আ স্টেজ,
অ্যান্ড অল দ্য মেন অ্যান্ড উইমিন মিয়ারলি প্লেয়ার্স;
দে হ্যাভ দেয়ার এক্সিট অ্যান্ড দেয়ার এন্ট্রান্সেস
অ্যান্ড ওয়ান ম্যান ইন হিজ টাইম প্লে মেনি পার্ট।
ওদিকে ম্যাকবেথএ তিনি বলছেন:
লাইফজ বাট আ ওয়াকিং শ্যাডো, আ পুওর প্লেয়ার
দ্যাট স্ট্রাটস অ্যান্ড ফ্লেটস হিজ আওয়ার আপ্ন দ্য স্টেজ,
অ্যান্ড দেন ইজ হার্ড নো মোর; ইট ইজ আ টেল
টোন্ড বাই অ্যান ইডিয়ট; ফুল অভ সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি,
সিগনিফাইয়িং নাথিং।
কী হতাশাভরা কথা।
জীবনের সংক্ষিপ্ততা তার চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার সবচেয়ে বিখ্যাত লাইনটা তুমি শুনেছো নিশ্চয়ই?
টু বি অর নট টু বিদ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন।
হ্যাঁ, হ্যামলেটের উক্তি। একদিন আমরা এই পৃথিবীর ওপর হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি তো পরের দিন হারিয়ে যাচ্ছি, মিশে যাচ্ছি মাটিতে।
ধন্যবাদ, বক্তব্যটা ধরতে পেরেছি আমি।
আর বাবোক কবিরা যখন জীবনকে মঞ্চের সঙ্গে তুলনা করেন না, তখন সেটাকে তুলনা করেন তাঁরা স্বপ্নের সঙ্গে, এই যেমন শেক্সপীয়ার বলেন,
স্বপ্ন গড়া যা দিয়ে আমরা তাই আর আমাদের এই ছোট্ট জীবনটা ঘুম দিয়ে ঘেরা?
এটা অবশ্য খুব-ই কাব্যিক বর্ণনা।
১৬০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী স্প্যানিশ নাট্যকার কলদেরন দে লা বার্কা (Calderon de la Barca) জীবন একটা স্বপ্ন নামে এক নাটকে বলেছেন: জীবন কী? একটা পাগলামি। জীবন কী? একটা মায়া, একটা ছায়া, একটা গল্প আর সবচেয়ে যা ভালো তা-ও খুবই কম, কারণ জীবন একটা স্বপ্ন…।
হয়ত তার কথাই ঠিক। স্কুলে একটা নাটক পড়েছিলাম আমরা। পাহাড়ের ওপর জেপ।
লুদভিগ হোলবার্গের (Ludvig Holberg) লেখা। এখানে, এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় খুবই বড় মাপের চরিত্র তিনি। বাবোক যুগ থেকে আলোকপ্রাপ্তির (Enlightenment) যুগে উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন তিনি।
তো, সেই জেপ একটা গর্তের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছিল একদিন। তার ঘুম ভাঙে এক ব্যারনের বিছানায়। তখন সে ভাবে সে যে এক কৃষক ছিল সেটা নিশ্চয়ই স্রেফ একটা স্বপ্ন। এরপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়তে লোকজন যখন তাকে ধরে আবার গর্তের ওখানে নিয়ে যায় তখন আবার ঘুম ভেঙে যেতে সে ভাবে ব্যারনের বিছানায় সে যে ঘুমিয়ে ছিল সেটা নির্ঘাৎ স্বপ্ন ছিল একটা।
হোলবার্গ এই থীমটা ধার নিয়েছিলেন কলদেরন-এর কাছ থেকে আর করেন নিয়েছিলেন প্রাচীন আরবী গল্প সহস্র এক রজনী থেকে। জীবনকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করার বিষয়টা অবশ্য আরো দূর অতীতের ইতিহাসেও পাওয়া যায়, চীন আর ভারতেও নেহাত কম নয়। এই যেমন প্রাচীন কালের চীনা সাধু চুয়াং-জু(Chuang tzo) বলেছিলেন: একবার স্বপ্ন দেখলাম আমি প্রজাপতি হয়ে গেছি, তো, এখন আমি ঠিক জানি না যে আমি চুয়াংজু কিনা যে স্বপ্ন দেখেছিল যে আমি প্রজাপতি হয়ে গেছি, নাকি আমি একটা প্রজাপতি যে স্বপ্ন দেখছে যে আমি চুয়াং-জু।
আমার মনে হয় কোনটা যে ঠিক তা প্রমাণ করা কঠিন।
নরওয়েতে এক সত্যিকারের বাবোক কবি আছেন, নাম পিটার ডাস (Petter Dass): তার জন্ম ১৬৪৭-এ, মৃত্যু ১৭০৭-এ। একদিকে তিনি জীবনকে ইহজাগতিক দিক থেকে বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে আবার তিনি এই বিষয়টি জোর দিয়ে বলতেন যে কেবল ঈশ্বরই শাশ্বত আর ধ্রুব।
সব জমি-ও যদি পতিত হয়ে যায়, তা-ও ঈশ্বর ঈশ্বরই, সব মানুষ যদি মরেও যায় তা-ও ঈশ্বর ঈশ্বরই।
কিন্তু সেই একই হিম-এ (hymn) তিনি উত্তর নরওয়ের গ্রামীণ জীবনের কথাও বলেছেন, বলেছেন লাম্প মাছ, কড মাছ আর কোল মাছের কথা। এটা একেবারেই বারোক একটি বৈশিষ্ট্য-একই সঙ্গে ইহজগৎ আর আধ্যাত্মিক বা পরজগতের কথা বলা। এই সব কিছুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগৎ আর ভাবের অপরিবর্তনীয় জগতের মধ্যে প্লেটো যে-পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন সে-কথা মনে করিয়ে দেয়।
আর তাদের দর্শন?।
সেটাও বিশিষ্ট হয়ে আছে প্রবলভাবে বিপরীত চিন্তাধারার মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কারণে। আগেই বলেছি, কিছু কিছু দার্শনিক বিশ্বাস করতেন যে অস্তিত্বশীল সব কিছুই শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে ভাববাদ (idealism)। এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির নাম বস্তুবাদ (materialism)। এই কথাটির সাহায্যে এমন এক দর্শনকে বোঝানো হয় যে-দর্শন মনে করে সব বাস্তব জিনিস নিরেট বস্তুগত দ্রব্য থেকে আসে। সপ্তদশ শতকে বস্তুবাদ-এর হয়ে কথা বলার মানুষও ছিলেন অনেক। সম্ভবত এঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস (Thomas Hobbes)। তিনি বিশ্বাস করতেন সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিস, মানুষ ও প্রাণী কেবল বস্তুকণা দিয়েই তৈরি। এমনকী মানবিক চেতনা বা আত্মা, তারও সৃষ্টি মস্তি ষ্কে সেই সব ক্ষুদে কণার চলাফেরা থেকে।
তার মানে ডেমেক্রিটাস যে-কথা দুই হাজার বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, হস তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলেন?
ভাববাদ আর বস্তুবাদ এমন দুটো বিষয় যা তুমি দর্শনের ইতিহাসের আগাগোড়াই দেখতে পাবে। কিন্তু বারোক যুগের আগে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি খুব কমই এমন পরিষ্কারভাবে একই সময়ে দেখা গেছে। নতুন বিজ্ঞান নিরন্তরভাবে রসদ যুগিয়ে গেছে বস্তুবাদকে। নিউটন দেখিয়েছেন যে সারা মহাবিশ্ব জুড়ে গতির একই সূত্র প্রযোজ্য এবং প্রাকৃতিক জগতের-পৃথিবীর আর মহাশূন্যের-সমস্ত পরিবর্তন সার্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ আর বস্তুর গতির নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।
অর্থাৎ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে একই অলংঘনীয় নিয়ম বা সূত্র বা একই মেকানিজম। ফলে, তত্ত্বগতভাবে একেবারে গাণিতিক সূক্ষ্মতায় প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবর্তন পরিমাপ করা সম্ভব। আর এভাবেই নিউটন আমরা যাকে বলি মেকানিস্টিক বিশ্বচিত্রতা সম্পূর্ণ করলেন।
জগৎকে কি তিনি বিশাল এক যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেছিলেন?
আসলেই তাই করেছিলেন তিনি। mechanic শব্দটা এসেছে গ্রীক শব্দ mechane থেকে, যার অর্থ মেশিন বা যন্ত্র। এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে হবস বা নিউটন এই মেকানিস্টিক বা যান্ত্রিক বিশ্বচিত্র আর ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে কোনো স্ববিরোধ দেখতে পাননি। কিন্তু অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সব বস্তুবাদীর ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য নয়। ফরাসী চিকিৎসক দার্শনিক লা মেরি (La Metrie) অষ্টাদশ শতকে একটি বই লিখেছিলেন লা হোমে মেশিন (L homme machine) নামে, নামটির অর্থ মানবযন্ত্র। পায়ের যেমন পেশী রয়েছে হাঁটার জন্যে, তেমনি মস্তিষ্কেরও পেশী রয়েছে চিন্তা করার জন্যে। এরপর ফরাসী গণিতবিদ লাপ্লেস (Laplace) একটি চরম যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এই ধারণাটির সাহায্যে: যদি কোনো বুদ্ধিমান সত্তা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুর সমস্ত কণার অবস্থান জেনে ফেলত তাহলে কোনো কিছুই অজানা থাকত না, ভবিষ্যৎ আর অতীত দুই-ই তার চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ত। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, যা কিছু ঘটে তার সবই পূর্বনির্ধারিত। ভাগ্যে লেখা আছে যে কোনো একটা কিছু ঘটবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে নির্ধারণবাদ(determinism)।
তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।
না। সব কিছুই একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফসল, আমাদের চিন্তা আর স্বপ্ন-ও। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান বস্তুবাদীরা দাবি করেছিলেন যে চিন্তার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক হচ্ছে প্রস্রাবের সঙ্গে কিডনি-র আর পিত্তর সঙ্গে যকৃতের সম্পর্কে মতো।
কিন্তু প্রস্রাব আর পিও-তো বস্তু। চিন্তা তো তা নয়।
তুমি প্রায় আসল জায়গায় হাত দিয়েছ। এই বিষয়ে একটা গল্প বলতে পারি তোমাকে। রাশান এক নভোচারী আর ব্রেইন সার্জন একবার ধর্ম নিয়ে আলাপ করছিলেন। ব্রেইন সার্জন খ্রিস্টান, কিন্তু নভোচারী তা নন। নভোচারী বললেন, বহুবার মহাশূন্যে গিয়েছি, কিন্তু কখনোই ঈশ্বর বা দেবদূতদের দেখিনি আমি। ব্রেইন সার্জন তখন বললেন, আমি অনেক চালাক-চতুর লোকের ব্রেইন অপারেশন করেছি কিন্তু কোনোদিনও একটা চিন্তার দেখা পাইনি।
কিন্তু এতে তো প্রমাণ হয় না যে চিন্তার অস্তিত্ব নেই।
তা নয়, কিন্তু এর মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে চিন্তা-ভাবনা এমন কোনো জিনিস নয় যার ওপর অপারেশন চালানো যায় বা যাকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে ফেলা যায়। এই যেমন ধরো, সার্জিকালি কোনো ভ্রান্তি দূর করা সম্ভব নয়। সেটা সার্জারির অন্তর্ভুক্ত নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক লাইবনিজ (Liebniz) মন্তব্য করেছিলেন যে, বস্তুগত জিনিস আর আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যে সঠিক পার্থক্য হচ্ছে বস্তুকে ছোট থেকে আরো ছোট অংশে ভেঙে ফেলা যায়; কিন্তু আত্মাকে এমনকী দুই ভাগে ভাগ করা যায় না।
না, তা সম্ভব নয়। ও-কাজে কোন ধরনের ছুরি ব্যবহার করবেন আপনি?
অ্যালবার্টো স্রেফ তার মাথা নাড়লেন। খানিক পর তিনি দুজনের মধ্যেকার টেবিলটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপর বললেন:
সপ্তদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুই দার্শনিক হলেন দেকার্ত আর স্পিনোজা। আত্মা আর দেহ-র মধ্যেকার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন তাদেরকেও ভাবিয়েছে বেশ। এবার আমরা তাঁদের কথা জানবো আরেকটু ভালো করে।
বলে যান। কিন্তু সাটার সময় বাড়ি ফেরার কথা আমার।