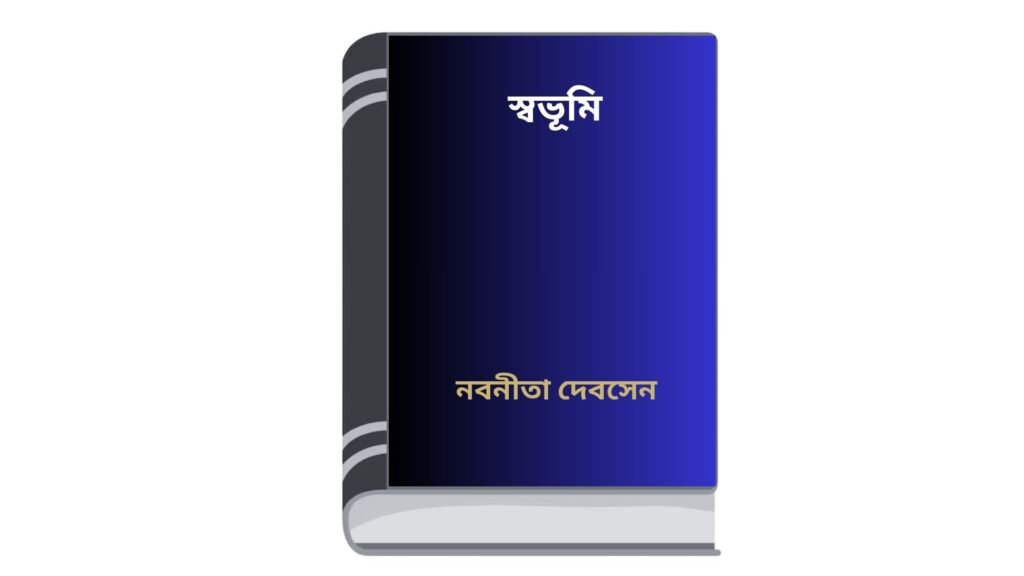স্বভূমি – ৩
ফ্রেডরিক নিকলসন
ঠিক সেই দেরি করেই রওনা হল প্লেনটা। কী যে হয়েছে আজকাল। কখনও যদি টাইমলি একটা প্লেনও ছাড়ে। হাইজ্যাকিংয়ের ভয়ে সিকিয়োরিটি সিস্টেমটা এতই জোর কড়াকড়ি করেছে যে তাতেই দেরি হয়ে যায়। প্রত্যেক এয়ার লাইনসেরই এক অবস্থা। এই তো সেদিন আবার টি. ডাব্লু. এ—র প্লেনটাকে ওই বিশ্রীভাবে হাইজ্যাক করল আরব গুন্ডাগুলো—অতগুলো নির্দোষ লোককে বিনা কারণে ধরে বন্দি করে রেখে দিয়েছে দিনের পর নি। হস্টেজ হিসেবে। ভয়েই তো আধমরা হয়ে যাবার কথা তাদের। অবশ্য এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনটা করাচির আগে থামছে না। গালফ কান্ট্রিতে নামবে না কোথাও। এই রক্ষে। নইলে আমার বউ যা, সে হয়তো কম্যান্ডোদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে খুনই হয়ে যাবে। ওই তেইশ বছর বয়সি মার্কিন ছেলেটার মতো। আহা আমাদের লালীর চেয়ে দু—তিন বছরের বড়। ছেলেটার বাবামায়ের কথা ভাবতে আমার খুব কষ্ট হয়। ওর বাবা যদিও একটা সাহসী পাবলিক স্টেটমেন্ট করেছে, আমার পুত্র শহিদ, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিয়েছে। তাকে নিয়ে আমরা গৌরবান্বিত। যাই মুখে বলুক আর বুকটা নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে। যুদ্ধের পর, যুদ্ধে বেঁচে ছুটি পেয়ে, ঘরের ছেলেটা ঘরে ফিরছিল। ফেরা হল না। তাকে গুলি করে মেরে কম্যান্ডোরা প্লেনের দরজা থেকে তার দেহটা টারম্যাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই তো সত্যের প্রতিদান। আলো তবুও ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেই। অত বুদ্ধিমতী মেয়ের এই দিকটা আমি সত্যি বুঝতে পারি না। আলোর প্লেন যদি হাইজ্যাকিং হয় তবে সে নির্ঘাত সত্যের ও ন্যায়ের হয়ে যুদ্ধ করতে যাবে, যাবেই, এবং প্রাণটি খোয়াবে, খোয়াবেই। প্রাণের ভয় বলে কিছুই নেই যে আলোর—যা দুর্দান্ত দস্যি মেয়ে সে। আর কথায় কথায় বুড়োআঙুল দেখাবে—”আর দশ বছর! আর আট বছর!” এখন বলে—”আর এক বছর।” ওর একটা রেচেড হরস্কোপ ছিল নাকি, তাতে নাকি কোন রেচেড ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছে ওর আয়ু মোটে পঁয়তাল্লিশ বছর। সেই নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ফাঁসির আসামির মতো আমার কাছে কেবলই স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দাবি করছে। সর্বত্র, সবসময়ে। সত্যি পাগল, একেবারে পাগলি। ক্রেজি গার্ল। একই রকম থেকে গেল তেইশ বছর। আশ্চর্য কিন্তু। আজ যখন পেছন ফিরে সিকিয়োরিটি চেকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে পড়ল, ও যখন শাড়ি পরে ক্যাম্পাসে হেঁটে যেত, আমি পেছন থেকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতাম। শাড়ি পরে হাঁটার একটা ছন্দ আছে। আলাদা একটা শ্রী আছে। এলিগ্যান্স আছে। আলো অবিশ্যি খুবই গ্রেসফুল আর এলিগ্যান্ট। এখনও প্রায় তেমনই সুন্দর ফিগার রেখেছে। অবশ্য ওর বিনা চেষ্টাতেই। ‘আছে’ বলাই ভাল, ‘রেখেছে’র চেয়ে,—কেন না আলো যা খুশি খায়, ক্যালোরি গোনে না। ফিগার সংরক্ষণের কোনও প্রোগ্রামই ওর নেই। সে বরং লালীর আছে। লালীর খুব ওজন বাড়ার ভয়। আমি আর লালী স্লিমিং করি, সাবধানে খাই, ব্যায়াম করি—মোটাও হই। আলোর ওসব ঝামেলা নেই। আজ যখন হেঁটে যাচ্ছিল, কে বলবে ও লালীর দিদি নয়, মা? লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় প্রাইম মিনিস্টার হলেন, জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর, সেই মাসেই লালীর জন্ম। জুন ১৯৬৪—তাই ওর নাম রাখা হয় লালী। লালবাহাদুর থেকে লালী। এই মাসেই ওর একুশ পূর্ণ হবে। মেজর হবে বলে মস্ত বার্থডে পার্টি দিচ্ছে ওকে ওর বন্ধুরা। মা থাকবে না বলে লালীর যত না মন খারাপ আলোই দারুণ মন খারাপ করতে করতে গেল। যতই লালী বলছে—”তুমি তো এমনিতেও আমাদের বন্ধুদের সেই পার্টিতে থাকতে পারতে না, মা, মন খারাপ করছ কেন?” ততই আলো বলে—”তবু, সেই দিনটাতে তোর কাছে তো থাকা হল না?” বড্ড সেন্টিমেন্টাল মেয়ে আলো। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বুঝতেই পারবে না আলোর আদ্ধেক কথাবার্তা, ওর মনের গতিবিধি। অথচ আলো প্রাচীন নয়, খুবই স্মার্ট, খুবই আধুনিক। কিন্তু ওই যে ওর ‘ঠাকুরঘরটা’ যেমন একটা কিম্ভূত একজটিক প্রেশাস ব্যাপার, ওর মনের ভেতরটাও ঠিক তেমনই। লোকে সামান্য গ্রিন কার্ডের জন্যেই প্রাণটা বের করে ফেলে আর আলো? কিছুতেই ইউ এস নাগরিকত্ব পেয়েও নেবে না। ক্যানেডিয়ানও হবে না। সেই গোঁ ধরে আঁকড়ে আছে তার ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট। আমার অবিশ্যি এই জন্যেই আলোকে অতটা ভাল লাগে। ওর আদর্শগত মতামতের মূল্য অনেকখানি ওর নিজের কাছে। তার জন্যে অনেকটা আত্মত্যাগে, সুবিধে ত্যাগে ও সর্বদা প্রস্তুত। আমাদের বিবাহিত জীবনটাই তো আলোর আদর্শগত আত্মত্যাগের একটা ঝলমলে দলিল। সত্যি, আমার কপাল অতিরিক্ত ভাল যে, জীবনে পেয়ে গেলাম এমন একজন মানুষকে। অথচ লোকে আলোকে অনবরতই ভুল বুঝছে। যা তার মনে আসে তাই মুখে বলে দেয়, সৌজন্যের ধার ধারে না, সুবিধাবাদেরও ধার ধারে না। নিজের ক্ষতি, স্বামীর ক্ষতি, কিছুই তার খেয়াল থাকে না। আমার বসকে রাম চটিয়ে দিয়ে আগের চাকরিতে আমার উন্নতি আটকে দিয়েছিল কে? আলোই তো। কারুরই তোয়াক্কা করে না সে। মার্কিন দেশ ছেড়ে এই কানাডায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম—এমনই বিশ্রী অসামাজিক অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। ছোট মার্কিন শহরগুলো তো গন্ডগ্রামের অধম। ‘নাগরিক বোধ’ যাকে বলে তা আশাই করা যায় না—মিড ওয়েস্টের ওই ভুট্টাখেতের বিস্তারে। ভালই হয়েছে, কানাডায় আমি অনেক ভাল চাকরিও পেয়েছি, অনেক শান্তিও আছি। এখানে আমরা দু’জনেই বিদেশি, দু’জনেই বাস্তুহারা, পরস্পরকে দেখতে পরস্পরই আছি। মা আসেন খ্রিসমাসের সময়ে। আমরা আর বড়—একটা যাই না লুইজিয়ানাতে। আমাদের সেই বড় বাড়িটা ছেড়ে মা এখন একা একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন যেটা পরিষ্কার রাখা মা’র পক্ষে সহজ। কিন্তু সেখানে আমাদের জায়গা নেই। বাবা মারা যাবার পরে মা সত্যি বড্ড একা হয়ে পড়েছেন। অবশ্য বাবা থাকতে আরওই অশান্তিতে ছিলেন। স্টিভটা মাকে একদম দেখে না। যদিও একই শহরে থাকে। অথচ মা ছোটবেলাতে আমাকে কী ভীষণ অবহেলাই করতেন, সবটা মনোযোগ দিতেন ছোটছেলের প্রতি। সেই ছেলেই এখন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখে না। খ্রিসমাসের সময়ে মাকে আসতে হয় কানাডায়, সেই ভারতীয় কালো পুত্রবধূরই বাড়িতে বড়দিনের উৎসব করতে। যার বিবাহে বাবা—মা প্রচুর বাধা দিয়েছিলেন এবং বাবা যাকে কখনও দেখেননি। সত্যি, কত তফাত দুটো কালচারে।
আলোর বাবা—মা—ও বিয়েতে খুশি হননি তখন, যদিও বাধা দেননি। এখন আলোর বাবা—মা—ও আসেন, আমার মা—ও আসেন। সাদা চামড়ার জামাই আর কালো চামড়ার বউকে দু’পক্ষই মেনে নিয়েছেন সম্ভবত লালীর জন্যে। লালীকে আমার মা—ও খুব ভালবাসেন যেমন, তেমনই ওঁরাও। কিন্তু আলোর মা এলে, আলোর পূর্ণ বিশ্রাম হয়। আর আমার মা এলে, আলো বলে—”মা’র তো সারাবছরই পরিশ্রম যায়, এই ক’টা দিন মা’র বিশ্রাম।” কথাটা সত্যিও বটে। কলকাতায় আলোর মা’র তো গৃহকর্মের জন্যে লোকই আছে। আমার মার বয়স তাঁর চেয়েও বেশি, কিন্তু তিনি সহায়হীন। দোকানপাট করা, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, কাপড় কাচা, রান্না করা, বাসন—ধোওয়া, সারাটা দিন মা’র এই করেই কাটে। তারই মধ্যে বা উল বোনেন। লালীর জন্যে চমৎকার এক একটা জামা তৈরি করে আনেন প্রত্যেক বছর। বাবাও মাকে কোনওদিন যত্ন করেননি, স্টিভও আজ ওঁকে দেখছে না। অথচ বাবার জন্য মা প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করেছেন। স্টিভের জন্যেই কী কম? তাই তো আমি আমার জন্যে আলোর কষ্ট করাটার যথসাধ্য মূল্য দিই। আমি দেখেছি স্বার্থপর পুরুষ কীরকমভাবে মেয়েদের মমতার সুযোগ নেয়। সর্ব উপায়ে তাদের দোহন করে। এবং শেষপর্যন্ত অকৃতজ্ঞ থাকে। সুখের সাথী হয়, দুঃখের ভাগীদার হয় না। বাবাকে দেখেই আমি শিখেছি কীরকম স্বামী না—হওয়া উচিত। মায়ের ওপরেই রাগ হয়ে যেত আমার, বাবার প্রতি তাঁর এই দুর্বলতা দেখে। বাবার শেষপর্যন্ত সাত খুন মাপ মায়ের কাছে। বাবাও সেটা জানতেন। জেনে, যা খুশি তাই করে বেড়াতেন। স্টিভ সেটাই দেখেছে। এবং ঠিক সেইরকম হয়েছে। ওর দুটি বউ ওকে ছেড়ে গেছে। সবাই তো আমার মা নয়। আবার একটা মেয়েকে জোগাড় করেছে স্টিভ। তবে সে মেয়ে এখনও ওকে বিয়ে করছে না। সহবাসিনী। এখন মেয়েরাও চালাক হয়েছে। তারাও হুটহাট বিয়ে করতে চায় না। আগে মেয়েরা বিয়ে না করলে শুতে চাইত না। অন্তত বিয়ে করবে, এই মুখের কথাটা না দিলে, কোনও ভদ্র মেয়েই বিছানায় যেত না। এখন শুনি তার উলটো। বিয়ে—থার বন্ধন, দায়িত্বভার, মাতৃত্ব—এ সবের মধ্যে না গিয়ে ফুর্তিফার্তা করতে মেয়েরাও রাজি। পিল সাম্রাজ্যের অধিবাসী যে সবাই। ভেবে—চিন্তে, দেখে—শুনে সুবিধাজনক বিবাহ। কিন্তু মজার জন্যে অতশত চিন্তার কী আছে? এ এক আশ্চর্য জীবনদর্শন।
লালীদের জীবনদর্শন। লালীর বন্ধুদের জীবনদর্শন। কত তফাত হয়ে গেছে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের।
আলোকে চুমু খেয়েই আমাকে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল। আর বাগদানের হিরের আংটি আঙুলে পরিয়ে, তার পরেই শয্যার কথা তুলতে সাহস পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রশ্ন শুনে আলো এতই আশ্চর্য চোখ তুলে তাকিয়েছিল যে আমি লজ্জায় লুকোতে পথ পাইনি।
তখনই পিল বেরিয়েছিল—তবে সদ্য চালু হয়েছে। তখনও কলকাতার অবিবাহিত মেয়েরা পিল খেতে শেখেনি। আমেরিকা সদ্য শিখেছে। ডায়াফ্রাম, জেলি, আর ফ্রেঞ্চ ক্যাপই চলত বেশি। কনডোমকে বলতাম আমরা ফ্রেঞ্চ ক্যাপ। আর ফ্রান্সে হয়তো কনডোমকে ইংলিশ ক্যাপ বলত—কে জানে? বাব্বাঃ, যা প্রুড ছিল আলোটা। ‘ভালোমেয়ে’র টিপিক্যাল প্রতিমূর্তি।
লালীও অনেকটা তেমনই হয়েছে, অন্যান্য সমবয়সি মেয়েদের তুলনায় ও অনেক বেশি প্রুড। একসঙ্গে একটার বেশি ছেলেকে পাত্তা দেয় না। ল্যারিকে নিয়ে যেভাবে মজেছে, সেটা আর কোনও চালাকচতুর মেয়ে হলে মজতই না! লালী একটা জাতীয় সায়েন্স ফাউন্ডেশনের স্কলারশিপ নিয়ে নামী কলেজে মামার মতো ফিজিক্স পড়ছে—এটা ওর সফোমর ইয়ার আর ল্যারি মোটে পড়াশুনো শেষই করেনি, একটা হ্যামবার্গার জয়েন্টে চাকরি করে, ওয়েটারের। দেখতে অবশ্য গ্রিক দেবতাদের মতো। জানি না লালী কী করে ওর সঙ্গে সারাজীবনটা কাটাবে! এদের বিয়ে আমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু না বললে শুনছে কে? আলো খুবই বুদ্ধিমতী, এই প্রথমবার দেখলাম একটা ট্যাক্সফুল আচরণ ও করল। মেয়েকেও বাধা দিল না, ছেলেটাকেও কিছু বলল না। এই জুটি পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও ভদ্র ব্যবহার করে চলেছে। ল্যারি ছেলেটাকে খারাপ লাগে না আমাদের। লালীর বন্ধু হিসেবে ঠিক আছে, কিন্তু তার জীবনসঙ্গী স্বামী হিসেবে ঠিক নেই। ক’দিন বাদে ওদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু কিছুই থাকবে না। একজনের মানসসঙ্গী আরেকজন হতে পারবে না। হয় একজনকে নামতে হবে, নয় একজনকে উঠতে হবে। ওঠা তো সহজ নয়, টেনে নামানোই সোজা। যে পড়া শেষ করেনি তার পক্ষে হঠাৎ হাই—ফিজিক্সের সমস্যা নিয়ে বুদ্ধিমানের মতো বাক্যালাপ করা সম্ভব হবে না। লালীর কর্মক্ষেত্রের বন্ধুবান্ধব আর ল্যারির কর্মক্ষেত্রের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে আশমান—জমিন ফারাক থাকবে, কোনও পার্টিতেই দু’পক্ষকে ডাকা যাবে না, ল্যারি সহজ বোধ করবে না লালীর সহকর্মীর বাড়িতে, লালীর সাহচর্যেও সহজবোধ করবে না ল্যারির সহকর্মীরা। কিন্তু এসব কথা কিছুই ওরা এখন শুনবে না, বুঝবে না। আর ওদের সন্তান হলে কী যে হবে ভাবতেই পারি না। ওরা এসব মানবে না। এখন যে ওদের মধ্যে কোনও অমিলই নেই। দু’জনেই হ্যামবার্গার খাচ্ছে, একজন দিচ্ছে আর একজন খাচ্ছে, দু’জনেই ড্রাইভ—ইন মুভি দেখতে যাচ্ছে, দু’জনেই ডিস্কো নাচছে, লেটনাইট বিয়র পার্টিতে যাচ্ছে, ব্রেকড্যান্সিং নাচছে, সুইমিংয়ে যাচ্ছে। দু’জনেই উইক এন্ডে লং ড্রাইভের দূরপাল্লায় হুস করে বেরিয়ে পড়ছে। ভালবাসছে। ওদের এখন সবকিছুই বহির্মুখী কাজকর্ম। সবই শরীর নির্ভর। যৌবননির্ভর। আবেগনির্ভর। এর পরে যখন শরীর পুরনো হবে—শুরু হবে মননের, রুচির, বুদ্ধির কাজ, সূক্ষ্মবোধের, চয়েসের প্রশ্ন উঠবে তখনই ধরবে ভাঙন। মননজগৎ ওদের একা নয়। এক হতেই পারে না।
ল্যারির মা তিনবার যত্রতত্র বিয়ে করেছে, শেষকালে একজন কালো হিপিকে বিয়ে করে নিজেও হিপি হয়ে শিশু দুটিকে ফেলে রেখে নেপালে চলে গেছে। তখন ল্যারি তিন বছরের শিশু। ল্যারি আর তার সদ্যোজাত বোনটিকে বড় করেছে তার দিদিমা। দাদু কারখানার শ্রমিক। চমৎকার মানুষটি, আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দিদিমা মানুষটিও খুবই ভাল, তবে ওরা কেউ বইপত্র পড়ে না। ল্যারিও বইপত্র ছুঁয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়নি। অথচ লালীকে আমরা বইয়ের মধ্যেই মানুষ করেছি। ল্যারি কমিউনিস্ট—ঘেঁষা কথাবার্তা বলে লালীকে। বেশ ইমপ্রেস করে ফেলেছে কিন্তু লালী জানে না, ও সবই ওর ইউনিয়নে শেখা বুলি, শোনা কথা। নিজের উপলব্ধিতে গড়া কথা নয়। আলোর সঙ্গে এ নিয়ে আরও কথা বলতেই হবে আমাকে। এখনও ফর্ম্যালি এনগেজড হয়নি ওরা, হলেও বিয়েটা হবার আগেই আমি মনে করি যে করে হোক এনগেজমেন্টটা ভেঙেই দেওয়া উচিত। আলো এটা হয়তো মানতে চাইবে না। আলোর নিজের পড়াশুনোর উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিয়ের অন্ধকারে ঘুচে গিয়েছিল। এ জন্যে অপরিসীম লজ্জা আমার। আমি চাই না আমার লালীরও ঠিক সেটা হোক। ল্যারিকে বিয়ে করা মানে, লালীর পড়া নষ্ট, তার কর্মজীবন নষ্ট, এককথায় জীবনের সব উজ্জ্বল রঙিন সম্ভাবনা ধ্বংস। প্রেম ভাল জিনিস, কিন্তু প্রেমের চেয়েও জীবন বড়, জীবনের চেয়ে প্রেম কেন বড় হয়ে উঠবে? সেটা কৃত্রিম। প্রেমের নাশকতার দিকটাতে উৎসাহিত করা উচিত নয় আমাদের। কে বলতে পারে আলো হয়তো বিয়ে না করে সময়মতো রিসার্চ শেষ করলে আমার চেয়ে ঢের বড় মাইক্রোবায়োলজিস্ট হতে পারত। এখন এত দেরিতে শুরু করেও তো রীতিমতো ভাল কাজ করতে পারছে। ওর এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। লালী সে জাতের মেয়েই নয়। এখনই না পারলে, লালী আর কোনওদিনই পারবে না। ওকে তলিয়ে বোঝানো দরকার যে—এ বিয়ে অসমান, ভিতের ওপরে, এ বিয়ে নড়বড়ে হবেই। তোমরা বন্ধু থাকো। বিয়েটা কোরো না। আসলে আলোই পারবে বোঝাতে। ইন্ডিয়াতে গেলে লালীর সঙ্গে ওকে কথা বলাতে হবে। আমি এখানে একদিন বরং ল্যারির সঙ্গে ম্যান—টু—ম্যান বাক্যালাপ করে দেখতে পারি। যদি কিছু হয়।
আলোর ইচ্ছে লালীকে ইন্ডিয়াতে বিয়ে দেয়। গৃহকর্মের লোকজন থাকবে, স্বামী—স্ত্রীতে মিল থাকবে। আত্মীয়স্বজন থাকে। তা ছাড়া ওর ফিজিক্সি—জ্ঞান ভারতের কাজে লাগবে। কিন্তু আমি মনে করি না লালী ইন্ডিয়াতে থাকতে পারবে। ও বড্ড আরামপ্রিয়। ইন্ডিয়াতে যতই গৃহভৃত্য থাকুক, জীবন মানেই জীবন সংগ্রাম। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিসপত্র পেতেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। তা ছাড়া লালীর ওসব একজটিক অন্যভাষী অন্যদেশি পুরুষমানুষও পছন্দ হবে না। ওই হ্যামবার্গার রুটবিয়ারের মতো ওর পছন্দ চুইংগাম—চিবোনো নর্থ আমেরিকান পুরুষ। লালীকে আমি যতটা বুঝতে পারি আলো ততটা বোঝে বলে মনে হয় না। আলো ওকে নিজের মতো করে ভাবে। আলো চায় আলোর যা ভাল লাগে লালীরও তাই ভাল লাগুক। সে কখনও হয়? হয় না যে—সেটাও বোঝে না আলো। অত বুদ্ধিমতী, অথচ মেয়ের বেলায় নির্বোধের মতো ভাবে। মেয়ে কি ওর নিজেরই প্রসারিত অংশ? মেয়ে অন্য লোক। অন্য মানুষ। অন্য যুগের, অন্য ধাতের, অন্য রুচির অন্য প্রকৃতির মানুষ। সে তার মায়ের ইচ্ছার বাহক হবে কেন? ইন্ডিয়া থেকে ফিরে যদি দেখি ল্যারি আর কারুকে ডেট করছে তা হলেই সব চেয়ে ভালো হয়। আজ ল্যারি এয়ারপোর্টে যেতে পারেনি বলে আমি অন্তত খুবই খুশি হয়েছি। পরিবারের একজনের বিদায় মুহূর্তে ভদ্রতা—লৌকিকতার সৌজন্য করতে ভাল লাগে না। তা হলে লালী সারাক্ষণ ল্যারিকে নিয়েই মত্ত থাকত আলোর দিকে মন দিত না। আলো মুখে কিছুই বলত না, কিন্তু প্লেনে সারাটা পথ একা একা মনে মনে গুমরে মরত। আমি তো জানি কত অল্পেই তার অভিমান হয়ে যায়। লালী না বুঝে ওকে অনবরত আহত করে।
বাড়ি ফিরে লালী ওপরে চলে গেছে স্নোয়িকে নিয়ে। নিজের ঘরে বসে কেব্ল টিভি দেখছে হয়তো। এই নেশাটা ওকে ধরিয়েছিল আলোই—কেব্ল টিভি দেখার নেশা। আর এখন তো আলোর নতুন নেশা ভিডিওতে সিনেমা দেখা। দিনরাত হিন্দি সিনেমার ক্যাসেট নিয়ে আসছে ক্লাব থেকে। আর বসে বসে আজেবাজে হিন্দি ছবি দেখছে। কী করে দ্যাখে যে? টিভিতেও দেখতাম আলো নিয়ম করে যাচ্ছেতাই সব সোপ—অপেরার সিরিয়ালগুলো মন দিয়ে দেখত আর চোখের জল মুছত। তাই বম্বে ফিল্ম দেখতে ওর ভাল লাগলে অবাক হবার কিছুই নেই। আনরিয়াল লাইফের ছবি ওর পছন্দ হয়। দারুণ রোমান্টিক যে ভিতরে ভিতরে! এই তো লালী, মোটেই হিন্দি জানত না। এখন হিন্দি ছবি দেখার কল্যাণে দিব্যি কাজ চালানোর মতো হিন্দি বলতে—বুঝতে পারে। আলো তাই কেবল দুঃখু করে কেন ক্লাবে বাংলা ছবি আনে না। কেবল সত্যজিৎ রায় আর মৃণাল সেন। তাও যদি ফেস্টিভ্যালট্যাল কিছু থাকে। অথচ বাংলাতে রীতিমতো হেভি এটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি চালু হয়েছে। টোরোন্টোতে বাঙালির অভাব নেই, কেন তবে ক্লাবগুলোতে বাংলা সিনেমার অভাব? আলো বলেছে কলকাতা থেকে যত পারে বাংলা ছবির ক্যাসেট কিনে আনবে। ঘরে বেশ কিছু বাংলা সিনেমা থাকলে, লালীকে ভিডিওতে ও বাংলা শিখিয়ে দেবে। লালী অবশ্য বাংলা জানে। আলোর মা তো বাংলাই বলেন, লালী সবই বোঝে। তবে বলতে পারে না। ‘বলতে চায় না’ বলাই ঠিক। ওর মামাতো ভাইবোনেরাও প্রায় তাই। তবে মায়া আর কালো তো বাংলাতেই কথা বলে বাড়িতে তাই বাংলা শুনতে পায় জয়—পিউরা লালীর চেয়ে বেশি। অবশ্য লালীও বাংলা কম শোনে না। আলো তো তেইশ বছর ধরে আমার সঙ্গে লাগাতার বাংলাই বলে এল। আমি ওর সমস্ত বাংলা বুঝি। উত্তর দিই ইংরেজিতে—লজ্জা করে বলতে। বাংলাতেও উত্তর দিই, মাঝে—মধ্যে। যেমন—’যাচ্ছি’, ‘ কোথায় গেল’, ‘এসো’, ‘চলো’, ‘পাচ্ছি না’, ‘দাও’, ‘খুব ভাল’, ‘বিশ্রী’, ‘আছে’, ‘নেই’, ‘লক্ষ্মী মেয়ে’, ‘তাড়াতাড়ি’, ‘হ্যাঁ’, ‘না’, ‘ঠিক আছে’, ‘ভাল আছি’, লালী তাও বলে না। অথচ আলো লালীর সঙ্গেও আগে সমানে বাংলা বলেছে। ছোটবেলাতে বাংলায় ঘুমপাড়ানি গান শোনাত। আলো এখন আর লালীর সঙ্গে বাংলা বলে না। এটা যে ওর কত বড় অভিমান, আমি বুঝি, কিন্তু লালী সেটাও বোঝে না। অথবা বুঝলেও গ্রাহ্য করে না। আজ লালীতে আর আলোতে বেশ সুন্দর আড্ডা হচ্ছিল গাড়িতে। এয়ারপোর্টে পৌঁছেও দু’জনে একসঙ্গে ঘুরছিল, মজা করছিল। প্লেনটা অনেক লেট করল তো। সব সময়ে ওদের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবসাব তো থাকে না। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড টেনশন হয়। তখন আমার খুব অসহায় লাগে। আমি বুঝতে পারি দু’জন পূর্ণবয়স্ক নারীর মধ্যে টেনশন হচ্ছে, মা—মেয়ে সম্পর্কটার চেয়ে, দু’জন এ্যাডাল্ট ফিমেলের নিজের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দেবার। লালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নটাই বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়ায় তখন। ভাগ্যিস আমার ছেলে হয়নি। বাবার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। বাবা আমাকে সহ্য করতে পারত না, আমিও পারতাম না বাবাকে। অথচ স্টিভের সঙ্গে বাবার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। ছোটছেলেকে বাবাও স্নেহ করত বেশি। একই সংসারে যে দুজন পুরুষের থাকা যে সম্ভব নয়, এটা বাবা আমাকে বেশ ছোটবেলাতেই বুঝিয়েছিল। স্টিভ কিন্তু বাবার মৃত্যু পর্যন্ত বাবার কাছেই ছিল। স্টিভকে বাবা হয়তো পরিণত পুরুষমানুষের মর্যাদা দেয়নি, বালসুলভ মমতায় দেখেছে। এক সংসারে দু’জন নারীরও স্থানসংকুলান হয় না। আলো আর লালী দু’জনেই আমার দু’টি অতি প্রিয়, প্রিয়তম মানুষ এবং তারা নারী। কিন্তু লালী যতই রূপবতী এবং যুবতী হোক না কেন শৈশবের পটের চেয়ারে বসে লাল—নীল বলের সারি নিয়ে নাড়াচাড়ার মধুর মূর্তিটি আর আমার মন থেকে ঘুচবে না। ফ্রয়েড পণ্ডিত যাই বলুন না কেন মেয়ের প্রতি আমার কোনওরকম সেকশুয়াল ডিজায়ার হয় না। মেয়ে আমার মেয়েই। মেয়েমানুষ নয়। আলো সেই মেয়েমানুষ। সেই আমার জীবনের বাকি আধখানা, যাকে ব্যতীত আমি অসম্পূর্ণ। আলো তো মা, লালীকেই হয়তো সে আমার চেয়ে বেশি করে ভালবাসে, কিন্তু ভেবেচিন্তে বলতে পারি পুরুষমানুষের জীবনে সন্তানের চেয়ে স্ত্রী ঢের বেশি জরুরি। আলোই প্রথম।
শেষপর্যন্ত লালীর জীবনে কে যে প্রথম হবে তা আমরা এখনও জানি না। ল্যারিকে আমি স্থায়ী সঙ্গী ভাবতেই পারি না। লালীকে বাঙালি বানাতে আলো আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, লালীও আপ্রাণ চেষ্টায় আলোর ইচ্ছায় বাধা দিয়ে চলেছে—সে একদমই বাঙালি হতে চায় না। তার লম্বা কালো চুলটি ভিন্ন সে আর কোনওই ভারতীয় চিহ্ন বহন করত না এতদিন। গতবছরে ইন্ডিয়াতে গিয়ে দেখছি নাকে একটা হিরে বিঁধিয়ে এসেছে। আলোও বছর কয়েক হল একটা বড় হিরে পরতে শুরু করেছে নাকে। এবার লালীও পরল। লালী আবার কানেও তিন—চারটে করে ফুটো করেছে, সেখানেও তিন চারটে করে হিরে মুক্তো কীসব যেন রত্নটত্ন পরে। যাচ্ছেতাই। এই যে নাকফুটো করে রত্নপরা, কান ফুটো করে, তাও আবার একটা নয়, সারি বেঁধে ফুটো ফুটো করে গয়না পরা আমার এসব বড্ড জংলি লাগে। আলোর হিরে—বিহীন মুখখানা আমার বেশি দ্যুতিময় মনে হত। বেশি স্বাভাবিক। যদিও সবাই বলেছে ওকে নাকি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখাচ্ছেও নিশ্চয়ই, নইলে লালী ওকে অনুসরণ করত না।
লালী তো সবরকম ভারতীয়ত্ব সযত্নে পরিহার করে চলে। এমনকী বাড়িতে কারি—রাইস খেতে পর্যন্ত ভালবাসে না। আলো যত চেষ্টা করে কোথাও পার্টিটার্টি থাকলে ওকে শাড়ি পরাতে, লালী ততই জিনস—গেঞ্জি পরে বেড়ায়, আলো যত চেষ্টা করে ওর চুলে বিনুনি করে দিতে, লালী তত একপিঠ দীর্ঘ এলোচুল খুলে ঘোরে।
আলো চায় লালী ভাল ভাল ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টদের ডেট করুক—লালী কেবলই ক্যানেডিয়ানদের ডেট করে, এবং ভারতীয় ছাত্রদের পরিহার করে চলে। আলো চেয়েছিল লালীকে ইন্ডিয়ান মিউজিক, ইন্ডিয়ান ডান্সিং শেখাতে, চমৎকার শিক্ষক আছেন টোরোন্টোতে—এখানকার বাঙালি মেয়েরা কত কিছুই শেখে—লালী তো কিছুতেই ভারতীয় কিছু শিখল না। ব্যায়ামের জন্য স্প্যানিশ ক্যালিপসো ডান্সিং শিখল। সে যেন জেদ ধরেই তার ইন্ডিয়ান পশ্চাৎপটটা উপেক্ষা করতে চায়। আলোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে এখন বেলি—ডান্সিং শিখছে। আশ্চর্য! আমি ধন্য হয়ে যেতাম এমন একটা দীর্ঘ মহার্ঘ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমার রক্তে থাকলে। আমি আলোর সঙ্গে মিশে যতটা পারি ভারতীয়ত্ব শুষে নিয়েছি—মূল্যবোধের দিক থেকে রুচিবোধের দিক থেকে। আলো চমৎকার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পেরেছে আমাদের দ্বৈত জীবনে। এই পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝখানে কোনও দ্বন্দ্বই যে এ সংসারে নেই, তা কেবল ওরই গুণে। সর্বান্তঃকরণে ভারতীয়তা বজায় রেখেও আলো বাহ্যিক প্রাত্যহিক জীবনে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ছন্দকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। এটা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারি আমি যখন আমার মা আসেন। মায়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও অস্বস্তি দেখি না। মা তো উদার নন, বদ্ধ দক্ষিণী সমাজের মধ্যবিত্ত মন তাঁর। আবার যখন কলকাতা থেকে বাবা—মা আসেন তাঁরাও বেশ স্বচ্ছন্দে থাকেন আমাদের সংসারে। হ্যাঁ, ওই সময়টায় অবশ্য লালীও কিছু কিছু কমপ্রোমাইজ করে। যেমন, রাতে দিদিমার রান্না কারি—রাইস খায়। দিদিমার জন্য সকালের পুজোর ফুল তুলে দেয়। দাদু—দিদিমাকে নিয়ে গাড়ি করে বিভিন্ন বাঙালি বন্ধুদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়, নিয়েও আসে। দাদু—দিদিমার সামনে কক্ষনও ধূমপান করে না। এমনকী নিজের ঘরে অ্যাশট্রে পর্যন্ত রাখে না। পুজোর ক’টা দিন শাড়ি পরে। দাদু—দিদিমার জন্য এসব লালী নিজে নিজেই করে—আলো বললে হয়তো করত না। আমাদের বাঙালি বন্ধুদের বাড়িতে লালী কিছুতেই আর যেতে চায় না। যখন তারা নিমন্ত্রণ করে, লালী বাড়িতেই ডিম ভেজে খায়। বাঙালি বন্ধুরা লালীর রূপগুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অথচ লালী তাদের বিশেষ পাত্তা দেয় না। শুনেছি বাংলাসাহিত্য বিপুল ঐশ্বর্যময়, আমি বৈজ্ঞানিক মানুষ, ইংরাজিতেও সাহিত্য—টাহিত্যের ধার ধারি না, তাই বাংলাও পড়ি না—কিন্তু লালীটা তো একটু শিখতে পারত? ওর দাদু কত চেষ্টা করলেন, কিন্তু লালী, বর্ণপরিচয় থাকা সত্ত্বেও বাংলা পড়তে রাজি নয়। বাংলায় এক লাইন চিঠিও লেখাতে পারে না আলো। অথচ অক্ষর পরিচয় ওর বাল্যকালেই হয়েছে। ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা হরফও দিব্যি লিখতে—পড়তে শিখেছে লালী। একবার আলো বলেছিল ওকে এক বছর শান্তিনিকেতনে রাখবে। ভেবেছিল যখন, তখন লালী ছোট, তারপর কখন যে কলেজে ঢুকে গেল, এখন চার বছরের পড়া। অবশ্য মধ্যে এক বছর চলে গেলেও হয় না এমন নয়। ফিরে এসে আবার পড়বে। কিন্তু প্রসঙ্গটা তুললেই লালী প্রবল আপত্তি করে। যদিও শান্তিনিকেতন ওর খারাপ লাগেনি। —”কলকাতার চেয়ে ঢের ভালো, কিন্তু খুব গরম, এয়ার কন্ডিশনিং নেই, আইসক্রিম নেই, ওখানে সাতদিন ক্যাম্পিং করা চলে। এক বছর কে থাকবে? নো ওয়ে।” শান্তিনিকেতন হল না। আলোর আর লালীকে বাঙালি করা হল না। মেয়ের বদলে আমিই চেষ্টা করি যথাসাধ্য আলোর মনের মতো বাঙালি হয়ে যেতে। কালো আমাকে ফ্রেডই ডাকে, কিন্তু মায়া ‘জামাইবাবু’ বলে। আর অতিকষ্টে ‘পি—সে’ বলে ডাকে আমাকে ওদের ছেলেমেয়েরা। অথচ লালী কালোকে ‘মামা’ বললেও ‘মামিমা’ কিছুতেই বলবে না। সেই ‘আন্টি মায়া’। তারপর ঠাট্টা করে ওকে বাংলা ঢঙে ‘মায়া আন্টি’ ডাকটা কালোই শিখিয়েছে। লালী না হয় আধা বাঙালি। আশ্চর্য! কিন্তু জয়—পিউ—মউরা? পুরোই বাঙালি তো? ওদের বাবা—মা দু’জনেই বাঙালি। অথচ ওরাও হয়েছে ঠিক লালীরই মতো! এক বর্ণ বাংলা পড়বে না, লিখবে না, বলবেও না। জিনস—টিশার্টে, হ্যামবার্গারে বাবলগামে, ওয়াকম্যানে, ব্রেক ডান্সিংয়ে ওরা একেবারে মার্কিন টিনএজার। মায়া বাংলা নিয়ে ওদের কিছুই বলে না। মায়ার তো আলোর মতো বাঙালিয়ানার জন্যে পাগলামি নেই। ওর সময়ও কম। বেবিসিটারের কাছেই ওর বাচ্চারা বড় হয়েছে, বাংলাটা আর শেখেনি। ফিজিসিস্ট মা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিই বলে। কালোর সঙ্গে বাংলা। টাইম সেভিং প্রসেস— যে যেটা ভাল বোঝে যাতে ওর সুবিধা।
আমি ওদের বুঝতে পারি না। মাতৃভূমির প্রতি ওদের টান নেই। মাতৃভাষা বলতে আমাদের ছেলেমেয়েরা লজ্জা পায়, মাতৃভূমির সংস্কৃতি ওদের জানতে ইচ্ছে করে না। মাদার টাং বলে একটা কথা তো আছে? মাতৃভাষা তো বাংলাই ওদের? অথচ ওরা সেটাই শিখতে রাজি নয়। এদিকে গড়গড় করে ফরাসি বলতে পারে লালী—অল্প অল্প হিন্দিও নাকি শিখে ফেলেছে, আলো তাতে মহা গর্বিত। মউ—পিউদের সমস্যাটা আরও গভীর। আরও প্রখরও বটে। এটা ওদের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রশ্ন। অবশ্য লালীদের প্রজন্মটাকে বুঝতে পারা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। আমি কি আলোকেই সবটা জেনেছি? ওর মনে নিশ্চয়ই গভীর কষ্ট আছে। ভারতবর্ষে বাস না—করার কষ্ট। একটি মাত্র মানুষকে ভালবেসে কাছে পেতে চেয়ে কোটি কোটি মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার কষ্ট। তাই ওর সঙ্গী হিসেবে বোধহয় ও লালীকে ভারতীয় করতে চেষ্টা করে, বাঙালি করতে চেষ্টা করে। ফলটা হয় উলটো। অবশ্য মায়া তো ভারতীয়তার কোনওরকম চেষ্টাই করে না, নিজেই শাড়ি পরে না। আর ফলও তো একই হয়েছে। কালো বলে, —”পৃথিবী ছোট্ট হয়ে আসছে ফ্রেড, এসবে আর এখন কিচ্ছু এসে যায় না। দু’দিন করে এসব এথনিক বাউন্ডারি উঠে যাবে। এখন যেমন জগতে অ্যান্টি—রেসিজম মুভমেন্ট হচ্ছে, তেমনই এ দেশে এথনিক গ্রুপিজম—এর বিরুদ্ধেও এখন থেকেই মুভমেন্ট হওয়া উচিত। টোরোন্টোয় তোমরা এসব এথনিক গ্রুপ নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করো।”
হ্যাঁ, সেটা অবশ্য করে টোরোন্টো। এখানে বিরাট উৎসব হয় সামারে—বিভিন্ন এথনিক গ্রুপের কালচারাল প্রোগ্রাম চলতে থাকে লেকের ধারে। আর তখনও তো টের পাওয়া যায় কী আশ্চর্য এই দেশটা! একটা মিনি—পৃথিবী। কত যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সংস্কৃতির মানুষেরা এসে এই টোরোন্টোকে আপনার করে নিয়েছে! কানাডা আর ইউনাইটেড স্টেটসের এই বিশেষ চরিত্রটি আছে। প্যারিসে নির্ভেজাল ফ্রেঞ্চ কালচার; বার্লিনে জার্মান; মস্কোয় রাশ্যাম; রোমে ইতালিয়ান কিন্তু টোরোন্টো? তাতে কী নেই? যেমন নিউইয়র্ক। সব দেশেরই মানুষের বাস সেখানে। সেটাই তার স্বকীয়তা। এথনিক গ্রুপ হিসেবে অঞ্চল ভাগ করেই বসবাস করে সেখানে মানুষেরা—ইতালির লোক, পোলান্ডের লোক, বুয়ের্তোরিকোর লোক, ইহুদিরা, চিনেরা, কালোরা। ভারতীয়দের অমন কোনও নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। আজকাল জ্যাকসন হাইটসের ওদিকটায় হচ্ছে বটে বেশ ভারতীয় জোট। পুজোটুজো হয়। প্রচুর ভারতীয় দোকানপাট হয়েছে। শাড়ির দোকান, টু টোয়েন্টি ভোল্টের ইলেকট্রিক্যাল গুডসের দোকান—ভারতীয়রা দেশে ফেরার সময়ে গাদাগাদা কিনে নিয়ে যায় ডিসকাউন্টে। টোরোন্টোর চিনেপাড়া যেমন একটা অপূর্ব দেখবার জিনিস দুঃখের বিষয় এখানকার ভারতীয় পাড়াটা কিন্তু তেমন নয়; যদিও সেখানেও বহু ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যের দোকান, শাড়িটাড়ি, ইন্ডিয়ান জিনিসপত্র প্রচুর বিক্রি হয়। ওপাড়ায় আলোকে তো প্রায়ই যেতে হয়। বিশেষত ওর মা—বাবা এলে। পান কেনা চাই তো! জর্দা! কালোর সঙ্গে আলোর এইখানে বিরাট তফাত। একজন তার এথনিক আইডেনটিটিকে কোনও মূল্যই দেয় না, যদিও সে বিয়েটা করেছিল বাঙালিকেই, আরেকজন সাত সমুদ্র পারের অজানা দেশের মানুষের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, অথচ নিজের এথনিক আইডেনটিটিটা সংরক্ষণ করতে তার প্রাণপণ চেষ্টা। আমি অবশ্য আমার লুইজিয়ানা—ব্যাকগ্রাউন্ড সংরক্ষণে মোটেই আগ্রহী নই। বরং সেটা ভুলতে পারলেই খুশি হই। প্রায়ই ভাবি ক্যানেডিয়ান হয়ে যাব। রেগনের কাণ্ডকারখানা যত দেখছি ততই আমার মার্কিনি পরিচয়টা কম সুস্বাদ বলে মনে হচ্ছে। ইউনাইটেড স্টেটসের একটা নব যৌবন এসেছিল ষাটের দশকে, যখন আমরা ছাত্র। পূর্ণ যৌবনে সেই স্বাস্থ্যকর, আদর্শ সমৃদ্ধ আবহাওয়াতে আমরা বড় হয়েছিলাম। লুইজিয়ানার গ্রামের ছেলে, আর ভারতবর্ষের শহুরে মেয়ে একসঙ্গে দিনের—পর—দিন সিট—ইন ডেমনস্ট্রেশন করেছি ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে। আর এখন? ইউনাইটেড স্টেটসের ছাত্ররা আর দাড়ি রাখে না। বোতাম—খোলা শার্ট পরে না। চটি পায়ে হাঁটে না। তারা ছোট করে চুল ছাঁটে, রোজ দাড়ি কামায়, জুতো—মোজা পরে শার্টের সব বোতাম এঁটে ভালো মাইনের চাকরির সন্ধান করে বেড়ায়। এ একটা নতুন প্রজন্ম—এরা কেবল নিজেরা ভালোভাবে থাকার কথা ভাবে। নিজের আরামের কথাটুকু ভাবে। বহির্বিশ্বের কথা মনের কোণেও ঠাঁই দেয় না। সরকারি সব শালিসিও সেই আদর্শে গড়া। অসম্ভব এভাবে একটা জাতের উন্নতি হওয়া। এতদূর স্বার্থকেন্দ্রিক জীবনের একটা কু—প্রতিক্রিয়া তো ঘটতে বাধ্য। আমি জানি না তার চেহারা কেমন হবে, তার চরিত্র কেমন হবে। কিন্তু সেটা ঘটবে লালীদের জীবনেই। আমি তো দেখছি প্রতি দশ বছরেই প্রজন্ম বদল হচ্ছে—আমরা বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব সেই পরিবর্তন—যদি না তৃতীয় মহাযুদ্ধ সকলের ভবযন্ত্রণার শান্তি করে ফেলে।
আলোর ভেতরে একটা খোলামেলা, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, আদর্শবাদী মন আছে—যেটা আমাকে প্রথমে আকৃষ্ট করেছিল, এখনও করে। আলো কখনও নিজের কথাটা আগে ভাবে না, প্রথমেই ভাবে অন্যের সুবিধা—অসুবিধার দিকটা। আলোর এই গুণটা লালী কিন্তু পায়নি। লালী বেশ স্বার্থপর মেয়ে হয়েছে। ওর দোষ নেই, যুগটাই এইরকম, ওর সব বন্ধুরাও এই একইরকম। লালী বরং অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি মানিয়ে চলে। তেমন জোরালো কোনও বিদ্রোহ এখনও পর্যন্ত করেনি আমাদের বিরুদ্ধে। বাড়িতেই তো আছে, অন্য অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে উঠে যায়নি তো বন্ধুদের সঙ্গে! সেটাই মস্ত কথা! ঘরদোর হুভার করতে কখনও কখনও মাকে সাহায্যও করে, বা সুইমিং পুল সাফ করতে আমাকেও সাহায্য করে। সেই বা কম কী? মেয়েটা ভালোই, লালী।
আলোকে পৌঁছে দিয়ে আজ যখন আমরা ফিরছি, লালীকে বললাম—”দাদু—দিদার বিয়ের পঞ্চাশ বছর হবে তুমি কী দেবে?” লালী বলল—”ভাবিনি এখনও। গোল্ডের তৈরি কিছু দিতে হবে তো? কোথায় পাব অত টাকা। দেখি, হয়তো জয়—পিউদের সঙ্গে একসঙ্গে কিছু দেব। ওদের সঙ্গে ফোনে পরামর্শ করতে হবে।”
এই ব্যাপারটা খুব ভালো লাগে আমার। এই মউ—পিউদের সঙ্গে লালীর বন্ধুত্বটা। কাজিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার ছোটবেলায় আমি বড় একটা দেখিনি। আপনভাই স্টিভের সঙ্গেই আমার তেমন ভাব ছিল না! জয়—পিউ—মউরা কিন্তু তিনজনে খুবই ঘনিষ্ঠ, লালীকেও ওরা ওদেরই একজন মনে করে। আলো আর কালোতে এখনও যে অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, এটাও তো হিংসে করবার মতোই। প্রত্যেকদিন রাত্রে ভাইবোনে ফোনে গল্প হয়। টোরোন্টো থেকে নিউইয়র্ক। মায়াও বেশ সেনসিবল স্বভাবের মেয়ে। উষ্ণতা আছে কিন্তু বাড়াবাড়ি নেই। আলো একদম মায়ার মতো নয়। সে বড্ড একরোখা। লালীকে নিয়ে আলোর যেমন সর্বক্ষণ বাধছে, মউ—পিউকে নিয়ে মায়ার তো তেমন বেধে যায় না? মউ—পিউও টিন এজ গার্লস; তাদের নিয়ে তো ডবল ঝামেলা হওয়া উচিত, তারা সংখ্যায় দু’জন। আলোর যে ভীষণ বাঁধাধরা সব প্রিন্সিপলস আছে। সেই প্রিন্সিপলে সে সন্তানকেও চালাতে চায়। আমরা কি আমাদের মা—বাবার আদর্শে চলেছি। আলো বলে, হ্যাঁ সে নাকি তার মা বাবার জীবনের মূল আদর্শগুলো মেনে চলে, আর যা সময়ের অনুপযোগী, সেগুলো মানে না। যেসব আদর্শ দেশকালের বাইরে, চিরকালের মানুষকে নিয়ে, সেগুলো নাকি ওর বাবার কাছেই শিক্ষা পেয়েছে। ভালো! ভাগ্যিস আমি সেগুলো আমার বাবার কাছে শিখিনি! কিংবা মায়ের কাছেও! অসীম ধৈর্য, অসীম সহ্য, অসীম প্রশয়, অসীম পরিশ্রম, অসীম দুর্বলতা, অসীম দৈব, অসীম দুঃখ। এই হল মায়ের আদর্শ। প্রায় জোব—এর মতো, আদর্শ কষ্টসহিষ্ণু ক্রিশ্চান তিনি। আর অসীম অত্যাচার, অসীম স্বার্থপরতা, অসীম নিষ্ঠুরতা, অসীম নির্বুদ্ধিতা এই হচ্ছে বাবার আদর্শ। আলোর বাবা—মা অবশ্য একেবারেই অন্য প্রকৃতির। আলোর বাবা খুব আদর্শবাদী লোক, সত্যিই। আলো সেইরকম হয়েছে। কিন্তু আলোর আদর্শ নিয়ে পাগলামি, আর ওর আন্তরিক ভালবাসার জুলুমে ক্ষমতা মিলিয়ে ও যা কাণ্ডকারখানা করে বসে মাঝেমধ্যে। মাত্র চারদিনের ছুটিতে জয় ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এল, নিজের বাবা—মায়ের কাছে না গিয়ে পিসির কাছে এল। বেচারা এই প্রথম একটা বিরাট মুক্তির মুখ দেখেছে। কলেজে গিয়ে রাজনীতি বিষয়ে সচেতন হয়েছে। থার্ড ওয়ার্ল্ড বিষয়ে সচেতন হয়েছে। নিজে আমেরিকান সিটিজেন হলেও সে তার থার্ড ওয়ার্ল্ড রুটস বিষয়ে অচেতন নয়। তার খুব শখ হয়েছে পাশ করে সে ব্রাজিলে যাবে, চাকরি করতে। ওদের অনেক এঞ্জিনিয়র দরকার হয়। জয় ব্রাজিলে গিয়ে থার্ড ওয়ার্ল্ডকে সার্ভ করবে শুনে আলো খেপে লাল। কী? তুমি ভারতীয় মা—বাবার সন্তান, তোমার ব্রাজিলে শ্রমদান করবার কী দরকার? তোমার নো—হাউ, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি, তোমার সহানুভূতি সবই পেলে বর্তে যাবে ভারতবর্ষ। সেও তো দরিদ্র! ব্রাজিল তো হোয়াইট, আফটার অল ব্রাজিল তো ইউরোপীয় কালচার, আফটার অল ব্রাজিলের জ্ঞাতিভাই নর্থ আমেরিকা, এবং তার কাছে গোটা লাতিন বিশ্ব। তুমি বরং গরিব ভারতবর্ষকে শ্রম দান করো, তোমার নো—হাউ তুমি পিতৃভূমিকে করো। তুমি ব্রাজিলে কেন যাবে? মার্কিন ছাত্ররা বামপন্থী বিপ্লবী হলে কিউবায় যেতে চায়—ব্রাজিলে, কলম্বিয়ায়, আর্জেনটিনায় যেতে চায়—তুমি নিজে বাঙালি হয়েও তাই চাইবে কেন? তোমার অরিজিন্যালিটি নেই? ইম্যাজিনেশন নেই? কমনসেন্স নেই? গো হোয়্যার ইউ আর নিডেড মোর, ওয়ান্টেড মোর। সেখানেই যাও। ব্রাজিল তোমাকে বলতেই পারে—”তুমি কে বট হে? তোমার রুটকান্ট্রির তো ওই অবস্থা। নিজের চরকায় তেল দাও গে?” জয় বেচারা সত্যি সত্যি খুব একটা রাজনীতি বোঝে না, সদ্য বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে জানতে—বুঝতে শুরু করেছে, মার্কিন ছাত্রদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে আইডেনটিফাই করে, তার জন্মই এ দেশে। মার্কিন নাগরিক সে। এই নিয়ে বাড়িতে কম অশান্তি করছে আলো? বাবা—মা’র বিয়ের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে সবাই দেশে যাচ্ছে, শুধু জয় যাচ্ছে না। জয় তার বন্ধুদের সঙ্গে ব্রাজিলে যাচ্ছে। সব ঠিকঠাক। ফ্লোরিডা থেকে জাহাজ ধরবে। এইজন্যে এই সামারে কোনও সামার—জবও করছে না। আলোর কাছে এটা মহাপাপ। আলোর মতো তাকেও দেশে যেতেই হবে। জয় মাত্র ক’টা দিনের জন্যে এল, আলো তাকে সর্বক্ষণ জ্ঞান দিয়ে, বকে, ধমকে বললে—যতই এ দেশে থাকো তোমার বাবা—মা ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়াতেই তোমার রুটস—এতদিন এদেশে থাকার পরেও দেখছ না, মার্কিন কালোরা তাদের শেকড় খুঁজছে আফ্রিকায়? আর নির্বোধ তোমরা ইচ্ছে করে তোমাদের চমৎকার শেকড় উপড়ে ফেলবে? আমি ফ্রেডকে ভালবাসি বলেই এদেশে থাকি, এদেশে সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যকে ভালবেসে থেকে যাইনি। আমার পক্ষে এখানে মানিয়ে নেওয়া ঢের সহজ ফ্রেডের পক্ষে ওখানে চাকরি পাবার চেয়ে। তা ছাড়া ওর বদলে একজন ভারতীয় ছেলে ভারতে চাকরি পাক এটাও কাম্য। তুমি যদি থার্ড ওয়ার্ল্ডের সেবা করতে চাও তা হলে গো টু দ্য কান্ট্রি দ্যাট ক্লোজ ইন ইয়োর ভেইন্স—যার জ্বালা—যন্ত্রণা তোমার ঠাকুরদা—ঠাকুমা জেনেছে, তোমার মা—বাবা জেনেছ, দাদামশাই—দিদিমা জেনেছে। তোমার মামাবাড়ি খুবই দীনদরিদ্র এবং গ্রাম্য। সেখানে একবার যাও। আসল ইন্ডিয়াকে চিনবে। যাও, দেখে এসো কীভাবে জীবনের উন্নতির পথে এখনও ভারতবর্ষ কতটা বাধা দেয়। শুধু নিচু জাতে জন্মানো…তোমার মাকেও চিনবে। সে কেমন একক বিদ্রোহী, কত দুঃসাহসী যোদ্ধা। কাস্ট সিস্টেমের জ্বালা—যন্ত্রণা চোখে দেখতে পাবে নিজের ফ্যামিলির মধ্যে। অশিক্ষা, দৈন্য—দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং তার ফলে কালচারাল ডিফারেন্স সব বুঝবে। ব্রাজিলে তুমি কতটুকু বা বুঝবে। ওদের ভাষাও তোমাকে নতুন করে শিখতে হচ্ছে। পর্তুগিজ কেন শিখছ, কেন বাংলা শিখছ না? পাগলি পিসিকে খুব ভালবাসলেও এত সব জ্ঞানের কথায় জয় খুবই বিরক্ত হচ্ছিল। সে ব্রাজিলে যাওয়া বন্ধ মোটেই করেনি, কলকাতাতে সে ফ্যামিলি রিউনিয়নে যোগও দিচ্ছে না। মায়ের নিম্ন জাতির পরিবারের দৈন্য, অশিক্ষা, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎমুখীনতা, এসব বিষয়ে সে মোটেই উৎসাহী নয়। আলোর এসব কথাবার্তা জয় পছন্দও করেনি। ওই ব্যাপারটা ওদের স্কেলিটন ইন দ্য কাবার্ড। মায়া তো কক্ষনও ভুলেও এ বিষয়ে একটা কথাও বলে না। বাপেরবাড়ির সঙ্গে কোনও যোগই রাখে না সে। বাপেরবাড়িটাকে স্মৃতি থেকে মুছেই ফেলেছে মায়া। আলো চেষ্টা করছে সেই ক্ষতস্থানকেই খুঁচিয়ে ফের পুনর্জীবিত করতে, তারই যুবক ছেলের মধ্যে। কী ভীষণ নির্বুদ্ধিতার কাজ। সেটাও বোঝে না। মায়াও চটে যাবে এ জন্য ওর ওপরে। মায়া কত ভাল সেটা বোঝানোই যদিও আলোর উদ্দেশ্য; কোথা থেকে কোথায় উঠে এসেছে, কত গভীর অন্ধকার পার হয়ে এসেছে, কত যুগের বঞ্চনা অতিক্রান্ত হয়ে এই একক উত্তরণ মায়ার—এসব নিয়ে আলো মায়ার জন্য খুব গর্বিত—কিন্তু মায়া একদম এ নিয়ে কথা বলে না। ও একেবারেই আলোদের পরিবারে মিশে তাদেরই একজন হয়ে থাকতে চায়। নিজের নিম্ন জাতের শেকড়টা মনে রাখতে চায় না। আমি মায়াকে বুঝি, কেন না আমিও আমার মাতাল অত্যাচারী অলস সাদার্ন হোয়াইট বাবার উত্তরাধিকার নিয়ে লজ্জিত, সে কথা মনে রাখতে চাই না।
হয়তো আমার কালো ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করার মধ্যে বাবার বিরোধিতা করারও একটা ব্যাপার ছিল। বাবা ছিল ভয়ানক রেসিস্ট, বর্ণবিদ্বেষী সাদার্নার। একদিনও আলোর মুখদর্শন করেনি। লালীকেও দেখেনি। বাবা মরে যাওয়ার পরেই মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমার। মা মোটামুটি দুর্বল মানুষ—নিজের কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। বাবার মতে চলত। এখন আমার মতটা মেনে নিয়েছে। যেহেতু স্টিভ তাকে একেবারেই দেখে না। নতুবা মা’র স্টিভের মতেই চলাটা স্বাভাবিক হত।
আমাদের রেসিজমের সঙ্গে ওদের কাস্টইজমের বেশ মিল আছে। আমাদের চেয়ে হয়তো ওদেরটা আরও বিশ্রী কেন না একই দেশের মানুষ। শুনি তো কাস্টের মূলত উৎপত্তি কাজের শ্রেণিবিভাগ থেকে। তা হলে এও কি ক্লাস—এক্সপ্লয়টেশনেরই অন্য একটা চেহারা নয়? আপার কাস্টরা সবাই আপার ক্লাসও হয়। মোটামুটি। আর লোয়ার কাস্টরা লোয়ার ক্লাস। আলো অবশ্য বলে কিছু কিছু লো কাস্টেও ধনী আছে—তাদের ব্যবসায় টাকা হয়েছে। কিন্তু যা বুঝি ভারতবর্ষের গ্রামে নিম্নজাতিরা খুব গরিবও। এখানে যেমন কালোরা গরিব। শ্রেণি সংগ্রাম এর সঙ্গে এই সংগ্রামগুলি ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত। আমাদের সময়কার রাজনৈতিক চেতনা আজকালকার ছেলেদের মধ্যে নেই—কিছু কিছু যেসব ছেলেমেয়ে শখের বিপ্লবী হতে চায় তারা মার্কিন দেশে কিছু না করে লাতিন আমেরিকায় কিছু করতে চায়। এও একরকমের এস্কেপিজম। আমেরিকাতেও কি গরিব নেই? পভার্টি লাইনের নীচে কম মানুষ? ক্যানাডার ছাত্রদের মধ্যেও দেখি লাতিন আমেরিকা আর আফ্রিকা নিয়ে প্রবল মাতামাতি। আলো বলে, ছাত্ররা সাহিত্য বলতে এখন পড়ছে নাকি কেবল লাতিন আমেরিকা আর আফ্রিকার সাহিত্য! লালীর ঘরেও দেখতে পাই আফ্রিকান, লাতিন আমেরিকান বইপত্তর। লালীর আগের বয়ফ্রেন্ড বিল ছিল প্রচণ্ড সাহিত্য—ভক্ত ছেলে—বিলই লালীকে এইসব সাহিত্য পড়তে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু লালীর ভেতরে সাহিত্য নেই। হয়তো বিলকে খুশি করতে তখন দু’চারটে বই পড়ত। লালীকে বিল প্রচুর বইপত্তর উপহার দিত—লালীকে থাড ওয়ার্ল্ডে উৎসাহিত করতে কম চেষ্টা করেনি বিল। কিন্তু ওর গাঁজা খাওয়াটাওয়া লালী সহ্য করতে পারেনি, ওরকম দাড়ি—রাখা গাঁজা—খাওয়া ছেলে ওর পছন্দ নয়। ভাগ্যিস! লালীর পড়াশুনোয় উৎসাহ আছে, সায়েন্সের জার্নাল টার্নাল পড়ে, কিন্তু সাহিত্যে ততটা রস পায় না। আমিও যেমন। গল্পের বই পড়বার ধৈর্য থাকে না। টিভি দেখা তার চেয়ে ভালো। আলো টি.ভি—র পোকা, কিন্তু বইও পড়ে। এখন রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত বলে ইদানীং ততটা টিভিও দেখতে সময় পায় না, গল্পের বইও পড়তে সময় পায় না কিন্তু ওর রিল্যাক্স করার আইডিয়া হল বই নিয়ে, এক গ্লাস বিয়র নিয়ে ওই কৌচটাতে শুয়ে পড়া। নইলে একটা হিন্দি ছবি! ভিডিওতে!
কালো—মায়াদের একটা ফোন করতে হবে এবার। বাসনগুলো মুছে তুলে রেখেই। এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিল আলো দেরি হচ্ছে বলে। ভালভাবে রওনা হয়ে গেছে যে, সেটা আর জানানো হয়নি ওদের।
আমাদের বিয়ে যেহেতু এদেশে হয়েছে, বিয়েতে নেমন্তন্ন খাওয়ানো হয়নি কাউকে, তাই বাবা—মায়ের বিয়ের পঞ্চাশ বছর নিয়ে আলো ওদেরও মাতিয়ে তুলেছে। মউ—পিউও কলকাতায় যাচ্ছে, মায়া—কালো তো যাচ্ছেই। কেবল জয়ই যেতে পারছে না। ও তখন ব্রাজিলে থাকবে। আমরা ভেবেছি এ বছরে সবাই মিলে কাশ্মীর বেড়াতে যাব। যদিও আগস্ট নাকি খুব একটা ভালো সময় নয়। কিন্তু এমন সুযোগ তো হয় না, যখন প্রত্যেকেই একসঙ্গে ভারতবর্ষে আছি—কখনওই হয়নি এর আগে। আলোর বাবা—মা’র নাকি স্বপ্ন ছিল একবার কাশ্মীর দেখা। ভারতবর্ষে সবাই কাশ্মীরে হনিমুন করার স্বপ্ন দেখে। পঞ্চাশ বছরের বিবাহ—জয়ন্তীতে সেটাই ওঁদের উপহার দেওয়া হচ্ছে। তবে দু’জনে নয়—সদলবলে—যেটা ওঁদের পক্ষে সবচেয়ে আনন্দের। পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন—যতবার ভাবছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। কপালে থাকলে আমাদেরও হবে। তেইশ তো হল, আর সাতাশ। সাতাশ বছর নিশ্চয়ই বাঁচব আমরা—আলোর এখন চুয়াল্লিশ, আমার তেতাল্লিশ। সত্তর—একাত্তর বছরে এখন আর কেউই মরে না এদেশে, ক্যানসার কিংবা মোটর দুর্ঘটনা না হলে আশি—নব্বই সবাই বাঁচে। আলো তো এখন অ্যাটলান্টিকের ওপরে উড়ে যাচ্ছে—ভাল ভাল ড্রিংক্স ওকে এয়ারলাইনসই খাওয়াচ্ছে—আমি বরং বাসনগুলো ধুতে ধুতে কফিটা বানিয়ে নিই। কফি আর ক্রুয়াসঁ ব্রেকফাস্ট হবে। কাল ভাল ক্রুয়াসঁ কিনেছে লালী টোরোন্টোয়। টি.ভিটা খুলে দিলে হয়। মর্নিং নিউজটা শুনি। নিজের জন্য বড় ব্রেকফাস্ট করবার ধৈর্য আমার নেই। মর্নিং টি.ভি—নিউজের সময় হয়ে এসেছে। ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিসের খেলাটাও আজ দেখার ইচ্ছে আছে টি.ভিতে। কাল অত রাত্রে ফিরেছি বলে সকালে এতক্ষণ ধরে এই যে বাসন ধুলাম, রান্নাঘর পরিষ্কার করলাম, ময়লা ফেললাম—এই হল আলোর ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার অসুবিধাগুলোর শুরু। কাজকর্ম সব করে দিয়ে দিয়ে আমাকে বিশ্রীরকম অলস বানিয়ে দিয়েছে আলো। আজকাল রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলেই তবু কিছু কিছু কাজ করা আবার নতুন করে অভ্যেস হচ্ছে আমার। লালীটার নিউজে ইন্টারেস্ট নেই। আশ্চর্য এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। আমরা তো এই বয়সেই পলিটিক্যাল প্রাণী হয়েছি। ওরা নিরপেক্ষ দর্শক। ইতিহাস—চেতনা বলতে ওরা হঠাৎ হঠাৎ কৃত্রিমভাবে কখনও ব্ল্যাক পাওয়ার কখনও উইমেন্স লিব কখনও থার্ড ওয়ার্ল্ড নিয়ে শৌখিন মাতামাতি করতে থাকে, নিজের সরকারের কোনও প্রকৃত মন্দ পলিসির কঠোর সমালোচনা করে না। কোনও ব্যক্তিগত রিস্ক নেয় না। জগতে কোথায় কী ঘটছে রোজ, তারই কোনও খোঁজখবর রাখে না। অথচ এই টি.ভিতে নিউজটা ওয়াচ করা আলোর নেশা। সি বি এস, এন বি সি তো বটেই। কোনওটা বাদ দেবে না। বি বি সি—ও ধরে। দেশে গেলে, আলো বলে, এটাই ও খুব মিস করে, এই টি.ভি নিউজ। সেই আলোর মেয়ে যে কী করে একরকম নির্লিপ্ত হল? জীবনেও লালীকে নিউজ দেখতে আসতে দেখলাম না, অ্যাকসিডেন্টালি ছাড়া। ওই ফকল্যন্ডের সময়ে, দেশটা নেহাত আর্জেন্টিনা বলে, বিল খুব মেতেছিল। আর বিলের সঙ্গে সঙ্গে লালীও কিছুটা নিউজে উৎসাহ দেখিয়েছিল। এখন বিল ছুটে গেছে, লালীর নিউজ দেখাও ছুটে গেছে। খেলার খবরেও মেয়েটার উৎসাহ নেই। দেখি—ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিসের কী হয় আজ।