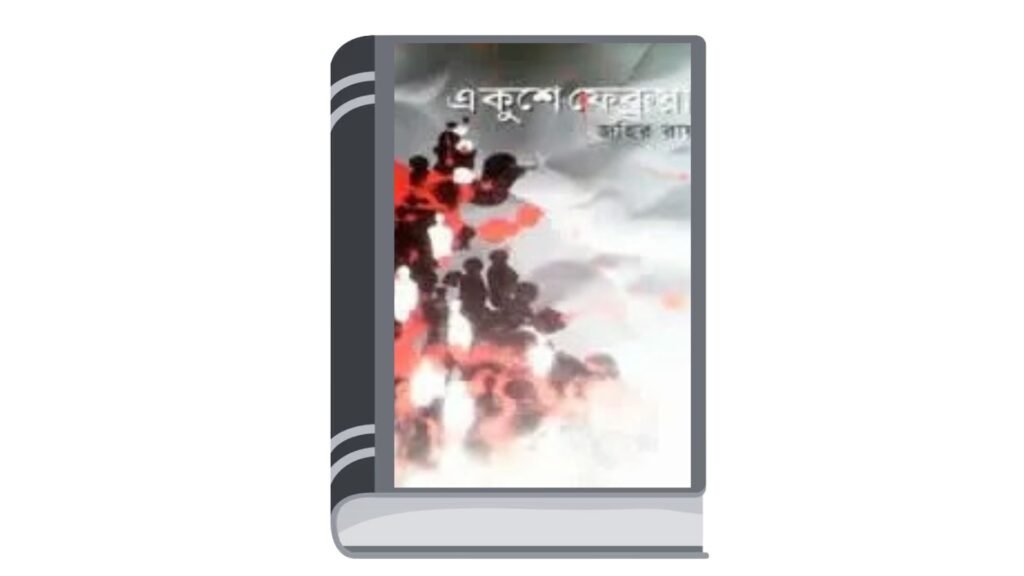০. একুশে ফেব্রুয়ারির ভূমিকা
বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন শুধু এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নতুন চেতনাপ্রবাহ সৃষ্টি করেছিলো। এই চেতনা ছিলো অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধসঞ্জাত। আমাদের শিল্প সাহিত্যে যাঁরা এই চেতনার ফসল, তাঁদের ভেতর জহির রায়হানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ভাষা আন্দোলনে তিনি শুধু যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তা নয়, তাঁর সাহিত্য প্রেরণার মূল উৎস ছিলো এই আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম সার্থক উপন্যাস–আরেক ফাল্গুন-সহ অজস্র ছোটগল্প ও নিবন্ধ লিখেছেন তিনি। এইসব লেখা এবং তাঁর রাজনৈতিক অঙ্গীকার থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনের আবেগ, অনুভূতি তাকে প্রচণ্ডভাবে আপ্লুত করে রেখেছিলো।
লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর জহির রায়হান চলচ্চিত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন পঞ্চাশ দশকের শেষে। এই শিল্প মাধ্যমটির প্রতি তার যোগাযোগ অবশ্য আরো আগের।
ষাট দশকের শুরুতে জহির রায়হান একজন পরিপূর্ণ চলচ্চিত্রকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন কখনো আসেনি, কাঁচের দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে। এরপর অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে কয়েকটি বাণিজ্যিক ছবি বানালেও তিনি তার লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। বাণিজ্যিক ছবি বানাবার সময় তার শিল্পসত্তা যতটুকু বিপর্যস্ত হয়েছিলো, যে তীব্র মানসিক যাতনার শিকার হয়েছিলেন তিনি কিছুটা লাঘবের জন্য আবার সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন, উপন্যাস লিখেছেন হাজার বছর ধরে। ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি আর কতগুলো কুকুরের আর্তনাদ-এর মতো গল্প লিখে জ্বালা মেটাতে চেয়েছেন।
কাঁচের দেয়াল বানাবার পর তিনি একুশে ফেব্রুয়ারী নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবে শিল্পোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়িক দিক থেকে তিনটি অসফল ছবি (কখনো আসেনি, সোনার কাজল ও কাঁচের দেয়াল) বানাবার ফলে একুশে ফেব্রুয়ারী প্রযোজনা করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। বাধ্য হয়ে তাঁকে বাজারচলতি ছবি বানাতে হয়েছে। তাবে ভবিষ্যতে একুশে ফেব্রুয়ারী বানাবেন এই ইচ্ছা সব সময় সযত্নে লালন করেছেন। তিনি। যখন নিজে চলচ্চিত্র প্রযোজনা করার পর্যায়ে এলেন, তখন বাধা হয়ে দাঁড়ালো দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তাঁর পরিকল্পিত একুশে ফেব্রুয়ারী ছিলো একটি রাজনৈতিক ছবি, আইয়ুবের স্বৈরাচার আমলে সে ধরনের ছবি বানানো ছিলো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই তিনি প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের ঊর্মিমুখর দিনগুলোতে বানিয়েছিলেন জীবন থেকে নেয়া। এ ছবিতে একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরী এবং আন্দোলনের দৃশ্যে জহির রায়হানের রাজনৈতিক আবেগের যে তীব্র প্রকাশ ঘটেছে, বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না ভাষা আন্দোলনের শেকড় তার চেতনার কত গভীরে প্রােথিত। এরপর আরো বড় ক্যানভাসে সর্বজাতির সর্বকালের আবেদন তুলে ধরতে চেয়েছিলেন লেট দেয়ার বি লাইট-এ, যে ছবি তিনি শেষ করতে পারেননি। এর কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি স্টপ জেনোসাইড-এ। তবু একুশে ফেব্রুয়ারী নির্মাণের পরিকল্পনা তিনি বাতিল করেননি। ৭২-এর দুর্ঘটনায় এভাবে হারিয়ে না গেলে হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি বানাতেন তার সেই স্বপ্ন আর আবেগের ছবি।
২.
বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হানের অংশগ্রহণ কোন আকস্মিক বা নিছক আবেগতাড়িত ঘটনা ছিলো না। তার রাজনৈতিক জীবন-প্রবাহের স্বাভাবিক গতি তাঁকে যুক্ত করেছিলো এই আন্দোলনের সঙ্গে। যে কারণে শুধু বায়ান্নতে নয়, ঊনসত্তর বা একাত্তরেও তাকে খোলাখুলি আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক লেখক শিল্পীদের ভেতর তিনি ছিলেন রাজনীতির প্রতি সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাকে যারা জানেন তারা সবাই স্বীকার করবেন, তিনি সব সময় খোলাখুলি তাঁর রাজনৈতিক মত ব্যক্ত করতেন। এর জন্য তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই রাজনীতির জন্যই তাঁকে অকালে হারিয়ে যেতে হয়েছে।
চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি জহির রায়হান যখন স্কুলের নীচের ক্লাশের ছাত্র, তখন অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। শহীদুল্লাহ কায়সার তখন কোলকাতার একজন ছাত্রনেতা। প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে এবং গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। জহির রায়হান তখন পার্টি-কুরিয়ার ছিলেন। পার্টির আত্মগোপনকারী সদস্যদের মধ্যে চিঠিপত্র ও খবর আদান প্রদানের কাজ করতেন। প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র স্বাধীনতা বিক্রি করতেন। তখনকার দিনে পার্টি কর্মীরাই পার্টির কাগজ বিক্রি করতেন। সেই আমলের একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জহির রায়হান সম্পর্কে বলেছেন, তখন ও ভালোভাবে হাফপ্যান্টও পরতে জানতো না। প্রায় বোতাম থাকতো না বলে একহাতে ঢোলা হাফপ্যান্ট কোমরের সাথে ধরে রাখতো। রায়হান ছিল ওর টেকনেম–পার্টি পরিচয়ের ছদ্মনাম (তার পিতৃদত্ত নাম জহিরউল্লাহ)। বড়ভাইর প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলো। জহির রায়হানের পার্টি জীবনের সূচনা সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতে পারিনি।
বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের সময় শহীদুল্লাহ কায়সার আত্মগোপন অবস্থায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছিলেন। জহির রায়হান জানতেন পার্টির নির্দেশ হচ্ছে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার। তিনি পরে বলেছেন, ছাত্রদের মিটিঙেও সিদ্ধান্ত হলো ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। ছাত্রদের গ্রুপে ভাগ করা হলো। আমি ছিলাম প্রথম দশজনের ভেতর। প্রথম দিকে যারা ১৪৪ ধারা ভেঙেছে পুলিশ ভঁদের গ্রেফতার করে ট্রাকে চাপিয়ে সোজা লালবাগে নিয়ে গেছে। পরে ছাত্রদের মনোভাব দেখে পুলিশ গুলি চালিয়েছিলো। জহির রায়হান কেন প্রথম দশজনের ভেতর ছিলেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি স্বভাবসুলভ স্মিত হেসে বহুবার পরিবারের সদস্যদের কাছে গল্প করেছেন, সিদ্ধান্ত তো নেয়া হলো ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। কিন্তু প্রথম ব্যাচে কারা যাবে? হাত তুলতে বলা হলো। অনেক ছাত্র থাকা সত্ত্বেও হাত আর ওঠে না। কারণ স্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে পজিশন নিয়ে বসে আছে। ভাবখানা এই যে, বেরুলেই গুলি করবে। ধীরে ধীরে একটা দুটো করে হাত উঠাতে লাগলো। গুনে দেখা গেলো আটখানা। আমার পাশে ছিলো ঢাকা কলেজের একটি ছেলে। আমার খুব বাধ্য ছিলো। যা বলতাম, তাই করতো। আমি হাত তুলে ওকে বললাম হাত তোল। আমি নিজেই ওর হাত তুলে দিলাম। এইভাবে দশজন হলো।
জহির রায়হান পরবর্তী সময়ে সরাসরি পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। শহীদুল্লাহ কায়সার যদিও তখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। জহির রায়হানের সেই সময়ের লেখা কিছুটা রোমন্টিক ও আবেগ বহুল হলেও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম তিনি তখনকার গল্প ও উপন্যাসে যথেষ্ট দক্ষতা ও দরদের সঙ্গে এঁকেছেন। প্রথম ছবি কখনো আসেনি এবং দ্বিতীয় ছবি কাঁচের দেয়াল-এর শহরের নিম্নবিত্ত জীবনের দারিদ্র, বেকারত্ব, ব্যবসায়ীদের ধূর্ততা, দুর্নীতি ও বৈষম্যের চিত্র রয়েছে।
১৯৬৬ সালে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির মতাদর্শগত বিরোধের ফলে অপরাপর দেশের মতো এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত হয়। শহীদুল্লাহ কায়সারের অবস্থান ছিলো মস্কোপন্থী শিবিরে। জহির রায়হান ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। পার্টি ভাঙার জন্য সরাসরি পার্টির নেতৃস্থানীয় লোকজনদের সমালোচনা করতেন। তাঁর বড় বোন নাফিসা কবির পার্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না থাকলেও চীনের লাইন সমর্থন করতেন এবং বড়দা শহীদুল্লাহ কায়সারের সঙ্গে কখনো তর্কও করতেন। নাফিসা কবির অবশ্য এই সময়ে বিদেশে থাকতেন, কখনো দেশে এলে পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা করতেন। এই সময় নাফিসা কবির জহির রায়হানকে রাজনৈতিকভাবে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন।
৬৯ এর অভ্যুত্থানের সময় জহির রায়হান রাজনীতির প্রতি অধিকতর আগ্রহী হলেন এবং এই সময় তিনি পিকিংপন্থী রাজনীতির প্রতি বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েন। লৌহমানব হিসেবে কথিত আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরাচারের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি রূপকের আশ্রয় নিয়ে জীবন থেকে নেয়া নির্মাণ করেন। জীবন থেকে নেয়ায় যথেষ্ট ভাবাবেগ ও মেলোড্রামা থাকলেও জহির রায়হানের ছবিতে এই প্রথমবার রাজনৈতিক বক্তব্য জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়। ৬৯ এর গণ-আন্দোলনের কিছু প্রামাণ্য দৃশ্য তিনি এই ছবিতে সংযোজন করেছেন। এই দৃশ্যগুলি তোলার জন্য দিনের পর দিন তিনি ক্যামেরা এবং দু-তিন জন সহকারী নিয়ে মিছিলে মিছিলে ঘুরেছেন। এই ছবিতে সংযোজন ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরীর প্রামাণ্য দৃশ্যটি তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট দুঃসাহসিকতা পূর্ণ কাজ ছিলো। ছাড়পত্র পেতে এই ছবিকে কি রকম ঝুঁকি পোহাতে হয়েছিলো এ কথা সবার জানা আছে। সেন্সরবোর্ডের বাধা পেয়ে জহির রায়হান এই ছবি নিয়ে হৈ চৈ করতে চেয়েছিলেন। যে জন্যে তিনি তখনকার বামপন্থী ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও কয়েকজন প্রতিবাদী সাংবাদিককে এ ছবি দেখিয়েছিলেন সেন্সরের ছড়িপত্র পাওয়ার আগে, যাতে তারা এ নিয়ে আন্দোলন বা লেখালেখি করতে পারেন। দেশের তৎকালীন বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সরকারী কর্তৃপক্ষ কিছু দৃশ্য কেটে রেখে ছবিটি মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলো।
৭০ সালে জহির রায়হান এক্সপ্রেস পত্রিকা বের করেন এবং এর যাবতীয় খরচ তিনি একাই বহন করতেন। পত্রিকা অবশ্য আগেও অনেক বের করেছেন তিনি। পঞ্চাশ দশকে প্রবাহ, অনন্যা প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। ভাবে এক্সপ্রেস ছিলো রাজনীতি সচেতন পত্রিকা। প্রথম দিকে কিছুটা কম। চরিত্র থাকলেও কয়েক সংখ্যা পরই রাজনৈতিক বক্তব্য জোরালোভাবে উপস্থিত হয়। এই সময় তিনি প্রথমবারের মতো মাও সেতুঙের স্বচনা পাঠ করেন এবং এর দ্বারা দারুণ রকম প্রভাবিত হন। তখন এখানে মাও সেতুঙের চিন্তাধারার অনুসারী কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি একাধিক দল উপদলে বিভক্ত ছিলো। এদের প্রায় সবার সঙ্গে জহির রায়হান যোগাযোগ রাখতেন, পার্টি ফাণ্ডে মোটা অংকের চাঁদাও দিতেন। ৭১ এর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তাঁর মরিস অক্সফোর্ড গাড়িটিও একটি সংগঠনকে সর্বক্ষণ ব্যবহারের জন্যে দিয়েছিলেন। পিকিংপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও জহির রায়হান মস্কোপন্থীদের অনুষ্ঠানাদিতে সময় পেলে যোগ দিতেন। তিনি তাঁর নির্মীয়মান ছবি লেট দেয়ার বি লাইট মস্কো প্রেরণ করার কথাও বলতেন। শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাব তার উপর এত বেশি ছিলো যে, তার সামনে তিনি সবসময় মস্কোপন্থীদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতেন। তাছাড়া মস্কোপন্থী অনেক লেখক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমন পর্যায়ে ছিলো যে, নিজে মাও সেতুঙের চিন্তাধারার অনুসারী হয়েও তিনি এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তিনি পিকিংপন্থীদের ঐক্য মনে প্রাণে কামনা করতেন।
৭১ এর ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা এদেশে যে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করে জহির রায়হান এতে এত বেশি বিচলিত বোধ করেন যে, রাতের পর রাত তিনি অস্থির ও নির্মম অবস্থায় কাটিয়েছেন। মাও সেতুঙেৱ সামরিক প্রবন্ধাবলীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তখন দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের কথা ভাবতেন। পার্টির কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তিনি যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যই ঢাকা ছেড়ে আগরতলা এবং পরে কোলকাতা চলে যান। কোলকাতায় তিনি প্রচার কাজ সংগঠিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পতিত হন এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতে হয়। কোলকাতায়
নয় মাস তাকে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়েছে। স্টপ জেনোসাইড ছবিটি নির্মাণের সময় আওয়ামী লীগের নেতারা তাকে নানাভাবে বাধা দিয়েছে। বিভিন্ন সেকটরে সুটিং করতে দেয়নি, এমন কি কোন কোন সেকটর তাঁর গমন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিলো। অবশেষে সাত নম্বর সেকটরে তিনি সুটিং এর সুযোগ পেলেন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাজেট ও সময়ে এই অপূর্ব ছবিটির নির্মাণ কাজ শেষ করলেন। আওয়ামী লীগ নেতারা ছবি দেখে ছাড়পত্র না দেয়ার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের সেন্সর বোর্ডকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। একজন উঁদরেল আওয়ামী লীগ নেতা এই বলে হুমকিও দিয়েছিলেন যে, এই ছবিকে ছাড়পত্র দেয়া হলে তিনি বাংলাদেশ মিশনের সামনে অনশন করবেন।
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সর কর্তৃপক্ষ এ ছবিকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করায় জহির রায়হানকে দিল্লী পর্যন্ত দৌড়াতে হয়। শহীদুল্লাহ কায়সারের কয়েকজন পুরোনো সহকর্মী ও বন্ধু যারা ভারতীয় সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন তাঁদের তদবিরে বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর এ ছবিকে ছাড়পত্র দেয়া হলেও জনসমক্ষে এ ছবি প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা জহির রায়হান করতে পারেননি।
স্টপ জেনোসাইড-এর প্রতি মুজিব নগর সরকারের কিছু নেতা এই কারণেই কুপিত ছিলো যে, এ ছবি শুরু হয়েছে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, আর শেষ হয়েছে আন্তর্জাতিক (জাগো জাগো সর্বহারা) এর সুর বাজিয়ে। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ তখনও আমেরিকার সাহায্য ও সমর্থন পেতে উন্মুখ ছিলো অথচ এ ছবিতে সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য উত্থাপন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতারা বাধা দিলেও জহির রায়হানের মস্কোপন্থী ভারতীয় বন্ধুরা এ ছবি মুক্তির ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করায়, তিনি সেই সময় মস্কোপন্থী ভারতীয় বন্ধুদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। সেই সময়টা ছিলো জহির রায়হানের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কাল। কারণ তিনি চীনের তখনকার ভূমিকাকে সমর্থন করেননি এবং প্রায় সর্বদাই মস্কোপন্থীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। তবু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও জহির রায়হান কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নকশাল নেতার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন এবং অসীম চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলোচনাকালে চারু মজুমদারের বিরুদ্ধে বিরূপ ও অশোভন মন্তব্য করার জন্যে তিনি অসীম বাবুর উপর বিরক্তও হয়েছিলেন।
৭১ সালের শেষের দিকে জহির রায়হানের কার্যকলাপকে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলো। কোলকাতার মস্কোপন্থী বুদ্ধিজীবীরা জহির রায়হানের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও মস্কোপন্থী পার্টির সঙ্গে জহির রায়হানের কোন যোগাযোগ ছিল না। অক্টোবর মাসে লণ্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জহির রায়হানকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং রিটার্ণ টিকিটও পাঠানো হয়। জহির রায়হানের প্রথমেই বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহ করতে গিয়ে। এরপর সমস্যা দেখা দেয় মস্কোর ভিসা পেতে। জহির রায়হানের অনুরোধে লণ্ডনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা (ঢাকা যাদুঘরের অধ্যক্ষ এনামুল হক ছিলেন আমন্ত্রণকারী) তাকে লণ্ডন যাওয়ার পথে মস্কো হয়ে যাবার টিকিট পাঠিয়েছিলেন। মস্কো দেখার সখ ছিলো জহির রায়হানের অনেক দিনের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিল্লী গিয়েও তিনি মস্কোর ভিসা সংগ্রহ করতে পারেননি এবং এই জন্য তখন ভর লণ্ডন যাওয়া হয়নি। জহির রায়হানের প্রতি সোভিয়েত দূতাবাসের এহেন আচরণে তার মস্কোপন্থী ভারতীয় বন্ধুরা বিস্মিত হলেও যেহেতু তিনি মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সুনজরে ছিলেন না, সে জন্য এই নাজুক পরিস্থিতিতে, মস্কোতে তাদের প্রতি অবিশ্বস্ত জহির রায়হানের উপস্থিতি সোভিয়েত দূতাবাসের কাম্য ছিলো না। মস্কোর ভিসা না পেয়ে জহির রায়হান সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের প্রতি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।
৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর শহীদুল্লাহ কায়সারের মৃত্যুর সংবাদ শুনে জহির রায়হান একবারেই ভেঙ্গে পড়েন। ১৭ তারিখে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক হেলিকপ্টারে করে ঢাকা এসে আলবদরের মরণ কামড়ের খবর বিস্তারিত জানতে পারলেন। বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি করে হানাদার বাহিনীর সহযোগী বহু চাঁই ব্যক্তির নাম সংগ্রহ করলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, তিনি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকেও দায়ী করেন। তিনি তখন মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। জামাতে ইসলামীর ঘাতক বাহিনী আলবদরদের দ্বারা ধৃত শহীদুল্লাহ কায়সারাকে খোঁজার জন্য পীর-ফকিরেরও শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। এমন এক জনের খপ্পরে পড়ে তিনি আজমীর পর্যন্ত গিয়েছিলেন।
৭২ এর ৩০ জানুয়ারী মিরপুরে তার অগ্রজকে খুঁজতে গিয়েছিলেন সে স্থানটি তখনও ছিলো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কিছু লোক ও তাদের সহযোগীদের নিয়ন্ত্রণে। তদন্ত করলে হয়তো জানা যেতো সেই অজ্ঞাত টেলিফোন কোত্থেকে এসেছিলো, যেখানে তাঁকে বলা হয়েছিলো শহীদুল্লাহ কায়সার মিরপুরে আছেন কিংবা মিরপুর থেকে কিভাবে তিনি উধাও হলেন। এটাও বিস্ময় যে, তার অন্তর্ধান সম্পর্কে কোন তদন্ত হয়নি। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে তার বিশ্বাসই ভাকে এভাবে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।
জহির রায়হান মার্কসীয় দর্শনের অনুসারী হলেও বড়দার মৃত্যু সংবাদে তিনি অদৃষ্টবাদী হয়ে গিয়েছিলেন। এর একটা কারণ এও হতে পারে যে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন প্রমুখের মূল রচনাবলী তিনি সামান্যই পড়েছেন। কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভ্রান্তি, নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা ও বিভক্তিতে তিনি বিক্ষুব্ধ হাতেন, কখনো বা হতাশ হয়ে পড়তেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কোপিকিং বিভক্তির পর তিনি পিকিংপন্থী শিবিরে অবস্থান করেও পরবর্তীকালে পিকিংপন্থীদের বিভক্তির সময় কোন বিশেষ দলের পক্ষ নেননি। তার লেখা ও ছবিতে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস পুরোপুরি প্রতিফলিত না হলেও কিছু লেখা ও ছবি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় জহির রায়হান কোন শিবিরের লোক–প্রগতির না প্রতিক্রিয়ার। নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রগতির শিবিরেই তার অবস্থান এবং এই শিবিরে অবস্থানের কারণেই প্রতিক্রিয়ার নির্মম শিকার হয়েছিলেন তিনি।
৩.
বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ অমান্য করে ছাত্ররা একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙ্গে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আগেই বলেছি যে দশজন ছাত্র প্রথম মিছিল করে বেরোয় জহির রায়হান ছিলেন তাদের একজন। প্রথম দিকের কয়েকটি দলকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলে লালবাগের কেল্লার পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর গুলি চালানো হয়।
এই ঘটনাটি জহির রায়হানের একুশে ফেব্রুয়ারীর কাহিনীতেও বিধৃত হয়েছে। এই কাহিনীর ছাত্র নায়ক তসলিম একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙ্গার জন্য বক্তৃতা দেয়। মিছিলে গুলি খেয়ে লাশ হয়ে হাসপাতালে যায়।
৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে একটি সংকলনের জন্য আমি জহির রায়হানের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু যারা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের এবং অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের কাছ থেকে লেখা নিয়েছিলাম। প্রত্যেকটি লেখার বিষয়বস্তু ছিলো এক বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে তারা কে কিভাবে দেখেছেন। জহির রায়হানের পর্যবেক্ষণের কাছাকাছি দুটি লেখার অংশ এখানে উদ্ধত করছি যা কিনা তাঁর এই কাহিনীর প্রামাণ্যভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এর একটি অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের অপরটি ঢাকা কলেজে তার সহপাঠী বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের।
শহীদুল্লাহ কায়সার লিখেছেন–
একুশে ফেব্রুয়ারী। ১৯৫২। উনিশ বছর পর একটি বিক্ষুব্ধ দিনের সব কটি মুহূর্তের উত্তেজনা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, রোমাঞ্চ বেদনা স্মরণ করা দুরূহ। অনেক মুখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। অনেক মুখ ঝকঝকে ছবির মত এখনও ভাসছে চোখের সামনে যা আর কোনদিন দেখা যাবে না। অনেক ঘটনা যা সেদিন মুখ্য মনে হয়েছিল আজ গৌণ হয়ে এসেছে। সেদিন যা দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল অভিজ্ঞতার আলোকে আজ তা স্পষ্ট।
দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আজ নতুন চেতনা এসেছে। এসেছে অনেক তব্রতা। গণসংস্থাগুলো অনেক বেশি সজাগ। তাই আজকের কোন আন্দোলনের সাথে বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীকে তুলনা করা অনুচিত।
যে এলাকায় একুশের ঘটনা প্রবাহের সূচনা হয় তা আজ চেনা দুষ্কর। সেখানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতালটা ছিল সেদিনের কলাভবন। যেখানে মেডিকেল হাসপাতালে আউটডাের এবং নার্সের কোয়ার্টার সেখানে ছিল কতগুলো ব্যারাক। তলার দিকে হাত চারেক পর্যন্ত ছিল পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনী, উপটা কঞ্চির বেড়া। শীতের দিনে কুয়াশা এবং শীত হুড়হুড় করে ভেতরে ঢুকে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়তো। এটাই ছিল মেডিকেল ছাত্রাবাস। এখানেই গুলি চলছিলো, যার একাংশকে নিয়ে আজকের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।
অনুজ শাহরিয়ার সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে লিখতে বলেছেন। কিন্তু তা লেখা সম্ভব নয়, কেননা এত কিছু লেখার আছে এবং এত কিছু স্মৃতি থেকে খুঁচিয়ে তোলার রয়েছে যা স্বল্প সময়ে সম্ভব নয়। আর এটা এমন একটা দিন এবং এমন একটা বিষয় যা নিয়ে ভাসা ভাসা বা আংশিকভাবে কলম চালান উচিত নয়।
আগেই বলেছি আজ ওই এলাকাটার পরিবর্তন হয়েছে, আজকের আন্দোলনের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু যে পরিবেশে সেদিনের সগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তার পরিবর্তন এখনও, উনিশ বছর পরও দেখছি না। সেটা হল শাসককূলের স্বৈরাচারী মনোভাব।
একুশের হরতাল ও জমায়েতকে পণ্ড করার জন্য ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যারাত্রিতে যখন ১৪৪ ধারা জারি করা হল তখনও কেউ বুঝতে পারেনি পরদিন অর্থাৎ ২১ তারিখে কি ঘটবে। কিন্তু মধ্যরাত্রির মধ্যেই অবস্থাটা পাল্টে গেল। মধ্যরাত্রির মধ্যেই ফজলুল হক হল, ঢাকা হল ও সলিমুল্লা হলের ছাত্ররা মিটিং করে জানিয়ে দিলেন যে তারা পিছ পা হতে রাজী নন। যদি সরকার ভয় দেখিয়ে রক্তচক্ষুর শাসানি ভাষায় রূপান্তরিত করতে চায় তবে এখনই তার ফয়সালা হয়ে যাক। এ মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত গোটা আন্দোলনের চেহারাটা পাল্টিয়ে দেয়। তাই আমরা দেখি শুধু পুলিশ নয় মুসলিম লীগের পালা গুণ্ডারা, মহল্লার সর্দাররা স্কুলে স্কুলে ভয় দেখিয়ে বেড়ানো সত্ত্বেও একুশে ফেব্রুয়ারী সব স্কুল কলেজে ধর্মঘট হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদ এবং মেডিকেল ছাত্রাবাস ছিল সেদিনের একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সারা পাকিস্তানে ঢাকা মেডিকেল কলেজই একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল যেখানে মুসলীম ছাত্রলীগ নামে প্রতিষ্ঠানে কোন কমিটি এমন কি একজন সভ্যও ছিল না। সংগ্রাম কমিটির প্রাণশক্তি ছিল মেডিকেলের ছাত্রসংসদ। সম্ভবতঃ এ কারণেই মেডিকেল ছাত্ররা পুলিশের বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য ছিল।
গুলি চালনার ধরনটাও লক্ষণীয়। প্রথম কয়েক রাউণ্ডের গুলি মেডিকেল ছাত্রাবাসকে লক্ষ্য করেই চালান হয়। এগার নম্বর, তিন নম্বর, এবং সাত নম্বর ব্যারাকের ঘরের ভেতরে পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালে ছেদ করে পড়ার টেবিলে, শোয়ার খাটিয়ার গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়। প্রথম রাউণ্ডের গুলিতেই বরকত শহীদ হন। এখানে যারা যারা আহত হন তাদের সবগুলো আঘাতই হাঁটুর উপর। মারার জন্যই যে সেদিন গুলি ছোঁড়া হয়েছিল এবং ছাত্রাবাসে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া হয়েছিল তাতে লেশ মাত্র সন্দেহ নেই।
(সচিত্র সন্ধানী ও একুশে ক্রোড়পত্র ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)
জহির রায়হানের সহপাঠী, তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র বোরাহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটি সম্পর্কে লিখছেন–
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ভিড়; বাইরে ১৪৪ ধারা; সকাল দশটা। চিৎকার শ্লোগান। বাইরে পুলিশ। আমরা ঘুরছি, কথা শুনছি; সবাই উত্তেজিত, সবকিছুই অনিশ্চিত, মধ্যে মধ্যে শ্লোগান; রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমরা ঘুরছি, কথা শুনছি, নেতারা ব্যস্ত, পরস্পরের উপর ক্রুদ্ধ, মধ্যে মধ্যে শ্লোগান; পুলিশ জুলুম চলবে না। ভিড় বাড়ছে ভিতরে আর রাস্তা ফাঁকা, পুলিশ বাদে।
হোস্টেলে থাকি, ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশের ছাত্র। আমরা কজন হাজির। কেন এসেছি স্পষ্ট। স্বপ্নের মধ্যে মার মুখ, তার একটি শব্দ; বাংলা; আমার মনে এছাড়া আর কিছু নেই। ভিড়; চিৎকার লোগন, সকাল সাড়ে দশটা।
হঠাৎ দেখি কারা যেন লোহার গেট খুলে দিয়েছে, আর সবাই দুজন দুজন করে রাস্তায়। পুলিশ তৎপর, গ্রেফতার করছে, খোলা গাড়িতে তুলছে, আর শ্লোগান রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই; পুলিশ জুলুম চলবে না। শ্লোগান তো নয় শব্দের প্রতিবাদ।
আমি আমগাছতলায়, চোখ ঐ সব। আকাশ নির্মম নীল। শব্দ পাগল করে দিচ্ছে পুলিশদের, বেড়ির মতো বাংলাভাষা তাদের ঘিরে ধরেছে, সেই তখন টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে শুরু করেছে তারা। টিয়ারগ্যাস ফাটছে, ধোঁয়ায় একাকার, অসহ্য যন্ত্রণা চোখে মুখে; আমরা ছুটে দোতলায়, সকাল এগারোটা। আধঘন্টা বাদে নিচে এলাম। পিছনের লোহার রেলিং ডিঙ্গিয়ে সঙুক বেয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। খিদেও পেয়েছে। এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। পুরানা পল্টনে পুলের কাছে এক রেস্টুরেন্ট, চা আর খাবার খেলাম। যখন বেরোলাম রাস্তা থমথম করছে। কি ব্যাপার? পুলিশ গুলি চালিয়েছে মেডিকেল কলেজের সামনে। কয়েকজন মারা গেছেন। স্বপ্নের মধ্যে মার মুখের মতো চারপাশে বাংলাদেশ, বাংলাভাষা আর বাংলাকে গুলি করছে কারা কারা—সমস্ত চেতনায় থরথর ঐ প্রশ্ন।
পিছনের গেট দিয়ে মেডিকেল কলেজে এলাম। রাস্তার ধারেই ছাত্রাবাস, সেখানে জটলা চিকার, শ্লোগান, ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি। বিকেল চারটায়, দৈনিক আজাদের বিশেষ সংখ্যা, কাড়াকাড়ি করে নিলাম। কারা যেন বলল, জেলে কি আজাদ পাঠানো সম্ভব? বন্ধুদের জানান উচিত নয় কি ঘটছে বাইরে?
আমরা ঠিক করলাম পৌছে দেব। জেলখানার পশ্চিম দিকে উর্দু রোড, মসজিদের উল্টোদিকেই জেলখানার প্রাচীর। মসজিদের মিনারে চড়ে আজাদ ছুড়ে দেয়া হল। জেলখানার মাঠে রাজবন্দীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারা দৌড়ে এসে কুড়িয়ে নিলেন।
অনলাম সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে। বেচারাম দেউড়ীতে ছাত্রাবাস, যখন পৌঁছালাম সান্ধ্য আইনের শুরু। পুলিশের গাড়ী রাস্তায়। কিছু একটা করা দরকার। ছাদে আমরা ঃ রাত্রি বিদীর্ণ করে শ্লোগান উঠছে নানাদিক থেকে। বেচারাম দেউড়ীতে ঢাকা কলেজের তিনটি ছাত্রাবাস, সেইসব ছাদ থেকে আওয়াজ উঠছে, মিলছে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ছাত্রাবাসে, মিলেছে গিয়ে সারা বাংলাদেশে। কোথাও থেকে গুলির শব্দ আসছে। রেডিওতে নূরুল আমীনের গলা। ঘৃণা ঘৃণা ঘৃণা!
ঘুমতো নয় আশা ও হতাশার নির্যাতন। (প্রাগুক্ত)।
জহির রায়হানের ঘনিষ্ঠ দুজন, একজন তার অগ্রজ, আরেকজন সহপাঠী–ঠিক এভাবেই বর্ণনা করেছেন বায়ান্ন সালের সেই আগুনঝরা দিনটির কথা। তাঁর অন্য বন্ধুরাও যারা তাঁর কাছাকাছি ছিলেন, প্রায় একইভাবে দেখেছেন এই দিনটিকে। সেদিন যারা ছাত্র ছিলেন অথবা ক্যাম্পাসে ছিলেন, প্রত্যেকের পর্যবেক্ষণই একই ধরনের ছিলো। জহির রায়হানের পর্যবেক্ষণ যে এর চেয়ে আলাদা কিছু ছিলো না–তাঁর আরেক ফরুন বা একুশে ফেব্রুয়ারী পড়লে পরিষ্কার বোঝা যাবে।
১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি জহির রায়হান একুশে ফেব্রুয়ারী ছবিটি বানাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি আরেক ফাল্গুন যদিও এর আগে লিখেছিলেন, কিন্তু ছবির জন্য ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা কাহিনী। শিল্পী মুর্তজা বশীরকে তিনি চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব দিয়ে বলেছিলেন, গল্পের কাঠামো হবে এই রকম চারটি পরিবার সমাজের চারটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। একটি উচ্চবিত্ত, একটি মধ্যবিত্ত, একটি শ্রমিক ও একটি কৃষক দম্পতি থাকবে, যারা ঘটনাক্রমে বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটিতে এমন একটি জায়গায় একত্রিত হবে যেখানে ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। গুলির শব্দ হওয়ার পরই দেখা যাবে একটি কাক আর্ত কণ্ঠে উড়ছে গোটা ঢাকা শহরের আকাশে।
মুর্তজা বশীর জহির রায়হানের মুখে বলা গল্পটির উপর ভিত্তি করে একুশে ফেব্রুয়ারীর চিত্রনাট্য লেখেন। শ্রমিক চরিত্রটির মুখে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করার জন্য বস্তিতে ঘুরে শব্দচয়ন করেন। চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ হলে জহির রায়হান এটি এফডিসি স্টুডিওতে জমা দেন। নবারুণ ফিল্মস-এর ব্যানারে নির্মিতব্য এই ছবির জন্য চরিত্র নির্বাচন পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো। এ ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিলো খান আতা, সুমিতা, রহমান, শবনম, আনোয়ার, সুচন্দা, কবরী প্রমুখ চিত্র তারকার। কিন্তু এ ছবি নির্মাণের অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়নি। মুর্তজা বশীর আমাকে পরে বলেছেন একুশে ফেব্রুয়ারীর চিত্রনাট্য লেখার জন্য জহির রায়হান তাঁকে অগ্রিম একশ টাকাও দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এফডিসিতে খুঁজলে এই চিত্রনাট্যটি পাওয়া যাবে।
এরপর জহির রায়হান বাণিজ্যিক ছবি বানাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একুশে ফেব্রুয়ারী বানাবার সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকে। পাঁচ বছর পর জহির রায়হানের একুশে ফেব্রুয়ারীর চিত্বকাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক সমীপেষুতে। আমি তখন সাহিত্য-চলচ্চিত্র বিষয়ক এই পত্রিকাটির সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলাম। একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। জহির রায়হানকে অনুরোধ করলাম একটি উপন্যাস লিখতে বিশেষভাবে বললাম একুশে ফেব্রুয়ারী নামে যে ছবিটি তিনি করার কথা ভেবেছিলেন তার কাহিনীটি দেয়ার জন্য। তিনি জানালেন, চিত্রনাট্যটি হারিয়ে গেছে। পরে তাকে বললাম, লেট দেয়ার বি লাইট নামে যে ছবিটি বানাবার কথা ভাবছেন তার কাহিনীটি দিতে। তিনি রাজী হলেন। কদিন পর হঠাৎ শুনলাম, সচিত্র সন্ধানীর (তখন মাসিক এবং আমাদের পত্রিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী) সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দীন, যিনি কিনা জহির রায়হানের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁর অনুরোধ ফেলতে না পেরে লেট দেয়ার বি লাইট-এর কাহিনীটি আর কত দিন নামে ভাঁকে সন্ধানীর জন্য দিয়ে ফেলেছেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই আমি ক্ষুব্ধ হই এবং জহির রায়হানও আমার আচরণে বিব্রত হন। শেষে তিনি সম্মত হন, আমাদের পত্রিকার জন্য একুশে ফেব্রুয়ারীর কাহিনীটি দেবেন, তবে শর্ত হচ্ছে। তিনি বলে যাবেন, আমি শুনে শুনে লিখবো।
জহির রায়হানের ক্ষেত্রে এটি নতুন বা অভিনব কিছু নয়। আমি যখন তাঁর সহকারী হিসেবে ছবিতে কাজ করছি তখন দেখেছি তিনি বলৈ যাচ্ছেন আর তাঁর দুজন সহকারী এক সঙ্গে দুটি ছবির চিত্রনাট্য তিলিখনে ব্যস্ত।
কখনো তিনি টেপরেকর্ডারে বলে গেছেন, সহকারীরা সেখান থেকে পাঠোদ্ধার করেছেন। তবে তখন আমার এটা মনে হয়েছিলো এভাবে বাজারচলতি ছবির চিত্রনাট্য হয়তো লেখা যেতে পারে, কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। ফলে তিলিখনের দ্বারা একুশে ফেব্রুয়ারীর কাহিনী লেখার ব্যাপারে আমি খুব একটা আশাবাদী ছিলাম না। দেখা গেলো এ ছাড়া উপায়ও নেই। তিনি ছবির স্যুটিং নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত।
তখন সম্ভবত ঈদের জন্য কয়েকদিন ছুটি ছিলো। আমি পর পর তিনদিন বসে জহির রায়হানের কথামতো লিখে গেলাম। তিলিখনের জন্য তিনদিন অনেক বেশি সময়, তবু লেখার ফঁাকে ফাকে চিত্রনাট্যের মত ছবির দৃশ্যগুরো বিস্তারিত শুনতে চাইতাম বলে লিখতে গিয়ে সময় বেশি লাগলো। এই শুনতে চাওয়াটাও অস্বাভাবিক ছিলো না। কারণ জহির রায়হানের অধিকাংশ চিত্রনাট্য খসড়ার মতো লেখা। ছবির শট বিভাজনের সময় এমনকি স্যুটিং-এর সময়ও অনেক নতুন উপাদান যোগ হতো। যে কারণে তার চিত্রনাট্য পড়ে বোঝা যাবে না। শেষ পর্যন্ত ছবিটি কি হবে। শুধু একবার এর ব্যতিক্রম দেখেছি। সেটা তার বহুল প্রশংসিত স্টপ জেনোসাইড-এর ক্ষেত্রে। মূল পরিকল্পনায় এ ছবি যেমনটি হওয়ার কথা ছিলো বাস্তবে এর এক চতুর্থাংশও রূপায়িত হয়নি। আমার ধারণা বাজেট সমস্যায় আক্রান্ত না হলে এটি গ্রানাড়া গ্রানাডা মাইন-এর চেয়ে বেশি আবেদন সৃষ্টিকারী ছবি হতে পারতো। দুর্ভাগ্য ছবিটির মূল চিত্রনাট্য চুরি হয়ে গিয়েছে।
তাঁর সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারীর শ্রুতিলিখনের সময় আলোচনা করতে গিয়ে বুঝেছি আইজেনস্টাইনের ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন আর অক্টোবর তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিলো। লেখা শেষ করার পর তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম ছবিটি কবে বানাবেন। তাঁর জবাব ছিলো– এখনো সময় হয়নি।
৬৫ সালে মর্তুজা বশীরকে যে একুশে ফেব্রুয়ারীর চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ৭০-এ সেই কাহিনীতে জহির রায়হান আরো কটি চরিত্র সংযোজন করেছেন। কাকের প্রতীকটি এখানে আছে কিন্তু মুখ্য হচ্ছে কাহিনীর শেষে নদীর প্রতীকটি। ছবি তৈরি হলে এই কাহিনীতে যে আরো বহু প্রতীক ও উপাদান যুক্ত হতো এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে প্রথম ও শেষ দৃশ্যে অনেকগুলো মন্টাজ এফেক্ট-এর কথা তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।
একুশে ফেব্রুয়ারী সমীপেষুতে ছাপার সময় শিল্পী হাশেম খানের কিছু কেঁচও অলঙ্করণ হিসেবে ছাপা হয়েছিলো। জহির রায়হান স্কেচগুলো পছন্দ করেছিলেন।
সমীপেষুতে প্রকাশিত লেখাটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ছিলো। তাড়াহুড়ো করে ছাপতে গিয়ে কিছু শব্দ ও বাক্য এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো। সংশোধিত কপিটি আমার কাছে থাকায় গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সংশোধন করেই ছাপা হয়েছে।
৪.
শেষের দিকে জহির রায়হানের সব লেখাই ছিলো চিত্রনাট্যের মতো। এমনকি প্রবন্ধেও তিনি ছোট ছোট বাক্যে চিত্রকল্প নির্মাণ করতেন। একুশে ফেব্রুয়ারী তার একেবারে শেষের রচনা। এরপর বড় কোন লেখায় তিনি হাত দেননি। ছোটখাট কিছু স্কেচ জাতীয় লেখা (অধিকাংশই একুশের স্মরণিকাসমূহের সম্পাদকদের তাগিদে) এবং কয়েকটি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন ৭০-৭১ সালে।
আঙ্গিকগত বিচারে একুশে ফেব্রুয়ারী আর কত দিন-এর সমশ্রেণীর লেখা এর কোনটাই আরেক ফাল্গন, বরফ গলা নদী, বা হাজার বছর ধরের মতো উপন্যাস নয়। এগুলোকে চিত্রনাট্যের রূপরেখা বা ছবির কাহিনী বলা যেতে পারে। এর ভেতর বহু সংযোজনের অবকাশ আছে। উপন্যাস আকারে লিখতে জহির রায়হান এগুলি অন্যভাবে লিখতেন। আবার ছবি করার সময়ও তিনি আরো বহু কিছু যোগ করতেন। জীবন থেকে নেয়া ছবিতে একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরী যারা দেখেছেন তারা জানেন এই ছবির সেরা অংশ এটি। অথচ চিত্রনাট্যে শুধু প্রভাত ফেরীর উল্লেখ ছিলো। উনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময় ২১শে ফেব্রুয়ারীর রাত থেকে তিনি শহীদ মিনারে প্রভাত ফেরীর প্রামাণ্য ছবি তুলেছেন। কয়েকটি পরিকল্পিত দৃশের সঙ্গে
অনেকগুরো প্রামাণ্য দৃশ্য সম্পাদনার টেবিলে বসে যোগ করে এর আবেদন বহুগুণ বাড়িয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারীর কাহিনীতে মিছিলে গুলির দৃশ্য আছে। জীবন থেকে নেয়া ছবিতে আমরা মিছিলে গুলির দৃশ্য দেখেছি। শেষােক্ত দৃশ্যের চেয়ে প্রথমটি অনেক বেশি শিল্পমণ্ডিত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী।
একুশে ফেব্রুয়ারী যদি ছবি হতো তাহলে এটি সরাসরি একটি রাজনৈতিক ছবি হিসেবে আখ্যায়িত হতো। রাজনৈতিক কাহিনীতে কাল একটি বড় বিষয়। রাজনীতি নির্দিষ্ট সময়ের গীতে এক ধরনের আবেদন সৃষ্টি করে, সময়ের ব্যবধানে সেই আবেদন ফিকে হয়ে যায়, যদি প্রামাণ্যকরণ কাহিনীর প্রধান উপজীব্য হয়। বহু রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত উপন্যাস বা ছবি নির্দিষ্ট সময়ে যতটা আবেদন সম্পন্ন হয় পরবর্তী সময়ে ততোটা নাও হতে পারে। অবশ্য মহৎ শিল্পকর্মের বিষয়টি আলাদা। উদয়ের পথে জাতীয় ছবি এক সময় আদর্শস্থানীয় ছিলো। এখন এর এতটুকু আবেদন আছে বলে মনে হয় না। নিছক সময় বোঝার জন্য বা নির্দিষ্ট সময়ের ছবির চরিত্র বোঝাৱ না এ ধরনের ছবি দেখা যেতে পারে।
একুশে ফেব্রুয়ারী বায়ান্ন সালের ঘটনা, মূল কাহিনী লেখা এর এক যুগ পরে। রাজনৈতিক কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও এর চরিত্রগুলি এখনো এই ছিয়াশি সালেও আধুনিক, মনে হয় সমকালের। আমলা, ব্যবসায়ী, কেরানী, ছাত্র, রিকশাওয়ালা, কৃষক কিম্বা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং সর্বোপরি শ্রেণীগত যে সম্পর্ক, সব কিছু এখনকার মতোই ক্রিয়াশীল। কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করলে এ কাহিনী উনসত্তরের কিংবা তিরাশিচুরাশির অথবা আগামী দিনের কোন আন্দোলনের হতে পারে। শাসকের ভাষা, শোষকের ভাষা এবং আচরণ এতটুকু বদলায়নি। এ কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারী মহৎ সৃষ্টির দাবী করতে পারে, এর আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও।
বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি ধারণা রয়েছে এটি বুঝি নিছক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন। বদরুদ্দীন উমর যদি তিনটি বিশাল খণ্ডে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস (পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি) না লিখতেন আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হতো না সেই সময়কার আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা বা ভাষা আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণের বিষয়টি। জহির রায়হানের একুশে ফেব্রুয়ারী লেখা হয়েছে এই ইতিহাস রচনার আগে। কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের আবেগ ও অংশগ্রহণের বিষয়টি তার এই লেখায় রয়েছে। যেহেতু এটি মূল চিত্রনাট্য নয়, সেজন্য বিস্তারিতভাবে না এলেও কৃষকের প্রতিনিধি গফুর এবং শ্রমিকের প্রতিনিধ সেলিম কাহিনীর শুরুতে কৌতূহলী বহিরাগত হলেও তাদের পরিণতি ছাত্রদের দ্বারা সূচিত এই আন্দোলনে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। এটি সম্ভব হয়েছে জহির রায়হানের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কারণে। একুশে ফেব্রুয়ারী কাহিনী রাজনীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও জহির রায়হানের অপরাপর গল্প উপন্যাসের মতো মানবিক উপাদান ও হার্দিক সম্পর্ক এতে অনুপস্থিত নয়। ফলে রাজনৈতিক হওয়া সত্ত্বেও এটি তত্ত্বগন্ধী বা শ্লোগানাক্রান্ত নয়। বর্ণানায় বরং কাব্যিক ব্যঞ্জন রয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কারণ আগেই বলেছি একুশে ফেব্রুয়ারী ছিলো জহির রায়হানের শিল্প-মানসের সৃজনশীল আবেগের অফুরন্ত উত্স।
শাহরিয়ার কবির।
১ ফাল্গুন, ১৩৯২