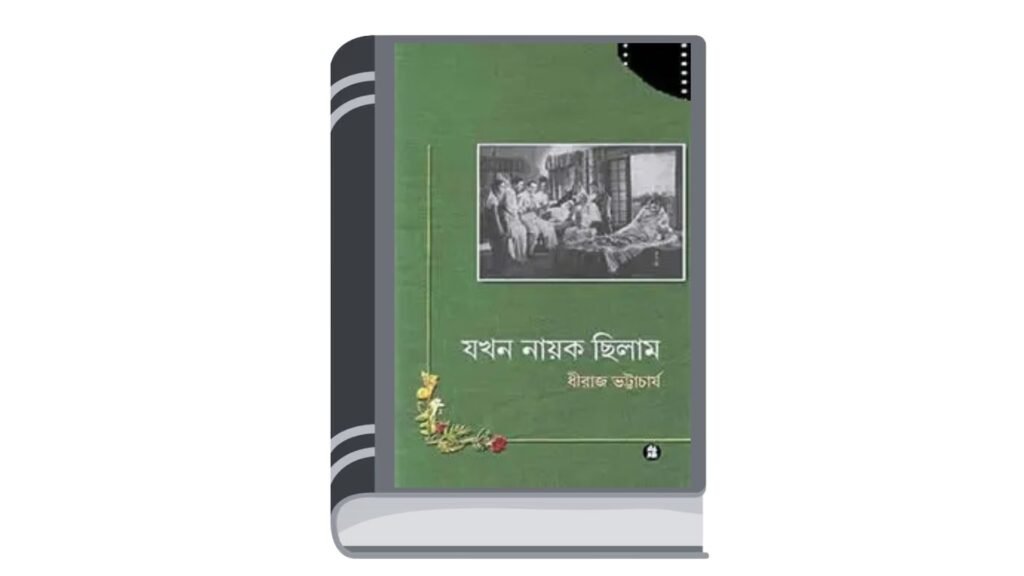১. পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র
যখন নায়ক ছিলাম – ধীরাজ ভট্টাচার্য
সম্পাদনা: দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৩৬৭
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
.
পটকথা
সন ১৯০৫। ধীরাজ ভট্টাচার্যর জন্ম হয় বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের যশোর জেলার পাঁজিয়ায়। ১৯২৩-এস্কুল পেরিয়ে পাঠ শুরু হল কলেজের। আর তখনই মনের গভীরের আশৈশব বাসনা রূপ নিল রূপোলি পর্দায়।
১৯২৫। তখনও ছবির কথা ফোটেনি। নির্বাক যুগ। ছবির নাম ‘সতীলক্ষ্মী’। এক বখাটে ছেলের মামুলি চরিত্রে ধীরাজের চিত্র-প্রবেশ। বাড়ির অজান্তেই ঘটল সে ঘটনা। ফলে ছবিমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে গেল আত্মীয়মহলে। অখুশি হলেন বাবা ললিতমোহনও। জোর করে পুলিশের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন ছেলেকে। নিজের শহর ছেড়ে যেতে হল চট্টগ্রাম। অনিচ্ছার চাকরিতে মন বসল না। হঠাৎই ছুটি নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। আর ফিরে যাননি।
১৯২৯। এ যাবৎ রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ ঘটেনি ছবির পর্দায়। তার ‘মানভঞ্জন’ রূপান্তরিত হল চলচ্চিত্রে—‘গিরিবালা’। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক মধু বসু। প্রযোজক ম্যাডান থিয়েটার্স। রবীন্দ্র সম্মতিতে শেষ হল চিত্রনাট্যের কাজ। নতুন করে কিছু সংলাপ লিখে দিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রযোজকদের পছন্দ হল সে নাট্যরূপ। আপত্তি উঠল নায়ক নির্বাচনে।
জাহাঙ্গীরজী (ম্যাডান থিয়েটার্স-এর কর্ণধার) বললেন : বোস, নতুন কোনো ‘হিরো’র সন্ধান কর।
সব ছবিতেই দুর্গাদাস আর দুর্গাদাস। একটু চেঞ্জ হোক।
আমি বললাম : দেখি চেষ্টা করে।
আমি নতুন হিরোর সন্ধানে লেগে রইলাম। অনেককে বললাম –শেষে একদিন বন্ধুবর সুধীরেন্দ্র সান্যাল একটি নতুন ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এলো। বেশ চেহারা, তার বয়স খুব কম। অবশ্য এর আগে ম্যাডানেরই একটা ছবি (‘সতীলক্ষ্মী’)–তে সে কাজ করেছিল। সে আমাকে তার জীবনের ইতিহাস বলল। সে আগে পুলিশে কাজ করত, কিন্তু অভিনয়ের দিকে তার ঝোঁক বেশী বলে সে পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।
আমি ঠাট্টা করে বললাম : পুলিশ থেকে একেবারে আটিস্ট?
এই শিল্পীটি আর কেউ নয় .. ধীরাজ ভট্টাচার্য।
(‘আমার জীবন’, মধু বসু)
.
নায়ক হিসেবে ধীরাজকে মেনে নিলেন প্রযোজকরা। নির্বাক যুগের পরিক্রমায় গিরিবালার পরপরই কালপরিণয় (১৯৩০), মৃণালিনী (১৯৩০) এবং নৌকাডুবিতে (১৯৩২) বন্দিত হলেন নায়ক ধীরাজ।
নির্বাক অবসানে এল সবাক যুগ। মুখর হল মূক ছবি। বিজ্ঞাপনি ভাষায় ‘shadows talk in human voice’ বা ‘Pictures do the talking’। স্ব-রবে অনেকে বাতিলের দলে গেলেও ধীরাজের স্বীকৃতি বেড়ে গেল। সেই নায়কজীবনের সময়, সমাজ ও সঙ্গীদের ঘিরে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি যেন এক চলচ্ছবি।বহু নায়ক চরিত্রের পরতে পরতে গড়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের অকথিত ইতিহাস।
বয়সের সঙ্গে বদলেছে চরিত্র। বখাটে ছেলে থেকে রোমান্টিক নায়ক, নায়ক থেকে ভিলেন। গ্রন্থশেষে তারই আভাষ। বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র-র ‘সমাধান’ চিত্রে চরিত্রবদল। ‘ভিলেন’ জীবনের শুরু। হারিয়ে গেল অনেক না-বলা কথানায়কের অন্তরালে। এ যেন ব্রিটিশ লেখক Quentin Crisp-এরই প্রকাশ : An autobiography is an obituary in serial form with the last instalment missing.’ (The Naked Civil Servant, Quentin Crisp) শুধু তাই নয় ভিলেনের ভানে কখনও হয়েছেন গোয়েন্দা, আবার কখনও নির্মল কমেডিয়ান। বখাটে ছেলের নীরব ভাষা বদলেছে সরব নায়কের রোমান্সে বদলেছেভিলেনেরক্রুরতায় বদলেছে ব্যঙ্গেরকশাঘাতে অবিচ্ছেদ্য বাঙালিয়ানায়। জীবনের তর-বেতর অস্তিত্বে গড়েছেন বহুবিচিত্র রূপময়তা। তার অভিনয়বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠা দেয় ব্রিটিশ পরিচালক-অভিনেতা Laurence Olivier-এর অভিজ্ঞতা।
চলচ্চিত্রের শতাধিক রূপায়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক অভিনয় করেছেন মঞ্চে–কখনও রঙমহল, কখনও নাট্যনিকেতন আবার কখনও বা কালিকা থিয়েটারে। জীবনসায়াহ্নে মঞ্চ ও চিত্র–দু’মাধ্যমেই ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’-এহাজারি ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয়ের বিরল কৃতিত্ব তার।
নায়ক জীবনের অভিজ্ঞতার এই গ্রন্থরূপের পাশাপাশি লিখেছিলেন পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতায় ‘যখন পুলিশ ছিলাম’। গল্পগ্রন্থ ‘সাজানো বাগান’ এবং ‘মহুয়া মিলন’ আর উপন্যাস মন নিয়ে খেলা তার সাহিত্যচর্চার প্রকাশ। তাও অপ্রকাশ রয়ে গেছে ধীরাজ-জীবনের বহু অভিজ্ঞতা। তবু যা পাওয়া গেছেতাই বা কম কী।
৪ মার্চ ১৯৫৯। কালের অমোঘ নিয়মে হারিয়ে গেলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য।
দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়
.
“আমার জীবন নদীতে জোয়ার নেই, শুধু ভাটা। অনাদি-অনন্তকাল ধরে একঘেয়ে মিনমিনে জলস্রোত বয়ে চলবে লক্ষ্যহীন, উদ্দ্যেশ্যহীন পথভোলা পথিকের মতো। বাঁকের মুখে ক্ষণিক থমকে দাঁড়াবে, আবার চলতে শুরু করবে গতানুগতিক রাস্তা ধরে। এ নদী শুকিয়ে চড়া পড়ে গেলেও জোয়ার কোনোদিন আসবেনা, এই বোধ হয় নিয়তির বিধান।”
ধীরাজ ভট্টাচার্য
.
ভূমিকা
সত্যিই একটা ভূমিকার বিশেষ দরকার, নইলে মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাবে পাঠক ও আমার মধ্যে। ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘যখন পুলিশ ছিলাম’ বার হবার সময় থেকেই বহু পাঠক-পাঠিকার অনুরোধপত্র আমি পাই। সবার বক্তব্য এক-পরবর্তী রচনা যেন আমার নায়ক জীবনকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়। তা না হয় হল। কিন্তু তারপর? এই তারপরের একটা সুষ্ঠু মীমাংসায় পৌঁছতেই প্রায় ছ’ মাস কাটিয়ে দিলাম।
কথায় বলে, একে রামানন্দ তায় ধুনোর গন্ধ। আত্মজীবনী, তাও আবার সিনেমা নায়কের! বিশ বছর আগে হলে কল্পনা করাও মহাপাপ ছিল। আজ পৃথিবীর রং হাওয়া বদলে গেছে। ঢিলে হয়ে গেছে তথাকথিত সামাজিক ও নৈতিক বাঁধনের শক্ত গেরোগুলো। আজ দর্শক শুধু পর্দার ছায়ার মায়ায় ভুলতে রাজি নয়। আজ তারা পর্দার অন্তরালের মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা, সুখ-দুঃখ বিরহ মিলনের বার্তা জানবার জন্যে উদগ্রীব, আগ্রহশীল। সে আগ্রহ মেটাবার সাহস থাকলেও সামর্থ্য নেই। দেশটা ভারতবর্ষ না হয়ে পৃথিবীর আর যে কোনও সভ্য দেশ হলে এত ভাবনা-চিন্তার কারণ থাকত না। ও দেশের নায়ক-নায়িকারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সব কিছুই খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি দিয়ে বিচার করে বলেই বুক ফুলিয়ে জীবনটাকে ভোলা চিঠির মতো দর্শক সাধারণের চোখের সামনে মেলে ধরে। উফুন্ন দর্শক হাসাহাসি করে, মাতামাতি করে, আবার দিনকতক বাদে সব ভুলেও যায়। কিন্তু এদেশের ভবি অত সহজে ভোলে না। ধরুন, বিশ বছর আগে রোমান্টিক আবহাওয়ায় কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে একটি সুন্দরী নায়িকাকে প্রেম নিবেদন করেছিলাম, সাড়াও হয়তো কিছু পেয়েছিলাম। বর্তমানে সিনেমা-জগৎ ছেড়ে স্বামীপুত্র নিয়ে তিনি হয়তো সুখের নীড়ে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছেন। আজ খুঁচিয়ে ঘা করার মতো একযুগ আগের বিস্মৃতপ্রায় সেই ঘটনা যদি আমার নায়ক জীবনে উল্লেখ করে বসি, পরিণামটা একবার চিন্তা করে দেখুন। তাছাড়াও আর একটা মস্ত বিপদ, নায়ক জীবন লিখতে বসে কোনও গোঁজামিল দিয়ে চলে যাবার উপায় নেই। কেননা অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী এখনও জীবিত রয়েছেন। এইবার আমার অবস্থাটা একবার ভাল করে ভেবে দেখুন। রোমান্টিক নায়ক জীবন লিখতে হবে রোমান্সকে বাদ দিয়ে। ঠিক নুন বাদ দিয়ে মুখরোচক খাবার রান্নার মতো নয় কি? অনেক ভেবেও কোনও কুলকিনারা না পেয়ে কাপুরুষের মতো পিছু হটতে লাগলাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি পৌঁছে গেছি পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে সিনেমার আদি যুগে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ দর্শক বা পাঠকের ধারণাই নেই কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, কত হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নির্বাক যুগের ঐ বোবা শিশু একটু একটু করে এগিয়ে এসে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বর্তমানের মুখর যুগের মাঝখানে। দেখি সেদিনের অবহেলায় ফেলে আসা ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনাগুলো আজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আজ এক নতুন চোখে তাদের দেখতে পেলাম। যত্ন করে তাই একটি একটি করে বুকে তুলে নিয়ে কথার মালা গেঁথে আঁকাবাঁকা পথে সামনে এগিয়ে চললাম। এরাই হল আমার নায়ক জীবনের মূলধন। এই হল যখন নায়ক ছিলাম’ এর সত্যিকারের ইতিহাস। সত্যকে যথাযথ বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি। কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজনবোধে পাত্র-পাত্রীর নামধাম গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছি, এইমাত্র।
আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। অনেক পাঠক পাঠিকার ধারণা, আমি ইচ্ছা করেই হঠাৎ কাহিনীর ছেদ টেনে দিয়েছি। ভুল ধারণা। যখন নায়ক ছিলাম’ বলতে আমি আমার রোমান্টিক নায়ক জীবন সম্বন্ধেই বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখাবার চেষ্টা করেছি। প্রশংসার জয়মাল্যের পরিবর্তে পেয়েছি সমালোচনার নিষ্ঠুর কশাঘাত। তাই একঘেয়েমি কিছুটা এড়াবার জন্য, চরম লাঞ্ছনার মধ্যেই কাহিনীর যবনিকা টেনে দিয়েছি।
অনেকে এই অভিযোগও করেছেন, এখনও তো আপনি নায়কের ভূমিকায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় করেন, সুতরাং যখন নায়ক ছিলাম’ অত আগে শেষ করলেন কেন? উত্তরে তাদের একটু ধীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি ‘টাইপ’ চরিত্রে আসার পর যে সব নায়ক চরিত্রে আমি রূপদান করেছি, সেগুলি কি রোমান্টিক নায়ক? ধরুন ‘নিয়তি’, ‘কঙ্কাল’, ‘মরণের পরে’, ‘ময়লা কাগজ’, ‘সেতু’ প্রভৃতি। ‘যখন নায়ক ছিলাম’-এ এগুলোর উল্লেখ করলে আর যে অসংখ্য ‘টাইপ’ চরিত্রে অভিনয় করে আমি পেয়েছি দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা, সেগুলি বাদ দেওয়া চলে কি? অই রোমান্টিক নায়কের চিতার আগুন নেববার আগেই কাহিনীর শেষ করেছি। এর জন্য যা কিছু অপরাধ সব আমার, পাঠক-পাঠিকার কাছে এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।
.
যখন নায়ক ছিলাম
মখমলের উপর সোনালী জরির বিচিত্র কারুকার্যখচিত পোশাক, মাথায় সোনার মুকুট, তাতে বহুমূল্য হীরে-জহরত বসান। সাদা ধবধবে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র চলেছেন কোন সে অজানা দেশের রাজকন্যার সন্ধানে। নীল আকাশে রূপালী মেঘের ছোট-বড় পাহাড়গুলো চোখের নিমেষে পার হয়ে পক্ষিরাজ ছুটে চলেছে। নীচেঅসংখ্য রাজ্য ও জনপদ, নদনদী ও অরণ্য–পর্বত হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঘোড়া বা ঘোড়সওয়ারের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা চলেছে দূরে, বহুদূরে, বুঝি বা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। যেখানে অচিন দেশের রাজকন্যা ময়নামতী মালা হাতে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছে রাজপুত্রের আশায় পথ চেয়ে। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। অবশেষে দেখা গেল বহুদূরে নীল সমুদ্রের মাঝখানে ছোট একটা দ্বীপ আর সমস্ত দ্বীপটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা সোনার অট্টালিকা। পড়ন্ত রোদের রক্তিম আভায় অপরূপ স্বপ্নের মায়াপুরীর মত দেখাচ্ছে। আনন্দে পক্ষিরাজ হ্রেষারব করে উঠে দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটে চলল, রাজপুত্র ঘোড়ার পিঠে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। এমন সময় ঘটল এক অঘটন। কোনো অদৃশ্য আততায়ীর এক বিষাক্ত তীর এসে বিল পক্ষিরাজের গলায়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে নীচে নামতে লাগল পক্ষিরাজ, ভীত চকিত চোখে নীচের দিকে চাইতে লাগলেন রাজপুত্র। ভাবলেন, নীচেঐ অসীম অনন্ত সমুদ্রে পড়লে আর বাঁচবার কোনও আশাই নেই। প্রভুভক্ত পক্ষিরাজ রাজপুত্রের মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় শেষ নিশ্বাস নেবার আগে দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে পড়ল এসে ঐ সোনার অট্টালিকার ছাদে–।
চোখ চেয়ে দেখি, পড়ে গেছি ঘরের সিমেন্টের মেঝেয়। প্রথমটা বেশ অবাক হয়ে গেলাম, নজর পড়ল জামা কাপড়ের দিকে। পরনে শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়, গায়ে তালি দেওয়া জামা, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল। সব মনে পড়ে গেল। ‘কালপরিণয়’ ছবির বেকার দরিদ্র নায়ক মণীন্দ্রের রূপসজ্জায় শুটিং-এর অবসরে ম্যাডান স্টুডিওর মেক-আপ রুমে কাঠের বেঞ্চের উপর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে পড়ে গেছি কঠিন সিমেন্টের মেঝের উপর। ভাগ্যিস ঘরে কেউ ছিল না, নইলে ভীষণ লজ্জায় পড়তাম। ডানহাতের কনুইটায় বেশ চোট লেগেছিল। হাত বুলোতে বুলোতে আরশির সামনে দাঁড়ালাম। নিজের চেহারা দেখে হাসি পেল আমার। কোথায় পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র, আর কোথায় দারিদ্র্যের আঁতাকলে নিষ্পেষিত বেকার শিক্ষিত যুবক মণীন্দ্র! হোক, তবু তো নায়ক! কতক্ষণ আরশির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। শুটিং-এর ডাক পড়ল। সারা স্টুডিওটা জঞ্জালে ভর্তি, শুধু খানিকটা জায়গা চৌকো উঠোনের মতো সিমেন্ট করা। তার উপর ঠিক স্টেজের মতো মোটা কাপড়ের উপর রং দিয়ে আঁকা সিন কাঠের ফ্রেমে এঁটে চারদিকে পেরেক আর পিছনে সরু কাঠ দিয়ে ঐ সিমেন্টের মেঝের খানিকটা জায়গায় আটকে তৈরী হয়েছে ঘর। তিন দিকে সিনের দেওয়াল, একদিকে খোলা। উপরে সাদা কাপড় সামিয়ানার মতো টাঙিয়ে সিলিং। পরে শুনেছিলাম সিলিং নয়, রোদের কড়া আলো খানিকটা কমিয়ে দেবার জন্যই ওটার প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশি।
ঘরের মধ্যে টেবিল চেয়ার খাট আলমারি মায় দেওয়ালে ঠাকুর-দেবতার ছবি পর্যন্ত টাঙানো। টেবিলের উপর দু-তিনটে ওষুধের শিশি, ওষুধ খাওয়ার ছোট্ট গ্লাস। পাশে কাগজের উপর খানিকটা বেদানা ও দু-তিনটে কমলালেবু। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি নেই।
খাটের উপর কাঁথা-কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে আমার তিন চার বছরের ছেলে। মাথার কাছে আধময়লা একখানি শাড়ি পরে স্ত্রী সীতাদেবী একখানা পাখা হাতে বাতাস করছে ছেলেকে। এমনি সময় ঘরে ঢুকলাম আমি। ঐ শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়, গায়ে তালি দেওয়া জামা, মাথায় একরাশ তৈলহীন রুক্ষ চুলের বোঝা ও একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে আমি খাটের মাথার দিকে এসে দাঁড়ালাম। স্ত্রী পিছন ফিরে হাওয়া করছিলেন, প্রথমে দেখতে পাননি আমাকে। ছেলের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আজ কেমন আছে খোকা?’ তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়ে বিষণ্ণ মুখে আমার দিকে চেয়ে স্ত্রী বললেন, ‘দি সেইম, নো চেঞ্জ অফ টেম্পারেচর।’
বললাম, ওষুধটা ঠিকমতো খাচ্ছে তো?’
উত্তরে একটা খালি শিশি টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে আমার প্রায় নাকের উপর সেটা নেড়ে চেড়ে দেখিয়ে স্ত্রী বললেন, ইট ইজ এম্পটি সিল মর্নিং। বাট হোয়ার ইজ দি মানি টু ব্রিং ফ্রেশ মেডিসিন?
শিশিটা রেখে স্ত্রী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলেন। মাথা নেড়ে বললাম, নাঃ, কোথাও কিছু হল না। আমার মতো অভাগার চাকরি কোথাও জুটল না।
হঠাৎ জ্বরের ঘোরে ছেলেটা কেঁদে ওঠে। স্ত্রী তাড়াতাড়ি মাথার কাছে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করেন।
সিনটা হল এই। ক্লোজ-আপ, মিড শট, লং শট–এইভাবে ভাগ করে সিনটা নিতে প্রায় চারটে বাজল। চা খাওয়ার জন্য খানিকটা সময় ছুটি পাওয়া গেল।
এখানে একটা কথা বলে রাখি, স্ত্রী সীতাদেবী ফিরিঙ্গি মেয়ে হলেও ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলতে পারতেন। কিন্তু পরিচালক গাঙ্গুলীমশাই বললেন, না, তাতে এক্সপ্রেশন নষ্ট হবে। কাজেই সীতাদেবী ইংরেজিতেই ডায়ালগ বলতেন, আমি বাংলায়। আর ছোট ছেলেটা শুনেছিলাম কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের কোনো এক। মুসলমান অভিনেত্রীর ছেলে। সে আবার কড়া উর্দু ছাড়া কথা বলতে বা বুঝতে পারত না। রক্ষে যে তার কোনও সংলাপ ছিল না, খালি জ্বরের ঘোরে অচেতন হয়ে উঃ আঃ বলা ছাড়া। নইলে টকীর যুগ হলে ব্যাপারটা একবার ভাবুন তো! বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিতে ঐ সিনটা পর্দার উপর পড়লে আমাদের পারিবারিক দুঃখ দেখে লোকে কাদত, না হাসত!
নির্বাক যুগের আরও অনেকগুলো সুবিধা ছিল। প্রথমত, সিনারিও বা স্ক্রিপ্টের কোনও বালাই ছিল না। ছাপানো একখানা বই বা নাটক যা তোলবার জন্য মনোনীত হত, তাতে শুধু সংলাপ অংশ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে নিলেই সিনারিও হয়ে গেল। পরিচালক শুধু সিনটা বুঝিয়ে দিয়ে অভিনয় শিল্পীদের ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে ঐ লাল পেন্সিলের দাগকাটা লাইনগুলো আউড়ে যেতে বলতেন। কোনও অভিনেতার যদি কোনও লাইন আটকে যেত, অমনি স্টেজের মতো প্রম্পট করে বলে দেওয়া হত। সব চাইতে বড় কথা, অপচয় বলে কোন কিছু নির্বাক যুগে ছিল না। অভিনয় করতে করতে কোনো অভিনেতা যদি হাঁদারামের মতো হঠাৎ সংলাপ ভুলে পরিচালকের দিকে চেয়ে থাকতেন, তাতে তার লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কিছু ছিল না। পরিচালকমশাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ‘কাট’ বলে চিৎকার করে ক্যামেরা থামিয়ে দিতেন না। বরং উৎসাহ দিয়ে বলতেন, ‘ঠিক আছে, চালিয়ে যাও।’ ফিল্ম এডিট বা জোড়া লাগাবার সময় ক্যামেরা বা পরিচালকের দিকে হঠাৎ চেয়ে ফেলার ছবিটা কাচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে একটা জুতসই টাইটেল জুড়ে দেওয়া হত। ব্যস, সব দিক রক্ষে।
সব চাইতে নিরাপদ ও সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল ভূমিকা নির্বাচন। যেটা বর্তমান টকীর যুগে একটা মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ছবিতে। ধরুন আপনার চাই এমন একটি নায়িকা, যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত সেক্স অ্যাপিলে ভর্তি। কিন্তু কোথায় পাবেন তেমন নায়িকা? অনেক খুঁজে পেতে
যদিও বা একটি পেলেন, দেখলেন সেক্স যদিও তার আছে, সেটা সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিজের মধ্যেই চেপে রেখে দিয়েছে। দশজনের কাছে তার আবেদন পৌঁছে দেওয়া দূরে থাক, কণামাত্র আদায় করতে পরিচালক বেচারিকে মদনদেবের আপিল আদালতে মাথা খুঁড়ে মরতে হয়। শেষকালে তিতিবিরক্ত হয়ে দিলেন ঐ ভূমিকা কোনো নামকরা অভিনেত্রীকে, ঐ ভূমিকায় যাঁকে একদম মানায় না। আর সেক্স অ্যাপিল? কোন সে সুদূর অতীতে ওঁর সেক্স অ্যাপিলে যাদের দেহে-মনে শিহরণ জাগতো, তাদের অনেকেই আজ অ্যাপিলের বাইরে বসে নিশ্চিন্ত মনে নাতি-নাতনি নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছেন। কিন্তু তাতে কী হল? মেয়েদের একটা অদ্ভুত সাইকোলজি, তারা কিছুতেই বয়সের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে চান না। সব সময় পিছনে পড়ে থাকতে চান। ফলে হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে মেক-আপের ‘ মায়াজালে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টায় এমন সেক্স অ্যাপিল দেখাতে শুরু করেন, যার ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি বোম্বাইয়ের ছবিকেও লজ্জা দেয়। আর সত্যিকার রসিক দর্শক বিরক্তিতে ভু কুঞ্চিত করে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে ভবিষ্যতে বাংলা ছবি না দেখার সংকল্প করে বসেন। বাংলাদেশের নায়িকাদের সম্বন্ধে এই কথাটা বোধহয় নির্ভয়ে বলা চলে যে, যার নেই কিছু, তারই দেবার ব্যাকুলতা। যার আছে, হয় সে কৃপণ, নয়তো দেবার ক্ষমতাই নেই।
এই তো গেল ভলাপচুয়াস নায়িকার কথা। সাধারণ নায়িকার ব্যাপারেও ফ্যাসাদ একটুও কম নয়। সত্যিকার নায়িকা হবার যোগ্যতা বাংলা ছবিতে মাত্র দুতিনজন মেয়ের বেশি নেই। সব প্রোডিউসার মিলে তাদের নিয়েই কাড়াকাড়ি। ফলে এক একজন নায়িকা বারো-তেরোখানা ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মোটা টাকা আগাম নিয়ে বসে আছেন। শুটিং শুরু করে আপনি দেখলেন, মাসে দুতিন দিনের বেশি ডেট তিনি কিছুতেই দিতে পারছেন না। অগত্যা ছবির সময় ও খরচা দুই-ই বেড়ে গেল।
এইবার দৃষ্টিপাত করুন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে নির্বাক যুগের দিকে। যে কোনো জাতের ভিতর থেকে অতি সহজে নায়িকা নির্বাচন করে ফেলুন যেমনটি আপনার চাই। তারপর স্টুডিওতে নিয়ে এসে শাড়ি-রাউজ পরিয়ে ছবি তুলে নিন। যার যে ভাষা, সেই ভাষাতেই অভিনয় করে যাক, কোনও ক্ষতি নেই। বাংলা টাইটেল দিয়ে শুধু বুঝিয়ে দিন, কী সে বলছে। নির্বাক যুগে খুব কম বাঙালি মেয়ের নায়িকা হবার সৌভাগ্য হত। বেশীর ভাগ মেয়ে নেওয়া হত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাড়া থেকে। এ ছাড়া ইহুদি, জার্মান, ইতালিয়ান, মুসলমান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের মনোনীত করা হত। তখনকার যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রীরা, যথা–সীতা দেবী (মিস রেনি স্মিথ), পেশেন্স কুপার, ললিতা দেবী (মিস বনি বার্ড), সবিতা দেবী, ইন্দিরা দেবী (নির্বাক কপালকুণ্ডলা’ ছবিতে নাম ভূমিকায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন) এঁরা সবাই ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে। আরও একটি বিশেষ কারণে বাঙালি মেয়েদের পারতপক্ষে নেওয়া হত না। সেটা হল তাদের অত্যধিক জড়তা ও লজ্জা, যেটা অন্য জাতের মেয়েদের ছিলই না বলা চলে। আমি নিজে দেখেছি, অজ পাড়াগেঁয়ে গরীবের ঘরের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, কিন্তু তিনি কিছুতেই খালি গায়ে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরতে রাজি হলেন না, পরলেন ফরসা শাড়ি ব্লাউজ। তারপর অভিনয়। ধরুন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা প্রণয়-নিবিড় দৃশ্য। স্বামী বেচারী হয়তো আদর করে একটু কাছে টেনে নিতে চান,স্ত্রী কিন্তু কাঠ হয়ে সেই একহাত ব্যবধান থেকেই তোতা পাখির মতো বইয়ের কথাগুলো আউড়ে গেলেন। ফিরিঙ্গি মেয়েদের বেলায় ঠিক এর বিপরীত। শুধু বলে দিলেই হল যে, এটা প্রেমের বা রোমান্টিক সিন। তারপর বেচারী নায়কের প্রাণান্ত ব্যাপার।
আবার শুটিং-এর ডাক পড়ল। এবার দৃশ্যটি হচ্ছে, পরদিন সকালবেলা। ময়লা একটা গেঞ্জি গায়ে চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছি, ধীরে ধীরে স্ত্রী এসে পাশে দাঁড়ালেন। কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলাম। ইজ দেয়ার এনি হ্যাপি নিউজ?”
আমি–নাঃ, যাও বা একটা ছিল, পাঁচশ টাকা সিকিউরিটি জমা দিতে হবে।
স্ত্রী–ডোন্ট ওয়রি ডার্লিং। ভেরি সুন দি ক্লাউডস উইল পাস।
গোয়ালা দুধের তাগাদায় বাইরে কড়া নাড়ল। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। রোদ্দুর কমে গেছে বলে শুটিং এইখানেই শেষ করতে হল। পরিচালকমশাই বলে দিলেন, কাল আউটডোর শুটিং, সকাল ঠিক ছ’টায় গাড়ি যাবে। মেক কাপ তোলার কোনো বিশেষ বালাই নেই। কাপড়-চোপড় ছেড়ে বাড়ি চলে এলাম।
.
ভোরে উঠে স্নান সেরে গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছি, গাড়ি এল ঠিক সাতটায়। উঠতে যাব, দেখি গাড়ির ভিতর অর্ধেক জায়গা জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো রং-বেরঙের ঘুড়ি আর সুতো ভর্তি প্রকাণ্ড একটা লাটাই। গাঙ্গুলীমশায়ের অ্যাসিস্টেন্ট মুখার্জির দিকে চাইতেই সে বলল, ঐ জন্যই তো আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। বললাম, কিন্তু ব্যাপার কী?
সব কথায় একটু রহস্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দেওয়া মুখার্জির স্বভাব। বলল, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। একটু পরেই সব বুঝতে পারবে। অগত্যা কৌতূহল চেপে চুপচাপ বসে রইলাম। গাড়ি রসা রোড ধরে উত্তরমুখো চলতে শুরু করল। একটু পরেই হঠাৎ ডাইনে জাস্টিস দ্বারকানাথ রোডে ঢুকে পড়ে একটু গিয়েই নর্দান পার্কের আগে দাঁড়াল। কিছু দূরে আর একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে, আর তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন পরিচালক গাঙ্গুলীমশাই ও ক্যামেরাম্যান যতীন দাস। নামতে যাব, মুখার্জি হাত চেপে ধরে বলল, যেমন আছ অমনি চুপচাপ বসে থাকে। কিছু বলবার আগেই মুখার্জি গাড়ির দরজা খুলে নেমে তাড়াতাড়ি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিন জনে কী যেন পরামর্শ হল, তারপর গাঙ্গুলীমশাই দেখলাম আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন।
কাছে এসে বাইরে থেকে গাড়ির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে চুপিচুপি বললেন, ‘শোন ধীরাজ, সিনটা একটু মাথা খাঁটিয়ে চালাকি করে নিতে হবে।
একটা সিন নিতে কী এত মাথা খাটানো বা চালাকির দরকার, আমার অল্প কদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝে উঠতে পারলাম না। গাঙ্গুলীমশাই বললেন, ‘সিনটা নেওয়া হবে নর্দান পার্কের ভিতর। দৃশ্যটা হল, তোমার শ্বশুর জোর করে তোমার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে এসেছেন নিজের বাড়িতে। একমাত্র আদরের মেয়ে কিশোরী তোমার মতো অপদার্থের হাতে পড়ে চরম দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিন কাটাবে, এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। তুমি বাড়িতে এসে শুনলে, তোমার স্ত্রী-পুত্রকে জোর করে শ্বশুর নিয়ে গেছেন। তখন তুমি পাগলের মতো ছুটলে শ্বশুরবাড়িতে ওদের ফিরিয়ে আনতে। শ্বশুরমশায়ের অবস্থা খুব ভাল। প্রকাণ্ডঅট্টালিকা, গেটে লাঠি হাতে হিন্দুস্থানী দারোয়ান। দারোয়ানের উপর কড়া হুকুম ছিল, তাই তুমি ভিতরে ঢুকতে পারলে না। তারপর দু’তিন বছর কেটে গেছে। অনেকবার শ্বশুরবাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করেও কোনও ফল হয়নি। অনেক কষ্টে আশেপাশের লোকের কাছ থেকে খবর নিয়ে তুমি জানতে পারলে, রোজ বিকালে বেয়ারার সঙ্গে তোমার ছেলে এই পার্কে বেড়াতে আসে।
চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললাম, কিন্তু আমার ছেলে কোথায়, আর সাজবেই বা কে!
নর্দার্ন পার্কের ঠিক উত্তরে একটি প্রকাণ্ড বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, ছেলে ঐ বাড়ির।
বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু আগে যে ছেলেটিকে স্টুডিওয় দেখেছিলাম–
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, ভুলে যাচ্ছ কেন? তারপর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। এখন চাই একটি বড়সড় বছরসাতেকের ছেলে আর চেহারাটাও বেশ নাদুসনুদুস হওয়া চাই। ধনী দাদামশায়ের ওখানে ঘি-দুধ খেয়ে খেয়ে বেশ–
হঠাৎ চুপ করে উত্তর দিকের ঐ বাড়িটার দিকে চাইলেন গাঙ্গুলীমশাই। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি সদর দরজা খুলে একটি চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কী কথা হল গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে শুনতে পেলাম না। তক্ষুনি গাড়ির দরজা খুলে চকিতে একবার চারদিক দেখে নিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, চটকরে এর সঙ্গে ঐ বাড়িটায় ঢুকে পড়। কার বাড়ি, আমি কেন ঢুকব, এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি। একরকম ঠেলে দিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, যাও দেরি কোনো না, কেউ দেখে ফেললে মুশকিল হবে।
এদিকে আমার মুশকিলটা গাঙ্গুলীমশাই দেখলেন না। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-জামা পড়েএকমুখ দাড়ি আর রুক্ষ চুল নিয়ে অত বড়লোকের বাড়িতে ঢুকতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার দাখিল। শেষ চেষ্টার মতো ক্ষীণ আপত্তির সুরে তবুও একবার বললাম, আমি না হয় গাড়িতেই থাকি।
গর্জন করে উঠলেন গাঙ্গুলীমশাই, না, যা বলছি তাই কর।
রাশভারি লোক, তার উপর প্রকাণ্ড জোয়ান চেহারা। রাগলে ভয়ানক দেখায়। আর দ্বিরুক্তি করবার সাহস হল না। যা থাকে কপালে, চাকরটার সঙ্গে ঐ অজানা রহস্যপুরীতে ঢুকে পড়লাম।
ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ করে দিল চাকরটা। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে দেখি বেয়ারার পোশাক পরে মাথায় পাগড়ি চাপিয়ে সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছে মুখার্জি। সামনে আর একটা সোফায় বসে আছে একটি বছর হয় সাতের আবলু-গাবলু ছেলে, দেখলেই মনে হয় বড়লোকের ঘি-দুধ খাওয়া আদুরে ছেলে, বোকা-বোকা মুখখানা। ম্যাডান স্টুডিওর খাটে-শোওয়া, জ্বরে-ভোগা মুসলমান ছেলেটির তিন-চার বছরের মধ্যে এ রকম বিস্ময়কর পরিবর্তন একমাত্র সিনেমাতেই সম্ভব। দেখলাম ওর মেক-আপ হয়ে গেছে। প্রথমে মুখে খানিকটা ভেসলিন মাখিয়ে নিয়ে তার উপর পাউডার, তারপর ভুসো কালি দিয়ে চোখ আঁকা। সব শেষে আলতার শিশি থেকে একটুখানি আঙুলে লাগিয়ে নিয়ে ঠোঁটে দেওয়া। বলা বাহুল্য অধুনাবিখ্যাত ম্যাক্স ফ্যাক্টরের মেক-আপ, লিপস্টিক, ব্রাউন ব্ল্যাক পেন্সিল এসবের সৃষ্টি তখনও হয়নি। আর হলেও আমেরিকা থেকে সুদূর কলকাতায় সবেধন নীলমণি ম্যাডান স্টুডিওতে, তার অস্তিত্ব তখন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। মেক-মাপম্যান আসেনি, মুখার্জি ছেলেটিকে মেক-আপ করে দিয়েছে। ছেলেটির কিছুদূরে ঈষৎ অন্ধকারে আর একখানা সোফায় দেখলাম ছোট ছেলেটির বৃহৎ সংস্করণ প্রিয়দর্শন একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ভদ্রলোক বসে বসে পা দোলাচ্ছেন আর পরম তৃপ্তিতে গড়গড়া টানছেন। মুখার্জি আলাপ করিয়ে দিল, ধীরাজ, ইনিই এই বাড়ি আর এই ছেলেটির মালিক, নাম শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া স্টেটের ছোট তরফের বড়বাবু, আর এটি ওঁরই ছেলে শ্রীমান দীপ্তেন সান্যাল। সিনেমার ছোঁয়াচ লেগে কিনা জানিনা, পরবর্তী জীবনে এরা দুজনেই স্বনামধন্য।সুধীরবাবুঅধুনা বিখ্যাত প্রচার সচিব ও শ্রীমান দীপ্তেন ‘অচলপত্রের মাধ্যমে বিখ্যাত।
পরস্পর নমস্কারান্তে বসতে যাব, কানে এল, কামাননি কদ্দিন? বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম, আজ্ঞে?
তেমনি গভীরভাবে গড়গড়া টানতে টানতে সুধীরবাবু বললেন, ‘দাড়ি-গোঁফ কামাননি কতদিন হল?
বললাম, তা প্রায় মাস-দুই হবে।
–তা ওরকম উজবুকের মতো একগাল দাড়ি-গোঁফ আর মাথায় একঝুড়ি রুক্ষ চুলের বোঝা নিয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে মেক-আপের চুল দাড়ি নিলেই তো হয়।
মনে মনে রেগে গেলাম। প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতেই ভদ্রলোক এমন মেজাজে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন, যেন উনি মনিব আর আমি ওঁর খাস তালুকের প্রজা। উত্তর দেব কিনা ভাবছি, প্রাণখোলা হাসির আওয়াজে মুখ তুলে চেয়ে দেখি গড়গড়ার নল হাতে ভঁড়ি দুলিয়ে সোফায় বসে হাসছেন সুধীরবাবু। চোখে চোখ পড়তেই বললেন, ‘রাগ কোরো না ভাই, এটা আমার একটা বিশেষ দোষ। চেষ্টা করেও আমি বেশিক্ষণ গম্ভীর হতে পারিনে। সেইজন্য দেখ না, জমিদারী দেখাশোনা করে ছোট ভাই। সে বেশ গম্ভীর আর রাশভারি ছেলে। আর আমি সেই টাকায় তোফা খেয়েদেয়ে আচ্ছা দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি।
সত্যিই ভাল লাগল সুধীরবাবুকে। বড়লোক হয়েও এমন সহজ সাদাসিধে রসিক লোক কমই দেখেছি। মনের মেঘ কেটে গেল। বললাম, মেক-আপ সম্বন্ধে কী বলছিলেন?
–ও হো হো, এই দেখ আসল কথাটাই ভুলে গেছি। বলছিলাম যে, অত কষ্ট করে দাড়ি না রেখে তৈরি করে নিলেই তো হয়।
বললাম, আমাদের ছবির এখন যাকে বলে শৈশবাবস্থা। মেক-আপ জিনিসটার আইডিয়াই ভাল করে নেই। যা দু-একখানা ছবি দেখেছি, তাতে পরচুলো আর তৈরি দাড়ির যা নমুনা দেখেছি, তার চেয়ে কষ্ট করে দাড়ি রাখা অনেক ভাল। আমাদের এই আলোচনার মধ্যেই একটি বছর-চব্বিশের ফরসা মহিলা এসে সুধীরবাবুর কাছে দাঁড়ালেন। পরনে লাল পাড় গরদের শাড়ি, এলো চুল। সৌম্য স্নিগ্ধ মুখে তৃপ্তির হাসি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। বুঝলাম সদ্য পূজার ঘর থেকে আসছেন। সুধীরবাবু বললেন, ইনি হলেন এই বাড়ির যথার্থ কী। শুধু বাড়ি কেন, এ বাড়িতে যে কটি প্রাণী বাস করে তাদেরও, ইনডিং মী, ইনি হচ্ছেন–
বললাম, বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললাম, নমস্কার বৌদি।
সেদিনের সেই সামান্য শুটিংকে উপলক্ষ করে এই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম পরবর্তীকালে তা গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আজও তা অটুট আছে। শুধু ছন্দপতনের মতো সাত বছর আগে বৌদির অকালমৃত্যু একটু বিষাদের ছায়া এনে দেয়।
নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বৌদি বললেন, বসুন, বসুন। আজ আপনাদের শুটিং দেখব, কখনো দেখিনি। ওমা, কেন্দুধনের মেক-আপ হয়ে গেছে দেখছি।
শ্রীমান দীপ্তেনের ডাকনাম কে বা কেলো। বাপ-মায়ের চেয়ে গায়ের রং বেশ দু তিন ডিগ্রী কম বলে, না অন্য কারণে ঠিক বলতে পারব না।
আমার দিকে ফিরে বৌদি বললেন, ও কিন্তু ভীষণ নার্ভাস। শেষকালে আপনাদের ছবি না নষ্ট করে দেয়।
প্রায় কাঁদকাঁদ সুরে কেলু বলে উঠল, তুমি কিন্তু কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে মা, নইলে আমি ছবিতে প্লে করব না।
চৌকশ মুখার্জি অনেক বোঝাল, কোনো ফল হল না। অগত্যা ঠিক হল শুটিং-এর সময় সামনের পার্কে কেলোর সামনে, মানে ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে, বৌদি দাঁড়িয়ে থাকবেন।
মুখার্জি আমায় দৃশ্যটা যা বুঝিয়ে দিল তা হল এই, আমার শ্বশুরবাড়ির বেয়ারার সঙ্গে ছেলে রোজ বিকালে পার্কে খেলা করতে আসে। ছেলেবেলা থেকেই ঘুড়ি আর লাটাইয়ের উপর ওর অদম্য ঝোঁক। তাই অনেক কষ্টে পয়সা যোগাড় করে তা দিয়ে কয়েকখানা ঘুড়ি আর লাটাই কিনে চোরের মতো ছেলের সঙ্গে পার্কে দেখা করতে এসেছি আমি। গাড়ির মধ্যে ঘুড়ি লাটাই-এর রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হল। একটা জিনিস তখনও পরিষ্কার হয়নি। বললাম, ছবি তুলবে, তা এত লুকোচুরি হাশহাশ কেন?
বেয়ারার পোশাকে বেমানান হলেও বিজ্ঞের হাসি হেসে মুখার্জি বলল, ভাই ধীরাজ, মাত্র কদিন এ লাইনে এসেছ তাই বুঝতে পারছ না, আমি আর গাঙ্গুলীমশাই কত মাথা খাঁটিয়ে এ সিনটা নেবার ব্যবস্থা করেছি। শোন, যদি পার্কে প্রকাশ্যে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তুলতে শুরু করি, দেখতে দেখতে ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে যাবে আর সেই অগুনতি জনতাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত ছবি তোলা অসম্ভব। এই সিনটা হলো বইয়ের মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্ট্যান্ট ও ইমোশনাল সিন। যাক, তোমায় যা করতে হবে শোন। গাড়ি করে আমরা তোমায় পার্কের দক্ষিণ দিকের গেটের কাছে নামিয়ে দেব। ছেলেটি উত্তরের গেটের কাছে ফুটবল নিয়ে খেলা করছে। ফুটবল! ফুটবল আমি খুব ভাল খেলতে পারি, না মা? বুঝলাম কেলুর একমাত্র সাক্ষী ও সমঝদার হলো মা।
মুখার্জি বলল, দক্ষিণ দিকের গেট দিয়ে ঢুকে চারদিকে তুমি খুঁজে দেখছো তোমার ছেলেকে। হাতে রয়েছে দুতিনখানা রঙিন ঘুড়ি আর সুতো ভর্তি লাটাই।
সবে এসে যাওয়া ঘুমের মাঝখানে ছারপোকার কামড়ের মতো কুটকুট করে বলে উঠল কেলো, ঘুড়ি লাটাই সব আমায় দিয়ে দেবে তো মা?
বিরক্ত হয়ে বৌদি ধমকে উঠলেন, আঃ, সব কথায় কথা কইতে তোমায় না মানা করেছি কে?
মুখার্জি বলে চলল, ঘুড়ি আর লাটাই-এর লোভ দেখিয়ে ওকে নিয়ে বসবে তুমি উত্তর দিকের পাঁচিলের গা ঘেঁষে যে কাঠের বেঞ্চিখানা পাতা রয়েছে তার উপর।
কৌতূহল বেশ বেড়ে গিয়েছিল। বললাম, তারপর মুখুজ্যে?
সিনেমা সম্বন্ধে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি জাহির করার এরকম সুযোগ ছাড়তে মুখার্জি মোটই রাজি নয়। ঘরসুদ্ধ সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুরু করল, তারপর? তারপর ঐ বেঞ্চিতে বসে খোকার হাতে ঘুড়ি লাটাই সব দিয়ে ওকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বলবে, খোকা, তুমিও যেন আমার মতো পলকা সুতোয় ঘুড়ি উড়িও না বাবা। ঠিক এমনি সময় দূর থেকে খোকার উড়ে বেয়ারা, মানে আমি, দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে খোকার হাত থেকে ঘুড়ি লাটাই ছুঁড়ে ফেলে দেবো মাটিতে। তারপর তোমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে খোকাকে কোলে করে বাড়ি চলে যাব।
আর ফুটবল? বা রে, ফুটবলটা ফেলে যাব নাকি? অবাক হয়ে বলে উঠল কেলো।
সবাই হেসে ফেললাম। মুখুজ্যে বলল, সত্যিই খোকা আমার একটা ভুল ধরেছে। ফুটবলটা মাটি থেকে আমিই কুড়িয়ে নিয়ে যাব।
দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দিতেই দেখলাম স্টুডিওর গাড়ির ড্রাইভার রামবিলাস। মুখুজ্যেকে চুপি চুপি বলল, ধীরাজবাবুকে গাঙ্গুলীমশাই ডাকছেন।
রামবিলাস চলে যেতেই দরজা ঈষৎ ফাঁক করে উটের মতো গলা বাড়িয়ে মুখুজ্যে বাইরের রাস্তার এধার-ওধার দেখে নিয়ে আমায় বলল, যাও, চট করে গাড়িতে উঠে পড়, রাস্তা একদম ফাঁকা।
কোনো দিকে না চেয়ে একরকম ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। পিছনের সীটে ঘুড়ি লাটাইয়ের মধ্যে একরকম লুকিয়ে বসে আছেন গাঙ্গুলীমশাই, আর ড্রাইভারের সীটের এক পাশে হাতে ঘোরানো ডেবরি ক্যামেরা নিয়ে সামনের কাঁচ তুলে রেডী হয়ে বসে আছে ক্যামেরাম্যান যতীন দাস। গাড়ি ঘুরে চললো নর্দার্ন পার্কের দক্ষিণ দিকের গেটমুখো। গাঙ্গুলীমশাই বললেন, মুখুজ্যের কাছে সিনটা সব বুঝে নিয়েছে তো? সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। দক্ষিণ গেটের একটু দূরে এসে গাড়ি থামলো। দুতিনখানা ঘুড়ি আর লাটাইটা আমার হাতে দিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, চারদিক দেখে নাও আগে। লোকজন বেশি থাকলে নেমো না।
বেলা প্রায় এগারোটা, পথ জনবিরল। গাড়ি থেকে নেমে পার্কে ঢুকে পড়লাম। আমাকে ফলো করে গাড়িখানা আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো পার্কের গা ঘেঁষে। বুঝলাম, যতীন ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। দু-চারজন চাকর-বেয়ারা ক্লাসের লোক আর কতকগুলো স্কুল-পালানো ডানপিটে ছেলে ছাড়া পার্কে বিশেষ লোকজন নজরে পড়ল না। ছেলের খোঁজে ওদেরই মধ্যে দিয়ে চারদিক চাইতে চাইতে ঘুড়ি লাটাই হাতে এগিয়ে চলেছি। পার্কের মাঝ বরাবর গিয়ে উত্তর দিকে চেয়ে দেখি কেলুধন ওর সমবয়সী চার-পাঁচটি ছেলের সঙ্গে দিব্বি ফুটবল খেলতে শুরু করে দিয়েছে। কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন বৌদি, আর বেশ খানিকটা দূরে দুতিনটে চাকরের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে মুখুজ্যে।
বেশ একটু উৎসাহের মাথায় সামনে এগিয়ে গেলাম যেখানে কেলুরা ফুটবল খেলছে। একটু দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলটাকে হাতে তুলে নিতেই ছেলেগুলো ভয়ে ভয়ে আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। কোনো কথা না বলে খপ করে কেলুর একখানা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম পূর্বনির্দিষ্ট বেঞ্চির দিকে। কেলু শুধু বলে চলেছে, বা রে, ফুটবলটা নিয়ে নিলে, ঘুড়ি লাটাই দাও!
কোনো জবাব না দিয়ে বেঞ্চির উপর দুজনে বসলাম। তারপর ফুটবলটা মাটিতে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ঘুড়ি লাটাই কেলুর হাতে দিলাম। মুখ দেখে বোঝা গেল ও বিশেষ খুশি হয়নি। বারবার লোলুপ দৃষ্টিতে নীচে ফুটবলটার দিকে দেখতে লাগল। এই অবসরে আড়চোখে দেখে নিলাম ক্যামেরাসুদ্ধ গাড়িটা এসে গেছে উত্তরের রেলিং ঘেঁষে একেবারে আমাদের সামনে। মহা উৎসাহে যতীন হাতল ঘুরিয়ে চলেছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। কেলোকে হঠাৎ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বেশ ইমোশন দিয়ে বলে উঠলাম খোকা, তুমি যেন আমার মতো পলকা সুতোয় ঘুড়ি উড়িও না বাবা।
শেষের কথাটা বলেছি কি বলিনি, দড়াম করে পড়লো এক লাঠি আমার পিঠে। যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি পাঁচ ছজন জোয়ান ছেলে লাঠি হান্টার আর হাতের আস্তিন গুটিয়ে ঘুষি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার ঠিক পিছনে।
একজন বলল, জানিস র, ব্যাটা যখনই ঘুড়ি লাটাই হাতে নিয়ে চোরের মতো চাইতে চাইতে পার্কে ঢুকেছে, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা বার করে সবাইকে খবর দিয়ে এসেছি। ওরা এল বলে।
কিছু না বুঝতে পেরে অপরাধীর মতো মুখ করে ভয়ে ভয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ওদের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে ভিড় বেড়ে উঠল। একটা ষণ্ডমার্কা ছেলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমার চুলের মুঠো ধরে বেঞ্চি থেকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর সবলে গালে এক চড় মেরে বলল, রোজ রোজ ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,। আজ ব্যাটাকে মেরেই ফেলব।
মেরেই ফেলতো যদি না হঠাৎ ভিড় ঠেলে মুখুজ্যে এসে আমায় আড়াল করে দাঁড়াত। মুখুজ্যে ওদের একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, ব্যাপার কী? আপনারা হঠাৎ একে মারধোর করছেন কেন?
ওদেরই মধ্যে একটু বেশি বয়সের একটা ছেলে ভেংচি কেটে বলে উঠল, তুই ব্যাটা উড়ে মোড়লি করতে এলি কেন? বড়লোকের বাড়ির বেয়ারা-মেজাজ দেখ না!
তাড়াতাড়ি মাথার পাগড়িটা খুলে মুখুজ্যে বেশ নরম সুরে বলল, ভাই, বেয়ারা আমি নই, সেজেছি।
আর যায় কোথায়! সবাই একসঙ্গে হৈহৈ করে উঠলো, দেখলি পানু? আমি বলেছি ওরা একা আসে না, দলবল নিয়ে আসে।
দুতিনটে ছেলে একরকম মুখুজ্যেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমার শতচ্ছিন্ন তালি দেওয়া জামাটার কলার চেপে ধরল। ঠিক এমনি সময়ে ত্রাণকর্তার মতো দামী গরম স্যুট পরা, লম্বা, সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘকায় গাঙ্গুলীমশাই দুহাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের দলকে জিজ্ঞাসা করলেন, হয়েছে কী, এত ভিড় কেন?
প্রায় দুতিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, আপনিই বিচার করুন তো মশাই, আজ দুতিন দিন ধরে আমাদের পাড়ায় ছেলেধরার উৎপাত শুরু হয়েছে। দুটো ছেলে এই পার্ক থেকে চুরি গেছে। একটা পাওয়া গেছে, আরেকটার কোনো পাত্তাই নেই। তাই আমরা পাড়ার ছেলেরা ঠিক করেছি পালা করে পাহারা দেব। দেখি ছেলেধরার উৎপাত বন্ধ করতে পারি কিনা। আজও সকাল থেকে ঘরের খড়খড়ি তুলে পন্টু। সাতটা থেকে ডিউটি দিচ্ছিল। হঠাৎ ও দেখে ছেলে ভোলাবার জন্য দুতিনখানা রঙিন ঘুড়ি ও লাটাই নিয়ে এই ব্যাটা চোরের মতো চারদিকে চাইতে চাইতে পার্কে ঢুকে যেখানটায় ছেলেগুলো ফুটবল খেলছে, সেইদিকে এগোচ্ছে। ব্যস, ও তখনই সাইকেলে করে দলের সবাইকে খবরটা দিয়ে দেয়। আজ যখন হাতেনাতে ধরেছি তখন আগে মেরে ব্যাটাকে আধমরা করব, তারপর পুলিশে দেব।
কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হৈহৈ করে সবাই মারবার জন্য এগিয়ে এল। হাত তুলে থামিয়ে দিলেন গাঙ্গুলীমশাই। তারপর বললেন, তোমাদের ভুলটা ভেঙে দিতে আমার সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু না দিয়েও উপায় নেই। যাকে তোমরা ছেলেধরা মনে করে মারধোর করছ, সে হচ্ছে আমার কালপরিণয় ছবির নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য। ছবিতে ঠিক এমনি একটা ঘটনা আছে, তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি সিনটা নিচ্ছিলাম, যাতে খুব ন্যাচারাল হয়। সিনটা আমার প্রায় তোলা হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলেই–
পাশ থেকে মুখুজ্যে বলল, আর এখানে নয়। বাকি সিনটা স্টুডিওতে একটা বেঞ্চি দিয়ে ক্লোজ শটে নিলেই চলবে। চলুন যাওয়া যাক।
ছেলের দলের সন্দেহ তখনো পুরোপুরি যায়নি বুঝতে পেরে ক্যামেরাসুদ্ধ যতীনকে ডেকে ওদের দেখিয়ে সমস্ত সিনটা বলে গেলেন।
হঠাৎ মুখুজ্যে বলে উঠল, কেলু? কেলো কোথায়? আর ঘুড়ি, লাটাই, ফুটবল এগুলোই বা গেল কোথায়?
চেয়ে দেখলাম নিজেদের বাড়ির বোয়াকে দাঁড়িয়ে ফুটবল, ঘুড়ি, সাটাই, সব দুহাতে জড়িয়ে ধরে মিটমিট করে হাসছে কেলুধন, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সুধীর ও বৌদি।
বেশ বুঝতে পারলাম ছেলের দল খুব নিরুৎসাহ হয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে আমায় ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে পথ করে ভিড় ঠেলে সবাই গাড়িতে গিয়ে বসলাম। স্টুডিওতে মালপত্র ক্যামেরা নামিয়ে গাঙ্গুলীমশাইকে বাড়িতে ছেড়ে গাড়ি আমার বাড়ির কাছে এলে নামতে নামতে মুখুজ্যেকে বললাম, তুমি আর গাঙ্গুলীমশাই অনেক মাথা খাঁটিয়ে যে ফন্দিটা করেছিলে, তাতে আমার পৈতৃক মাথাটা যেতে বসেছিল।
কিছুমাত্র দুঃখিত বা লজ্জিত না হয়ে মুখুজ্যে জবাব দিল, ছবির নায়কের পক্ষে এসব কিছুই নয়, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।
কোনো উত্তর দেবার আগেই দেখি গাড়ি বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। অবাক হয়ে চলমান গাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।
.
কালপরিণয় ছবির আর একদিনের আউটডোর শুটিং-এর কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। দৃশ্যটা হল, সারাদিন চাকরির চেষ্টায় এ-আফিস সে-আফিস ঘুরে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে বাড়িতে এসে শুনি, আমার স্ত্রী-পুত্রকে ধনী শ্বশুর একরকম জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তখনই হেঁটে চললাম শ্বশুরবাড়ি। শেয়ালদার মোড় থেকে সোজা পশ্চিমমুখো হ্যারিসন রোড ধরে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত ঐভাবে জোরে হেঁটে যেতে হবে।
মুখার্জি বলে দিল, তুমি কোনো দিকে না চেয়ে সোজা ভিড় ঠেলে ডান দিকের ফুটপাথ দিয়ে চলে যাবে, আমরা গাড়ির মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথের গা ঘেঁষে তোমায় ফলো করে যাব। কেউ জানতেই পারবে না যে, ছবি তোলা হচ্ছে।
সেদিনের পিঠের ব্যথাটা তখনও মিলিয়ে যায়নি। বললাম, মুখুজ্যে—
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখুজ্যে বলল, সেদিনকার দৃশ্য আর আজকের দৃশ্যে অনেক তফাত। সেদিনকার দৃশ্যটা তোলায় বিপদ ছিল। আজ শুধু ভিড় ঠেলে রেগে জোরে জোরে হেঁটে যাওয়া।
অগত্যা তাই ঠিক হল। একে ঐ রকম পাগলের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ, তার উপর রেগেছি। দুহাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি, দুএকজন বিরক্ত হয়ে বেশ শক্ত দুচার কথা শুনিয়েও দিল। কোনো দিকে ক্রুক্ষেপ না করে শুধু সামনে এগিয়ে চলা।
আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হতেই কানে এল, কে, ধীরাজ না?
মনে মনে প্রমাদ গণলাম। কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এবার বেশ কাছ থেকেই প্রশ্ন হল, ঠিক দুপুরবেলায় এমন ভাবে কোথায় চলেছিস?
কোনও দিকেই না চেয়ে জবাব দিলাম, শ্বশুরবাড়ি।
–শশুরবাড়ি! তুই আবার বিয়ে করলি কবে? বেশ বাবা, তিন মাস কলকাতায় ছিলুম না, এই ফাঁকে বিয়ে করে আমাদের ফাঁকি দিলি তো?
প্রশ্নকর্তা আমার সহপাঠী নির্মল বোস। মাসতিনেক হল এলাহাবাদে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। দিন দুই হল কলকাতায় ফিরেছে। নির্মল নাছোড়বান্দা। বেঁটে লোক, আমার সঙ্গে অত জোরে হেঁটে পারবে কেন? একরকম ছুটেই সঙ্গে সঙ্গে চলল।–কই, জবাব দিচ্ছিস না কেন?
–কী জবাব দেব? বড়লোক শশুর জোর করে আমার স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে। গেছে। সেইখানে একটা হেস্তনেস্ত করতে যাচ্ছি।
বিস্ময়ে দুচোখ কপালে তুলে হাত ধরে আমায় একরকম জোর করে দাঁড় করিয়ে নির্মল বলল, ছেলে! তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে তোর ছেলে হয়েছে? গাঁজা-টাজা খাচ্ছিস নাকি? তা, চেহারাখানা যা করেছিস, তাতে তো তাই মনে হয়।
কলেজ স্ট্রীটের মোড় তখনো খানিকটা বাকি আছে, হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম, আজ গাঙ্গুলীমশাই আর মুখুজ্যের কাছে নির্ঘাত বকুনি খাব। দৃশ্যটা এভাবে নষ্ট হয়ে গেল!
সামনের গাড়ি থেকে গাঙ্গুলীমশাই আর মুখুজ্যে হাসতে হাসতে নেমে এলেন। আমি তো অবাক। গাঙ্গুলীমশাই কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বললেন, ভেরি গুড! আজকের সিনটা খুব ভাল হয়েছে। আমি এতটা আশা করিনি।
অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু আমার এই বন্ধুটি প্রায় সারা পথটা প্রশ্ন করতে করতে এসেছে।
মুখুজ্যে বলল, সেটা আরও ভাল হয়েছে। তোমরা যদি ক্যামেরার দিকে চেয়ে ফেলতে তাহলে সব মাটি হয়ে যেত। ছবির নায়ক মণীন্দ্র কলেজে-পড়া শিক্ষিত ছেলে। তাকে রাস্তা দিয়ে ওভাবে পাগলের মতো হাঁটতে দেখে তার দু-একজন সহপাঠী বা বন্ধুর প্রশ্ন করাটা স্বাভাবিক। বরং পাবলিক কারুর সঙ্গে দেখা না হলে সেইটেই আনন্যাচারেল হতো। বাঁচা গেল। বেচারী নির্মল! সব শুনে সে এমন বোকা বোকা চোখে আমাদের দিকে চেয়ে রইল যে, না হেসে পারলাম না।
এই ঘটনার পর মাসখানেক কী কারণে জানি না কালপরিণয় ছবির শুটিং বন্ধ ছিল। এরই মধ্যে একদিন ৫ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট, নিউ সিনেমার সামনে ম্যাডান কোম্পানির আফিসে গিয়ে শুনি, জার্মানি থেকে ফিল্ম শিল্পে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছেন মধু বোস। ম্যাডান কোম্পানির হয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প মানভঞ্জন-এর চিত্ররূপ দেবেন। কিন্তু নায়ক গোপীনাথের ভূমিকা কাকে দেবেন, এই নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছেন। আফিসের সর্বময় কর্তা রুস্তমজী মধু বোসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, আমিই নায়ক গোপীনাথের ভূমিকায় মনোনীত হলাম। আমার বিপরীতে নায়িকা গিরিবালার জন্যে নির্বাচন করা হল একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে, নাম মিস বনি বার্ড। বাংলা নাম, অর্থাৎ ছায়াচিত্রের নাম হল ললিতা দেবী।
মহা সমারোহে সিনারিও লেখবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। দেখলাম, মধু বোস ছাপার বই-এ ডায়ালগের নীচে লাল পেন্সিলে দাগ টেনে সিনারিও করার পক্ষপাতী নন। সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে সিনারিও শেষ হয়ে গেল, ডাক পড়ল রিহার্সালের। প্রথমেই চমকে উঠলাম, নির্বাক ছবিতে আবার রিহার্সাল কী রে বাবা! জার্মানি-ফেরতা ডিরেক্টর, প্রতিবাদ করবে কে? রোজ রিহার্সালে যাই, বেলা চারটে পাঁচটা পর্যন্ত বসে বসে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর সংলাপ আউড়ে, সিনের পর দিন রিহার্সাল দিয়ে, চা-টোস্ট-ডিমের সদ্ব্যবহার করে বাড়ি চলে আসি। হঠাৎ শুনি, ছবির নাম পাল্টে গেছে, নায়িকার নাম অনুসারে ছবির নাম হয়েছে গিরিবালা।
একদিন সন্ধ্যেবেলা রিহার্সাল দিয়ে ফিরতেই বাবা ডেকে পাঠালেন। কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি বাবা বললেন, ধীউ বাবা, দুখানা ভাল ছবিতে তুমি নায়কের ভূমিকা পেয়েছ। ভাল কথা। কিন্তু ওঁরা এর জন্যে পারিশ্রমিক কী দেবেন না দেবেন, সে সম্বন্ধে কোনও কথা হয়েছে কি?
ভারি লজ্জা পেলাম। সত্যি, নায়ক হবার স্বপ্নে এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওদিকটার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।
বললাম, না বাবা, কালপরিণয় ছবিতে নামবার সময় টাকার প্রশ্নই ওঠেনি। কেননা, আমি ভাবতেই পারিনি যে, অত সহজে মুলান্ড সাহেব আমার রেজিগনেশান অ্যাকসেপ্ট করবেন। তারপর গিরিবালা ছবিটাও হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। আমি কালই গাঙ্গুলীমশাই আর মিঃ বোসকে জিজ্ঞাসা করবো।
পরদিন আফিস, মানে ৫ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে যেতেই গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রুস্তমজী সাহেবের কাঁচের পার্টিশন দেওয়া ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। নমস্কার করে আমার বক্তব্য বিষয় তার কাছে নিবেদন করলাম।
একটু চুপ করে থেকে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, শোনো ধীরাজ, একটা কথা তোমার জানা দরকার। ছবিতে নেমেই নায়কের চান্স পাওয়াটা ভাগ্যের কথা, পারিশ্রমিকের প্রশ্নই ওঠে না। বহু সুশ্রী বড়লোকের ছেলে নায়কের জন্য লালায়িত, এমন কি তার জন্য বেশ কিছু আমাকে অফারও করেছে। সেসব চিঠিপত্তর, ফটো আমার আফিস ঘরের ড্রয়ারের মধ্যে রয়েছে। দেখতে চাও?
বেশ একটু দমে গিয়ে বললাম, না না, আপনার কথাটাই যথেষ্ট।
–তবুও তোমার সব কথা মুখুজ্যের কাছে শুনে আমি সমস্ত ছবিটার জন্যে তোমার পারিশ্রমিক ঠিক করে দিয়েছি দেড় শ টাকা। এইমাত্র সাহেবের সঙ্গে সেই কথাই পাকা করে এলাম।
কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। এত বড় বিরাট চেহারার মতো হৃদয়টাও বড় না হলে মানুষ সত্যিই বড় হতে পারে না।
পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বের করে পেন্সিল দিয়ে তাতে কী লিখলেন গাঙ্গুলীমশাই, তারপর কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এইটে নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে গেলেই তিনি তোমায় পঞ্চাশ টাকা দেবেন। পরে দরকার হলে কিছু কিছু করে নিও।
দেহে মনে একরকম লাফাতে লাফাতে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে রিহার্সাল রুমে ঢুকে পড়লাম। মধু বোস তখনও এসে পৌঁছননি।
ঘর ভর্তি অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল, তারই মধ্যে দিব্যি আরামে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন অধুনা বিখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র। একটু অবাক হয়ে বললাম, নরেশদা আপনি!
এখানে বলে রাখা দরকার, কালপরিণয় ছবিতে একটি দুর্ধর্ষ ভিলেন চরিত্রে রূপ দিচ্ছিলেন নরেশদা। এবং অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় শিক্ষার ভারও ছিল নরেশদার উপর। আমার অভিনয় শিক্ষার হাতেখড়ি নরেশদার কাছ থেকেই।
জবাব না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগলেন নরেশদা। একটু পরে ঘরসুদ্ধ সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন, ধীরাজ, তুমি মদ খাও?
স্তম্ভিত, বজ্রাহত হয়ে গেলাম। এ কী প্রশ্ন! মদ খাওয়া দুরের কথা, যারা খায় তাদের পর্যন্ত মনে মনে ঘৃণা করি তখন। সব জেনেও এ কী প্রশ্ন করলেন নরেশদা? জবাব দিলাম না, দেবারও কিছু ছিল না।
আবার প্রশ্ন, অস্থানে কুস্থানে, মানে মেয়েমানুষের বাড়ি যাওয়া-টাওয়া অভ্যাস আছে?
গুরুর মতো শ্রদ্ধা ও মান্য করি নরেশদাকে। তাছাড়া, অল্প কয়েকদিনের মাত্র আলাপ, ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি তখন। সত্যিই ব্যথা পেলাম।
আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বোধহয় নরেশদা কাছে ডেকে বসালেন। তারপর বললেন, না হে, অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। গিরিবালা ছবিতে আমাকে মিঃ বোস দিয়েছেন তোমার একটি বন্ধুর ভূমিকা। আমার একমাত্র কাজ হলো তোমাকে মদ খেতে শেখান, মেয়েমানুষের বাড়ি নিয়ে যাওয়া আর রাত্রে বাড়ি ফিরতে না দেওয়া। যে সৎ গুণগুলি না থাকলে সমাজে বড়লোক কানে বলে পরিচয় দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।
এতক্ষণে নরেশদাকে বোঝা গেল। গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং আমার কালপরিণয় ছবির পারিশ্রমিকের কথা সব নরেশদাকে বললাম। শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন নরেশদা। বললেন, পারিশ্রমিকটা একটু কম হয়ে গেল না? দেড় বছরে মাত্র দেড়শ টাকা বাধা দিয়ে বললাম, দেড় বছর। কালপরিণয় ছবি শেষ হতে দেড় বছর লাগবে?
হ্যাঁ, যতদিন না গিরিবালা শেষ হয়, ধর মাসতিনেক, গাঙ্গুলীমশায়ের শুটিং বন্ধ থাকবে। তারপর শুরু হয়ে শেষ হতে তাও তিন-চার মাস।হরে দরে সেই দেড় বছরের ধাক্কা।
বললাম, আচ্ছা নরেশদা, এই যে গিরিবালা ছবিতে মিঃ বোস আমাকে নিয়েছেন, এর জন্যও কিছু দেবেন তো?
নিশ্চয়ই–তুমি মিঃ বোসের সঙ্গে কথা বলনি?
বললাম, না।
একটু চুপ করে থেকে নরেশদা বললেন, আজই কথা বলে নিও। আর যদি পারমানেন্ট, মানে মাস-মাইনে করে নিতে পার তো কথাই নেই। এই দ্যাখো না, তোফা মাসের তিন তারিখে এসে মাইনে নিয়ে যাই। ছবি তোমার দেড় বছরে তোক আর দু বছরে হোক, বয়েই গেল।
স্বপ্নের সেই সোনার পাহাড়টা চোখের সামনে ভেসে উঠতে না উঠতেই কোথায় মিলিয়ে গেল। বললাম, কাকে বলবো নরেশদা?
–কেন, গাঙ্গুলীমশাই ইচ্ছে করলে অনায়াসেই করে দিতে পারেন। উনি তো শুধু পরিচালক নন, এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসের (অধুনা মিনার্ভা থিয়েটার) ম্যানেজার। তাছাড়া, মনিবরা কোম্পানির আরও অনেক জটিল বিষয়ে ওঁর পরামর্শ নিয়ে থাকেন।
পরিচালক মধু বোস ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে সিল্কের শাড়ি পরিহিতা অপূর্ব সুন্দরী একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে। বুঝলাম, ইনি নায়িকা বনি বার্ড ওরফে ললিতা দেবী।
আমার আর নরেশদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মধু বোস বললেন, আপনারা বসে আলাপ করুন, আমি একবার রুস্তমজী সাহেবের ঘর থেকে আসছি।
তিনজনে চুপচাপ বসে আছি। মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবছি, কী কথার সূত্র ধরে কথা আরম্ভ করা যায়। আমারই নায়িকা, কিছু একটা না বলাও অশোভন।
নরেশদাই শুরু করলেন, মিস বার্ড, ডু ইউ লাইক ইওর হিরো?
ললিতা দেবী আমার আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে বললেন, হিইজ ভেরি হ্যান্ডসাম নো ডাউট।
দুষ্টুমিভরা একটা হাসির কটাক্ষ আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পরম কৌতুকে বসে পা দোলাতে লাগলেন নরেশদা। এতক্ষণ ধরে মনে মনে যা বলব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম সব তালগোল পাকিয়ে গেল। ক্লাস ভর্তি ছেলের সামনে পড়া বলতে না পারা ছেলের মতন লজ্জায় মুখ নীচু করে সামনের কাঠের টেবিলটার একটা কোণ নখ দিয়ে খুঁটতে লাগলাম।
আমার দিকে একটু ঝুঁকে নরেশদা বললেন, আলাপ হতে না হতেই এত নার্ভাস হয়ে পড়ছে ধীরাজ, এরপর যখন চুচুরে মাতাল হয়ে জোর করে বউ-এর কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি কেড়ে নিয়ে একরাশ গয়না নিয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন কী করবে?
অবাক হয়ে বললাম, গিরিবালায় আমার এইসব সিন আছে নাকি নরেশদা!
–শুধু এই? আমার অমোঘ শিক্ষার গুণে তোমার মতো মুখচোরা লাজুক ছেলে হয়ে উঠেছে একেবারে চৌকশ নামকরা কাপ্তেন। লবঙ্গ নামে একটি মেয়েকে বাঁধা রেখে রাতদিন তার ওখানেই পড়ে থাকো মদে চুরচুর হয়ে। শুধু টাকার দরকার হলেই বাড়ি এসে স্ত্রীকে মারধোর করে যা পাও নিয়ে বেরিয়ে যাও।
ললিতা দেবীর দিকে চাইতেও সাহস হচ্ছিল না। ফ্যালফ্যাল করে নরেশদার দিকে চেয়ে বসে রইলাম।
নরেশদা বলেই চললেন, একদিক দিয়ে তোমার উপর হিংসে হয় ধীরাজ। সিনেমায় ঢুকতে না ঢুকতেই সীতা দেবী আর ললিতা দেবীর মতো স্ত্রী পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। মনে হল ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও যেন ফেললেন নরেশদা। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, ললিতা দেবী আমাদের দিকে চেয়ে আছেন একাগ্রভাবে। হয়তো আমাদের আলোচনাটার মর্মোদঘাটন করবার চেষ্টা করছেন। ঘরের মধ্যে আরও দুচারজন অভিনেতা, যাঁরা এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তারাও উৎকর্ণ হয়ে আমাদের কথাগুলো শুনছেন। ভারি লজ্জা করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, নরেশদাকে থামিয়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। নরেশদা যেন আজ সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন। সে ভাষণ যত দীর্ঘ, যত নিরসই হোক, শেষ না হলে সভাভঙ্গের কোনো সম্ভাবনাই নেই।
আবার তেড়ে শুরু করলেন নরেশদা, বয়সে ও অভিজ্ঞতায় তোমার চেয়ে আমি বড়। সেই অধিকারে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। মন দিয়ে শোন, ভবিষ্যতে ভাল হবে। না শোন, দুদিনেই পাঁকে তলিয়ে যাবে।
ভূমিকা শুনেই বুক কেঁপে ওঠে। চুপ করে নরেশদার পরের কথাগুলো শোনবার জন্য বসে রইলাম।
পেশাদার যাদুকরের মতো দর্শকের কৌতূহল পুরো মাত্রায় জাগিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন নরেশদা। তারপর ধীরে সুস্থে পকেট থেকে এক প্যাকেট ক্যাভেন্ডার সিগারেট বের করে তা থেকে একটা ধরিয়ে দুতিনটে টান দিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, এ লাইনে বড্ড বেশি লোভন। বিশেষ করে তোমার মতো অল্পবয়সের ছেলের পক্ষে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই এ বয়সে সাধারণত প্রেমে পড়বার একটা ঝোঁক আসে, আর সেটা স্বাভাবিক। বাইরে থেকে সে ঝোঁকটা চেষ্টা করলে সামলে নেওয়া যায়। কিন্তু এ লাইনে সেটা সামলে নেওয়ার সুযোগ খুব কম। ধরো, সীতা দেবী বা ললিতা দেবীর মতো মেয়ের সঙ্গে তুমি বেশ জড়াজড়ি করে প্রেমের অভিনয় করে রাতদিন তাদের কথাই ভাবতে শুরু করলে। তোমার আহার-নিদ্রা গেল। এই যে কড়া মনোবিকার, এর একমাত্র প্রতিকার হল দৃঢ় মনোবল আর স্টুডিওর বাইরে গিয়ে ওসব স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দেওয়া। খুব শক্ত, তবে এ ছাড়া বাঁচবার উপায়ও আর নেই। তাছাড়া, এই সব মেয়ে-সীতা, ললিতা এরা মাকাল ফল। ঐ বাইরে থেকে দেখতেই যা, ভিতরে বিষের ছুরি। ভালবাসা বলে কোনো জিনিস ওদের মধ্যে নেই, শুধু দুহাতে টাকা সুটতে আর তোমার মতো সুন্দর কচি ছেলেদের হাড়মাস চিবিয়ে খেতেই ওরা এ লাইনে ঢুকেছে।
নিস্তব্ধ ঘরে বাজ পড়লে যেন। সশব্দে চেয়ারখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ললিতা দেবী। চোখ নাক মুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। নরেশদাও দেখি আমার মতো বেশ ভড়কে গেছেন।
রাগে কাঁপতে কাঁপতে ললিতা দেবী বললেন–
Mr Mitter, I think you are going too far. I am sorry to let you know that though I cannot speak properly, I can understand Bengali. (মিঃ মিত্র, আমার মনে হয়, আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, যদিও ভাল বলতে পারি না, তবে বাংলা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি।)
মঞ্চ ও পর্দার পাকা ঝানু অভিনেতা নরেশদা। অনেক রকম অভিব্যক্তি তার বিভিন্ন ভূমিকায় দেখেছি। কিন্তু সেদিনকার ঐ ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া অভিব্যক্তি তুলনা নেই। চেষ্টা করেও কোনো ভূমিকায় আর কোনোদিন দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ।
কথা শেষ করে দমকা হাওয়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গিরিবালার নায়িকা ললিতা দেবী। মনে হল বুঝি বা আমার জীবন থেকেও। শুধু হিলতোলা জুতোটার খটখট আওয়াজ খানিকক্ষণ পর্যন্ত সিমেন্টের মেঝেয় প্রতিধ্বনি তুলে আস্তে আস্তে চুপ করে গেল।
.
পুরোদমে শুটিং চলেছে গিরিবালার। সকাল ছটায় গাড়ি আসে, আটটার মধ্যে লোকেশনে পৌঁছে মেক-আপ করে প্রস্তুত হয়ে থাকি। বেলা বারোটা পর্যন্ত শুটিং চলে। তারপর সূর্য মধ্যগগনে দেখা দিলে, অর্থাৎ টপ সান (top sun) হয়ে গেলে শুটিং বন্ধ হয়। তখন আমাদের লাঞ্চের ছুটি। আবার দুটো থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত কাজ চলে। রোদের তেজ কমে এলে শুটিংও বন্ধ হয়ে যায়।
গিরিবালার শুটিং-এ আর একটা নতুন জিনিস দেখলাম রিফ্লেকটর বা ঝকঝকা ব্যবহার। আগে শুধু সানলাইটে শুটিং হতো। একটু অন্ধকার জায়গা, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না, সেখানে বড় বড় আয়না দিয়ে সূর্যের আলো ধরে ফেলা হত। তার ফলে আলোর সমতা রক্ষা হতো না। কেমন যেন ছোপ-ছোপ আলোর এফেক্ট হতো। মধু বোসকেই প্রথম দেখলাম কাঠের বড়, মাঝারি ও ছোট ফ্রেমে সোনালী ও রূপালী কাগজ এঁটে সূর্যের বিপরীতে ধরে সেই আলো শিল্পী ও লোকেশনের উপর ফেলে ছবি তুলছেন। প্রয়োজনমতো এই রকম রিফ্লেকটর পনেরো-কুড়িখানাও ব্যবহার করা হত। ফটোগ্রাফির উৎকর্ষ যে আগের চেয়ে অনেক ভাল হল একথা বলাই বাহুল্য।
ভাল কথা। নরেশদার সঙ্গে ললিতা দেবীর (মিস বনি বার্ড সেদিনকার অপ্রিয় ব্যাপারটা মধু বোসই একদিন মিটিয়ে দিলেন। সেও এক মজার ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছি, শুটিং-এর সময় ললিতা দেবীকে সাদরে জড়িয়ে ধরে হেসে ডায়ালগ বলি। শট শেষ হয়ে গেলে গম্ভীর মুখে উঠে চলে এসে অন্যদিকে পায়চারি করে বেড়াই। নরেশদাও যথাসম্ভব ওকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। ললিতা দেবীর প্রসঙ্গ উঠলেই নরেশদা হঠাৎ মধু বোসের সিনারিও খাতাটা গভীর মনোযোগর সঙ্গে পড়তে শুরু করেন অথবা আমাকে ডেকে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে বসেন। ব্যাপারটা মধু বোসের দৃষ্টি এড়াল না।
একদিন আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী বলতো ধীরাজ? হিরোইন, তার সঙ্গে কোথায় একটু ভাবসাব করবে, যাতে দুজনের জড়সড় ভাবটা কেটে যায়। তা না, নর্থ পোল আর সাউথ পোল!
আমতা আমতা করে সে প্রসঙ্গ কোনও রকমে এড়িয়ে গেলাম। মধু বোস কিন্তু নাছোড়বান্দা। নরেশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা সত্যিই কী হয়েছে বলুন তো নরেশবাবু? ধীরাজ আর ললিতা পরস্পরকে খালি এড়িয়েই চলেছে। এতে কিন্তু বিয়ের পর ওদের প্রণয়দৃশ্যটা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
একগাল হেসে নরেশদা অম্লানবদনে বলে বসলেন, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কী! ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার।
মধু বোস ও আমি দুজনেই থ বনে গেলাম।
–দুদিনের তো আলাপ, এর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই বা হল কখন! না, ব্যাপারটা তো খুব সহজ মনে হচ্ছে না। শোন ধীরাজ, আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে মধু বোস বললেন, সত্যি কী হয়েছে বলতো?
সত্যি কথা বলতে কি নরেশদার উপর মনে মনে বেশ একটু রাগও হয়েছিল। কাণ্ডটা আসলে বাধালেন উনিই, আর বেগতিক দেখে সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর দোহাই পেড়ে খালাস? গোড়া থেকে শুরু করে সেদিনকার ব্যাপারটা সব বললাম মধু বোসকে। সব শুনে প্রথমটা বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় হয়ে গেল মধু বোসের। তারপর হাসতে শুরু করলেন, যেন হিস্টিরিয়ার হাসি। প্রথমে কুঁজো হয়ে, তারপর পেটে হাত দিয়ে। সব শেষে শুয়ে পড়লেন ঘাসের উপর।
শুনেছিলাম হসি জিনিসটা সংক্রামক। এবার সে প্রবাদবাক্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম। মধু বোসকে ওভাবে হাসতে দেখে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।
তারপর কখন কেমন করে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় একটু একটু করে হাসতে হাসতে হাসিতে ফেটে পড়লাম মনে নেই। একটু পরে দেখি, ব্যাপারটা অনুমানে বুঝে নিয়ে অপ্রস্তুত্রে হাসি হাসতে হাসতে নরেশদা এগিয়ে আসছেন। ওরই মধ্যে চেষ্টা করে একটু দম নিয়ে মধু বোস বললেন, নরেশবাবু, আপনি যদি ধর্মযাজক হতেন, তাহলে সমস্ত পৃথিবীটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ ভরে যেত। আবার হাসি, এবার নরেশদাও যোগ দিলেন।
সেদিনের লোকেশন ছিল ওঙ্কারমল জেঠিয়ার বাগানবাড়িতে। চেয়ে দেখি, আমাদের ওভাবে হাসতে দেখে ইউনিটের আর সব কর্মীরাও হাসতে শুরু করেছে। শুধু পূর্বদিকের গঙ্গার ধারে একখানা বেতের চেয়ারে বসে উদাস চোখে নদীর অপর পারে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন ললিতা দেবী। আমাদের এ হাসির উৎস যে উনি নিজেই, মনে হল তা বুঝতে পেরেই যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। হঠাৎ হাসি থামিয়ে মধু বোস বললেন, আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি।
একটু পরেই অনিচ্ছুক প্রতিবাদরতা ললিতা দেবীকেএকরকম টানতে টানতে এনে আমাদের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন মধু বোস। তারপর ইংরেজিতে বললেন, বনি, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। সেদিন নরেশবাবু তোমায় ইচ্ছে করে অপমান করেননি। অনভিজ্ঞ নতুন ছেলে এ লাইনে এলে পাছে তারা খারাপ হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় উনি তাদের বাঁচাবার জন্য তৎপর হয়ে মরালিটি সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুরু করে দেন। সেদিন ধীরাজকেও এ সম্বন্ধে সচেতন করবার সদিচ্ছায় উদাহরণ খুঁজে না পাওয়ায় হাতের কাছে তোমাকে দেখে তোমার নামই করে ফেলেন। সবচেয়ে মুশকিল হল, তুমি যে বাংলা বুঝতে পার, এটা উনি ভাবতেও পারেননি। নাও, মিটমাট করে ফেল। তোমাদের ভুল বোঝাবুঝির ঠেলায় আমার সিনগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।
গম্ভীর মুখে তবুও ললিতা দেবী বসে আছেন দেখে নরেশদা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন– মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিস বার্ড, আই অ্যাম সরি!
ব্যস, মেঘ কেটে গেল। হেসে নরেশদার প্রসারিত হাতখানা ধরে ললিতা দেবী বাধো বাধো বাংলায় বললেন, আমি বাংলা বুঝটে পারি, এর জন্য সরি।
আবার হাসির তুফান উঠলো। পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, সূর্যদেব রাগে অথবা লজ্জায় লাল হয়ে পশ্চিম দিগন্তে আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন।
সেদিন আর শুটিং হল না। তল্পিতল্প নিয়ে যে যার বাড়ি চলে এলাম।
কালপরিণয় ছবির শুটিং আপাতত বন্ধ আছে। শুনলাম গিরিবালা রিলিজ হয়ে গেলে আবার শুরু হবে। গাঙ্গুলীমশাই অমন তাড়াহুড়ো করে ছবি তুলতে ভালবাসেন না, তা ছাড়া তিনি অনেক কাজের মানুষ। শুধু ছবি তোলা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে
গিরিবালা প্রায় শেষ হয়ে এল। রোজ শুটিং, বেশ লাগে। শুটিং না থাকলেই মনটা খুঁতখুঁত করে। এর মধ্যে মনে রাখবার মতো কিছু ঘটেনি। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে বেশ বুঝতে পারতাম, ললিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে, হাসাহাসিও করে, গ্রাহ্য করি না।
সেদিন হঠাৎ শুটিং-এর শেষে মধু বোস বললেন, কাল গিরিবালার শেষ শুটিং।
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমার। আড়চোখে লক্ষ করে দেখলাম, ললিতার মুখখানাও ম্লান। আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে একটু দুরে বেঞ্চির উপর বসে পড়লাম। নরেশদা আর মধু বোসও এগিয়ে এলেন। কাছে এসে মধু বোস কোনও রকম ভূমিকা না করেই বললেন, আজকাল ললিতার সঙ্গে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না ধীরাজ?
বেশ একটু ঝাজের সঙ্গেই বললাম, আপনারাই তো বলেন হিরোইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করলে স্বাভাবিক অভিনয়, বিশেষ করে লাভ সিন করা, সম্ভব নয়।
কোন জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে নরেশদা ও মধু বোস গাড়ির দিকে চলে গেলেন।
ওঙ্কারমল জেঠিয়ার বালির বাগানবাড়ি থেকে ভবানীপুর বেশ খানিকটা দূর। এই দীর্ঘ পথ সেদিন নীরবেই কাটিয়ে দিলাম। চেষ্টা করেও কোনো কথা বলতে পারলাম
না।
রাত্রে শুয়ে ঘুম আর আসে না। নিজের মনের সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিলাম।
–অন্যায়! কী অন্যায়টা করেছি শুনি?
–প্রথমেই নরেশদা তোমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন, এ লাইনে প্রলোভন বিছানো।
নরেশদার সবতাতেই একটু বাড়াবাড়ি। ললিতাকে যদি আমার ভাল লাগে তাতে দোষ কী?
–দোষ এই যে, ছবি শেষ হতে চললো অথচ তোমার ভাললাগা দিন দিন বেড়েই চলেছে।
সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য যুক্তিপূর্ণ পথে যে আলাপ-আলোচনা চলে তাকেই বলে তর্ক। আর কোনো যুক্তিই মানবো না, যেভাবে হোক আমার নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবই, এটা হল বিতণ্ডা। সোজা পথ ছেড়ে মনের সঙ্গে এই বিতণ্ডা করতে করতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।
ঘুম ভাঙলো মায়ের ডাকে। বলছেন, শুটিং-এর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তিন তিনবার ডেকে গেলাম এখনও ঘুম ভাঙলো না? আজ তোর হলো কী?
লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে কোনরকমে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের কাছে শুনলাম, আজ আর অন্য আর্টিস্ট কেউ নেই, শুধু আমি আর ললিতা। সারা পথ চুপচাপ কাটিয়ে জেঠিয়ার বাগানবাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন প্রায় আটটা বাজে।
আমার আগেই মধু বোস ললিতাকে নিয়ে পৌঁছে গেছেন। তাড়াতাড়ি মেক-আপ করতে গেলাম।
সেদিন নেওয়া হল কতকগুলো বিক্ষিপ্ত শট। যেমন মত্ত অবস্থায় আমার টলতে টলতে হেঁটে যাওয়া, উপরের জানলা খুলে ললিতার উঁকি মেরে দেখার ক্লোজ-আপ, সিঁড়ি দিয়ে টলায়মান দুখানি পা নেমে আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর নেওয়া হল বিভিন্ন ভঙ্গিতে আমার আর ললিতার একত্রে কতকগুলো স্টীল ফটো পাবলিসিটির জন্য।
লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। প্রতিদিনের বরাদ্দ যথারীতি খাবারের সঙ্গে, অবাক হয়ে দেখলাম, কেক, সন্দেশ ও কমলালেবুর অতিরিক্ত আয়োজন। একটু পরেই জানতে পারলাম বাড়তি খাওয়াটা খাওয়াচ্ছেন ললিতা দেবী, বিদায় আপ্যায়ন হিসাবে। আমিও বাদ গেলাম না। কেমন অভিমান হল। যুক্তিহীন অভিমান ঐ বয়সের নিত্যসঙ্গী। ভাবলাম, আমাকেও ললিতা দেবী সবার সঙ্গে এক করে বিদায় দিতে চান?
মুখ দেখে বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। একটু নিরিবিলি হতেই কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, ধীরাজ, তোমার জন্য রেখেছি একটা বিগ সারপ্রাইজ। মামি নিজে রান্না করেছে, মুরগ মসল্লম। রাত্রে আমাদের ওখানে তুমি খাবে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে খপ করে ললিতার একখানি হাত ধরে ফেললাম, কথা খুঁজে পেলাম না।
চকিতে চারদিক দেখে নিয়ে ললিতা বলল, ছাড়ো ছাড়ো! সবাই দেখলে কী ভাববে বল তো? বি পেশেন্ট ডারলিং।
ডারলিং? আমি আর নেই! ছবিতে নামতে শুরু করে, আমার এই একুশ-বাইশ বছর বয়সে, ইংরেজি জানা কোনো কটা রঙের মেয়ের মুখ থেকে ডাইরেক্ট ডারলিং ডাক এই প্রথম। ভাবলাম, আর বাড়ি যাব না। গঙ্গার তীরে ওঙ্কারমল জেঠিয়ার এই বাগানবাড়িতে মালি হয়ে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি যদি ললিতার মতো মেয়ে রোজ মাত্র একটিবার ডারলিং বলে ডাকে।
সেদিন আর বিশেষ কিছু কাজ হল না। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বেলা আড়াইটে বেজে গেল। কাজ শেষ করার আনন্দে সবাই বিভোর। মধু বোস ক্যামেরাম্যান যতীনকে নিয়ে কতকগুলো প্যানোরামিক দৃশ্য তুললেন এডিটিং শট হিসাবে। বেলা যেন তবু শেষ হয় না।
অবশেষে তল্পিতল্পা বেঁধে বালি থেকে যখন রওনা হলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ছোট গাড়িটায় আমি, ললিতা ও মধু বোস। বড় ভ্যানটায় আর সব স্টুডিও কর্মীরা। হৈ-হা করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার লোক অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলে ভাবে, ব্যাপার কী!
ধর্মতলায় আসতেই মধু বোস ৫ নম্বর বাড়িতে নেমে গেলেন রুস্তমজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। গাড়ি আমাকে ও ললিতাকে নামাতে চললো। ললিতারা ম্যাডান স্ট্রীটে একটা বড় ব্যারাক বাড়িতে থাকতো। তখন অবশ্য রাস্তাটির অন্য নাম ছিল, আর রাস্তাও অত চওড়া ছিল না। সবে দুধারে বাড়িগুলো ভাঙতে শুরু করেছে। ম্যাডানের আফিস ও বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি ম্যাডান স্ট্রীট ধরে দক্ষিণমুখে একটু এগোতেই ডান দিকে একটা পুরনো প্রকাণ্ড ব্যারাক বাড়ি পড়ে। সেইখানেই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে ললিতারা থাকে।
গাড়ি থামতেই ললিতা নেমে পড়ল। আমি গম্ভীর হয়ে চুপ করে একপাশে বসে আছি, হাত ধরে একটু টান দিয়ে ললিতা বলল, এসো।
তবুও ইতস্তত করছি, দেখি ড্রাইভার রামবিলাস মুচকি মুচকি হাসছে। অগত্যা নামলাম। সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে সামনে একটা অন্ধকার নোংরা স্যাঁতসেঁতে উঠোন। একটু এগিয়ে গিয়ে কাঠের নড়বড়ে একটা সিঁড়ি, তাই বেয়ে উপরে উঠতে হবে। কেমন একটু নিরুৎসাহ হয়ে গেলাম। ললিতার হাত ধরে সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, হঠাৎ পাশ দিয়ে দু-তিনটি ছেলে-মেয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল। বহুদিনের পুরনো সিঁড়ি যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে উঠল। রোমান্টিক নভেল পড়ে পড়ে যে কুসুমবিছানো পথ কংক্রিটের মতো মনে স্থায়ী আসন পেতে রেখেছিল, এই অন্ধকার নড়বড়ে সিঁড়িই প্রথম সেটায় নাড়া দিয়ে কাঁটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিল। হঠাৎ নরম বালিশের মতো একটা পদার্থ পায়ের ওপর পড়তেই সভয়ে চিৎকার করে পড়তে পড়তে ললিতাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেও টাল সামলাতে পারলাম না। সিঁড়ির উপর দুজনে জড়াজড়ি করে বসে পড়লাম বা পড়ে গেলাম। কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে পরম কৌতুকে খিলখিল করে হেসে উঠল ললিতা। শীতের সন্ধ্যায়, বেশ বুঝতে পারলাম, কপালটা আমার ঘামে ভিজে উঠেছে। সিঁড়ির চার-পাঁচটা ধাপ উপরে উঠতেই দোতলার বারান্দা। হঠাৎ ডানদিকের ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর এক ঝলক আলো এসে সামনে পড়ল। একটি মোটাসোটা আধবয়সী মহিলা, পা পর্যন্ত ছিটের গাউন পরা, টর্চ হাতে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। টর্চের আলোয় দেখি কোলের উপর একটা মিশমিশে কালো লোমশ কুকুরকে জড়িয়ে ধরে হেসেই চলেছে ললিতা। এতক্ষণে খেয়াল হল আমার হাত দুটো তখনও জড়িয়ে আছে ললিতাকে। লজ্জায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টর্চ-হাতে মহিলাটির বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। গায়ের রং ফরসা নয়, বেশ চাপা। মুখ দেখলে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, এই প্রেীরাই ললিতার মা। নাক চোখ মুখ হুবহু এক।
বেকুবের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নির্বিকার মুখে মহিলাটি ডাকলেন–বনি!
নিমেষে হাসি থেমে গেল ললিতার। তাড়াতাড়ি উঠে কুকুরটাকে কোলে করে সিঁড়িগুলো একরকম লাফিয়ে পার হয়ে মার কাছে গিয়ে বলল, মামি, এই ধীরাজ, আমার হিরো।
জীর্ণ নড়বড়ে সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে শুধু মনে হচ্ছিল,এই মুহূর্তে ওটা যদি ভেঙে আমায় নিয়ে পড়ে যায় তাহলে বেঁচে যাই। ললিতার মায়ের সঙ্গে প্রথম আলাপে খানিকটা ভাল ইম্প্রেশন দেব বলে কতকগুলো জুতসই ভাল ভাল কথা মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলাম। সব ভেস্তে গেল। অপরাধীর মতো এক-পা দু-পা করে উঠে সামনে গিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়ালাম। স্নিগ্ধ হাস্যে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় ললিতার মা বললেন, তোমরা ভিতরে এসো।
সবাই ভিতরে ঢুকলে ললিতার মা দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। লোকমুখে কয়েকটি বিখ্যাত পীঠস্থানের কথা শুনেছিলাম, যেখানে অতি দুর্গম কষ্টকর পথ বহু ক্লেশে অতিক্রম করে দেবতার কাছে পৌঁছে মানুষ পথ আর পথের কষ্ট সব ভুলে যায়। যেন মানুষের একাগ্রতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা নেবার জন্যই পথের ছলনা।
আমারও ঠিক তাই হল। নীচের ঐ দুর্গন্ধময় অন্ধকার উঠোন, জীর্ণ নড়বড়ে অন্ধকার সিঁড়ি, সব ভুলে গেলাম এদের ছিমছাম পরিষ্কার ঘরখানি দেখে। মাঝারি ঘর। একপাশে শোবার খাট, তার উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানা। অন্য পাশে তিন চারখানি সোফা ও তার সঙ্গে মিল রেখে গোল একটা টেবিল।তার উপর ফুলদানি। তাতে টাটকা সুগন্ধি নাম-না-জানা ফুলের স্তবক। দেওয়ালে দু তিনখানা ছবি, সবই নাম করা। আর্টিস্টের আঁকা। ঘরের মধ্যে কাঠের ফ্রেমে ফিকে সবুজ কাপড় দিয়ে একটা মুভেবল পার্টিশন। দরকার হলে গুটিয়ে একপাশে রাখা যায়। সব মিলিয়ে মনে হল, এদের দারিদ্র্য আছে, দৈন্য নেই। রুচি আছে, সচ্ছলতা নেই। কেমন একটা সম-মাখানো বিস্ময়ে সব ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।
চমক ভাঙল ললিতার মায়ের কথায়। আমাদের এই জোড়াতালি দিয়ে দারিদ্র্য ঢাকবার চেষ্টা দেখে মনে মনে হাসছ ধীরাজ?
হেসে জবাব দিলাম–না। বরং শিখে নিচ্ছিলাম পরিচ্ছন্নতা ও রুচি দিয়ে কী করে দারিদ্রকে হার মানাতে হয়।
বোধহয় খুশি হলেন ললিতার মা। আমাকে ওঁর পাশে এসে বসতে বললেন। দুজনে সোফায় বসলাম। ললিতা তখনও দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে আদর করছে।
মিসেস বার্ড এবার একটু রেগেই বললেন, বনি, এখনও দাঁড়িয়ে লোলাকে আদর করছ? যাও, বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে এসো।
কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েই সে পশ্চিমদিকের অন্ধকার বারান্দায় ছুটে গেল, ললিতাও তার পিছনে পিছনে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। আমিই শুরু করলাম, দেখুন মিসেস বার্ড, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলতে পারেন, কিন্তু ললিতা–
বাধা দিয়ে ললিতার মা বললেন, ভাল বলতে পারে না। অবাক হবারই কথা, তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, আমি বাঙালি খ্রীস্টান। আমার স্বামী ছিলেন আইরিশম্যান, ই, আই, আর.-এ গার্ডের কাজ করতেন। বনিকে আমরা ইচ্ছে করেই বাংলা শেখাইনি। কারণ, আমাদের এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের কোনো অভিজ্ঞতা যদি তোমার থাকতো, তাহলে বুঝতে পারতে এ সমাজে বাংলা বলা বা বোঝা একটা অপরাধ।
বিস্মিত হয়ে ললিতার মায়ের মুখের দিকে চাইতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ অপরাধ। যদি কেউ জানতে পারে, আমি ভাল বাংলা বলতে পারি বা বুঝতে পারি, তাহলে সমাজের চোখে আমি অনেকখানি নেমে গেলাম এবং ছুতোয়নাতায় সবাই আমাদের এড়িয়ে চলবে। এ সমাজে রঙের কোনো দামই নেই। আবলুস কাঠের মতো রঙও যদি তোমার হয়, আর বুলি যদি ইংরেজি হয়, ব্যস সাত খুন মাফ। এই দেখ না, আমাকে দেখেই বুঝতে পারবে আমি বেশ কালো। কিন্তু বনি? বনি পেয়েছে ওর বাপের রং।
হঠাৎ কথা বন্ধ করে ললিতার মা পুবদিকের দেওয়ালে আলোর ব্র্যাকেটের নীচের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি ঠিকআলোর নীচে ছোট একখানা বাঁধানো ফটো টাঙানো রয়েছে। অনুমানে বুঝতে পারলাম উনিই মিঃ বার্ড, বনির বাবা।
চুপ করে রইলাম। ভাবলাম এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা বদলানো দরকার। বললাম, আচ্ছা মিসেস বার্ড, সিঁড়িটায় কোনো আলো নেই কেন? ওরকম অন্ধকার, তার উপর সিঁড়িটা তো মোটেই নিরাপদ নয়। বাড়িওয়ালাকে আপনারা বলেন না কেন?
ললিতার মা বললেন, বাড়িওয়ালার কোন দোষ নেই। এই বাড়িটায় খুব কম করে দেড়শোটি পরিবার বাস করে। কারো সঙ্গে কারো ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, ভাল পরিচয়ও নেই। সারা দিনরাত কে কখন আসে, কে কখন বেরিয়ে যায় ঠিক নেই। প্রথম প্রথম বাড়িওয়ালা আলো দিয়েছিল। সকালে দেখা গেল বালব নেই। এইরকম পাঁচ সাতবার বালব চুরি যাবার পর আর আলো দেয় না।
হঠাৎ মাথার উপর হুড়মুড় শব্দ। মনে হল সমস্ত ছাদটা এখুনি ভেঙে মাথায় পড়বে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের ছবিগুলো কেঁপে দুলতে লাগল। ভয়ে ও উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম।
অভয় দিয়ে ললিতার মা বললেন, বোসো ধীরাজ, ওপরের ঘরে পেগি আর মেরি দুবোনে নাচতে শুরু করেছে। কান পেতে শুনলাম, তাই বটে। একটা গ্রামোফোনে নাচের রেকর্ড বাজছে-বীভৎস তার আওয়াজ। আর তারই তালে তালে নাচের নামে দুরমুশ করছে উপরের ছাদটা পেগি আর মেরি দুই বোন। অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশ, এর আগে এ রকম আবহাওয়ায় আর কোনও দিন পড়িনি।
পশ্চিমের বারান্দার ডানদিক থেকে বনি ডাকল, মামি, মামি!
ললিতার মা উঠে গিয়ে বারান্দায় উঁকি দিয়ে এসে কাঠের সেই মুভেবল পার্টিশনটা দিয়ে ঘরের খানিকটা জায়গা আড়াল করে দিলেন। বুঝলাম বনির বেশ পরিবর্তন হবে। অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে একটা ইংরেজি গানের দুলাইন গুনগুন করে গাইতে গাইতে পার্টিশনের আড়ালে প্রসাধন শুরু করল বনি।
চুপ করে বসে আছি। কানে আসছে শুধু বনির গুনগুন গুঞ্জন আর উপরে মুগুর দিয়ে ছাদ পেটানোর আওয়াজ। হঠাৎ শুনি গান থেমে গেছে। পার্টিশনের আড়াল থেকে বনির ন্যাকা কান্নার আওয়াজ ভেসে এল, মামি, উই আর হাঙরি মামি!
ক্ষুধা-তৃষ্ণা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম আমারও খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কোনো কথা না বলে ললিতার মা উঠে পশ্চিমের বারান্দার বাঁ দিকে চলে গেলেন, বুঝলাম ঐ বারান্দার ডানদিকে হলো বাথরুম আর বাঁ দিকে কিচেন।
পার্টিশনের দিকে চোখ পড়তেই দেখি অপরূপ সাজে বেরিয়ে আসছে ললিতা। পরনে গোলাপী রঙের ফিনফিনে পাতলা সিল্কের ঢিলে পাজামা, গায়ে ততোধিক পাতলা শুধু একটা নকশা কাটা কিমোননা। পায়ে বেডরুম স্লিপার, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল ফাঁপানো ফোলা। ললিতা কাছে এসে দাঁড়াতেই ইভনিং-ইন-প্যারির মিঠে গন্ধে ঘরটা মশগুল হয়ে উঠল।
হতবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। হাসিমুখে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে ঝুপ করে আমার সোফাটার হাতলের উপরে বসে পড়ল ললিতা। তারপর চক্ষের নিমেষে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের পাশে মুখ রেখে গদগদ কণ্ঠে বলল, নাউ মাই ডারলিং, মামির সঙ্গে কী কী কথা হলো বল।
গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার। সোফাটার একপাশে জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে বসে পাংশু মুখে পশ্চিমের বারান্দার বাঁ দিকে চাইতে লাগলাম–যদি দয়া করে ললিতার মা খাবার নিয়ে এখুনি এসে পড়েন তো বেঁচে যাই। কিন্তু এলেন না। জবাব না পেয়ে কপট অভিমানে মুখটা আমার বুকের উপর রেখে আরও নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ললিতা বলল, এত সাজগোজ করে এলাম তোমার জন্যে, আর তুমি একবারটি বললে না কেমন দেখাচ্ছে আমাকে।
বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছিল। অতি কষ্টে বললাম, ভালো।
মোটই খুশি হলো না ললিতা। মুখ তুলে তেমনি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, মোটই না। কী রকম হিরো তুমি? অন্য দেশ হলে হিরোইনকে এভাবে নির্জনে পেলে হিরো বুকে জড়িয়ে নাচতে শুরু করে দিত।
সাহস খানিকটা ফিরে এসেছিল। বললাম, তুমি হলে বিশ্বের নায়িকা, আর আমি? বাংলাদেশের মুখচোরা লাজুক হিরো। তফাতটা অনেকখানি কিনা–কাটিয়ে উঠতে সময় নেবে।
পরম কৌতুকে হেসে উঠল ললিতা। তারপর বলল, মাই ডারলিং, শুধু ভাল ভাল কথাই বলতে পারো, ইউ আর হোপলেস!
জড়সড় ভাবটা ততক্ষণে কেটে এসেছে। হেসে বললাম, ধরো, সবে আমাদের সিনটা জমে উঠেছে, এমন সময় তোমার মামি খাবার নিয়ে ঢুকলেন–তখন?
বেশ একটু জোর দিয়েই ললিতা বলল, মোটেই না। মামি এতক্ষণে কিচেনে বেতের চেয়ারটায় বিয়ারের বোতল খুলে বসেছে। এটা মামির বিয়ার খাবার সময়। এখন ভূমিকম্প হলেও অন্তত হাফ অ্যান আওয়ার এদিক মাড়াবেন না।
ভাবলাম, ললিতাকে জিজ্ঞাসা করি অবস্থা তো বলছ তেমন সচ্ছল নয়, অথচ রোজ মামির বিয়ার, তোমার রং-বেরঙের পোশাক এসব আসে কোত্থেকে? লজ্জা ও সংকোচ এসে বাধা দিল।
ললিতা বলল, অনেস্টলি ধীরাজ, বলতো, এর আগে আর কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছ?
প্রথমটা চমকে উঠলাম। সামলে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে জবাব দিলাম, না।
–দ্যাটস হোয়াই! তাই তুমি অত শাই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি সাতদিন যদি তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা করো, আমি তোমায় স্মার্ট ড্যাশিং হিরো বানিয়ে দেবো।
অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই কি সেই লজ্জানতা স্বল্পবাক গিরিবালা? হাত বাড়ালেই যে মেয়ে ছুটে এসে বাহুবন্ধনে ধরা দেয় তাকে নিয়ে আর যাই চলুক, প্রেম করা চলে না। ললিতা সম্বন্ধে যে মিষ্টি মধুর রোমান্সের জাল এতদিন যত্ন করে বুনে চলেছিলাম, আজ হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তার অনেকখানি উড়িয়ে নিয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, এই গায়ে-পড়া প্রেম, এর জন্য প্রস্তুতও যেমন ছিলাম না, ভালও তেমনি লাগছিল না।
বাইরের বারান্দায় একটা বিশ্রী গোলমাল শোনা গেল। মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে চিৎকার করে কী বলছে, এক বর্ণও বোঝা গেল না। ললিতা তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেল। নির্বিকারে তেমনি ঠায় বসে রইলাম। মনে হল আজ আমার ভয় বিস্ময় কৌতূহল কিছুই আর নেই যেন। এই রহস্যময় পুরোনো ব্যারাকবাড়িতে সব কিছুই সম্ভব।
হাসতে হাসতে ফিরে এসে একরকম আমার গায়ের উপর পড়ল ললিতা। তারপর দু হাত দিয়ে আমায় দুতিনটে কঁকানি দিয়ে বলল, জান ধীরাজ, কী মজার ব্যাপার হয়েছে? দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটায় লিজি বলে একটা মেয়ে থাকে। সে এই ব্যারাকের টমি বলে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রেম করছিল। এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে চুপিচুপি উঠে এসে হঠাৎ ওদের উপর টর্চের আলো ফেলেছে ওর লাভার। অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছিল, হাতেনাতে ধরে ফেলেছে আজ। ব্যস, আর যায় কোথায়! কিল, চড়। তারপর টমির সঙ্গে শুরু হল ঘুষোঘঁষি। আবার হাসিতে ফেটে পড়ল ললিতা।
সমস্ত দেহ-মন ঘেন্নায় রি-রি করে উঠল। ললিতার উচ্ছ্বাস ও হাসি তখনও থামেনি। বলল, রাত দশটার পর হঠাৎ যদি কেউ বারান্দায় একটা আলো জ্বেলে দেয়, অন্তত টেন পেয়ার্স অফ লাভার হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।
আমার কাধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আবার সেই কুৎসিত ইঙ্গিতে ভরা গা-জ্বালানো হাসি। রোমান্সের নেশা পুরোপুরি ছুটে গেছে আমার। কতক্ষণে এদের হাত থেকে, এই নোংরা আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাব এখন তাই শুধু একমাত্র চিন্তা।
ভেজানো দরজায় খটখট করে দুতিনটে টোকা পড়ল। আর এক নতুন বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলাম। তাড়াতাড়ি উঠে স্থানভ্রষ্ট কিমোনোটা ঠিক করে নিয়ে গম্ভীরভাবে ললিতা বলল, কাম ইন!
ঘরে ঢুকল একটা বছরদশেকের পশ্চিমা মুসলমান ছেলে। পরনে ময়লা লুঙ্গি, গায়ে ততোধিক ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি। দেখলাম, ওর হাতে রয়েছে শালপাতা দিয়ে মোড়া পুরু কয়েকখানা পরোটা।
ললিতা বলল, কিচেনমে মামি কে পাস লে যাও। ছেলেটিকে নীচের কোনও মুসলমান হোটেলের বয় বলেই মনে হল। মিনিটখানেক বাদেই দুহাতে রেজকি ও পয়সা গুনতে গুনতে ঘরে এসে আমাকে ও ললিতাকে সেলাম করে চলে গেল।
এই অদ্ভুত ব্যারাকবাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ঘরের মাঝখানে অপরূপ ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করে দিয়েছে ললিতা। ভূতলে এক পা আর স্বর্গে এক পা তুলে বিচিত্র অদ্ভুত নাচ। একটু কান খাড়া করে শুনি উপরতলায় পেগি মেরি বোধহয় ক্লান্ত হয়ে নাচ থামিয়েছে, কিন্তু গ্রামোফোনটা থামায়নি। তারই ভাঙা অস্পষ্ট সুরের রেশ টেনে স্বর্গ-মর্ত তোলপাড় করে নাচছে ললিতা। হাসি পাচ্ছিল, অতি কষ্টে সামলে নিয়ে ভাললাগার ভান করে চেয়ে রইলাম।
নাচ থামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ললিতা, মামি, আই হ্যাভ ডান ইট! চেয়ে দেখি দুহাতে ধরা বড় ট্রের উপর কতকগুলো খাবারের ডিশ নিয়ে মিসেস বার্ড কখন এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পিছনে। বড় ড্যাবডেবে চোখ দুটো তার গর্বে ও প্রশংসায় উজ্জ্বল।
আমার দিকে ফিরে বললেন, এই ডিফিকাল্ট নাচটা সত্যিই বনি শিখে ফেলেছে, কী বল? কিছু না বুঝেই হাসিমুখে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।
বুঝলাম, রাত্রি আটটার পর থেকে মিসেস বার্ড একটু বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন। আর ললিতার নাচই যে তার একমাত্র কারণ নয়, এটা বুঝতেও দেরি হল না। গর্বস্ফীত চোখে কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে থেকে মিসেস বার্ড বললেন, ভেরি গুড ডারলিং। নাউ গিভ ইওর পুয়র মামি এ কিস।
ছুটে এসে ললিতা চুমোয় চুমোয় মাকে অস্থির করে তুলল। আদরের ঠেলায় খাবারসুদ্ধ ট্রেটা মাটিতে পড়ে আর কী! কোনো রকমে সামলে নিয়ে মিসেস বার্ড বললেন, নাউ চিলড্রেন, হিয়ার ইজ ডিনার।
দুজনে মিলে গোল টেবিলটার উপর খাবারগুলো তিনটে প্লেটে সাজিয়ে দিল। সত্যিই ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছিল। আর দ্বিরুক্তি না করে সবাই খেতে বসে গেলাম। প্রায় এক পোয়া ওজনের ঘিয়ে জবজবে মোটা পরোটা একখানা করে, অন্য প্লেটে মুরগ মুসল্পম, আর ছোট একটা চিনামাটির বাটিতে খানিকটা করে সাদা পুডিং। এই অদ্ভুত বাড়িটায় এতক্ষণ বাদে সত্যিকার আনন্দ পেলাম খেয়ে, একথা স্বীকার
করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। মুরগির এরকম প্রিপারেশন এর আগে খাইনি। শুনলাম, এক পরোটা ছাড়া, মাংস, পুডিং ললিতার মা নিজে তৈরি করেছেন। বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রশংসার যতগুলো ভাল ভাল কথা মনে এল সব উজাড় করে দিলাম। ফলে লাভ এই হল, ললিতার মাকে কথা দিতে হল যে, সপ্তাহে অন্তত একদিন ওঁদের এখানে এসে খেয়ে যেতে হবে।
খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই রাত নটা বেজে গেল। বাড়ি ফেরার জন্যে উসখুস করতে থাকি, কিন্তু ওরা কিছুতেই উঠতে দেবে না। নানা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। যথা বাড়িতে কে কে আছেন, অবস্থা কেমন, ভাই বোন কটি ইত্যাদি ইত্যাদি। এতেও নিস্তার নেই। ললিতা মায়ের সামনেই স্পষ্ট বলে ফেলল, বাড়িতে না আছে বউ, না আছে লাভার, অত তাড়া কীসের?
অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর খানিকটা বসতে হল।
.
অবশেষে সত্যিই বিদায় নিয়ে, আবার আসবার এবং পরবর্তী ছবিতে যাতে ললিতাকে হিরোইন নেওয়া হয় তার জন্য গাঙ্গুলীমশাই, নরেশদা এবং মধু বোসবক বিশেষ করে অনুরোধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর থেকে যখন বার হলাম তখন দশটা বাজে। এদের এতখানি আদর-আপ্যায়নের অর্থ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল।
অবশেষে সত্যিই একদিন ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমান উত্তরা সিনেমা) গিরিবালা মুক্তিলাভ করল। তারিখটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। বাংলা ১০ ফান, শনিবার, ১৩৩৬ সাল। ইংরেজি ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার দু একদিন আগে মিঃ বোস ও ম্যাডান কর্তৃপক্ষ ম্যাডান থিয়েটারে (বর্তমান এলিট সিনেমা) সকালে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে সমস্ত নামকরা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সমালোচকদের এই প্রদর্শনীতে আহ্বান করা হয়। এখানে বলে রাখি, তখনকার দিনে কোনও ছবির মুক্তির আগে এ রকম প্রেস-শো বা স্পেশাল শোর রেওয়াজ ছিল না। কাজেই অনেকেই বেশ একটু কৌতূহলী হয়ে নতুনত্বের সন্ধানে ছুটে এসেছিলেন সেদিনের সকালের শো-এ। তখনকার দিনের বিখ্যাত চিত্র ও মঞ্চ সাপ্তাহিক নাচঘর তো স্পষ্ট লিখেই ফেলল–
সেদিন রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে গৃহীত গিরিবালা চিত্রনাট্যের অপ্রকাশ্য অভিনয় দেখবার জন্য ম্যাডান কোম্পানি অনেক সাংবাদিক ও নাট্যসমালোচককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমাদের মতন আরো অনেক বাঙালি নাট্যসমালোচক নিশ্চয়ই অল্প বিস্মিত হননি। কারণ এটা অভূতপূর্ব। (নাচঘর, ২ ফাল্গুন, ১৩৩৬)
একখানা নির্বাক ছবির মুক্তিতে এত হৈচৈ ও চাঞ্চল্য এর আগে বাংলাদেশে হয়নি। প্রতিটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক গিরিবালার স্তুতিগানে মুখর হয়ে উঠল। আর সে কী প্রশংসা! সবগুলো এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া সম্ভব নয়, কয়েকটি নমুনা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না–
The Statesman, Tuesday, Feb. 11,1930:
Dhiraj Bhattacharjee, Naresh Mitter and Chakrabartty gave good performances in the male roles.
স্টেটসম্যান ছাড়াও ইংরেজি বেঙ্গলী, লিবার্টি ও অ্যাডভান্স পত্রিকা অভিনয়, পরিচালনাও ফটোগ্রাফিরভূরিভূরি প্রশংসা করেছিল। বাংলা সাপ্তাহিকভোটরঙ্গ গল্প, পরিচালনা ও ফটোগ্রাফির পর আমাদের সম্বন্ধে লিখল–
এই তিনটি চরিত্রের সবটুকু বৈচিত্র্যই অভিনেতৃবর্গ ছবির ওপরে ভালো করে ফুটিয়েছেন। যেমন হয়েছে ললিতাদেবীর গিরিবালা, তেমন হয়েছে ধীরাজবাবুর গোপীনাথ, আবার তাদেরই সঙ্গে সমানভাবে পা ফেলে চলেছেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র–গোপীনাথের বন্ধুর ভূমিকায়।(ভোটরঙ্গ, রবিবার, ৪ ফামুন,১৩৩৬)
সাপ্তাহিক শিশির লিখল–
বলিতে দ্বিধা নাই যে, এই চিত্রনাট্যের প্রায় প্রত্যেকেই বেশ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। গোপীনাথের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্যের এবং তাহার বন্ধুর ভূমিকায় নরেশবাবুর অভিনয় হইয়াছিল অতি চমৎকার। (শিশির, শনিবার, ২৮ ফামুন, ১৩৩৬)
সাপ্তাহিক নাচঘর লিখল—
গিরিবালা দেখে আমরা বাংলা ফিল্ম-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েছি। অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে গোড়াতেই ম্যাডান কোম্পানির নতুন সংগ্রহ প্রিয়দর্শন তরুণ নট শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্যকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। (নাচঘর,১৬ ফানুন, ১৩৩৬)
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক বায়োস্কোপ প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় কলমে লিখল–
গিরিবালার পরিচালক শ্রীযুক্ত মধু বোস তার এই প্রথম তোলা ছবিতে তার যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবিখানি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোেলবার প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি কোথাও হয়নি। ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে আমরা আরো অনেক কিছু আশা করি। …গিরিবালায় গোপীনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য। ছায়ালোকের এই নবীন শিল্পীকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। (বায়োস্কোপ, ১৬ সংখ্যা, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০)
এছাড়াও কুরুক্ষেত্র, বাঙলা, ভগ্নদূত প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সবার এককথা, এ রকম নীট ছবি বাংলায় আর হয়নি। আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত ও ভাবিত করে তুলল, তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিক নবশক্তি। অধুনাবিখ্যাত সমালোচক ও চিত্রপরিচালক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (চন্দ্রশেখর) গিরিবালার সমালোচনা প্রসঙ্গে নবশক্তিতে লিখলেন
আমরা কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছি নায়ক গোপীনাথের ভূমিকায় একজন নতুন অভিনেতার অভিনয় চাতুর্যে।
…চমৎকার ফিল্ম ফেস আছে তাঁর। তার ভাব প্রকাশের ভঙ্গিও অনিন্দনীয়, তার সংযত অভিব্যক্তি আমাদের বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছে। সমজাতীয় না হলেও ধীরাজবাবুর মুখের নিম্নাংশের সঙ্গে ওদেশের অতুলনীয়া গ্রেটা গার্বোর মুখের আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করেছে বলেই আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি। আমাদের বিশ্বাস এই একটি ভূমিকায় অভিনয় করেই ধীরাজবাবু এদেশের চিত্রপ্রিয়দের কাছে বিশেষভাবেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। (নবশক্তি, শুক্রবার, ২ ফারুন, ১৩৩৬)
বলতে লজ্জা নেই, আজ এত দীর্ঘদিন বাদেও চন্দ্রশেখরবাবুর ঐ গ্রেটা গার্বোর মুখের নিম্নাংশের সঙ্গে তুলনার মানেটা ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারিনি। কখনও মনে হয় বুঝি প্রশংসা, আবার কখনও সন্দেহ জাগে ঠাট্টা করলেন নাকি?
পরিচালক মধু বোস বাবাকে নিয়ে গিরিবালা দেখালেন। হাবেভাবে বুঝতে পারলাম বাবা মনে মনে খুশি হয়েছেন। অনেক দিন বাদে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।
ইতিমধ্যে আমার সেই দূর সম্পর্কের কাকাটি সপরিবারে একদিন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। যখন পুলিশ ছিলাম-এর পাঠকবর্গের বোধহয় মনে আছে, পড়া ছেড়ে প্রথম যখন অভিনয় আরম্ভ করি, ইনিই উপযাচক হয়ে এসে বাবা-মাকে অনেকগুলো কটু অপ্রিয় কথা শুনিয়ে গিয়েছিলেন। আজ হঠাৎ এঁর আবির্ভাবে আমরা সবাই মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। কাকার বড় মেয়ে রিনির বয়স তের-চৌদ্দ। ইশারায় তাকে একটু দূরে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী পার্ল হোয়াইট?
ফুটফুটে সুন্দর নিটোল চেহারা রিনির। গোল মুখে হাসলে টোল খায়, তখনকার দিনের সর্বজনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্ল হোয়াইটের মতো। আমি ঠাট্টা করে তাই ওকে ঐ নামেই ডাকতাম। রিনি খুশিই হত, কাকা-কাকিমা চটে যেতেন।
ছোট্ট সহজ কথাও অকারণে ফেনিয়ে ঘোরালো করে ভোলা বোধহয় মেয়েদের অভ্যাস। চারদিকে সভয়ে চেয়ে গলাটা খাটো করে রিনি বলল, জান ছোড়দা, ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার গিরিবালা।
বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। মুখে আস্ফালন করে বললাম, ফাজলামো করিসনি, ব্যাপারটা কী বল?
মুখখানা কাঁচুমাচু করে রিনি বলল, বাবা-মা বলতে বারণ করে দিয়েছে যে?
বেশ বুঝলাম কথাটা বলবার জন্যে রিনি ছটফট করছে। বললাম, ও আচ্ছা, তাহলে বলিসনি।
চলে আসবার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই পিছনের শার্টের একটা কোণ টেনে ধরল রিনি। ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হবার ভান করে বললাম, কী রে?
–তুমি যদি কাউকে না বল তো বলতে পারি।
–দরকার নেই আমার শুনে অমন কথা। ছেড়ে দে, আমায় এখুনি স্টুডিওতে যেতে হবে।
স্টুডিও আর শুটিং–এই দুটোর উপর রিনির কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এ যেন অদৃষ্টের পরিহাস। কাকা কাকিমা বায়োস্কোপ-থিয়েটারের নাম শুনতে পারতেন না আর ছেলেমেয়েগুলো, বিশেষ করে রিনি, সবার বড় বলে সিনেমা-থিয়েটারের কথাগুলো যেন গিলতে। নিমেষে আমার আরও কাছে এসে চুপিচুপি বলল রিনি, বাবা করুক রাগ, জান ছোড়দা, বাবার অফিসের বড়বাবু থেকে শুরু করে অনেকেই তোমার গিরিবালা ছবি দেখে এসেছে।
ঠোঁট দুটো উটে তাচ্ছিল্যের ভান করে বললাম, এই কথা!
রিনি দমবার মেয়ে নয়। বলল, শুধু এই কথা নয়, এর পরের কথাগুলো আরও দরকারী।
পরের দরকারীকথাগুলো শুনবার কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করে চুপ করে আছি দেখে অভিমান কঠে রিনি বলল, বেশ বেশ, নাই বা শুনলে, আর কখনো তোমাকে কিছু বলব না।
বুঝলাম আর বাড়াবাড়ি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বললাম, হ্যাঁরে রিনি, তোকে পার্ল হোয়াইটের সিরিয়ালে The Iron Claw ছবিটার শেষ ইনস্টলমেন্টটা বলেছি কি?
হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রিনি। আমার হাত ধরে বলল, বল না ছোড়দা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।
–তার আগে ঐ পরের দরকারী কথাটা বল।
গড়গড় করে বলতে শুরু করল রিনি–
বায়োস্কোপ-থিয়েটারের উপর বাবা বরাবরই চটা। তোমার কথা উঠলেই বাবা মাকে বলতেন, ধীরেটা এবার উচ্ছন্নে যাবে। রাঙাবৌ আর রাঙাদাকে কত করে বললাম, শুনলেন না। পরে বুঝবেন মজাটা। এই বয়সে ঐ সব সংসর্গে পড়ে দুদিন বাদেই মদ-ভাঙ খেতে শুরু করবে। তারপর ওদেরই মধ্যে একটা খ্রীস্টান ছুঁড়িকে বিয়ে করে আমাদের বংশের নাম ডোবাবে।
যৌবনে আমার মা নামকরা সুন্দরী ছিলেন। দুধে-আলতা মেশানো গায়ের রং, নিখুঁত গড়ন। সব মিলিয়ে মায়ের মতো সুন্দরী মেয়ে আমাদের গ্রামে এর আগে আর কেউ দেখেনি। তাই বধূবেশে প্রথম পদার্পণ থেকেই ছোট-বড় সবাই মাকে রাঙাবৌ বলে ডাকত। বাবাও খুব ফরসা ছিলেন, ঠিক কাঁচা হলুদের মতো রঙ। কাকারা এবং আত্মীয় যারা বয়সে বাবার হোট, সবাই রাঙাদা বলে ডাকতেন।
একটু থেমে দম নিয়ে বলতে শুরু করল রিনি, চারদিকে সব নাম করা শিষ্য। তারা যখন ছবির পর্দায় গুরুপুত্রের কাণ্ডকারখানা দেখবে তখন? তাই বাবা আমাদের সবাইকে বলে দিয়েছে, তোমরা যে আমাদের আত্মীয় একথা যেন কাউকে না বলি।
আমার সিনেমায় যোগ দেওয়া সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজন কেউ খুশি হয়নি একথা জানতাম। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়েছে জানা ছিল না।
রিনি বলল, আমাদের পাড়ার রায়বাহাদুরের মেয়ে গোপাকে জান ছোড়দা? কাকা থাকতেন খিদিরপুরে হেমচন্দ্র স্ট্রীটে (আগে নাম ছিল পদ্মপুকুর রোড)। দুতিনবার মাত্র গিয়েছি কাকার বাড়ি, তাও খুব অল্প সময়ের জন্যে। এর মধ্যে রায়বাহাদুরের মেয়ে গোপাকে না জানা খুব একটা মারাত্মক অপরাধ বলে মনে হয়নি। সহজভাবেই বললাম, না।
বিস্ময়ে দুচোখ কপালে তুলে রিনি বলল, তুমি কী ছোঁড়া? গোপা তোমাকে চেনে আর তুমি ওকে জান না?
সত্যিই ভাবিত হয়ে পড়লাম। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে গোপানামী মেয়েটির পরিচয়-রহস্য উদঘাটন করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।
রিনিই বাঁচিয়ে দিল। বলল, গোপা এবার ম্যাট্রিক পাশ করে বেথুনে আই.এ. পড়ছে। চেহারা আর পয়সার দেমাকে আগে আমাদের সঙ্গে কথাই কইত না। তোমার ছবি দেখে এসে যেচে আলাপ করেছে গোপা।
কৌতূহল বেড়ে গেল। বললাম, কী রকম?
রিনি বলল, আগে চোখাচোখি হলে মুখ ঘুরিয়ে নিত। কথাই কইত না। হঠাৎ কদিন থেকে দেখি আমাদের বাড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিন ছাদে কাপড় মেলে দিয়ে চলে আসছি, কানে এল, শোনো রিনি। আমি তো অবাক। চেয়ে দেখি ওদের ছাদের আলসের উপর ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে আছে গোপা। চলে আসব কি না ভাবছি, গোপা বলল, ধীরাজ ভট্টাচার্য, যিনি গিরিবালা ছবিতে নেমেছেন, তিনি তো তোমার ভাই হন, না? একবার ভাবলাম বলি, না। বললাম া। গোপা বলল, আগে মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়ি আসতেন, এখন আর দেখতে পাই না কেন?
কাকিমার গলা শুনতে পেলাম, রিনি!
রিনি বলল, মা ডাকছে, আমি চলি ছোড়দা!
বাধা দিয়ে বললাম, চলি মানে! তারপর কী কথা হল বল?
–ফিরে এসে বলব। একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল রিনি।
রায়বাহাদুরের সুন্দরী মেয়ে গোপার চেহারাটা কল্পনার তুলিতে আঁকবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।
.
বাইরের ঘরে কাকা ও বাবা কী একটা কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন, আমি ঘরে ঢুকতেই দুজনে চুপ করে গেলেন। কাকাকে নমস্কার করে চলে আসছিলাম, বাবা ডাকলেন, ধীউ বাবা, ভূপতির আফিসের বড়বাবু ও আরও অনেক অফিসার তোমার গিরিবালা দেখে এসেছেন। ওঁদের খুব ভাল লেগেছে। ভূপতির উপর হুকুম হয়েছে একদিন ওদের আফিসে তোমায় নিয়ে যেতে, আলাপ করবেন।
দেখলাম পুত্রগর্বে বাবার মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
আমার কাকার নাম ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবার মামাতো ভাই। কলকাতার একটা বড় সওদাগরী আফিসে সিনিয়র কেরানী।
কাকা বললেন, হ্যাঁ, আরও মুশকিল হয়েছে। ওরা কী করে জানতে পেরেছে ও আমার ভাইপো। তা যাস একদিন আফিসে, আলাপ করিয়ে দেব।
হঠাৎ কাকার এতখানি পরিবর্তনে মনে মনে বেশ খানিকটা বিস্মিত হলেও মুখে বললাম,যাব।
কাকা বললেন, বইটা লিখেছে তো রবি ঠাকুর। তা এইরকম বইয়ে নামলে লোকেও ভাল বলে, আর নামও হয়।
জবাব না দিয়ে চলে আসছিলাম, কাকা বললেন, আজকাল আমাদের বাড়ি যাসনে কেন?
বললাম, ছবির কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তা ছাড়া–
–তা ছাড়া কী?
–তা ছাড়া বায়োস্কোপে কাজ করি, যখন-তখন আপনাদের বাড়ি গেলে লোকের কাছে আপনার–
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকা বললেন, আমার মাথা নীচু হয়ে যাবে, না? ডেঁপোমিটুকু ষোল আনা আছে। ওরে মুখ, আমরা গুরুজনেরা যা বলি তোদর ভালর জন্যেই বলি। ওসব মনে রাখতে নেই।
কাকার বিব্রত অবস্থাটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বাবা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, গুরুজনের কথায় রাগ করতে নেই। যেদিন শুটিং থাকবে না, ঘুরে এসো খিদিরপুরে ভূপতির বাসায়।
ভূপতির বাসার চেয়েও বেশি আকর্ষণ আমার রায়বাহাদুরের প্রাসাদেই। কাজেই তখনই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম রিনির খোঁজে।
সারা বাড়ি নিঝুম নিস্তব্ধ, রিনির খোঁজ আর পাইনা। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে আসবার সময় মা আর কাকিমার গলা পেলাম।
কাকিমা বলছেন, এখনও বলছি তোমায় রাঙাদি, ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও। পরে একদিন দেখবে একটা মেমসাহেব, নয়তো বাজারের একটা অ্যাকট্রেসকে বিয়ে করে এনে তুলবে, নয়তো বিয়ে না করে তাকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকবে। বাড়িই আর আসবে না।
দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারলাম, মা আঁতকে উঠলেন। তারপর প্রায় কাদ-কাঁদ গলায় বললেন, কী হবে ছোটবৌ? আমি বলে বলে হার মেনে গিয়েছি। কর্তার ঐ এক কথা, ছেলে নিজে থেকে বিয়ে না করলে আমি কোনো দিন বলবো না। তুই একবার ঠাকুরপোকে দিয়ে বলতে পারিস?
উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাকিমা বললেন, তুমি যদি চাও বলতে পারি, কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। যাই বল দিদি, ভাশুরঠাকুর একটু নরম প্রকৃতির, পুরুষমানুষ একটু শক্ত না হলে চলে?
আর দাঁড়ানো নিরাপদ নয় মনে করে ডাকলাম, কইরে পার্ল হোয়াইট! রান্নাঘরের ভিতর থেকে একটা অব্যক্ত গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। বিস্মিত হয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে একনজর চেয়েই হেসে ফেললাম। রান্নাঘরের একপাশে মা আর কাকিমা মুখোমুখি গম্ভীর হয়ে বসে, আর একপাশে কাকার দুতিনটে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে রিনি একখানা বড় থালায় একগাদা পরোটা ও খানিকটা আলু-চচ্চড়ি নিয়ে তাদের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। মনে হল একখানা আস্ত পরোটায় খানিকটা আলুর চচ্চড়ি দিয়ে সেটা তালগোল করে পাকিয়ে মুখে পুরে। দিয়েছে রিনি, সেই সময় আমার ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই ঐ রকম গোঙানির আওয়াজ। দেখলাম, প্রাণপণে সেটা গেলবার চেষ্টা করেও পারছে না রিনি।
অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললাম, ব্যস্ত হবার দরকার নেই পার্ল হোয়াইট। পরশু রবিবারে তোদের বাড়ি গিয়ে গল্পটা শুনিয়ে আসব। এখন আমি বাইরে যাচ্ছি।
চলে আসতে যাচ্ছি, বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই কাকিমা বললেন, তবু ভাল, এতদিন বাদে গরিব কাকিমার কথা মনে পড়েছে ছেলের।
একটু আগে রিনির কাছে শোনা কাকার কথাগুলো বুকের মধ্যে কিলবিল করে উঠল। একটা কড়া জবাব দিতে গিয়ে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে হেসেই বললাম, গরিব হওয়ার ঐ এক মস্ত অসুবিধে কাকিমা। কেউ ফিরে তাকায় না, এমন কি ভগবান পর্যন্ত। তিনিও তেলা মাথায় তেল মাখাতে ব্যস্ত।
বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমার ঘরে ঢুকে পড়লাম।
বাইরে যাচ্ছি তো বলে এলাম, এখন যাই কোথায়? হঠাৎ মনে পড়ল আজ ম্যাডান স্টুডিওতে জাল সাহেবের পরিচালনায় আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ হিন্দি ছবিটার শুটিং আছে। হিন্দি ছবি মানে টাইটেলগুলো হিন্দিতে লিখে দেওয়া হবে। তাড়াতাড়ি ফরসা জামাকাপড় পরে বেরোতে যাচ্ছি, নজর পড়ল জুতোটার উপর। মনে হল যেন জিভ বার করে ভেংচি কাটছে। অনেকদিনের পুরোনো এলবার্ট, ডান পায়ের টো-এর বাঁ দিকের খানিকটা সেলাই ছিঁড়ে যেন হাঁ করে আছে। ছেঁড়া সুতোর টুকরোগুলো মনে হল দাঁত, আর সেই ছেঁড়া ফাঁকের মধ্যে বুড়ো আঙুলের খানিকটা জিভের মতো দেখা যাচ্ছে। একটু চললে বা পা নাড়লে ঠিক মনে হবে জিভ বার করে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। হতাশ হয়ে বিছানার উপর বসে পড়লাম। কিছুদিন আগে হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত গিরিবালার নায়ক এই ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়ে স্টুডিওতে যেতে পারে? বিদ্রোহী মন চিৎকার করে উঠল, কখনই না। তাহলে উপায়? বাবার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।
ট্রাম থেকে ধর্মতলায় নেমে চীনের দোকানের জুতো কিনব বলে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে উত্তরমুখোএগিয়ে চলেছি, ও হরি, সব দোকান বন্ধ। ব্যাপার কী! আশেপাশের দুএকজন মুসলমান দোকানীকে জিজ্ঞাসা করেও কোনও সদুত্তর পেলাম না। জুতো ব্যবসায়ী সব চীনেম্যান একজোট হয়ে ধর্মঘট করে বসল নাকি! হতাশ হয়ে অদ্ভুত নামের সাইনবোর্ডগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। থা থট, লুং ফো, লি চং, সুং হিং, মা থিন।
মা থিন! (যখন পুলিশ ছিলাম দ্রষ্টব্য) সারা দেহের উপর দিয়ে একটা বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। ফুটপাথের একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখনকার মতন আমার সর্বেন্দ্ৰিয় অবশ, পঙ্গু হয়ে গেছে। মাথা ঘুরছিল, পাশের একটি বন্ধ দোকানের সিঁড়ির উপর বসে পড়লাম।
কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম মনে নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। এক-পা দু-পা করে সেই সর্বনেশে সাইনবোর্ডের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভাল করে চেয়ে দেখি মা থিন নয়, নামটা মং থিন। অনুস্বরটা আকারের মতো এমন খাড়া করে লিখেছে যে, ম-এর মাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে। একটু দূর থেকে দেখলেই মা ছাড়া কিছুই মনে হবে না। হঠাৎ মনে পড়ল স্টুডিওর শুটিং-এর কথা। আপাতত জুতো কেনা স্থগিত রেখে ধর্মতলা থেকে টালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসলাম।
স্টুডিওতে ঢুকে দেখি গেট থেকে শুরু করে সারা স্টুডিও-চত্বরটা শুধু চীনেম্যান আর চীনেম্যান, কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের জুতোর দোকানগুলো কেন আজ বন্ধ, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।
মাথার প্রকাণ্ড টিকিটা মাটিতে পায়ের কাছে লোটাচ্ছে, ঠোঁটের উপর নাকের নীচে খানিকটা ফাঁক, তারপর দুটো সরু গোঁফ গালের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে বুকের কাছাকাছি। পরনে বিচিত্র রঙের ঢিলে পায়জামা, তার উপর ঢিলে আলখাল্লার মত রংচঙে চীনে প্যাটার্নের জামা, পায়ে চীনে চটি বা ক্যাম্বিসের অদ্ভুত জুতো, চণু আর চুরুটের ধোঁয়া, তার সঙ্গে অদ্ভুত দুর্বোধ্য ভাষা। সব মিলিয়ে মনে হলো স্টুডিওর আবহাওয়াটা বদলে গেছে। অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে একটু একটু করে এগোচ্ছি, সামনে দেখি মুখার্জি। অকূলে কূল পেলাম যেন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মুখার্জি বলল, চীনেপাড়ায় আজ চীনেম্যান নেই–তিনখানা লরি বোঝাই করে সব ঝেটিয়ে নিয়ে এসেছি।
জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এসব অদ্ভুত পোশাক-আশাক–
কথা শেষ করতে পারলাম না। মুখার্জি বলল, পার্শি অ্যালফ্রেড থিয়েটার আর কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের সমস্ত পোশাক, পরচুলো আর বারোজন ড্রেসার, মেক-আপ ম্যান কাল রাত্রের শো শেষ হবার পর থেকেই এখানে এসেছে। জাল সাহেবের শুটিং, একেবারে দুর্গোৎসবের ব্যাপার।
বেশ একটু কৌতূহল হল। বললাম, আচ্ছা মুখার্জি, জাল সাহেব খুব বড় ডিরেক্টর, না?
মিনিটখানেক চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল মুখার্জি। তারপর কী ভেবে বলল, নিশ্চয়ই! প্রথমত জাল সাহেব জাতে পার্শি, ম্যাডানদের আত্মীয়। তার উপর নিজে ক্যামেরা ঘোরান, সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেকশন দিয়ে থাকেন। বাপরে, এতগুলো কোয়ালিফিকেশন যার, তাকে বড় ডিরেক্টর বলতেই হবে–না বললে চাকরিই থাকবে না।
উত্তরের অপেক্ষা না করেই মুখার্জি চীন সমুদ্রে তলিয়ে গেল। একবার ভাবলাম বাড়ি চলে যাই, আবার তখনই মনে হল, এত বড় ব্যাপারটা না দেখে গেলে আফসোস থেকে যাবে। এক-পা, দু-পা করে ভিড় ঠেলে আবার এগোতে শুরু করলাম।
উত্তরমুখো আর একটু এগিয়ে দেখি পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন এবং আরও দু-তিনজন বাঙালি স্টুডিওকর্মী দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়–ডাকনাম মনু। অধুনা নিউ থিয়েটার্সের চীফ ক্যামেরাম্যান। আমার সমবয়সী। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। সব সময়ে মুখে পান আর দোতা ঠাসা, প্রতি কথায় অকারণে খানিকটা হাসা, এই নিয়েই মনমোহন। সাদা জামা-কাপড় পরে মনমোহনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা কওয়া খুব নিরাপদ ছিল না। তার ঐ অকারণ হাসির ধাক্কায় পান দোক্তার রস পিচকারির মতো প্রতিপক্ষের বুক রাঙিয়ে দিত। ভুক্তভোগী, তাই একটু দূর থেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী মনু, কাজকর্ম ছেড়ে এখানে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে?
এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার মনমোহন পরিচালক জ্যোতিষবাবুর নিকট আত্মীয়। অভিনেতা হবার প্রবল ইচ্ছে নিয়ে জ্যোতিষবাবুকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে ম্যাডানে ঢোকে। কিন্তু বাদ সাধলো ঐ পান আর দোক্তা। অনেক চেষ্টা করেও যখন মনমোহন ওদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারল না, তখন অগত্যা জ্যোতিষবাবু এডিটিং ডিপার্টমেন্টে ঢুকিয়ে দিলেন।
যা ভয় করেছিলাম তাই। নিমেষে কাছে এসে আমার ফরসা সাদা জামাটা ডান হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে এক পকড় হেসে নিল মনমোহন। তারপর বলল, জাল সাহেবের শুটিং, এ ফেলে কাজ? পাগল হয়েছিস?
ততক্ষণে আমার যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। জোর করে জামা থেকে ওর হাতখানা ছাড়িয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছি, হঠাৎ হুড়মুড় করে আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মুখখানা চেপে হাসতে শুরু করল মনমোহন। বেশ বিরক্ত হয়েই বললাম, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে?
হাসি থামিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলল মনমোহন, জালসাহেব, ঐ দ্যাখ ক্যামেরা ঘাড়ে করে চলেছে।
নামই শুনেছিলাম, চোখে কোনোদিন দেখিনি। স্থান-কাল-পাত্র এমন কি আমার শখের জামাটার পরিণাম ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। লম্বা খুব বেশি যদি হয় তো সাড়ে চার ফুট, চওড়া তিন ফুট। প্রকাণ্ড জালার মতো কুঁড়িটা প্রায় বুক থেকে নেমেছে। গায়ে লম্বা পার্শি কোট।পরনে সাদা জিনের প্যান্ট ঐ দীর্ঘ পার্শি কোটের আওতায় পড়ে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। প্রকান্ড একটা ধড়ের উপর ততোধিক প্রকাণ্ড একটা মুণ্ড কে যেন চেপে বসিয়ে দিয়েছে। গলা বলে কিছু নেই। মাংসল সুগোল লালচে মুখ, রোদে পোড়া রং। ভাটার মতো গোল দুটো চোখ, দেখলেই মনে হবে ভদ্রলোক সব সময় চটেই আছেন। ধ্যাবড়া বড়ির মতো ছোট্ট নাকের দুপাশ দিয়ে দুগাছা শ্রীহীন গোঁফ গালের পাশে নেমে এসেছে, যেন অবহেলার লজ্জায় মাথা উঁচু করে কারো দিকে চাইতে পারছে না। মাথায় লম্বা গোল পার্শি টুপি, একটু বেশি লম্বা, বোধহয় খোদার উপর খোদকারি করে উচ্চতা বাড়াবার চেষ্টা।
মনে হল জীবনে এই একটি বার মনমোহন অকারণে হাসেনি। অপলক চোখে চেয়েই আছি। সব মিলিয়ে মানবদেহে এতবড় একটা গরমিল আর কোনোদিন আমার চোখে পড়েনি।
চারপাশে বিচিত্র পোশাক পরা অগণিত চীনেম্যান, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যামেরায় হাত দিয়ে ম্যাডানের এস (ace) পরিচালক জাল সাহেব। পুরো নাম জাল খাম্বাটা না জাল মার্চেন্ট মনে নেই। মনমোহনের কাছে শুনলাম, জাল সাহেবের ছজন অ্যাসিস্টেন্ট। দুজন বাঙালি হিন্দু–অসিত ও জগন্নাথ। দুজন পার্শি, আর দুজনের একজন মুসলমান, অপরটি পাঞ্জাবী। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে একজন সহকারী হলেই পরিচালকের কাজ চলে যেত। গাঙ্গুলীমশাই, মধু বোস, জ্যোতিষবাবু এঁদের একজনের বেশি সহকারী ছিলেন না। শ্রদ্ধা ও কৌতূহল বেড়ে গেল। ভিড় ঠেলে খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আধ ডজন সহকারীর মাঝে নেপোলিয়নের মতো দাঁড়িয়ে আছেন জাল সাহেব। পাশে লম্বা তেপায়া স্ট্যান্ড এর উপর ফিট করা রয়েছে একটা কালো চৌকো কাঠের বাক্স। লম্বা প্রায় দেড় ফুট, চওড়া আট ইঞ্চি। বাক্সটার মাঝখানে একটা ছোট হ্যাঁন্ডেল ফিট করা, ঐটাই হল ক্যামেরা।
বেশ একটু অবাক হয়ে মনমোহনকে জিজ্ঞাসা করলাম, যতীন দাস যে ক্যামেরায় গাঙ্গুলীমশাই বা মধু বোসের ছবি তোলে সে তো হল এল-মডেল ডেবরি। এটা কী ক্যামেরা?
এবার আমার পিঠের উপর মুখ রেখে হাসল মনমোহন। বুঝলাম পৃষ্ঠরক্ষা করার চেষ্টা বৃথা।
একটু পরে মুখ তুলে বলল মনমোহন, ওটা হল প্যাথে নিউজরীল ক্যামেরা। অতি পুরোনো মডেল, আজকাল লেটেস্ট মডেলের অনেক ভাল ভাল ক্যামেরা বেরিয়েছে, কিন্তু জাল সাহেব সিনেমার শুরু থেকেই ঐটা আঁকড়ে পড়ে আছেন।
হঠাৎ চুপ করে গেল মনমোহন। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি বিচিত্র পোশাক পরা চীনেম্যানের দল হৈ-হল্লা করতে করতে পুবদিকের বাগানে ঢুকছে। এখানে বলে রাখি অত বড় ম্যাডান স্টুডিওটার সিকি অংশ শুধু পরিষ্কার করে শুটিং এর কাজ চলতো। বাকিটা, বিশেষ করে পুবদিকটা, ছিল একেবারে গভীর জঙ্গল, বড় বড় গাছ ও আগাছায় ভর্তি।
চীনেম্যানের দল বাগানে ঢুকছে, যেন রক্তবীজের বংশ। শেষই হয় না। আমাদের কাছ থেকে কিছু দূরে ঐ অদ্ভুত ক্যামেরাটার উপর একটা হাত রেখে সেনাপতির মতো অন্য হাত নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কী সব বলছেন জাল সাহেব। খানিকটা ইংরেজি, খানিকটা গুজরাটি আর উর্দু মেশানো। একটা কথারও মানে বুঝতে পারলাম না। সহকারী ছজন ছুটোছুটি করে একবার যাচ্ছে চীনেম্যানদের কাছে, আবার ছুটে আসছে জাল সাহেবের কাছে। রীতিমতো একটা যুদ্ধযাত্রার পূর্বাভাস। মনমোহনের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি নেই, রীতিমতো অবাক হয়ে চেয়ে আছে।
একটু পরে সব চুপচাপ।বিস্মিত হয়ে দেখলাম, যেন কোনো যাদুমন্ত্রে সব চীনেম্যান অদৃশ্য হয়ে গেছে স্টুডিওর জঙ্গলে। এইবার ক্যামেরাটি ঘাড়ে নিয়ে পুবমুখো করে দাঁড় করালেন জাল সাহেব। তারপর ডান হাত দিয়ে হাতলটা ঘোরাতে যাবেন, এমন সময়ে সহকারী জগন্নাথ কী যেন বলতে ছুটে এল জাল সাহেবের কাছে। বিকট পার্শি হুংকার ছাড়লেন জাল সাহেব। ভাষা না বুঝলেও যার ভাবার্থ হল :এখন কোনও কথা নয়, ডোন্ট ডিসটার্ব মি! বেশ একটু দমে গিয়ে হতাশ দৃষ্টিটা জঙ্গলের দিকে মেলে অপরাধীর মতো চেয়ে রইল জগন্নাথ।
কানের কাছে ফিসফিস করে বলে উঠল মনমোহন, ই, এ বাবা বাঘা ডিরেক্টর! কাজের সময় আজেবাজে কোনো কথাই চলবে না।
ক্যামেরার হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে জাল সাহেব হাঁকলেন, কাম ফরোয়ার্ড।
মিনিটখানেক চুপচাপ। শুধু একটানা ক্যামেরার ঘরর ঘরর আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।
কিন্তু কই? কেউ তো এগিয়ে এল না! আরও খানিকক্ষণ ক্যামেরা ঘুরিয়ে চললেন জাল সাহেব। তারপর হঠাৎ ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন হিন্দিতে, ইধার আ যাও ইউ ফুলস। এই হুংকারে চীনেম্যান একটিও এলো না, এলো ছজন সহকারী পরিচালক। ভয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ পাংশু হয়ে গিয়েছে।
জাল সাহেবের লাল মুখ আরও লাল হয়ে গিয়েছে। তার উপর ঘামে সমস্ত মুখখানা সপসপ করছে। রুমাল দিয়ে দুতিনবার মুছেও কিছু হলো না। রাগে ভিজে রুমালখানা আছড়ে মাটিতে ফেলে হিন্দি ও ইংরেজির তুবড়ি ছুটিয়ে দিলেন, ক্যা মতলব? হোয়াট ইজ অল দিস? হামারা ইন্ট্রাকশন্স ক্যা থা?
প্রথমটা ভয়ে কেউই জবাব দেয় না। আবার গর্জন করে উঠলেন জাল সাহেব, সে সামথিং ইউ বাঞ্চ অফ ফুলস।
অসিত এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দি ও বাংলায় একনিশ্বাসে বলে গেল, আপনি বলেছিলেন যে, আপনি প্রথমে আমাদের ইশারা করবেন, তারপর আমরা সাদা রুমাল নেড়ে ওদের আসতে বলব। আমরাও ওদের তাই বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি সে সব কিছু না করেই চেঁচিয়ে উঠলেন, কাম ফরোয়ার্ড।
–এনাফ। টেল দেম হোয়েন আই সে কাম ফরোয়ার্ড–কাম।
আবার ছুটল অ্যাসিস্টেন্টের দল জঙ্গলে। চারদিক থেকে শোনা গেল বহুকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন। চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব, খামোশ।
নিমেষে গুঞ্জন থেমে গেল। একটু পরে সহকারীর দল ফিরে এসে জানাল সব ঠিক আছে।
শুরু হলো শুটিং। ক্যামেরা খানিকটা ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়লেন জাল সাহেব–কাম ফরোয়ার্ড! একটু পরে দেখি ভয়ে মড়ার মতো পাংশু মুখে একটি একটি করে চীনেম্যান বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে, চোখে শঙ্কিত চাউনি।
আট-দশজন এইভাবে আসার পর হঠাৎ ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে শুন্যে একটা তুড়িলাফ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব, স্টপ, রোখখো!
চীনেম্যানের দল কিন্তু থামল না। একটির পর একটি এগিয়েই চলল। দুতিনটি সহকারী ছুটে গিয়ে ওদের হাত-মুখ নেড়ে কী সব বলতে তবে থামল।
এরই মধ্যে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন জাল সাহেব। দুহাত দিয়ে মাথার দুপাশের রগ দুটো টিপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে সহকারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, উন লোগোঁকো বোল দো ইট ইজ নট ফিউনারেল সিন, ইট ইজ হ্যাপি সিন। হাসনে বোলো।
তাই হলো, অনেক কষ্টে হাত-মুখ নেড়ে হেসে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, এটা শোকের বা দুঃখের দৃশ্য নয়, সবাই হাসতে হাসতে আসবে। আবার চীনের দল জঙ্গলে ঢুকল।
ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হলেন জাল সাহেব। জগন্নাথ কাছে এসে বলল, একটা কথা স্যার।
আবার চিৎকার করে উঠলেন জাল সাহেব, বাত নেহি মাংতা, কাম মাংতা। যাও, ডোন্ট ডিসটার্ব মি নাউ।
ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গিয়ে সঙ্গীদের ফিসফিস করে কী বলল জগয়াথ। ততক্ষণে জাল সাহেব ক্যামেরা ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছেন। একটু পরেই কাম ফরোয়ার্ড বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিলপিল করে চীনের দল আসতে শুরু করে দিল। ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টি তাদের জাল সাহেবের দিকে, মুখে জোর করে আনা এক অদ্ভুত হাসি বর্ষার ক্ষণিক ভিজে রোদের মতো নিষ্প্রাণ। ক্যামেরার পাশ দিয়ে এক এক করে সবাই চলে গেলে হাতল ঘোরানো বন্ধ করলেন জাল সাহেব। বুঝলাম, এ শটটা শেষ হল।
বেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল মনমোহন, এটা কী হাসি ভাই?
হেসে জবাব দিলাম, যে সিই হোক, তোমার হাসির চেয়ে ঢের নিরাপদ। এ হাসিতে মনে তো নয়ই, এমন কি জামা-কাপড়েও স্থায়ী ছাপ রেখে যায় না।
জাল সাহেবের গলা শুনলাম, সব কো বুলাকে জঙ্গল চলল। সেনাপতির মতো হুকুম দিয়েই স্ট্যান্ডসুদ্ধ ক্যামেরাটি ঘাড়ে করে জঙ্গলের পথ ধরলেন জাল সাহেব। সহকারীর দল ছুটোছুটি করে ঐ দেড়শ দুশ চীনেম্যান নিয়ে সঙ্গে চলল। মনমোহন আর আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো কৌতূহলী হয়ে চলতে শুরু করলাম।
একটু যেতেই অসিত আর জগন্নাথ কাছে এসে বলল–আর এগিয়ো না ভাই। দেখছো তো সাহেবের মেজাজ, তার উপর কড়া হুকুম দিয়েছে, যাদের কাজ আছে তারা ছাড়া কেউ যেন জঙ্গলে না ঢোকে।
অগত্যা ফিরে গিয়ে আমগাছতলায় দুখানা ভাঙা নড়বড়ে টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।
একটু পরে বহু লোকের সম্মিলিত বিকট হাসির আওয়াজ ভেসে এল জঙ্গলের দিক থেকে। অনুমানে বুঝলাম, চোখ রাঙিয়ে বা ভয় দেখিয়ে ঐ চীনের পালকে হাসাতে শুরু করেছেন জাল সাহেব।
বেলা প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। মনমোহনকে বললাম, চল বাড়ি যাওয়া যাক। ওদের ঐ জঙ্গলপর্ব শেষ হতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।
নীরব সম্মতি দিয়ে উঠে দাঁড়াল মনমোহন। গল্প করতে করতে দুজনে গেটের কাছে এসে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কাছে এলে চিনলাম, ভবেশ। ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী ভবেশ? ও-রকম করে ছুটে চলেছ কোথায়?
দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে বলল ভবেশ, আপনাদের কাছেই আসছিলাম।
বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, তার মানে!
ভবেশ বলল, এর মধ্যেই চললেন কোথায়?
বললাম, বাড়ি।
বিজ্ঞের মতো একটু হেসে বলল ভবেশ, নাচ না দেখে বাড়ি যাবেন না। সারা জীবনের মতো আফসোস থেকে যাবে।
মনমোহন আর আমি প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম, নাচ! কোথায়?
একনিশ্বাসে বলে গেল ভবেশ, একটা অপূর্ব সুন্দরী বাঙালি মেয়েকে নিয়ে এসেছেন জাল সাহেব এই ছবিটায় একটা নাচের জন্যে। একটা সিনের ছোট্ট একটা নাচের পারিশ্রমিক পাঁচশ টাকা। বেলা দুটো থেকে তিনটে ড্রেসার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাকে পোশাক পরাতে, এখনও শেষ হয়নি।
উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, ভবেশ, তোমার উপকার জীবনে ভুলব না। এ নাচ না দেখে যদি বাড়ি যাই, সারা জীবন তীব্র অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরলেও তার ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হবে না।
আর কোনও কথা না বলে অ্যাবাউট টার্ন করে স্টুডিওয় ঢুকতে যাব, পিছনে জামাটায় টান পড়ল। ফিরে দেখি মনমোহন। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বলল, আমি বলছি নাচের এখনও বেশ দেরি আছে। ততক্ষণ চ না ভাই, মোড়ের দোকান থেকে এক কাপ চা আর পান খেয়ে আসি।
ভেবে দেখলাম, কথাটা মন্দ বলেনি মনমোহন। এতক্ষণ ভুলে একরকম ছিলাম ভাল। মনে করিয়ে দিতেই প্রাণটা চা-চা করে আর্তনাদ করে উঠল। চেয়ে দেখি, লোভাতুর দৃষ্টিটা গোপন করবার অছিলায় অন্য দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভবেশ। বললাম, এত বড় একটা সুখবর এনেছ, প্রতিদানে অন্তত এক কাপ চা না খাওয়ালে নেমকহারামি হবে, এস ভবেশ। তিনজনে দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটতে হাঁটতে টালিগঞ্জের তেমাথায় সবেধন নীলমণি দোকানটিতে ঢুকে তিন কাপ চা ও তিনটে ওমলেটের অর্ডার দিয়ে বাইরের বেঞ্চিটায় বসে পড়লাম।