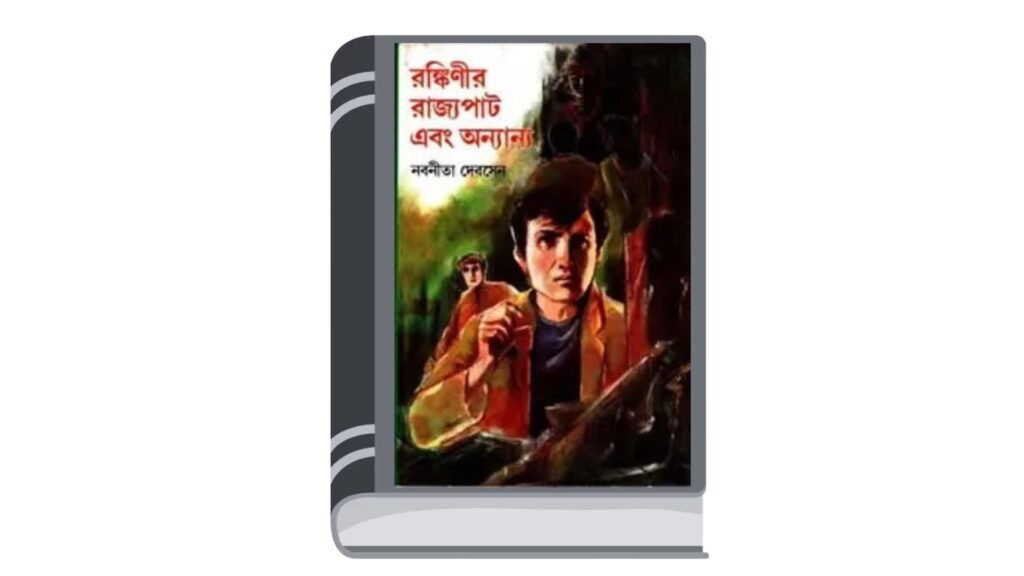প্রথম পর্ব – রঙ্কিণীর রাজ্যপাট
টুলকি
জেঠুমণি কাগজ পড়ছিলেন না।
একমনে একটা ছবি দেখছিলেন। পুরনো, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, পোকায় ফুটো ফুটো করে দেওয়া একটা সিপিয়া কালারের ফোটোগ্রাফ। এক মহিলার ছবি।
না, আমাদের বড়মার ছবি নয়।
বড়মাকে কোনো উপায়েই এই ভদ্রমহিলার মতো দেখতে বলা যাবে না। কিন্তু ছবিটা আমার কেমন যেন চেনা—চেনা লাগছে। যেন আগে কোথাও দেখেছি। বড়মার মৃত্যুর পর থেকে জেঠুমণি বড় একলা হয়ে গেছেন। নিজে নিজে পেশেন্স খেলেন। আর আমাদের কাউকে ধরে এনে দাবা খেলেন। জেঠুমণি বলেছিলেন রিটায়ার করে, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস পেলে তো অনেক টাকা হাতে আসবে। তখন আমাদের জন্যে ছোটনাগপুরে কোথাও একটা বাংলোবাড়ি বানাবেন। হাজারিবাগ—টাগের দিকে। লালমাটি আর শালবনের মধ্যে। লালটালির ছাদওয়ালা সাদা কটেজ। মস্ত বড় বাগান থাকবে। উঠোন থাকবে। উঠোনে ইঁদারা থাকবে। তার জল শীতকালে উষ্ণ আর গ্রীষ্মকালে শীতল। বড়মা ঐরকম একটা বাড়িতে জন্মে বড় হয়েছিলেন। কলকাতায় এসে অবধি সারা জীবন ওঁর মন কেমন করত ঐরকম একটা বাড়ির জন্যে। ‘পশ্চিমের মেয়ে’ তিনি। বিয়ে হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। শ্বশুরবাড়িতে। আমরা তো চিরকালই কলকাতার। চিরকাল না হোক, অনেককাল। দাদু ঠাকুমা তো কলকাতাতেই থাকতেন—এই বাড়িটা তো দাদুরই। বাবারা সবাই কলকাতার লোক। এই বাড়িতেই বড় হয়েছেন সবাই—এক জেঠুমণি ছাড়া। শুনেছি জেঠুমণির ছোটবেলায় দাদু কার্মাটার না কোথায় যেন কাজ করতেন। সেও ‘পশ্চিমে’। আমরা তো সকলে এই ভবানীপুরেই জন্মেছি, বড়ো হচ্ছি। এতদিন বাড়িটা আমাদের একদম ভরভর্তি ছিল। তারপর প্রথমে ঠাকুমা। তারপরে দাদুভাই—এক এক করে দু’বছরে দু’জনেই চলে গেলেন। তার ওপরে হঠাৎ একদিন বড়মাও। বড়মা চলে গিয়ে আমাদের পরিবারটা হঠাৎ যেন কেমন মলিন হয়ে গেছে। বড়মা একটা বটগাছের মতন সকলকে স্নেহের আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিচ্ছু হয়নি অসুখ—বিসুখ। হঠাৎ স্ট্রোকে অজ্ঞান, আর জ্ঞান ফিরলই না। জেঠুমণিও রিটায়ার করলেন তার পরেই। অফিসে যাওয়া বন্ধ, বাড়িতে আছেন, অথচ বড়মা নেই। বড়মাই তো সারাদিন বাড়িতে থাকতেন। বাবা, মা, কাকুমণি, ছোটমা, সবাই কাজে বেরিয়ে যান। আমাদেরও স্কুল কলেজ আছে—জেঠুমণি বাড়িতে একলা হয়ে গেছেন হঠাৎ। বাড়িতে এখন তিনজন মানুষ কমে গিয়ে, আমরা তিন ভাইবোন, বাবা, মা, কাকু—ছোটমা, আর জেঠুমণি—মাত্র এই আটজন থাকি। দাদু—ঠাকুমার ঘরটা খালি। ওটাকেই এখন আমাদের পড়াশুনার ঘর করে দিয়েছেন ছোটমা। কম্পিউটার বসেছে ওঘরেই। পড়ার টেবিল। বইয়ের সেলফ সব ওখানে। এতদিন আমাদের পড়াশুনোর জন্যে আলাদা কোনো ঘর ছিল না। যদিও কলকাতার লোকের বাড়িঘরের তুলনায় আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা আছে। বড়মা খোলা—মেলা আকাশ বাতাসে মানুষ, তাঁর কলকাতায় দমবন্ধ লাগতো। তাই তাঁর জন্যেই জেঠুমণির প্ল্যান ছিল ”পশ্চিমে” একটা বাংলো বানাবেন। কিংবা কিনবেন। ওদিকে নাকি পুরনো সাহেবদের বাড়ি বিক্রি হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু বড়মাই নেই, ওই বাড়িটাড়ির প্ল্যানও আর শুনতে পাই না।
এবাড়িতে বাবামা, ছোটমা, কাকু, জেঠুমণি বড়মা আর পিসিমণি—পিসেমশাইয়ের বড় বড় চারটে ঘর আছে। তাছাড়া বৈঠকখানা ঘর, খাবার ঘর, দুটো রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বক্সরুম, ঠাকুরঘর, কাজের লোকেদের দুটোঘর, ছাদে চিলেকোঠা, আর নিচে একটা গেস্টরুম আছে, ঠাকুমা দাদুর ঘর বাদ দিলে। এই ঘরটা খুব বড়, দিব্যি আলোবাতাস খেলে। সঙ্গে দক্ষিণের বারান্দা আছে, অ্যাটাচড বাথরুম—এখন আমাদের পড়ার ঘর। আমাদের বাড়িতে মাটি নেই। ‘লন’ নেই, ঘাসটাস নেই—এটাই চিরজীবন বড়মার দুঃখু ছিল। কিন্তু আমাদের বাড়িটা আমার খুব ভালো লাগে। হোক তিনতলা। তবু, ফ্ল্যাট তো নয়। আমার বন্ধুরা বেশিরভাগই সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাটে থাকে। খুব সুন্দর, কিন্তু তত জায়গা নেই। আমাদের বাড়িটায় অনেকগুলো ঘর অনেকগুলো বারান্দা। গোটা একটা ছাদ আছে। কিন্তু বাগান নেই। আমার বড়মার খুব দুঃখ ছিল সেটা। তাই তিনি ছাদেই চমৎকার একটা বাগান তৈরি করেছিলেন। বড়মা থাকতে তিনিই সেটার যত্ন নিতেন, এখন মা দেখাশুনো করেন। বড়মাকে আমরা সবাই খুব মিস করি।
আমাদের সঙ্গে বড়মার তেমন ”ভাব” ছিল না, ছোটমার সঙ্গে যেমন ভাব—ফ্রেন্ডশিপ—কিন্তু বড়মা সর্বদাই আমাদের পক্ষে ছিলেন। সবদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। খুব আদর দিতেন আমাদের—মা যখনই কমপ্লেন করতেন আমাদের নামে, তখনই বড়মা সেটার মীমাংসা করে দিতেন।—আমরা সর্বদাই যে নিরপরাধ প্রমাণ হতুম তা নয়, তবু বড়মা ছিলেন খুব ‘ফেয়ার’। কোনো অনুচিত শাস্তি দিতেন না। আর উচিত শাস্তি তো হওয়াই ঠিক—আমাদের সব শাস্তিই হতো পড়াশুনো, অথবা ঘরকন্নার কোনও কাজ। ঐ ফাঁকে সেটি করিয়ে নেওয়া। কবিতা মুখস্থ, আলনা গোছানো, ড্রয়ার সাফ করা বা নিজের কাপড়চোপড় ইস্তিরি করা—এইরকম। কক্ষনো ‘দুই থাপ্পড়’ জাতীয় শাস্তি নয়। বড়মা আজ নেই কিন্তু মা—কাকিমা পুটুসের বেলায় সেইরকমই শাস্তির ব্যবস্থা করেন। পুটুস আমাদের খুড়তুতো ছোট ভাই। কাকু আর ছোটমার ছেলে। আর কুলটু আমার ঠিক পরের ভাই। আমি যাদবপুরে ঢুকেছি এবছরে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি হিস্ট্রি। বুলটু টেনে। পুটুস থ্রি। আমাদের আরেক বোন আছে, পুলকি। আমাদের চেয়ে দু’বছরের ছোট। ইলেভেনে পড়ছে—আমাদের পিসতুতো বোন। আমি টুলকি, সে পুলকি। পিসিমণি আমাদের একটাই, আর পিসতুতো বোনও একটাই। পিসেমশাই ল’ইয়ার আর পিসিমণি বায়ো—কেমিস্ট। আমাদের এই চার ভাইবোনের একটা দল আছে। পুলকি পড়ছে পাঠভবনে, আমরা সাউথ পয়েন্টে। পুটুসটা খুব ছোট তবু ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবেই বুলটুর ল্যাংবোট হয়ে। আমি আর পুলকি সবকিছু একসঙ্গে করি। বুলটুটা মাঝে মাঝে পুলকিকে ভীষণ খ্যাপায়। ওরা তো পিঠোপিঠি, আগে আগে মারামারিও করতো দুজনে। এখন বড় হয়ে গেছে, এখন ব্যাপারটা খ্যাপানোতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পুলকিও কম যায় না। বুলটুকেও যথেষ্ট হেনস্তা করতে পারে। আমি দিদি—আমাকে সববাই ভয় পায়। ভয় না পাক, মান্য করে। জেঠুমণি তো আমার নামই দিয়ে দিয়েছেন ‘দ্য লিডার’। জেঠুমণি দারুণ ভালো দাবা খেলতে পারেন। আমাকে আর বুলটুকে শিখিয়ে দিয়েছেন—বুলটুকে বলেন চেষ্টা করো, কাসপারভ হতে। দিব্যেন্দু বড়ুয়া তো হতে চেষ্টা করতেই পারো? কী দারুণ খেলতো ছেলেটা। মেয়ে—দাবাড়ু কেউ তেমন নাম করেনি বলেই বোধহয় জেঠুমণি আমাকে তেমন করে বলেন না। কিন্তু আসলে বুলটুর চেয়ে আমিই বেশি ভালো খেলি দাবাটা। বুলটু ক্রিকেট বেশি ভালোবাসে। তবু জেঠুমণি ওকেই বলেন World champion হতে—আমাকে বলেন না।
দাদুঠাকুরমার ঘরটা ঠিক পড়ার ঘর হয়নি। না। হয়েছে। পড়ার ঘরও হয়েছে, আবার দিব্যি আড্ডার ঘরও হয়েছে। দাদুঠাকুমা দুজনেই খুব গল্প বলতে ভালবাসতেন। এক নম্বর আড্ডাবাজ ছিলেন দাদু। দিদিমা তেমন আড্ডাবাজ না হলেও ঘুমপাড়ানি গল্প বলার রানী ছিলেন। তাঁদের ঘর। আড্ডার আমেজ না থেকে পারে?
আমাদের দাবার বোর্ডটা একটা antique জিনিস—ছোট্টো একটা পুরনো কাঠের টেবিলের মধ্যে তৈরি—করা সাদাকালো চৌখুপি। সাদাগুলো বোধহয় হাতির দাঁতই হবে। কিন্তু হাতির দাঁতের তৈরি ঘুঁটিগুলো আর নেই, হারিয়ে টারিয়ে গিয়েছে। ঘুঁটিগুলো কাঠের সবই—সাদাও কালোও। জেঠুমণি দারুণ ভালবাসেন দাবা খেলতে। কাকুও খেলে। তবে তার চেয়ে গল্পের বই পড়তে বেশি ভালবাসে, আর টিভি দেখতে। বাবার দাবা খেলা পছন্দ নয়, গল্পের বই পড়াও পছন্দ নয়, বাবার একটু সিরিয়াস টাইপের বইটই পড়ার অভ্যাস। সেগুলো উলটে দেখতেও ভাল লাগে না আমার। তবে বাবা গান ভালবাসেন। গান শোনেন খুব। মা? মা কী ভালবাসেন?—মা তো টিচার? ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেই ভালবাসেন, পড়াশুনো করতেও ভালবাসেন। আর ভালবাসেন রান্না করতে। রান্না করতে অবশ্য জেঠুও ভালবাসেন। মাংস। শুধু মাংস রান্না করতে জানেন জেঠুমণি। যখনই বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হয় জেঠুমণি নামেন আসরে। মাংস কেনা থেকে শুরু হয়, পরিবেশনে এসে শেষ। কাকু খুব খ্যাপায় জেঠুমণিকে, এই মাংস রান্না নিয়ে। নিজে এক কাপ চা—ও বানাতে পারে না কিন্তু। ছোটমা কুকারি ক্লাসে গিয়ে অনেক বিলিতি রান্না শিখে এল। আভেন কেনা হল। ক’দিন কেক প্যাটিস হল। তারপর ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো। ছোটমার রান্নার ইন্টারেস্ট মিটে গেল। পুটুসটা যা দুরন্ত ছিল। এখনও ভীষণ দুরন্ত। কুলটু অত দুষ্টু ছিল না, পুটুসের মতো। বুলটু মিচকে শয়তান। ঠাকুমা বলতেন কাকু নাকি ঐরকম ছিল, আর বাবা ছিলেন পুটুসের মতো দুরন্ত। জেঠুমণি কেমন ছিলেন, ঠাকুমা বলতেন, খোকা? খোকার তুলনা হয় না। ওর জন্যে আমি কোনও কষ্ট পাইনি। খুব শান্ত ছিল। দাবা দিয়ে বসিয়ে দাও দিন কেটে যাবে, খেতেও চাইবে না। জেঠুমণি নাকি দাবা শিখেছিলেন তাঁর জেঠুর কাছে। সেই যে তিনি, জেঠুমণির জেঠু—দাদুর দাবা, তিনি নাকি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে আসতেন, পরনে গেরুয়া পোশাক, কাঁধে একটা ঝোলা, পায়ে গেরুয়া কেডস জুতো। মাথায় বিবেকানন্দের মতো পাগড়ি। এতটুকুই মনে আছে বাবার। জেঠুমণির মনে আছে। এই টেবিলটা তিনিই একদিন কিনে দিয়েছিলেন কোথা থেকে। আর ছোট্ট জেঠুমণিকে দাবা খেলতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন ঘুঁটিগুলো হাতির দাঁতের ছিল। জেঠুমণির জ্যাঠামশাইকে কাকু দেখেননি। তাঁর জন্মের আগেই তিনি উধাও হয়ে যান হিমালয়ে। কেউ আর তাঁর কোনও খোঁজ পায়নি। সন্ন্যাসী মানুষরা নাকি এইভাবেই পৃথিবী ত্যাগ করেন। কাকু তাঁকে দেখেনি।
বাবার জ্যাঠামশাই নাকি খুব ছোটোবেলায় দেশের বাড়ি থেকে উধাও হয়েছিলেন। দাদু বলতেন সেই গল্প। ‘হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখা গেল রাঙাদা নেই!’ রাঙাদা কেন? উনিই তো একমাত্র দাদা। না, আরও সব জ্ঞাতি সম্পর্কে দাদারা ছিলেন। কি আশ্চর্য, না? দাদুর সেই বড়দা মেজদারা সব কে কোথায় আছেন কে জানে? দাদু নেই, তাঁর দাদারাও নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েরা? দাদুরা তো ছিলেন পূর্ববঙ্গের মানুষ। দেশভাগের অনেক বছর আগেই ওঁরা এদেশে চলে এসেছেন। সেই মেজদা—সেজদারা আসেননি। তাঁরা রয়ে গিয়েছেন জন্মভূমিতে। সেটাই এখন অন্যের দেশ। দাদুর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল না।
দাদুর দাদা ঐ পূর্ববঙ্গ থেকেই পালিয়ে গিয়েছিলেন একদিন। সন্ন্যাসী হবার জন্যে। তখন দাদুর বাবামা বেঁচে। বাবা মারা যাবার পরে তিনি নাকি প্রথম বাড়ি ফিরেছিলেন। গেরুয়া পরে এসে মার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। প্রণাম করেননি। সাধু সন্ন্যাসীদের বুঝি মাকেও প্রণাম করতে নেই কিন্তু বলেছিলেন—”মা তোমার একজন তো হারিয়ে গেল, কিন্তু আরেকটা হারানো জিনিস ফিরে এল।” তারপর মার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। দাদুর মা মারা যাবার পরও দাদুঠাকুমার কাছে এসেছেন কিছুদিন, জেঠুমণিকে, বাবাকে আদর করেছেন। কাকু জন্মানোর পরে আর আসেননি। দাদু মাঝে মাঝে বলতেন তাঁর দাদার কথা। জেঠুমণিও বলেন, ঐ দাবার ছকটা তাঁকে তাঁর জ্যাঠামশাইকে ভুলতে দেয় না।
আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে এই বাড়িতে। আজকে আমাদের দাদুর খোঁজ করতে তিনজন মানুষ এসেছিলেন! তাঁরা নাকি দাদুর ভাইপো হন। দাদুর সেই সন্ন্যাসী দাদার ছেলে।
হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ভাই।
আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, যে এরকম হতে পারে। সত্যি সত্যি হয়? এতদিনের হারানো সম্পর্কের মানুষ ফিরে আসে? সন্ন্যাসীর আবার ছেলেপুলে থাকে নাকি? সন্ন্যাসীরা তো ব্যাচেলর মানুষ, তারা সংসারই করে না।
কিন্তু হ্যাঁ। সন্ন্যাসী হবার আগে যদি সে বিয়ে করে, তার সংসার হয়, তবে সম্ভব। নতুবা, সন্ন্যাসধর্ম ছেড়ে সে যদি গৃহস্থ হয়ে যায়, তবে। আজ আমাদের বাড়িতে যে আজব ঘটনার সাক্ষী হয়েছি আমি, মা আর জেঠুমণি, সেসব কেবল রহস্য রোমাঞ্চের বইতেই পাওয়া যায়। আমার ভেতরে ব্যাপারটা, সবটা যেন এখনও ঠিক ঢোকেনি। ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না—এরকম গল্পের বইয়ের মতো ঘটনা কখনও আমাদের জীবনেও ঘটতে পারে। এতবছর পরে হঠাৎ জেঠুমণি জানতে পারলেন তাঁদের একদল অচেনা ভাইবোন আছে। জ্যাঠতুতো ভাইবোন। আপন জ্যাঠতুতো ভাইবোন। আমাদের দাদুর নাম ছিল সারদাপ্রসাদ, তাঁর দাদার নাম শম্ভুপ্রসাদ। এরা সব দাদুর সেই দাদার ছেলে। শম্ভুর সঙ্গে মিলিয়ে আর বংশের ‘S’ অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের প্রত্যেকের নাম—বাবা, কাকু, জেঠুমণির সঙ্গে খুব মিলে যায়। আমি তাঁদের দেখেছি। দেখলে একজনকে সত্যিই মনে হয় জেঠুমণির ভাই। অনেকটাই কাকুমণির মতো দেখতে। দেখলে একজনকে সত্যিই মনে হয় জেঠুমণির ভাই। অনেকটাই কাকুমণির মতো দেখতে। অন্য দুজনের চেহারায় সাঁওতালী ধরন আছে। জেঠুমণি একেবারে অবাক। উনিও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তাঁর জেঠামশাই সন্ন্যাস ত্যাগ করে সংসারে ফিরেছিলেন, অথচ একদিনের জন্যেও এখানে আসেননি। এদিকে সন্ন্যাসজীবনে তো এখানে অনেক এসেছেন। ভদ্রলোকের বয়স জেঠুর চেয়ে অনেক কম। একজনকে তো কাকুর চেয়েও ছোট বলে মনে হচ্ছিল দেখে। ওদের গল্প শুনে জেঠুমণি তো স্ট্যাচু! দাদু তো মারা গেলেন গতবছর নাইনটি কমপ্লিট করে। দাদুর দাদার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তারও পরে। মাসতিনেক আগে, হঠাৎ সেরিব্রাল স্ট্রোকে। মৃত্যুর পরে তাঁর উইল আবিষ্কৃত ও পাঠ করা হয়েছে। তাতে তাঁর বিপুল ভূসম্পত্তির মধ্যে আমাদের জন্যে তিনি দিয়ে গিয়েছেন তিরিশ শতাংশ জমি। দাদুর নামেই দানপত্র করা হয়েছে। কিন্তু দাদুর অবর্তমানে তাঁর দুই ছেলে সত্যপ্রসাদ ও শুভেন্দুপ্রসাদ পাবেন শম্ভুপ্রসাদের প্রদত্ত সেই ভূসম্পত্তি। ছেলেগুলি অনেক চেষ্টায় দাদুর ছোট বোন, বাবার পাতাপিসিকে খুঁজে বের করেছে। পাতাপিসির কাছ থেকে পেয়েছে আমাদের এই নতুন ঠিকানা। রীতিমতো রিসার্চ করেই আমাদের খোঁজ পেয়েছে। ওরা তো কলকাতার লোক না। ঝাড়খণ্ডের। যাকে আমরা বলি ঝাড়খণ্ড? এখন প্রশ্ন হচ্ছে শম্ভুপ্রসাদ, দাদুর দাদা তো সন্ন্যাসী ছিলেন—অকস্মাৎ তিনি ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে লোধা—মাহাতোদের গ্রামে গিয়েছিলেনই বা কেন? ওদের মেয়েকে বিয়ে—থাই বা করলেন কেন? কী করেই বা করেছিলেন? এত সম্পত্তি এল কোথা থেকে? বাবার জ্যাঠামশাইয়ের এসব জমিজমা আছে সেখানেই। ঝাড়খণ্ডে। অনেকখানি জায়গাজমি খেতবাগান পুকুরটুকুর করেছিলেন—সেসব ছেড়ে দিয়ে এঁরা মেদিনীপুরের শহরে চলে যেতে চাইছেন। ‘জনযুদ্ধের’ সন্ত্রাসে গ্রামাঞ্চলে টেঁকা কঠিন। জমি তো বেচতে হবে—তাই তাঁর কাগজপত্তর ঘাঁটতে গিয়ে দেখা গেল ছোটভাই সারদাপ্রসাদকেই দিয়ে গেছেন সম্পত্তির তিরিশ ভাগ। তিরিশ তিন পুত্রকে। স্ত্রীকে বিশ। দুই মেয়েকে বিশ। এখন তাঁর সেই ছোটভাই সারদাপ্রসাদ তাঁর তিরিশ ভাগ বিক্রি করতে চান, না ভোগ করতে চান, সেটা খবর নিতেই এসেছিল তিনজন ভাই। জেঠু বললেন, তোমরাই তো শম্ভুপ্রসাদের ছেলে, তার প্রমাণ কি? তার জবাবে তারা শম্ভুপ্রসাদের মায়ের একটি ছবি দিয়েছে জেঠুমণিকে। আর দিয়েছে শম্ভুপ্রসাদের উইলের একটি জেরক্স কপি করা পাতা। জেঠুমণি সেই ছবিটাই দেখছেন সকাল থেকে। জেঠুমণির ঠাকুমার ছবি।
বুলটু
আজ একটা স্ট্রেঞ্জ ডে।
সকাল না সন্ধ্যে, বোঝা যাচ্ছে না।
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি।
কিছু ভালো লাগছে না আমার। আজ খেলতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু এতটা বৃষ্টির মধ্যে সেই মুকুন্দপুরে খেলতে যাবে কে। মাঠে প্রচুর কাদা থাকবে। পা মচকে গিয়েছিল তিন হপ্তা আগে, এখনও সারেনি ঠিকমতো, পিছল মাঠে নামতে সাহস নেই। একটু আগে কুশল ফোন করেছিল। যাবো না বলে দিয়েছি।
বলে তো দিলুম ‘যাবো না’, কিন্তু মেজাজও ভালো লাগছে না।
কী করি কী করি।
দিদিকে ধরা যাক যদি দাবা খেলতে বসে। দিদিটা দারুণ দাবা খেলে, আমাকে খেলতে শিখিয়েছে ও—ই। আর দিদিকে শিখিয়েছেন জেঠুমণি নিজে। জেঠুমণিই এখনও বাড়ির বেস্ট প্লেয়ার, যদিও দিদি বলে ”বুলটুই বেস্ট”। মাত্র দু বছরের বড়ো হলে কি হবে, ভাবটা এমন, যেন দিদি। আমার দিদি নয়, দিদিমা।
দিদি খেলবে না। শি ইজ বিজি ওয়াচিং টিভি। মন দিয়ে টিভি দেখছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে ”নেফারতিতি” বলে ডকুমেন্টারি দেখাচ্ছে। পিরামিডের ধনরত্ন, টুটানখামেনের সমাধি। হাঁ করে ঐসব দেখছে দিদি। শি লাভস ইজিপ্ট। ওর একটা ‘মিসর—বাতিক’ আছে। প্রায়ই দেখায় এই প্রোগ্রামটা। আমিই দু’তিনবার দেখেছি। দিদির প্রত্যেকবারই দেখা চাই। ও ইজিপ্টোলজিস্ট হতে চায়।—”অনেকবার তো দেখলি ওটা, এবার চল না—এক দান খেলবি—”
—”তুই জেঠুমণিকে ডেকে নে না—জেঠুমণি তো কাগজ পড়ছেন এখনও। তুই ডাকলেই খেলবেন।”
আমি ডাকতে গেলুম। জেঠুমণি কিন্তু কাগজ মোটেই পড়ছিলেন না। একটা সিপিয়া রঙের আবছা মতন ফোটোগ্রাফ দেখছিলেন মন দিয়ে। আমাকে দেখেই বললেন, ”তোর ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা নিয়ে আয় তো বুলটুন?”
ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আমার একটা আছে, কবে সেই খেলনার ‘সায়েন্স সেট’ উপহার দিয়েছিল কাকু ছোটবেলাতে, তাতে কিন্তু সত্যিকারের ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা ছিল। জেঠুমণি আমাকে আদর করে বুলটুন, দিদিকে টুলকুন ডাকেন। আর পুটুসকে বলেন পুটকুন। বড়মার দেওয়া নাম পুটকুন। আমি ভেবেছি বুঝি ফোটোটা বড়মার। কাছে যেতে জেঠুমণি নিজেই ডেকে দেখালেন—”দেখে যাও। তোমার বাবার ঠাকুমা—তোমাদের কর্তামাকে দেখে যাও।”
ছবিটা আমিও চিনতে পেরেছি—এরকম একটা ছবি আমাদের অ্যালবামেও আছে, ঘোমটা মাথায় টিপপরা নাকে নথ—মুখটা বেশ সুন্দর—মা দেখিয়েছিলেন একবার। বাবা জেঠুদের grandparents ঠাকুর্দা ঠাকুমা। আমাদের ঠাকুমাকে তো আমরাই দেখেছি। পুটুস দেখেনি অবশ্য। ইনি তিনি নন। ইনি আমাদের ঠাকুর্দাদার মা। অর্থাৎ বাবার ঠাকুমা। শ্রীমতী মনমোহিনী দেবী। জেঠুমণির কেমন একটা নস্টালজিক মুড এসেছিল আজ, বোধহয় এই বৃষ্টি বৃষ্টি ভাবটাই দায়ী। জেঠুমণি ওঁদের ছোটবেলার কথা বলছিলেন আমাকে। বলছিলেন, এই ঠাকুমা তাঁদের কত যত্ন করেছেন।—জেঠুর জ্যাঠামশাই বাড়ি থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন বলে জেঠুর ঠাকুমার দুঃখের নাকি শেষ ছিল না। জেঠুর বাবা—মার কাছেই থাকতেন ঠাকুমা, মানে আমাদের ঠাকুর্দাদা ঠাকুমার কাছেই—কিন্তু সারাক্ষণ বড় ছেলের জন্যে মন খারাপ করতেন, মাঝে মাঝে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে যেতেন হারিয়ে যাওয়া ছেলের খোঁজে—ঠাকুর্দাই সঙ্গে নিয়ে যেতেন তাঁর মাকে, হরিদ্বারে, বেনারসে, এমনকি এলাহাবাদের কুম্ভমেলাতেও গিয়েছিলেন ওঁরা। সেই বছরে নাকি নাগাসন্ন্যাসীদের হাতির দল তাণ্ডব করেছিল, স্ট্যামপিড হয়ে অনেক তীর্থযাত্রী মানুষ মারা গিয়েছিল। ঠাকুর্দা তাঁর মাকে নিয়ে ঠিকঠাক ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে ভীষণ ভয়ে উদ্বেগে কষ্ট পেয়েছিল বাড়িতে সবাই। তার পর থেকে কর্তামা নিজেই নাকি ছেলেকে খুঁজতে বেরোননি আর।
আজ যে ছবিটা জেঠুর হাতে দেখলুম সেটা ওঁর সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলের কাছে ছিল। মায়ের ছবিটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সেই সন্ন্যাসী ছেলে! অথচ, জেঠুই বলছিলেন সন্ন্যাসী হতে হলে নাকি নিজের পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হয়। বাবা—মা—ভাইবোন সকলকে ভুলে যেতে হয়—নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে, নতুন করে সন্ন্যাসী জন্ম নিতে হয়। সেই পুরনো মানুষটাকে তখন as good as dead, মৃত। কিন্তু সপরিবারেই কি মৃত? তারা তো মরেনি। তাদের কেন ভুলে যাবে? অথচ জেঠু বলছিলেন পুরনো আইডেনটিটিটা পুরোপুরি অস্বীকার করতে হয়। মুছে ফেলতে হয়, recognize করতে নেই, মাকে মা নয়, বাবাকে বাবা নয়। স্ত্রীকে স্ত্রী নয়, ছেলেকে ছেলে নয়। ভাইকে ভাই নয়। সকলেই সমান। সকলেই অচেনা মানুষ। পুরনো ‘সেলফ’ যেটা, পুরনো ‘আমি’ যেটা। সেটারই তো শ্রাদ্ধ হল, সেই মরা, অতীত জীবনটার নাম ‘পূর্বাশ্রম।’ পাস্টটেন্স হয়ে গেছে এখন সেই মানুষটা, তার মেমারিও নাকি ক্যানসেলড হয়ে যাওয়া নিয়ম। নো ট্রেস। জেঠুমণি সেটাই বলেছিলেন। তাঁর জ্যাঠামশাই সত্যিই যদি সন্ন্যাসী হবার জন্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন তাহলে নিশ্চয়ই মায়ের ফোটোটা সঙ্গে নিয়ে যেতেন না। মা মানেই তো root—মা মানেই the whole family, self, past-present সব কিছু। যেখান থেকে জন্ম! তাই জেঠুমণি is worried he thinks all that সাধু—সন্ন্যাসী business must have happened later on—অন্য কোনো একটা কারণে প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের জ্যাঠামশাই। সেটা কী কারণ হতে পারে? He has no idea—তবে এটাও ঠিকই যে তিনি শেষ পর্যন্তও সন্ন্যাসী ছিলেন না। বিয়েটিয়ে করেছিলেন, মস্ত বড় প্রপার্টি বানিয়ে ছিলেন, he became quite rich and felt the pangs of conscience তাঁর বিধবা helpless মাকে দেখাশোনা করেননি বলে খারাপ লেগেছিল। ভাই মাকে দেখেছে বলেই gratefully ভাইকে আর ভাইপোদের অনেকটা property—র share ‘উইল করে দান করে গেছেন। জেঠুমণি does not think those strangers were pretenders—জেঠুমণি তাদের ভাই বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। আমাকে সব explain করেছিলেন। They had a meetings already—ভাইবোনেরা! জেঠুমণি, বাবা, কাকু, পিসিমণি—ওঁরা সবাই মিলে ভাবছেন পুজোর ছুটিতে একসঙ্গে শালডুংরি that’s the name of the place—যাওয়া হবে। To find out for ourselves what the matter is—তখন নাকি আমাদের জমিটমি মাপজোকও করা হবে, সরকারী লোক আসবে and all that।
দারুণ excited মনে হল জেঠুমণিকে। খুব খুশিও। জেঠুমণি বললেন—”তোমাদের আরও একজন ঠাকুমা আছেন, জানো? ঝাড়গ্রামের কাছে একটা গ্রামে থাকেন। ছেলেপুলে নাতি—নাতনী নিয়ে একটা ফার্মের মধ্যে বাস করেন। এই যে আমাদের এই চেস—বোর্ডওয়ালা টেবিলটা? এটা যিনি দিয়েছেন না, ইনি তোমাদের সেই বড় ঠাকুরদার স্ত্রী। আমার জ্যাঠাইমা। হেসো না, হেসো না, জ্যাঠারও জ্যাঠা থাকে। আমারও ছিল। তাঁরই কাছে আমার দাবা খেলার হাতেখড়ি?”
—”যেমন তোমার কাছে আমার দিদির।”
—”ঠিক। যেমন আমার কাছে তোমার দিদির তেমনি এই জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আমার দাবা—শিক্ষা। তিনি সন্ন্যাসী হলে কি হবে, দারুণ দাবাবোড়ের চাল দিতেন। পরের জীবনে অবশ্য জ্যাঠামশাই বিয়ে করেছিলেন, সন্ন্যাস ত্যাগ করেছিলেন বলেই শুনেছি। তিনজন ভদ্রলোক এসে আমাকে বলে গেছেন, তাঁরা আমাদের জ্যাঠতুতো ভাই। বাবার ভাইপো হন। তাঁরা থাকেন শালডুংরির গ্রামে। আমার হাতে প্রুফস্বরূপ তারা আমাদের ঠাকুমার ছবির কপি আর উইলের Relevent Page—এর Xerox দিয়েছেন।
—”ছবিটা জেনুইন। সত্যিই ঠাকুমার ছবি ওটা। উনিই নাকি ওদেরও ঠাকুমা। কিন্তু জেঠুমণি বললেন, ”একটা জিনিস বুঝলুম না। ওদের কাছে ছবিটা আধখানা কেন? আমাদের বাড়িতেও তো এই ছবিটাই আছে, ঠাকুর্দা—ঠাকুমা পাশাপাশি। এখানে শুধুই ঠাকুমা। এই একার ছবিটা আমি দেখিনি।” ইন ফ্যাক্ট সেই যুগ্ম ছবিটা আমিও দেখেছি। খুব গম্ভীর মুখ করে দুজনে বসে আছেন। একজনের গোঁফ ঝুলছে, আরেকজনের এতবড় ঘোমটা, আর এতবড়ো নথে মুখটা প্রায় ঢাকা। মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন,—”দ্যাখ তোদের কর্তাবাবা। কর্তা মা—বাবার ঠাকুর্দা—ঠাম্মা”—আমরা সবাই দেখেছি ছবিটা। but জেঠুমণি is quite right, here we have half the photo—what happened to the other half? বাকি ছবিটা, কর্তাবাবার ছবিটা কী হল?
জেঠুমণির এটাও খচমচ করে লাগছে যে why should a সন্ন্যাসী carry his man’s photo with him? তার মানে সে অন্য উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়েছিল। পরে পাকেচক্রে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। আবার চান্স পেয়েই সন্ন্যাসী ছেড়ে দিয়ে সংসারী হয়ে গেছে। But why? Quite a mysterious character কিন্তু বাবার এই জ্যাঠামশাই। তাঁর বৌ এখনও বেঁচে আছেন, she is a tribal lady—আমাদের বড় ঠাকুমা।
বুলটু—পুল্কি
হ্যালো পুল্কি? জানিস, সামথিং ভেরি স্ট্রেঞ্জ হ্যাপেনড। জেঠুমণির কাছে খুব অদ্ভুত তিনজন লোক এসেছিল। আমি তখন স্কুলে ছিলুম। দিদি বলল, ওরা বলেছে আমাদের কাকা হয়। ওরা নাকি বাবার জ্যাঠতুতো ভাই। বাবাদের সেই যে জ্যাঠামশাই ছিলেন যিনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি নাকি আবার বিয়েও করেছিলেন। তাঁরই তিন পুত্র। জেঠু বিলিভস দেম।
আমি বুঝতে পারছি না।
এ কখনও হতে পারে? আমাদের এতসব আত্মীয়স্বজন রয়েছে ঝাড়গ্রামে, আর আমরাই জানি না! দিদি আর জেঠুমণি কিন্তু প্রায় কনভিন্সড। লোকগুলো (কাকারা) বাবার ঠাকুমার ফটো আর উইলের জেরক্স কপি এনেছিল, আর বাবার জ্যাঠামশায়ের ডায়েরিতে নাকি দাদুঠাকুমার অনেক আগের বাড়ির (টালাপার্কের বাড়ির) ঠিকানা ছিল। সেই বাড়িতে দাদু—ঠাকুমারা যখন থাকতেন তখনও বাবা স্কুলে ভর্তি হননি, আর পিসিমণি ছোট্ট, কাকু জন্মায়নি। তাহলেই ভেবে দ্যাখ কত দিন আগেকার কথা! তোর কি বিশ্বাস হচ্ছে? কী মনে হচ্ছে তোর?
—আমার? আমার তো নাচতে ইচ্ছে করছে! জাস্ট লাইক আ ফেয়ারি টেল! কি সুন্দর হবে, যদি সত্যি সত্যি আমাদের অচেনা সব ভাই—বোন, মামা—মামী মামাবাড়ি থাকে? ইস কী মজা রে! সত্যি বলছিস? আমার তো ভী—ষণ আনন্দ হচ্ছে! ইটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল নিউজ! কিন্তু ওঁরা কেন এসেছিলেন রে এতদিন পরে? এত খুঁজে—পেতে? এতদিন কী করছিলেন? আসেননি কেন?
—এতদিন নাকি আমাদের একজিসটেন্সই জানতো না ওরাও। এখন কী সব প্রপার্টি বেচাকেনা করতে হবে, তাই উইলটা বেরিয়েছে বাবার জ্যাঠামশাইয়ের। সেই উইলে লেখা আছে আমাদের দাদুর নাম। তাতে জেঠুমণির আর বাবারও নামও আছে। ওঁদের খুদে খুদে দেখেছিলেন তিনি। কাকুকে মোটেও দেখেনইনি। তাই কাকুর নাম দেননি।
—আর মাকে? মাকে দেখেননি? মার নাম নেই?
—না বোধ হয়। পিসিমণিও তো বাবার চেয়ে ছোটো। পিসিমণিকেও দেখেননি হয়তো—উনি কেবল দুজনকেই দেখেছেন তাই দুজনের নাম দিতে পেরেছেন।
—এতদিন কেন কানেকশান রাখেননি রে?
—আমি কেমন করে জানব? সন্ন্যাসী ছিলেন তো। বিয়ে—থা করে বোধহয় লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন, আর মুখ দেখাতে পারেননি। এমব্যারাসমেন্ট। কুড’ন্ট ফেস দেম। আফটার অল পতন তো? সন্ন্যাসীর পেডেস্ট্যাল থেকে ধড়াম করে অধঃপতন। তাই বোধহয়—কিন্তু আমি ভাবছি হঠাৎ বুড়ো বয়সে বিয়ে—থা করলেন কেন? উনি তো ছোটবেলা থেকেই সন্ন্যাসী।
—অপ্সরা—টপ্সরা দেখে আগেকার দিনে দুশো বছর বয়সেও মুনি—ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যেত—ইনি তো শুধু সাধু।
—আমি তো অতশত জানি না—আই অ্যাম এক্সট্রিমলি ইরিটেটেড—দিদি আর জেঠুমণি মিলে সকলকে বোঝাচ্ছে যে ওরা জেনুইন লোক—এই ছবিটা নাকি সত্যি বাবার ঠাকুমার ছবি, জেঠুমণি তাঁকে দেখেছেন।—তাঁর ছবি রয়েছে দাদু—ঠাকুমার অ্যালবামে। ঐ ছবিটাই আছে ইন ফ্যাক্ট।
—এটা ওরা দিয়ে দিল? কি আশ্চর্য! ওরকম ফ্যামিলি ট্রেজার কেউ বিশ্বাস করে অচেনা লোককে দিয়ে দেয়? যদি আমরা আর ফেরত না দিই?
—ধুৎ! তুইও যেমন? গাববুস কোথাকার! ওটা কি আসল ছবিটা নাকি? স্ক্যান করে কপি করেছে। আসলটা কেউ দেয়?
—বুলটু, আমার ভীষণ ওদের দেখতে ইচ্ছে করছে রে! এক্ষুনি!
—দিদি বলল, একজনকে জেঠুমণির মতো দেখতে, কাকুর সঙ্গে খুব মিল। বাকি দুজনকে সাঁওতালদের মতো দেখতে।
—সাঁওতাল? কি স্ট্রেঞ্জ! আচ্ছা ওদের বয়েস কত রে? ওই মামাদের?
—কাকুর চেয়ে ছোটো বলল তো—
—ওদের নাম কী?
—দিদি ওসব বলতে পারবে। আই ডোন্ট রিমেমবার দিজ ডিটেইলস—আই ডোন্ট ইভন নো দিজ পিপল—নেভার মেট দেম—মা মিট করেছেন অবশ্য—
—তাই? মেজমা কী বলছেন?
—শি, আই থিংক, ইজ কনভিন্সড টুউ! নইলে আপত্তিগুলো আমরা এতক্ষণে শুনতে পেতুম।
—দিদিভাইকে দে না, নামগুলো জিজ্ঞেস করি?
—দিদি তো টিভি দেখছে—ইজিপ্ট—
—তবেই তো হয়েছে।
—নামগুলো মাও জানেন, দেবো মাকে?
—থাক মেজমাকে ডিস্টার্ব করিস না। কালই আমি চলে আসবো, দিদিভাইকে বলবি, এখন অনেক রাত, নইলে এক্ষুনি যেতুম—ই—শ আই কান্ট ওয়েট টু মিট দেম—অ্যাই বুলটু, ওরা নেক্সট কবে আসবে রে?
—আই ডোন্না—বাট—ডেফিনিটলি। আসবে আবার। ওই জমিজমার কীসব কথাবার্তা আছে—
—কী জমিজমা?
—ওহো সেটাই বলিনি? ওই যে উইলে নাম—
—উইলে নাম বলেছিস, কেন নাম আছে সেটা বলিসনি।
—ওরা আমাদের অনেক জমিজমা দান করতে এসেছে—আ লট অফ ল্যান্ড ইন ঝাড়গ্রাম।
—দান? রিয়েলি? লোকে সেধে সেধে কিছু দিতে আসে নাকি? তার ওপরে সম্পত্তি? ধ্যাৎ—
—এগজ্যাক্টলি! পুলকি, ঐ জন্যেই আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না ওদের…
—কিন্তু এটা তো ফেয়ারি টেল, ফেয়ারি টেলে সব কিছু হয়। বুলটু আই থিংক দে আর অনেস্টলি অফারিং হোয়াটএভার দে মে বি অফারিং—লেটস বিলিভ দেম—মা তো সবসময়ে বলেন অবিশ্বাস করে জেতার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকে যাওয়াও ভালো—
—পিসিমণি ইজ রাইট। অবিশ্বাস করলে নিজেরই অশান্তি—ঠিককথা, বাট উই মাস্ট বি কেয়ারফুল…।
—এটা তো কিছু বেচাকেনার ব্যাপার না যে অত কেয়ারফুল হতে হবে—এ তো গিফট নেওয়া—
—না, না, দেওয়া—নেওয়া দুটোই কিন্তু গোলমেলে হতে পারে, কার কী মোটিভ তার ওপরে ডিপেন্ড করছে, ওদের মোটিভটা আমার কাছে ক্লিয়ার নয়—
—সত্যিই তো, কেন দিচ্ছে রে?
—ওরা বলছে ওরা ঠিক করেছে, পুরো প্রপার্টিটা বিক্রি করে দেবে—তার মধ্যে আমাদের অংশে রয়ে গিয়েছে—সেটা বিক্রি করে দিতে পারলে সুবিধে হয়, তাই…
—তাই অনুমতি নিতে এসেছে? তাই বলো। ওরা অন্যের জমি বেচে দেবে, তার পারমিশান চাইছে? আর বড়মামা তো ওইরকম মানুষ—ওদের নিশ্চয় তক্ষুনি লিখে দিয়েছেন।
—না না, জেঠুমণি সেসব করেননি। আসল উইলটা তো ওরা দেখাবে আগে। এটা তো শুধু জেরক্স দেখিয়ে মৌখিক ইনটিমেশান। এর পরেই শুরু হবে আসল কাণ্ডকারখানা—তুই ওদের অনেকবার দেখবার চান্স পাবি, নিশ্চিন্ত থাক। ব্যাপার অল্পদিনের নয়—দিজ জি ওনলি দ্য বিগিনিং।
টুলকি
মা বিশ্বাস করেছেন। জেঠুমণিও বিশ্বাস করেছেন যে তাঁদের আপন জেঠতুতো ভাইয়েরা এসেছিলেন তাঁদের সম্পত্তির অংশের ভাগ দিতে।
আবার আসবেন, সব কাগজপত্তর নিয়ে। যিনি লম্বা মতো তাঁর নাম শঙ্করপ্রসাদ। তিনিই বড়ভাই। আর গাঁট্টাগোট্টা গুণ্ডার মতোন খোঁচা—খোঁচা চুল—তাঁর নাম শিবপ্রসাদ। যিনি জেঠুমণির মতো দেখতে সেই সরোজপ্রসাদই সবচেয়ে ছোট। কাকুর সঙ্গেই খুব মিল। আমার অবাক লাগছিল ওঁদের দেখে। শঙ্কর আর শিব ওখানে জমিজমার দেখাশুনো করেন। সরোজ মেদিনীপুরে একটা কলেজে পড়ান। তিনজনের কথাবার্তাতেও অনেক তফাত। শিবপ্রসাদের ধানকল আছে, আর ট্রাকের ব্যবসাও আছে বলছিলেন। কিরকম যেন রাফ কথাবার্তা ওঁর। কুলিমজুর চালিয়ে ওরকম হয়ে গিয়েছে। শঙ্করপ্রসাদ চুপচাপ মানুষ। উনি শুধুই জমিজমা বোঝেন বললেন। বাবার জ্যাঠামশাই নাকি পঞ্চান্ন বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন। জেঠিমা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর বয়েসও বেশি নয়। ষাট পূর্ণ করেছেন। আমার মনে হয় আমাদের উচিত আগে গিয়ে ঐ জেঠিমার সঙ্গে দেখা করে, সব ঠিকঠাক জেনে নেওয়া।
কিন্তু ছোটমা আর কাকু বোধহয় ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। বুলটুও ওদের সঙ্গে। বাবা বেচারী মাঝপথে—বুঝতে পারছেন না কাদের দলে যাবেন। বাবার অবস্থাটা টের পাচ্ছি—আমিও প্রায় ওই রকমই। এক একবার মনে হচ্ছে মানুষগুলির উদ্দেশ্য অন্য কিছু, ঠিক যা মনে হচ্ছে তা নয়। যা বলছে, তা নয়।
কাল ওঁরা ফোন করেছিলেন। জেঠুমণি বলেছেন, রবিবার আসতে। সবাই বাড়িতে থাকবে। পিসিমণিকেও আসতে বলেছেন। পিসেমশাই তো ল’ইয়ার, তাঁর থাকা ভালো। পিসিমণির অবশ্য ভাগ নেই, কাকুরও না। তবে জেঠুমণি আর বাবা নিশ্চয় তাঁদের অংশ থেকে প্রাপ্য ভাগ দিয়ে দেবেন। এটা তো আসলে দাদুর পাওয়া সম্পত্তি। দাদুর সব সন্তানেরই ভাগ থাকা উচিত। উনি তো এদের জন্মানোর খবরই পাননি। আজকাল ইনরেহিটেন্স ল’ পালটেছে, মেয়েদেরও সমান অধিকার থাকে বাবার সম্পত্তিতে। পিসিমণিরও আছে। বাবা আর জেঠুমণি এসব কথা বলাবলি করছিলেন নিজেদের মধ্যে।
কাকু—ছোটমার কেবলই মনে হচ্ছে ওদের কোনো সেলফিস মোটিভ আছে এর মধ্যে, সেটা আমরা ধরতে পারিনি। ওরাও তো সবটা আমাদের খুলে বলছে না। মা আর জেঠুমণি বেশি সহজে ওদের কথা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। কাকু বলছিল, ওদের প্রপার্টির ম্যাপ একটা দেখা দরকার, তাছাড়া সরকারকে দিয়ে জরিপ করানো দরকার। এবং সার্চ করানো দরকার। অলরেডি ওটা কাউকে বেচে দেওয়া হয়েছে কিনা—আবার বেচতে গিয়ে আমরা না ঠগ দায়ে ধরা পড়ি। একথাটা বাবার পছন্দ হয়েছে—জেঠুমণিরও। রবিবার ওঁরা এলে এসব কথা হবে।
মা বলছেন সেদিন রোববারের মাংসটা তিনিই রাঁধবেন। জেঠুমণি তো কথাবার্তা বলবেন—ওঁকে আর রান্নাঘরের দিকে আসতেই দেওয়া হবে না।
ওঁরা এসেছিলেন। এতবড় এক থলি কাজুবাদাম নিয়ে। এত কাজুবাদাম? জীবনেও দেখিনি। ওঁরা বললেন ওঁদের বাগানের। বললেন, আমাদেরও নাকি কাজুবাদামের বাগান আছে। আম—কাঁঠালও হয় প্রচুর। আতাফল, পেঁপে, পেয়ারাবাগান, লিচুবাগান আছে। নারকেল হয়, আরও কত কি হয়। ওঁরা একথলি তিলও এনেছিলেন। অমন সাদা ধবধবে তিল কখনও দেখিনি আমি আগে। সাদা সর্ষেও এনেছিলেন, ‘রাইসর্ষে’ বলছিলেন। ওঁদের অ্যাটিচ্যুডটা ভালো লাগল। Long lost friends—এর মতোই আচরণ করছেন। মাও ওদের জন্য অত্যন্ত চমৎকার খাসির মাংসের ঝোল, চিংড়ি মাছের মালাইকারী, লাউয়ের সঙ্গে মুগডাল, পুঁইশাক দিয়ে মাছের মুড়োর চচ্চড়ি, রুইমাছের কালিয়া, আর আমসত্ত্বের চাটনি রান্না করেছিলেন। দারুণ হয়েছে আজকের খাওয়াদাওয়া। কিন্তু আই মাস্ট সে এত কাজুবাদাম!
—আর কী বড়ো বড়ো আস্ত আস্ত, যেন sculpted—কি যে সুন্দর খেতে! ওঁদের সর্ষেখেত আছে। সর্ষের তেল হয়। তিলখেত আছে। তিলেরও তেল হয়—সে তো বোঝা গেল। কিন্তু ওঁদের নাকি ধানখেত, আর ধানকলও আছে। আখের খেতও আছে, গুড়ও হয়। ওঁরা বলছেন আমাদের বেড়াতে যেতে। ওঁদেরও ভীষণ খারাপ লাগছে। যে জীবনে আমাদের অস্তিত্বই ওঁদের জানা ছিল না এতদিন। ওঁদের কোনও আত্মীয়স্বজনই ছিল না মোটে বাবার দিক থেকে।
আর মা, মানে আমাদের বাবার যিনি জ্যাঠাইমা, তিনি নাকি শবরদের মেয়ে, লোধা শবর। তারাই ওঁদের আত্মীয়। বাবার জ্যাঠামশাই কেমন করে হঠাৎ সন্ন্যাসী মানুষটা হিমালয় থেকে নেমে এসে শবরদের মেয়ে বিয়ে করে শবরদের মধ্যেই থেকে গেলেন, সেটাই খুব আশ্চর্য। আমার মনে হয় মা—বাবা জেঠুমণি সকলেই সেই ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এই ক’দিন। এই সব গল্পই আজ ওঁরা এসে বলে গেলেন। সেদিন এত কথা হয়নি। কাকু ভীষণ বেশি প্রশ্ন করে কিনা। জেঠুমণি অত প্রশ্ন করেননি তো।
কাকুর প্রশ্নেই জানা গেল, জেঠুর জ্যাঠাইমা বেঁচে আছেন, তাঁর মাত্র একষট্টি বছর বয়েস, প্রায় জেঠুমণিরই সমবয়সী। তাঁর নামটাও খুব অদ্ভুত মতোন। সুন্দর। লোকের নাম চাঁপা হয়। গোলাপ হয়। জবা হয়, পদ্ম হয়, শিউলি হয়—ওঁর নাম তিলফুল। তিলফুল যিনি নাসা—সেই তিলফুল। তিলখেত। তিলফুল, এসব কোনোদিন চোখে দেখিনি। জানি না কেমন দেখতে, কিন্তু নামটা আমার ভারি সুন্দর লেগেছে। ওঁরাই বলছিলেন বড় দুই ভাইকে মায়ের মতোন দেখতে, ছোটো ভাইটি বাবার মতোন হয়েছেন।
দেখতে তো ভালোই, বেশ টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম, হতেই পারতেন, শুধু পালিশ একটু কম। দুজনের মধ্যে আমার মেজজনকে একটু অন্যরকম লাগলো। এই যে, মজুর খাটিয়ে খাটিয়ে কিঞ্চিৎ রাফ হয়ে গেছেন। বড়জনকে বেশ মাইলড টাইপের মনে হল, চাষবাস খেতখামার ফল বাগানটাগান দেখাশোনা করেন। ট্রাকের ব্যবসা আর ধানকল, এ দুটোকে চালায় মেজ ছেলে, শিব। শঙ্করকে ওরা ডাকে ”দাদা” বলে। তিনি শিবকে ডাকেন ”শিবো”। কিন্তু সরোজকে সরোজই বলছিলেন। বেশি কথাবার্তা উনি বলেননি অবশ্য, ব্যবসা বোঝেন বলে ঐ শিবো—ই সব কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। সরোজকেও আমার বেশ ভালো লেগেছে। পুটুসকে তিনি মজার ধাঁধার খেলা শেখাচ্ছিলেন। পুটুস তো খুবই ইমপ্রেসড। তিনি এসব আলোচনার ব্যাপারে মোটে ঢুকছিলেনই না। ওই সময়ে তিনি আমাদের ডেকে ডেকে আলাপটালাপ করছিলেন। তাঁর কাছেই তো জানলুম ওই তিনফুল নাম। আমাদের সবার পরিচয় জানছিলেন,—কে কী পড়ি। ওঁর ছেলের নাম টোটো, সে ক্লাস থ্রিতে পড়ছে, মেদিনীপুরে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে। উনি মেদিনীপুরের কোনো কলেজে পড়ান। আমি ফার্স্ট ইয়ারে শুনে তো অবাক, আমাকে আরও ছোটো মনে করেছিলেন। আর বুলটু টেনে শুনেও তো অবাক, তাকে ভেবেছিলেন বড়ো! অবশেষে বেটে পুলকি ইলেভেন শুনে উনি আর অবাকটবাক কিছু হননি। আমাদের পুটুসকে উনি বিশেষ করে অনেক লোভ দেখিয়েছেন। বলেছেন ওঁদের ওখানে গেলে, নানা রকম মজা হবে যা কখনও কলকাতাতে আমরা ভাবতেই পারি না। আমাদেরও বারবার করে বললেন যেতে। ওখানে আমাদের একটা বোন আছে। আমাদেরই কাছাকাছি বয়েস তার—এবারে স্কুল ফাইনাল দিয়েছে। তার নাম বাসন্তী। আর লালা বলে ছোট্ট ভাই আছে। পাঁচ বছর বয়স। তার দাদা আছে, শুভ, আরেকটা ভাই, দশ বছরের। আমার তো এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে ওদের গ্রামে, শালডুংরিতে।
কি সুন্দর নামটা না? শালডুংরি? ”ওরে বকুল—পারুল ওরে শাল—পিয়ালের বন” নামটা শুনলেই গানটা মনে আসে। শালডুংরি গ্রামে আমাদেরও সত্যি সত্যিই নাকি নিজেদের অনেক জমি আছে, শাল পিয়ালের বন আছে, তাতে নুড়ি ভরা ঝরনা আছে, পাথুরে টিলা আছে—সরোজকাকু আমাদের এই সব গল্প করছিলেন। ওঁরা খুব খুশি আমাদের সন্ধান পেয়ে। শুধুই ওঁদের আদিবাসী দিকটিরই পরিচয় ওঁদের কাছে এতদিন ছিল তো, পিতৃবংশের কোথাও কোনো চিহ্ন ছিল না—জেঠুমণিকে দেখে তো উনি এক্কেবারে আনন্দে অস্থির। দুজনের চেহারায় এত আশ্চর্য মিল! কপাল, চোখ, ভুরু, নাক, নাকের তিল, ঠোঁট, থুতনি—এমনকি কপালের থেকে মাথার চুলে টাক পড়বার ধরনটা পর্যন্ত এক রকম। যেন উনি জেঠুমণিরই ছেলে। আত্মীয় যে, তা দেখলেই চেনা যাচ্ছে। জেঠুমণি তো কেঁদেই ফেলেছেন আজ। বড়মা এঁদের দেখে যেতে পারলেন না বলে। সেই তাঁর অতি প্রিয়, পশ্চিমে যে আমাদেরও জমিজমা আছে, সেই সুখবরটা উনি তো জেনে যাননি। সারা জীবনই জেঠুমণি ভাবতেন ওদিকে কোথাও একটু জমি কিনে একটা বাংলোবাড়ি আর বাগান বানিয়ে দেবেন বড়মাকে।
বুলটু—পুল্কি
বুলটু—থ্যাঙ্কস গড। খুব ভালো হয়েছে যে পিসিমণি, পিসেমশাই এসেছিলেন। ওরা আজ সব কাগজপত্র নিয়ে এসেছিল। দুজন কালো মতোন। ট্রাইবাল লুকিং লোক, তারা হচ্ছে বাবাদের জেঠতুতো ভাইদের মধ্যে বড় আর মেজো—আই ডিড নট লাইক দেম—আর একজন নরমাল ঐ যাকে বাবা জেঠুমণিদের মতো দেখতে—সে ছোটো। সে মেদিনীপুর কলেজে পড়ায়। হি সিমস ওকে অন্য দুজনও সিম কোয়াইট ওকে, বাট দে ডোন্ট লুক লাইক আস। জেঠুমণির মতো দেখতে লোকটির নাম বলল সরোজ। সে আমাদের সঙ্গে খুব ভাবসাব করবার চেষ্টা করছিল। আই ডোন্ট নো হোয়াই। দিদি আর পুটুসকে হাত করে ফেলেছে মনে হয়। পুটুসকে তো হাত করাটা কোনা ব্যাপারই নয়। বাট আই অ্যাম কিপিং মাই ডিসেন্ট। তুই তো দেখলুম খুব গা ঘেঁষে ঘেঁষে যাচ্ছিস ভাব করতে ওদের সঙ্গে। মিনি বেড়ালের মতো। মিঁয়াও।
পুলকি—হ্যাঁ, তো যাবই তো। আমার মামা না ওঁরা? আরেকখানা আস্ত মামাবাড়ি আবিষ্কার। ক্যান ইউ ইম্যাজিন? দ্য প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ? আ স্ট্রোক অফ লাক। কি বল? আর জগতে কারুর তো এমন হয়েছে বলে শুনিনি। নতুন একসেট মামা।…ইই—শ!
বুলটু—অ্যান্ড নতুন এক সেট কাজিনস।
পুলকি—জানি জানি। একজন তো আমারই বয়সী, তার নাম বাসন্তী। তোর সঙ্গে পড়ে যদিও। গ্রামে একটু দেরিতে পড়তে শুরু করে তো। এসপেশ্যালি মেয়েরা লেটে স্কুলে যায়।
—পুটুসের মতনও একটা আছে রে, টোটা। আরও ছোট্ট একটা আছে। লালটুক।
—তাহলে তো দারুণ গ্যাং ফর্ম করা যাবে যখন আমরা যাব বেড়াতে।
—দিদি ওখানেও লিডার। ওর চেয়ে বড় কেউ নেই ওখানে—শি ইজ দি ওলডেস্ট।
—ভালোই তো। তুই কি ভাবছিস আর কেউ লিডার হলে তোকে আরেকটু মান্যি করতো?
—আই! মার খাবি কিন্তু।
—বুলটু! মার কে কার কাছে খাবে সেটা দেখতে চাস?
—ঐ তো সাড়ে তিনফুট চেহারা।
—তাতে তোর সাড়ে পাঁচ ফুটের চেয়ে ঢের বেশি শক্তি রাখি—তুই যা প্যাংলা, ঠিক পাটকাঠি। আমার গায়ে—
—হ্যাঁ, তোর অবশ্য স্পেশিফিক গ্র্যাভিটিটা ঢের বেশি। অত মাটির কাছাকাছি গুড়গুড় করছিস—অতোখানি ওজন নিয়ে—
—বুলটু! ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!
—কী করবি? মাকে বলে দিবি? পিসিমণি আমাকে কিছু বলবে না।
—আজ্ঞে না। মাকে নয়, সোজা গিয়ে দিদিকে বলে দেব—তোমার মজা বের করে দেবে।
বুলটুর গাঁইয়ামতন লোকগুলিকে পছন্দ হয়নি। পুটুসের সঙ্গে কেবল ভাব হয়েছে। সরোজ নামে ভদ্রলোকের (এখনও ‘কাকু’ বলে ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে আর কি) একারই। তিনি অনেক ধাঁধাটাধা জানেন। পুলকি তো গদগদ, আরও একটা মামাবাড়ি! তায় ঝাড়গ্রামে, শালবন, লালমাটি, ঝর্নাটর্না, পুলকি তো আহ্লাদে নাচছে। আমার ধারণা জেঠুমণি, মা এবং বাবারও মনের অবস্থা ঐ রকমই। ওঁরা বড় বলে ততটা প্রকাশ করছেন না। পিসিমণি কিন্তু কাকু ছোটমার দলে।
পিসিমণির ঠিকমতো বিশ্বাস হচ্ছে না যে স্বেচ্ছায় কেউ সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়ে দিতে চেয়ে অচেনা আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে বের করে। এর মধ্যে কোথাও একটা ‘ক্যাচ’ আছে বলে মনে করছে ওরা। পিসেমশাই কী ভাবছেন তিনিই জানেন, এত কথা কম বলেন! সব শুনলেন, দু’চারটে প্রশ্ন করলেন। কোনও মন্তব্যই করলেন না। পিসেমশাইয়ের ওপরেই জেঠুমণি, মা, বাবা সবাই ভরসা করে আছেন। ল’ইয়ার তো, যদি কিছু আইনের অসঙ্গতি থাকে, ঠিকই ধরে ফেলবেন। আমার সেদিক থেকে কোনো ভাবনা হচ্ছে না—পিসিমণিদের কেন হচ্ছে জানি না। আমারও আসলে কিন্তু ভিতরে ভিতরে পুলকির মতোই উত্তেজিত লাগছে।
সত্যিকথাই তো। আরেকটা গোটা আত্মীয়কুল! আস্ত একজন ঠাকুমা, তিনজন কাকা, একগোছা ভাইবোন। আর খোলা মাঠ, বনবাদাড়। ঝরনা! আমি তো ভাবতেই পারছি না। চিরদিনই এই তিনতলা বাড়িতে রয়েছি আমরা। বাগান নেই, মাঠ নেই, চারদিক বন্ধ। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি যতই ভালোবাসি না কেন আমাদের এই বাড়িটাকে, এটা তো ঠিকই একটুও খেলার জায়গা নেই, এক ছাদে ছাড়া। বড়মা তো সবসময়ে দুঃখু করতেন—ওঁদের ছোটোবেলার বাড়ির গল্প করতেন। লালমাটির মাঠ, শালবন, সরু নদী, খরগোস, হরিণ, এমনকি ছোটো ছোটো বাঘও বেরুতো নাকি মাঝে মাঝে। হাজারিবাগে তখন বনজঙ্গল ছিল। আমাদের যেখানে জমিজায়গা আছে। ইশ কি আশ্চর্য একটা সেনটেন্স লিখলুম—”আমাদের যেখানে জমিজায়গা আছে”—পড়েই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—পুলকি যে বলছে না, ‘ফেয়ারি টেল’। সত্যি সত্যি তাই। ‘রূপকথা’ ছাড়া আবার কি? আমার মনে হয় কাকু পিসিমণিদের সেই জন্যে বিশ্বাস হচ্ছে না। একদম রিয়ালিস্টিক শোনাচ্ছে না তো ব্যাপারটা। খুব আনরিয়্যাল। একদম অবাস্তব। বাবাদের ঠাকুমা ওই কাকাদেরও ঠাকুমা। ভাবা যায়? ওটা অবশ্য হাজারিবাগ নয়। কিন্তু শালডুংরিও খুব সুন্দর। ওখানে একটা নদী আছে ওই সরোজকাকু বলছিলেন। তার নাম ডুলুং। কি মিষ্টি নাম না? ডুলুং! সুবর্ণরেখা নামটিও খুব সুন্দর। সে নদীও বেশি দূরে নয়। কাছাকাছিই। ওখানে বালিজল ছেঁকে ছেঁকে এখনও সোনার গুঁড়ো বের করে অনেকে। লোকাল লোকেরা নাকি শতশত বছর ধরে সোনা ছেঁকে নিয়েছে। তাই এই নামকরণ—সোনার নামে নাম। আমরাও চেষ্টা করব—পাতলা সাদা ন্যাকড়া নিয়ে যাব, জেঠুমণির ধুতির টুকরোই বেস্ট—তাতে সুবর্ণরেখার বালিজল ছাঁকবো। সোনা বেরোয় যদি? ইশ কি মজাই না হবে, যদি বেরোয় সোনার গুঁড়ো? স্বর্ণরেণু! বুলটুটাকে বলতে হবে—তাতে যদি ওর একটু ইন্টারেস্ট হয়। ওকে কিছুতেই ইন্টারেস্টেড করা যাচ্ছে না—পুলকি তো হাল ছেড়ে দিয়েছে।
বোধহয় যাওয়া হবে। কাকু—পিসিমণি—ছোটমা সবাই যেতে রাজি হয়েছে—কেননা সার্চ করানো হবে। ম্যাপ দেখিয়ে গেছেন ওঁরা—এবারে আমাদের সকলের ঢালা নিমন্ত্রণ শালডুংরিতে—যতদিন খুশি থাকতে পারি।
পুলকি
একটা অদ্ভুত কথা শুনেছি—অদ্ভুত মানে শুনলুম আমাদের একজন দিদিমা আছেন, মা’র জ্যাঠাইমা, তিনি নাকি ট্রাইবাল মহিলা। বুলটু বলল তিনি সত্যি সত্যিই আমাদের মা—মামাদের জ্যাঠাইমা হন, তাঁর কাছে মার আপন ঠাকুমার ছবি আছে। তাঁর ছেলেরা তিনজন এসেছিল, মামাবাড়িতে বড়মামুর সঙ্গে কথা বলে গেছে, রবিবার আবার আসবে, সেদিন আমরাও যাব। সবাই সবাইকে meet করবে for the first time—কী কাণ্ড দ্যাখো। আমরা এই সব ট্রাইবালদের বিষয়ে কত কী ভাবি,—তারা uncivilized, তারা backward তারা অশিক্ষিত, unsophisticated—সেসব কথাই ভুল। বড়মামু বলছিলেন আদিবাসীদের নিজস্ব সব কালচারাল ট্র্যাডিশন আছে, তাদের নিজেদের মতো করে তারা যথেষ্ট বেশি কালচার্ড—শুধু সিনেমায় দেখা আদিবাসীদের মতন নাচগানই করে না। ওই সব গানের মধ্যে হিস্ট্রি আছে, মিথলজি আছে—ফোকলোর আছে। রিচুয়ালস আছে—ফোকলিটারেচার তো লিখিত হয় না, মৌখিকই হয়। তাই বলে কি সেগুলো লিটরেচার নয়? বড়মামু আমাদের বলছিলেন ওঁদের জ্যাঠাইমা লোধা—জাতির মেয়ে। এই লোধাদের নাকি ইংরেজ রুলাররা ”ক্রিমিন্যাল ট্রাইব” বলে চিহ্নিত করে রেখেছিল। ওরা নাকি চুরি ডাকাতি করে খায়, চাষবাস করে না। বড়মামু বলছিলেন এখন আর লোধারা ওরকম নেই। বেদে—জিপসীদের মতোই ওদেরও নিন্দে—ওরা শিকার—টিকারও করত। নোম্যাডিক রেস তো, ঘুরে ঘুরে বেড়াতো, পশুপাখি শিকার করে খেত—ওদের অত কিছু চুরি ডাকাতির টেনডেন্সি নেই যতটা সাহেবরা বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখেছে। বড়মামু বলছিলেন কোনও ট্রাইবকেই ক্রিমিন্যাল ট্রাইব বলে ডিক্লেয়ার করা ঠিক নয়। ওগুলো ইনডিভিজুয়াল লোকের চয়েস—কেউ অভাবে পড়লে চুরি করে, কেউ শত অভাবেও চুরি করতে পারে না। কেউ কেউ লোভের জন্যও চুরি করে they are the worst লোভের জন্য খুনও তো করে লোকে। কাগজে রোজই পড়ি খুনের খবর। একটা জাতিকে শুধু শুধু ওরকম ছাপ দেওয়া অন্যায়।
আমার এই newfound মামারা কিন্তু খুবই special যে নিজে নিজে খুঁজে খুঁজে এসে আমাদের discover করেছে, জমির ভাগ দেবে বলে। নিজেরা নিজেরাই তো সবটা নিয়ে নিতে পারতো। আমরা তো কিছু জানতেই পারতুম না। শালডুংরির existence—ই জানি না। Property—রও existence—ই জানি না, মামাদেরও existence not known before Friday. মামারা অবশ্য লোধা নয় সবাই লাহিড়ী। ওই বড় দিদিমার বাড়ির লোকেরা লোধা ছিলেন। তাঁর দুই ছেলেও নাকি tribals—দের মতো দেখতে। দিদি বলল, কেবল একজনেরই আমাদের মতো চেহারা।
দু’দিন ধরে কেবল বৃষ্টি বৃষ্টি চলছে। ”মেঘ ছায়ে সজল বায়ে”—বলে যেই এককলি গান ধরেছি, অমনি শুনি রেডিওতে বলছে একটা ঝড় উঠতে পারে। সকাল থেকে অন্ধকার করে আকাশও যেন ঘনঘটার জন্যেই সেজেছে! দেখলে ভয় করে। মনে হয় ‘সুপার—সাইক্লোন’ টেনে আনছে হয়তো!—সমুদ্রতীর বেয়ে এসে আছড়ে পড়বে শহরে। যেরকম ওড়িশাতে পড়েছিল—উঃ। কি ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল মানুষের। জীবজন্তু, গোরু, মহিষ, বাড়িঘর খেতখামার বড়বড় গাছপালা। কিছু বাকি ছিল না—কত বছরের মতো সব উন্নতি নষ্ট হয়ে আবার পিছিয়ে পড়ল ওড়িশা—যদি আবার সেইরকম—নাঃ, ভাবতে নেই। কক্ষনো হবে না। ওরকম মহাপ্রলয় একবারই হয়। আরেকবারও হয়েছিল অন্ধ্রে। আরেকবার চট্টগ্রামে। সেসবগুলো আমার স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু ওড়িশার সময়েই নতুন করে জানতে পারলুম। আমার খুব ইচ্ছে করেছিল ওড়িশার গ্রামে গিয়ে রিলিফের কাজ করি। কিন্তু বয়েস কম বলে নিল না। কলেজে উঠলেই যেতে পারতুম। আমার খুব ইচ্ছে করছিল। যখন নিউইয়র্কে ‘নাইন—ইলেভেন’ হল, এগারোই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধবংস করলো টেররিস্টরা—তখনও আমার ইচ্ছে করছিল। দৌড়ে যাই, ওখানকার মানুষগুলোকে হেল্প করি—কিন্তু শক্তি কই যে দৌড়ে দৌড়ে নিউইয়র্ক চলে যাব? এই যে আমাদের দেশেই কত কিছু ঘটে যাচ্ছে আমি কি দৌড়ে রিলিফ দিতে যাচ্ছি? কাগজে পড়েছি কচ্ছের ভূমিকম্পে অনেক ছাত্র গেছিল, মালদার বন্যায় অনেক ছাত্র গেছিল, গুজরাটের সময়েও কলেজ থেকে একদল ছেলেমেয়ে প্রাইভেট ভিজিটে রিলিফের কাজে আমেদাবাদ গিয়েছিল। আর আমাদের তো এখনও কলেজে ঢোকাই হয়নি। দিদিটাই শুধু একাই কলেজে পড়ছে। ও খুব খাটতে পারে। ওর নেচারটাও খুব রেগুলার। নিয়মিত জগিং করতে যায়। আমিও রোজ ভাবি আজ যাব। তারপর ফের ঘুমিয়ে পড়ি। ছুটতে যাওয়া আর হয় না।
লেটেস্ট খবর মামাবাড়ি থেকে যা শুনছি, অর্থাৎ বুলটুর লেটেস্ট নিউজ বুলেটিনে জানলুম—পুজোর ছুটিতে সবাই মিলে শালডুংরি যাবো। ওখানে গিয়ে মামাবাড়ির আদর খাওয়াই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বুলটু বলল ”তাহলে তুই যা, আমরা আর যাই কেন, আমাদের তো মামাবাড়ি নয়।” হাউ মিন অফ হিম। দিদিভাইটা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। সোজা বলে দিল—”আদর খেতেই পারিস, কিন্তু কষ্টও করতে হবে—তোদের তো কোনো কষ্ট করার অভ্যাসই নেই। ওখানে কাছাকাছি দোকানপাটও নেই।” কথায় কথায় পেপসি হবে না। জানি, ওখানে বাজারহাট নেই—খালি খোলা মাঠ। বনজঙ্গল, ঝর্না টর্না, ছোটো ছোটো পাহাড়। টিলার মতন। হরিণ আছে। বুলটু as usual অসভ্যতা করতে লাগলো—”বাঘও বেরোয়, আর বেরুলেই তোকে ধরবে। এমন নধর নাদুসনুদুস আর কে আছে বল আমাদের মধ্যে? পিৎসা খেয়ে খেয়েই আশি কিলো—” আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমরা যাচ্ছি। কিন্তু বাবা কীসব কাগজপত্তর ঠিকঠাক করার কথা বলছিলেন ছোটমামুকে—ম্যাপট্যাপ, ফ্যামিলিট্রি, আরও কী কী! আই থিঙ্ক দে আর সিরিয়াস—যাওয়া হচ্ছে। তবে দিদিভাই একটা খুব খারাপ কথা বলেছে। ওখানে নাকি টয়লেট নেই—কমোড তো নেই—ই—কিছুই নেই। মাঠে যায়।
টুলকি
বুলটুটা বেজায় হাঙ্গামা করে মাঝেমাঝে। সত্যি! আমরা যাচ্ছি বেড়াতে। ও এয়ারগান নেবেই—ও নাকি খরগোশ, পাখি মারবে। আমরা প্রত্যেকে ওয়াইলড লাইফ সংরক্ষণে বিশ্বাসী। শিকার বিরোধী। ওই বন্দুক ওকে আমাদের বাড়ি থেকে কেউ দেয়নি। একটা কমপিটিশনে লাকি ড্র জিতেছিল। তিনটে চয়েস ছিল, ও নিয়েছে এয়ারগান। জানে তো বাড়িতে কেউ জীবনে ওকে ওই জিনিস কিনে দেবে না। আমরা সবাই অ্যান্টি—ওয়র, সবাই পিস—এ বিশ্বাসী, খেলনা বন্দুক কেনায় বাবামায়ের ঘোর আপত্তি। বুলটুটা যে কোথা থেকে এরকম মারকুট্টে হল কে জানে! সত্যি সত্যি ছাদে উঠে প্র্যাকটিস করে একটা কাক মেরে ফেলেছিল। তারপর কী কাণ্ড। সারা পৃথিবীর যত কাক সবাই আমাদের ছাদে এসে ধরনা দিল, ঘেরাও করল, চেঁচামেচি, কাকেদের মিটিং মিছিল, স্লোগান, কত কি চলল ছাদে সারাদিন। পাড়ার লোক অস্থির। রাতে কাকেরা যে যার বাসাতে ফিরে যেতেই রঘুভাই মরা কাকটাকে নিয়ে ভ্যাট—এ ফেলে দিয়ে ছাদে ফিনাইল ছড়িয়ে দিল। আর মা এয়ারগানটাকে নিয়ে আলমারিতে তুলে দিলেন। সেই এয়ারগানটা বের করে দিতে বলছে বুলটু। মা দেবেন না। রীতিমতো লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে, বাড়িতে দুটো দল। কাকু, জেঠুমণি, পুটুস বুলটুর পক্ষে। বাবা, মা, ছোটমা, আমি, এগেইনস্টে। সংখ্যায় যে সমান সমান হয়ে গেছে দুটো দল। তাই ঝগড়া মেটেনি। পিসিমণি আসুক, পুলকি ”গ্রিন—পিস” শান্তির জাহাজের জন্য চাঁদা না কি যে, তুলছিল একবার—ও শান্তিবাদী। ও বন্দুকের বিপক্ষে। পিসেমশাই, পিসিমণি? ঠিক জানি না। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির সময়ে ওদের দু’রকম মত ছিল, পিসেমশাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আর পিসিমণি প্রাণদণ্ড। সেবারেও আমাদের পরিবার বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ছোটকাকু আর ছোটমা প্রাণদণ্ডবিরোধী। বাবামা জেঠুমণি…ধনঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে। বুলটু—পুলকি আমিও অবশ্য বাবামার দলেই। ইশ! হেতাল পারেখের কী অবস্থাই করেছিল লোকটা! পুলকির চেয়েও ছোট মেয়ে ছিল সে তখন।
দেখা যাক আজ কী হয়। মা—ই জিতবেন শেষপর্যন্ত, কেননা আলমারির চাবিটি মায়ের কোমরে বাঁধা। মা বন্দুক বের করে দেবেন না। জঙ্গল বললেই বন্দুক মনে হবে কেন? হরিণ, খরগোশ খেলা করছে সেটাই তো ভালো। শিকার মানেই তো খুন। মার্ডার। নিরীহ প্রাণীদের অযথা সংহার করা মানুষের কাজ নয়। জীবজন্তুরাও খিদে না পেলে শিকার করে না। মানুষই কেবল খুন করবার শখে খুন করে। হাতি, হরিণ, পাখি—কেন যে মারে মানুষ? এখন অবশ্য অনেক সংরক্ষিত অরণ্য হয়েছে। বাঘ সিংহ তো সংরক্ষিত প্রাণী, তাদের কেউ আর হত্যা করে না। কিন্তু শিং আর চামড়ার জন্য হরিণ, দাঁতের জন্য হাতি, খড়গের জন্য গন্ডার—চোরাশিকারীর দল অনবরত অন্যায় করে মেরে ফেলছে। ব্যবসার জন্যে ভাল্লুক, সাপ—কত কী যে ধবংস করছে লোভী মানুষ। ভাল্লুকের ‘ফার’, সাপের চামড়া, সবই বিদেশে রপ্তানি হয়, অনেক ডলার পায় ব্যবসায়ীরা। কিন্তু শিকারীরা? যারা এই মহাপাপ করছে? তারা কিন্তু খুব একটা কিছু বেশি অর্থ উপার্জন করে না এই নৃশংস কাজ করে! বসে বসে সবটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মা আমাদের। বুলটুকেও। তার জেদ, সে কোনও অসংরক্ষিত প্রাণী মারবে। খরগোশ তো কোটি কোটি জন্মাচ্ছে রোজ রোজ। একটা দুটো মারলেই বা। ছোটমা বললেন—মানুষ তো কোটি কোটি জন্মাচ্ছে, তাবলে মানুষ মারবে?
আমি ক্যামেরা নিচ্ছি, তিনটে ফিল্ম নিচ্ছি। পুলকি পিসিমণিকে ভিডিও ক্যামেরাটা নিতে সাধছে—ওটা পিসিমণির চেয়ে পুলকিই বেশি ভালো হ্যান্ডল করতে পারে। কিন্তু পুলকির হাতে তো অত দামী ক্যামেরা ছেড়ে দেবেন না পিসিমণি। যা অন্যমনস্ক মেয়ে! পুলকিটাকে পিসেমশাই তাঁর পুরোনো Cell phoneটা দিয়ে দিয়েছিলেন—সেই শুনে বুলটুর কী কাণ্ড। পুলকিও কেন পাবে? ওর কেন নেই? জেঠুমণি যে আমাকেও একটা Cell phone কিনে দিয়েছেন। কলেজে ঢুকেছি বলে উপহার—যাতে যোগাযোগ রাখতে পারেন বাড়ির সকলে। খুব কমই ব্যবহার করি—SMS করি প্রধানত। আমরা ট্রেনে করে ঝাড়গ্রাম অবধি যাবো। সেখানে গাড়ি নিয়ে থাকবেন নতুন কাকাবাবুরা। নতুন কাকাবাবুদের শঙ্করকাকা, সরোজকাকা, শিবকাকা এই বলেই ডাকবো—’কাকু’ বলা কঠিন। এখন তো আমরা বড় হয়ে গেছি। পুলকি আসছে—কিন্তু পিসেমশাই পিসিমণি এখন আসবেন না। ওঁর কেস আছে, কোর্ট খোলা। ওঁরা দুজন পরে সোজাই গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন। ওঁদের সেই মস্ত ‘কোয়ালিস’ গাড়ি নিয়ে। তাতে আমরা সবাই এঁটে যাবো ফেরবার পথে। পুটুসকে নিয়ে আমরা মোট এগারোজন, প্লাস পিসিমণির ড্রাইভার নওশাদভাই। ওতে আঁটে দশজন। ঠাসাঠাসি হবে। তা হোক। তবু আমার দারুণ লাগছে ভাবতে—সবাই মিলে যেন একটা লম্বা পিকনিকে যাচ্ছি। শুধুই পিকনিক নয়, একটা ডিসকভারির জার্নিও তো বটে?