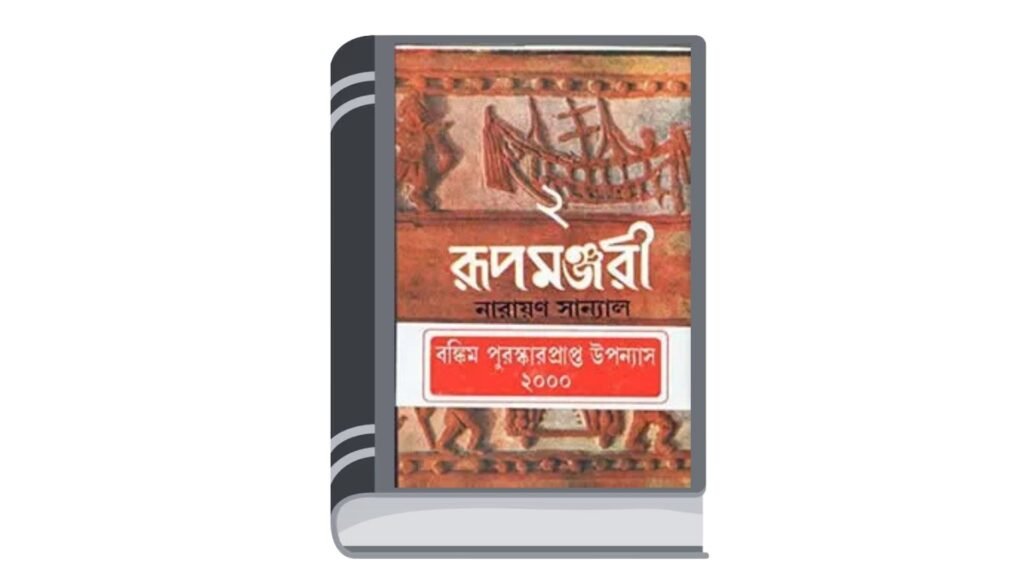রূপমঞ্জরীর সন্ধানে – সপ্তম পৰ্ব
রূপমঞ্জরীর সন্ধানে—সপ্তম পৰ্ব
১
দ্যাখ না-দ্যাখ আমি যদি লোটাকম্বল কাঁধে নিয়ে রূপমঞ্জরীর সন্ধানে রওনা হয়ে পড়ি তাহলে আপনাদের আপত্তি করার সঙ্গত কারণ থাকতে পারে, বিশেষ যাঁরা প্রথম খণ্ড ‘রূপমঞ্জরী’ এখনো পড়েননি। আমি আশা করব : ‘পেরথম ভাগ’ শেষ করে তারপর আপনারা ‘দ্বিতীয় ভাগ’ বা ‘কথামালায়’ হাত দেবেন। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে যদি তা না হয় তাহলে সেই ব্যতিক্রম পাঠক-পাঠিকাকে গল্পের ধরতাইটা আমাকেই ধরিয়ে দিতে হবে।
প্রথম প্রশ্ন: ‘রূপমঞ্জরী’ লোকটা কে? তার দুটি উত্তর। প্রথমত, এটা যদি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হতো তাহলে বলতে পারতাম—‘রূপমঞ্জরী আমার দিদিমার দিদিমার-দিদিমা টু দ্য পাওয়ার টেন’—অর্থাৎ ‘দশম-নারী’ পর্যন্ত উজানে গেলে তাঁকে পাবেন। সে হিসাবে রূপমঞ্জরী হচ্ছেন উত্তর-শ্রীচৈতন্য ও প্রাক্-শ্রীরামমোহন যুগের প্রথম নারী বিদ্রোহিণী।
দু-দুটি ঐতিহাসিক নারী গতদশকের শেষাশেষি আমার রাত্রের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে কালের ব্যবধান বা ভৌগোলিক দূরত্ব তবু কিছুটা আছে, কিন্তু নাম, রূপ ও চরিত্রে বিশেষ ফারাক নেই। দুজনেই অসামান্যা বিদুষী, দুজনেই পুরুষশাসিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় সমাজকে নস্যাৎকরেছিলেন। প্রতিবেশী রাজ্যে মৌলবাদী ধর্মান্ধদের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে তসলিমা নাসরিন যে ভাবে তাঁর স্কন্ধস্থিত মাথাটি নিয়েই ইউরোপে চলে গেছেন, হটী বিদ্যালঙ্কারও প্রায় সেইভাবে গৌড়মণ্ডলকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন কাশীধাম। হটা বিদ্যালঙ্কার (1743–1810) চিতাভষ্টা অবস্থায় কাশীধামে উপস্থিত হয়ে এক মহাপণ্ডিতের ভদ্রাসনে আশ্রয় পান। তাঁরই পালিতাকন্যারূপে ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারিণী হন। কাশীর পণ্ডিতসমাজ যখন তাঁকে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি প্রদান করেন তখনো রাধানগরে শ্রীরামমোহনের আবির্ভাব হতে প্রায় এক দশক বাকি! তদানীনন্তন কাশীর কট্টর পণ্ডিতেরা ঠিক এই দু-আড়াই’শ বছর পরে পুরীর ধর্মান্ধ ‘শঙ্করাচার্য’ যেমন নিদান হেঁকেছেন—বলেন স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নেই। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে একটি বিচারসভায় এ নিয়ে তর্ক হয়। হটী বিদ্যালঙ্কার প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করে প্রমাণ করেন, স্ত্রীলোকের বেদপাঠের অধিকার হিন্দুধর্মে স্বীকৃত। অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন কাশীর চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাদান করেছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন তার পরের বছর হটা কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। প্রথম যুগে আন্দাজ করা যায় অধ্যাপিকা এবং ছাত্ররা প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন! তিনি প্রকাশ্যে পণ্ডিতসভায় তৰ্কাদিতে যোগ দিতেন এবং পণ্ডিতদের প্রাপ্য দক্ষিণাও গ্রহণ করতেন।
দ্বিতীয়া, হটু বিদ্যালঙ্কার—বয়সে হটী অপেক্ষা তিন দশকের অনুজা। জন্ম : কলাইঝুটি, বর্ধমান (আঃ 1775–1875)। পিতা পরম বৈষ্ণব নারায়ণ দাস। কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় লাভ করে তিনি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার নির্দেশে আত্মজার বাল্যবিবাহ দানে অস্বীকৃত হন। পরিবর্তে তাকে নানান বিদ্যাচর্চায় শিক্ষিতা করে তোলেন : ব্যাকরণ, সাহিত্য ন্যায়, নব্যন্যায় এবং আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যা। এঁর ডাকনাম হটু; কিন্তু পোশাকী নাম রূপমঞ্জরী!
হটু তরুণী বয়সে সরগ্রামনিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের গুরুগৃহে বাস করে সাহিত্য এবং চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি চিরকুমারী। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, ইনি পুরুষদের মতো মস্তকমুণ্ডন, শিখাধারণ ও উত্তরীয় পরিধান করতেন। সমাজ তা মেনে নিয়েছিল।
এই দুই অলোকসামান্যা মহিলার সন্ধান পাই আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ ধন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চটি বইতে: সাহিত্যসাধক চরিতমালা সিরিজের প্রামাণিক সূত্রে: চতুষ্পাঠীর বিদুষী মহিলা।
স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, বিগত দশকে এঁরা দুজন আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন যখন হামাগুড়ি দিতে শেখেননি, তখন কোনও পিতৃহীন বাঙালি ‘বালবিধবা চিতাভষ্টা পরিচয়ে বারাণসীধামে উপনীত হয়ে অন্তিমে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি গ্রহণ করছেন, অথবা বিচারসভায় পুরুষ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করছেন লেখকের কল্পনায় নয়, বাস্তবে এটা প্রণিধান করে গর্বে বুকটা ফুলে উঠেছিল। কিংবা রামমোহনের প্রায় * সমবয়সী একটি বাঙালি মহিলা আজীবন অবিবাহিতা থেকে পুরুষের বেশে স্বগ্রামে নর-নারী নির্বিশেষে চিকিৎসা করছেন; ছাত্রদের শারীরবিদ্যা শেখাচ্ছেন, এটা কি কম বড় কথা?
রূপমঞ্জরীর দ্বিতীয় পরিচয়: তিনি আমার দিদিমার-দিদিমার-দিদিমার দিদিমা…নন। সে আমার কন্যা! তাকে আমি নতুন করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম আমার উপন্যাসের পাতায়। ওই দুই অসামান্যা হটী আর হটু’র সংমিশ্রণে।
রচনা কিছুটা অগ্রসর হবার পর গত দশকের শেষ বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে—কিছু ‘চিত্তচাঞ্চল্য’ অনুভব করি। একটি নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এক কালো মুখোশধারীর সঙ্গে আমার কিছু তার হয়—একটি প্রত্যঙ্গের দখলদারী নিয়ে। সওয়া তিনকুড়ি বছরের স্বত্বাধিকার আগ্রাহ্য করে সে আমার হৃদপিণ্ডটা জবরদখল করতে চাইছিল। অনেক লড়াই করে বাড়ি ফিরে এসে দেখি ইতিমধ্যে আমার সেই মেয়েটি হারিয়ে গেছে! ‘বামি’র হাতের প্রদীপশিখাটির মতো!
তাই এই: ‘রূপমঞ্জরীর সন্ধানে’!
২
কিন্তু ওটা তো আত্মনেপদী কৈফিয়ৎ। আপনাদের গল্পের ধরতাইটা সংক্ষেপে ধরিয়ে দিই: পরস্মৈপদী কৈফিয়ৎটা : ইংরেজি 1744 খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ ক্রান্তিকারী পলাশীযুদ্ধের পূর্বদশকে, সদ্যোবিবাহিত একটি দম্পতি—হবু-রূপমঞ্জরীর পিতা ভেষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা মঞ্জরী নৌকাযোগে তীর্থদর্শনে বার হয়ে পড়েন। রূপেন্দ্রনাথের পৈত্রিক নিবাস বর্ধমানের সোঞাই গ্রামে, দামোদরের তীরে। ওঁরা কিছুটা পদব্রজে, কিছুটা নদীপথে এসে ভাগীরথীর দুই তীরে সেকালীন বর্ধিষ্ণু জনপদগুলির—রনার ঘাটি, চক্রদহ, প্রদ্যুম্ননগর, ত্রিবেণী, বংশবাটি, সপ্তগ্রাম, ওলন্দাজনগর, মূলাজোড়, বৈদ্যবাটি প্রভৃতির—বিভিন্ন মন্দিরে দেবদর্শন করছিলেন ক্রমে ক্রমে। পথে পড়ল ‘মাহেশ’ সেখানে বাস করতেন শ্রীভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়, রূপেন্দ্রের পিসাশ্বশুর। অগত্যা সেখানে আশ্রয় নিতে হল, কদিনের জন্য। এ-ঘটনা রূপেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় দেড়বছর পরে। মুশকিল হল এই যে, মঞ্জরীর পিসিমার অভিজ্ঞ চোখে ব্যাপারটা আর গোপন রইল না। রূপেন্দ্ৰ জানতে পারলেন, তাঁর স্ত্রী পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। পিসাশ্বশুর ওঁদের যৌথ তীর্থভ্রমণ বন্ধ করে দিলেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে গৃহের বাহিরে যাওয়াটাই অনুমোদনযোগ্য নয়। অগত্যা রূপেন্দ্র একলাই ভাগীরথীর দুই তীরে তদানীন্তন গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতিতে কী যেন একটা খুঁজে বেড়াতে থাকেন।
তিনি কী খুঁজছিলেন জানতে হলে রূপেন্দ্রনাথের চরিত্রটাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করতে হবে।
রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পিছনে কী যেন একটা উপাধি ছিল; কিন্তু এখন আর তার কোন নিশানা নেই। রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম অথবা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল না বটে, কিন্তু ওঁর গ্রামখানিকে কেন্দ্রবিন্দু করে পঁচিশ ক্রোশ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত টানলে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে দেখা যেত সে-আমলে তিনি সুপরিচিত : রূপেন্দ্রনাথ নামে নয়; দুটি পৃথক অভিধায় : ‘একবগ্গা ঠাকুর’ আর ‘ধন্বন্তরি’।
প্রথম উপাধিটা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কারণ সমকালের ধারণায় তিনি এক সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক আধুনিকমনা প্রগতিবাদী। প্রতিটি শাস্ত্রীয় অনুশাসন তিনি নিজের বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে গ্রহণ করতেন। তা বেদবাক্য হলেও।
দ্বিতীয় উপাধিটা তাঁর অসাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য। বাল্যকালে তিনি চলে যান ত্রিবেণী। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, ন্যায়, নব্যন্যায়, দর্শন ইত্যাদি শেষ করে তিনি চলে আসেন সরগ্রামনিবাসী স্বনামধন্য কবিরাজ আচার্য গোকুলানন্দের পিতামহের কাছে। দীর্ঘ সাত বছর আয়ুর্বেদশাস্ত্র, চরক, সুশ্রুত ও নিদান আয়ত্ত করেন। গোকুলানন্দের নির্দেশে তিনি স্ত্রীরোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন—যা নাকি সমকালে এক সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। তবে কোনও রোগিণীর দেহস্পর্শ করার সময় গুরুর আদেশে একটি শর্ত তিনি আরোপ করতেন ওই সময় প্রাপ্তবয়স্ক দ্বিতীয় একটি রমণীর উপস্থিতি আবশ্যিক।
‘মধুচন্দ্রিমা’ শব্দটা তখনও অভিধানে ওঠেনি! ওমা! কী বোকার মতো বলছি! বাংলা ‘অভিধান’ বস্তুটাই তো তখনও জন্মায়নি।* মোট কথা, যে-আমলের কথা, তখন সদ্যোবিবাহিতাকে নিয়ে ‘হনিমুন’ তো ছাড়, প্রচলিত নির্দেশটি ছিল : পথি নারী বিবর্জিতা।
[* প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিই : রূপমঞ্জরীর (বাস্তব হটী বিদ্যালঙ্কারের) জন্মের পূর্ব বৎসর ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ এবং ‘বাঙলা ব্যাকরণ’ প্রকাশিত হয়েছিল পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে মানোএল-দা আসুম্পসাঁও-এর প্রচেষ্টায়।]
তবে ওই! একবগ্গা-ঠাকুর ছিলেন ব্যতিক্রম। তাই বছর না ঘুরতেই সহধর্মিণীর শাঁখাপরা হাতটি ধরে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন পিতৃমাতৃহীন রূপেন্দ্রনাথ। সোঞাই গ্রামের বাড়িতে পড়ে রইলেন বৃদ্ধা পিসিমা জগুঠাকরুন, এক পিসতুতো বোন কাত্যায়নী আর তার ঘরজামাই স্বামী।
বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে উনি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করেছিলেন ভাগীরথীর দুই কিনারে। নদীমাতৃক বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এই ভাগীরথীর দুই তীর। গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত . ‘গঙ্গারিডি’ যথার্থ গঙ্গাহৃদি। জননী তাঁর স্তনভাণ্ডারের নির্মল ধারায়, পলিমাটির আশীর্বাদে, নাব্য স্রোতধারায় এ-দেশকে দিয়েছেন পানীয়, শস্য, পরিবহনের সুযোগ। তাই ভাগীরথীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে বঙ্গ-সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রগুলি : নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, মূলাজোড়, কালীঘাট।
গঙ্গাতীরের অযুত-নিযুত মন্দিরে ‘পেন্নাম’ ঠুকতে নয়, তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন একটি ‘পরশপাথর’।
আকৈশোর তিনি যে একটা স্বপ্ন দেখে আসছেন :
‘ধর্মসংস্থাপনার্থায়’ ‘তাঁর’ যে আবার আসার কথা!
ঠিক যেমন অদ্বৈতাচার্য প্রতীক্ষা করেছিলেন নবদ্বীপে প্রায় তিনশো বছর আগে। তিনি আবার আসবেন, তাঁকে আসতেই হবে! এই অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে ধরে আবার তিনি একটা ঝাঁকি দেবেন। এটাই ভারত-সংস্কৃতির ট্র্যাডিশন। শাক্যসিংহ এভাবে সমাজকে ধরে নাড়া দিয়েছিলেন দু-আড়াই হাজার বছর আগে। দিয়েছেন আদি শঙ্করাচার্য। দিয়েছেন সম্প্রতি চৈতন্যদেব। রূপেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, সেই তিনি আবার ওঁর সমকালে আবির্ভূত হয়েছেন এখনও প্রকট হননি, এই যা! তাহলে তিনি লুকিয়ে
আছেন এই ভাগীরথী-বিধৌত কোনও একটি পুণ্যতীর্থে। শাক্যসিংহ ছিলেন রাজপরিবারভুক্ত–রানী ভবানী বা কৃষ্ণচন্দ্রও তাই। আদি শঙ্করাচার্য বা নিমাই পণ্ডিত শৈশবে সোনার ঝিনুকে দুধ খাননি–যেমন তা করেননি বুনো রামনাথ বা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। এঁদের মধ্যে কে এগিয়ে আসবেন রূপেন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক হতে?
ভারতীয় সংস্কৃতি আজ ভগ্নপক্ষ সম্পাতির মতো ধুঁকছে।
কিন্তু কেন?
রূপেন্দ্রনাথের ধারণা, তার দুইটি হেতু।
প্রথমত, ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা চাপিয়ে দিয়েছে তার পিঠে এক জগদ্দল বোঝা। তা পিঠে নিয়ে আকাশে ওড়া মহাশক্তিমান গরুড়-এর পক্ষেও সম্ভবপর হচ্ছে না। সেই বোঝা অবহেলিত, উপেক্ষিত একদল শক্তিমান মানুষ—টুলো-পণ্ডিত সমাজের নিয়ন্ত্রকদের মতে যারা অদ্ভুত, জল-অচল, শূদ্র।
দ্বিতীয় বাধা, বিহঙ্গমের একটি পাখা বিদীর্ণ করা হয়েছে। করেছেন, ওই মহামহা পণ্ডিত তথা কূপমণ্ডুকের দল : নারী-সমাজ। অশিক্ষায়, অবজ্ঞায়, অন্ধকারে, অত্যাচারে নারীসমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাকে ‘নরকের দ্বার’ রূপে চিহ্নিত করেছিলেন স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্য! চৈতন্যদেব যবন হরিদাসকে বুকে টেনে নিলেন। আচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন কিন্তু হতভাগী বিধবাদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি! রূপেন্দ্রনাথ ভাগীরথীর দুই তীরের নানান জনপদে সন্ধান করে ফিরছেন সেই পরশপাথরটি—
রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি, সেই মহাপুরুষটি তখনও অজাত।
রাধানগরে তাঁর আবির্ভাব হতে তখনও তিন দশক বাকি।
৩
দীর্ঘ তীর্থপরিক্রমা সমাপ্ত করে রূপেন্দ্রনাথ যেদিন মাহেশে ফিরে এলেন, ঘটনাচক্রে সেদিনই মঞ্জরীর প্রসব-বেদনা উঠেছে। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের গোশালার পাশে নবনির্মিত একটি সূতিকাগারে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মঞ্জরী।
দুর্ভাগ্য একেই বলে! সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে প্রাণ দিল মঞ্জরী। ‘মৃত্যু’টা ট্র্যাজেডি নয়—মৃত্যু তো ছায়ার মতো ঘুরছে জীবনের পিছু পিছু। মঞ্জরী প্রাণ দিল মাত্র বিশ বছর বয়সে সেটাও বেদনার সূচীমুখ নয় চরম ট্র্যাজেডি হল : সূতিকাগারে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না আচার্য গোকুলানন্দের শ্রেষ্ঠ ছাত্রটিকে,—প্রসূতিবিদ্যায় যাঁকে ‘ধন্বন্তরি’ আখ্যা দিয়েছিল গাঁয়ের মানুষ। রূপেন্দ্রনাথ জীবনে যিনি কখনও মাথা নিচু করেননি, তাঁর শ্বশুরালয়ের প্রতিটি মানুষের কাছে করজোড়ে মিনতি করেও অনুমতি পাননি—ওই সূতিকাগৃহে প্রবেশের। অথচ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নিজে হাতে প্রসব করাতে পারলে তিনি সন্তান ও জননীকে বাঁচাতে পারতেন। জটিলতাটা কী তিনি বুঝেছেন, কিন্তু সেটা বুঝতে বা শুনতে রাজি হল না বৃদ্ধা ধাত্রী!
–কী অসৈরণ কতা গো! আঁতুড়ে বেটাছেলে!
প্রসূতির কী জাতীয় জটিলতা হচ্ছে, কেন সে মর্মান্তিক কাতরাচ্ছে তা কানে শুনতে হল অশিক্ষিতা ধাত্রীর কাছে। আন্দাজে বিধান দিতে গেলেন। তাও সে শুনলো না। বললে, ছেলে বিইয়ে বিইয়ে চুলগুলো সব সনের দড়ি হয়ি গেল, ওই একফোঁটা লেড়াডার কাছে বিধান নিতি হবে? ক্যানে গো? গলায় দড়ি জোটে না মোর!
নিষ্ফল আক্রোশে শৃঙ্খলাবদ্ধ শার্দুলের মতো ত্রিযামারাত্রি পায়চারি করে ফিরেছেন তারাভরা আকাশের নিচে—সূতিকাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে। দ্বিতল বাড়ি। পুরুষেরা যে- যার শয়নকক্ষে নিদ্রাগত। আজ রাত্রে অনেকেই শয্যাসঙ্গিনীবঞ্চিত। কারণ মহিলাদের অধিকাংশই সুতিকাগৃহের আনাচে-কানাচে। বর্ষীয়সী কয়েকজন আর পরিবারের তিনকাল- গিয়ে-এককাল-ঠেকা এক বৃদ্ধা ধাত্রী রয়েছে সুতিকাগারের অভ্যন্তরে। গোয়ালঘরের পাশে এটি একটি নবনির্মিত সাময়িক আচ্ছাদন বুকা-পিঠা মুলিবাঁশের চৌখুপি দেওয়াল, বেনাঘাসের একচালা। প্রতিবারই পরিবারে কোনও স্বামীসোহাগিনীর সন্তানবতী হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে এখানে সাময়িক খড়ো-চালা নির্মিত হয়। পাকা প্রসূতি-আগার নাকি নিয়ম- বহির্ভূত। ঠিক জানা নেই হয়তো স্বয়ং মনুর বিধান। হবেও বা—স্বয়ং জগত্রাতা যীশুখ্রিস্টকেও তাই আবির্ভূত হতে হয়েছিল অশ্বাবাসের একান্তে।
দ্বার রূদ্ধ। গৃহাভ্যন্তরে কী ঘটছে জানতে পারছেন না। দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু মাঝে মাঝে স্বকর্ণে শুনছেন ধর্মপত্নীর মর্মান্তিক আর্তনাদ। সে আর্তনাদ–মনে হচ্ছিল রূপেন্দ্রনাথের–শুধু দৈহিক যন্ত্রণায় নয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডুকদের এই নৃশংস ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যেন এক জান্তব প্রতিবাদ!
হঠাৎ মনে পড়ে গেল ক’মাস আগেকার কথা। এই বাড়িরই ওই উপরের ঘরে। যেদিন মশারি-ফেলা জনান্তিকে একপ্রহর রাত্রে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে কুসুমমঞ্জরী প্রথম স্বীকার করেছিল যে, সে মা হতে চলেছে! রূপেন্দ্র ওকে বুকে টেনে নিয়ে মুখচুম্বন করে বলেছিলেন, তুমি আমাকে সন্তান দিয়েছ, তোমার একটা পুরস্কার পাওনা! বল মঞ্জু, কী নিয়ে আসব তোমার জন্য এবার, তীর্থ থেকে ফেরার সময়?
ভারি সুন্দর জবাবটি দিয়েছিল মঞ্জু। বলেছিল, তুমি না ফুলশয্যার রাতেই আমাকে বলেছিলে : স্বামী আর স্ত্রীর সমান অধিকার! তাহলে ও-কথা বলছ কেন? কে কাকে উপহার দিল তার তো হিসেব নেই!
তা বটে। তবু রূপেন্দ্রনাথ ওকে বলেছিলেন কিছু চাইতে। আর্জকের এই রাত্রিটি, এই বিশেষ মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখতে একটা স্মারকচিহ্ন দিতে চান তিনি।
কুসুমমঞ্জরী বলেছিল, তাহলে আমি যা চাইব তাই দেবে?
—দেব, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়।
—আমার বড় সাধ লেখাপড়া শেখার। তুমি আমাকে শেখাবে? লুকিয়ে লুকিয়ে?
রূপেন্দ্র শয্যাপ্রান্তে উঠে বসেছিলেন। এমন একটি গোপন বাসনা যে কুসুমমঞ্জরীর অন্তরের গভীরে সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে তা আন্দাজ করতে পারেননি। যে-কালের কাহিনী সে-কালের প্রচলিত সংস্কার ছিল স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় হলে তার বৈধব্যযোগ অনিবার্য! তাই রূপেন্দ্র অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী বলছো মঞ্জু?তোমার ভয় হয় না? লোকে বলে, লেখাপড়া শিখলে….
মঞ্জু তার শাঁখা-পরা হাতটা বাড়িয়ে ওঁর মুখে চাপা দিয়েছিল। বলেছিল, ও-কথা বলো না! তুমিই তো বলেছো সেটা ভুল, সেটা মূর্খদের কুসংস্কার!
তা বলেছেন। গার্গী-মৈত্রেয়ীর কাহিনী শুনিয়েছেন ধর্মপত্নীকে। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, তাই হবে, মঞ্জু। শেখাব, তোমাকে বাঙলা পড়তে, লিখতে শেখাব। সংস্কৃতও শেখাব। কিন্তু এখানে তো তা সম্ভবপর নয়। এখানে সুযোগ হবে না। জানাজানি হয়ে যাবে। তোমার পিসিমা বা পিসেমশাই যদি একবার নিষেধ করে বসেন
—না, না, এখানে নয়। সোঞাই ফিরে গিয়ে।
—সেই ভাল, কথা দিচ্ছি ওর হাতেখড়ি দেবে ওর মা, বাবা নয়। অক্ষর পরিচয়ও করাবে তার মা। ঠিক যেমন পৌরাণিক যুগে কাশীর রাজমহিষী মদালসা শিক্ষিত করেছিলেন, দীক্ষা দিয়েছিলেন রাজপুত্র অলকের।
মঞ্জু বুদ্ধিমতী। বুঝেছিল ঠিকই, তবু দুষ্টুমি করে শুনতে চেয়েছিল, কার কথা বলছ তুমি?
—আত্মদীপের।
মঞ্জু সলজ্জে মুখ লুকিয়েছিল ওঁর বুকে।
আত্মদীপ! নামটা রূপেন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বেই স্থির হয়ে আছে। নামকরণ করেছিলেন রূপেন্দ্রনাথের বয়স্য, সমকালীন বঙ্গ-সরস্বতীর প্রিয়তম সেবক–অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
বিবাহের পূর্বে রূপেন্দ্রনাথ বিশেষ কারণে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কবিগৃহে। কবি একাই থাকতেন প্রোষিতপত্নীক; অতিথি রূপেন্দ্রনাথ অবিবাহিত। যদিও বিবাহের দিন ও পাত্রী নির্বাচন তার পূর্বেই হয়েছিল। বিদায়ের দিনে রূপেন্দ্র বন্ধুবর ভারতচন্দ্রকে সুসংবাদটি জ্ঞাপন করেন এবং বিবাহরাত্রে সোঞাইগ্রামে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন।
কবিবর বলেছিলেন, রূপেন্দ্র, তোমার আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম; কিন্তু বুঝতেই পারছ, এত দূরের পথে আমার পক্ষে নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। হয়তো তোমাতে আমাতে আর কখনও দেখাই হবে না। তাই—তুমি যদি অনুমতি দাও—আমি তোমার-আমার বন্ধুত্বের একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিতে ইচ্ছুক, যাতে আমার কথা তোমার বারে বারে মনে পড়ে যায়। তোমার শুভবিবাহে এই দীন কবি আর কী উপহার দিতে পারে বল?
—কী উপহার? শুনি আগে জানতে চেয়েছিলেন রূপেন্দ্র,
—মদনারিরিপুর আশীর্বাদে তোমাদের মিলন সার্থক হবেই। সেই অনাগত মানবশিশুটির নামকরণ আমি করে দেব। তাকে যতবার ডাকবে ওই সূত্রে ততবারই এই দীন কবির কথা তোমার স্মরণ হবে।
রূপেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। প্রশ্ন করেন, বল? কী নাম?
-–তোমার পুত্রের নাম দিও: আত্মদীপ।
—আত্মদীপ?
—হ্যাঁ। বিবেকনির্দেশে জীবনে পথ খুঁজে এগিয়ে যাওয়াই তোমার ব্রত। কোনও শাস্ত্রবাক্যকেই বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করো না। শোন, মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধ যখন কুশীনগরে শেষশয্যায় শায়িত, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য আনন্দ। তিনি জানতে চেয়েছিলেন : ‘আপনার মহাপরিনির্বাণের পর আমরা কার কাছে যাব পথনির্দেশ যাজ্ঞা করতে?” জীবনের শেষনিশ্বাসের সঙ্গে পরমকারুণিক তথা পরমবুদ্ধ অন্তিম নির্দেশ দিয়েছিলেন:
‘আত্মদীপো ভব!
আত্মশরণো ভবো!
অনন্যশরণো ভব!’
নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালাও। কারও কাছে পথের সন্ধান চাইতে যেও না। নিজের বিবেকের আলোয় জীবনের পথ পরিক্রমা করো।
রূপেন্দ্র হেসে বলেছিলেন, বন্ধু! তুমি অপূর্ব নামকরণটি করেছ। আমার পুত্রসন্তান হলে নিশ্চয় তার নাম দেব : ‘আত্মদীপ’, কিন্তু তুমি কট্টর স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো এ-পরামর্শ দিলে; কিছু মনে করো না বন্ধু, ঠিক কবির মতো নয়!
—কবির মতো নয়? কেন, কী ত্রুটি হল আমার?
—তুমি কবি হিসেবে বিস্মৃত হয়েছো—এই রূপরসশব্দ গন্ধস্পর্শময় জগতের অধিকার একা পুরুষের নয়। এ-বিবাহ সার্থক হলে পুত্রের পরিবর্তে আমার প্রথমে কন্যা-সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, তাই নয়?
ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, ঠিকই বলেছ বন্ধু! পুত্রের নামকরণ করেছিল কট্টর বামুনপণ্ডিত; এবার কন্যার নামকরণ করবে: ‘কবি’। রূপেন্দ্রনাথ আর কুসুমমঞ্জরীর যৌথ মনসিজ-সাধনার ফলশ্রুতি যদি কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়, তবে তার নাম হোক : রূপমঞ্জরী!
সহসা চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল রূপেন্দ্রনাথের। সুতিকাগৃহের অভ্যন্তর থেকে ভেসে এল এক মিলিত ক্রন্দনরোল!
শেষ হয়ে গেল! সব শেষ হয়ে গেল! আত্মদীপ নয়, রূপমঞ্জরী নয়–কেউই এল না। অকালে বিদায় নিল তাদের মা! বিনা চিকিৎসায়! কুসংস্কারের বলির পশু! সূতিকাগারের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করে সম্মিলিত নারীকণ্ঠের ক্রন্দনরোল, তারই প্রমাণ।
রূপেন্দ্রনাথ বাঁশের খুঁটিটা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন। মাথার ভিতর টলে উঠেছিল তাঁর। পরমুহূর্তেই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। অপরিসীম নির্বেদে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর। মুহূর্তে জীবনের অর্থটাই যেন হারিয়ে গেল। আশঙ্কা হল এখনি হয়তো শ্বশুরবাড়ির গুরুজনেরা যাঁরা কুসংস্কারের কৈঙ্কর্যে আদরের মেয়েটাকে বাঁচতে দিলেন না তাঁরা সহানুভূতি জানাতে হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসবেন। সেটা সহ্য হবে না ওঁর। সম্মোহিতের মতো পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এলেন বাহিরে। তারায় ভরা আকাশের নিচে। টুপ-টুপ করে শেষ রাতের শিশির ঝরে পড়ছে গাছ থেকে। এক আকাশ কৌতূহলী তারা। পুব আকাশটা সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে। পাখ-পাখালির কিচিমিচি এখনো শুরু হয়নি বনে-বনান্তরে। ধীরে ধীরে সমুখপানে মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে চললেন রূপেন্দ্রনাথ—নগ্ন গাত্রে, নগ্ন পদে, কপর্দকহীন অবস্থায়। চেতনাহীন সম্মোহিতের মতো।
৪
নিজেকে আবিষ্কার করলেন পুণ্যতোয়া মা গঙ্গার তীরে। এক প্রহর বেলায়। ছয় ক্রোশ দূরে। ফ্রেডরিক নগরের পারানিঘাটের একান্তে এক বিশাল বটবৃক্ষের নিচে বসে আছেন তিনি। সামনে দিয়ে লোকজন চলেছে গঙ্গাস্নানে। গঙ্গায় সারি সারি নৌকা–ছিপ, পানসি, মাছমারাদের নৌকা, বজরা। মাঝ-গাঙে ভাসছে এক বিচিত্র জলযান–অর্ণবপোত।
মাহেশ আর রাধাবল্লভপুর—দুখানি পাশাপাশি গ্রাম। রাধাবল্লভপুরে আছে রুদ্রপণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের অপূর্ব মূর্তি; আর মাহেশের রথ তো সুবিখ্যাত। মনে আছে নিশ্চয়, বঙ্কিমের মানসকন্যা রাধারাণীও হারিয়ে গেছিল এই মাহেশের রথযাত্রার মেলাতেই। আমরা অবশ্য এখন আছি বঙ্কিম-জন্মের প্রায় একশ বছর আগে। এই দুই বর্ধিষ্ণু গ্রামের গঙ্গাতীরে : ফ্রেডরিক নগর। তোমরা বোধকরি ও-নামে চিনবে না। তাই বলি, তার বর্তমান নাম : শ্রীরামপুর। সেকালে তা ছিল দিনেমারদের ঘাঁটি। অদুরেই, কাহিনী-বর্ণিত স্থানকালের পরবর্তী যুগে, এখানে কবরস্থ হবেন: মার্শম্যান, ওয়ার্ড আর কেরীসাহেব। বাঙলা ছাপাখানায় প্রথম সংবাদপত্রটি যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন: ‘সমাচার দর্পণ”।
রূপেন্দ্রনাথ নিশ্চুপ বসে রইলেন ঘাটের কিনারে। অস্নাত, অভুক্ত। কী করবেন স্থির করে উঠতে পারছেন না। স্বপ্ন ছিল তীর্থপরিক্রমা সমাপ্ত করে সপুত্র, সস্ত্রীক প্রত্যাবর্তন করবেন পৈত্রিক ভিটেতে—সোঞাই গ্রামে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। না, ভুল হল, ভাগ্য নয়, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কিছু পণ্ডিতম্মন্যের সংস্কারের কৈঙ্কর্যে! গ্রামে ফিরে পুনরায় কবিরাজ বৃত্তি গ্রহণের বাসনা নেই। সে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন এক প্রিয় শিষ্যকে।
হঠাৎ নজর পড়ল মাঝগঙ্গায় ভাসমান সুবিশাল অর্ণবপোতটির উপর। ফ্রেডরিক নগরের বন্দরে আরও দু-তিনটি সমুদ্রগামী বড়জাতের জাহাজ ভাসছে। আকারে ওটি তাদের সমতুল; কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় মাস্তরে উপরিস্থিত অভিজ্ঞান।
তিন-তিনটি মাস্তুলে পাঁচ স্তরে পনেরোটি পাল। যুদ্ধজাহাজ নয়, কামান নজরে পড়ছে না। যাত্রীবাহী বা মালবাহী জাহাজ। কেন্দ্রীয় বৃহত্তম মাস্তুলের উপরে একটি ধাতব চক্ৰচিহ্ন
সূর্যালোকে ঝলমল করছে এবং তৎসংলগ্ন ত্রিকোণাকৃতি গরুড়-ধ্বজা বলে দেয় এটি ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ বা দিনেমারদের জাহাজ নয়। বাঙালির জাহাজ এবং হিন্দুর–যা বহু-বহুদিন নজরে পড়েনি রূপেন্দ্রের। বঙ্গোপসাগর আছে আজ কয়েক শতাব্দী বিদেশীদের কব্জায়—বিজয়সিংহ, চাঁদসদাগর, লক্ষিন্দর, ধনপতিদের কীর্তি ও কাহিনী ক্রমশ চলে গেছে মহাকালের নেপথ্যে টিকে আছে শুধু মঙ্গলকাব্যের পুঁথিতে।
বঙ্গোপসাগরে বিদেশীদের আগমন ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি–গৌড়েশ্বর মামুদ শাহের আমলে। তারা ছিল পর্তুগীজ। তারা ঘাঁটি গেড়েছিল প্রধানত মগের মুলুকে–চট্টগ্রামে। ক্রমে ভাগীরথী বেয়ে হুগলি-ব্যান্ডেলে। তারপর এল দিনেমারেরা। ওদের ঘাঁটি ছিল ওলন্দাজনগর, যার বর্তমান অভিধা: চুঁচুড়া। সবশেষে এসেছে ইংরেজ আর ফরাসী। প্রথমজন ইজারা নিয়েছে সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কালীঘাট অঞ্চল; ফরাসীরা চন্দননগর। দু- আড়াইশো বছরে নিঃশেষ হয়ে গেছে বাঙালি বণিকদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি, সিংহল থেকে চম্পানগর পর্যন্ত ছিল যাদের বিচরণভূমি, বিজয়সিংহের স্মৃতিবাহী : মধুকর, সপ্তডিঙা, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি অর্ণবপোত।
তাই অস্নাত, অভুক্ত ক্লান্ত মানুষটি উদাসনেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন ওই বিচিত্র জলযানটিকে। কার জাহাজ? কোথায় চলেছে? কোন্ ভরসায় চলেছে বোম্বেটে-অধ্যুষিত বঙ্গোপসাগরে?
হঠাৎ লক্ষ্য হল, ওই বিশাল জলযান থেকে একটি ডিঙি নৌকো জলে ভাসানো হল। দুজন মাঝি দাঁড় বেয়ে ঘাটের দিকে নিয়ে আসছে একমাত্র আরোহীটিকে। লোকটার মাথায় শামলা ধরনের শিরস্ত্রাণ, পরিধানে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে পিরাণ ও উত্তরীয়। নৌকাটি ঘাটে এসে ভিড়ল। মাঝি দুজন সাহায্য করল বাবুমশাইকে ঘাটে নামতে। জুতো-জোড়া হাতে নিয়ে তিনি জল ছপছপ করতে করতে ঘাটে উঠে এলেন। রূপেন্দ্রের মনে হল লোকটি ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। উনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। কাছাকাছি এসে লোকটি পদস্পর্শ করে ওঁকে প্রণাম জানিয়ে বললে, ঠাকুরমশাই, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম বলে মার্জনা চাইছি। কর্তার নির্দেশে আপনার কাছে একটি প্রশ্নের প্রত্যুত্তর জানতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন…
রূপেন্দ্র প্রতিনমস্কার করে বলেন, কর্তা বলতে?
—আজ্ঞে, ওই জলযানটা যিনি ভাড়া নিয়েছেন। আমার নিয়োগকর্তা—বঙ্গাধিপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের অধীনস্থ নায়েব কানুনগো—বর্ধমানভুক্তির ইজারাদার বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্ত! আমি তাঁরই গোমস্তামাত্ৰ।
[এইখানে বোধহয় বলে রাখা ভালো যে, ওই ‘বঙ্গাধিপতি’ শব্দটা একটা উপাধিমাত্র। আমাদের কাহিনীর কালে বাস্তবে বঙ্গাধিপতি সিরাজ-উদ্দৌলার দাদামশাই নবাব আলিবর্দি খাঁ।]
রূপেন্দ্র বলেন, আপনাদের কর্তা কী করে জানলেন যে, আমি এখানে বিশ্রাম করছি?
—আজ্ঞে, দূরবীনের সাহায্যে।
—বুঝলাম। কী তাঁর প্রশ্ন?
—মহাশয় কি বর্ধমান সোঞাই গাঁয়ের ধন্বন্তরি কবিরাজমশাই?
রূপেন্দ্র বললেন, আজ্ঞে হাঁ, আমার পৈত্রিক নিবাস সোঞাই গ্রাম এবং পেশায় আমি কবিরাজ বটে; তবে উপাধি ঐ যেটা বললেন, তার কোনও ভিত্তি নাই।
—তাহলে মহাশয়কে অনুগ্রহ করে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। কর্তামশাই আপনার সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।
হঠাৎ স্মরণ হল রূপেন্দ্রের। হ্যাঁ, নগেন দত্তের আমন্ত্রণে তিনি দত্তমশায়ের স্ত্রীর চিকিৎসা করতে বছর দেড়েক পূর্বে বর্ধমান শহরে গিয়েছিলেন বটে। রোগিণীকে পরীক্ষা করেছিলেন, ঔষধের ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চিকিৎসকের প্রাপ্য সম্মানমর্যাদা গ্রহণ করেননি–এতক্ষণে সব কথা মনে পড়ে গেল।
রূপেন্দ্র সম্মত হলেন। গোমস্তামশাই ওঁকে ডিঙিনৌকায় তুলে ওই অর্ণবপোতের দিকে নিয়ে চলেন।
একে একে সব কথা মনে পড়ছে। নগেন দত্ত টাকার কুমির। বর্ধমান মহারাজের পরেই গোটা বর্ধমানভুক্তিতে ধনিকশ্রেষ্ঠ। বয়স আড়াইকুড়ি কিন্তু শরীর মজবুত। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়স বিশ-বাইশ। মূর্ছারোগে ভুগছিলেন। স্থানীয় চিকিৎসকেরা বলেছেন রোগটার নাম: মৃগী।
কুমারী অবস্থায় কোনও উপসর্গ ছিল না। বিবাহের পর প্রথম ছয়মাসও উপসর্গ ছিল না। এখন ঘন ঘন মূর্ছা হয়। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, তাবিজ-কবচ, হাকিমী-কবিরাজীর হদ্দমুদ্দ করে নগেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠিয়ে ‘ধন্বন্তরি’কে পাকড়াও করে এনেছিলেন সোঞাই গ্রাম থেকে। রূপেন্দ্র প্রথামতো দ্বিতীয়া মহিলার উপস্থিতিতে রোগিণীকে পরীক্ষা করার পর নগেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন, কী বুঝলেন বলুন, কোবরেজমশাই। আমার স্ত্রীর ওই ভুতুড়ে অসুখ সারবে?
রূপেন্দ্র বলেছিলেন, সারবে। যদি আপনার সামর্থ্যে কুলায়।
স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ধনকুবের: মানে?
—আর সবাইকে চলে যেতে বলুন। কথাটা গোপন! জনান্তিকে বলতে চাই।
ঘর নির্জন করে গৃহস্বামী বললেন, এবার বলুন?
—আপনার স্ত্রীর অসুখটা দৈহিক নয়, মানসিক। রোগের মূল হেতু– যেহেতু তিনি আপনার কাছ থেকে যথাপ্রত্যাশিত স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছেন না।
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন নগেন দত্ত। বলেন, কী বলছেন আপনি? স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছে না! সে তো যা চায়, তাই পায়।
—না, পান না। নিশ্চয় জানেন, চিকিৎসকের কাছে কোন কিছু গোপন করতে নেই? এবার বলুন তো দত্তমশাই—আপনি কতদিন পূর্বে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেছেন? কবে আপনার স্ত্রীর মর্যাদা শেষবার মিটিয়েছেন?
নগেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠল। রুদ্ধস্বরে বললেন, আপনার স্পর্ধার তো একটা সীমা থাকবে, কোবরেজমশাই? কতদিন আগে আমি স্ত্রীকে নিয়ে এক শয্যায় শয়ন করেছি, এই অশ্লীল প্রশ্নটা করতে আপনার বাধল না?
—প্রশ্ন করতে আমার বাধেনি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন, উত্তর দিতেই না বাধছে আপনার? শুনুন, ক্ষুৎপিপাসা-নিদ্রার মতো এও এক জৈবিক বৃত্তি। শুধু পুরুষের নয়, স্ত্রীলোকেরও। আমি জানি না, আপনার বাগানবাড়ির আয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি এই বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেছেন। আমি পরীক্ষা করে দেখিনি, কিন্তু আমার আশঙ্কা আপনার স্ত্রী অক্ষতযোনি!
—চোপরাও বেয়াদপ!–গর্জন করে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দুলের মতো বার-কয়েক কক্ষমধ্যে পায়চারি করে ফিরে এসে ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যথেষ্ট হয়েছে! আমার স্ত্রীর চিকিৎসা আপনাকে আর করতে হবে না। কী বৈদ্যবিদায় দিতে হবে বলুন?
রূপেন্দ্রনাথও আসনত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। শান্ত স্বরে বলেছিলেন, আমি আপনার দেউড়ির বাইরে গিয়ে সড়কের উপর অপেক্ষা করছি। আমার জিনিসপত্র সব লোক দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিন।
নির্গমনদ্বারের দিকে রূপেন্দ্রনাথ চলতে শুরু করামাত্র নগেন্দ্রনাথ ছুটে আসেন। যেন সম্বিত ফিরে পান। কবিরাজমশায়ের দুটি হাত ধরে বলেন, আমার মাথার ঠিক ছিল না অন্যায় হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না…
রূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, না, আমি কিছু মনে করিনি। আপনি প্রচুর অর্থের মালিক শিক্ষাদীক্ষা বোধকরি কিছু জোটেনি। আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারবেন না, এ তো প্রত্যাশিত।
এত বড় অপমান ধনকুবেরকে ইতিপূর্বে কেউ করেনি। তবু তিনি সেটা গায়ে না মেখে বলেছিলেন, আমি আপনার হাত ধরে মার্জনা ভিক্ষা করছি ভেষগাচার্য! ঠিকই বলেছেন আপনি! শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ আমার হয়নি। বলুন, ক্ষমা করেছেন?
—করেছি!
দুজনেই উপবেশন করেছিলেন অতঃপর। নগেন্দ্রনাথ বলেন, এবার বলুন, কী চিকিৎসা করতে চান? ঔষধপত্রের ব্যবস্থা…
—চিকিৎসার প্রয়োজন তো আপনার স্ত্রীর নয়। আপনার। মদ্যপান রাতারাতি ত্যাগ করতে বলছি না, ধীরে ধীরে কমান। কিন্তু সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। সাত দিন ওই ওষুধই চলবে, গৃহাবরোধে পরিমিতি মেনে মদ্যপান। অষ্টম দিনে তাঁর কাছে গিয়ে বলতে হবে, এইমাত্র আমাকে যা বললেন।
—বুঝলাম না। কাকে কী বলতে হবে?
—বলবেন আপনার ধর্মপত্নীকে। যেকথা এখনি আমাকে বলেছেন: ‘আমি তোমার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি। বল, ক্ষমা করেছো।’
নগেন্দ্রনাথ নতনেত্রে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর জানতে চাইলেন, শুধুমাত্র এতেই ও ভালো হয়ে যাবে?
—আমার তাই ধারণা। বাগানবাড়ি, বাঈজী বা উপপত্নীকে যে আপনি একেবারে ত্যাগ করতে পারবেন এতটা আশা করি না। কিন্তু আপনার স্নেহ, প্রেম, সোহাগ না পেলে কোনও ওষুধে ওঁর এই মূর্ছারোগ সারবে না।
নগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমি চেষ্টা করে দেখব। ক্ষমা যখন করেছেন এবার বলুন, কী বৈদ্যবিদায় দেব?
—আজ নয়, দত্তমশাই। আমাকে বৈদ্যবিদায় দেবার অধিকার আপনাকে অর্জন করতে হবে। আত্মসংযমের মাধ্যমে। আমি যে ব্যবস্থা দিয়ে গেলাম তা যদি যথাযথ পালন করতে পারেন, আপনার ধর্মপত্নীকে সুস্থ করে নবজীবন দান করতে পারেন, তাঁকে সন্তানবতী করে তুলতে পারেন, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমি বৈদ্যবিদায় নিয়ে যাব!
—কিন্তু বৈদ্যের কাছে পরামর্শ নিয়ে বৈদ্যবিদায় না দিলে যে নরকদর্শন করতে হয়।
—একথা আয়ুর্বেদে কোথায় লেখা আছে তা আমার জানা নেই; কিন্তু জনমানসে এমন একটা সংস্কার যে আছে, তা জানি। বেশ তো, অন্তত সেই আতঙ্কেই আপনি যদি আপনার জীবনযাত্রার ছকটা পালটাতে পারেন, তাহলেই আমি খুশি!
সেই ওঁদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।
৫
ডিঙি নৌকাটা জলযানের গায়ে এসে ভিড়ল।
গঙ্গার জলতল থেকে অর্ণবপোতের পাটাতনের সমতল এক-মানুষ উঁচুতে। দড়ির মই বেয়ে জাহাজে উঠতে হল। রূপেন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হল জলযানের অভ্যর্থনাকক্ষে। উপরের ডেক-এ। নগেন দত্ত বসেছিলেন একটি আরামকেদারায়। সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন আগন্তুককে। নগেনের বয়স রূপেন্দ্রের দ্বিগুণ; কিন্তু এটাই ছিল সেকালের শিষ্টাচার। সোৎসাহে দত্তজা বলে ওঠেন, আমার দূরবীন তাহলে মিছে বলেনি! আপনি যথার্থই ধন্বন্তরি কোবরেজ মশাই! তা সারাটা সকাল গঙ্গাতীরে অমন নিশ্চুপ বসেছিলেন কেন? স্নানাহার তো কিছুই হয়নি আপনার। চেহারাটাই বা এমন বাউণ্ডুলের মতো হল কেন?
রূপেন্দ্র প্রতিনমস্কার করে বললেন, আমার রোগিণী কোথায়?
—কোথায় আবার? বর্ধমানে, তাঁর অন্দরমহলে। ‘পথি নারী বিবর্জিতা’ শোলোকটা নিশ্চয় আপনার জানা আছে, কোবরেজমশাই। আপনিও তো দেখছি ধর্মপত্নীকে বাড়িতে রেখে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে এসেছিলেন।
রূপেন্দ্র ম্লান হাসলেন। নিজ ধর্মপত্নীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, এখন শারীরিক কেমন আছেন দত্তগৃহিণী?
—ভালো, খুব ভাল। অতিশয় ভাল। মূর্ছা আর হয় না। এখন তো তিনি শুধুমাত্র আমার স্ত্রী নন, মাসখানেক হল আমার খোকনের মা! আমার প্রতি তাঁর নজরই পড়ে না।
এবার তৃপ্তির হাসি হাসলেন রূপেন্দ্র। ঘর ফাঁকা হলে নগেন্দ্র স্বীকার করেন, মদ্যপান একেবারে ত্যাগ করতে পারিনি, বুয়েছেন না? তবে পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছি। উপপত্নীটিকেও তাড়িয়ে দিতে মন সরেনি। বেচারি যাবে কোথায়? তবে আপনার বিধান আমি যে মেনে নিয়েছি, সেকথা ইতিপূর্বেই বলেচি। এবার বলুন, আপনাকে মুলতুবি বৈদ্যবিদায়টা দিয়ে ঋণমুক্ত হতে পারি কি না?
সরাসরি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রূপেন্দ্র বলেন, এই বিশাল অর্ণবপোত নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সিংহল, না কি চম্পানগর?
—বলব, সব বলব। তার পূর্বে আপনার স্নানাহার হোক।
রূপেন্দ্রর মনে পড়ে গেল মাহেশে ওরা বোধহয় এতক্ষণে স্থিরনিশ্চয় বুঝেছে যে, রূপেন্দ্র নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করেছেন। ফলে শববাহীরা তাঁর অনুপস্থিতিটাকে মেনে নিয়ে এতক্ষণে শ্মশানের দিকে যাত্রা করেছে। এমন অবস্থায় স্নানাহারে রুচি হল না ওঁর। বললেন, আমার একটি ব্রত আছে আজ, দত্তমশাই। সমস্ত দিন উপবাস। সন্ধ্যার পর হয়তো কিছু ফলাহার করব। আপনি সব কথা খুলে বলুন। এ নৌকায় কারা আছেন, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন?
নগেন দত্ত ধীরে ধীরে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। অর্ণবপোতটি চলেছে দক্ষিণাভিমুখে। ফ্রেডরিক নগর থেকে পানিহাটি, সোদপুর, পীরের থান, উতোরপাড়া, ঘুসুড়ি হয়ে কালীঘাট তারপর আরও দক্ষিণে হীরকবন্দর, সাগরদ্বীপ হয়ে কপিল মুনির আশ্রম। সেখানে ওঁরা গৈরিকবর্ণা গঙ্গাকে পিছনে ফেলে আশ্রয় নেবেন নীলাম্বুরাশির কোলে : বঙ্গোপসাগর। যাবেন দক্ষিণ-পশ্চিমে। বুড়িবালামের মোহনায় বালেশ্বর অতিক্রম করে মহানদীর ব-দ্বীপে। তারপর মহানদীর ‘বড়গঙ্গা’ ধরে কটক। সেখান থেকে পদব্রজে একাম্রকানন-সাক্ষীগোপাল-কমলপুর- আঠারোনালা হয়ে নীলাচলের শ্রীক্ষেত্র। ওঁদের গন্তব্যস্থল সেই: আদি অকৃত্রিম-সর্বতীর্থসার : পুরুষোত্তমক্ষেত্র।
রূপেন্দ্র জানতে চাইলেন, সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়েই যখন যাচ্ছেন তখন আংশিক তীর্থপথ পদব্রজে যেতে হচ্ছে কেন? কেন সরাসরি পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই জাহাজ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না?
জবাবে দত্তজা বুঝিয়ে বললেন, পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা পুরী সমুদ্রতীরে বটে, কিন্তু সেখানে কোনও বন্দর নেই। বেলাভূমি থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ সমুদ্রের ভিতরে ছাড়া জাহাজ নোঙর করা যায় না। জাহাজের তলদেশ আটকে যায়। এজন্য তাম্রলিপ্তি বা কটকের বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো ছাড়া উপায় নেই। যাত্রীরা বাকি পথ যখন পদব্রজে যাবে ও আসবে ততক্ষণ বন্দরে জাহাজকে প্রত্যাবর্তন যাত্রার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রঙ ফেরাতে হবে। টুকটাক মেরামত করতে হবে। বহু পূর্বযুগে বাঙলার বাণিজ্য যখন মধ্যগগনে, তখন এভাবেই গৌড়বাসী শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যেত। পরে এ-পথ পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে বন্ধ হয়ে যায়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য কাটোয়া-শান্তিপুর থেকে যাত্রা শুরু করে গঙ্গাঘাট থেকে ভাগীরথী ত্যাগ করে মেদিনীপুরের অরণ্যপথে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন।
রূপেন্দ্র বললেন, জানি। একসময়ে আমার গুরুদেব শ্রীমৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীচৈতন্যদেবের পদরেখা ধরে জগন্নাথধামে পদব্রজে যাবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমার গুরুদেবের পিতৃদেব রুদ্রদেব তর্কবাগীশও শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্নরেখা ধরেই শ্রীক্ষেত্রে তীর্থদর্শনে যান। তাঁর শ্বশুরমশাইও যান এবং স্বপ্নাদেশ পান যে, তাঁর কন্যার গর্ভে এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুত্রের জন্ম হবে। বস্তুত, স্বয়ং জগন্নাথ স্বপ্নাদেশে আমার গুরুদেবের নামকরণ করেছিলেন: জগন্নাথ। সে যাই হোক, গুরুদেবের নির্দেশে সে-সময় আমি বিভিন্ন গ্রন্থ বিচার করে শ্রীচৈতন্যদেবের পথ পরিক্রমার একটি সম্ভাব্য মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলাম।
নগেন দত্ত বলেন, এ তো বড় আশ্চর্যের কথা! ঠিক ওই কাজটিই যে বর্তমানে করানো হচ্ছে জগৎশেঠের অর্থানুকূল্যে। রাজা জগৎ শেঠ সেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পদচিহ্নলাঞ্ছিত তীর্থপথটি সংস্কার করাতে চান। আপনি এ-বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন?
রূপেন্দ্র বলেন, এ-বিষয়ে আমার আদৌ কোনও উৎসাহ নেই। শ্রীচৈতন্যদেব যে-পথে জগন্নাথধামে গিয়েছিলেন সেই পথরেখা ধরে একটি রাজপথ নির্মিত হলে আমি খুশিই হব; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হব দেখলে যে, ধনকুবের জগৎশেঠ উৎসাহী হয়েছেন অন্য একটি সামাজিক পথের সংস্কার করতে যে-পথে যুগাবতার যেতে পারেননি; কিন্তু যে-পথে যেতে পারলে খুশি হতেন।
নগেন দত্ত বলেন, বুঝলাম না।
—স্বাভাবিক। এ-বক্তব্যের গূঢ়ার্থ সহজে বোঝা যায় না দত্ত-মশাই। তবে আপনি যে- পথের সন্ধান করছেন, তার ইঙ্গিত পাবেন কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোঁসাই, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এবং মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি পুঁথিতে সন্ধান করলে। মোটামুটি আমার স্মৃতিপটেও আছে তাম্রলিপ্তি থেকে মেদিনীপুর অতিক্রম করে উনি নারায়ণগড়, দন্তপুর, জলেশ্বর, রেমুণা হয়ে ভদ্রক জনপদে এসেছিলেন। তারপর যাজপুর-পুরুষোত্তমপুর- চৌদ্ধার হয়ে শহর কটক। বাকি পথ তো আপনারাই পরিক্রমা করবেন: একাম্রকানন, সাক্ষীগোপাল, আঠারোনালা হয়ে শ্রীক্ষেত্র।
নগেন দত্ত ওঁর হাত দুটি ধরে বলেন, পথের বর্ণনা তো দেখছি আপনার মুখস্থ। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে যাবেন? আমাদের জলযানে একশো বাইশজন নরনারী—অধিকাংশ বর্ধমানভুক্তির। সঙ্গে কোনও কবিরাজ নেই। আপনার যদি উপস্থিত কোনও আরব্ধ কাজ না থাকে…
রূপেন্দ্র বললেন, কিন্তু আমি যে বর্তমানে কপর্দকহীন, একবস্ত্রে নগ্নপদে গঙ্গাতীরে বিশ্রাম করছিলাম, এ তো আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন!
নগেন দত্ত বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আজ্ঞে না কবিরাজমশাই! আপনি আদৌ কপর্দকহীন নন। আমাকে ঋণমুক্ত হবার অনুমতি দিলে আমি স্বয়ং এ-দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। যাত্রীদলের সকলে আপনার প্রতি আমৃত্যু কৃতার্থ হয়ে থাকবে। যেহেতু আমাদের দলে একজনও চিকিৎসক নেই। ঘটনাচক্রে আপনাদের সোঞাই গ্রামের একজন বৃদ্ধও চলেছেন আমাদের সঙ্গে। গ্রাম সম্পর্কে আপনার খুড়ামশাই—শ্রীদুর্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
যেন প্রতিবর্তী প্রেরণা। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ গাঙ্গুলীমশায়ের চতুর্থপক্ষটির কথা—রূপেন্দ্রের বাল্যসহচরী মৃন্ময়ী—মীনু। রূপেন্দ্রের চেয়ে নয় বছরের ছোট, প্রতিবেশী পীতাম্বর মুখুজ্জের কন্যা। গুরুগৃহ থেকে বাৎসরিক একমাসের জন্য প্রত্যাবর্তনের নিয়ম ছিল জগন্নাথ পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে—শারদীয় অকালবোধনের সময়। নাহলে পিতামাতা, পরিবার থেকে ছাত্র মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—এই ছিল ত্রিবেণীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের অভিমত। তাই রূপেন্দ্রও বছরে একবার করে সোঞাই গ্রামে ফিরে আসতেন। বছরে বছরে দেখেছেন মীনুকে বালিকা থেকে কিশোরীতে রূপান্তরিতা হতে।
“পহিলে বদরিসম, পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে অনঙ্গ আবরিল অঙ্গ”। দুজনের অন্তরের অস্তস্তলে যে রঙ ধরেছিল সেটা উপলব্ধি করা গেল বড় বিলম্বে। উপাধি নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে রূপেন্দ্র দেখেছিলেন নয় বছরের অনুজা মীনু ইতিমধ্যে হয়ে গেছে ওঁর খুড়িমা! রূপেন্দ্ৰ যখন সস্ত্রীক তীর্থ পরিক্রমায় যাত্রা করেন, তখন দুর্গা গাঙ্গুলীর ওই চতুর্থপক্ষের পত্নীটি ছিলেন সন্তানসম্ভবা।
সে-কথাই মনে পড়ে গেল। তাই বললেন, গাঙ্গুলীখুড়ো তীর্থে চলেছেন? এ তো বড় অদ্ভুত সংবাদ। তিনি তো তাঁর তেজারতি কারবার নিয়েই মেতে ছিলেন তিনকুড়ি বছর—কোনদিন গাঁয়ের বাইরে যাননি।
নগেন দত্ত বলেন, জানি। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। সেই আঘাতেই বৃদ্ধ কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন। ডাকব তাঁকে? কথা বলবেন?
রূপেন্দ্র শিউরে উঠেছিলেন মৃন্ময়ীর মৃত্যুসংবাদে। কোনক্রমে বললেন, না! না! না!
নগেন্দ্র সে-আর্তনাদে রীতিমত অবাক হয়ে যান। তিনি তো জানেন না, ওই যুবকটি একই দিনে পেল দু-দুটি নারীর মৃত্যুসংবাদ, যারা-দুজনই ওঁকে প্রাণাধিক ভালবেসেছিল!
৬
রূপেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হয়েছেন। এই তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে জগন্নাথক্ষেত্রে যাবেন তিনি। হেতুটা যে কী, তা আন্দাজ করতে পারেননি নগেন্দ্র। এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন মানসিকভাবে রূপেন্দ্র পীড়িত। কী একটা অন্তর্লীন বেদনা গোপনে বহে বেড়াচ্ছেন। সে এমন একটি আঘাত যার ক্ষতচিহ্ন নীরবে নিভৃতে লুকিয়ে রাখতে হয়। সর্বদাই আত্মমগ্ন হয়ে বসে থাকেন। পূর্বের মতো প্রাত্যহিক পূজা-অর্চনাদি করেন না তিনি—কিন্তু ধ্যান করেন। কথাবার্তা বড় একটা বলেন না কারও সঙ্গে। কখনও কখনও লক্ষ্য করেছেন নগেন্দ্র—ঐ নিঃসঙ্গ নায়কটি মধ্যরাত্রে একা বসে আছেন পদ্মাসনে নৌকার গলুইয়ে। নগেন দত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। হেতুটা জানতে চাননি। ব্রাহ্মণকে আত্মস্থ থাকতে দিয়েছেন। এমনকি তিনি প্রথম দিন যেভাবে দুর্গাচরণের সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেন, তাতে সংবাদটা তিনি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছেও গোপন রেখেছেন। কবিরাজমশায়ের যাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জীবনযাপনের উপকরণ লোক পাঠিয়ে সংগ্রহ করেছেন ধুতি, পিরাণ, পাদুকা ইত্যাদি।
রূপেন্দ্র জগন্নাথক্ষেত্রে যেতে স্বীকৃত হলেন এ-কারণে নয় যে, পত্নী-বিয়োগে তীর্থ তাঁকে আকর্ষণ করছিল; এ-কারণে নয় যে, এই নৌকার শতাধিক নর-নারীর অসুখ-বিসুখে তিনি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করার নেই। তিনি মনস্থির করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন হেতুতে :
তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন। কুসুমমঞ্জরী তাঁকে মুক্তি দিয়ে গেছে। মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁকে পথের ইঙ্গিতও দিয়ে গেছে। যুগাবতার এসেছেন, এখনও প্রকট হননি, এই বিশ্বাসে আজীবন পরশপাথর খুঁজে মরার কোনও অর্থ হয় না। যেটুকু ওঁর ক্ষমতার ভিতর সেটুকুই করবেন। ‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে’। সমাজের দু-দুটি হিমালয়ান্তিক ত্রুটি সম্বন্ধে ব্যথিত হয়েছেন উনি। কিন্তু হিন্দু-সমাজের ওই বিরাট অবহেলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—যাদের জল-অচল, অচ্ছুৎ করে সরিয়ে রেখেছে কূপমণ্ডুক ব্রাহ্মণ্যসমাজ, তাদের নিয়ে আন্দোলন একা-হাতে করা যায় না। অপর ক্ষতটার নিরাময়ের চেষ্টা তিনি নিজেই করতে পারেন। অন্তত শুরু করতে পারেন। নির্যাতিতা নারীসমাজকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মৈত্রেয়ী গার্গীর যুগ চলে গেছে। বৈদিকযুগের স্ত্রীশিক্ষার দ্বিধারা—ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোদ্বাহা অবলুপ্ত হয়ে গেছে বহু বহু যুগ অতীতে। বস্তুত, আর্যাবর্তে মুসলমান আগমনের পর থেকেই। তার পূর্বযুগে বৈদিক ও উপনিষদের যুগে পুরুষের মতো স্ত্রীলোকদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ছিল। তাঁদের উপনয়ন হতো, তাঁদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো। যাঁরা আজীবন দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় নিরত থাকার সঙ্কল্প করতেন, তাঁদের বলা হতো ‘ব্রহ্মবাদিনী’। তাঁদের পক্ষে আশ্রমিক, চিরকুমারী বা বিগতভর্তা হবার কোনও আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল না। অনেকেই সীমন্তিনী। সংসারধর্ম পালনের অবকাশে তাঁরা যোগসাধনা করতে পারতেন। রাজবৈভব যেমন রাজর্ষি জনকের সাধনমার্গে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি, ঠিক তেমনি কাশীরাজ-মহিষী মদালসাও স্বামী-সংসার-পুত্র-কলত্ৰ-দাসদাসী পরিবেষ্টিতা হয়েও রাজান্তঃপুরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী হতে পেরেছিলেন। পঙ্কসরোবরে ভাসমান রাজহংসীর মতো মহারানী মদালসা রাজবৈভবের মধ্যেও ছিলেন নিষ্কলঙ্ক। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। সীমন্তিনী হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মচারিণী!
এছাড়া ছিল আর এক শ্রেণীর ছাত্রী। তারা ঈশ্বরতত্ত্বের সন্ধানী নয়। তাদের অক্ষর- পরিচয় হতো, কিছুটা ব্যাকরণ, এবং অলঙ্কার, নানা শ্রেণীর কাব্য। সচরাচর প্রাগ্বিবাহ কালেই বিদ্যাচর্চার আয়োজন হতো বটে, তবু প্রথম যুগে বিবাহিতা ও বিগতভর্তা অবস্থাতেও কেউ কেউ এ-জাতীয় বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন। তাঁদের বলা হতো; ‘সদ্যোদ্বাহা”!
এই দু-শ্রেণীর বিদ্যোৎসাহিনী মহিলার দলই প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো নিঃশেষে অবলুপ্ত।
রূপেন্দ্র স্থির করলেন: সেই পরিবেশটি উনি ফিরিয়ে আনবেন। ধর্মপত্নীর কাছে উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কুসুমমঞ্জরীকে ছিনিয়ে নিয়েছেন মহাকাল, কূপমণ্ডুক সমাজপতিদের সাহায্য পেয়ে। তাই রূপেন্দ্র স্থির করলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণ করবেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সোঞাই প্রত্যাবর্তন করে তিনি শুধুমাত্র স্ত্রীলোকদের জন্য একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। অনেক অনেক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তিনি চিকিৎসক হিসাবে অপরিসীম শ্রদ্ধার মানুষ। ‘একবগ্গা ঠাকুর’কেঁ সবাই ভালবাসে। জমিদার ভাদুড়ীমশাই ওঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বিদ্যায়তনটি শুধুমাত্র বালিকাদের জন্য হবে না, যুবতী এবং বিবাহিতা, বিধবাদের জন্যও! বুদ্ধিমান রূপেন্দ্রনাথ বুঝেছেন, ওঁর এই প্রচেষ্টায় মুষ্টিমেয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গ্রামবাসী গোপনে সহানুভূতি জানালেও তাঁকে কূপমণ্ডুক স্মাতপণ্ডিতদের করতলগত বিরাট সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। তারা যুক্তি বোঝে না, নিজেদের মঙ্গল বোঝে না–সমাজের উন্নতি বোঝে না বোঝে অর্কফলার আন্দোলন, বোঝে শাস্ত্রবাক্য: ‘তট-তট-তট-তোটয়’!
তাই উনি স্বীকৃত হয়েছেন এই তীর্থযাত্রীদলের সহযাত্রীরূপে জগন্নাথধামে যেতে। ওঁর লক্ষ্যস্থল পুরীমন্দিরের সেই ত্রিমূর্তি নয়, সমুদ্রতীরে গোবর্ধন মঠের মঠাধীশ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য। শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য দশনামী সম্প্রদায়কে একসূত্রে আবদ্ধ করে ভারতবর্ষের চারপ্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। বহুধারায় বিচ্ছিন্ন হিন্দুধর্মকে দশনামী সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করার সেই প্রথম প্রয়াস :
দ্বারকাশ্রমে সামবেদাশ্রয়ী সারদামঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: পশ্চিমখণ্ড: সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতানা এবং কাথিয়াবাড়
বদরীকাশ্রমে অথর্ববেদাশ্রয়ী যোশীমঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: উত্তরখণ্ড : কুরু, পাঞ্চাল, পঞ্জাব, কাশ্মীর, কম্বোজ এবং গঙ্গা-যমুনার অববাহিকার মধ্যবর্তী আর্যাবর্তের ভূভাগ।
রামেশ্বরমাশ্রমে যজুর্বেদাশ্রয়ী শৃঙ্গেরীমঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: দক্ষিণখণ্ড : অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র।
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ঋকবেদাশ্রয়ী গোবর্ধন মঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: পূর্বখণ্ড : অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও পূর্বাঞ্চল।
ভেষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য গোবর্ধন-মঠাধ্যক্ষ পূর্বাঞ্চলের শঙ্করাচার্য। আদি শঙ্করাচার্য বিধান দিয়ে গেছেন এই চার ধামের চার মঠাধ্যক্ষ সমস্ত ভারতবর্ষে অতঃপর হবেন হিন্দুধর্মের রক্ষক ও অভিভাবক। ফলে অন্তত পূর্বাঞ্চলে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে হিন্দুসমাজের কাছে ‘নিদান’ হাঁকার অধিকার গোবর্ধনমঠের শঙ্করাচার্যের। তিনি যদি রূপেন্দ্রনাথকে ভূর্জপত্রে এক স্বীকৃতিপত্র লিখে দেন যে, হিন্দুধর্মে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে কোনও বিধিনিষেধ নাই তবে সেই সনদটিই হবে রূপেন্দ্রনাথের অধিকারপত্র। কূপমণ্ডুক সমাজপতি- জোঁকের মুখে ঐ সনদটি হবে লবণের মতো। গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি নিঃসংশয় যে, ভূম্যধিকারী আধুনিকমনা ভাদুড়ীমশাই ওঁকে সমর্থন করবেন। এই বিদ্যায়তনটি হবে স্ত্রীশিক্ষাসদন। শুধু বালিকা নয়, কিশোরী, যুবতী, বিবাহিতা, বিগতভর্তার দলও এসে অনায়াসে ভর্তি হতে পারবে তাঁর স্ত্রীশিক্ষাসদনে। তারা শিখবে প্রাচীন বাংলা হরফ, দেবনাগরী হরফ; পড়বে কৃত্তিবাস থেকে কালিদাস। কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ–না, দর্শন আবশ্যিক পাঠ্য নয়, কিন্তু অঙ্ক, সুদকষা, হিসাবরাখা, এবং সন্তান পালনের আদিপাঠ হবে আবশ্যিক। সোঞাই গ্রামে ওই জয়ধ্বজাটি প্রোথিত করে রূপেন্দ্র যাবেন দিগবিজয়ে। আদি শঙ্করাচার্য করেছিলেন ভারতবিজয়, উনি করবেন বঙ্গবিজয়! প্রথমে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে। নদীয়ারাজ ওঁর পৃষ্ঠপোষক। জনশ্রুতি তিনি প্রাচীনপন্থী, কিন্তু নিঃসন্দেহে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান। রূপেন্দ্র নিশ্চয় পারবেন তাঁকে স্বমতে আনতে। নিশ্চয়, তিনি গোয়াড়িতে, শান্তিপুরে, উলায়, নবদ্বীপধামে স্ত্রীশিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠা করবেন। তারপর বর্ধমানরাজ। উত্তরে নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায় (যাঁর দেহাবসানে রানী ভবানী পাঁচ বছরের ভিতরেই হবেন নাটোরের শাসনকর্ত্রী) তারপর মুর্শিদাবাদে গিয়ে ধরবেন জগৎশেঠকে
রূপেন্দ্রের মনোগত ইচ্ছা গোবর্ধনমঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কাছ থেকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক অনুমতিপত্রটি লাভ করার পরে তিনি তাঁর কাছে হিন্দুসমাজের আর একটি মারাত্মক কুপ্রথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন: সতীদাহ। এই নৃশংস লোকাচার তো মুসলমান সমাজে নেই, খ্রিস্টানদের ভিতর নেই। তাদের সমাজে তো বিগতভর্তার দল সসম্মানে টিকে আছে। সমাজের কাঠামো তো কই ভেঙে পড়েনি। তাহলে হিন্দুসমাজেই বা ওই নির্দয় প্রথাটিকে বাঁচিয়ে রাখার কী অর্থ? বৈদিক শাস্ত্রে তো নয়ই, এমনকি পৌরাণিক যুগেও সতীদাহের প্রসঙ্গ সামান্যই। সম্ভবত সেগুলি পরবর্তী যুগের কূপমণ্ডুকেরা সুকৌশলে পুঁথি অনুলিপিকালে যোগ করেছে। তাই প্রামাণিক কোনও শাস্ত্র এ-নির্দেশ দেয়নি যে, স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় তুলে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারতে হবে! এ-বিষয়ে রূপেন্দ্রের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এই কুপ্রথাটি রদ করার বিষয়েও তিনি আগ্রহী। গোবর্ধনমঠের শঙ্করাচার্য যদি উৎসাহ দেখান, তাহলে তিনি ওই প্রস্তাব নিয়ে ভারত-পরিক্রমা করবেন। চার মঠের শঙ্করাচার্য- চতুষ্টয়ের যৌথ সনদ নিয়ে দিল্লীশ্বরের কাছে দরবার করবেন। প্রয়োজনে ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে।
নগেন দত্ত এসব কিছু অনুমান করেননি। রূপেন্দ্রও তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনও আলোচনা করেননি। নগেন দত্ত ধনী, কিন্তু এসব সামাজিক কুসংস্কার নির্মূল করার বিষয়ে তত্ত্বকথা আলোচনা করার মতো শিক্ষা তার নেই।
দুর্গা গাঙ্গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে; কিন্তু কী-জানি-কেন তিনি রূপেন্দ্রকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। সামান্য কুশল প্রশ্ন করেই অন্তরালে সরে গেছেন। রূপেন্দ্রর মনে হল, তিনি ওঁকে দেখে খুশি হতে পারেননি। দুর্গা যেন কী এক অপরাধবোধে ভুগছেন। কুসুমমঞ্জরীর প্রশ্ন আদৌ উত্থাপন করেননি। রূপেন্দ্র খুড়িমার প্রসঙ্গ তোলার উপক্রম করতেই দুর্গা গাঙ্গুলি বললেন, সে তো ভাগ্যবতী রূপেন–আমাকে ফেলে রেখে সতীলক্ষ্মী ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে চলে গেল। আমারই ভবিতব্য—
বলেই পাশ কাটালেন।
মীনুর কথা মনে পড়ে। মীনু আর ওঁর পিসতুতো বোন কাত্যায়নী সমবয়সী, বান্ধবী। সেই সূত্রে বালিকা বয়স থেকেই পীতু মুখুজ্জের ওই মেয়েটি—মীনু—এ-বাড়ি আসতো। দিনরাত রূপেন্দ্রের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত। রুপোদার হাত ধরে রথের মেলায়, গাজনের সঙ দেখতে বা পীরপুরে মহরমের তাজিয়া দেখতে গেছে। ঘুমিয়ে পড়লে কোলে করে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। তখন মীনুর বয়স-পাঁচ-ছয়, তাহলে তার রুপোদার কত? চোদ্দ-পনের
তারপর মীনু যখন মৃন্ময়ী, তখন? মনে পড়ছে আর একদিনের কথা। মীনু তখন একাদশবর্ষীয়া কিশোরী। রঙ-দোলের দিন। মীনু এসেছিল তার রুপোদার বাড়ি কাতুকে রঙ দিতে। কাতু কোথায় বুঝি লুকিয়ে বসেছিল ঘাপটি মেরে। মীনু আনাচে-কানাচে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল রুপোদার। রুপোদার হাতে একটা আবীরের পুঁটলি। দোর আগলে, সে বলেছিল, এবার?
বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠেছিল কিশোরী মেয়েটির। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে, কেউ কোথাও নেই! কী সর্বনাশ! এখন যদি ওই তালঢ্যাঙা ছেলেটা ওকে বুকে টেনে নেয়! ওর মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে…
দুরন্ত লজ্জায় থমকে থেমে দু-হাতে মুখ ঢেকে মীনু বলে উঠেছিল, নৃ-না!
রূপেন্দ্রনাথও থমকে থেমে গিয়েছিল। ওর আতঙ্কতাড়িত কচি মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। অবাক বিস্ময়ে জানতে চেয়েছিল, কী ব্যাপার রে মীনু? কাকে এত ভয়! আমাকে না আবীরকে?
মুখ থেকে হাত সরায়নি। ও শুধু পুনরুক্তি করেছিল : নৃ-না!
রূপেন্দ্রনাথ বলেছিল, দূর বোকা! আবীরের দাগ কি চিরকাল মুখে থাকে? ও তো ধুলেই উঠে যায়।
ছেড়ে দিয়েছিল মীনুকে।
আজ বুঝতে পারেন, মৃন্ময়ী হতাশ হয়েছিল তাতে। বোকা মেয়েটা আশা করেছিল—ঐ তালঢ্যাঙা ছেলেটা ওর আপত্তিতে কান দেবে না। জোর করে বুকে টেনে নিয়ে ওর মুখে, গলায়, বুকে… সেদিন তা বুঝতে পারেননি রূপেন্দ্র।
একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের–সেই বাল্যসহচরী মৃন্ময়ী–মীনু—আজ অমর্ত্যলোকের বাসিন্দা।
৭
অর্ণবপোত ইতিমধ্যে দক্ষিণদিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ঘুসুড়ি, হাওড়া, কালীঘাট, উলুবেড়িয়া অতিক্রম করে রূপনারায়ণের মিলনস্থল। জাহাজের কর্ণধার এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। নদীপথে জাহাজ চালানোতে তার কোনও ভূমিকা নেই। জাহাজের দায়িত্বে আছে ‘গাঙ- সারেঙ’। নদীপথে সব কিছু তার নখদর্পণে। সে জানে কোন্ দিকে, কোথায় চড়া পড়েছে, কোথায় ডুবো-চর, আর কোন্ দিকে বড়গঙ্গার গভীরতর খাদ। তার দুই সহকারী জলযানের দু’পাশে বসে ক্রমাগত জল মেপে যাচ্ছে : একবাম মে-লে-না; দু’বাম মে-লে-না!
রাতে জাহাজ চলে না। তার দক্ষিণাভিমুখে ভেসে-চলা শুধু দিবাভাগে। হাওয়া এখন দক্ষিণ দিক থেকে। ফলে পাল অকেজো। জোয়ারের সময় জাহাজ নোঙর করে রাখতে হয়। শুধুমাত্র ভাঁটার অমোঘ আকর্ষণে জাহাজ এগিয়ে চলে দক্ষিণাভিমুখে কপিলমুনির আশ্রমের দিকে।
জাহাজ যখন নোঙর করা থাকে, তখন শুরু হয় সমবেত হরিসংকীর্তন। যাত্রীদলের বৃকোদরভাগ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। খোল-করতাল সঙ্গে নিয়েই এসেছে তারা। নগেন দত্ত রূপেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন প্রতিদিন কিছু কিছু করে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে, যাতে যে-পথে ওরা যাচ্ছে বা যাবে, তার সম্বন্ধে কিছুটা পূর্ব-পরিচয় হয়ে থাকে। রূপেন্দ্রনাথ কথক নন, তবু তিনি যখন দেখলেন তাঁর শ্রোতার দল অত্যন্ত আগ্রহে তাঁকে বারে বারে অনুরোধ করছে, তখন তিনি স্বীকৃত হলেন। সূর্যাস্তের পর জাহাজ চালানো বিপদজনক। তাই সন্ধ্যায় গাঙ-সারেঙ লোহার নোঙর নামিয়ে দিত। জলযান স্থির হত। অল্প অল্প দুলত মা-গঙ্গার দোলুনিতে। রোজ ওরা দল বেঁধে এসে বসতো সন্ধ্যার সময়। রূপেন্দ্রনাথ বর্ণনা করতেন শচীনন্দনের প্রথম নীলাচল অভিযানের কাহিনী :
তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁর কয়েকজন প্রিয় শিষ্যসহ শান্তিপুর থেকে পুরুষোত্তম- ক্ষেত্রের তীর্থপথে যাত্রা করলেন। আচার্য অদ্বৈত শহরপ্রান্ত পর্যন্ত এসে প্রাণের ধন নিমাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। সাশ্রুলোচন শান্তিপুরবাসীদেরও ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।
সঙ্গে চললেন কয়েকজন মাত্র শিষ্য। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখেছেন :
“নিতানন্দ গোঁসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ।।”
ওই সঙ্গে যোগ দিতে হবে শ্রীগোবিন্দ দাস কর্মকারের নাম। কারণ নিজ কড়চায় গোবিন্দদাস লিখেছেন : “প্রভুর সহিত যাই নাচিতে নাচিতে।”
ভাগীরথীর পূর্ব-উপকূল ধরে দক্ষিণাভিমুখে চললেন ওঁরা। কোনও পাথেয় সঙ্গে নেবার অনুমতি ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি শুধু সন্ন্যাসদণ্ড, করঙ্গ, কৌপীন আর বহির্বাস। জীবনধারণের আর কী উপকরণ চাই? আহার?
“প্রভু যারে যে দিনে বা না লিখেন আহার।
রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার।।”
৮
চরিতকারেরা শান্তিপুর এবং আঁটিসারার মধ্যবর্তী স্থানগুলির কোনও উল্লেখ করেননি।
এইখানে কিছু ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এ পথের সন্ধান কোথা থেকে কী করে পেলাম। সেটি পেয়েছি বর্তমান লেখকের অনুজপ্রতিম ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দের গ্রন্থে। অচ্যুতানন্দ অনুমান করেছেন ভাগীরথীর পূর্ব তীর দিয়ে “ত্রিবেণী, নৈহাটি, খড়দহ, পানিহাটি, চিত্রপুর, কালীঘাট, চূড়াঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রসা গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাহীনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর পার হয়ে প্রভু বারুইপুর গ্রামের কাছে আঁটিসারায় এসে উপস্থিত হলেন।”
চৈতন্যভাগবত এসব স্থানের উল্লেখ করেননি। সংক্ষেপে বললেন, “উত্তরিলা আসি আঁটিসারা নগরেতে।”
আঁটিসারা গঙ্গাতীরের অতি প্রাচীন একটি গ্রাম। বর্তমান নাম আটঘরা। বারুইপুরের পুরনো বাজারের ভিতর দিয়ে দেড়-দু’মাইল এগিয়ে গেলে লুপ্তস্রোতা গাঙ্গেয় মরা খাত এখনো দেখা যায়। তার পলিমাটির স্তরের নিচে এখানে প্রাচীন রোমক মুদ্রা, মৌর্য ও কুষাণযুগের তৈজস ও পোড়ামাটির যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই আঁটিসারা গ্রামে প্রভু মিলিত হয়েছিলেন তাঁর পরমভক্ত অনন্তরাম পণ্ডিতের সঙ্গে। মিলনস্থলে একটি চৈতন্যমন্দির আজও বর্তমান। এখনও বৈশাখ মাসে সেই অনন্তরামের শ্রীপাটে পক্ষকালব্যাপী মেলা হয়, অষ্টপ্রহর চলে নামসঙ্কীর্তন।
শ্রীচৈতন্য অতঃপর গঙ্গার তীর ধরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে চলেছেন। পশ্চিম পাড় নয়, পূর্ব পাড়। চৈতন্যের সমকালীন গৌড়াধিপতি নবাব হুসেন শাহর রাজ্যের দক্ষিণতম সীমা ছিল ‘ছত্ৰভোগ’। চৈতন্যদেব নামগান করতে করতে এগিয়ে চলেছেন সেই ছত্রভোগের দিকে। পথে গঙ্গাতীরের যেসব জনপদ পড়ল, আজ তারা হুগলি নদী থেকে অনেকটা দূরে। কারণ ভাগীরথীর জলধারা সরে গেছে। গৌরসুন্দরের পদরজধন্য সেই সব জনপদের নাম : বারুইপুর, দক্ষিণ বারাসাত, সরিষাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটি। শেষ সীমান্ত : ছত্ৰভোগ।
“এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতুহলে।।”
সে-আমলে ছত্রভোগের জমিদার ছিলেন রাজা রামচন্দ্র খান। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় চৈতন্যদেব গঙ্গার ওপারে, অর্থাৎ পশ্চিমপারে যাবার চেষ্টা করলেন। কাজটি কঠিন। এখানে গঙ্গার বিস্তার ভয়ানক–ঢেউ প্রচণ্ড; কিন্তু আসল বিপদ রাজনৈতিক। গঙ্গার পশ্চিমপার উৎকলরাজের শাসনাধীন। চৈতন্যদেবের সমকালীন গৌড়াধিপতি হুসেন শাহর সঙ্গে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেবের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত নেই। এপারের মানুষ ওপারে যায় না। ওপারের লোক এপারে আসে না।
তবু রাজা রামচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় একটি বড় নৌকার আয়োজন হল। স্থির হল রাতারাতি নৌকায় যাত্রীরা ওপারে যাবেন। শান্তিপুর থেকে আঁটিসারা পদযাত্রার বর্ণনা পদকর্তারা অধিকাংশই সংক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু এই গঙ্গা পারাপারের বর্ণনায় প্রায় সকল কবিই বাঙ্ময়।
বিভিন্ন কড়চা অন্বেষণ করে চৈতন্যসেবক অনুজপ্রতিম ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দ গঙ্গা পারাপারের যে বর্ণনাটি দিয়েছেন (নীলাচল অভিসার) তারই সংক্ষিপ্তসার এখানে লিপিবদ্ধ করি। ধরে নেওয়া যাক, নগেন দত্তের অর্ণবপোতে যাত্রীদলের কাছে আমাদের কাহিনীর নায়ক রূপেন্দ্রনাথও এই বর্ণনা দিয়েছিলেন :
ছত্রভোগের রাজা রামচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় এক ভক্ত ব্রাহ্মণের ভদ্রাসনে সশিষ্য চৈতন্যদেবের আতিথ্যের ব্যবস্থা হয়েছে। ভক্তের ভিটায় ঘর মাত্র দুটি। এতগুলি শিষ্যের শয়নব্যবস্থা কী করে হবে? ওঁরা স্বামী-স্ত্রী বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেও। আহারের আয়োজনই বা কী করবেন? সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন নিত্যানন্দ। বিব্রত ভক্ত বৈষ্ণব দম্পতিকে অন্তরালে টেনে এনে বললেন, শয়নের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছেন কেন? আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। চাঁদের আলোয় আমরা তো সারারাত আপনার প্রাঙ্গণে নামগান করব। আপনি বরং তুলসীমূলে কিছু আলপনা দেবার ব্যবস্থা করুন। আর একটি কাংসপাত্রে কিছু বাতাসা–‘হরির লুট’ দিতে হবে তো!
ব্রাহ্মণ প্রতিবাদে কী যেন বলতে গেলেন। বলা হল না। তার পূর্বেই ভেসে এল সমবেত নামগান :
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।
ব্রাহ্মণ তবু কিছু বলতে গেলেন। ফলে ধমক খেতে হল প্রভু নিত্যানন্দের কাছে : কেমনতর বৈষ্ণব আপনি? নামগান শুরু হয়ে গেছে এখনও আহার-নিদ্রার কথা চিন্তা করছেন?
ব্রাহ্মণীর দিকে ফিরে বললেন, আপনি মা, ওই আলপনা আর বাতাসার ব্যবস্থাটুকু করে দিন শুধু। বাদবাকি দায়দায়িত্ব এই ছেলের উপর দিয়ে যান।
অবগুণ্ঠনের আড়ালে সম্মতি জানিয়ে ব্রাহ্মণী ছুটলেন অন্দরে।
রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এলেন রাজা রামচন্দ্র। পণ্ডিত জগদানন্দকে জনান্তিকে টেনে নিয়ে এসে বললেন, নৌকা প্রস্তুত। এই শেষ রাত্রিই প্রশস্ত সময়, সেই সময় উৎকলী প্রহরীদের একাগ্রতা স্বাভাবিকভাবেই শিথিল হয়ে যায়। ওরা নিদ্রা যায়। প্রভু সশিষ্য হয়তো অলক্ষিতে ওপারে পৌঁছে যেতে পারবেন।
পণ্ডিত জগদানন্দ হেসে বললেন : প্রভু জগন্নাথদর্শনে যাচ্ছেন সেটা কোনও চৌরকার্য নয়। তবু শুধু হাতি-নারায়ণের কথা শুনলেই তো চলবে না, মাহুত-নারায়ণের কথাও শুনতে হবে। আমি প্রভুকে নিয়ে এখনি রওনা হব।
রাত্রির তৃতীয় যামে তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গা পার হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলছেন : নৌকায় উঠেও প্রভুর সশিষ্য নামসঙ্কীর্তন থামতে চায় না। নৌকা উথাল-পাথাল দুলছে, যতটা ঢেউয়ের দাপটে তদোধিক যৌথ নর্তনকুর্দনে।
“অবুধ নাইয়া বোলে হইল সংশয়
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয়।।…
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই
তাবত নীরব হও সকল গোঁসাঞি।।”
চৈতন্যদেব যে ঘাট থেকে গঙ্গা পার হয়েছিলেন, তাকে কেউ বলেছেন ‘প্রয়াগঘাট’, কেউ ‘গঙ্গাঘাট’। সম্ভবত সেটা বর্তমান কুলপির কাছাকাছি। গঙ্গাঘাট নামে একটা গ্রাম ওই অঞ্চলে এখনো আছে, কিন্তু ভাগীরথী সেখানে নেই। এর কাছাকাছি ছিল তিন-তিনটি নদীর সঙ্গম : সরস্বতী, দামোদর আর মন্ত্রেশ্বর (বর্তমান রূপনারায়ণ)। তাই এর আর এক নাম : প্ৰয়াগঘাট।
‘তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য’-গ্রন্থের লেখক ভূপতিরঞ্জন দাস লিখছেন, “রেনেলের মানচিত্র দৃষ্টে মনে হয়, মহাপ্রভুর সময়ে ছত্রভোগের কাছ থেকে বেশ প্রশস্ত নাব্য একটি খাড়ি বর্তমান তারানগর ও গঙ্গাধরপুরের পাশ থেকে পশ্চিমমুখী হয়ে কাকদ্বীপের সামান্য দক্ষিণে বুধোখালির কাছে মুড়িগঙ্গা বা বারাতলা নদীতে মিশেছিল ও সাগরদ্বীপের মাঝামাঝি ফুলডুবি খাল ছিল অতি প্রশস্ত! সম্ভবত মহাপ্রভুর নৌকা ছত্রভোগ থেকে এই পথে গিয়ে মেদিনীপুরের কণ্টাই মহকুমার রসুলপুর নদীতে প্রবেশ করে।…তিন নদীর সঙ্গম বলে সম্ভবত বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই স্থানটিকে প্রয়াগঘাট বলেছেন।”
…প্রথম সন্ধ্যায় কথকঠাকুর রূপেন্দ্রনাথ এখানেই থামলেন–অর্থাৎ প্রভুকে উৎকলরাজ্যে নামিয়ে দিয়ে। সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে : জয় গৌর! জয় নিতাই!
তারপর শুরু হয়ে যায় খোল-করতাল সহযোগে নামসঙ্কীর্তন।
ইতিপূর্বে একদিন দেখেছিলেন। সন্দেহ ছিল। তাই রূপেন্দ্রনাথ পুনরায় তৃতীয় সারির সেই নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে দৃকপাত করলেন। দেখলেন এখন আর অবগুণ্ঠনবতীর মুখটি দেখা যাচ্ছে না।
রূপেন্দ্রনাথ উঠে পড়েন। নিজের কক্ষে চলে যান। মেয়েটিকে–বলা উচিত ‘মহিলাটি’কে—ভাল করে দেখবার সুযোগ হয়নি। সচেতনভাবেই হোক অথবা ঘটনাচক্রেই, সে বসেছিল একটু পিছনে, তৃতীয় সারিতে, একটা আলো-আঁধারি পরিবেশে। শ্রীচৈতন্যের ‘নীলাচল অভিসার’ বর্ণনা করতে করতে উনি বারে বারেই শ্রোতৃবৃন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। অধিকাংশই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। দু-চারজন তরুণ-তরুণী। অনেকেরই নাকে রসকলি, মালা-চন্দনে বৈষ্ণব রূপটা প্রকটিত। দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওই সধবা মহিলাটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কথকের দিকে। চোখাচোখি হতেই অবগুণ্ঠন টেনে দেয়’।
রূপেন্দ্র রীতিমত চমকে উঠেছেন। প্রথম দৃষ্টিভ্রমে ওঁর মনে হয়েছিল ও কুসুমমঞ্জরী! তাই ওঁর চমকটা বেশ জোরদার। মেয়েটি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ফেলার পরমুহূর্তেই ওঁর মনে হল ও কুসুমমঞ্জরী নয়, হতে পারে না। তবে তার মুখের সঙ্গে ওই মেয়েটির মুখের আদলে কোথায় যেন মিল আছে তাই এত চেনা-চেনা লাগছে। না, চিত্তচাঞ্চল্য কিছু হয়নি রূপেন্দ্রনাথের আত্মসংযম অত লঘু নয়। তবে দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল : কে ওই মেয়েটি? কেন ওকে মনে হল এত চেনা-চেনা। রোগিণী হিসাবে কি কোথাও ওর চিকিৎসা করেছেন? মনে করতে পারলেন না।
৯
উড়িষ্যায়, অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর জেলায়, প্রবেশ করে চৈতন্যদেব বুঝলেন, রাজপথ ধরে অগ্রসর হওয়ায় নানান জাতের অসুবিধা। গৌড় থেকে শ্রীক্ষেত্রে যাবার সে-কালীন ওই রাজপথের নাম ছিল ‘জগন্নাথ সড়ক’। অসুবিধা দুই জাতের। প্রথমত এই সময় উৎকল- অধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের সঙ্গে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের যুদ্ধ চলছে। জগন্নাথ সড়কে অতর্কিতে দু-পক্ষের সৈন্যদলই মাঝে মাঝে এসে পড়ে। হাতি-ঘোড়া-পদাতিকের কোলাহল। তীর্থযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করে অশ্বারোহী রাজপুরুষেরা ঘোড়া ছোটায়। দ্বিতীয়ত, এ-পথে ‘দানীর’ অত্যাচার। ‘দানী’ অর্থে উড়িষ্যা রাজার পক্ষে ‘পথকর’ আদায়কারী। পদকর্তারা অনেকেই এই ‘দানী’দের অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐসব কারণে ‘জগন্নাথ সড়ক’ পরিহার করে চৈতন্যদেব অরণ্যপথে বা গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে চলতে থাকেন।
শিয়াখালা গ্রামের মধ্য দিয়ে ওঁরা এসে উপনীত হলেন রূপনারায়ণ নদের তীরে তাম্রলিপ্তে। নদের তীরে কপালমোচন তীর্থে মায়ের মন্দির। বাহান্নপীঠের একপীঠ, ‘বর্গভীমা’ মায়ের মন্দির। তাম্রলিপ্তি অতি প্রাচীন বন্দর। খ্রিস্টপূর্ব প্রাগশোক যুগেও ছিল তার প্রসিদ্ধি। শোনা যায়, এই তাম্রলিপ্তি বন্দরে নির্মিত জাহাজ নিয়ে, এখান থেকেই বাংলার নৃপতি সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ সিংহলদ্বীপ জয় করেন। আন্দাজ করা হয়, সময়টা ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সমকালীন। বিজয়সিংহের এই সিংহলবিজয় কাহিনীটি সবিস্তারে আঁকা আছে অজন্তার দ্বিতীয় গুহাবিহারে।
বর্গভীমা মূর্তিতে আছে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের দেবী উগ্রতারার ছাপ। হিন্দুদের তন্ত্রমতে, এই শক্তিপীঠে পতিত হয়েছিল সতীর বাম গুল্ফ। দেবীর নাম ভীমরূপা; ভৈরব : কপালী।
রায়গুণাকর কবি ‘অন্নদামঙ্গল’-এ লিখেছেন :
“বিভাষেতে বাম গুল্ফ ফেলিলা কেশব
ভীমরূপা ভৈরবী আর কপালী ভৈরব।।”
শ্রীচৈতন্য যে শিয়াখালার পথে তমলুকে এসেছিলেন তার প্রমাণ শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায়:
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবনদ পার হৈঞা
উত্তরিলা তমোলিপ্তে সেয়াখালা দিয়া।।
এখানে ‘দেবনদ’ কিন্তু রূপানারায়ণ নয়, দামোদর। গোবিন্দদাসের কড়চায়, ওঁরা হাজিপুর গ্রামের পথে তমলুক থেকে এসে উপনীত হলেন মেদিনীপুর। কংসাবতী নদীর তীরে ধনবান বণিক কেশব সামন্ত চৈতন্যদেবের সঙ্গে কৌতুক করতে এসেছিল। গোবিন্দদাস বর্ণনা করেছেন, কীভাবে কেশব সামন্তকে প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়ে ‘হরিনামসর্বস্ব’ করে প্রভু শ্রীক্ষেত্রের পথে রওনা হলেন। নারায়ণগড়েও ঘটল একই ঘটনা: বীরেশ্বর আর ভবানীশঙ্কর নামে দুই মহাধনী সহোদর ভ্রাতা চতুর্দোলায় চেপে প্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁরাও কৃষ্ণপ্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ হলেন। চতুর্দোলা ফিরে গেল। ওঁরা আখড়ায় রয়ে গেলেন।
নারায়ণগড়ের পরবর্তী স্থান: দন্তপুর।
‘দন্তপুর’-এর মহিমা অতিপ্রাচীন। মেদিনীপুর জেলার ‘দাঁতন’ কড়চা-বর্ণিত ‘দন্তপুর’ হতে পারে; কিন্তু ‘মহাভাষ্য’ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে যে ‘দন্তপুর’-এর বর্ণনা আছে, এই দাঁতন বোধ হয় তা নয়।
আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতকে মগধসম্রাট মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। তার পূর্ব যুগ থেকেই অর্থাৎ খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকেই কলিঙ্গের রাজধানী ছিল দন্তপুর ‘কুরুধম্ম জাতক’ এবং ‘মহাভাষ্যে’ একথা বলা আছে। বুদ্ধশিষ্য ক্ষেম বুদ্ধদেবের চিতা থেকে সংগৃহীত একটি শব্দন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত সেই দাঁতটির উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। সুদীর্ঘকাল ঐ স্তূপে বুদ্ধদেবের শ্ব-দন্তটি পূজিত হতে থাকে। কথিত আছে ওই দন্তের প্রভাবে কলিঙ্গরাজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ ঘটতে থাকে। তাই দেখে মগধরাজ ওই শ্ব-দন্তটি স্বীয় রাজধানী পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। করদরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রতিবাদ করতে পারেননি। কাহিনী অনুসারে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত ছিলেন ধর্মমতে বৌদ্ধ। অথচ তাঁর সম্রাট মগধরাজ ছিলেন শৈব। ওই শ্ব-দন্তটি পাটলিপুত্রে নিয়ে আসার পর মগধসম্রাটের মতিগতির পরিবর্তন হতে থাকে। তিনি বৌদ্ধভাবাপন্ন হয়ে যান। ইতিমধ্যে ওই দন্ত বিষয়ে নানান অলৌকিক কাণ্ডও ঘটতে থাকে। ফলে সম্রাটের ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সভাসদেরা দন্তটিকে বিদায় করতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। কাহিনী মতে, কলিঙ্গরাজ গুহাশিবের কন্যা হেমবালা এবং জামাতা, উজ্জয়িনীর রাজপুত্র (তাঁর নামই হয়ে যায় দন্তকুমার), ওই অমূল্য শ্ব-দন্তটি সিংহলে পাচার করেন। তাঁরা ওই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন, যে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বোধিদ্রুমের চারা নিয়ে যান সিংহলে। এই কাহিনী অনুসারে সিংহলের অনুরাধাপুরের জগদ্বিখ্যাত স্তূপের ভিতরে রাখা আছে গৌতমবুদ্ধের সেই শ্ব-দন্তটি।
দন্তপুরের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কানিংহ্যামের মতে, গোদাবরী-তীরবর্তী রাজমহেন্দ্রী ছিল সেই প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী এবং দন্তপুর হচ্ছে নীলাচল বা পুরীধাম।
দন্তপুর থেকে জলেশ্বর, বাঁশদহ, রেমুণা, ভদ্রক হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব সশিষ্য এসে উপনীত হলেন যাজপুরে। বিরজাদেবীর পীঠস্থান এই যযাতিপুর। এখানে উপনীত হয়ে সকলে যখন রাত্রের মতো বিশ্রামের ঠাঁই খুঁজছেন তখন কাউকে কিছু না জানিয়ে চৈতন্যদেব সহসা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে প্রভুর দর্শন না পেয়ে ভক্তেরা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অন্তর্যামী! সঙ্গীদের ব্যাকুলতা দেখে তাঁদের বললেন তোমরা ব্যাকুল হয়ো না। প্রভু আজ বিশেষ কারণে অপ্রকট হয়েছেন। আগামীকাল এখানেই আমরা তাঁকে পাব।
“আজি থাকি, কালি প্ৰভু আইব এথাই।।”
…এই পর্যন্ত বর্ণনা করে কথকঠাকুর—রূপেন্দ্রনাথ–সহসা থেমে গেলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগল: অতঃপর ওদের সেই প্রশ্নটাই বাঙ্ময় হয়ে উঠল প্রথম সারিতে উপবিষ্ট নগেন দত্তমশায়ের কন্ঠে: তারপর কী হল?
রূপেন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন, আজ এই পর্যন্তই! আগামী কাল আমরা এখানেই তাঁকে পাব–“আজি থাকি, কালি প্ৰভু আইব এথাই।।”
কথকের দৃষ্টি পতিত হল শ্রোতৃবৃন্দের একটি বিশেষ একান্তে। কপাটের আড়াল থেকে একজন বিশেষ শ্রোত্রী তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। তাঁর সর্বাবয়ব দরজার কপাটের আড়ালে, শুধু অনবগুণ্ঠিত মুখখানি দেখা যায়। তন্ময়তাজনিত কারণে তার অবগুণ্ঠন যে কখন খসে পড়েছে তা সে নিজেও জানতে পারেনি। রূপেন্দ্র দেখলেন, মেয়েটি সধবা, তার কপালে কুমকুমের টিপ, সিঁথিতে সিন্দুর, স্বর্ণমণ্ডিত কর্ণাভরণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা।
উনি নিশ্চিত: মহিলাটি ওঁর পরিচিত। সুপরিচিত। শুধু রোগিণী হিসাবেই ওর সান্নিধ্যে আসেননি।
নিঃসন্দেহ হলেন যখন সম্বিত ফিরে পেয়েই মেয়েটি অবগুণ্ঠনের আড়ালে আত্মগোপন করল। মহিলাটি ওঁর পূর্বপরিচিতা, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক সে আত্মপ্রকাশ করতে অনিচ্ছুক! আলো-আঁধারিতে প্রতিদিন সে এসে বসছে ইচ্ছা করেই–যাতে কথকঠাকুর তাকে চিনতে না পারেন! কেন?
পরদিন শ্রীচৈতন্যের নীলাচল অভিসারের বর্ণনা করতে বসে রূপেন্দ্রনাথ দর্শকমণ্ডলীর ভেতর সেই বিশেষ মেয়েটিকে সনাক্ত করতে পারলেন না। প্রতিদিন সে ঠিক একই স্থানে এসে বসত। কপাটের আড়ালে। নিজে অন্ধকারে থেকে লক্ষ্য করত কথককে। গতকাল মহিলাটির অসতর্কতায় ক্ষণিকের জন্য হলেও চার চোখের মিলন হয়েছিল। আজ তাই সেখানে অন্য একজন অনবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া। মেয়েটি কি বুঝতে পেরেছে যে, উনি তাকে দর্শকদলে অন্বেষণ করেন? তাই যদি হয়, তাতে কুণ্ঠার কী আছে? যদি সে ওঁর পরিচিতা হয়, তাহলে এগিয়ে এসে সে তো স্বচ্ছন্দে ওঁকে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিতে পারে। সর্বসমক্ষে সেটা করতে সঙ্কোচ হলে সে তার স্বামীকে বলতে পারে। আঠারো-বিশ বছরের একটি সধবা রমণী একা-একা তীর্থদর্শনে যাচ্ছে না নিশ্চয়! তাহলে?
—বলুন, কোবরেজ মশাই? ঠাকুর যাজপুরে এসে অপ্রকট হলেন কেন?
রূপেন্দ্র বললেন, সে-কথাই আজ বলব। আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, জীবনে এমন একটা পর্যায় আসে যখন মানুষে আত্মগোপন করতে চায়। ধরুন, আপনি আমাকে চেনেন, খুব ভাল ভাবেই চেনেন। আপনাতে আমাতে একদিন অনেক কথা হয়েছে, হয়তো প্রাণের কথাও। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, সর্বসমক্ষে আপনি সে-কথা স্বীকার করতে পারছেন না। তখন আপনি আড়ালে সরে যাবেন। একবারও ভেবে দেখবেন না, সেজন্য আমি কী পরিমাণে ব্যথিত হচ্ছি। হয়তো আমি আপনাকে চিনতেও পেরেছি, তাই আপনার ঐ দূরে সরে যাওয়া আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক হচ্ছে। আমি ভাবছি: লোকলজ্জাটাই বড় হল! আমাদের ভালবাসাটা নয়?
নগেন দত্ত বসেছিলেন সামনে। প্রশ্ন করেন, হঠাৎ এ-কথা বলছেন কেন, কোবরেজমশাই? ঠাকুরের কি তেমন কোনও সমস্যা হয়েছিল?
—আমি জানি না। কী কারণে যাজপুরে গৌরাঙ্গদেব প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য আত্মগোপন করেছিলেন তার কোনও কৈফিয়ৎ নেই। পরদিন সকালে সত্যিই গোরাচাঁদ এসে হাজির। হারানো মানিক ফিরে পেয়ে সবাই হরিধ্বনি দিয়ে ওঠে। প্রভু নিত্যানন্দ বলেন, তোমরা দেখলে তো! আমি বলেছিলাম!
এই রহস্যময় সাময়িক অন্তর্ধানের কথা অনেকেই বলেছেন। স্পষ্ট না বললেও ইঙ্গিত দিয়েছেন কৃষ্ণদাস গোঁসাই, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত বা গোবিন্দ দাস কর্মকার। কিন্তু কার্যকারণ-সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু লেখেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীজয়ানন্দ মিশ্রের ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’:
“চৈতন্য গোঁসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেতে পলাইয়ে গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে।।
সেই বংশের পরম বৈষ্ণব কমললোচন নাম।
পূর্ব জন্মের তপে গোঁসাঞি তার ঘরে করিলা বিশ্রাম।।”
জয়ানন্দ মিশ্র বয়সে চৈতন্যদেবের ছাব্বিশ বছরের অনুজ। তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ শিষ্য নন, অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি গৌরসুন্দরের স্নেহধন্য। বস্তুত, তাঁর পিতৃদত্ত নাম ‘জয়ানন্দ’ নয়, এ নাম চৈতন্যদেবের দেওয়া। জয়ানন্দ ‘চৈতন্যমঙ্গল’ রচনা করেন চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে। কিন্তু তাঁর রচনা নানান ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। সম্ভবত এক্ষেত্রে তিনি শ্রীচৈতন্যের সাময়িক আত্মগোপনের হেতুটি যথার্থ বর্ণনা করতে পেরেছিলেন :
গৌরাঙ্গদেবের পূর্বপুরুষেরা উৎকলখণ্ডের যাজপুরে বসবাস করতেন। মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের (যাঁর উপাধি ছিল ভ্রমর) অত্যাচারে পণ্ডিত মধুকর মিশ্র সপরিবারে যাজপুর থেকে পালিয়ে পুববাংলার শ্রীহট্টে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা উৎকলবাসী, মাত্র কয়েক পুরুষ তাঁরা শ্রীহট্টে এসে বাঙালি হয়েছেন। মধুকর মিশ্রের বংশধর, নিমাই পণ্ডিতের পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র আবার শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, নবদ্বীপে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর নিমাই পণ্ডিত শ্রীহট্টে গমন করেন এবং সেখানে কয়েকমাস পিতৃকুলের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যা বিতরণ করেন। সেখান থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে নিমাই পণ্ডিত জানতে পারেন যে, তাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে।
পদকর্তা জয়ানন্দ জানাচ্ছেন যে, শ্রীচৈতন্যের জনককুলের এক জ্ঞাতিভ্রাতা পরমবৈষ্ণব কমললোচন মিশ্র যাজপুরেই বসবাস করতেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর সংসারাশ্রমের আত্মীয়তা স্বীকার করে লৌকিক সৌজন্য দেখানো নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি? ঈশ্বরের অবতার পরমভাগবত শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যদেব তেমনই এক সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। প্রেমের অবতার পরমবৈষ্ণব কমললোচনকে কৃপা করতে চান, তার আতিথ্যগ্রহণ করতে চান, তার স্বহস্তে প্রস্তুত শাকান্ন গ্রহণ করতে চান—হেতু এ নয় যে, কমললোচন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা, পরন্তু কমললোচন পরমভক্ত! কিন্তু এই তত্ত্বকথাটা সাধারণ বুদ্ধির শিষ্যদল বুঝতো না। তারা এটাকে অজুহাত দেখিয়ে ব্রাত্য হবার কৈফিয়ৎ খুঁজতো। হয়তো এ আমাদের অনুমান মাত্র হয়তো তাই, ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য করুণার অবতার অপ্রকট থেকে দুই কুল রক্ষা করলেন। গৌরাঙ্গসুন্দরকে স্বহস্তপক্ব শাকান্নে সেবা করে কমল তার মানবজীবন সার্থক করল। শিষ্যরাও কিছু জানল না। অর্থাৎ লাঠিটাও ভাঙল না, সাপটাও–না, মরল না, নির্বিষ হয়ে গেল মাত্র!
এদিন সন্ধ্যায় কথকঠাকুর নিমাই সন্ন্যাসের অনুগামী হয়ে মানসভ্রমণে যাজপুর থেকে এলেন পুরুষোত্তমপুর। সেখান থেকে চৌদ্বার হয়ে মহানদী তীরের বন্দর কটক। বললেন, কটক থেকে জগন্নাথক্ষেত্রের পথ-বর্ণনা আমি জাহাজে বসে করব না। সে-পথে আপনারা পদব্রজে যাত্রা করবেন। সম্ভবত কটকের পর চার রাত আমাদের চটিতে, যাত্রীনিবাসে বা মন্দির-প্রাঙ্গণে কাটাতে হবে—একান্নকানন, সাক্ষীগোপাল, কমলপুর যাত্রী-আবাসে সন্ধ্যা কাটাতে সেসব তীর্থের মহাত্ম্য বর্ণনা করব। আমরা এখানেই আসর ভাঙছি। কালই আমরা সমুদ্রে পড়ব। সেখানে জাহাজ খুব দুলবে, এমন স্থির হয়ে বসে গল্প করার হয়তো অবকাশ থাকবে না।
রূপেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। অনেকেই ব্রাহ্মণের পদধূলি নিতে এগিয়ে এল। অভ্যাসমতো উনি সমভঙ্গে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলতে থাকেন, ওঁ নমঃ নারায়ণায়!
সহসা লক্ষ্য হল, অন্ধকার থেকে অবগুণ্ঠনবতী একজন সধবা এগিয়ে আসছে। তার পরিধানে সেই বাসন্তী রঙের কল্কাপাড় মুর্শিদাবাদী রেশমের শাড়িখানাই—যা ওঁর পরিচিত মেয়েটি ওঁর কাছাকাছি এসে স্পর্শ-বাঁচানো একটি প্রণাম করল গলায় আঁচল দিয়ে। রূপেন্দ্র নিমীলিত নেত্রে যথারীতি উচ্চারণ করলেন : ওঁ নমঃ নারায়ণায়।
মেয়েটির আজ কী যেন হয়েছে! সন্ন্যাসজীবনের নিয়মবিরুদ্ধ জানা সত্ত্বেও প্রেমের ঠাকুর ভক্তের আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন—তাঁর মানবজন্ম সার্থক করেছিলেন শুনেই বোধহয় সে আজ আর স্থির থাকতে পারেনি। সর্বসমক্ষে মাথার ঘোমটা অল্প একটু সরিয়ে দিয়ে বললে, রুপোদা! বৌঠান কোথায়?
সে-কণ্ঠস্বরে বজ্রাহত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হলেন মুহূর্তে। দুই বলিষ্ঠ মুঠিতে ওর দুই বাহুমূল চেপে ধরে বললেন, মীনু! তুই বেঁচে আছিস?
দৃঢ়হস্তে ওর দুই বাহুমূল ধরে আছেন বলেই ও ভূলুণ্ঠিতা হল না। না হলে ওর পদযুগল ঠিক সেই মুহূর্তে বেপথুমান দেহটি হয়তো ধরে রাখতে পারত না।
হাঁ-হাঁ করে ওপাশ থেকে শশব্যস্তে ছুটে আসেন দুর্গা গাঙ্গুলী। ধরে ফেলেন স্ত্রীর পতনোন্মুখ দেহটি। বলেন, ছি, ছি, ছি, ছি! ও কী করছো ছোটবউ? রুপোকে কি পেন্নাম করতে আছে? তুমি যে ওর খুড়িমা!
মৃন্ময়ী ততক্ষণে সামলেছে। দুই পুরুষের মুঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। অবগুণ্ঠনে পুনরায় ঢেকেছে আরক্তিম আনন।
রূপেন্দ্র দুর্গা গাঙ্গুলীর দিকে ফিরে বললেন, তাহলে সেদিন কেন বললেন: ‘তোমার খুড়িমা ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে চলে গেছেন?’
অনেকেই ঘটনাটা লক্ষ্য করেছে, পিছনের দিকের মানুষজনও আন্দাজ করেছে ওখানে কৌতুককর কিছু ঘটছে। সকলে ঘনিয়ে আসে।
দুর্গা আমতা-আমতা করেন, কী আশ্চর্য! সে তো তোমার বড়-খুড়িমা, মানে শোভার মা। ছোট-বউ সগ্যে গেছে তা আমি মুখ ফসকেও বলিচি?
রূপেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখেন মৃন্ময়ী পায়ে পায়ে অন্ধকারের দিকে সরে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইছে। উনি বললেন, বুঝেছি!
একজন বর্ষীয়সী মহিলা রূপেন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, ওই মেয়েটি কি তোমার খুড়িমা? ওই যে এখনি তোমারে পেন্নাম করল?
রূপেন্দ্র বললেন, ও সম্পর্কে আমার ছোট বোন।
—তাইলে ওই বামুনঠাকুর কেন বললেন, ও তোমার খুড়িমা?
বার মহড়া নিতে এগিয়ে এলেন রীতিমতো বৃদ্ধা একজন। সাড়ে তিন-কুড়ি পাড়ি দিয়েছেন বিধবা। এগিয়ে এসে বর্ষীয়সীকে ধমক দিয়ে ওঠেন, তোমার মাথায় গোবর পোরা, কায়েত-বউ। বুঝলে না? ওই মেয়েটি আমাদের কথকঠাকুরের সম্পর্কে ছোট বোন, আর ওই তিন-কাল-গে এককালে-ঠেকা বুড়োটা তারে তৃতীয়পক্ষ করেচে! কী গো বুড়ো বামুনঠাকুর? ঠিক বলিচি তো? তৃতীয়? নাকি চতুখ?
দুর্গা গাঙ্গুলী ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। রূপেন্দ্রও পিছন ফিরে নিজের ঘরের দিকে চলতে শুরু করেছিলেন। তবু শুনতে পেলেন কায়েতগিন্নির প্রশ্নটা, তা যাই বল কেনে বাঁউনদিদি, খুড়িমা যখন একবার হয়ে গেচে তকন আর পুরনো সম্পক্যের জের টেনে ওর পেন্নাম করাটা ঠিক হয়নি। ধম্মে তা সইবে না!
বামুনদিদির অন্তিম নিদানটাও তাঁর কানে যায় : তুই আর আমারে ধম্মো শোনাতে আসিস না, কায়েতবউ! সন্নেসী হয়েও প্রেমের ঠাকুর যদি পুরনো সম্পক্যের জের টেনে জ্ঞাতিভাইয়ের শাকান্ন সেবা করতে পারেন তাইলে ওই আবাগী ঘাটের মড়ার বউ হবার অপরাধে দাদারে এট্টা পেন্নাম করতেও পারবেনি? এটা তোর কোন পণ্ডিতের বিধেন? অ্যাঁ?
রূপেন্দ্র দ্বার রূদ্ধ করে দেন।