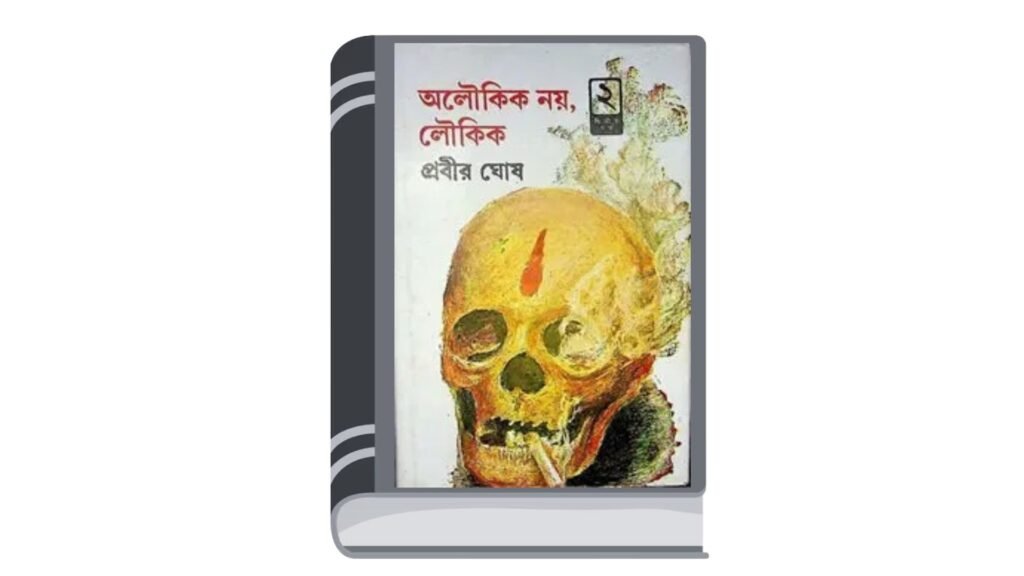কিছু কথা – যুক্তিবাদ প্রসঙ্গ
এই গ্রন্থটি অবশ্যই পরিবর্ধিত সংস্করণ। যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রথম কথা, প্রথম শর্ত—আমরা সব কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করব, শুধুমাত্র তার পরই গ্রহণ করব বা বাতিল করব। আমরা লক্ষ্য রাখব—আমাদের যুক্তি যেন শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত না হয়। তেমনটি হলে আমরা যুক্তির পরিবর্তে গলার জোর ও পেশিবলের উপরই একটু বেশিরকম নির্ভরশীল হয়ে পড়ব।
কিছু সন্ধিক্ষণ আসে যখন মানুষ যুক্তির চেয়ে আবেগকে মূল্য দেয় বেশি। সেই সময় একটি মানুষ কোন যুক্তিকে গ্রহণ করবে এবং কোন যুক্তিকে বর্জন করবে—এই বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা, গোষ্ঠীস্বার্থ ইত্যাদি। এই আবেগকে কাজে লাগিয়েই শোষিত মানুষদের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস ও ঘৃণার বীজ বপনে পরিকল্পিতভাবে সচেষ্ট থাকে শাসক ও শোষক শ্রেণি। এই পরিকল্পনা শোষিতদের উন্মাদনার নেশায় ভুলিয়ে রাখার স্বার্থে, শোষকদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। আর তাইতেই জন্ম নেয় রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ সমস্যা, চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সমস্যার মতো সমস্যাগুলো। শোষক নিজ স্বার্থেই চায় সাধারণ মানুষ যুক্তির দ্বারা নয়, আবেগের দ্বারাই পরিচালিত হোক।
শোষক শ্রেণি কখনওই চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের
চেতনাকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে, বেশি দূর পর্যন্ত
এগিয়ে নিয়ে যেতে।
এর বাইরেও আমরা ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে অনেক সময় হৃদরোগে আপ্লুত হয়ে যুক্তিছাড়া যুক্তিকে অর্থাৎ কুযুক্তিকে সমর্থন করি। যখন আমি একজন বাসকর্মী তখন অপর কোনও বাসকর্মীর প্রতি যে কোনও কারণে আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই—তা সে আইন ভাঙার জন্য পুলিশ আইনসম্মত ব্যবস্থা নিলেও। যখন আমি ছাত্র, তখন আমারই সহপাঠী বিনা টিকিটে ট্রেনে কলেজে আসার সময় গ্রেপ্তার হলেও রেলকর্মীদের হাত থেকে বন্ধুকে মুক্ত করতে স্টেশনে হামলা চালাই। আমি কখনও প্রতিবেশীর মৃত্যুতে ডাক্তারের দায়িত্বহীনতার দাবি তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়ি। আমিই আবার হাসপাতাল-কর্মী হিসাবে ওই আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার দাবিতে হাসপাতালের কাজকর্মকে অচল করে দিই। এই ব্যক্তি স্বার্থে বা গোষ্ঠী স্বার্থে পরিচালিত হয়ে কখনও আমরা বাঙালি, কখনও বিহারি, কখনও অসমিয়া, কখনও অন্য কিছু। কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও বা অন্যধর্মী। কখনও শুধুমাত্র ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়ার অপরাধে, ভিন্ন ধর্মীয় হওয়ার অপরাধে, ভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাস পোষণ করায় একে অপরের জীবনধারণের অধিকার কেড়ে নিতেও দ্বিধা করি না। যুক্তিহীন আবেগই আমাকে হত্যাকারী, অত্যাচারী, করে তোলে, কুযুক্তির দাস করে তোলে।
মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব অতি প্রবল। আমরা পরিবেশগতভাবে সাম্প্রদায়িক হয়েছি, প্রাদেশিক হয়েছি। যুক্তির পরিবর্তে শুধুমাত্র কুযুক্তির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি। সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের ইতিহাস পড়ে সাম্প্রদায়িক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছি। ‘হিন্দু’ ঐতিহাসিকরা হিন্দু রাজাদের রাজাংশ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধকে স্বদেশ প্রেমের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভুলে থাকতে চেয়েছি—দেশ শুধুমাত্র একটা ভূ-খণ্ড নিয়ে নয়, ভূ-খণ্ডের মানুষদের নিয়ে। কোনও দেশের উন্নতির অর্থ সেই দেশের অধিবাসীদের উন্নতি। স্বদেশ প্রেম বলতে, দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির প্রতি প্রেম। এই অর্থে রাজাদের দেশপ্রেমের সামান্যতম হদিশ মেলে কি?
সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের যুদ্ধকে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুদ্ধ বলে প্রচার করতে চাইলেও বাস্তব সত্য কিন্তু আদৌ তা নয়। আকবরের পক্ষে হিন্দু রাজপুত সেনার সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। সেনাপতি মানসিংহও ছিলেন রাজপুত। অপরপক্ষে রাণা প্রতাপের বাহিনীতে ছিল বিশাল সংখ্যায় পাঠান সৈনা। সেনাপতি ছিলেন হাকিম খাঁ। এ-ছাড়া তাজ খাঁর নেতৃত্বেও ছিল আর এক পাঠান বাহিনী। অতএব দুই রাজার এই লড়াই কোনও সময়ই মুসলমান ও হিন্দুদের যুদ্ধ ছিল না। ছিল দুই রাজার মধ্যের স্বার্থের লড়াই।
রাণা প্রতাপের রাজ্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টাকে স্বদেশপ্রেম
বলার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও কারণই থাকতে পারে না।
নিজ স্বার্থে লড়াই স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন হলে,
আকবর কেন স্বদেশপ্রেমিক হবেন না?
**
একইভাবে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজির লড়াইও ছিল এক
বাদশাহ এবং এক রাজার স্বার্থের দ্বন্দ্ব মাত্র।
ইতিহাসের নিরিখে ভারতের মধ্যযুগের দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক। তুর্কি সেনার বিরুদ্ধে রাজপুত প্রভুদের লড়াই শুধুই দু-দলের সেনাবাহিনীর লড়াই ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রেই। কোথাও তুর্কি সেনাদের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। ভোগসর্বস্ব হিন্দু রাজাদের জন্য লড়াই করার কোনও প্রেরণাই প্রজারা অনুভব করেনি। এই কঠিন সত্যকে হিন্দু ইতিহাস রচয়িতারা ‘হিন্দু’ স্বার্থেই দেখতে চাননি। তাঁরা দেখাতে চাননি—মুঘল যুগে মুঘল বা মুসলমান প্রজারাও ছিল চূড়ান্তভাবে শোষিত, দারিদ্রে জর্জরিত। ‘হিন্দু’ ঐতিহাসিকরা যেভাবে তুর্কিদের বহিরাগত বলে বর্ণনা করেছেন, আগ্রাসকের ভূমিকায় বসিয়েছেন, সেভাবে তো তাঁরা বর্বর আর্য উপজাতিদের চিত্রিত করেননি? তুর্কিদের চেয়ে তো আর্যরা কোনো অংশেই কম বহিরাগত বা কম বিধর্মী ছিল না। কয়েক সহস্রক আগে তারাও তো তুর্কি ভূখণ্ড থেকেই ভারতে প্রবেশ করেছিল। আর্যরা ভারতীয় হতে পারলে তুর্কিরা কেন ভারতীয় বলে পরিচিত হবে না? প্রাক্ আর্য জাতি পরাজিত হয়েছিল বলেই তাদেরকে অনার্য-রূপে এমনভাবে ঐতিহাসিকরা চিত্রিত করেছেন যে, বর্তমানে ‘অনার্য’ শব্দটি ‘অসভ্য’-র প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও নর্মদা উপত্যকার প্রাক্ আর্য যুগের যে নিদর্শন পেয়েছি তা ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচারিতারই প্রমাণ। তাদের গৃহনির্মাণ প্রণালী, নগরবিন্যাস, বয়ন, অঙ্কন, লিখন, ভাস্কর্য প্রতিটিই ছিল অতি উন্নত পর্যায়ের। আর্যরা প্রাক্ আর্য মানুষদের কাছ থেকে এইসব বহু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এ কথা চূড়ান্তভাবেই সত্য। আর্য সভ্যতার কোনও নিদর্শন না পাওয়ার অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, আর্য সভ্যতা ছিল গ্রামীণ। তাই প্রাত্নিক উপকরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি।
আর্যরাই ভারতে প্রথম সভ্যতার আলো এনেছে, এ কথা যেমন
মিথ্যা, একইভাবে মিথ্যা ভারতের বর্তমান সভ্যজাতি
গোষ্ঠীগুলো সবই আর্যদের থেকেই সৃষ্ট। এই চিন্তাই
আমাদের আর্যজাতির বংশধর হিসেবে ভাবতে
শিখিয়েছে প্রাক্ আর্য জাতিকে অনার্য,
অসভ্য হিসেবে চিত্রিত করতে।
আমাদের দেশের ‘হিন্দু’ জাতীয়তাবোধ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সুলতান মামুদ এবং ঔরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসকে ‘হিন্দু’ বিদ্বেষের এবং হিন্দুত্বের অপমানের প্রমাণ হিসেবে হাজির করেছে। একই সঙ্গে ষষ্ঠ শতকে হর্ষের একের পর এক হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনের ঘটনা বিষয়ে নীরব থেকেছে। হর্ষ তো মন্দির লুণ্ঠনের জন্য ‘দেবোৎপাটননায়ক’ নামে এক শ্রেণির রাজকর্মচারীরাই নিয়োগ করেছিলেন। মন্দির লুণ্ঠনের জন্য যদি মামুদ ও ঔরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত হন, তাতে হর্ষ একই কাজের জন্য কেন হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত হবেন না?
হর্ষের মন্দির লুণ্ঠন প্রসঙ্গে আমার এক ইতিহাসের অধ্যাপক বন্ধু জানিয়েছিলেন, “আমাদের আলোচনা করা উচিত শুধুমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে নয়, বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে। সে যুগে মন্দির শুধু দেবোপাসনার স্থল ছিল না, মন্দিরের গুপ্ত কক্ষে সঞ্চিত থাকত ভক্তদের দান ও শ্রেষ্ঠীদের রত্নরাশি। অর্থ ও রত্ন রাজ্য শাসনে অপরিহার্য। রাজ্য শাসনের স্বার্থেই রত্ন আহরণের জন্য হর্ষ মন্দিরে হাত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।’
এই যুক্তিই মামুদ বা ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হবে না? গোটা হিন্দু যুগব্যাপী বীর-শৈব ও লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়গুলো যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির মঠ পুঁথি ধ্বংস করে গেছেন, আমাদের দেশের ইতিহাসের বইগুলো সে বিষয়ে নীরব কেন?
হিন্দুদের জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য মুঘল যুগের শাসকদের ‘হিন্দু’ ঐতিহাসিকরা যতই তাঁদের লেখনিতে অভিযুক্ত করুন, বাস্তবক্ষেত্রে কোনও মুঘল সম্রাটই কিন্তু গণ-ধর্মান্তরের চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেননি। এমনকী ঔরঙ্গজেবও নন। সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে রাজধর্মে দীক্ষিত করা নিন্দনীয়ই যদি হয়, তবে নিন্দার প্লাবনে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত সম্রাট অশোককে। নিজ ধর্মে দীক্ষিত করতে তিনি কী না করেছেন? তবু তিনি মহান! তিনি ধর্মাশোক। তিনি শান্তি ও অহিংসার প্রতীক!
সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা এমন ইতিহাসই রচনা করেছেন যা পড়ে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ভারতের সমস্ত কিছু গৌরবের কৃতিত্ব হিন্দুদের, যা কিছু অগৌরবের তার সমস্ত কিছুর দায়ই মুসলমানদের। দেশের এই শিক্ষা পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে সাধারণভাবে মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষই পোষণ করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যমূলক আচরণ পেয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতি সন্দেহই পোষণ করছে। ফলে একই দেশে বাস করেও সংখ্যাগুরুদের অবিশ্বাস ও পক্ষপাত সংখ্যালঘুদের ভারতকে আপন দেশ ভাবার সুযোগ দিচ্ছে না। বরং ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে মৌলবাদী পরিবেশই আরও বেশি করে জাঁকিয়ে বসছে।
ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠীস্বার্থে যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা
হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই পুষ্ট করেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের
বিষবৃক্ষের বীজ কৈশোরেই ইতিহাস পাঠকদের
মাথায় বপন করা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে
সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, রক্তপাত, লুণ্ঠন,
হত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ
করেই চলেছে।
যুক্তিবাদীদের কাছে কোন যুক্তি গ্রহণীয় হবে? নিশ্চয়ই এমন কোনও যুক্তি গ্রহণীয় হবে না যা সাম্প্রদায়িক, শুধুমাত্র গোষ্ঠিস্বার্থে চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা। যুক্তিবাদীরা পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও গোষ্ঠীস্বার্থকে সমর্থনের প্রশ্নই যদি বিশাল বড় হয়ে ওঠে, তবে আমরা দ্বিধাহীনভাবে শোষিতদের স্বার্থকেই নিজ স্বার্থ জ্ঞান করব। কারণ, যুক্তিবাদীরা মানবিকতার বিকাশকামী, যুক্তিবাদীরা দেশপ্রেমী। যুক্তিবাদীদের ধারণায় ‘দেশ’ বলতে মাটি নয়, দেশ বলতে ভূখণ্ডের মানুষগুলো। ভূখণ্ডের সংখ্যাগুরু মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমই দেশপ্রেম। আমরা চাই ধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে। যার পরিণতিতে তাঁরা যুক্তি দিয়ে বিচার করে শুধুমাত্র তারপরই কোনও কিছুকে গ্রহণ করবেন অথবা বর্জন করবেন। যুক্তিবাদী চিন্তাই তাঁদের বুঝিয়ে দেবে তাঁদের প্রতিটি বঞ্চনার কারণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
এই মুহূর্তে প্লেটোর একটা কথা বড় বেশি মনে পড়ছে।
প্লেটো বলেছিলেন, “মহান মিথ্যে ছাড়া রাষ্ট্র চালানো যায়
না।” এই ‘মহান মিথ্যে’ দিয়েই শোষিত মানুষগুলোর
প্রতিবাদের কণ্ঠ, বিপ্লবের ইচ্ছে, একত্রিত সংগ্রামের
প্রয়াসকে প্রতিহত করার চেষ্টা চলেছে
ধারাবাহিকভাবে।
এককালে ‘ঈশ্বরতত্ত্ব’ মহান মিথ্যে হিসেবে যতখানি কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল এখন আর ততখানি জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রশক্তির কাছে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে অবতারদের হজাজির করার প্রয়োজনীয়তা তাই অনেক কমেছে। রাষ্ট্রশক্তি এখন বিজ্ঞান বিরোধিতা করতে বিজ্ঞানীদের উপরই বেশি করে নির্ভর করছে। এসেছে প্যারাসাইকোলজিস্টের দল, যারা বিজ্ঞানের নামাবলি গায়ে দিয়ে বিজ্ঞানেরই বিরোধিতা করতে চায়। উদ্দেশ্য—বিজ্ঞানমনস্কতার ছোঁয়া থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখা।
সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি ঘোষণা করেছে, তারা পরীক্ষা করে দেখেছে শসোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়ে কুলাগিনা অতিপ্রাকৃত কখমরাত অধিকারী। ইতিমধ্যে কুলাগিনাকে নিয়ে ফিল্ম তোলা হয়েছে। নিজের দেশে এবং বিদেশে দূরদর্শনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের সামনে কুলাগিনাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবেই হাজির করা হয়েছে। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় কুলাগিনা সম্পর্কে বিজ্ঞান-আকাদেমির সিদ্ধান্তের কথা অতি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হওয়ায় ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের অলৌকিক বিরোধী বক্তব্যের ক্ষেত্রে বহু মানুষের মধ্যেই যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের যুক্তি রুশ সায়েন্স আকাদেমি কি আর মিথ্যে বলেছে? ওদের কাছে আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান আন্দোলনকারীরা তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ি না। ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রকাশিত ‘যুব সমীক্ষা’য় কুলাগিনাকে নিয়ে একটি বহু ছবি-সহ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনেও বিজ্ঞান আকাদেমির পরীক্ষা গ্রহণ ও সিদ্ধান্তের কথা লেখা ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ‘যুব সমীক্ষা’কে এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি আমাদের সমিতির কর্মপদ্ধতি। জানিয়েছি, আমাদের সমিতির একটি দল কুলাগিনার ঘটানো অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। এও জানিয়েছি, কুলাগিনার ঘটানো তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা লৌকিক উপায়েই আমি ঘটাতে সক্ষম। শেষ পংক্তিতে ছিল— আপনাদের তরফ থেকে সহযোগিতা না পেলে ধরে নিতে বাধ্য হবে—আপনারা সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং একই সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কালো দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। দূতাবাস আমাদের চিঠি পেয়েছে ফেব্রুয়ারি ‘৯০-এ। এখনও পর্যন্ত কোনও রকমের সাড়া না পেয়ে আমাদের মনে সেই সন্দেহটাই গভীরতা পাচ্ছে—সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতে বিজ্ঞানকেই কাজে লাগিয়েছে।
এই ধরনের উদাহরণ দেওয়া যায় ভূরি ভূরি। শুধু সোভিয়েত দেশেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশের রাষ্ট্রশক্তিই বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখতে বিজ্ঞানীদেরই কাজে লাগাচ্ছেন প্যারাসাইকোলজি বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে গবেষণাকে নানাভাবে উৎসাহিত করছেন। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়।
যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে বহু ধরনের প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে সেইসব রাষ্ট্রশক্তি, যারা সাধারণ মানুষের চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভয় পায়, যারা জানে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগতাড়িত মানুষগুলোকে ‘মহান মিথ্যে’র সাহায্যে অবহেলা শাসনে রাখা যাবে, শোষণ করা যাবে। পরিণতিতে ‘যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি’কে কাজে লাগাতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচেষ্ট হতে দেখছি।
এখন রাষ্ট্রশক্তিগুলি টিকে থাকার পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে।
যুক্তির বিরুদ্ধে বিপরীত যুক্তির আক্রমণ চালিয়ে
সরাসরি লড়াইয়ে নামার চেয়ে যুক্তিনির্ভর
কোনও আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া
কেড়ে নিতে আপাতদৃষ্টিতে সমধর্মী
যুক্তিনির্ভর সাজানো আন্দোলনকে
গতিশীল করাকে অনেক বেশি
কার্যকর মনে করছে।
তারই প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দিতে ‘যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি’কে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়া যুক্তভাবে প্রচারে নেমেছিল নিউক্লিয়ার বোমার বিরুদ্ধে।
ভারতবর্ষে অসমান বিকাশের ফলে কোনও অঞ্চলে পুরোহিততন্ত্র প্রবল বিক্রমে বিরাজ করছে, কোথাও পরাবিদ্যা সে জায়গা দখল করতে হাজির করেছে কম্পিউটার জ্যোতিষ, অ্যাস্ট্রোপামিস্ট, বিজ্ঞানসম্মতভাবে জ্যোতিষ চর্চার নানা প্রকরণ, আবার কোথাও যুক্তিবাদের সম্প্রসারণ ঠেকাতে মুখোশধারী যুক্তিবাদীদের পথে নামিয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তি মহান মিথ্যে হিসেবে এ সবের সঙ্গে আসরে নামিয়েছে। লটারি, জুয়া, টেলিভিশন স্ক্রিনে রামায়ণ, মহাভারত, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান।
বিভিন্ন যুগে ‘মহান মিথ্যে’ পাল্টায়, যুক্তিবাদ কখনওই
একটা স্তরে থাকতে পারে না। প্রতিটি স্তরের
যুক্তিবাদের পাশাপাশি ‘মহান মিথ্যে’
পাল্টায়, পাল্টায় কুসংস্কার।
আমাদের দেশে যুক্তবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করতেই কোনও কোনও বিদেশি রাষ্ট্রশক্তি এবং আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রশক্তির কাছে এ এক বিপদ সংকেত। কু-সংস্কার ও জাতপাতের বিশ্বাস যতদিন শোষিত মানুষগুলোর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে ততদিন শ্রেণিসংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগোতে পারবে না। শোষিত একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর একটি গোষ্ঠীর অবিশ্বাস ও ঘৃণাকে যতদিন বজায় রাখা যাবে, ততদিন প্রাণের মধ্যে শ্রেণিচেতনা, শ্রেণিসংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পাবে না।
শ্রেণিচেতনা বৃদ্ধি পেলে কুসংস্কার, জাতপাতের মতো বিষয়গুলো দূরে সরে যায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই শ্রেণিসংগ্রাম এবং শ্রেণিচেতনাই হিন্দু-মুসলমানদের একসঙ্গে লড়াইতে নামিয়ে ছিল। মাও সে তুং-এর ‘হোনান’ রিপোর্টেও দেখি শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষকরা নিজেরাই বাড়ির ‘থানের’ অধিষ্ঠিত কাঠের দেবমূর্তিগুলোকে অপ্রয়োজনীয় এবং কুসংস্কার প্রসূত জ্ঞান করে চ্যালা কাঠ করে জ্বালানি বানিয়েছিল।
আমাদের দেশে ‘যুক্তিবাদ’ এখন আন্দোলন গড়ার স্তরে। প্রতিরোধে স্বার্থান্বেষী মহল অতি সচেতন। ‘যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। মেকি আন্দোলন সৃষ্টি করতে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা, রাষ্ট্রশক্তি। বিদেশি সাহায্যে বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতায় শুরু হয়ে গেছে তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলন।
জনগণের মধ্যে যুক্তিবাদী চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একান্তভাবেই প্রয়োজন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার। এর জন্য প্রয়োজন অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ না পাওয়া তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মধ্যে হাজির হয়ে তাদেরই সঙ্গে আপনজনের মতো মিশে গিয়ে কুসংস্কার ও তার মূল কারণগুলো বিষয়ে সচেতন করা। প্রয়োজনে তাদের সামনে হাতে-কলমে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়গুলো হাজির করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই নিরক্ষর। আমাদের লেখা তাদের মধ্যে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজ সচেতন মানুষরা নিজেদের তৈরি করে নিয়ে তাদের কাছে আহরিত জ্ঞান বিতরণ করলে তবেই সাধারণ বঞ্চিত মানুষদের চেতনার বিকাশ সম্ভব, যুক্তিবাদী চিন্তাকে জনগণের আন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর জন্য চাই বহু সমাজ সচেতন কর্মী। কিছু কিছু মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে যতটুকু কাজ করছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল।
আমাদের সমিতি বহু সহযোগী ও সম-মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাহায্যে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে যাচ্ছে, মানুষের মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, সক্ষমও হচ্ছে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি কৃষক-শ্রমিক ঘরের নিরন্ন ছেলে-মেয়েরা কী অসাধারণ দক্ষতায় প্রাণঢালা আন্তরিকতায় মানুষের ঘুম ভাঙাতে গান বেঁধেছে, গাইছে, নাটক করছে, আলোচনাচক্রে অন্যদের বোঝাচ্ছে, হাতে-কলমে ঘটিয়ে দেখাচ্ছে অনেক বাবাজি-মাতাজিদের বুজরুকি। সাধারণ মানুষদের দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—যে কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা তারা দেবে। গ্রহণ করবে যে কোনও অবতার বা জ্যোতিষীদের চ্যালেঞ্জ। এদের প্রত্যেকটি আশ্বাস ও চ্যালেঞ্জকে মুল্য দিতে, রক্ষা করতে আমি ও আমাদের সমিতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা প্রয়োজনে প্রতিটি সহযোগী সংস্থার এই জাতীয় দায়-দায়িত্ব অতি আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করে থাকি। পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও সম-মনোভাবাপন্ন মানুষদের নিয়ে স্টাডি ক্লাসের ব্যবস্থা করি, নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানকে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও স্বচ্ছ করতে।
শুধু সহযোগী সংস্থার ক্ষেত্রেই নয়, যে ব্যক্তি বা সংস্থা আমাদের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করেছেন, তাঁরাও যখনই কোনও অলৌকিক বিষয়ক ব্যাখ্যা চেয়েছেন অথবা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন—আমরা সহযোগিতা করেছি।
আমরা জানি, তবু আমরা অনেকেরই দাবি মেটাতে পারছি না, অনেকেরই বিশাল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছি না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে যখনি কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়, সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসতে থাকে উৎসাহী, জিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছ থেকে। তাঁরা চান পত্র-পত্রিকাগুলোয় এই বিষয়ে আমার বা আমাদের মতামত যেন জানাই। বিশেষ করে যখন কোনও পত্র-পত্রিকায় আমাকে বা আমাদের সমিতিকে আক্রমণ চালিয়ে বা চ্যালেঞ্জ চানিয়ে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই আমায় এবং আমাদের সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল সর্বশ্রেণির মানুষ প্রত্যাশার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোন—আমি নিশ্চয়ই কিছু উত্তর দেব। সহৃদয় উৎসাহী পাঠক এবং বিজ্ঞানকর্মী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীরা আমার এবং আমাদের সমিতির উভয়ের প্রত্যাশায় পত্র-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য রাখেন। উত্তর প্রকাশের প্রত্যাশিত সময় পার হয়ে গেলে নিরাশ, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল মানুষগুলো আমাকে চিঠিও দেন। নীরবতার কারণ জানতে চান। জানি, চিঠি দেন না এমন আশাহত মানুষের সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি। বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে এই নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয়। মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তরে যা জানাই, এখানেও সমস্ত সহানুভূতিশীল শ্রদ্ধেয় প্রতিটি জিজ্ঞাসু পাঠকদের, মানুষদের তাই জানাচ্ছি। অতি স্পষ্টভাবেই জানাতে চাই, আমি জেনেছি, শুনেছি অথবা পড়েছি অথচ উত্তর দিইনি, এমন ঘটনা একটিও ঘটেনি। কিছু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সেগুলো প্রকাশ না করে ধারাবাহিকভাবে আশ্চর্যজনক নীরবতা পালন করে চলেছেন।
এমনকী এমন ঘটনাও বহুবার ঘটেছে, আমাদের বিরুদ্ধে
চ্যালেঞ্জ জানানো চিঠি যে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন,
তাঁরাই কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের উত্তর
প্রকাশ করার সামান্যতম নৈতিক
দায়িত্বটুকুও পালন করেননি।
সত্যতা বিচার করার সামান্যতম চেষ্টা না করে মিথ্যে খবর প্রকাশ করার প্রবণতা বহু পত্র-পত্রিকাতেই বিপজ্জনক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতাকে রোধ করার দায়িত্ব কিন্তু প্রতিটি সমাজ সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের, শুধুমাত্র আমাদের নয়।
আমরা যখন এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষিত নিরন্ন মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংস্কৃতি ও চেতনাকে তুলে আনতে চেষ্টা করছি, সমাজ সচেতন করে তুলতে চাইছি, ঠিক তখনই আমাদের সামনে এল বিদেশি সাহায্যের প্রলোভন। আমাদের স্পষ্টতই মনে হয়েছিল, সাহায্য পাওয়ার বিনিময়ে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে যুক্তিবাদী আন্দোলনের মৃত্যুবাণ। বিদেশি সংস্থারা যেমন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে, যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিকে নিয়োজিত করতে সাহায্যের ঝুলি হাতে ব্যক্তি ও সংস্থাকে ধরতে বেরিয়ে পড়েছে, তেমনই কিছু সংস্থার কর্ণধার ও কিছু ব্যক্তি বিদেশি সাহায্য শিকার করতে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে আমরা যে আমেরিকান সংস্থার সাহায্য ঠেলে দিয়েছি অবহেলে পরম ঘৃণায়, সে সাহায্য নিয়েই সগর্বে নিজেদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে চলেছে এক স্বঘোষিত যুক্তিবাদী সমাজসচেতন পত্রিকাগোষ্ঠী ও তাদের গুরু—বিদেশি প্রেমে আনন্দমুখর মহান যুক্তিবাদী নেতা। এই পত্রিকাগোষ্ঠী সোচ্চারে ঘোষণা করে, জেমস র্যাণ্ডি, মার্ক প্লামার ও তাঁদের ভারতীয় এজেণ্টদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে বিপ্লব আনবে। আমেরিকা থেকে যাঁরা বিপ্লব আমদানির কথা বুক ঠুকে ঘোষণা করেন, তাঁরা এক নিশ্বাসে আরও দুটি কথা ঘোষণা করে থাকেন—অবতার ও জ্যোতিষী বিরোধী ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জ ‘মহান’ এবং প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ ‘অশোভন’। বিচিত্র এঁদের ‘মহান’ যুক্তি। এঁদের এই স্ববিরোধিতা ও যুক্তিহীনতার পিছনে দুটি বিষয় কাজ করতে পারে। এক তীব্র ঈর্ষাকাতরতা। দুই, বিদেশি সাহায্যকারীরা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে যে যোগ্য ও অপরিহার্য মানুষদেরই বেছে নিয়েছেন, এই বিষয়ে তাঁরা যে সর্বোত্তম, এমনটা প্রমাণ করতে গিয়ে উচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়িয়েছে। এমনও হতে পারে, দুটো কারণই কাজ করছে।
এই মেকী আন্দোলনকারীরা দীর্ঘজীবী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার আয়াসসাধ্য ব্যাপার স্যাপারে আগ্রহী নন। এঁরা নিরাপদ দূরত্বে বসে মহানগর থেকে পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিজেদের পক্ষে হাওয়া তুলতে আগ্রহী। ওঁদের কাছে ‘আন্দোলন’, ‘সংগঠন’ ইত্যাদি শব্দগুলো বড় বেশি স্বার্থ-বিরোধী। তাই মূল যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে, একজনকে কিংবদন্তি পুরুষ করে তুলাতে প্রতিনিয়ত ব্যাপক ও নিবিড় প্রচার চালিয়েই যান। যাঁর পক্ষে এই প্রচার তিনি কিন্তু একদিনের জন্যেও সমাজ সচেতনতার প্রতি পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উচ্চারণ করেননি—ঈশ্বর, অবতার, জ্যোতিষী, অলৌকিক, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদির প্রতি সাধারণ মানুষের শোষিত মানুষের প্রবল অন্ধ-বিশ্বাসের কারণগুলো আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, পালিত হচ্ছে, পুষ্ট হচ্ছে শোষক শ্রেণি ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীদের স্বার্থে। শোষক শ্রেণি চায় শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী না করে দায়ী করুক নিজেদের ভাগ্যকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে এবং ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে।
ওই কিংবদন্তির নায়কও যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার আরামসাধ্য ব্যাপার-স্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। নিজের প্রয়াসকে নিয়োজিত রেখেছিলেন শুধুমাত্র বাবাজি মাতাজিদের চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যেই। সাধারণ মানুষেরা ওই অসাধারণ বিজ্ঞান পত্রিকা গোষ্ঠীর চোখে কেমন? তার একটা উদাহরণ পেশ করছি। ‘৮৯-তে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে সাত-আটটি বিজ্ঞান সংস্থা মিলে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন, শিরোনাম ছিল ‘বিজ্ঞান আন্দোলন কী? ও কেন?’ আমন্ত্রিত ছিলেন এই পত্রিকা গোষ্ঠী, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং আমাদের সমিতি। পত্রিকাগোষ্ঠীকে বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানাতে পর্যায়ক্রমে উঠলেন এক ডাক্তার ও এক ডক্টরেট। তাঁরা দর্শকদের বললেন—’বিজ্ঞান আন্দোলন কী? ও কেন?’ ও-সব নিয়ে আলোচনা এ সভায় অর্থহীন বলেই মনে করি। কারণ ও-সব ভারী ভারী কথা বললে আপনারা কিছুই বুঝবেন না। তার চেয়ে বরং আপনাদের কোনও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিন, উত্তর দিচ্ছি।’
এঁদের নাক উঁচু ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যে দর্শকরা অপমানবোধ করেছিলেন। আমরাও হতচকিত হয়েছিলাম, এমন চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন, নাকতোলা বক্তব্যে। ওঁরা তবে সাক্ষরতার সুযোগ না পাওয়া মানুষকে কী বলবেন? তাঁদের বাদ দিয়েই শুধু উচ্চকোটির মানুষকে নিয়েই কি ওঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ার স্বপ্ন দেখেন? সেদিন ওঁদের ধৃষ্টতার জবাব শ্রোতারাই দিয়ে দিয়েছিলেন তীব্র ধিক্কারে।
আবার আর এক ধরনের সদাসতর্ক বিজ্ঞান আন্দোলনের স্রোতও এদেশে লক্ষ্য করছি। যাঁরা অবতার বা জ্যোতিষীদের বুজরুকি ফাঁস করার নামে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হানতে নারাজ, তাদের ধারণায় এই পথ ‘হঠকারী’ পথ। এতে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। এঁদের চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ বিজ্ঞানীদের সব চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে সব চেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলন।
আমাদের সমিতির দৃষ্টিভঙ্গিতে সে কাজ সরকারের প্রশাসনের। গ্রামে গ্রামে টিউব-কল, বিদ্যুৎ, ফোন, দূরদর্শন ইত্যাদি বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়া যদি বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য হয়, তবে তো রাজীব গান্ধীকেই ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলনের সবচেয়ে বড় নেতা হিসেবে ওই বিজ্ঞান আন্দোলন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।
আমাদের চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ—
বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ার আন্দোলন, সাধারণ
মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ করার
আন্দোলন।
বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিজ্ঞান আন্দোলনের জন্য অর্থের প্রয়োজনের চেয়ে, অর্থের জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন করাটা বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।
মুখোশধারী যুক্তিবাদীদের ভিড় যত বাড়বে, সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের বিপদও ততই বাড়বে। ভারতীয় উপমহাদেশে কমিউনিজমের হাওয়া পৌনে এক শতাব্দী ধরে বইলেও, এই অঞ্চলে যুক্তিবাদী মানুষ আজও দুর্লভ। যুক্তবাদী বলে পরিচয় দিয়ে যাঁরা সমাজে বিচরণ করেন তাঁদের বেশির ভাগই রত্নধারী যুক্তিবাদী, তাবিজধারী যুক্তিবাদী, হিন্দু যুক্তিবাদী, মুসলমান যুক্তিবাদী, ব্রাহ্মণ যুক্তিবাদী, তফসিলী যুক্তিবাদী, বাঙালি যুক্তিবাদী, বিহারি যুক্তিবাদী, পারলৌকিক কর্মে মুণ্ডিত মস্তক যুক্তিবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা একই সঙ্গে বিজ্ঞানমেলা ও ধর্মসভা উদ্বোধন করেন, পুজো কমিটি ও বিজ্ঞান সংস্থার চেয়ারম্যানের চেয়ারটি কৃপা করে অলংকৃত করেন, জ্যোতিষ সভা ও বিজ্ঞান সভা দুয়েরই সমৃদ্ধি কামনা করে বাণী পাঠান। এরই সঙ্গে আর এক নতুন হুজুক—আধ্যাত্মিক জগতের রাজা-মহারাজাদের দিয়ে বিজ্ঞান সভার উদ্বোধন করানো। এইসব রাজা-মহারাজের দল ‘অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার কোনও বিরোধ নেই’ ইত্যাদি বলে শ্রোতাদের চিন্তাকে আরো বেশি বিভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ করে তুলছেন।
‘৮৮-র একটি ঘটনা। স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ‘জ্যোতিষ ‘বনাম বিজ্ঞান’ শীর্ষক আলোচনা সভায় গেছি। সেখানে আমার বক্তব্যের সূত্র ধরে এক স্বীকৃত মার্কসবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বললেন, ‘আমি প্রবীরবাবুর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। বস্তুবাদে বিশ্বাসী মানুষও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতেই পারেন।’
বছর দুয়েক আগে জনৈক প্রগতিশীল বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক একটি আড্ডায় বলেছিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেও যুক্তিবাদী হওয়া যায়।’
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতাকে বলতে শুনেছিলাম, ‘বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বা অধ্যাত্মবাদের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। বরং অধ্যাত্মবাদই পরম বিজ্ঞান।’
‘৮৩ সালে তফসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ডাইনিবিদ্যা ও ডাইনি বিশ্বাসের রূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এক আলোচনাচক্রে যোগ দেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণাগারের গবেষকবৃন্দ, নৃতাত্ত্বিক সমাজতত্ত্ববিদ ও বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এইসব সমাজ সচেতনতার দাবিদার ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেরই আলোচনায় যুক্তির পরিবর্তে একান্ত বিশ্বাসের কথাই উঠে এসেছিল। এঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী জানগুরুরাও। ডাইনিবিদ্যার অপকারিতা বিষয়ে ডাইনিদের সচেতন করতে নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বললেন কেউ। কারও বা ধারণা, এখনকার জানগুরুদের আগেকার দিনের জানগুরুদের মতো অতটা অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তবে জানগুরুদের ঠেকাতে তাদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
বুঝুন! আলোচকদের ধারণাটাই যদি এমনতর ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ হয়, তবে আদিবাসীরা রোগের ও মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডাইনিদের দোষী সাব্যস্ত করলে সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে কি?
এতক্ষণ যেসব মুখোশধারী যুক্তিবাদীদের, অস্বচ্ছ চিন্তার যুক্তিবাদীদের, ভ্রান্ত চিন্তার যুক্তিবাদীদের কথা বললাম, জানি না এঁদের কতজন অস্বচ্ছ চিন্তার শিকার, কতজন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর ঠিকা নিয়েছেন।
বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যেও চিন্তার স্ব-বিরোধিতা, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির অভাব, আদর্শহীনতা এবং নেতা সাজার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীরা সচেতন না হলে, যারা শোষিত শ্রেণির চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভীত, তারাই কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে মেকি আন্দোলনের পালে ঝড় তুলবে।
আপনি আমি আমরা যারা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে, বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, সেই আমরা যদি নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।
আমরা অর্থাৎ বিভিন্ন গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যারা যুক্তিবাদী আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে ব্রতী বা ইচ্ছুক, সেই আমরা যদি স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, গণসংগঠন ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করি কুসংস্কার বিরোধী আলোচনা, শিক্ষণ-শিবির, নাটক, মাইম, গান, পোস্টার ইত্যাদি যদি হাতে কলমে ঘটিয়ে দেখাই অলৌকিক বাবাদের সব কাণ্ডকারখানা, যদি স্পষ্ট ঘোষণা রাখি—আপনাদের এলাকার কোনও অলৌকিক বাবাজি-মাতাজিদের লৌকিক কৌশল জানতে চাইলে আমরা অবশ্যই জানাব। আপনার এলাকার কোনও অবতার বা জ্যোতিষী তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে চাইলে সে চ্যালেঞ্জ আমরা নেব—তবে নিশ্চিতভাবে দেখবেন আমরা স্থানীয় মানুষদের দীর্ঘদিনের অন্ধ বিশ্বাসকে নিশ্চয়ই নাড়া দিতে পেরেছি। কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যার প্রশ্নে, কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রয়োজনে অথবা আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোনও সহযোগিতার প্রশ্নে আমি ও আমাদের সমিতি আপনাদের পাশে আছি, থাকব। আসুন আমরা সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনের শরিক হই।
কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনে নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা নিজেরা নিশ্চয়ই আমাদের নিজেদের এলাকার মানুষদের নিয়ে বসতে পারি সপ্তাহে বা মাসে অন্তত একটি করে দিন। সাধারণ মানুষকে পাশাপাশি ডাকি না কেন দল-মত নির্বিশেষে আমাদের পাড়ার শিক্ষক, ছাত্র, অধ্যাপক, চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীদের। আলোচনায় বসার আগে সুযোগ থাকলে আলোচ্য বিষয় নিয়ে সাধ্যমতো পড়াশুনো করে নিলে প্রয়োজনে প্রশ্ন তুলে, অথবা নিজের পড়ে জানা মতকে সাধারণের সামনে তুলে ধরে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনাসভাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি। আর, একান্ত পড়ার সুযোগ না পেলে আলোচকদের কথা শুনে নিজেদের জ্ঞান বর্ধিত ও পরিমার্জিত করতে পারি। মনে কোনও প্রশ্ন হাজির হলে, নিশ্চয়ই আমরা তা হাজির করব। না জানা বিষয় জানার চেষ্টায় প্রশ্ন করা বিজ্ঞতার এবং না জেনে জানার ভান করা মূর্খতারই লক্ষণ। আলোচনার বিষয়ের তো অভাব নেই—যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান আন্দোলন, ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, আত্মা, জাতিস্মর, প্ল্যানচেট, ভর, বিশ্বাসে রোগমুক্তি, এমন কত বিষয়ই পাওয়া যাবে।
আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেই নিশ্চয়ই কুসংস্কার বিরোধী বুলেটিন, বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করতেই পারি, তা যে যত কৃশ কলেবরের বা হাতে লেখাই হোক না কেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা চেষ্টা করলে কিছু লিখতে পারি, আসুন না তাঁরা সাধারণের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে সাধ্য-মতো কলম ধরি সংস্কার মুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে। এই জাতীয় লেখার বিষয়ের তো শেষ নেই। শেষ কথা তো কোনওদিনই বলা হবে না। বা লেখা হবে না। যুক্তিবাদ এগুবে, প্রতিটি স্তরের যুক্তিবাদের পাশাপাশি ভাববাদী দর্শনও যুক্তিবাদকে রোখার স্বার্থে পাল্টাবে, এগোবে নতুন নতুন রূপে।
শত-সহস্র বছর ধরে আমরা ভাববাদী সাহিত্য, সংগীত, নাটক, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই বেড়ে উঠছি। সেই পরিমণ্ডলের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে চাই যুক্তবাদী মুক্ত-চিন্তার এক পরিমণ্ডল। এর জন্য সাহিত্য, সংগীত, নাটক ইত্যাদিতে চাই ভাববাদী চিন্তার বিরোধিতা, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার। এর জন্য চাই বেশি বেশি করে ভাববাদ বিরোধী বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হোক, রচিত হোক সংগীত, নাটক, শিল্প।
বহু সংস্থা ও ব্যক্তি এ-বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের সাধ্যমতো বিজ্ঞানমনস্ক বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন, যদিও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পক্ষে বর্তমানের এই সামগ্রিক প্রচেষ্টাও প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। তবু যুক্তিবাদী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে প্রচণ্ড রকমের আশাব্যঞ্জক। আশা রাখি, নতুন চেতনার পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে আরো বেশি বেশি করে মানুষ ও সংস্থা এগিয়ে আসবেন এবং তাঁদের সাধ্যমত নিজেদের ভূমিকা পালন করবেন।
আমাদের সমিতি এবং আমি মনে করি, শুধুমাত্র কোনও সংস্থার ওপর বা সেই সংস্থার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলে তা শুধুমাত্র স্বপ্নই থেকে যাবে। কারণ, ভাববাদী দর্শনের ওপর আক্রমণ যখন তীব্রতর হবে তখন শোষক শ্রেণি স্বার্থ বা রাষ্ট্রশক্তি কঠিন প্রত্যাঘাত হানবে। এরা আন্দোলনের মূল উৎপাটন করতে নেতৃত্বদানকারী সংস্থা ও ব্যক্তিদেরই চিহ্নিত করে তাদের উপর সর্বপ্রকার নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাবে। এই জাতীয় আক্রমণে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি শেষ হয়ে গেলেই যাতে আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে না যায় তারই জন্য প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংস্থার যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী হওয়া একান্তই প্রয়োজন। এমনটি হতে পারলে শোষক শ্রেণি ও রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্বকে আঘাত হেনে আন্দোলন শেষ করে দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য।
এই একটি মাত্র কারণে আমরা সংগঠনের তরফ থেকে কোনও মুখপত্র প্রকাশ থেকে বিরত ছিলাম এতদিন। জানতাম, আমরা প্রথম থেকেই আমাদের মুখপত্র ‘যুক্তিবাদী’ প্রকাশ করতে থাকলে আমাদের সহযোগী, সহযোদ্ধা বহু সংগঠন ও শাখা সংগঠন আমাদের ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আমরা বরং বিভিন্ন সংগঠন ও সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করেছি পত্র-পত্রিকা ও বই প্রকাশে। আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।
আমাদের সমিতি যখন সামগ্রিকভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন সংস্থাকে নানা ধরনের কার্যক্রমে, অনুসন্ধানে, পরিসংখ্যান গ্রহণে ও গবেষণার কাজে, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে, নাটক করতে সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করে চলেছে, ঠিক তখনই একটি কুসংস্কার বিরোধী গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদকারী জনৈক বিজ্ঞান লেখক তাঁর বইটির ভূমিকায় সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, তাঁর বইয়ের (অনুবাদ কমিটির) জনপ্রিয়তায় অনেকেই নাকি স্রেফ কিছু কামানোর ধান্দায় অথবা ব্যক্তি প্রচারের জন্য এই জাতীয় বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে মন দিয়েছেন।
অনুবাদকের এই ধরনের রুচিহীন মন্তব্যে বহু সংস্থা ও ব্যক্তি ব্যথিত হয়েছেন—আমরা জানি, আমাদের সমিতিও একইভাবে ব্যথিত। তাঁর এই জাতীয় অশালীন মন্তব্যকে উপযুক্ত ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। এই অনুবাদক যদি মনে করে থাকেন, কুসংস্কার বিরোধী বই লেখার ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি এবং তাঁর ক্ষুদ্র পত্রিকাগোষ্ঠীই একচেটিয়া ‘ঠিকা’ নিয়ে রেখেছেন তবে বলতেই হয়, তিনি ভাববাদী পরিমণ্ডল বজায় রাখার ক্রীড়নক হিসেবে শোষক শ্রেণি ও রাষ্ট্রক্ষমতারই সহায়তা করছেন। অনুবাদকের কাছে আমাদের একটি বিনীত জিজ্ঞাসা- তিনি যে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন, সেই মূল গ্রন্থটি অনুবাদের বহু বছর আগে থেকেই যুক্তিবাদী নির্ভর দর্শন, রচনা, শ্লোক, গ্রন্থ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেইসব রচনার জনপ্রিয়তার কারণেই কি মূল গ্রন্থের লেখক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন বলে অনুবাদক একাস্তভাবে বিশ্বাস করেন? বিনীতভাবে আর একটি কথা নিবেদন করি—এই লেখক ওই অনুবাদকের দ্বারা গ্রন্থটি অনুবাদের বহু আগে থেকেই বাংলা ভাষার এক সময়কার জনপ্রিয়তম সাপ্তাহিক ‘পরিবর্তন’ পত্রিকায় ‘লৌকিক-অলৌকিক’ শিরোনামে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জের ‘প্লাস পয়েণ্টকে’ কিছু অক্ষম ঈর্ষাকাতররা ‘ব্যক্তি প্রচার’ অশোভন ইত্যাদি ভাষায় ভূষিত করে নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট।
আমরা মনে করি, একতরফাভাবে যুক্তিবাদী আলোচনায় সাধারণ মানুষের ওপর যতটা প্রভাব ফেলা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি প্রভাব ফেলা যায় জ্যোতিষী, অবতার, অলৌকিক ক্ষমতাধর ও ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তাদের মুখোমুখি হয়ে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে পারলে। আমরা তাই বার বার জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হয়েছি বেতারে, জ্যোতিষ সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে, আমরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে হাজির হয়েছি আলোচনায়, আমাদের সমিতির আয়োজিত বিতর্কসভায় ধর্মের পক্ষে আমন্ত্রণ করে এনেছি তাবড় ধর্মবেত্তাদের, আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে শ্রোতাদের সামনে আনতে পেরেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রথম শ্রেণির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের। আমরা প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতাবান ও জ্যোতিষীদেরও মুখোমুখি হয়েই তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে চাই। এ-পথে তাঁরা কিছুতেই এগুতে চাইবেন না, যাঁদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আছে, যাঁদের অনেক জায়গায় হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিজেদের খামতিকে আড়াল করতে তাই গোয়েবলেসর কায়দায় প্রচারে নেমে পড়েন অক্ষমরা। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর পাগল মেহের আলির মতোই রেকর্ড বাজিয়েই চলেন—’চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জ সব ফালতু হ্যায়’, বলে এক নাগাড়ে।
সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার দায়-দায়িত্ব শুধুমাত্র যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী বা বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের নয়। এগিয়ে আসতে হবে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের দৃঢ় প্রত্যয়ে বুঝে নিতে হবে সত্যিই তাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসারে কী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সাধারণ মানুষদের মধ্যে, অক্ষরজ্ঞানের সুযোগলাভে বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা গড়ে তুলতে কী পথনির্দেশ দিতে পেরেছেন? শিক্ষক-অধ্যাপক, যাঁদের হাতে রয়েছে শিক্ষিত করে তোলার ভার, তাঁদের ওপর স্বভাবতই আমাদের কিছুটা বাড়তি প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক যে, তাঁর ছাত্রদের অন্ধ-বিশ্বাস, ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূর করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। শিক্ষা দেওয়ার অর্থ শুধু বইয়ের পড়া বোঝানো নয়, কুসংস্কার দূর করাও শিক্ষা প্রসারেরই অঙ্গ। আমরা যারা আজ শিক্ষায় ও কর্মজীবনে কিছুটা অন্তত প্রতিষ্ঠিত, তাদের এ কথা মনে রাখা একান্তই প্রয়োজনীয় যে, আমাদের দেশের সংখ্যাগুরু শোষিত শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদের করের টাকায় গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি। সেই ঋণের কিছুটাও কি আমরা শোষিত মানুষদের শোধ দেওয়ার চেষ্টা করব না? সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাও কি আমরা করব না?
আমাদের দেশে কিছু নামী-দামি বিজ্ঞান সংস্থা রয়েছে—ছোট ছোট অসংখ্য বিজ্ঞান সংস্থা, যুক্তিবাদী সংস্থা ও অসংখ্য মানুষ ওইসব জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোর দিকে সঠিক পথনির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। জ্যেষ্ঠদের পথনির্দেশ যদি ভুল পথে বা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হয় তবে কনিষ্ঠদের এবং সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্তির পথে পা বাড়ানোর সম্ভাবনাও থেকে যায়। জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোর সদস্যদের উচিত সংস্থার নেতৃত্ব এমন হাতে ন্যস্ত করা, যাঁরা কথায় ও কাজে বিপরীত মেরুতে বিচরণ করেন না।
‘৮৭-তে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছাব্বিশটি বিজ্ঞান সংগঠন একসঙ্গে মাসাধিককালব্যাপী সারা ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠার আয়োজন করেছিল। দেশের পাঁচটি ভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচটি আঞ্চলিক জাঠা মোট প্রায় পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিল। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে, বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে যে সব বিষয় জাঠা বেছে নিয়েছিল সেগুলো হলো: স্বনির্ভরতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্র, বিজ্ঞান ও ভারতবর্ষ, স্বাস্থ্য ও ঔষধ, পরিবেশ দূষণ, জল, গৃহ, শিল্পক্ষেত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শাস্তি।
না, মানুষের কুসংস্কার বিষয়ের কোনও স্থান ছিল না জাঠার বিষয়গুলোর মধ্যে। বিপুল অর্থ বায়ের এই জন-বিজ্ঞান জাঠা তাদের কাছে এগিয়ে আসা শোষিত অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে বিজ্ঞানমনস্ক করার চেষ্টা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু জায়গায় অবতারদের কিছু কিছু কৌশল সাধারণ মানুষদের কাছে ফাঁস করার অনুষ্ঠান হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো হয়েছিল নেহাৎই হালকা চালে, সাধারণ মানুষকে ম্যাজিক দেখানোর মতো করে, অবসর বিনোদনের অনুষ্ঠানের মতো করে। পশ্চিমবঙ্গে এই জাঠা ছিল ধর্ম ও জ্যোতিষ বিশ্বাসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে। ২ অক্টোবর মালদায় জাঠা উদ্বোধন করলেন এমন এক বিজ্ঞানী যাঁর নাম আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখেছি ধর্মানুষ্ঠান, ভাগবতপাঠের আসর, অবতারের জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে। ৭ অক্টোবর কলকাতার টালাপার্কে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-জাঠার এক অনুষ্ঠানে একটি পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ‘শক্তি’ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই বললেন, ‘যবে থেকে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি—।’ বাক্যটা শেষ হবার আগেই সভার গুঞ্জনে সচেতন হয়ে উঠলেন। বক্তব্য পাল্টে বললেন,—‘অবশ্য আমরা বিবর্তনবাদে পড়েছি কেমন করে মানুষ এল।’ জাঠার উত্তর কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি দাপটে বিজ্ঞান সভার পরিচালনা করলেন, দু হাতের আঙুলে গোটা চার-পাঁচেক গ্রহরত্নের আংটি ধারণ করে।
এমন দ্বিচারিতার উদাহরণ এখানে শেষ নয়। এবার আপনাদের যাঁর কথা বলছি, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত বামবুদ্ধিজীবী লেখক। বস্তুবাদ প্রসঙ্গ-টসঙ্গ নিয়ে অনেক বইও লিখেছেন। এই বুদ্ধিজীবী ‘জন-বিজ্ঞান’ আন্দোলনের নেতাদের আমন্ত্রণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোচ্চারে জানালেন, বিজ্ঞান আন্দোলনের নামে ধর্মকে কোনও আঘাত নয়।
মাস কয়েক পরে তিনিই আবার ‘গণ-বিজ্ঞান’ মঞ্চে উঠে ঘোষণা করলেন, সাধারণের কাছে ধর্মের বিজ্ঞান-মনস্কতা বিরোধিতা’র স্বরূপকে তুলে ধরতে হবে, চিনিয়ে দিতে হবে, আঘাত হানতে হবে।
পরজীবী এইসব বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিবাদী আন্দোলনের
পক্ষে নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বিশাল বাধা হয়ে উঠতে
পারেন। কারণ পরিচিত শত্রুর বিরুদ্ধে
লড়াই করা সহজ, অপরিচিত
শত্রু চিরকালই ভয়াবহ।
অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার ও জ্যোতিষীদের বিরোধিতার স্বরূপ আমাদের জানা, তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু এইসব ভণ্ড যুক্তিবাদীদের মুখোশের আড়াল সরাতে না পারলে তাদের অজ্ঞাত শত্রুরা, গোপন আঘাত আমাদের আন্দোলনকে বহুগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
‘৮৯-এ পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমি এবং আমাদের সমিতি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। অধিবেশনে আমাদের সমিতির বক্তব্য ছিল-বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ দূষণ, জল সমস্যা, বাসগৃহ ইত্যাদি সমস্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও আমাদের সমিতি মনে করে এর সঙ্গে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করা উচিত। বিজ্ঞান আন্দোলনে যদি বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ার আন্দোলনের, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের স্থান না থাকে, তবে সেটা আর যাই হোক, বিজ্ঞান আন্দোলন নয়। পিপলস্ সায়েন্স কংগ্রেস আন্দোলনের বিষয় হিসেবে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’কে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু যুক্তিবাদী চেতনা গড়ার আন্দোলনকে পাশে সরিয়ে রেখে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা গড়ার আন্দোলন, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মতোই বাতুলতা। ‘কুসংস্কার মুক্তি’ এবং ‘বিজ্ঞান-মনস্ক চেতনা’কে স্থান না দিয়ে আপনার যদি আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান, তবে সেটা হবে মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞান আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান আন্দোলন।
আমাদের বক্তব্যেরই জের টেনে বক্তব্য রাখলেন, কেরলের ‘শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ’-এর প্রতিনিধি। কেরল শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরিষদ কাগজে-কলমে ভারতবর্ষের বৃহত্তম বিজ্ঞান সংগঠন। তাদের প্রতিনিধি সোচ্চারে জানালেন—আমরা আপনাদের সমিতির কর্মধারা সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি। আমাদের পক্ষে এক্ষুনি কুসংস্কার বিরোধী কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করা অসম্ভব। কারণ এর দ্বারা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আমাদের পক্ষে কারও ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করার কথা অচিন্ত্যনীয়। আমাদের পরিষদকে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান সব ধর্মের সভ্যদের নিয়েই চলতে হয় এবং হবে।
পরিষদের প্রতিনিধি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলনের নামে অনেক কিছু করলেও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার বিষয়টা, সাধারণ মানুষের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টা সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতে চান।
বিজ্ঞান আন্দোলনকে
ঘোলা করে অনেক স্বার্থন্বেষী
ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন। এইসব
স্বার্থান্বেষী বহুরূপীদের চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব
বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মী এবং
সমাজ সচেতন সংস্থা ও মানুষদেরই শক্ত হাতে
পালন করতে হবে। কারণ এইসব বহুরূপীরা
অবতার ও জ্যোতিষীদের চেয়েও
অনেক বেশি বিপজ্জনক।
আন্দোলন গড়ার স্বার্থে, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে আমাদের অনেক বেশি সৎ, সতর্ক, আপসহীন এবং নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে—এর কোনও বিকল্প নেই।
আজ হাজারে হাজারে দামাল ছেলে-মেয়েরা শহুরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন অনেক তথাকথিত অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। ফাঁস করছেন অলৌকিক-বাবাদের বুজরুকি। এইসব অলৌকিক বিরোধী প্রদর্শনীগুলো ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শিরোনামে আমাদের সমিতি, সহযোদ্ধা সহযোগী সংস্থাগুলো এবং খাতায় কলমে সহযোগী না হলেও সহমত পোষণকারী বহু সংস্থা পরিবেশন করে থাকেন। ‘অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক’ শিরোনামেও কিছু কিছু সংগঠন কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করে থাকে। কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ‘অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক’ স্লোগান থেকে আমাদের বিরত থাকতেই হবে। ‘ভূতে ধরা’, ‘ঈশ্বরে ভয়’, ‘বিশ্বাসে রোগ আরোগ্য’, ‘সম্মোহন’ ইত্যাদি কি ম্যাজিক? অলৌকিক সব কিছুর ব্যাখ্যা কি বাস্তবিকই শুধুমাত্র ম্যাজিকের সাহায্যেই দেওয়া যায়? কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী যদি এমনটা ভেবে থাকেন তবে সেটা তাঁর জানার অসম্পূর্ণতা।
আমার সম্পর্কে এক দিদি প্রাইভেট বাসকে বলেন, ‘পাবলিক বাস’। তাঁকে প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর নিয়ে অনেক বোঝানোর পরও দেখেছি, তিনি নিজের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করেননি। কারণটা দিদির চোখে ছিল এই—ভুল সংশোধন করা মানে ছোট ভাইয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। তাঁর এই মিথ্যে অহমিকা বোধ এখনও তাঁকে ভুল বলিয়েই চলেছে।
এই ঘটনাটা বলার কারণ, ‘আমাদের ভয় হয়, আমার সেই দিদিটির মতো এঁরাও না অহংবোধে প্রতিনিয়ত ভুল করে যেতেই থাকেন। ভয় হয়, কারণ বিজ্ঞানকর্মীদের এমন মারাত্মক ভুলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হবেন। আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শিরোনামে অলৌকিক বিরোধী আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী এ শিক্ষাচক্র পরিচালনা করি। শিরোনামেই বক্তব্য স্পষ্ট। প্রতিটি আপাত অলৌকিকই বাস্তবে লৌকিক অর্থাৎ আপাত-অলৌকিকের পিছনে কোনও কৌশল থাকতে পারে, অথবা থাকতে পারে শরীর ধর্মের কোনও বৈশিষ্ট্য।
পশ্চিমবাংলার একটি নামী বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত এক গণ জাদুকরের মতে অবতার ও জ্যোতিষীদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ নাকি নেহাৎই ‘সস্তা চমক’। আমাদের নাকি চ্যালেঞ্জের ‘নেশা’ পেয়ে বসেছে।
ওই গণ-জাদুকরের প্রতি আমার ও আমাদের সমিতির একটিই জিজ্ঞাসা, আপনি যখন কুসংস্কার বিরোধী কোনও অনুষ্ঠানে সোচ্চারে ঘোষণা করতে থাকেন, ‘অলৌকিক বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, নেই, থাকবেও না তখন যদি কোনও বে-রসিক ব্যক্তি আপনারই সভায় বুক ঠুকে ঘোষণা করেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং প্রমাণ দিতে প্রস্তুত, তখন হে মহান আন্দোলনের নেতা আপনি কী করবেন? চ্যালেঞ্জের মতো ‘সস্তা চমক’ ও ‘অশোভন’ ব্যাপার থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন?
একটি অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হচ্ছি,
‘অক্ষম ও ঈর্ষাকাতর দের কাছে ‘চ্যালেঞ্জ’কে ‘অশোভন’
বলে প্রচার চালানোই অক্ষমতাকে আড়াল করার শ্রেষ্ঠ
পন্থা বলে বিবেচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।
চ্যালেঞ্জ আমাদের সমিতির কর্মধারার বিভিন্ন পর্যায়ের একটি পর্যায় মাত্র। ‘চ্যালেঞ্জ’ অক্ষমদের কাছে ‘সস্তা চমক’ অবশ্যই, তবে আমাদের কাছে আন্দোলনের ‘হাতিয়ার’। ‘চ্যালেঞ্জ’কে যে সব ধান্দাবাজরা ‘নেশা’ বলে প্রচার করতে চান, তাঁদের উদ্দেশে জানাই—সাধারণ মানুষকে অবতার ও জ্যোতিষীদের ‘নেশা’ মুক্ত করতেই আমাদের চ্যালেঞ্জ। যতদিন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতার ও জ্যোতিষীদের ‘নেশা’ থাকবে, ততদিন ‘নেশা’ কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জের নেশাও থাকবে।
তাঁদের উদ্দেশে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁদের প্রতিটি চিঠি, প্রতিটি যোগাযোগ, প্রতিটি উষ্ণ অভিনন্দন, প্রতিটি গঠনমূলক সমালোচনা, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি সহযোগিতা আমাকে এবং আমাদের সমিতিকে প্রেরণা দিয়েছে, সঠিকপথে এগোতে সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, গতিশীল রেখেছে। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রতিবেশী বাংলাদেশের লড়াকু সাচ্চা যুক্তিবাদী মানুষদের উদ্দেশে যাঁদের লড়াইয়ের অদম্য শক্তি, যাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাকে দিয়েছে, প্রেরণার চেয়েও বেশি কিছু। তবুও এর পরও অকৃতজ্ঞের মতো যাঁদের কাছ থেকে শুধু নিয়েইছি, দিতে পারিনি চিঠির উত্তরটুকুও, তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। পত্র লেখক-লেখিকাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, চিঠির সঙ্গে অনুগ্রহ করে একটি জবাবি খামও পাঠাবেন। এমন কিছু চিঠির উত্তর দিতে পারিনি—যার উত্তরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল, যা চিঠির স্বল্প পরিসরে সম্ভব ছিল না। বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এবং পরবর্তী পশুগুলোতে তাঁদের সকলের জিজ্ঞাসা নিয়েই আলোচনা করেছি এবং করব।
আমার সংগ্রামের সাথী, প্রেরণার উৎস প্রত্যেককে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।
প্রবীর ঘোষ
দেবী কমপ্লেক্স
ব্লক ‘সি’, ফ্ল্যাট-১০৪
কলকাতা ৭০০ ০৭৪