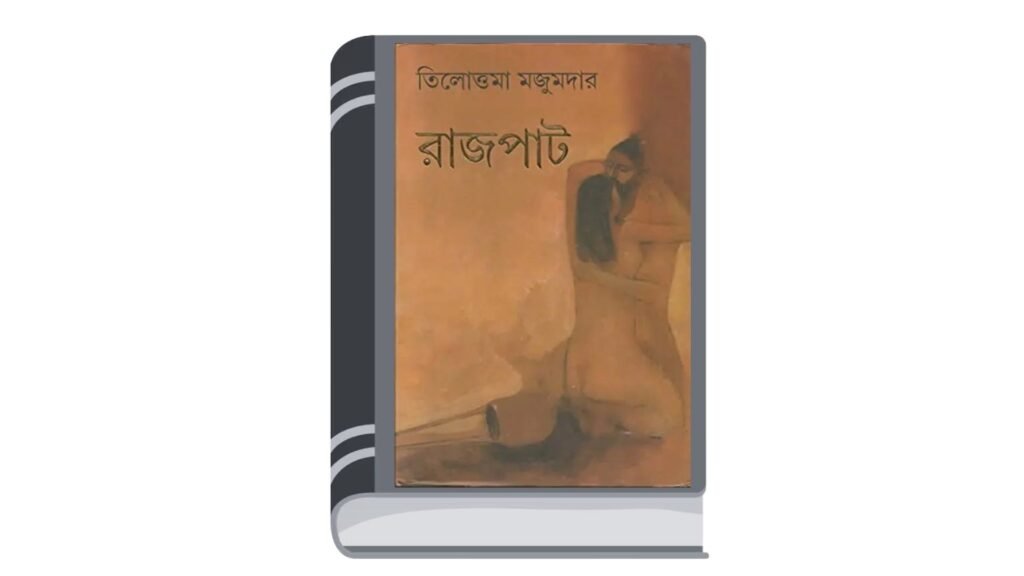রাজপাট – ২৯
২৯
কিংবা এই জীবনেরে একবার ভালোবেসে দেখি!–
পৃথিবীর পথে নয়, এইখানে—এইখানে ব’সে,—
মানুষ চেয়েছে কিবা? পেয়েছে কি? – কিছু পেয়েছে কি!—
হয়তো পায়নি কিছু, যা পেয়েছে, তা-ও গেছে খ’সে
অবহেলা ক’রে ক’রে, কিংবা তার নক্ষত্রের দোষে;—
নির্বাচনের আর দেরি নেই। অন্তত এক-দেড় বছর আগে থেকে তার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে যে-কোনও দল। যদিও সেই প্রস্তুতিকে আপাতভাবে কর্মতৎপরতা বলেই মনে হয়। নির্বাচনের রঙিন স্বপ্নদাগ সেইসব কাজে লেগে থাকে না। কিংবা এত মিহি, মসৃণ, সূক্ষ্ম সেই রং, চোখ অস্বীকার করতে না চাইলেও স্বীকার করার সাহস হয় না সাধারণ মানুষের।
অবশ্য একথা বললেও ভুল হয় না যে, যে-কোনও রাজনৈতিক দলের সকল কর্মসূচিই নির্বাচন-অভিমুখী। বিরাশিতে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়েছিল বিধানসভায়। বহরমপুরের আসন তখন আর এস পি-র দখলে গিয়েছিল। অবশ্য সাতাত্তরেই কংগ্রেসকে হটিয়ে বিধানসভার আসন দখল করেছিল আরএসপি। সেইসময় আর এস পি-র জয়কে সি পি আই এম প্রায় নিজের জয় বলেই ধরে নিয়েছিল। সকল বামপন্থী দলই তখন পরস্পরের জয়কে অভিনন্দিত করেছে সম্ভবত। বামফ্রন্ট সরকার গড়ে তোলার সেই শুভ এবং ঐতিহাসিক মুহূর্ত—তখন মন্ত্ৰ একটাই—মিলেমিশে করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। মিলেমিশে চলা, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দপ্তর ভাগাভাগি এবং ন্যায়-নীতি-ভালবাসার সমন্বয়ে সোনালি সেই দিন। গলাগলির দিন। কিন্তু প্রায় এক দশকে সেই অবস্থান থেকে তারা সরে এসেছে। কারণ এতদিনে বোঝা গেছে, শরিক দলের জয় কেবলমাত্র চূড়ান্ত আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত বহু আঞ্চলিক ক্ষমতা হাতে পাওয়া যায় না। এমনকী বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও পাওয়া যায় না নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। বরং সমর্থন হারানোর ভয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদলের নেতৃত্বকেও চুপ করিয়ে রাখে। স্বাভাবিকভাবেই এলাকার সি পি আই এম নেতারা এবার আর এস পি-র হাত থেকে ক্ষমতা সরাসরি নিজের হাতে নিতে চাইছেন।
নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অনেক ভেবে সিদ্ধার্থ অনুভব করছে, কাজটা সহজ নয়। কারণ এই এলাকায় আর এস পি-র নিখিলেশ চৌধুরী যদি প্রথম শক্তি হয়ে থাকেন, তা হলে দ্বিতীয় শক্তি অবশ্যই রাসুদা বা মিহির রক্ষিত নন, সেই দ্বিতীয় শক্তি হলেন পরমেশ্বর সাধুখাঁর পরিবার এবং অধ্যাপক আসাদুর রহমান। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
বিশেষত সাধুখাঁ পরিবার। তাঁরা শুধু বহরমপুরেই নন, ফারাক্কা, সুতি, জঙ্গিপুর, লালগোলা থেকে শুরু করে বেলডাঙা, নওদা, বড়ঞা, কেতুগ্রাম, হরিহরপাড়া, ডোমকল—সর্বত্র পরিচিত নাম। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন এই পরিবারের মানুষগুলি। মুর্শিদাবাদে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যুগের সদস্য অনন্ত ভট্টাচার্য ও সনৎ রাহা যখন কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন তখন এই পরিবারের শিবেশ্বর সাধুখাঁ ছিলেন নেতৃস্থানীয়। সর্বজনশ্রদ্ধেয় পরোপকারী হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি আগাগোড়া রক্ষিত ছিল। শিবেশ্বরের দুই ছেলে পরমেশ্বর ও দেবেশ্বর আজও কংগ্রেসকে আঁকড়ে আছেন। এই জেলায় কংগ্রেসের যা-কিছু শক্তি, তার জন্য পরমেশ্বর এবং দেবেশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। শিবেশ্বরের মতোই তাঁরাও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাঁদের ভাবমূর্তি। পরমেশ্বর উকিল। দেবেশ্বর ডাক্তার। শিবেশ্বরও চিকিৎসক ছিলেন। এবং বংশানুক্রমিকভাবে লক্ষ্মী তাঁদের ঘরে সরস্বতীর সঙ্গে বাঁধা আছেন। ইদানীং লোকে বলে সাধুখাঁরা বহরমপুরের নেহরু পরিবার। কারণ তাঁদের ঘরের বধূরাও কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠেছেন। আর এই পরিবারের ওপর নির্ভর করতে না পারলে যেন এই জেলায় কংগ্রেস অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে।
উনিশশো একুশ সালে বহরমপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটি গড়ে উঠেছিল। ব্রজভূষণ গুপ্ত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের কর্ণধার। শিবেশ্বর সাধুখাঁকে বলা যেতে পারে ব্রজভূষণ গুপ্তের অনুগামী এবং শিষ্য।
কংগ্রেসের জেলা কমিটি তৈরি হওয়ার সময় শিবেশ্বর ছিলেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র। ব্রজভূষণ গুপ্তরই প্রতিষ্ঠিত কর্মকুটিরের প্রথম কয়েকজন তরুণ কর্মীর মধ্যে ছিলেন শিবেশ্বর। সেইসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পুড়িয়ে ফেলার একটা হাওয়া উঠেছিল। কিন্তু শিবেশ্বর সেই উন্মাদনার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে থাকার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই। তাঁর চিকিৎসক পেশা তাঁকে পরবর্তীকালে সাহায্য করেছিল। তরুণ বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে না পারলে, তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে না পারলে, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব সফল হয় না। এমনকী তাঁর এই ধারণা ছিল যে, ব্রজভূষণ গুপ্তর দারুণ জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল তাঁর পেশার কারণেই। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমিদারি শাসনের বিরুদ্ধে বেলডাঙার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গরিব কৃষকদের পক্ষে তিনি আইনজীবী হিসেবে সওয়াল করে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে বিপুল শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছিলেন তা তাঁকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের নিকটে পৌঁছে দিয়েছিল। বিভিন্ন আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসকে একটি গণচরিত্র দিতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্রজভূষণ গুপ্ত
মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল প্রতিষ্ঠার প্রায় সূচনাকাল থেকেই। শিবেশ্বর সর্বান্তঃকরণে সংগঠনের কাজে ব্রজভূষণ গুপ্তকে সাহায্য করেছিলেন। সমস্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থাকা কংগ্রেসের এই নেতা সিদ্ধার্থর কাছে আদর্শ নেতৃত্বের পথিকৃৎ। শিবেশ্বর সাধুখাঁ যাঁকে অন্তর দিয়ে মান্য করেছিলেন, তাঁকে মনে মনে প্ৰিয় নেতার স্থান নিঃসংকোচে দিয়েছিল সিদ্ধার্থ। কিন্তু শিবেশ্বরকেও সে দিয়েছে প্রায় একই স্থান। পৃথক দলীয় মতবাদ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। সুযোগ্য নেতৃত্বের কিছু লক্ষণ আছে বলে সে বিশ্বাস করে। সেই লক্ষণগুলির প্রতি সে সশ্রদ্ধ।
শিবেশ্বরের লেখা কিছু প্রবন্ধ ও ছেলেদের উদ্দেশে লেখা কিছু চিঠিপত্র সমেত একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল কয়েক বছর আগে। সেই বই শিবেশ্বরের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিচয় বহন করে। শিবেশ্বরের বিভিন্ন নীতি সিদ্ধার্থ নিজেরও নীতি করে নিয়েছে। নিতে পেরেছে এ কারণে যে তার নিজের ভাবনার সঙ্গে শিবেশ্বরের ভাবনার মিল পেয়েছে সে। এবং সে জানে, কোনও ভাবনা, কোনও নীতিই মানুষের কাছে ততক্ষণ গ্রাহ্য হয় না যতক্ষণ সে নিজের ভাবনার প্রতি তার সমর্থন না পায়।
সে বিশ্বাস করে যে, মানুষের সঙ্গে একেবারে ব্যক্তিগত সম্পর্কই নেতৃত্বকে আদর্শ জায়গা দিতে পারে। সেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের মুখোমুখি সম্পর্ক হবে তার কোনও মানে নেই। কোনও সাধারণ স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। মানুষকে বুঝতে দিতে হয় যে, কোনও নির্দিষ্ট দাবি বা স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। এই দাবি ব্যক্তিগত হতে পারে, আবার সমষ্টিগতও। অনেক সময় কোনও ব্যক্তিগত দাবিকে সমষ্টিগত করে তুলতে হয়। হরিহরপাড়ার এক নগণ্য মানুষ হিসেবে ময়না বৈষ্ণবী যে-দাবি তুলেছিল, যে-প্রতিবাদ সে রটনা করেছিল ঘরে ঘরে, তাকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিয়েছিল তারা। ময়না বৈষ্ণবীর করুণ ও বীভৎস মৃত্যু সেই আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাপক রূপ দেয়।
সিদ্ধার্থ ময়না বৈষ্ণবীর জন্য কষ্ট পায়। ময়না বৈষ্ণবী তার কাঁধের ক্ষতচিহ্ন হয়ে আজীবন জড়িয়ে থাকবে। রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে কোনও একটি নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তার চলে না। কোনও সমস্যার সমাধান না হতেই অন্য এক সমস্যার নির্বাপনে ছুটে যেতে তার হতাশ লাগে। তবু, তেমনই তাকে করতে হয়। তাকে এবং তাদের মতো প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীকে। অথচ এমনও হতে পারত যে, তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা সমস্যা মেটাবার চেষ্টা করছে! ছোট ছোট ক্ষেত্রে তা হয়। কিন্তু বড় ক্ষেত্রে তা হয় না। এমনকী একই বিষয়, দু’রকমভাবে গুরুত্ব পেতে পারে। হতে পারে ছোট বা বড়। যদি কোনও একটি পাড়ায় জল না আসে, তবে তার মতো কেউ পুরসভায় কথা বলে সমস্যা বিতাড়নের ভার নিতে পারে। কিন্তু যদি সারা শহরে জল বন্ধ হয়, তখন একটি গণআন্দোলন গড়ে উঠবে এবং গোটা সমস্যাটি হয়ে উঠবে বৃহৎ। তখন তারা সবাই সমস্যার মোকাবিলা করতে ছুটবে। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার পর হরিহরপাড়ার সাধারণ মানুষ কারও কোনও নেতৃত্ব ছাড়াই পুলিশের প্রতি যেভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করেছে— তার কোনও তুলনা নেই। এই হল সাধারণ মানুষের গণ-নেতৃত্ব। কখনও কখনও তার উন্মেষ হয়। এই মানসিকতারই ব্যাপকতর রূপ, মহত্তর উদ্ভাসের নাম গণ-অভ্যুত্থান।
ব্যক্তিগত সম্পর্ককে সে বিশ্বাস করে বলে অনেক ছোটখাটো কাজের মধ্যেও সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। কোনও পাড়ায় পথবাতি না থাকার মতো ঘটনাকেও সে দেখেছে অধিক গুরুত্ব সহকারে। বহরমপুরে ইতিমধ্যেই সে এক চেনা নাম। হরিহরপাড়ার ঘটনার পর সে হয়তো-বা সারা মুর্শিদাবাদেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে যাওয়া নাম। গুলি লাগার কারণে বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলিতে ছবিসহ নাম ছাপা হয়েছিল তার। যদিও কাগজগুলি তাকে ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচয় দেয়। কিন্তু সে নিজে জানে, ছাত্রনেতা তাকে বলা যায় না কোনও মতেই। কয়েকটি কাগজ তার সাক্ষাৎকার দাবি করেছিল। কিন্তু সে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করেছে।
এমনিতেই গোটা ব্যাপারটাই সে ঘটিয়েছিল রাসুদার সঙ্গে যথাযথ পরামর্শ না করেই। তাদের পার্টিলাইনে এই ধরনের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সুনজরে দেখা হয় না সে জানে যদিও। সুতরাং সাক্ষাৎকার দিয়ে ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে অতিমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করা তার পক্ষে সরাসরি পার্টি নেতৃত্বকে অস্বীকার করার পর্যায়ে চলে যেত। সে যে সাক্ষাৎকার দেয়নি তাতে খুশি হয়েছিলেন রাসুদা।
সে যখন কাঁধে গুলি লাগা অবস্থায় হাসপাতালে ছিল তখন বহু লোক তাকে দেখতে এসেছিল। হঠাৎই তার খ্যাতিমান এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠার লক্ষণগুলি ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি মিহির রক্ষিত। তিনি সরাসরি বলেছিলেন—এ ধরনের হুলিগ্যানিজম পার্টির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।
সে অবাক হয়ে বলেছিল-হুলিগ্যানিজম? মেয়ে পাচার করার মতো একটা ঘটনার বিরুদ্ধে পুলিশে যাওয়া হুলিগ্যানিজম? প্রথমে তো নিজের হাতে সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়া হয়নি। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করেছিল।
—করেছিল করেছিল। তুমি আমাদের জানাতে পারতে। আমরা ওপর থেকে চাপ সৃষ্টি করতে পারতাম। তোমরা সরাসরি মঠে গিয়ে অত্যন্ত ভুল কাজ করেছ। আমি বলব, তোমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যই মহিলার মৃত্যু হল। এতগুলো নিরীহ প্রাণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে তোমরা। ভবিষ্যতে পার্টির সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও কাজ করে ফেলবে না আশা করি। এ কথা আমরা অমরেশ বিশ্বাসকেও জানিয়েছি।
সে মেনে নিতে পারেনি মঠে গিয়ে তারা ভুল করেছিল। সাধারণত মঠ আখড়া ইত্যাদির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভক্তি থাকে। ঘোষপাড়া মঠ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভক্তির একেবারে গোড়ায় আঘাত করা প্রয়োজন ছিল বলে সে মনে করে। অমরেশ বিশ্বাস বর্ষীয়ান নেতা। তিনিও তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলেন। তারা বলা সত্ত্বেও পুলিশ ঘোষপাড়া মঠে যেতে চায়নি। সাধারণত পুলিশ এ ধরনের গণদাবির বিরোধিতা করে না। বিশেষত শাসকদলের বিরোধিতা করার জোর কোথায়? হতে পারে হরিহরপাড়া বামশাসিত নয়। এ হল কংগ্রেসি এলাকা। কিন্তু তা বলে এ জায়গা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নয়! এবং আগামী নির্বাচনেই কংগ্রেস এই এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য হবে না, তা কে বলতে পারে? তবু, অমরেশ বিশ্বাসের উপস্থিতি ও নির্দেশকে উপেক্ষা পুলিশ এ ক্ষেত্রে করেছিল কারণ তার ধারণা ঘোষপাড়ার মঠ থেকে থানায় নিয়মিত পারিতোষিক যেত। ওই এলাকায় এতদিন ধরে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে আসছে। পুলিশ কিছুই জানে না তা হতে পারে না। ওপর থেকে নির্দেশ এলে তারা দু-চারদিন মঠে যেত। কিছুই পেত না। উল্টে মঠ থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে, তাদের দলীয় অভিযানের বিরুদ্ধে প্রচার করার সুযোগ উপস্থিত হত।
ওইদিন যারা মারা গিয়েছিল তাদের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল। সে স্থির করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সে পরবর্তীকালে সাহায্য করবে। কীভাবে করবে, তা সে জানে না। অমরেশ বিশ্বাস জেলাশাসকের কাছে দরবার করে মৃত ব্যক্তিবর্গের পরিবারকে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের অভাব অর্থ দ্বারা পরিশোধ্য নয়। পাঁচ হাজার টাকাও কোনও মূল্যেই এক মানুষের চিরনিদ্রিত সত্তার পরিপুরক হতে পারে না। তবু এর বেশি কিছু করা সম্ভব হয়নি। ভাবলে তার খারাপ লাগে। কিন্তু সেদিন সে নিজেও মারা যেতে পারত। এমন নয় যে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে দিয়ে সে নিজের গা বাঁচিয়েছিল।
আসলে মিহির রক্ষিতের মনোভাব সে বুঝতে পারে। পার্টির মধ্যেই ঢুকে আছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার লড়াই। রাসুদা এবং মিহির রক্ষিত দু’ জনেরই আছে আলাদা আলাদা বাহিনী। তারা যে-যার নিজের এলাকা সামলায়। আবার দরকারমতো একত্র হয়েও কাজ করে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাসুদা আজও পর্যন্ত জিতে আসছেন কারণ রাসুদা সি পি আই এম-এর পুরনো সংগঠক। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অত্যন্ত আস্থাভাজন। দীর্ঘদিন ধরে সি পি আই এম-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকের কাজ তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে আসছেন। একটি ব্যাপার এ পর্যন্ত প্রমাণিত যে, রাসুদা যতই ক্ষমতাবান হোন, আসনের প্রতি ওঁর লোভ নেই। উনি কখনও লোকসভা বা বিধানসভার প্রার্থী হতে চাননি। ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার তুঙ্গাসনে বসে রাজপাট গড়ে তুলতে ব্যগ্র হননি কখনও। সংগঠনের কাজেই ওঁর আত্মনিবেদন। অন্তরালে থেকে কাজ পরিচালনা করতেই উনি অনেক বেশি পছন্দ করেন। কমিউনিস্ট দলগুলি বিবিধ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে এ ধরনের পরোক্ষ নেতৃত্বকে সবসময়ই গুরুত্ব দেয়।
এবং সিদ্ধার্থ নিজেও যতখানি রাসুদার প্রতি অনুগত ততখানি মিহির রক্ষিতের প্রতি নয়। মিহির রক্ষিত বয়সোচিত অগ্রাধিকার পাচ্ছেন, এই মাত্র। তা ছাড়া দল বৃহৎ হলে, বিশাল সাম্রাজ্য শাসনকাঠামোর মতোই দাবি করে বিচিত্র মুখ। দাবি করে কবি ও জল্লাদ। দাবি করে নম্র, মৃদুভাষ সংগঠক এবং প্রলাপবাক্ নিরবধি ক্ষমতার তিষায় উন্মাদ নেতৃত্ব। তার এ-ও চাই, ও-ও চাই। তার রাসু চাই, মিহিরও চাই। অতএব সে-ও ধীরে ধীরে তৈরি করছে তার নিজস্ব বাহিনী। নিজস্ব পরিকাঠামো। বাসস্ট্যান্ডের পাশে নতুন রেস্তোরাঁটির মালিক শম্ভু পালিত তাকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিচ্ছেন। বিনিময়ে সেও রেস্তোরাঁটির জন্য করেছে অনেক। এখনও তার নিজস্ব বাহিনী ওই রেস্তোরাঁর ওপর নজর রাখে। এমন সহায়তা সে পেয়ে থাকে আরও। তার জন্য তাকে পক্ষ অবলম্বন করতে হয়। সম্পূর্ণ আত্মবেদী কি হতে পারে মানুষ কখনও? সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারে? সে জানে না। তার মনে হয়, নিরপেক্ষতা একটি আদর্শ শব্দ, প্ৰত্যেক সংবেদনশীল মানুষ তা ধারণ করে, তার প্রতি ধীময় শ্রদ্ধায় অবনত থাকতে চায়। সে-ও চায়। পারে না। হতে পারে, এখানেই মানুষের সংগ্রাম নৈতিকতার। সংগ্রাম এমনকী নিজেরও ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারে। সে অনুভব করে নিরন্তর।
নিজের মেয়ের নামে শম্ভু পালিত রেস্তোরাঁর নাম রেখেছেন মহুয়া রেস্তোরাঁ। মোটামুটি আধুনিক এবং পরিচ্ছন্ন। বহরমপুর-শিলিগুড়ি রুটে দুটি বাস আছে শম্ভু পালিতের। মহুয়া রেস্তোরাঁর এই জায়গাটা ওঁর নিজের ছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দোকান জায়গাটি দখল করেছিল। টাকা দিয়েও তাদের তোলা যাচ্ছিল না যখন, শম্ভু পালিত রাসুদার শরণাপন্ন হন। এই ধরনের কাজে রাসুদা আর নিজেকে জড়াতে চান না ইদানীং। বলেন—এখন তোদের হাত পাকাবার সময়
রাসুদাই তাকে এই সমস্যা সমাধানের ভার দিয়েছিলেন। এ নিয়ে রীতিমতো ভাবনা-চিন্তা করতে হয়েছিল তাকে। যারা তাকে আর্থিক গুরুত্ব দেয়, তারা ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই বিনিয়োগ করে, বর্তমানকেও রাখে সুরক্ষিত।
সে খোঁজ নিয়ে দেখেছিল আর এস পি-র মধ্যমমানের নেতা আনিসুর রহমান বাসস্ট্যান্ডের এই ছোট ছোট দোকানদারদের আশ্রয় দিচ্ছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে অসদুপায়ে সীমানা ডিঙিয়ে আসা মানুষ। এরা আসে, গ্রাম বা শহরের কোনা-খামচিতে থাকে কিছুদিন, কিংবা কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে, তারপর কোনও একটি রাজনৈতিক দলকে আশ্রয় করে শেকড় ছড়িয়ে বসে। প্রত্যেক পার্টিই এদের আশ্রয় দেয় একটিমাত্র স্বার্থে। সেই স্বার্থের নাম নির্বাচন। এদের কোনও পরিচয় নেই। এই দেশ ভারতবর্ষের প্রতি এদের কোনও টান জন্মায় না। সে চতুষ্কোনায় গিয়েছিল কিছুদিন আগে। তখন ওখানেও দেখেছে একই দৃশ্য। সীমান্ত পেরিয়ে আসা বেশ কয়েকটি পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন তাদের দলের একজন প্রভাবশালী পঞ্চায়েত সুকুমার পোদ্দার। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা মানবিক। যারা খেতে পায় না বলে এদেশে আসে তাদের নির্ভরতা দেওয়া মানবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর আড়ালের স্বার্থও পরিষ্কার। যদিও সে এই আশ্রয়দান সমর্থন করে না। পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতবর্ষ লোকসংখ্যার চাপে অর্ধমৃত। তার ওপর বহিরাগতের চাপ আরও বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে। পাঁচজনের অন্নে ভাগ বসাচ্ছে পঁচিশজন। এর ফলে কখনওই যথাযথ অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হবে না। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন না ঘটলে জনজীবনের মান ক্রমশ নিম্নগামী হবে। শুধু জেলা মুর্শিদাবাদই নয়, শুধু রাজ্য পশ্চিমবঙ্গই নয়, গোটা ভারতবর্ষের পক্ষে এই পরিস্থিতি অকল্যাণকর। এই মত সে প্রকাশ করতে পারে না।
সে জানে, তাদের দলীয় নেতৃত্ব এত বড় করে ভাবে না। তারা আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসুক হয়ে থাকে এবং পদ পেতে চায়। বিধানসভার লোকসভার সদস্যপদ। রাজ্যের ক্ষমতায় তারা হতে চায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেন্দ্রে চায় গুরুত্বপূর্ণ আসন। দেশ বলতে এই মাত্ৰ ধারণা। রাসুদার মতো মানুষ, যাঁরা পদের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁরাও দলীয় স্বার্থ ছাড়া কিছু ভাবতে চান না। সে নিজে গোটা ভারতবর্ষের জন্য ভাবতে চায়। যদিও আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সে সীমায়িত হয়ে আছে এখন এবং সেইসব কাজ খুব বড়মাপের কিছু নয়, তবে সে টের পায়, দেশ সম্পর্কিত ধারণার বিষয়ে তার রয়েছে প্রভূত আবেগ। হায়! এ আবেগ প্রকাশ করলে সে হাস্যাস্পদও হতে পারে। ব্রিটিশ শাসন হাজার অকল্যাণ এবং শতপর্বের কল্যাণের সঙ্গে দিয়েছিল এক অখণ্ড দেশের বোধ। এই বোধ নির্মাণের জন্য তাদের কৃতিত্ব কিছু নেই। কেবলই অবলম্বন তারা। তাদের মুঠোয় করে ইতিহাস সেই বোধ গড়েছিল। সেই বোধ ছিল আবেগময়, ব্যেপমান। সাতচল্লিশ থেকে সাতান্ন, সাতান্ন থেকে সাতষট্টি, সাতাত্তর, সাতাশি—দশকের পর দশক ধরে তরঙ্গায়িত এই প্রবাহধারা, এই ব্যেপমান আবেগ, ইছামতী নদীর মতো সংকীর্ণ এখন। ক্ষীণতোয়া। শৈবাল, ঝাঁকি ও কর্দমে আচ্ছন্ন। তাকে গ্রাস করছে খণ্ড। খণ্ডবোধ।
বহু শিক্ষিত সুচেতনা সম্পন্ন লোককে বলতে শোনে সে—দেশ আমাকে কী দিয়েছে?
সে বলতে চেয়েছে তখন—তুমি দেশকে কী দিয়েছ? তুমি তো নিজেই দেশ। দেশ তো আলাদা কোনও সত্তা নয়। তুমি, আমি, আমরা মিলেই এই দেশ। আমাদের দেশ।
বলতে চেয়েছে সে। বলতে চায়। কিন্তু বলা হয়নি কোথাও। হয়তো তার ভবিষ্যৎ জীবন অপেক্ষা করে আছে এ কথা বলার জন্যই।
রাসুদা মনে করেন, আবেগ রাজনীতির পরিপন্থী। সম্পূর্ণ নিরাবেগ এবং বাস্তববোধ-সম্পন্ন হতে না পারলে সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সম্ভব নয়। সে একথা মেনে নিতে পারেনি। রানীতিকে দুভাবে দেখা যেতে পারে বলে সে মনে করে। শুধু ক্ষমতা দখলের লড়াই হলে রাজনীতি অবশ্যই আদিম আবেগশূন্য অস্তিত্ব রক্ষার পথ। তা হলে রাসুদার কথা মেনে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে যদি মিশে থাকে প্রগতিশীলতা এবং গণকল্যাণের ইচ্ছে তা হলে রাজনীতি আবেগশূন্য হতে পারে না কিছুতেই। কাকে বলে সঠিক বাস্তববোধ সে জানে না। সে কি জনচেতনাকে বুঝতে পারা? সে কি শাসনক্ষমতা দখলের উদ্দেশে ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপ? সে কি সম্পূর্ণ স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠা মিহির রক্ষিত?
সে চোখ বন্ধ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। আজ বিকেলে তার একটি পথসভা আছে। বক্তা হিসেবে রাসুদা ও মিহির রক্ষিতের সঙ্গে সে-ও থাকছে। যদিও তাকে এই সভায় বক্তা করার বিষয়ে মিহির রক্ষিতের আপত্তি ছিল। তাঁর মতে সিদ্ধার্থর উচিত সভায় যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না হয়, সেটাই দেখা। শেষ পর্যন্ত রাসুদা তাকে বক্তা হিসেবে বহাল রেখেছেন। হরিহরপাড়ার ঘটনার পর এই প্রথম সে বড় পথসভায় বক্তব্য রাখতে চলেছে।
বক্তব্য বিষয় আগে থেকেই দলীয় দপ্তরে আলোচিত হয়ে থাকে। তাদের বক্তব্যের অধিকাংশই কেন্দ্রের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা। কিছু থাকে স্থানীয় সমস্যার বিষয়, কিছু বিরোধী নেতৃত্বের প্রতি বিষোদ্গার। সে সাধারণত বিরোধী নেতৃত্বের বিষয়ে কিছু বলে না। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কখনও সে সরব হয় ঠিকই, তবে তার বিশেষ পছন্দ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলা। এর মধ্যে গঙ্গার ভাঙন এক বৃহৎ বিষয়।
সম্প্রতি বহরমপুরের খুব কাছেই চতুষ্কোনা নামে একটি গ্রামে ভাগীরথীর ভাঙন শুরু হয়েছে। এই ভাঙন বড় আকার নিলে শুধু চতুষ্কোনাই নয়, বহরমপুর শহরও বিপন্ন হয়ে পড়বে। সে এই নিয়ে একটি বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছিল। সে স্থির করেছে, এখন থেকে তার বক্তব্যের প্রধান বিষয়ই হবে ভাঙন। নারীপাচার চক্র বিষয়েও সে কিছু বলতে চেয়েছিল। শাসনযন্ত্র কতখানি শিথিল হলে এ ধরনের চক্র সক্রিয় হতে পারে- এ নিয়েই সে বিস্তারিত হতে চেয়েছিল। কিন্তু রাসুদা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে দেওয়ার বিরোধী হলেন। তাঁর মতে, এটা একটা বড় বিষয় ঠিকই, তবে সরাসরি শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে বলা মানে এখন সি পি আই এম-এর বিরুদ্ধেই বলা।
বাইরে সে নীরবে মেনে নিয়েছে রাসুদার নির্দেশ। কিন্তু মনে মনে সে প্রতিবাদী। আরক্ষা বিভাগ একটি প্রাচীন যন্ত্র। তার কলকব্জায় ঘুণ এবং মরচে ধরে যেতেই পারে। তার জন্য কোনও দল বিশেষভাবে দায়বদ্ধ হবে কেন। শাসনযন্ত্র অসৎ এবং দুর্বল হলে যে-দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আরক্ষা, শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, সাহিত্য–প্রভৃতি প্রত্যেকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এখন নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা। এর ফলে এক বিশেষ শ্রেণি ও বিশেষ দলের মানুষ বৈশেষিক সুবিধা লাভ করে। তার দ্বারা সার্বিক কল্যাণ সম্ভব নয় সে জানে। কিন্তু তার যুক্তি তার নিজের কাছে। এগুলো কোথাও বলার জায়গা নেই তার। সে, যতক্ষণ না কোনও লোক তার কাছে আসছে কিংবা দলের কোনও ছেলে, এই দোতলার দক্ষিণের ঘরে বসে বসে ভাবে সমস্তই। নিজের মধ্যেই চালিয়ে যায় বাদ-প্রতিবাদ। সংগঠনের জন্য শিখতে হয় শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলার জন্য আনুগত্য অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু সে ক্রমশ টের পাচ্ছে প্রশ্নবিহীন আনুগত্য কত কঠিন। এবং যদিও সে শৃঙ্খলার সমর্থক, তবুও, সংগঠনের স্বার্থেই আত্মসমালোচনাকে সে জরুরি বলে মনে করে। আত্মসমালোচনার কোনও জায়গা তাদের দলে নেই। থাকলে এই শহর বহরমপুরেই সি পি আই এম শক্তিগুলি গোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে পড়ত না।
এই সমস্ত ভাবনাতেই সে তলিয়ে থাকল কিছুক্ষণ এবং এবম্বিধ বিরোধিতা থেকে বেরিয়ে তার বক্তব্যকে সাজাতে শুরু করল। এই প্রস্তুতি নেওয়াই তার অভ্যাস। জনগণকে সে কখনও এমন নগণ্য ভাবে না, যাতে কোনও প্রস্তুতি বিনাই সে উঠে দাঁড়াতে পারে মঞ্চে। একটি সিগারেট ধরাল সে এবং তুলে নিল একটি ছোট ডায়রি ও কলম। যা সে দেখে এসেছে চতুষ্কোনায়, যা সে দেখে এসেছে ভৈরবের পাড়ে, সেইসব বৃত্তান্ত সে ছোট ছোট বাক্যে লিখতে থাকল এবং ভৈরবের অনুষঙ্গেই তার মনে পড়ে গেল আবার ময়না বৈষ্ণবীকে।
একটা আলাদা কিছু ছিল ওই মহিলার মধ্যে। একটা অন্যরকম কিছু। বিদ্রোহের এক চাপা শক্তি। কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত সত্যিই কিছু করতে পারল না ময়না বৈষ্ণবীর জন্য। সে বুঝতে চেষ্টা করল, হরিহরপাড়ার ঘটনা একটা জনবিবেকের স্ফুরণ ঠিকই, কিন্তু কোনও এক আশাপ্রদ পরিণতির দিকে কি পৌঁছনো গেল? হয়তো যেত যদি এ নিয়ে বলতে পারত সে। কিন্তু পারছে না। একটি ঔচিত্যের সঙ্গে এভাবেই আপস করে নিচ্ছে সে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে মন তুলে প্রতিস্থাপিত করছে নির্বাচনী প্রচারে। একেই কি রাসুদা বলছিলেন রাজনীতিকের বাস্তবতাবোধ! কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে আটকে না থেকে দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থের চাহিদামতো সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে কালযাপন? সেও কি তা হলে ক্রমশই হয়ে উঠছে একজন গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মী? সে এরকম হতে চায় না। প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে অন্ধভাবে অনুসরণ করলে প্রকৃত নেতৃত্বের স্ফুরণ হয় না কখনও
সে গালে কলম ঠেকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। এই সকালেই বাগানে কাজ করছেন বোধিসত্ত্ব। আশি বছরের এই মানুষটি তার একমাত্র পিছুটান। এবং সে জানে, সে-ও বোধিসত্ত্বের একমাত্র পিছুটান। কিন্তু এই দুই পিছুটানের পার্থক্য আছে। সে এই জীবন থেকে এক বৃহত্তর জীবনের দিকে যেতে যেতে এই টান অনুভব করছে। আর বোধিসত্ত্ব জীবন ছাড়িয়ে মহামৃত্যুর দিকে যেতে যেতে তাকে আঁকড়ে জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছেন। সিদ্ধার্থ টের পায়, বোধিসত্ত্বের একচোখ কাঙাল, অন্যচোখ নিঃস্ব। অসম্ভব দীন তাঁর স্নেহপরায়ণতা। সিদ্ধার্থকে আগলে রাখা ছাড়া আর কোনও পার্থিব চাহিদা নেই তাঁর। অথচ তাঁকে অধিকারপ্রবণ বলা চলে না। তাঁর স্নেহও এমনকী তিনি আরোপ করে দেন না কারও প্রতি। তাঁর একমাত্র অবলম্বন সিদ্ধার্থর প্রতিও নয়। তাঁর স্নেহ শুধু সঙ্গে সঙ্গে যায়। সারাক্ষণ সিদ্ধার্থর সত্তায় অন্তর্লীন থাকে। বিরাট শোকপর্বত পার হয়ে তারা এই দুই পৃথক প্রজন্মের মানুষ, পরস্পরের একাকিত্ব দ্বারা জড়িয়ে আছেন পরস্পরকে।
আজ এই আশি বছরেও তিনি সুদেহী। কর্মঠ। নিষ্ঠাবান। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। হয়তো তাঁরই জন্য সিদ্ধার্থ নিজে ইতিহাস পড়েছিল। ইতিহাস না পড়লে সে পদার্থবিদ্যা পড়ত, অর্থনীতি পড়ত, কিংবা সমাজবিদ্যা। মেধা তার প্রতি বিরূপ ছিল না। পরীক্ষার নম্বর যদি মেধার প্রকাশ হয়, তবে সে ছিল ছাত্র হিসেবে উজ্জ্বল। কোনও অন্তর্ঘাত, কোনও চক্রান্ত, কোনও স্বপ্নতত্ত্ব তাকে, ওই মেধা দ্বারা অশ্বারোহী হতে শেখায়নি।
গত কুড়ি বৎসর ধরে বোধিসত্ত্ব একজন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। এক টাকা মাত্র দর্শনীর বিনিময়ে তিনি প্রত্যহ রোগী দেখে দেন। নানা শ্রেণির লোক তাঁর কাছে আসে। একেবারে বিনা পারিশ্রমিকেই তিনি এ কাজ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি মনে করেন দাতব্য করার মধ্যে মানুষের প্রতি যে করুণা প্রকাশ পায় তা মানুষকে অপমানই করে শেষ পর্যন্ত। মানুষের অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজন তার মধ্যে জেগে থাকা অহং। এই অহং বিপুল হলে অন্ধত্ব আসে, এই অহং খর্ব হলে আসে আত্মগ্লানি। গ্লানিময় মন নিয়ে মানুষ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে না। অতএব বোধিসত্ত্ব মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ জাগরূক রাখতে সচেষ্ট থাকেন।
বাগান এবং চিকিৎসা—দুটোই বোধিসত্ত্বের নেশা যা তাঁর শরীর এবং মনকে কাজে ব্যাপৃত রেখে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।
সিদ্ধার্থ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার চেষ্টা না করে পুরোপুরি দলের কাজের দিকে চলে যাচ্ছে তখন বোধিসত্ত্ব তাকে ফেরাবার চেষ্টা করেননি বা বাধাও দেননি। একদিন বলেছিলেন— জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে গতি এবং বিস্তার। এই দুটি ধর্ম না থাকলে জীবনকে আর জীবন বলা চলে না। তোমার বাবার মধ্যে এই দুটির একটাও ছিল না তাই সে ধ্বংস হয়ে গেল।
সে এইসব গভীর কথার দিকে নির্নিমেষ তাকায়। এবং ভাবে। পিতামহের বিবিধ কথা নাড়েচাড়ে। উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। সে কি তবে প্রবেশ করছে কোনও গতিময় জীবনের বিস্তারে? কাকে বলে জীবনের গতি ও বিস্তার? সে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে। বিশ্বাস ও সংস্কারে যখন বাঁধা পড়বে না মন, যখন আসা ও যাওয়া—দু’দিকেরই দ্বার সে খোলা রাখতে পারবে, পাহাড়ের পর পাহাড় আর সমুদ্রের পর সমুদ্র পেরিয়ে যাবে সে যখন, তখন সে গতিময়। জীবন তখনই গতিশীল থাকে যখন মনের জঙ্গমধর্ম থাকে বর্তমান। মনের গতিময়তাই জীবনকে নিয়ে যায় বিস্তারে।
সে বোধিসত্ত্বের মধ্যে থেকে গভীর জীবনবোধ আঁতিপাতি করে খুঁজে নেয়। এবং মাঝে মাঝে তাঁর মৃত্যুভয়ে ভীত হতে থাকে। এই মানুষটা চলে গেলে সে পাবে কোন অবলম্বন?
তখন সে ঘুরেফিরে সেই বিস্তারবোধের মুখোমুখি দাঁড়ায়। জীবনের সেই বৃহৎ হতেই কি সে পেয়ে যাবে না তার শ্বাসবায়ু? এবং হয়তো বোধিসত্ত্ব বিনা তার অসম্ভব একাকিত্বর কথা ভেবেই তিনি ওই গতি ও বিস্তারের কথা বলেন। গতি পুরনোকে সদা নতুনে টেনে আনে। আর বিস্তার অনাত্মীয়ের মধ্যে দেয় আত্মীয়তা। সে, এই সম্ভাব্য আত্মীয়তার কথা ভেবে একা একা অবশিষ্ট জীবনপাতের শক্তি সংগ্রহ করে। তবু কোনও কোনও মুহূর্তে কিছু আলোড়ন, কিছু অশান্তি, তার হৃদয় মথিত করে দেয়। এখন, সেই হৃদয়ভোগ হতে নিস্তার পেতে, সে চোখ বন্ধ করে বসে পদ্মাসনে। চিত্তকে করে তুলতে চায় সচেতন ও শাস্ত। তখন তার দুয়ারে শব্দ হয়।
চোখ খুলল সে। তাকাল। যে-মহিলা তাদের দু’জনের সংসার পরিপাটি রাখতে সহায়তা করেন, তাদের রেঁধেবেড়ে খেতে দেন, তিনি দাঁড়িয়ে। নাম তাঁর সাবিত্রী। এই সাবিত্রীর সত্যবান একজন ফিরিওয়ালা। একই এলাকায় সে থালা-বাসনও বিক্রি করে, আবার ফিতে-চুড়িও। চারটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সে এক সাংঘাতিক পুরুষ। সুযোগ পেলেই সাবিত্রীকে মেরে তার শরীরে কালশিটে ফেলে দেয়। সিদ্ধার্থ বহুদিনই ওই সত্যবানের হাত ভেঙে দেবার সংকল্প করেছে, কিন্তু সাবিত্রীর উপরোধে তা ঘটিয়ে উঠতে পারেনি। আজও সাবিত্রীর মুখ ফোলা। ঠোঁট কেটে গেছে। সিদ্ধার্থর হাত মুঠিবদ্ধ হল। কিন্তু প্রথমে সে বলল না কিছুই। সাবিত্রী বললেন—আর বাড়ি ফিরে যাব না গো দাদা। তোমাদের বাড়ির এককোণে পড়ে থাকতে দেবে?
—আবার মেরেছে? তোমার ঠোঁট কাটল কীভাবে?
—কাল ঠোঙা বানাচ্ছিলাম। কখন ঝিমুনি এসে গেছে বুঝতে পারিনি। সে এসে লাথি মারল পিঠে। মুখ থুবড়ে পড়লাম। আঠার বাটিতে লেগে ঠোঁট কেটে গেল। বাড়ি থেকে বার করে দিল আমাকে। রাত্রে গেলাম পাশের বাড়ি। সেখান থেকে এক কাপড়ে চলে এলাম। তোমরা আশ্রয় না দিলে আর যাব কোথায় বলো?
—তোমাকে তো বললাম, একদিন ধরে আচ্ছা করে পিটিয়ে দি।
—না না। স্বামীকে মারলে পাপ হয়। ওসব কোরো না।
—আরে তুমি তো মারছ না। পাপ হলে আমার হবে। একটু বুঝতে দাও, দিনের পর দিন তোমার কেমন লাগে।
—না না। মেরো না। রোগা-ভোগা মানুষ। সারাদিন রোদ্দুরে ঘুরে মাথার ঠিক থাকে না।
—বাঃ! এ তো ক্ষমাই করে দিয়েছ। তা হলে আর বাড়ি যেতে চাইছ না কেন?
—না গো। বাড়ি থেকে বের করে দিলে বড় অপমান লাগে। মারে ধরে সে একরকম। কিন্তু বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া! আর তার দেখাদেখি ছেলেমেয়েরাও আমাকে চাপে। অনেক সয়েছি। আমারও তো মানুষের মতো একটু বাঁচতে ইচ্ছে করে। মেয়েমানুষ হলেও তো আমি মানুষ। বলো?
—তুমি যে মানুষ, সে-বিষয়ে আমাদের কোনও সংশয় ছিল না। তুমি নিজে তা বুঝেছ, সেই হল আসল কথা। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ছাড়া থাকতে পারবে না তুমি সাবিত্রীদি।
—থাকব। দেখো তুমি। তারা এখন বড় হয়েছে। যে-যার নিজের বুঝতে জানে। আমি না হলে তাদের আর কিছুই পড়ে থাকে না।
—বেশ তো। কিন্তু এ বাড়িতে থাকার জন্য দাদুর অনুমতি লাগবে। তাঁকে বলো।
—বললাম। বড়বাবু বললেন…
—কী বললেন?
—ওঃ! সে আমি বলতে পারব না।
—ওফ! আমার সময় নেই। বলো তাড়াতাড়ি। দাদু মজা করেছেন নিশ্চয়ই। কী বললেন?
-–বললেন… শোনো মনোর মা, এ বাড়িতে একজন বিপত্নীক পুরুষ, একজন অবিবাহিত, তুমি এখানে থাকলে লোকের সইবে তো?
সিদ্ধার্থ হেসে ফেলল। বোধিসত্ত্ব আজও কত রসপূর্ণ মানুষ! অথচ তার বাবা বুদ্ধদেব কেন হলেন ওইরকম শুকনো, নিষ্প্রাণ! মুহূর্তের অন্যমনস্কতা থেকে ফিরে সে বলল— সাবিত্রীদি, দাদুর মত জানা দরকার। তুমি আর একবার কথা বল। কিংবা আমিও বলতে পারি।
—শোনো দাদা, উনি বললেন, আমাকে শুধিয়ো না। বলো ছোটবাবুকে। ছোটবাবু এখন বড়বাবু হয়ে উঠছেন। তিনিই আমার অভিভাবক।
নীচে কথাবার্তার শব্দ পেল সে। তার মানে লোকজন আসা শুরু হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি সাবিত্রীর পর্ব মেটাবার জন্য বলল-তুমি তো সারাদিনই এ বাড়িতে আছ। রাতে থাকলে ক্ষতি কী! বরং একদিকে ভাল যে দাদু একা থাকবেন না। থেকে যাও তুমি যতদিন ইচ্ছে।
সাবিত্রী চোখ মুছলেন একবার। সতেরো বছর বয়স থেকে সন্তানের জন্ম দিতে দিতে আজ তিনি চল্লিশের নিকটবর্তী। অথচ দারিদ্র্য ও মনোকষ্টে তাঁকে দেখায় পঞ্চাশের প্রৌঢ়ার মতোই। এই বাড়িতে তিনি কর্মীমাত্র। তবু এই বাড়িই হয়ে উঠছে তাঁর পরম আশ্রয়। তিনি জানেন এ-গৃহে তাঁর আশ্রয় মিলে যাবে। তবু কী এক আবেগ অশ্রু হয়ে ফোটে। কিংবা এক বেদনা! ছেলেমেয়ে-স্বামীর দ্বারা তাড়িত হওয়ার নির্বিচার বেদনা! তিনি পায়ে পায়ে ফিরে যেতে থাকেন। সিদ্ধার্থ এই চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ডাকল তাঁকে—সাবিত্রীদি শোনো।
সাবিত্রী দাঁড়ালেন। ফিরলেন সিদ্ধার্থর দিকে। সিদ্ধার্থ বলছে—তুমি কি সত্যি থাকবে?
সাবিত্রী স্থির চোখে চেয়ে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিতে আশঙ্কা ঘনায়। ছোটবাবু কি তাহলে মত বদল করলেন? সিদ্ধার্থ সেই শঙ্কিত চোখ পড়ে নেয় এবং সাবিত্রীর থাকার ইচ্ছার প্রাবল্য উপলব্ধি করে। সে বলে—তা হলে দোতলার যে-কোনও ঘরে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে নিয়ো। নীচে মাঝে-মধ্যে পার্টির ছেলেরা থাকে জানো তো।
—ঠিক আছে।
—শোনো।
সিদ্ধার্থ উঠে গিয়ে তার প্যান্টের পকেট থেকে টাকা নেয়। কিছু দেয় সাবিত্রীকে। বলে— তুমি রাখো। তোমার তো নিজের জিনিস কিনতে লাগবে।
প্রকাশ্যেই চোখ মুছতে মুছতে চলে যান সাবিত্রী। সিদ্ধার্থ নীচে নামার আয়োজন করে। সাবিত্রীকে সামান্য সাহায্য করতে পেরে তার হঠাৎ মন ভাল হয়ে যায়। এমনই হয়েছিল যখন সে মহুয়া রেস্তোরাঁর কাজটা করেছিল। শম্ভু পালিতের জমি থেকে ছোট ছোট দোকানদারদের তোলার পথ সে খুঁজে পাচ্ছিল না কিছুতেই। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল আনিসুর রহমানকে কোনওভাবে প্যাঁচে ফেলা দরকার। অনুসন্ধান করতে করতে সে হঠাৎই এক রাস্তা পেয়ে যায়। স্টেশনের নিকটে চারকাঠা মতো জমি কিনে রেখেছিলেন আনিসুর রহমান। সিদ্ধার্থ নিজের দলের কয়েকজনকে কিছু পসরা সমেত বসিয়ে দিয়েছিল ওই জমিতে। যথারীতি এই নিয়ে এক বাদানুবাদ ও শাসানির পর্ব সৃষ্টি হয়। সে-ও এই পরিস্থিতি চাইছিল। ওইসব দোকানিদের প্রতিনিধি হয়ে সে আনিসুর রহমানের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। প্রথমে সে চায় দোকানিদের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ। তার প্রস্তাবে আনিসুর রহমান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন— ওরা কি তোমার লোক?
সে জবাব দিয়েছিল—যে-কোনও লোকই আমার হতে পারে। আমিও হতে পারি যে-কোনও লোকের।
—মানে?
—আমার লোক, আপনার লোক এসব আমি মানি না। তবে ওরা আমার সাহায্য চেয়েছে।
—এত লোক থাকতে তোমার সাহায্য কেন? আমি যদি বলি তুমি ওদের ওখানে বসতে বলেছ?
—আপনি একথা কেন বলবেন? বহরমপুর শহরে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা বাড়ছে জানেন তো? লোকও বাড়ছে। আপনারা কিছুই করতে পারেননি এই শহরের জন্য। এখন যদি কোনও ফাঁকা জমিতে বসে সামান্য জিনিস বেচে কেউ সংসার চালায়, তা হলে আপনি তাদের কী বলে তুলে দেবেন?
—কী বলে তুলে দেব মানে? মেরে পিটিয়ে তুলব।
—বেশ। গরিব মানুষগুলোর ভাত কেড়ে নেবেন আপনি। আমরা জনগণকে জানাব।
—তু-তুমি ক্-কী বলতে চাও? সেদিন রাজনীতিতে এসে দাদা হওয়ার চেষ্টা করছ?
—না। দাদা এখনও হইনি। এখনও বন্ধু আছি। আপনাদের মতো সুবিধাবাদী হতে পারলে দাদা হয়ে যাব।
—তুমি জানো? তোমাকে আমি… তোমাকে আমি…
—মেরে ঠান্ডা করে দিতে পারেন? আমি জানি।
দাঁতে দাঁত পিষেছিলেন আনিসুর রহমান। ক্রোধে লাল মুখ থেকে আগুনের আঁচ উঠে আসছিল। চাপা স্বরে বলেছিলেন—ঠিক কী চাও তুমি?
সে কোনও তাড়াহুড়ো না করে বলেছিল—জমি বেদখল হয়ে গেলে অসুবিধা হয়। ভাল লাগে না। তাই না? নিজে যদি সেটা বুঝে থাকেন তা হলে অন্যের জমিতে দখলদার বসানো আপনার উচিত হয় কি?
—কার জমি? কাকে আমি বসিয়েছি? আমি একটি সমাজতান্ত্রিক পার্টির সক্রিয় সদস্য। আমি কোনও অন্যায় করি না।
—না। গরিবকে সাহায্য করেন মাত্র। যেমন শম্ভু পালিতের জমিতে দোকান বসিয়ে সাহায্য করেছেন।
—কীসের শম্ভু পালিতের জমি? ওটা ফাঁকা পড়ে ছিল। আর লোকগুলো খেতে পাচ্ছিল না।
—আপনার জমিটাও পড়ে ছিল। জমি পড়েই থাকে প্রথমে। লোকে ধীরে-সুস্থে জমির ওপর বাড়ি বানায়। যেমন আপনি বানাবেন। কিন্তু গরিব-গুর্বোরা কী করবে? ফাঁকা জায়গা দেখলেই দখল নিয়ে কিছু উপার্জন করতে চাইবে।
—কী চাও তুমি বলো।
—দোকানগুলো তুলে দিন শম্ভু পালিতের জায়গা থেকে। আমিও কথা দিচ্ছি আপনার জমি ফাঁকা হয়ে যাবে।
—এখন আর সম্ভব না সিধু। লোকগুলো বেঁকে বসবে।
—তা হলে আপনার জমি গেল।
—শোন, শোন। বলছিলাম কিছু ক্ষতিপূরণ তো চাইবে ওরা।
—এই লোকগুলোও ক্ষতিপূরণ চাইবে তা হলে।
—তুমি আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করছ।
—সেটাই তো আমার কাজ, নয় কী? আপনারা এখন এই শহরের ক্ষমতায়।
দিন পনেরো সময় দিয়েছিল সে আনিসুর রহমানকে। এই পনেরো দিনে সে বিবিধ অশান্তির আশঙ্কা করেছে। মারামারি বোমাবাজি হলেও কিছু করার ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে শান্তিতেই মিটে গেছে সব। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছে সে। আনিসুর রহমানের জমির সন্ধান না পেলে কী করতে পারত সে জানে না। কিন্তু এই ঘটনার জন্য তার কোনও অনুশোচনা হয়নি। এর জন্য বড়লোকের বন্ধু হিসেবে তার অপনাম হতে পারত। কিন্তু না হয় যাতে, সেদিকে সে সচেষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে সমস্ত উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারের নাম ও বাসস্থান জেনে নিয়েছিল সে। অধিকাংশই মেথর বস্তির দিকে সস্তায় ঝুপড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। সে নিজে দেখা করেছিল লোকগুলোর সঙ্গে। ভিন দেশ থেকে উৎপাটিত মানুষ। বেঘর। বেসাহারা। সে চায় না এইসব মানুষ এসে জমুক। ভিড় বাড়াক। দারিদ্র্য বর্ধিত করুক। তবু, পরিস্থিতির বিচারে, সে পৌঁছে গিয়েছিল তাদের কাছে। সে বুঝতে পারছিল, যে একবার শিকড় চারিয়ে দিতে চেয়েছে, সে আর ফিরে যাবে না। অতএব এইসব মানুষকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দলের অন্তর্গত করে নেওয়া ভাল। অতএব, বিপদে ত্রাতা হয়ে এসেছিল সে। শম্ভু পালিতের কাছ থেকে পাওয়া টাকা বিলিয়েছিল উচ্ছিন্ন মানুষগুলির মধ্যে, আর বুঝিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির ছাপ থাক বা না থাক, সি পি আই এম ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলই গরিবের চিরস্থায়ী বন্ধু নয়। হাতে হাতে সাহায্য পেয়ে লোকগুলি বিশ্বাস করেছিল তাকে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বাসস্ট্যান্ডের চৌহদ্দিতেই তাদের দোকান করে দেবে।
কথামতো এ পর্যন্ত সে তিনটে দোকান বসিয়েছে। এ কাজ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কারণ বাস ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরদের ইউনিয়নের নেতা তার বন্ধু। এমনকী বাসের কর্মীদেরও অন্তরঙ্গ সে। সিধুদা গরিবের জন্য ভাবে। মানুষের ভালর জন্য জানের পরোয়া করে না। একথা এ শহরের বহু লোক বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে আরও।
সে জানে, ছোট-বড় সমস্ত সাহায্যের কথাই লোকমুখে পল্লবিত হয়ে যায়। এই যে সাবিত্রীকে সাহায্য করল সে কিছুক্ষণ আগে, তাও তাকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে দরদি হিসেবে প্রচারিত করবে।
দোকানদারদের ব্যাপারটা সে খুবই সতর্কভাবে ঠান্ডা মাথায় অঙ্ক কষে ঘটিয়েছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে যা-কিছু সাহায্য করে, সবই প্রচার কামনার তাগিদে। এই ভাবনা আসা মাত্র সে একবার থমকায়। সে কি ঠিক জানে? সত্যিই প্রচারকামনা থেকেই সে সাহায্য করে না? সে বিমূঢ় হয়ে যায় এই প্রশ্নের মুখোমুখি এসে। নিজেকে চেনা সম্ভব হয় না। এক-একবার মনে হয়, রাজনীতি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও কর্ম যেহেতু তার জীবনে নেই, সেহেতু তার সকল সিদ্ধান্তই হয়ে ওঠে এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ। হয়তো নিজের কোনও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুঁজতে যাওয়াই তার পক্ষে নিরর্থক। আর যদি সে আদ্যন্ত এক রাজনৈতিক মানুষ হয়ে ওঠে তা হলেই বা কী! মানুষের কর্মই তার জীবন। কর্মজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে। প্রচার তো বর্জ্যবস্তু নয় কোনও। প্রচারের শক্তি কাজ করতে সাহায্য করে বরং। যে-কাজ সে করবে ভাবে, তার জন্য সে বেপরোয়া। ঝুঁকি নিতে সে ভয় পায় না। এই চরিত্রের ওপর লোকে নির্ভর করতে ভালবাসে। স্বচ্ছন্দ বোধ করে। সে জনজীবনের অন্তরঙ্গ হতে চায়। প্রচার কি তাকে জনগণের দুয়ারেই পৌঁছে দেয় না?
নীচ থেকে তৌফিকের স্বর ভেসে এল তখন। তৌফিক তার অন্তরঙ্গ সহকারী। নির্ভরযোগ্যও বটে। ঘন ও ব্যাপ্তিময় তার স্বর। সে সম্ভবত চিৎকার করছে—এ কী! কে করল এরকম? আরে বসিয়ে দিন, বসিয়ে দিন। সিধুদা, সিধুদা।
সিদ্ধার্থ দ্রুত নামতে থাকল সিঁড়ি বেয়ে। নীচের ঘরে পৌঁছে কেঁপে উঠল সে। সাদা পোশাকে চাপ-চাপ রক্ত মেখে চেয়ারে এলিয়ে আছে একজন লোক। এক তরুণ তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। একটি গামছা সে চেপে ধরে আছে লোকটির চোখে। সে সামনে দাঁড়াতেই হা-হা করে কাঁদতে শুরু করল যুবক। আর, প্রায় প্রলাপের মতো বলতে থাকল—দেখেন, বাবু দেখেন! কী করেছে আমার আব্বা!
সে তুলে ধরল গামছা। আর সিদ্ধার্থ দেখল সেই বীভৎসকে। বাঁ চোখের জায়গায় এক ব্যর্থ রক্তের দলা। লোচন পরাস্ত করে রেখে দিয়েছে চক্ষুগহ্বর কেবল। সেই হা-গহ্বরে শুধু রক্ত মাংস স্নায়ু ও লসিকা। খাবলে তুলে নিয়েছে কেউ চোখ এই প্রৌঢ় মানুষটির।
সে-দৃশ্য সহনীয় নয়। সিদ্ধার্থ উত্তেজিত হল। চিৎকার করল সে—এখানে কেন? এখানে কেন এনেছ? এখুনি ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।
—কী করেছে দেখেন বাবু! কী করেছে! চোখ খুবলে নিয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে এখানে কিছু হবে না।
সিদ্ধার্থ, এক মুহূর্ত দেরি করাও বাতুলতা, এই বোধে ছুটে গেল বাগানে। বোধিসত্ত্ব, সে কিছু বলার আগেই বললেন-গাড়ি ধুচ্ছে রামু। ওর কাছেই চাবি আছে। গ্যারেজে চলে যাও।
বাড়ির পেছনের দিকে গ্যারেজ। সে ছুটল সেদিকে। এ গাড়ি সে সাধারণত ব্যবহার করে না। বোধিসত্ত্বও করেন না। এ গাড়ি ছিল তার মায়ের জন্য। এখন একে শুধু সচল রাখা হয়।
গাড়ি বাড়ির সামনের দিকে এনে ধরাধরি করে লোকটিকে পেছনের আসনে তুলে দিল সে। নিজে সামনে বসল। এখনও সে জানে না কে এ কাজ করেছে। বা কারা করেছে। কিন্তু প্রথমেই তার মনে হল, সরকারি হাসপাতাল পুলিশের হস্তক্ষেপ চাইবে এবং দেরি করবে অযথা। সে রামুকে বলল—ডা. কোঙারের নার্সিংহোমে চল।