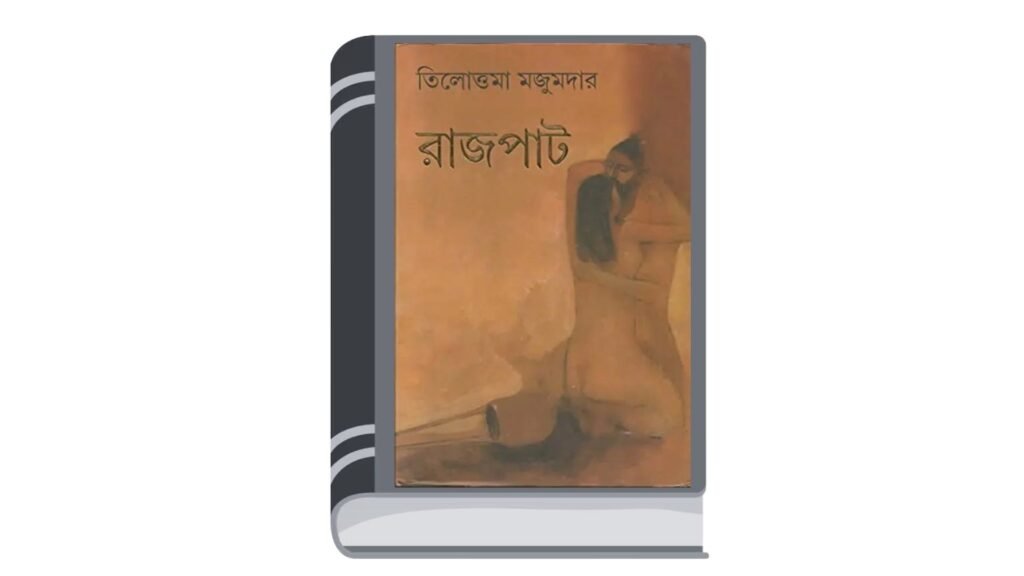রাজপাট – ৪১
৪১
চত্রি না মাসের দিনে
ঠাটা ভাঙা রইদ।
জামাই যাইন শ্বশুরবাড়ি
ভাই বন্ধুর সইদ ॥
জামাইয়াখানি আসলে হয়
বড় ধুমধাম।
পরিবাড়ি বিয়া পারে অইতে
খাইতে দেখতে আরাম।।
হক্কোল অক্তে খাওয়া যায়
পুয়াপুড়ি সইতে।
বেশ করি ঢালি দেয়
কইতে না কইতে।।
.
রমজান মাস পড়েছে। তেকোনার ঘরে ঘরে এখন রোজা রাখার পালা। ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই রোজা রাখে। যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলাম ধর্ম অধিষ্ঠিত, তার মধ্যে প্রধান হল রমজান মাসের তিরিশ রোজা এবং পাঁচ ওযুক্তের নামাজ। প্রত্যুষের প্রথম নামাজ ফজর। মধ্যাহ্নের নামাজ জোহর। অপরাহ্ণেরটি আসর। সন্ধ্যার নামাজ হল মগরেব এবং মধ্যরাত্রির পূর্বভাগে পালিত পঞ্চম ও শেষ অবশ্য পালনীয় নামাজ ঈশা।
রমজান মাসে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্জলা উপবাস—তার নাম রোজা। ইসলামে যে বর্ষপঞ্জী তৈরি হয়, তা চান্দ্রমাস ঘিরে। রোজার সময় চন্দ্রের উদয় এবং অস্ত এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ।
চন্দ্রাস্তের আগে, সেহরি গ্রহণ করা নিয়ম। সেহরি হল রোজার পূর্বাহ্নিক আহার। উপবাস ভঙ্গকালীন আহার হল ইফতার। রমজান মাসের শেষ সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলেই সে রাতটাকে বলা হয় চাঁদ রাত। রমজান শেষে ঈদের নামাজটি হল ঈদ-উল-ফিতর। ফিতর মানে দান। রমজানের শেষে ফেতরা দেওয়া বা খয়রাতি করা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। অনেক গৃহস্থ মুসলমান সপ্তাহে অন্তত একদিন দরিদ্র-মিশকিন বা অনাথ-এতিমদের আহার্যের ব্যবস্থা করেন। কোনও ভিক্ষাপ্রার্থী যদি মুসলমানের দুয়ারে এসে বলে—ভিক্ষা দাও গো মা, খ্যায়রাত দাও…গৃহস্থের কর্তব্য হাতের কাজ ফেলে রেখে আগে খয়রাত দিয়ে আসা। ভিক্ষুকের ধর্মাধর্ম এখানে কোনওভাবেই বিচার্য নয়।
রমজান মাসে ইফতার উৎসবে বরকত আলির গৃহে দাওয়াত বাঁধা থাকে চাটুজ্জেদের। চিরকাল। এবং চমৎকার সব ভোজ্য তারা প্রস্তুত করে তখন। গোস্ত হিন্দুর খাদ্য নয় বলে আলাদা করে খাসির মাংসও তৈরি করা থাকে। মোহনলাল যখন বহরমপুরে থাকত, তখন রমজান মাসে তার মন উৎসুক হয়ে পড়ত এই নিমন্ত্রণের জন্য। কোনও বছর আসতে না পারলে মন খারাপ হত রীতিমতো। বরকত আলির তিন ছেলের মধ্যে প্রথম দুটি তারই বয়সী। বয়সের সামান্য হেরফের বন্ধুত্বের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে না। এরশাদ ও হাসনাতের সঙ্গেও মোহনলালের ছিল সহজ সম্পর্ক। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই যখন যুবা হয়ে উঠল তখন বন্ধুত্বের মধ্যে এসে পড়ল শিক্ষার দূরত্ব। তারা যখন ছোট ছিল, তখন এ গ্রামে স্কুল ছিল না। একটি মক্তব ছিল মাটির মসজিদের ইমাম ফৈজুদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধানে। তাতেও লেখাপড়ার কর্মটি খুব নিয়ম করে চলত এমন নয়। বৃদ্ধ ফৈজুদ্দিন সাহেব এখন পাকা মসজিদের ইমাম। মক্তবও তাঁর এখন খোলা আছে। প্রাইমারি স্কুল হয়ে যাওয়ায় এখন কেউ মক্তবে যায়, কেউ যায় স্কুলে। কেউ দু’ জায়গাতেই হাজির থাকে। কিন্তু কোথাও-ই নিয়মিত যায় না। যুধিষ্ঠির সেনের মাধ্যমিক পাশ মেয়ে কবিতা স্কুলে যাবার আগে ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি ঘুরে ঘুরে কয়েকজনকে সংগ্রহ করে স্কুলে নিয়ে যায়। পড়ায়। ছাত্রেরা যা শিখে আসে, বাড়ি ফিরে সব ভুলে যায়। মেরে-ধরে পড়তে পাঠানোর কোনও দায় নেই বাবা-মায়ের। কী হবে? শেষ পর্যন্ত তো সেই হাল ঠেলবে!
ইমামসাহেব এই গরহাজিরায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলেন—বারোটা সুরা মুখস্থ করুক অন্তত। না হলে ধর্ম-কর্মও তো করতে পারবে না।
তা বটে। ধর্ম-কর্ম করতে না পারা অপরাধ। লোকে চিন্তিত হয়। তারপর আপনাকে আপনি ভরসা দেয়— শিখে যাবে! ওমনি জেনে যাবে। আমরা কী করে জানলাম!
ইমামসাহেবের সেই গরহাজির, পালানো ছাত্রদের মধ্যে ছিল এরশাদ ও হাসনাত। যদিও বরকত আলি তাদের অন্তত হাই মাদ্রাসা পাশ করাতে চেয়েছিলেন। ছেলেদের বাইরে রেখে পড়ানোর জন্য তিনি কিছু খরচ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কোনও সন্তানই তাঁর সেদিকে আগ্রহ দেখায়নি। অথচ পরিণত চিন্তা শিক্ষিত এবং শিক্ষাবিহীনতার মধ্যে টেনে দিয়েছে অভিমানী দূরত্ব। মোহনলালের সঙ্গে বরকত আলি এখন যত সহজ, এরশাদ ও হাসনাত তেমন নয়। তারা চাষ-বাস করছে। বিবাহ করে পুত্রোৎপাদন করেছে। এবং রাজনীতি করছে। তেকোনা গ্রাম সংসদ উন্নয়ন সমিতিরই তারা সদস্য।
মোহনলাল এই দূরত্ব চায় না। কিন্তু এই মধ্যবর্তী শৈথিল্য সে অতিক্রমও করতে পারছে না। কেন পারছে না সে জানে না। কিন্তু এটুকু উপলব্ধি তার আছে যে তার জায়গায় সিদ্ধার্থ থাকলে এই দূরত্ব নিমেষে চলে যেত। হয়তো তৈরিই হত না। সিদ্ধার্থ যত সহজে যে-কোনও শ্রেণির মানুষের আপনার হয়ে ওঠে, যত অনায়াসে, মোহনলাল তা পারে না। অথচ সে হতে চায় তেমনই। সিদ্ধার্থের মতোই। কিংবা সিদ্ধার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া কেউ। সে আশা করছে, গ্রামে থাকলে, ক্রমাগত মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনায় সে হয়ে উঠতে পারবে গ্রামেরই একজন।
কাজটা সহজ নয়। কারণ যে-আকাঙ্ক্ষা তাকে গ্রামে আকর্ষণ করেছে, তার বাইরে আর কোনও টান গ্রাম সম্পর্কে সে বোধ করে না। এ তার নেতা হয়ে ওঠার পদক্ষেপ মাত্র। শহরে সিদ্ধার্থের সংসর্গে সে কখনও হয়ে উঠতে পারবে না স্বয়ম্ভূ। দু’জন পরাক্রমশালী ব্যাঘ্রেরই মতো তাদের অঞ্চল পৃথক হওয়া দরকার। সে শহরে থেকে, বড় বড় নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় থেকে নিজেকে জাহির করবে না সিদ্ধার্থর মতো। সে প্রথমে পঞ্চায়েত জয় করবে। তারপর ব্লক জয় করবে। তারপর যাবে জেলাপরিষদে। কতদিন লাগবে? কত বছর? পনেরো? একজন রাজনীতিবিদের পক্ষে পনেরো বছর কিছুই নয়। পনেরো বছর পর তার বয়স মাত্র চল্লিশ। খুব হিসেব করে চললে এরই মধ্যে সে হয়ে যেতে পারে বিধায়ক পদের প্রার্থী। কিন্তু এই সমস্তই তাকে করতে হবে অল্প অল্প করে। ধীরে ধীরে সে এই অঞ্চলে হয়ে উঠবে এমন এক নাম যা মানুষের উচ্চারণে অগ্রাধিকার পাবে।
তার বাড়ির লোক তার এই সিদ্ধান্তে খুশি নয়। সোমেশ্বরের ধারণা- কাপড়ের দোকান অচিরেই বন্ধ করে দিতে হবে তা হলে। তাঁর পক্ষে, আত্মীয় বিবর্জিত অবস্থায়, একা অধিকাংশ দিন বহরমপুরে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। আর কাপড়ের দোকান বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ ধনলক্ষ্মীর বিতাড়ন। একা, কৃষিলক্ষ্মী নন ততখানি ধনদা।
কথা মিথ্যে নয়। বহরমপুরে পিতার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন মায়ের জন্য তার প্রাণ পুড়ত। গাঁয়ের জন্যও। একসময় সমস্ত টানের বাঁধন আলগা হতে হতে সে হয়ে উঠল শহুরে যুবক। শিক্ষিত। আপাদমস্তক পরিশীলিত। ক্ষৌরকর্মের পর গালে সুগন্ধীমাখা তার স্বভাব। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন চুলে শ্যাম্পু দেওয়া তার প্রিয় বিলাসিতা। স্নানান্তে প্রতিদিন গায়েও সে ছড়িয়ে নেয় সুবাস।
তেকোনা গ্রামের হাওয়ায় ভাসে মলের গন্ধ, গোবরের দুর্বাস ও ভৈরবের পাড়ে জমে থাকা কাদার পাঁক-গন্ধ। তার মধ্যে তার ওই দেহবাস দু-চার দিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সম্ভার ফুরোলে মোটরবাইক নিয়ে ছুটতে হয় হরিহরপাড়ায়। শ্যাম্পুর ছোট ছোট পাতা সে পেয়ে যায় মরালীর ছোট ছোট দোকানে। কিন্তু কিনতে মন চায় না। কবেকার, কে জানে! ধুলো পড়া, কোঁচকানো পাতা। কোনও উৎসব আয়োজন ছাড়া এখানকার মানুষের নিত্য শ্যাম্পু করার অভ্যাস আজও তৈরি হয়নি।
অসুবিধে তার বিস্তর। পণ্যসম্ভারের অসুবিধে। তার বিশুদ্ধ ভাষার সঙ্গে স্থানীয় পরিভাষার অসুবিধে। গ্রাম্য জীবনের যে নিজস্ব ধীর লয়, তার সঙ্গে মানানোও অসুবিধে। তবু তার স্বপ্ন তাকে টেনে রাখছে এই গ্রামে। স্বপ্ন— নেতা হওয়ার। সিদ্ধার্থকে ছাড়িয়ে যাবার। এ স্বপ্ন ক্ষুদ্র না বৃহৎ তা ব্যাখ্যাতীত। ক্ষুদ্র ও বৃহতের তুলনা ব্যক্তিবিশেষে তার মাত্রা পরিবর্তন করে। অতএব এই আপেক্ষিকতা ঘিরে সদাই তৈরি হয় ব্যাখ্যারহিত জীবন। মোহনলালও তেমনই জীবনের পশ্চাতে ধাবমান, যার সম্পর্কে তার নিজের ধারণাও স্বচ্ছ নয়। মাঝে মাঝে সে ভাবে, সেদিন, হরিহরপাড়া থানা ঘেরাওয়ের সময় গুলিটা তার গায়ে লাগল না কেন! তার বিচারে সিদ্ধার্থ অবশ্যই ভাগ্যবান যে সে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। গভীর ক্ষত না-হওয়া সত্ত্বেও সে ওই ঘটনার জন্যই বাগড়িতে, প্রাতঃস্মরণীয় নাম। ‘অত সাহস আর আজকাল ক’জন নেতার হয়?’ এমন সব বলাবলি শুনেছে সে। ক্ষোভ জন্মায় তার মনে। ঝড়ে বক মরে আর কেরামতি দাবি করে ফকির।
স্কুলে পড়ার সময় একদিন সিদ্ধার্থ না এলে তার মন খারাপ করত। সিদ্ধার্থর সকল ব্যাখ্যা, সকল বক্তৃতার প্রতিই তার ছিল মুগ্ধ অনুসরণ। অথচ সে যখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল সিদ্ধার্থকে ছাড়াই, তখন তার মোহ কেটে গেল অচিরেই। বরং বিগত অনুগমনগুলির জন্য নিজের কাছেই নিজে সে হয়ে উঠল ক্ষুদ্র, অসম্মানীয়। অনুগত হওয়ার মধ্যে মর্যাদা কোথায়?
ময়না বৈষ্ণবীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তার এই বোধকে ত্বরান্বিত করেছে সন্দেহ নেই। আপাতত এই গ্রামে স্থিত হয়ে বসার শক্তি সে অর্জন করতে চায়। অমরেশ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। হরিহরপাড়া উচ্চতর বিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে সে ঢুকে যেতে চায়। আর দু’বছর পরে এরকম একটি পদ খালি হতে চলেছে। এখন থেকেই ওই পদ অধিকারের পরিকল্পনা চলছে। সি পি আই এম-এর প্রার্থী হিসেবে সে আছে। কংগ্রেসেরও প্রার্থী আছে একজন। সে হিসেব করে দেখেছে, তার চাকরির জন্যই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে অমরেশ বিশ্বাসের জয়লাভ করা দরকার।
দলের সারাক্ষণের কর্মী হতে চায় সে সিদ্ধার্থের মতোই। কিন্তু একেবারে উপার্জনহীন হতে চায় না সে। পারিবারিক আয় তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তার ব্যয়নির্বাহের জন্য দায়ভাগী হয়ে থাকতে হয় অন্যদের কাছে। সে জানে নেতা হয়ে উঠতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। যদিও সে উপার্জন করলে তা হবে ঘরের টাকা। এ টাকা শুধু নেতৃত্বের জন্য ব্যয় করতে সে পারবে কি না শেষ পর্যন্ত সে জানে না। বনের মোষ তাড়ানোর টাকা সম্ভবত তাকে সংগ্রহ করতে হবে বন থেকেই। কীভাবে? সে এখনও জানে না। কিন্তু শিক্ষকতার চাকরির জন্যও সে তার প্রচেষ্টা থামাবে না। শুধু অর্থ নয়, এই কাজ তাকে দেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা।
যদিও এই পন্থা গৃহসমস্যার সমাধান করে না। তাদের বহরমপুরের দোকান এবং তেকোনা গ্রামের জমিজমা সামলানোর যুগপৎ দায়িত্ব পালনের কোনও সুরাহা হয় না তাতে। এই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন একমাত্র নয়াঠাকুমা। তিনি বলেছেন— মোহনের বিয়ে দাও তোমরা। আমি নাতি-নাতবউ নিয়ে এখানে থাকি। নন্দিনী শহরে চলে যাক।
মোহনলাল একবার আপত্তি করার চেষ্টা করেছিল— আমি এখনই বিয়ে করব না।
নয়াঠাকুমা বলেছিলেন- তুমি যদি সবকিছুই নিজের মতে করতে চাও তা হলে কী করে হবে?
সেও আর আপত্তি করেনি। সত্য কথা বলতে গেলে, বিবাহে তার খুব আপত্তিও নেই কারণ ইদানীং শরীর অহরহ জাগে। বর্ধমানে হস্টেলের ঘরে ভিডিও এনে তারা নীলছবি দেখত। সংগ্রহ করত পত্র-পত্রিকা। নগ্ন মেয়ের ছবি বা সঙ্গমদৃশ্য দেখতে দেখতে বন্ধুরা পাশাপাশি বসে হস্তমৈথুন করত। সেইসব স্বাদ হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শরীরে আকাঙ্ক্ষা কামড়ায়। নেতৃত্বের স্বপ্ন বা হরিহরপাড়ায় স্কুলের শিক্ষকতার পরিকল্পনা তার প্রশমন ঘটাতে পারে না। সে অতএব ভদ্রতাবশত বাইরে খানিক আপত্তি করলেও ভেতরে একটি নারীপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে।
শহরে থাকার জন্য কৃষি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই তার। তাদের কৃষিজমি ও উৎপাদন বিষয়ে তার বাবা আবদুস মল্লিকের ওপর সর্বাংশে নির্ভর করেন। তারও উপায় নেই এ ছাড়া। সেদিন আবদুস বলছিলেন— তুমি গ্রামে থাকতে চাও শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। এইবার সব বুঝে নাও। আমারও তো বয়স হচ্ছে। সোমেশ্বর বুঝতে চায় না।
—আমি আর কী বুঝব! আপনি যখন আছেন!
সে বলেছিল। আবদুস বলেছিলেন— আমি তো চিরকাল থাকব না। দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে।
—দায়িত্ব আর কী বুঝে নেব চাচা? আমার সময় কোথায়?
—তা বললে হয়? আমি সব দেখাশোনা করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলাম। ভৈরব সব জমিজমা কেড়ে নিয়েছিল। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছিলাম। ভিটেটুকুও ছিল না। তোমাদেরও অনেকখানি জমি গিয়েছিল। তবু সোমেশ্বর কাঠা তিনেক জমি দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল, ঘর বানাও, হাঁস-মুরগি পালন কর। আর আমার যা আছে, নিজের মনে করে দেখাশোনা করা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তার জমিজমা দেখে আসছি। আল্লার দোয়ায় সংসারে অভাব নেই। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। এখন দুই ছেলে আছে বাকি। তাদের একটা ব্যবস্থা করতে হয়।
—বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে?
মোহনলাল জিগ্যেস করেছিল। আবদুস মল্লিক বলেছিলেন— সোমেশ্বর আমার সকল জানে।
—কী করছে ওরা এখন?
—তোমাদের জমিতেই তারা খাটে। নাসের আর হাফেজ। কৃষিকাজ শিখেছে ভাল দু’জনাই। নিজেদের জমিতেও হাল ধরে। তবে সামান্য জমি আমার। একজন কাজ করলেই অনেক। তার পরেও হাতে অবসর থাকে। তখন তোমাদের জমিতেই লাগিয়ে দিই।
—তা হলে কাজ তো করছেই।
—হ্যাঁ। তা করছে। সোমেশ্বরকে বলেছিলাম, আমার বয়স হচ্ছে। তদারকির কাজে আস্তে আস্তে নাসেরকে লাগিয়ে দিই। বেইমানি করবে না আমার ছেলে।
—বাবা কী বললেন?
—সোমেশ্বর বলেছে লাগিয়ে দিতে।
—তা হলে তো হয়েই গেল।
—না। তবু তোমাকে জানাতে হয়। আমাদের দিন চলে যাচ্ছে। এবার তোমরা বুঝে-শুনে নাও। নাসেরকে তুমি বিশ্বাস করবে কী করে? নাসেরই বা তোমাকে মান্য করবে কেন? তোমাদের চেনাজানা হওয়া দরকার।
—সে হয়ে যাবে।
তিনি তখন আড়ালে অপেক্ষমাণ নাসের এবং হাফেজকে আহ্বান করেছিলেন। তারা সামনে এসেছিল। নাসের মোহনলালেরই বয়সি বা তার চেয়ে কিছু বড়। হাফেজের বয়স আঠারো- উনিশ।
তারা আসতেই আবদুস বললেন – সালাম কর। সালাম কর। ইনি ছোটবাবু। চিনিস ছোটবাবুকে?
মোহনলাল গম্ভীর হয়ে ছিল। সারা মুখে মেখে রেখেছিল মনিবি একপ্রকার। এরা তাকে চিনবে না কেন? দেখছে ছোট থেকে। সে-ও দেখেছে। তবে আবদুসচাচার ছেলেরা তার বন্ধু হয়নি কখনও। একমাত্র এরশাদ আর হাসনাত ছাড়া গ্রামের আর কোনও সমবয়সিই তার বন্ধু ছিল না।
আবদুস চাচার ছেলেরা, নাসের আর হাফেজ তাকে যথার্থ অভিবাদন করে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। তার মনে হল, আবদুস মল্লিক ভূমি হারিয়েছিল ভাঙনে। ওই তিন কাঠা দানের জমি ছাড়া আর যদি জমি না থাকে তাঁর তা হলে কি তাঁকে ভূমিহীন কৃষক বলা যায়? যদি ভূমিহীন হন তিনি তা হলে এতদিনে ভূমিবণ্টন রীতি অনুযায়ী তাঁর কি জমি পাওয়া উচিত ছিল না? কথাটা ভেবে তার নিজেরই নির্বোধ লাগল নিজেকে। ভূমি বণ্টিত হলে কার জমি থেকে বণ্টন হবে? তাদেরই কি নয়? এ গ্রামে তাদের জমির পরিমাণ সর্বাধিক। কত, সে জানে না। বেনামি জমি আছে কি না, জানে না তা-ও। বরং সবই জানে ওই আবুদস মল্লিক। সে অতঃপর প্রশ্নটা না করে পারল না। বলল-এই দীর্ঘ সময়ে আপনার আর জমি-জমা হয়নি?
হাঁ-হাঁ করে উঠলেন আবদুস—হয়েছে হয়েছে। কেন হবে না? সোমেশ্বর আমার সব বিষয়ে খেয়াল রেখেছে। আটবিঘে জমি ছিল আমার। ওপারে পয়োস্তি হওয়ার পর যখন জমিদখলের সময় এল তখন মারামারি লেগে গেল বহেরার সঙ্গে তেকোনা গ্রামের। তখন পঞ্চায়েত এত সক্রিয় ছিল না। হরিহরপাড়া ও ডোমকল থানার দারোগাবাবুরা এলেন। কংগ্রেসের আমল তখন। যুধিষ্ঠির সেনের বাবা দশরথ সেনের খুব দাপট। তিনিও এলেন। সকলের সামনে বিলিব্যবস্থা হল। সোমেশ্বর আমার জন্য দশরথ সেনের কাছে গিয়ে বলল। ও তো রাজনীতি করেনি কখনও। দশরথ সেনকে গিয়ে বলল, কাকা! এর সব গেছে। একে জমি দিতেই হবে। যতখানি জমি গিলেছিল ভৈরব, ততখানি জমায়নি। জমিতে টান পড়ল। অনেক হিসেব-নিকেশ করে বিলি-ব্যবস্থা হল। আমি পেলাম আট কাঠা। পরে ওপারের জমি বিক্রি করে এপারে দু’বিঘে জমি কিনেছিলাম আজ্জু সরকারের থেকে।
—আজ্জু সরকার কে?
—তুমি চিনবে না। ছোটবেলায় দেখেছ। মারা গেছে আজ্জু। তার ছেলে আছে এখন। নিসার। চোর বলে বদনাম আছে। চুরি করেই সংসার চালায়। কিন্তু ধরা পড়েনি কখনও। একেবারে সাফা হাত।
—ও। তা জমি ওই দু’বিঘে?
—হ্যাঁ বাবা। জমি ওই দু’ বিঘে। বছরে তিনবার চাষ করলে আয় মন্দ না। কিন্তু দুই ছেলেকে ভাগাভাগি করে দিলে আর থাকে কী? তাই বলছিলাম, নাসের এ কাজটা আস্তে আস্তে ধরুক হাফিজকে পরে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
সে মনে মনে হিসেব করছিল। কংগ্রেসের দশরথ সেন সাহায্য করেছিলেন আবদুস চাচাকে। সেই ঋণ কি আজও শুধে যাচ্ছেন না ওঁরা? তার মাথায় জয়ের নেশা জাগছিল। জাগছিল আনুগত্যের প্রত্যাশা। আর ক’বছর আগে হলেই আবদুসচাচার পরিবারকে তাদের প্রজা বলা যেত। এখন আর কেউ কারও প্রজা হয় না। কিন্তু সে তো আনুগত্য দাবি করতে পারে। সোমেশ্বর রাজনীতি করতেন না, তাঁর এসব নিয়ে মাথাব্যথাও ছিল না। কিন্তু মোহনলালের না ভাবলে চলবে কেন! সে সরাসরি তাকিয়েছিল ছেলেদুটির দিকে। বলেছিল—পার্টি করিস?
—জি?
সহসা উত্তর দেয়নি তারা। আবদুস মল্লিক বলেছিলেন—পার্টি করে না ওরা।
সে আবার বলেছিল—ভোট দিস?
তারা মাথা নেড়েছিল। সে বলেছিল— গতবার পঞ্চায়েতে কাকে ভোট দিয়েছিলি?
–জি, অর্জুন সেনকে
আবুদস মল্লিক বলেছিলেন— আমরা সবসময় কংগ্রেসেরই সমর্থক।
তাঁর কথার মধ্যে গর্ব প্রকাশ পাচ্ছিল। কংগ্রেস সম্পর্কে এখনও অনেকের মনে আছে মোহ, যে-মোহ সেই স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মোহনলাল ভারী স্বরে বলল—এবারে আর কংগ্রেসকে ভোট দিবি না। আর হ্যাঁ, কোনও মিছিল করলে খবর দেব। মিছিলে আসবি।
—জি।
আবদুস মল্লিক কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়েছিল তার দিকে। তারপর বলেছিল- তুমি বললে তো যাবেই। হ্যাঁ যাবেই। কংগ্রেসের আর আছে কী এখন? কিছু না, কিছু না।
উল্লাস হয়েছিল তার। জয়ের উল্লাস। এক মুহূর্তে তিনটি লোককে জয় করেছে সে। নিজের জোরে জয় করেছে। জয়ের নেশায় ঘোর লেগেছিল। মনে হয়েছিল, ক্রমশ সে ছড়িয়ে পড়বে গ্রামে-গ্রামান্তরে। দলে আনবে তাদের যারা কখনও সি পি আই এম-এর সমর্থক ছিল না। ক্রমশ বিস্তার করবে সে নিজেকে। ক্রমশ অধিকার করবে সাম্রাজ্য। ক্ষমতা, ক্ষমতা! ক্ষমতা চাই তার। এত ক্ষমতা যা সিদ্ধার্থর বিকাশ থমকে দিতে পারে।
সিদ্ধার্থ! ভাবতে চেষ্টা করেছিল সে। তার জায়গায় সিদ্ধার্থ থাকলে নাসের ও হাফেজের সঙ্গে সে কী আচরণ করত? ‘আরে তোমাদের চিনতেই পারিনি’ বলে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হত হয়তো। ওদের চৈত্রের রোদে পোড়া, ঘামে ভেজা পিঠে হাত রেখে জানতে চাইত খেত-খামারের কুশল। বিবিধ সমস্যার কথা। কখনও জোর করত না কংগ্রেস ছেড়ে দেবার জন্য। বরং তার অন্তরঙ্গতায়, আলিঙ্গনের টানে ওই নাসের আর হাফেজ ধীরে ধীরে সিদ্ধার্থর অনুগামী হয়ে পড়ত।
কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল তার। সে কি ওই মনিবি গাম্ভীর্য রেখে, ওই জোর প্রকাশ করে ভুল করল?
না। বরং দাহ বাড়ছিল তার হৃদয়ে। সে সিদ্ধার্থকে অনুসরণ করতে যাবে কেন? সিদ্ধার্থ তার অনুগামীদের সঙ্গে ব্যবহার করে এমন যেন প্রত্যেকেই তার সহোদর। তার ঘেন্না হয়। আরে, তুমি আমার ভাই—বললেই কি লোকে ভাই হয়ে যায় নাকি? অত সহজই যদি হত সব, পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকতই না। সত্যিকারের সহোদর পরস্পরের বুকে ছুরি মারছে, সেখানে সকলের গলায় গলায় হওয়ার অর্থ কী! তা ছাড়া মানুষ কখনও নিজের সাংস্কৃতিক বলয় বিস্মৃত হতে পারে না। শ্রেণিবৈষম্যের বোধ মানুষের চেতনায় ব্যাপ্ত। তার থেকে মুক্ত ভাবলেই মুক্ত হওয়া যায় না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থ এবং শক্তি- এই সকলই মানবসমাজে শ্রেণিবৈষম্য জারি রেখেছে। তাতে অস্বচ্ছ আবরণ পরিয়ে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাকে কাজে লাগাতে হয়। সেখানেই নেতৃত্বের কৌশল। নেতৃত্বের মূল শক্তি জোর। গায়ের জোর। মনের জোর। অর্থের জোর। সিদ্ধার্থের অর্থের জোর কোথায়? নেই বলেই সে প্রীতির পথে জোর বাড়াতে চায়। মোহনলালের পথ প্রীতির পথ নয়। সে এক জোরে জমিয়ে তুলতে চায় অন্য জোর।
আপাতত তার প্রথম কাজ এ অঞ্চলে তার পরিচিতি বাড়িয়ে তোলা। গ্রামে এবং গ্রামের বাইরে। বরকত আলির সঙ্গে কথা হয়েছে তার। রমজান মাস শেষ হলে সে বরকত আলিকে মোটরবাইকে চাপিয়ে ঘুরবে গ্রামে-গ্রামান্তরে। যদিও প্রধান হিসেবে এই পঞ্চায়েতের সর্বত্র বরকত আলির সমাদর তবু গ্রামান্তরে যাবার খুব একটা গরজ তাঁর আছে বলে মোহনলালের মনে হয়নি। তেকোনা, মরালী ও তেকোনার পাশে রেশমকুচি ও আরও কয়েকটা ছোট গ্রাম নিয়ে এই পঞ্চায়েত। এর মধ্যে মরালীর জনসংখ্যাই সর্বাধিক। পঞ্চায়েতের দপ্তরও মরালীতে। এই পঞ্চায়েতের মোট ছ’টি আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যাবে শোনা যাচ্ছে। সব পঞ্চায়েতেই হবে। তখন অন্তত দুটি আসনে মহিলা প্রার্থী দিতে হবে। ব্যাপারটা ভাবলে মোহনলালের হাসি পায় সর্বাগ্রে। এই অঞ্চলে এমন কোন মহিলা আছে যে রাজনীতি নিয়ে ভাববে? নিজের ঠাকুমা ছাড়া আর কোনও মুখ তার মনে পড়ে না! যদিও, সে জানে, কোনও মহিলা রাজনীতি বোঝেন কি বোঝেন না-তার বিচারে আসন-প্রার্থনা আটকে থাকবে না। বিধি প্রবর্তিত হলে বিধি পালিত হবে। ফলাফল যাই হোক না কেন! চোর ধরে আনতে বললে নগরকোটাল বজ্রসেনকেই বেঁধে নিয়ে যাবে।
রেশমকুচির নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য নুর মহম্মদ কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এ ছাড়া এই পঞ্চায়েতের বাকি সব সদস্যই সি পি আই এম-এর। এই ক’দিনে মোহনলাল এটুকু বুঝতে পেরেছে, পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সমিতি এবং গ্রাম সংসদের সক্রিয় সদস্যরা তাদেরই দলভুক্ত। মুসলিম লিগের সামান্য ক’জন এবং কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় কিছু সদস্য কোনও কিছুরই বিরোধিতা করে না এখানে। কোনও দাবিও তোলে না। এখানকার নির্বাচনের প্রস্তুতি কীভাবে হয়, কেমন হয়, দেখবে সে এবার। দেখতে হবে তাকে আরও অনেক কিছু।
এই চৈত্রেই গরমের তাত লাগছিল তার। রাত্রির বসন্ত এখনও জিইয়ে রেখেছে কিছু শীতল বাতাস। কিন্তু দিনে শরীর ঝলসে যায় রোদ্দুরে। বিদ্যুৎহীন গ্রামে একটু বাতাসের জন্য প্রাণ আনচান করে তার। গ্রীষ্ম আসছে। ছুটির সময় যখন সে আসত এখানে, গ্রীষ্মের দুপুরে, তাপে নেতিয়ে পড়ত। ভৈরবের সরু ধারায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ত যখন-তখন। এখন সেই সহজ স্নানের বেলা যেন ফুরিয়েছে। কে জানে, এখানে থাকতে থাকতে ফিরে আসবে কি না সব পুরনো অভ্যাস। হয়তো আসবে। কিন্তু যে-নারী জন্মেছে তার জন্য, তার অজানিত ভাবী বধূ, সে কোথায়? যদি শহরের হয় সে, মানাতে পারবে কি এই পরিবেশে? নয়াঠাকুমা পেরেছিলেন। নন্দিনীও কাটিয়ে দিলেন একরকম। তাঁরা দু’জনেই শহুরে। শিক্ষিত। পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁরা দু’জনেই ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের পরিশীলন। কিন্তু যে নতুন আসবে সে? দিনকাল বদলে গেছে অনেক। সে বুঝতে চেষ্টা করে। নন্দিনীর মধ্যে যে পাথর-বিষাদ, কথা কম বলা আপাত নিরাসক্ত যে-আচরণ তাঁর, তা কি গ্রাম্য পরিসরের একঘেয়েমিতে কাটাবার জন্য? হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। তাঁর জীবনের ভেবে দেখার মতো বিষয় তাঁর স্বামীসন্নিধানরহিত দিনাতিপাত। এমনকী সন্তানসঙ্গ-বঞ্চিতও তিনি। সে আর তার বাবা ছুটিতে এলে নন্দিনী একটা গোটা সংসার পেতেন। প্রতি সপ্তাহের আসা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে আসত। দিনের আলোয় নন্দিনীর উজ্জ্বল মুখের ওপর দিনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ছায়া নামত। তার মন খারাপ হয়ে যেত তখন। শৈশবের অবুঝপনায় থেকে যাবার জন্য বায়না করত সে। কিংবা নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য আবদার করত। নয়াঠাকুমা বলতেন—তা যাক না। নন্দিনী যাক।
সোমেশ্বর বলতেন না।
সে বলত কেন না? মা কেন যাবে না?
—মা গেলে ঠাকুমা কার কাছে থাকবেন?
নয়া ঠাকুমা বলতেন তখন—আমি একাই থাকতে পারব। আবদুস আছে। বরকত আছে। ওপাশে সেনরা আছে। অসুবিধা কী!
সোমেশ্বর আবার বলতেন— না।
—ঠাকুমাও চলুক তা হলে?
—ঘর কে দেখবে?
—তালাবন্ধ করে দাও।
—না।
আর কোনও কথা খুঁজে পেত না সে। কাঁদত। এবং কাঁদতে কাঁদতে একদিন তার সয়ে গেল সব। মাকে ছাড়া বাঁচতে জানল সে। এবং মা-র ওই নির্লিপ্তি ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে মাকে বুঝতে চাওয়ার যে ইচ্ছে সে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তাও মরে গেল একদিন। এখন মা এক আলাদা জগৎ। অভিমানের আবরণে, অভিযোগের নীরব প্রকাশে নন্দিনী নিজেকে করে তুলেছেন এক শীতল প্রাসাদের অর্গলবদ্ধ মানুষ। কর্তব্যের কাঠিন্যে পা ঘষে ঘষে তিনি আজ নিজেই বড় কঠিন। এই পরিবার দায়ী তার জন্য। তাই নন্দিনীর নিকটে আসার সাধ্য এ পরিবারে কারও নেই। মায়ের চেয়ে ঠাকুমাকে মোহনলালের বুঝতে সুবিধা হয় অনেক বেশি। নন্দিনীর চেয়ে নয়া ঠাকুমাই তার অধিক কাছের।
এখন, তার জীবনে এক নারী আসার উপক্রমে সে পরিস্থিতি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে টের পেল, মায়ের ওপর অবিচার করেছে তারা সবাই মিলে। নয়াঠাকুমা ঘরবাড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য গ্রামে থেকে গেলেন। তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য নন্দিনীকে থেকে যেতে হল। তার বাবা সোমেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ব্যবসার জন্য অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিলেন বহরমপুরে। নন্দিনীকে মেনে নিতে হল। সে পড়াশুনোর জন্য বাবার সঙ্গে সঙ্গে গেল। নন্দিনীর বাধা দেবার কোনও উপায় পর্যন্ত রইল না। কেউ কখনও জানতে চায়নি— নন্দিনী, তোমার কী ইচ্ছা? তুমি কী চাও?
এমনকী এখনও পর্যন্ত তারা চালিয়ে যাচ্ছে এই স্বার্থপর অবিচার। আজ যখন নয়াঠাকুমা বিধান দিলেন, মোহনের বিয়ে দেওয়া হোক, নন্দিনী চলে যাক বহরমপুর-তখনও তাদেরই স্বার্থ দেখা হল। সে নিজের ইচ্ছেয় থাকবে গ্রামে, তাই নন্দিনীকে যেতে হবে শহরে। সোমেশ্বরের বয়স হয়েছে বলে নন্দিনীকে যেতে হবে। তারা এবারও কেউ নন্দিনীকে জিগ্যেস করেনি—তোমার কী মত? তুমি কোথায় থাকতে চাও?
সে টের পায়, নন্দিনীর সব ইচ্ছেগুলি স্বপ্নগুলি এই দোতলা বাড়িটির কোনায় কোনায় শুকিয়ে পড়ে আছে! সে দুঃখ বোধ করে। কিন্তু কোনও ভাবে এই দুঃখ লাঘব করা যায় কি না- এ ভাবনাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। এ জগতে কোনও কোনও মানুষ জন্মায় নীরবে। নিজেকে বিলিয়ে দেয় প্রতিবাদহীন। তাদের জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব এমনই অনুচ্চ যে, যা ঘটছে তাকেই ধরে নেওয়া হয় স্বাভাবিক। যেমন এখন এটাই স্বাভাবিক যে, নন্দিনী তাঁর প্রৌঢ় স্বামীর সেবাধর্ম পালনের জন্য শহরে যাবেন। ভারবাহী তিনি। বহন তাঁকে করতেই হবে। ধোপার গাধা ভারে বেঁকে গেলে ধোপা সহানুভূতিতে চুঃ-চুঃ শব্দ করে। কিন্তু ভার কম করে কিছু নিজের স্কন্ধে নেয় না। কারণ ভারের চাপে বেঁকে যাওয়াকেই সে গাধার ধর্ম মনে করে।
মোহনলাল সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার নিয়ে দোতলার খোলা বারান্দায় দাঁড়ায়। ফিকে জ্যোৎস্নায় নরম হয়ে আছে চরাচর। ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাম কখন। বিদ্যুৎ নেই বলে এখানে রাত্রি নামে তাড়াতাড়ি। ছ’ মাস হল সে গ্রামে বসবাস করছে। কিন্তু এখনও তার ঘুম আসতে দেরি হয়। ঘুম ভাঙেও দেরিতে। সে সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে থাকল বাইরের দিকে। বাইরে কিছুক্ষণ হেঁটে আসতে ইচ্ছে করল তার। নীচে এল সে। দরজা বন্ধ করবে কে? নীচের ঘরে দু’জন মুনিষ ঘুমোয়। নয়াঠাকুমা ও নন্দিনীর সুরক্ষার জন্য রাখা হয় তাদের। আলাদা করে কিছু পয়সাও তারা পেয়ে যায় এজন্য। সে তাদের ডেকে তুলল। বলল—আমি বেরোচ্ছি। দরজা বন্ধ করে দে। আমি ডাকলে খুলবি।
মুনিষ দু’জন, নেহাতই ষোলো-সতেরোর দুটি ছেলে, চোখ রগড়ে তাকায়। বলে—জি, এত রাত্তির! এখন কোথায় যাবেন বাবু?
সে কোনও উত্তর দেয় না। বেরিয়ে যাবার পথ ধরে। তখন একজন বলে—রাত্তিরে জিন-ফেরেস্তা ঘুরে বেড়ায় বাবু।
সে ফিরে তাকায়। বলে- তোরা তোদের কাজ কর।
সে টের পায় ছেলেদুটি নিঃশব্দ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে হিসেব করতে থাকে, কতজন মুনিষ তাদের, পরিবারের সদস্যসংখ্যা কত। এদের প্রত্যেককে সে টেনে আনবে নিজের দলে। এরা হবে তার নিজের ভোটার। নিজের। সে আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে এগোতে থাকে দক্ষিণমুখী। অন্ধকারের প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে তার চোখ সয়ে আসে। এবং একটি লোক তার দিকে ছুটে আসছে দেখতে পায়। শুনতেও পায় তার ব্যস্ত পদধ্বনি। এমনকী তাকে লক্ষ্য মাত্র না করে সে পাশ কাটিয়ে যেতে চায় দ্রুত। সে তার দীর্ঘ বাহু দ্বারা ধরে ফেলে লোকটির কাঁধ। লোকটি বোবা আর্তনাদ করে— আঁ আঁ আঁ!
সে এক ঝটকায় তাকে মুখোমুখি করে নেয়। সাধারণ যুবক চেহারা। কিন্তু ভয়ে চোখদুটি বিস্ফারিত। এই গ্রামীণ আঁধারে, তারাদের আলোর নীচে সেই বিস্ফারিত চোখের সাদা গোলক বীভৎস দেখায়। মোহনলাল তাকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়— কে তুমি? কোথায় গিয়েছিলে? এরকম ছুটছ কেন?
—জি-জি-জি জিনপরি! বাবু, জিনপরি!
—কোথায় জিনপরি?
—মা মাঠে। ন-নদীর ধারে।
মোহনলালের বিস্ময় জাগে। গ্রামের এইসব বিশ্বাসের সঙ্গে সে পরিচিত। শুধু গ্রামেই বা কেন! ভূত-প্রেত পরি-হুরির বিশ্বাস শহরেও রাজিত। কিন্তু স্বচক্ষে জিনপরি দেখে পালিয়ে যাচ্ছে কেউ—এমন সম্ভব? সে বলে— তুমি নিজে দেখেছ?
—জি, বাবু! একদম সাচ্চা কথা।
—নাকি অন্য মতলব?
—খোদা কসম বাবু। নিজের চোখে দেখলাম।
—চলো আমাকে দেখাবে।
—না। না। চলে গেছে।
—ও! তোমাকে দেখা দিয়েই চলে গেল?
—তারা মুহূর্তের জন্য আসে। তারপর মিলিয়ে যায়।
—তুমি কে?
—জি!
—জি!
লোকটি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। নিজেকে স্ববশে আনতে চায়। বোকা চোখে সে মোহনলালকে দেখে কিন্তু পালাবার চেষ্টা করে না। মোহনলাল তার ভাব-ভঙ্গি নজর করার চেষ্টা করে। কড়া গলায় ধমকায়।
— নাম বলো। এত রাতে কী করতে বেরিয়েছিলে?
—জি। আপনাকে চিনি আমি। আপনি মোহনবাবু। কিন্তু আমাকে আপনি চিনবেন না।
–সেকথা জানতে চাইনি আমি। আমি বলছি তুমি কে?
—জি। আমি আজ্জু সরকারের ছেলে নিসার। এই গ্রামেই থাকি।
—তা হলে তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি তা সত্যি? চুরিই তোমার পেশা? কী বলো? চুরি করতে বেরিয়েছিলে?
সে জিভ কাটে। কানে হাত দেয়। আল্লার নামে কিরা কেটে বিশ্বাস উৎপাদন করাতে চায় যে সে চোর নয়। মোহনলাল ভয় দেখায় তাকে এখন যদি লোক ডাকি আমি, তোর কী হবে রে নিসার?
নিসার নামের লোকটি পায়ে পড়ে যায় মোহনলালের। বলে— ওটা করবেন না বাবু। দাগি হয়ে যাব আমি। আমাকে চালান করে দেবে থানায়।
—সে তো তুই যে-কোনও দিনই ধরা পড়তে পারিস নিসার।
—তা পারি। কিন্তু কী করব বাবু?
—খাটবি। মাঠে কাজ পাস না? চল বসি।
এই অন্ধকার সম্ভবত তার মনিবি মানসিকতায় কিছু প্রলেপ দিয়েছিল। তা ছাড়া, লোক মানেই এখন তাকে মনে হয় ভোটার। অতএব তার হাল-হদিশের খবর নিতেই হয়। তা ছাড়া জিনপরি দেখে যে পলায়ন করে, তার কাছে মানুষ কিছু রহস্যগল্প দাবি করে। সে একটি বন্ধ বিপণির সামনে রাখা বাঁশের বেঞ্চ দেখায়। নিজে গিয়ে বসে ওই বেঞ্চে। নিসার তার পাশে বসে না। বসে পায়ের কাছে। প্রভুত্বপুলকে শিরশির করে মোহনলালের শরীর। এরকমই তো চায় সে। লোক এসে বসে থাকবে তার পায়ের কাছে। সকাল থেকে নানা আবেদন নিয়ে লোক দরবার করবে তার গৃহে। যেমন সে দেখছে রাসুদাকে। যেমন সে দেখে বরকত আলির বাড়ি। যেমন ইদানীং হয়ে থাকে সিদ্ধার্থর বাড়িতেও। ওই দরবারের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে সে। আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে—জিনপরির কথা কী বলছিলি?
নিসার উত্তেজিত হয়ে ওঠে আবার। বলে— জি, বিশ্বাস করেন। পরিষ্কার দেখলাম আমি। পরিষ্কার। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নাচছিল। আমি ভাবলাম, কে, পাগল মেয়েমানুষ! সামনে যেতেই দেখি, নেই। আবার পিছন ঘুরলাম, দেখি নাচতে নাচতে মাঠের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। এক পলক ফেলতেই আর নেই।
—সত্যি? কী করে বুঝলি ওটা জিনপরি?
—ডানা দেখলাম যে পিঠে। হ্যাঁ। বিশ্বাস করেন। ডানা পাতলা ফিনফিনে। তা ছাড়া এই এ-ধারে ছিল, এই ওধারে গেল কী করে? ডানা ছাড়া? ভয় করল খুব। যদি মেরে দেয়? যদি রক্ত চুষে খায়? ছুটলাম।
মোহনলাল সিগারেটে সুখটান দেয়। বলে জিনপরিকে কীরকম দেখতে নিসার?
—জি, সে আর কী বলব! সোমত্ত মেয়েছেলে। গায়ে একটা সুতোও নেই, মাথায় কী চুল! –বাঃ! তোর তো কপাল ভাল নিসার। ওই জিনপরিকেই চুরি করতে বেরোসনি তো তুই?— তওবা! তওবা! কী যে বলেন! ভয়ে আমার প্রাণ চলে যাচ্ছিল বলে। নিই আমি ছোট-খাটো জিনিস। ঘটি-বাটি। কী করব! জমিজমা নেই। পেট তো চালাতে হবে!
—পেট চালানোর জন্য চুরি করিস? মাঠে কাজ করিস না কেন?
—জি, করতাম। সেনবাড়ির জমিতে জন খাটতাম। একবার ওঁদের দুটো বলদ চুরি গেল। লোকে বলল আমিই দোষী। গ্রামের লোক পুলিশে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেনবাবুরা ছেড়ে দিলেন। বললেন, আর কাজে আসিস না। সেই যে বদনাম হল, আর কেউ কাজে নেয় না।
—কে নিল বলদগুলো? তুই-ই তো?
—বিশ্বাস করেন বাবু। আমি না। তবে কে নিয়েছে আমি জানতে পেরেছিলাম।
—কে?
–কারওকে বলবেন না তো বাবু?
—না। বল।
—ওই সমিরুদ্দিন, মাতিন শেখ, কালু মিঞা, মফিজ মিঞা। ওদের একটা দল আছে গ্রামে।
—তুই বললি না কেন ওদের কথা?
—যদি মেরে দেয় বাবু? বড় দল ওদের। তখন ওইসবই করত। গোরু ধরত। পাচার করত। এখন অনেক বড় বড় কাজ করে।
—বড় বড় কী কাজ?
—সে আমিও ঠিক জানি না। বর্ডার থেকে কী সব নেশার বস্তু আনে। ওপার থেকে এপারে লোকও পার করায় শুনেছি।
—হুঁ। বেশ খবর রাখিস তো।
নিসার এই প্রশংসায় গর্ব বোধ করে। মোহনবাবু বড় মানুষ। চাটুজ্যেদের মতো ধনী এ তল্লাটে নেই। কাঁহা কাঁহা থাকে ওই বাড়ির ছেলেরা। কলকাতা। দিল্লি। আমেরিকা। লন্ডন। তাঁরা সব সাহেব হয়ে গেছেন এখন। সে সোৎসাহে মোহনের কাছে নিজেকে খুলে দেয় বেশি করে। বলে— তা রাখি বাবু। এই রাতে ঘুরে ঘুরে কত কিছু জানা হয়ে যায়।
— যেমন?
—ওই যে ধরেন না কেন জব্বার মণ্ডলের কথা।
—কে জব্বার?
—একেবারে ওধারে থাকে। উত্তরে। বিঘে ছয়েক জমি আছে। চাষ করে খায়। জব্বার আর সুলেমান ॥ দুই ভাই থাকে। ওদের কারও তিনটার বেশি সন্তান নাই। কেন বলেন?
—কেন?
নিসার সরকার অকারণেই গলা নামায়। বলে— বাউলের ধর্ম নিয়েছে ওরা। গোপনে চৰ্চা করে। আখড়ায় গুরু এলে লুকিয়ে যায় মাঝরাতে। এমনিতেও যায় মাঝে-মধ্যে। সারা রাত সাধন করে। অথচ বাইরে দেখেন, খাঁটি মুসলমান। নমাজ পড়ে। রোজা রাখছে। মসজিদে যায়। কারওকে বলবেন না বাবু। গ্রামের কেউ জানলে ওকে আস্ত রাখবে না।
— কেন?
—বাউলদের আমরা পছন্দ করি না বাবু।
গম্ভীর দেখায় নিসারকে। এই অন্ধকারেও তার চোখ জ্বলে ওঠে। সে হিসহিস করে বলে- জব্বার মিঞা, সুলেমান মিঞা গোস্ত খায় না। আমি জানি। বাউলের নিষেধ আছে। শোনেন বাবু, সাচ্চা মুসলমান যে হবে, সে বাউলকে মানতে পারবে না। ওরা খারাপ বস্তু খায় বাবু। মল-মূত্র খায়। আরও কী কী খায়। থুঃ!
একদলা থুতু সে ছুঁড়ে দেয় অন্ধকারে। মোহনলালের গা গুলিয়ে ওঠে। শৈশব থেকেই গ্রামের প্রান্তে সে দেখে আসছে বাউল, দেখে আসছে আখড়া। বাউলের গান সে ভালবাসে। কিন্তু বাউলচর্চা বিষয়ে জানতে তার কোনও আগ্রহ ছিল না। সে ঘৃণাবোধ করে এবং নিসারের ঘৃণা সম্যক টের পায়। কিন্তু বুঝতে পারে না, জব্বারদের বিষয়ে জানা সত্ত্বেও নিসার কেন তা গোপন রাখতে চায়। সে এ প্রশ্ন না করে পারে না। নিসার বলে— রাত্তিরে ঘুরে বেড়াই। কত লোকের কত কীর্তির কথা জেনে ফেলি। সেগুলি প্রকাশ করলে আমার চলে না। কত পরিবারের কত গোপন কথা। সব কি বলা যায়?
—আমাকে বললি কেন তবে?
—জি আপনি লেখাপড়া জানা মানুষ। আপনি কথা পাঁচকান করবেন না আমি জানি। তা ছাড়া জেনেশুনে জব্বারদের ক্ষতি করব কেন? সাচ্চা মুসলমান অপরের ক্ষতি করে না।
—তাই নাকি? তা হলে চুরি করিস কেন নিসার? ওতে ক্ষতি হয় না?
—জি। সে তো পেটের দায়ে। চারটি পেট বাড়িতে। বউ-বাচ্চা! কী করি!
— কাল আসবি আমার বাড়িতে।
—জি।
—আবদুসচাচাকে বলে দেব। আমাদের জমিতে কাজ দেবে।
—জি।
—এরপর চুরি করা ছেড়ে দিবি তো?
—জি আল্লা কসম।
—নিজেকে সাচ্চা মুসলমান ভাবিস তুই নিসার?
—জি বাবু।
— পাঁচ ওয়ক্ত নামাজ পড়িস?
—সে সবসময় কি আর হয়!
—রোজা রেখেছিস?
—জি বাবু, আমাদের তো সারা বছর রোজা। গরিব মানুষ, অর্ধেক দিন না খেয়ে কাটে।
—বাঃ! সারা বছর রোজা করিস তুই! খুব ভাল। তা হলে চুরি ছেড়ে দিবি তো তুই?
—জি আল্লা কসম।
—না।
—জি বাবু!
—লোকজনের জিনিস তুলবি না। কিন্তু রাতে ঘুরবি। কে কী করছে জানাবি আমাকে। অন্য কারওকে এ কথা বললে তোকে পুলিশে দেব আমি।
—জি না। নিমকহারামি করব না আমি। কিন্তু রাতে যদি অন্য কেউ দেখতে পায়। চোর
ভাববে আমাকে।
—আমি দেখব তখন। কাজটা করবি কি না বল?
–রোজ বেরুতে হবে বাবু?
–এখন রোজ বেরুস?
—না। দিন বুঝে। রমজান মাসে বেরুনো মুশকিল। লোকে রাত না ফুরোতে জেগে ওঠে। ঘরে কিছু নেই বলে তবু এই আগরাত্রে বেরুলাম।
—পেলি কিছু?
—না। জিনপরি সব বেকায়দা করে দিল।
—কাল আসিস। দেখব
—জি।
অন্ধকারে কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন মোহনলালের ঘাড়ের কাছে এসে জমা হয়। এইবার সে একটি একটি করে তুলে নেবে হাতে। কারওকে ভয় দেখিয়ে জয় করতে হয়, কারওকে সুবিধে দিয়ে। সে নিসারের দিকে ছুড়ে দেবে বলে প্রশ্ন নিক্ষেপ করে।
—নিসার?
—জি।
—ভোট দিস?
— তা তো দিই।
কাকে দিস?
করম মণ্ডলকে নেতা মানি বাবু। মুসলিম লিগ। তিনি যে-ভোটে যেখানে দিতে বলেন, সেখানে দিই। গেল পঞ্চায়েতে বরকত আলিকে দিয়েছিলাম। বড় ভোটে কংগ্রেসকে দিয়েছি।
—হুঁ। ঠিক আছে। এবার আমি যাকে বলব তাকে ভোট দিতে হবে নিসার।
—জি।
—ওই জব্বাররা কোন দলের?
—ওরা কংগ্রেসের। ওদের বাপের আমল থেকে।
মোহনলাল উঠে দাঁড়াল এবার। ফিরে যাবে। হৃদয়ে সন্তোষ। আরও একজনকে জয় করল সে। এখন তার মনে হচ্ছে সে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেই লোকে তার দলভুক্ত হয়ে যাবে। দর্পণের সামনে দাঁড়ালে সে পরিতোষ লাভ করে। যথার্থ নায়কোচিত চেহারা তার। এই একটা জায়গায় সিদ্ধার্থকে ছাড়িয়ে সে অনেক দূর এসেছে। রূপবান সে। এই রূপের জন্য মুগ্ধ নারীচোখ দেখতে সে অভ্যস্ত। এ পর্যন্ত তার জীবনে নারী এসেছে অন্তত ছ’ জন। তার বেশিও হতে পারে। কলেজে বন্ধুরা বলত, মোহন ছ’ মাসে একজন করে প্রেমিকা পাল্টায়। কথাটা একদিকে সত্যি। কিন্তু পুরো সত্যি নয়। এইসব মেয়েরা তার রূপের আলোয় উড়ে আসত। তার নিজের কোনও তাগিদ ছিল না। গভীর প্রেমের সম্পর্ক তার কারও সঙ্গে হয়নি। তার রূপ আছে, বিত্ত আছে। মেয়েরা তার পদতলে পড়বেই। সে তৃপ্ত পা ফেলে। নিসার তার পিছু পিছু যায়।
.
মোহনলালকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিসার একা একা হেঁটে চলল বাড়ির দিকে। ধীর হয়ে গেল গতি। তখন জিনপরি দেখে ভয় পেয়েছিল সে। কেন পেল? চাঁদের আলোয় ওই অসম্ভব নগ্নতা তাকে পাগল করে দিয়েছিল সম্ভবত। আতঙ্কগ্রস্ত করেছিল। না হলে কত দিনই তো কত কিছু দেখেছে সে। ভয় পায়নি। সে জানে নিশুতি গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ায় তারা। সে দেখতে পায় নানাবিধ ছায়ামূর্তি। তারা ক্ষতিকারক নয়। বরং করুণ। সে মসজিদ পেরিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তার সামনে দু’ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে ছোট বালিকা। উলোঝুলো চুল। খালি গা। বুক নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। আহা! দাফালিদের মেয়েটা বুঝি। এ দুনিয়ার মায়া কাটাতে পারছে না। পারবে কী করে! এ কি কম টান! সে নিজেও কতদিন ভেবেছে মৃত্যুর কথা। মরতে পেরেছে কি? চৌর্যবৃত্তি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে দু’রকমভাবেই। রাতে ঘরে থাকতে চায় না সে। কারণ সে জানে তার বিবি তার পাশে শুয়ে ভাবছে অন্যের কথা। সে বেরিয়ে এলেই আসে একজন। এমন বিবিকে তালাক দিচ্ছে না কেন সে? কেন নালিশ করছে না পঞ্চায়েতে ন্যায়বিচারের জন্য? রাবেয়াবিবির কথা ভেবে বুকের মধ্যে টনটন করে তার। সেই একজন রাবেয়াকে কিছু টাকা দিয়ে যায়। সে-লোক নিজেও কিছু এলেমদার নয়। তলে লেংটি, উপরে জামা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সব। তবু ওই টাকা সংসারের কাজে তো লাগে। তার তো রোজগার ঘটি-বাটি বিক্রির আনি-সিকি। বাপ জমি বেচে খেয়েছিল। সে ভিটে বেচে খেয়েছে। রাবেয়ার বাপ ছোট ঘরখানা দিয়ে গেছিল রাবেয়াকে। সেখানেই গিয়ে মাথা গুঁজেছে নিসার। নিজের অজ্ঞাতে পাপ নেই। রাবেয়াকে তালাক দিলে সবার আগে সে-ই হয়ে যাবে গৃহহীন। রাবেয়া ওই লোকটার সঙ্গে নিকাহ করে নিতে পারে তখন। এতে তার লাভ কিছু হয় না। নিয়ম হল, মেয়েরা আশ্রয় হারানোর ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে। তার বেলা আল্লা দিয়েছেন সব উলটো করে। বিবির ঘরে থাকা মানে একরকম ঘরজামাই সে। আর ঘরজামাই হল কুত্তা।
পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে।
দোস্বা কুত্তা ঘর ঘর বুলে।।
তো কুত্তা জরুকা ভাই।
চৌথা কুত্তা ঘরজামাই।।
সে এক কুত্তা। তার নিজের যদি একটা তালপাতার প্রাসাদও থাকত, বাঁচত কিছু সম্মান কিন্তু সে হল একেবারে ন্যাড়া ন্যাংটা! না আছে ঘর, না আছে ঘোড়ি! কুত্তা সে। রাস্তারই কুকুর। মান-সম্ভ্রম না থাকলে মানুষে আর কুকুরে তফাত কী!
যে আসে রাতে সেও আর এক কুত্তা। সম্পর্কে সে রাবেয়ার দূরসম্পর্কের ভাই একরকম। কত ঘরের কত কেচ্ছা তার মুখস্থ। কিন্তু নিজের ঘরের কেচ্ছা সে কাকে বলবে। চাল নেই, চুলো নেই, নিজের বিবিকে পর্যন্ত বশ করতে পারে না—লোকে জানলে তাকে নিয়ে আমৃত্যু হাসাহাসি করবে।
বাড়ির দিকে যত এগোয় তত তার পা অসাড় হয়ে আসে। যদি গিয়ে দু’জনকে দেখে ফেলে একসঙ্গে! না। দেখতে চায় না সে। তার অস্তিত্ব জানে, সে না হয় একরকম। কিন্তু একেবারে সামনাসামনি দেখে ফেললে কি না মেরে থাকতে পারবে? দেখাবেও তা খুবই অশোভন। বিবির আশিককে হাতেনাতে ধরেও ছেড়ে দেওয়া দারুণ অবমাননার। তার চেয়ে এই ভাল। না দেখাই ভাল।
সে পায়ে পায়ে ভৈরবের পাড়ে চলে যায়। পাড়-ঘেঁষা এই জমি কার জানে না সে। একটু হেলে-থাকা নারকেল গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে। আকাশে অসংখ্য তারা তার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করে। রাবেয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সে বুকে হাত বুলোয়। এইখানে রাবেয়ার স্থান। এইখানে। সে গুনগুন করে, দিল করতা হ্যায়, সিনে সে লাগালু তুঝে…। গান গাইতে গাইতেই আকাশের দিকে তাকায় সে। আর চারখানি তারার চারটি নাম দিয়ে ফেলে ভালবাসা, পেয়ার, মহব্বৎ, আশিকি। প্রেম শব্দটি মনে পড়ে না তার। অতএব লক্ষ তারার একটি তারা নাম-বঞ্চিত হয়ে কাঁদে। তার কান্নার দ্রবণ পৃথিবীতে পৌঁছতে লেগে যাবে কত আলোকবর্ষ! এই ফাঁকে নিসার ভেবে নেয় একবার, সন্তানগুলি তারই কি না! যদি না হয়, তাতেই বা কী! পৃথিবীর সকল শিশুই তারই সন্তান, এমন উদার বোধে তার চোখে ঘুম নেমে আসে। হেলে যাওয়া নারকেল গাছে শরীর এলিয়ে সে সময় কাটাবার ছলে নিদ্রা যায়। আর তার নিদ্রিত শরীরের তলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে ক্ষয়ে যাওয়া মাটি। আপাত সমতল সেই আবাদি প্রান্তের গোপন গর্ভ ধসে পড়ার আয়োজন করে। চৌর্যবৃত্তির সজাগ অনুভূতির তাড়নায় ধড়ফড় করে জেগে যায় নিসার। সহসা তার মনে হয়, সে এক হেলা নৌকায় টাল খাচ্ছে বুঝি। কিংবা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে খসে পড়ছে শূন্যতায়। তার সামনে এক চওড়া ফাটল। আবাদের গাছপালা সমেত, নিসার ও নারকেল বৃক্ষ সমেত ঝুলে আছে ভূমিখণ্ড
মুহূর্তে লাফ দেয় সে। ফাটল পেরিয়ে ছুটে যায় এবং চরম উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে প্রাণপণ। একটু ধাতস্থ হয়ে ঘুরে দেখে। ফাটল বাড়ছে, দ্রুত, অতি দ্রুত, নারকেল গাছ ও আবাদি জমি নিয়ে নিঃশব্দে খণ্ড খণ্ড মাটি পড়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে। হায় আল্লা! কী সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল তার! কোন মৃত্যুর হাতছানিতে সে গিয়ে বসে ছিল নারকেল গাছের তলায়। যদি না জাগত সে সময়মতো! একতাল মাটি সমেত হুড়মুড়িয়ে পড়ত নদীতে। অতখানি জমি ভাঙছে, দমচাপা হয়েই মরত সে। নারকেল গাছের গোড়ায় তখনও তার গামছা। বিড়ে করে দিয়েছিল মাথার তলায়।
সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। জমিটার অনেকখানি নিয়ে নিল নদী। তার মনে হল, ভৈরবও চোর। তারই মতো চোর। রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে নিচ্ছে ডাঙা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ির দিকে পা চালাল সে। যার জমি, কাল সে সব দেখেশুনে কপাল চাপড়াবে। কৃষকের কাছে জমি তো জমি নয় শুধু, বুকের পাঁজর যেন। জমি ধসে গেলে অস্থি উপড়ে নেবার বেদনাই পায় তারা।
সকালে সাড়া পড়ে গেল গ্রামে। মোরাদ আলির জমি অনেকখানি ধসে পড়েছে নদীতে। প্রত্যুষে মাঠ করতে এসেছিল মোরাদ আলি। এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেছে। তিন বিঘে জমি তার। অন্তত আধ বিঘে চলে গেছে ভৈরবে। বাকিটাও যাবে। এই শুরু হল। পবিত্র রমজান মাসের সকল প্রার্থনা অর্থহীন হয়ে গেছে তার কাছে। সকলে ঘিরে দাঁড়িয়ে ধসে পড়া জায়গাটা দেখছিল। প্রত্যেকেই বিমর্ষ। এ-দৃশ্য এভাবেই ঘিরে দাঁড়িয়ে বহুবার দেখেছে তারা। এরপর কার পালা? ভাঙতে ভাঙতে পাড় এখন ফারুকের দোকান অবধি এসেছে। ছুঁয়ে ফেলেছে সেনবাড়ির রান্নাঘরের দেওয়াল। আগে ওই রান্নাঘর থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছিল নদী পর্যন্ত। সে সিঁড়ি আর নেই। কেবল ভাঙা-চোরা দেওয়ালের মতো খাড়া পাড়। এই বর্ষার পর ওই রান্নাঘর আর থাকবে কি না তার ঠিক নেই। ফারুক তার দোকানে দিনে টুকি-টাকি তেল-নুন বেচে। রাত্রে গোপনে বিক্রি করে দেশি মদ। এই করেই চলে তার সংসারের ন’টা পেট। দুই বিবি সহ আধডজন সন্তান। কত দিন চালাতে পারবে সে? পাড় ভাঙতে লাগে এক নিমেষ। কিন্তু উলটোদিকের পাড় গড়তে, পয়োস্তি হতে, সময় লাগে বছরের পর বছর। বালুচরে মাটির স্তর পড়ে কাশ ও তৃণ জন্মানোর সময় দিতে হয়। পুবপাড়ে এমন ভূখণ্ড তৈরি হচ্ছে এখন। সেই ভূখণ্ড, স্থিত হয়ে, বণ্টিত হয়ে, আবাদযোগ্য হতে এখনও অনেকদিন। যাদের জমি চলে যাচ্ছে, মধ্যবর্তী সময় তারা করবে কী? খাবে কী?
এ-সব উত্তর জানে না কেউ। কেবল এক অনিশ্চয়তায় দিন গোনে। অপেক্ষা করে খরা বা বন্যার। অপেক্ষা করে চাকলা-চাকলা হয়ে ভেঙে পড়া মাটির নিঃশব্দ মৃত্যুর জন্য। নিজেরও মৃত্যু মানুষগুলি প্রত্যক্ষ করে ওখানে।
মোরাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে মোরাদ অসহায় মুখ করে বরকত আলির দিকে তাকায়। বরকত আলি ততোধিক অসহায়তায় পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসেন। পঞ্চায়েত হয়েছেন তিনি। পঞ্চায়েত। অসহায় মানুষ তাঁর মুখের দিকে তাকায়। তিনি কী করবেন? গ্রামের কোন উন্নয়ন করবেন? অর্থ কোথায়?
পঞ্চায়েতের আভ্যন্তরীণ উৎসগুলি থেকে আয় হয় না বললেই চলে। বিভিন্ন কর, অভিকর, মাশুল, উপশুল্ক দেওয়ার ক্ষমতা যাদের আছে তারা ফাঁকি দেয়। অধিকাংশের কর দেবার সঙ্গতি থাকে না। আগে, নবাবি আমলে বা ব্রিটিশ শাসনকালে নব্য জমিদার শ্রেণির রাজত্বে তাঁতি, জেলে, কৃষক, কারিগরের পিঠে চাবুক মেরে কর আদায় করা হত। চাবুক মেরেও আদায় না হলে চাষির ঘরে আগুন দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করত জমিদার। এখন সরকার মালিক। তার কর অনাদায়ী থেকে যায় বছরের পর বছর। চাবুক নিয়ে কর আদায় করতে আসে না কোনও বর্বর। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরাও ফাঁকি দেয় নানা প্রকারে। কর আদায়কারী ব্যক্তিটির সঙ্গে রফা করে নেয়। করের ধার্য পরিমাণকে কমিয়ে আনে। মূল আয় গোপন করে। ফলে উন্নয়ন তহবিল শূন্য পড়ে থাকে। সরকারি অনুদান একমাত্র ভরসা। কোনও একটি নির্দিষ্ট চাহিদা কেন্দ্র করে এই অনুদান বরাদ্দ করে সরকার। পথনির্মাণ, পাড়ঘাট তৈরি, বন্যা হলে ত্রাণবন্টনের বস্তু ও অর্থ। তারও আছে নানান হিসেব। সরকারের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে আসে কর্মচারী, প্রধান ও উপপ্রধানের বেতন। সদস্যদের রাহাখরচ ও দৈনিক ভাতা। কিন্তু তা হলেও পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস এখনও যথেষ্ট নয়। নিজস্ব আয়ের সূত্র থেকে যে-সামান্য পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়, তাই দিয়ে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজ চালানোই অসম্ভব। এই অঞ্চলে পৌর সুযোগ-সুবিধা এত কম যে সেই সুবিধার ওপর অতিরিক্ত মাশুল বসিয়ে আয়ের পথও বন্ধ নব্বই শতাংশ গৃহে পায়খানা-প্রস্রাবাগার নেই যে আবজনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে পঞ্চায়েত অভিকর বসাবে। কোনও মেলা হয় না এখানে। পানীয় জল বলতে প্রধান ভরসা নদী। অর্থসঙ্গতি আছে যাদের, তারা আপন ব্যয়ে বসিয়ে নেয় নলকূপ। নদী থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে আছে চাহিদার তুলনায় অনেক কম সংখ্যক নলকূপ। দৈনন্দিন জীবনের জন্য সেখানে ভরসা পুকুরগুলি। সেই পুকুর পরিষ্কার হয় না কখনও। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে, রোগ-ব্যাধি দূর করতে নেওয়া হয় না কোনও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। আশে-পাশের কুড়িটি গ্রাম খুঁজলেও কোনও হাসপাতাল পাওয়া যাবে না। শহর সংলগ্ন দু’-একটি গ্রামে হাসপাতালের বাড়ি তৈরি হয়েছিল সরকারি ব্যয়ে। সেসব এখন গবাদি পশুর বিশ্রামাগার। গৃহপালিত পশু-পাখির ওপর মাশুল বসাতে পারে পঞ্চায়েত। কিন্তু বসিয়ে কী হবে? আদায় হবে না। পেটের জ্বালায় লোকে আপন বলদ বেচে দেয়। জমি-জমা ভিটে উজিয়ে দেয় সব। এসব মানুষ মাশুল দেবে কী! গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত নৰ্দমা অবধি নেই যে পঞ্চায়েত নর্দমা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে মাশুল নেবে।
পঞ্চায়েত এখন রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র। কিন্তু অর্থভাণ্ডারের উৎস নয়।
.
বরকত আলিও, ছোটখাটো হলেও, রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁকে দেয় সম্মান, সম্ভ্রম, কিছু-বা ক্ষমতা, কিছু গোপন প্রাপ্তি। এটুকুর জন্য তিনি আকুল। এটুকুর জন্য কোনও কোনও ব্যক্তি লোভাতুর। কেউ ঈর্ষাকাতর।
মোরাদ মিঞার জমির অনেকখানি ভেঙে পড়েছে বলে আজ গ্রামের জীবন শুরু হল দেরিতে। না হলে ছোটখাটো ভেঙে পড়া দেখে লোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং যে-যার কাজে চলে যায়। সকাল ন’টা মানে গ্রামের বেলা কম নয়। আবদুস মল্লিক মুনিষদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন নিসার এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। আবদুস মল্লিক বললেন— কী রে নিসার? এখানে হঠাৎ?
—জি চাচা। ছোটবাবু আসতে বললেন।
—ছোটবাবু?
—জি। কাল দেখা হয়েছিল রাত্রে, মানে ওই সন্ধ্যাকালে আর কী! আমার খোঁজখবর করলেন। কাজকর্ম নাই শুনে বললেন, আসিস, কাজ দেব।
—তোকে কাজ কে দেবে রে ব্যাটা চোর? মোহনলাল কি তোর ব্যাপার জানে?
নিসার নীরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। আবদুস মল্লিক নিসারের কথার সত্যতা যাচাই করতে ভিতরে গিয়েছিলেন। নয়াঠাকুমা বললেন- ওমা! একটা চোরকে ঘরে ঢোকাবি কি মোহন?
মোহনলাল বলল—ও তো ঘরের কাজ করছে না ঠাকুমা। করছে বাইরের কাজ।
আবদুস মল্লিক বললেন—তবু কাজে কামে বাড়িতে আসবে তো। দেখে যাবে কোথায় কী আছে।
—ও এ-বাড়িতে চুরি করবে না।
কথা বাড়াল না কেউ। ধীরে ধীরে কর্তৃত্ব গড়ে তুলছে একজন। এমনই সংসারের নিয়ম। বাপ বুড়ো হতে থাকে, ছেলে সংসারের দায়িত্ব তুলে নেয়। মেয়েরা সেই কর্তৃত্বের মুখাপেক্ষী। অতএব নিসার বহাল হয়ে যায়। চৌর্যবৃত্তি হতে উত্তরণ ঘটায় চরবৃত্তিতে। রাত্রে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। গতরাতে সে বেরিয়েছিল, অতএব গতরাতে সেই লোক এসেছিল রাবেয়ার কাছে। এখন দিন সাতেকের মধ্যে সে-ও বেরুবে না। সেই লোকও আসবে না অভিসারে। অনেকদিন পর যথার্থ কৃষিজীবীর মতোই কায়িক শ্রম করেছে সে আজ। অতএব রাত্রি ন’টা না গড়াতেই চোখে ঘুম নেমে এল তার। হাত-পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল সে।
কিন্তু ঘুম এল না মোহনলালের চোখে। রাত্রি আঁধারে অবিবাহিত পুরুষের শয্যা হয়ে ওঠে বেখাপ্পা রকমের বড়। প্রবাদ আছে এমন। সে-ও সেই প্রাচীন প্রবাদের অনূঢ় যুবকের মতোই এপাশ-ওপাশ করতে থাকল। কী এক ইচ্ছা সবল পা বেয়ে, জানু পেরিয়ে, ঊরুতে চেপে বসে মুখ ঘষে দিল তার শ্রীদণ্ডে। ধ্বজা হয়ে ফুঁসে উঠল তা। তার চোখে নেমে এল রাত্রির ফেরেস্তা। নিসারের দেখা জিন-পরি। যার গায়ে সুতোটুকু নেই। যার পিঠে ফিনফিনে ডানা। ঢাল চুলে মেঘ নামিয়ে সে নেচে বেড়ায় চরাচরে। হায়! কী অপূর্ব কল্পনা! সে জানে, নগ্নতার কল্পনা, যৌনদৃশ্যের কল্পনা যৌনক্রিয়াকে করে তোলে অনেক বেশি উপভোগ্য। অতএব সে কল্পনা আঁকড়ে ধরতে চায়। এবং উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমূল পিপাসায় সে উঠে বসে এবং ভাবে, শুধুই কল্পনা? নাকি ওই চোরচোট্টা নিসার সত্যিই নারী দেখেছিল! হতে কি পারে না? কিন্তু ডানা! হয়তো, কল্পনা ওই ডানাটুকু। বাকিটা বাস্তব! সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। এই অজ গাঁয়ে কে আছে এমন সাহসিকা? নাকি পাগলিনী কোনও? শহরের রাস্তায় এমন তো দেখা যায় ন্যাংটো উলঙ্গ উন্মাদ নারী! সে দেখেছে দু’বার এবং অন্যায় জেনেও নগ্নতা না দেখে পারেনি! এ রাতে এমন কি আছে কেউ, রাত্রে যার উন্মত্ততা ঘটে!
সে নেমে আসে নীচে। নিশি পাওয়া মানুষের মতো। ঘুমন্ত তরুণদ্বয়কে জাগিয়ে দোর খুলে পথে আসে। চলতে থাকে দক্ষিণমুখী। গতরাতে ওদিক হতেই এসেছিল নিসার। সে দু’পাশে রাখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ফিকে জ্যোৎস্না আজও ঢেলেছে চাঁদ। সে জ্যোৎস্না মাড়িয়ে হাঁটে। নদীপাড়ে দাঁড়ায়। কেউ নেই কোথাও। সে এগোতে থাকে আরও। দেখে জমি। দেখে গাছপালা। দেখে এবড়ো-খেবড়ো পথ। দেখে ভাঙা-পাড় ঘেঁষে ভৈরবের শীর্ণ চলে যাওয়া। কিন্তু জিন-পরি দেখা দেয় না তাকে। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে সে। নিদ্রাহীন রাত বিছানায় একলা শুয়ে কাটে। সারাদিন অবসন্ন হয়ে থাকে সে। বরকত আলির সঙ্গে আলোচনায় বসে না। দলে টেনে নেবার শিকার খুঁজতে ইচ্ছে করে না। খাদ্যে মেলে না রুচি। সমস্ত দিন এলোমেলো কাটিয়ে অন্ধকার ঘরে শুয়ে রাত্রি গভীরের প্রতীক্ষা করে। এবং একসময় নিশিগামী হয়। চাঁদের করুণা বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ে জ্যোৎস্না হয়ে। রাতজাগা পাখিরা সাক্ষী হয়ে থাকে। ভৈরবের জলধারা আসন্ন গ্রীষ্মের ত্রাসে কৃশ হয়ে যায় আজও বহতা থেকে। মোহনলাল নামের এক নেতৃত্বকামী যুবক অভিসারী হয়ে ফেরে একা। ভাবে সারাক্ষণ। সে কি সত্যি? সে কি মিথ্যা? সে কি কল্পনা? মরীচিকা? এবং দেখা না পেয়ে ফিরে এলে তার চোখের তলায় পড়ে গাঢ় কালির প্রলেপ। নয়াঠাকুমা ওই ক্লান্তির প্রকার দর্শনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। নন্দিনীকে বলেন— বয়সের ছেলে, ওর চোখের তলে কালি তো পড়বেই। তোমরা তাড়াতাড়ি পাত্রী দেখো বাপু। কোথায় কার পাল্লায় পড়ে যায়!
এবং এক নিশীথিনীর কল্পনায় মোহনলাল তৃতীয় রাত্রি বিহারে নির্গত হয়। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে সহসা সে লাভ করে তাকে। জল থেকে উঠে আসছে একাকী, নগ্ন, চুলে মেঘ টেনে আনা নারী। তার দেহের স্থানে স্থানে জমে আছে অন্ধকার।
এই দর্শনে শরীর অবশ হয়ে আসে তার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। পাড় ঘেঁষে দাঁড়ানো একটি ঋজু গাছের আড়ালে সরে আসে সে। গাছ আঁকড়ে ধরে। গাছতলায় জমে থাকা মলে তার জুতোসুদ্দু পা ডুবে যায়, সে বুঝতেও পারে না। সে অপলক দেখে ওই জিনপরি! নাকি ফেরেস্তা! নাকি তীব্র অপ্সরা কোনও, স্বর্গ হতে নেমে আসা— পথ ভুলে। সে ডানা খোঁজে। কই, ডানা কই! ওই ওই ওই তো! ফিনফিনে ডানা। চন্দ্রিমায় চিকচিক করে। সেই নারী নেচে ওঠে তখন। দুলে-দুলে ঘুরে-ঘুরে নাচে। সে-নাচের নির্দিষ্ট ছন্দ নেই, লয় নেই, ললিত বিভঙ্গ নেই। কিন্তু ঘন যৌবনভরা নগ্নিকার অঙ্গ ওঠা-পড়া, সঞ্চালন অপূর্ব তাল-বাদ্য সহকারে ছন্দ হয়ে ওঠে। অমন অপরূপ নৃত্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে তার। সে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায়। সেই মূর্তি তখন লঘু শরীরে উড়ে উড়ে যায়। পথ বেয়ে যেতে থাকে কোথায়!
যেয়ো না। সে বলতে চায়।
কে তুমি! জানতে চায় সে।
আর একটু দাঁড়াও!
এই মাত্র বলার আবেগ তাকে অস্থির করে মারে। কিন্তু স্বর ফোটে না। সে সম্মোহিতের মতো পিছে পিছে চলে। বাতাসে ভেসে ভেসে সে নারী দূরত্ব বাড়িয়ে চলে ক্রমে। সে গতি বাড়ায়। আরও বাড়ায়। আরও আরও আরও। উত্তেজনা, আতঙ্ক, কৌতূহল এবং এবং এবং তীব্র ভয় তার হৃদযন্ত্র ফাটিয়ে দিতে চায়। সে দৌড়য় তখন। উঁচু-নিচু কাঁচা পথ— দৌড়নো সহজ নয়। তবু সে ছুটে যায় প্রাণপণ। সেই নারী হাত দুটি তুলে দেয় দু’পাশে আর পাখনার মতো নাড়ে। তার মিহিডানা তিরতির কাঁপে। চাঁদের আলোয় চিকচিক করে তার স্বচ্ছতা। ওই উড়ল সে, ওই উড়ল, ওই, ওই, ওই— সে শক্ত হাতে ধরে ফেলে কাঁধ। দুটি কাঁধ ধরে ফেলে জোর করে নেয় তাকে মুখোমুখি। আর হাঁপায়। জোরে জোরে। জোরে জোরে। চোখগুলি মুখোমুখি অপলক। এর-ওর দুইয়েরই দুই চোখে ত্রাস। বিস্ফার। নারী তার হাত ছাড়াতে চায়। সে বজ্রজোরে ধরে। মেয়েটি জানু ভাঁজ করে বসে পড়ে তখন। সেও বসে আর ঠেলে দেয় তাকে। সে-নারী চিত হয়ে পড়ে। তার ফিনফিন ডানাগুলি মাটির শক্ত চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো হয় ভেঙে মেঘমল্লার কেশ ভুঁয়ে ছড়িয়ে যায়। সে চেপে ধরে রাখে নারী। যদি উড়ে যায়! যদি চলে যায় পরি! কিন্তু ফিনফিনে ডানা ভেঙে সে তখন মানবী প্রকার। তার গুরুস্তন ছড়িয়ে ঢলে পড়া। উন্মুক্ত ত্রিবলীতে চাঁদের চুম্বন নেমে আসে। সে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টাও করে না। মোহনলাল ঘন শ্বাসে স্বর ডুবিয়ে বলে— কে তুমি? কে? এভাবে… এই ভাবে… কে?
সেই নারী কথাটি বলে না। বরং বন্ধ করে চোখ। সে আর ফেরাতে পারে না তার খোলা চোখ। ছবির নিষ্প্রাণ নারী, নীলমাখা মিথ্যে দেহগুলি সকল উষ্ণতাসহ ধরা আছে হাতের মুঠোয়। সে এক ক্ষুধিত চিতার মতো ঝাঁপ দেয়। স্তন কামড়ে ধরে। এতটুকু আপত্তি করে না সেই নারী! বরং জানু ভাঁজ করে পুরুষের প্রিয় পথ বিস্তৃত করে দেয়। সে অনভ্যাসে আঘাত করে ভুল ভুল ভুল স্থানে বারংবার এবং সহসা অপার মসৃণতায় ধারণ হয়ে যায়। একবার, দু’বার, তিনবার মাত্র গমনাগমনে সে স্খলিত হয়ে ঢলে পড়ে খোলা বুকে। ধকধক করে তার হৃদযন্ত্র। একসময় উঠে বসে সে। যেন ঘোর ঘুম ভেঙে জাগরণ পৌঁছয় অচেনা জগতে। গাঢ় অবসাদে সে চায় ওখানেই শয্যা পেতে নিতে। কী অপূর্ব স্বাদে ভরে আছে দেহ! কী বিস্ময়ে জড় হয়ে আছে মন! সে দেখে জিন-পরিটির মুখ। বলে–কে তুমি?
এতক্ষণে কথা বলে সে নারী। বলে—সরেন। যেতে দ্যান।
—কে তুমি? এভাবে ঘুরে বেড়াও! কে?
সে বলে—চারিচন্দ্রের সাধিকা আমি গো। চাঁদের পুরুষ, আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। আজ যাই। কে দেখে ফেলে!
—কে তুমি? বলো! না বললে লোক ডাকব।
—ডাকো না ডাকো। আমি বলব এ আমার চাঁদ। আমারে ডেকেছে।
—ছিঃ!
—ছিঃ? ছিঃ কীসের গো চাঁদ? এবার যাই। এবার লজ্জা লাগছে গো আমার। এককণা সুতা নাই দেহে!
মোহনলালের হাত ছাড়িয়ে ছুট দেয় সে। কী মনে করে থমকে দাঁড়ায়। ফিরে আসে। বলে—চাঁদ! দু’দিন ছাড়া ছাড়া। কেমন?
এক ছুটে চলে যায় সে। ওড়ে না। নাচে না। গায়ে ধুলো-মাটি মেখে চাঁদের আলোয় হাজার প্রশ্ন রেখে চলে যায় সাধারণ নারীটির মতো। মোহনলাল বসে থাকে কিছুক্ষণ। অতঃপর অবসন্ন দেহ টেনে উঠে দাঁড়ায়। ঘরমুখে চলে। তার ভাবনাগুলি ভেঙে ভেঙে যায়। এতক্ষণে চটিতে মেখে যাওয়া, পায়ে লেগে যাওয়া বিষ্ঠার ঘ্রাণ তাকে বিচলিত করে। ঘৃণায় কুঞ্চিত মুখে ঘষে ঘষে বিষ্ঠা তোলে সে। পথপার্শ্বের ঘাসে মুছতে মুছতে যায়। তার মনে হয় সারা দেহে বিষ্ঠা লেগে আছে। সে নিজেকে বোঝাতে বোঝাতে ফেরে— আর আসবে না। এইসব ভাল নয়। কে এই মেয়ে সে জানে না। কেন সে এমন ঘোরে জানে না। অলীকের মধ্যে হতে পারে কোনও অকল্যাণ আছে। সে অন্ধকারে পায়ে পায়ে ফেরে আর মন থেকে জিন-পরি তাড়াতে তাড়াতে, গোপন সুখের তাড়নায় ভেবে নেয়— কী যেন বলে গেল! কবে আসবে! দু’দিন ছাড়া ছাড়া! কাল নয়। পরশু নয়। তার পরের দিন।