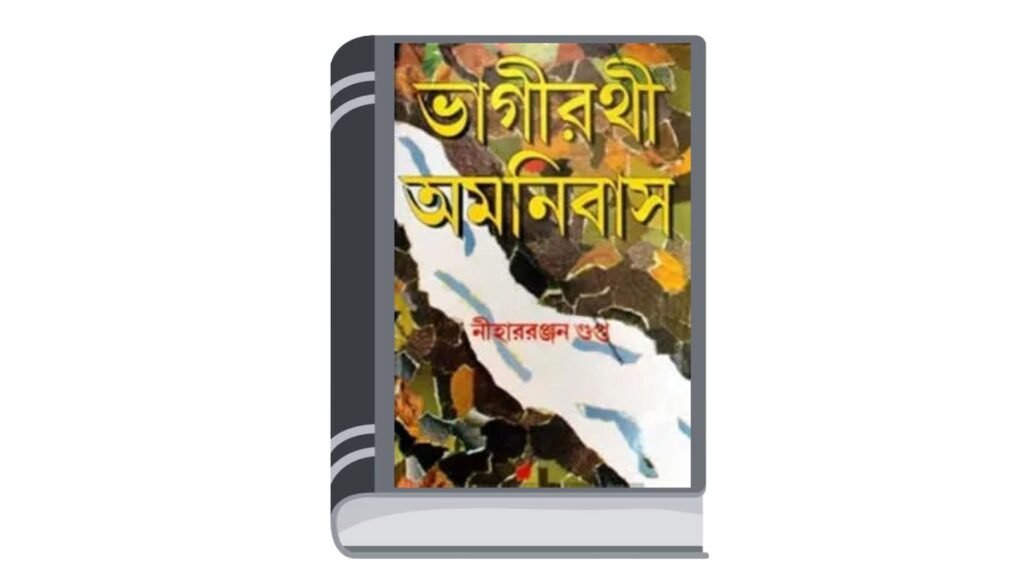মধুমতী থেকে ভাগীরথী – ১৬
॥ ষোল ॥
আনন্দচন্দ্র ও অন্নদাসুন্দরীর যুগটা সেই যুগ, যে যুগে ইংরেজী শিক্ষার আলোকে দেশ জুড়ে একটা রীতিমত সামাজিক বিপ্লব চলেছে ভিতরে ভিতরে এবং যেটা শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই—বলতে গেলে, সেই ইংরেজ যখন ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এক নতুন যুগের বীজ রোপণ করতে শুরু করেছিল এ দেশের মাটিতে, পাকাপোক্ত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্গে সঙ্গে।
অবিশ্যি সেই নয়া যুগের যারা ধারক ও বাহক সেই সামান্য কয়েকজন চিহ্নিত ব্যক্তি, যারা ইংরেজের স্নেহচ্ছায়ায় নিজেদের আখের গুছিয়ে সমাজে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল, তাদের বাদ দিলে যারা, তাদের মধ্যে তখনো কেউই বড় একটা ওই যুগের সামাজিক বিপ্লবে তেমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি, গতানুগতিকের মধ্যেই গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে।
সংস্কৃত ভাষায় তেমন দখল না থাকায় হিন্দু ধর্মের আসল তত্ত্বটা তাদের নাগালের বাইরেই থেকে গিয়েছিল। বেদের যে আসল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তার কোন সন্ধান পায়নি বলে ধর্মের ভিতরে সত্যটাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের খোলসটাকে নিয়ে তার উপরে আরো এক পৌঁচ নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা মত রঙ চড়িয়ে তারা ধর্মের নামে মাতামাতি করত। তারা তখনো ধর্মাচরণ বলতে বুঝত গুরুভজনা, দোল-দুর্গোৎসব, বলিদান, নন্দোৎসব, কীর্তন, গঙ্গাস্নান, অনশন, ব্রাহ্মণ- বৈষ্ণকে দান, তীর্থভ্রমণ, পুষ্করিণী খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।
তাদের ধারণা ছিল, ওই সব কিছুর দ্বারাই সমস্ত প্রকার পাপ হতে বুঝি মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তারপর বিপ্লব যখন আরো প্রকট হয়ে উঠল, তাদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত পড়ল এবং যিনি সেদিন কুঠারাঘাত করেছিলেন তিনি রাজা রামমোহন রায়— পারসী, আরবী, সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা তাঁর কর্মজীবনের শুরুতেই ধর্ম-সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এ দেশে, বিপ্লবের আগুন তিনি ক্রমশ ভাল করেই জ্বেলে দিলেন। রাধারমণ মল্লিক মশাইয়ের স্বর্গীয় পিতার সেই যুগটা। যুগের প্রভাব অনিবার্যভাবে তাঁর উপরেও কিছুটা পড়েছিল। কিন্তু তথাপি তিনি রাজার একেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মজ্ঞানকে মেনে নেননি, বেদান্ত-দর্শনের অনুবাদও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি তেমন। তিনি দোল-দুর্গোৎসব পূজা-পার্বণ তখনো হিন্দুর অবশ্যকরণীয় বলে মানতেন, অর্থাৎ সেদিনকার সেই বিপ্লব পুরোপুরি তাঁর উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি।
তিনি ইংরেজদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের সঙ্গে খানাপিনা করতেন, কিন্তু সেইসঙ্গে আবার নিত্য প্রাতে গঙ্গাস্নান করতেন; পূজা-পার্বণও চালিয়ে গিয়েছেন।
ছেলে রাধারমণ মল্লিকের সময় যুগটা আরো এগিয়ে গিয়েছে তখন, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা যেন এক নতুন চেতনার দ্বার তখন খুলে দিয়েছে, যদিও সেই শিক্ষার উগ্রতা বা ঝাঁজটা আজকাল বেসামাল করে দিচ্ছে। সে এক বিশ্রী টালমাটালের যুগ। প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন রাধারমণ মল্লিক মশাই। তাই বোধ করি তিনি সেদিন সেই বিপ্লবের আসল রূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল বোধ করি বিশেষ একটি ব্যক্তির জন্যই—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
রাজা রামমোহনের কর্মযজ্ঞের রশিটা তখন তিনি তাঁর শক্ত হাতের মুঠোয় ধরেছেন এবং ক্রমশ তার প্রভাব একটু একটু করে জনগণের মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পাশাপাশি তখনো চলেছে আর এক সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা সে যুগের তরুণ দলের মধ্যে, হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে।
আনন্দচন্দ্র সেই তরুণ দলেরই একজন হলেও তখনো তার মনের মধ্যে থেকে পূর্বপুরুষদের সংস্কার অনেকখানিই রয়েছে।
অবিশ্যি এটা ঠিক, ছেলেবেলায় গ্রামে থাকাকালীন যাই সে দেখুক বা শুনুক না কেন এবং যাই মনে মনে সত্যি বলে মেনে নিক না কেন, বিধবা পিসীদের দুঃখে যেমন তার মন কেঁদেছে নিরুপায় বেদনায়, তেমনি কেঁদেছে সুহাসিনীর বৈধব্যদুঃখে।
মনে হয়েছে এও যে, এ অন্যায়, এ অত্যাচার। কিন্তু ওই পর্যন্তই, তার বেশী কিছু নয়! মনে হয়েছে সুহাসিনীকে দেখে; মনে প্রশ্ন জেগেছে, সুহাসিনী যে বিধবা সেটা কি তার দোষ? যে দোষে সে নিজে দোষী নয় তার ফলভোগটা আজ তাকে করতে হচ্ছে বলেই না তার আত্মা আজ ভিতরে ভিতরে অমন করে বিদ্রোহিনী হয়ে উঠতে চায়! গূঢ় ধর্মের মর্ম বুঝুক, না-বুঝুক—ধর্মের অনুশাসনগুলো তাকে মেনে চলতেই হবে?
কিন্তু কেন?
আনন্দচন্দ্র সে রাত্রে দীঘির পাড় থেকে ফিরে সেই কথাগুলোই ভাবছিল। সারাটা জীবন বলতে গেলে এখনো সুহাসিনীর সামনে পড়ে আছে, পড়ে আছে জীবনের দীর্ঘ পথ। আজ তার বাপ রাধারমণ মল্লিক মশাই বেঁচে আছেন। রাধারমণ মল্লিক মশাইয়ের বিরাট সম্পত্তি, যে সম্পত্তির জন্য দূর ও নিকট আত্মীয়ের দল ওঁৎ পেতে বসে আছে কবে মৃত্যু হবে ওই মানুষটার, আর তারা সকলে মিলে ছেঁড়াছিড়ি কামড়াকামড়ি করবে!
তখন সুহাসিনীর কি হবে? কে সুহাসিনীকে রক্ষা করবে?
দূর ছাই, সুহাসিনীর কথা এত সে ভাবছেই বা কেন? উঠে পড়ল আনন্দচন্দ্ৰ, আজ আর পড়াশুনা হবে না, রন্ধনশালায় গিয়ে খেয়ে এসে শুয়ে পড়া যাক।
অন্দরবাড়িতে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হল আনন্দচন্দ্র। রান্নাঘরের আশেপাশে কেউ নেই। কাউকেই দেখতে পেল না আনন্দচন্দ্র। উন্মুক্ত কবাটপথে রন্ধনশালার মধ্যে উঁকি দিল।
উনুনে একটা বিরাট কড়াইয়ে কি যেন ফুটছে, মঙ্গলা দিদি সেই দিকে তাকিয়ে বসে আছে।
একটু যেন ইতস্তত করল, তারপর আনন্দচন্দ্র ডাকল মৃদুকণ্ঠে, মঙ্গলা দিদি!
কে? কড়াইয়ে হাতটা নাড়তে নাড়তেই সাড়া দিল মঙ্গলা।
আমি আনন্দ।
আনন্দ! কিছু বলছিস বাবা?
মঙ্গলা দিদি, তোমার রান্না হয়েছে?
ডাল ভাত তরকারি হয়ে গিয়েছে, মাছটা এখনো বাকী। একটু ঘুরে আয় না বাবা-
যা হয়েছে তাই দাও মঙ্গলা দিদি, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।
তবে পিঁড়িটা নিয়ে বসে পড়।
আনন্দ আর দেরি করে না, একটা পিঁড়ি পেতে এক গ্লাস জল কলসী থেকে গড়িয়ে নিয়ে বসে পড়ল।
মঙ্গলা আনন্দকে ভাত বেড়ে দিল থালায়—হ্যাঁ রে আনন্দ!
কি, মঙ্গলা দিদি?
দীঘির ঘাটে তুই গিন্নীকে কি বলেছিস?
কই, কিছু তো বলিনি!
ভোলার কথা কি বলেছিস?
আমি তো কিছু বলিনি। গিন্নীমাই বলেছিলেন-
কি বলেছিলেন?
ওই সুহাসের কথা—
কাদু ঠাকরুণ কি করে যেন শুনেছে কথাটা, একটু আগে সে এখানে এসে আমাকে যা নয়-তাই শুনিয়ে গেল। আর শোনাবেই বা না কেন? ওই ছেলের জন্য দেখছি আমাকে একদিন গলায় দড়ি দিতে হবে। কাঁদতে লাগল মঙ্গলা।
ভোলাদাকে তুমি একটু সমঝে দিলেই তো পার মঙ্গলা দিদি।
ও কি ভাল কথা শোনার ছেলে রে, অলপ্পেয়ে হতচ্ছাড়া বোঝে না, কর্তাবাবুর কানে গেলে কথাটা ওর এই আশ্রয় আর মুখের অন্ন ঘুচবে, সেই সঙ্গে আমারও। তারপর একটু থেমে মঙ্গলা ডাকল, আনন্দ!
কি, মঙ্গলা দিদি?
তোকে তো ও খুব ভালবাসে, এক ঘরে তোরা থাকিস, ওকে একটু বুঝিয়ে বলবি
বাবা আনন্দ!
আমার কথা কি শুনরে ভোলাদা?
তবু একবার বলিস বাবা বুঝিয়ে
বলছ যখন বলব।
আনন্দের আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে এঁটো থালা নিয়ে উঠে পড়ল। মঙ্গলা দিদিকে তো সে কথা দিয়ে এল, কিন্তু ভোলাদার সঙ্গে এক ঘরে থাকলেও দেখাই বা তার সঙ্গে কখন হয়! ভোলা যে কখন কোথায় থাকে তাই জানে না সে। রোজ রাত্রে ঘরে শুতেও আসে না। তবু বলতে হবে ভোলাদাকে কথাটা তার একবারটি।
কিন্তু সেরাত্রে রাধারমণ সিন্দুক থেকে টাকার তোড়া নিয়ে কোথায় গেলেন? এত রাত্রে হঠাৎ তাঁর কেন টাকার দরকার পড়ল?
বরাবরই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ ছিলেন রাধারমণ মল্লিক। তখনকার দিনে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের যে সব খেয়াল বা শখ বা নেশা ছিল—বুলবুলির লড়াই দেখা, ঘুড়ি ওড়ানো, অধিক রাত্রি পর্যন্ত বারাঙ্গনাদের ঘরে গিয়ে নৃত্যগীত শোনা বা তাদের সঙ্গে করে নৌকাভ্রমণ—সে সবের কিছুই ছিল না। অর্থাৎ তাঁর কোন বদ নেশাই ছিল না। সাহেবসুবোদের ঘরে যেতেন, গানবাজনা মধ্যে মধ্যে শুনতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁদের সঙ্গে খানাপিনাও করতেন, এবং যা কিছু করতেন সব তাঁর ব্যবসার জন্য। বন্ধু বলতে তাঁর বড় একটা কেউ ছিল না, একমাত্র জানকী দত্ত ছাড়া।
জানকী দত্তও এককালে খুব নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর পড়তি অবস্থা। জানকী দত্তর একটি রক্ষিতা ছিল—জলদবালা।
জানকী দত্তর চাইতে বয়েসে অনেক ছোট। বলতে গেলে তাঁর বড় কন্যা কমলিনীর বয়েসী। শহরে জলদবালাকে একটা বাড়ি করে দিয়েছিলেন জানকী দত্ত এবং দিবারাত্র বেশির ভাগ সময় তারই গৃহে পড়ে থাকতেন। সরকার, কর্মচারীরা তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করতেন এবং কর্মচারীদের হাতে ব্যবসার ভার ও দায়িত্ব থাকলে যা হবার তাই হয়েছিল। তবু জানকী দত্তর খেয়াল ছিল না।
মধ্যে মধ্যে জানকী দত্ত রাধারমণ মল্লিকের কাছ থেকে ধার নিতেন। রাধারমণ জানতেন যে টাকা কোনদিনই আর জানকীর কাছ থেকে ফিরে পাবেন না। তবু ধার দিতেন বন্ধুকে।
সেদিন দ্বিপ্রহরে জানকীর একজন কর্মচারী এক জরুরী পত্র নিয়ে এসেছিল, জানকীর কিছু টাকার দরকার। টাকাটা যেন রাধারমণ কর্মচারীর হাতেই দেন। কিন্তু টাকার পরিমাণটা একটু বেশী হওয়ায় রাধারমণ জানকীর কর্মচারীর হাতে টাকাটা দেননি। অতগুলো টাকা দিয়ে তাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই তাকে বলেছিলেন, সন্ধ্যার পর তিনি নিজে গিয়ে জানকীকে টাকা দিয়ে আসবেন।
কিন্তু সারাদিনে কাজের ভিড়ে কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন রাধারমণ। গদিতে বসে হিসাব দেখতে দেখতে হঠাৎ কথাটা মনে হওয়ায় গৃহে চলে আসেন সিন্দুক থেকে টাকাটা নেবার জন্য।
টাকা নিয়ে রাধারমণ সোজা গেলেন জানকী দত্তর গৃহে, কিন্তু তাঁকে পেলেন না গৃহে। জানকীর এক ছোট ভাই ছিল শিবনাথ, সে বললে, দাদা কি এ সময় বাড়িতে থাকেন!
তবে কোথায় থাকে?
তাঁর রক্ষিতা জলদবালার গৃহে।
কথাটা এই প্রথম শুনলেন রাধারমণ। বললেন, জানকীর একটি রক্ষিতা আছে নাকি?
সে তো অনেক দিন। আপনি জানেন না সেকথা?
না তো। কখনো ত সে বলেনি। তা সে রক্ষিতা কোথায় থাকে?
শিবনাথ ঠিকানাটা বলে দিল।
চিন্তিত রাধারমণ বের হয়ে গেলেন জানকীর গৃহ থেকে।
জানকীর চরিত্র সম্পর্কে কানাঘুষায় ইতিপূর্বে অনেক কথাই রাধারমণের কানে এসেছে, কিন্তু রাধারমণ সে-সব কথায় কখনো কান দেননি। অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির লোক বরাবর জানকী দত্ত। নিত্য গঙ্গাস্নান, পূজাআর্চা করেন, কখনো কারো সঙ্গে এক পয়সারও তঞ্চকতা করেননি। খানিকটা ভীরু প্রকৃতিরও মানুষটা, বরাবর দেখে এসেছেন জানকীকে। সেই লোকের এতটা অধঃপতন হতে পারে রাধারমণ বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আজ তার নিজের সহোদর ভাই শিবনাথের মুখে কথাটা শুনে রাধারমণ যেন সত্যি- সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যা শুনেছেন লোকপরম্পরায় তা হলে মিথ্যা নয়!
জানকী দত্তর গৃহ হতে নির্গত হয়ে একবার ভাবলেন নিজের গৃহেই ফিরে যাবেন টাকাগুলো নিয়ে, কারণ ওই চরিত্রের লোককে টাকা ধার দেওয়ার কোন মানেই হয় না। আবার পরক্ষণেই মনে হল তাঁর, হয়ত সত্যিই বিপদে পড়েছে জানকী, তাই চিঠি দিয়ে টাকার জন্য সকালে তার গদিতে লোক পাঠিয়েছিল। বন্ধুর বিপদের সময় বন্ধু যদি একটু উপকারই না করতে পারল তো কিসের বন্ধুত্ব!
শিবনাথের ঠিকানানুযায়ী হাঁটতে লাগলেন রাধারমণ। বেশী দূর নয় — কাছেই।
বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। দরজায় ধাক্কা দিতেই অন্দর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এল, কে গা?
দরজাটা খুলুন।
দরজা খুলে গেল, হাতে একটি ছোট সেজবাতি—একত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়স্কা এক যুবতী সামনে দাঁড়িয়ে। যুবতীর দিকে তাকিয়ে যেন রাধারমণের চোখের পলক আর পড়ে না।
তাঁর নিজের স্ত্রী অন্নপূর্ণা সত্যিই সুন্দরী এবং সুন্দরী স্ত্রীলোক যে ইতিপূর্বেই দেখেননি রাধারমণ তাও নয়। বহু সুন্দরী স্ত্রীলোক জীবনে তিনি দেখেছেন, কিন্তু ঐ মুহূর্তে সেজবাতিটি হাতে যে যুবতী স্ত্রীলোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে, তার রূপের বুঝি তুলনা নেই।
পাতলা দেহের গড়ন। কাজল-টানা দুটি ডাগর চক্ষু, দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে একটি কাঁচপোকার টিপ, বাতির আলো পড়ে টিপটি চিকচিক করছে। পাতা কেটে চুল বাঁধা, পরনে একখানি শান্তিপুরী চওড়া লালপাড় জলডুরে তাঁতের শাড়ি। দুই হাতের হাঙ্গরমুখী কঙ্কন ও কয়েকগাছি করে সোনার চুড়ি। ওষ্ঠ দুটি পানের পিকের রসে লাল টুকটুক করছে।
কাকে চাই গো?
জানকী আছে?
দত্ত মশাই? হ্যাঁ, আছেন।
কোথায়?
উপরে। আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?
গিয়ে বল রাধারমণ মল্লিক এসেছেন।
আসুন আসুন। আগ্রহের সঙ্গে ‘আসুন’ ‘আসুন’ বলেও যেন হঠাৎ কেমন থমকে দাঁড়ায় যুবতী।
তা তুমি কে?
ফিক করে হেসে ফেললে যুবতী। তারপর স্মিত কণ্ঠে বললে, আমি?
হ্যাঁ!
আমি জলদবালা।
ওঃ, তাহলে এই জানকীর রক্ষিতা জলদবালা! নিজের অজ্ঞাতেই যেন রাধারমণের ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। একবার মনে হল ফিরে যাবেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার জলদবালার আহ্বান শুনে তাকালেন তার মুখের দিকে।
আসুন মল্লিক মশাই। দত্ত মশাই উপরে আছেন—
হ্যাঁ, চল।
বাড়িটি ছোট। নীচে বোধ করি খানচারেক ঘর। একটি আঙ্গিনা—আঙ্গিনাটা অন্ধকার, সরু সিঁড়ি—অন্ধকার।
জলদবালা বললে, আমি আলো ধরছি, আপনি এগিয়ে চলুন মল্লিক মশাই।
রাধারমণ জলদবালার কথার কোন জবাব দিলেন না। জলদবালার প্রদর্শিত আলোয় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।
দোতলায় একখানি বারান্দা। বারান্দার দেওয়ালে একটি ছোট দেওয়ালবাতি জ্বলছে, কিন্তু সে আলো পর্যাপ্ত নয়, একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। সাধনের একটা ঘরের উন্মুক্ত কবাটপথে আলো দেখা যাচ্ছিল।
যান, ওই ঘরে আছেন দত্ত মশাই।
রাধারমণ কক্ষমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন। একটা পালঙ্কের উপর শায়িত ছিলেন জানকী দত্ত। গায়ে একটা বালাপোশ। চক্ষু দুটি মুদ্রিত। রাধারমণ ইতস্তত করেন, ডাকবেন কি ডাকবেন না বন্ধুকে।
জানকী শুয়ে আছে—ঘুমুচ্ছে নাকি? জলদের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রাধারমণ।
আজ দু’দিন থেকে দত্ত মশাইয়ের জ্বর। মৃদু গলায় জলদবালা বললে।
জ্বর?
হ্যাঁ।
কে? জানকী দত্ত সাড়া দিলেন ওই সময়
জানকী, আমি!
কে?
আমি রাধারমণ।
জানকী তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করেন। তুমি-তুমি রাধারমণ!
থাক থাক, উঠো না।
কিন্তু কথা শুনলেন না, ততক্ষণে শয্যার উপর উঠে বসেছেন, তুমি—তুমি এখানে আসতে গেলে কেন রাধারমণ? আমার এখানকার খবর তোমাকে কে দিলে?
জানকীর কথার জবাব দিলেন না রাধারমণ। অন্য কথা বললেন, দ্বিজপদকে সকালে তুমি পাঠিয়েছিলে আমার কাছে চিঠি দিয়ে?
হ্যাঁ, কিছু টাকার জন্য।
কিন্তু সে তো কই বললে না যে তুমি এত অসুস্থ, জানকী!
জলদবালা সেজবাতিটা হাতে অল্পদূরে দাঁড়িয়েছিল। সে বাতিটা এক পাশে নামিয়ে রেখে একটা ছোট জলচৌকি এনে সামনে রেখে বললে রাধারমণকে, বসুন।
রাধারমণ আর একবার জলদবালার মুখের দিকে না তাকিয়ে যেন পারলেন না। এ কি অপরূপ সৌন্দর্য! এমনটি তো আর তিনি কখনো দেখেননি!
জলদবালাও রাধারমণের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। দুজনের চোখাচোখি হতেই সে তার চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিল।
জানকী! ডাকলেন রাধারমণ।
বল ভাই?
তোমার টাকাটা এনেছি।
ওটার আর প্রয়োজন হবে না ভাই।
প্রয়োজন হবে না কেন?
না, আমার সর্বস্ব আজ নারায়ণ চৌধুরীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।
সে কি!
হ্যাঁ, ভাই। দেনায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওই টাকাটা দিয়ে কিছুদিন চৌধুরী মশাইকে ঠেকিয়ে রাখব। তারপর মনে হল সে তো দু’দিন, তারপর কি হবে? তবু যদি বসতবাটিটা থাকে—তাই তার প্রস্তাবে একমাত্র ওই বসতবাটিটুকু ছাড়া সব তার হাতে তুলে দিলাম। বিক্রয়-কোবালাও আজ দুপুরে সই হয়ে গিয়েছে।